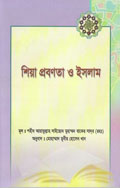শিয়া প্রবণতা ও ইসলাম
মূল: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)
অনুবাদ: মোহাম্মাদ মুনীর হোসেন খান
শিয়া প্রবণতা ও ইসলাম
মূলঃ শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)
অনুবাদঃ মোহাম্মাদ মুনীর হোসেন খান
সম্পাদনাঃ মোহাম্মাদ আশরাফউদ্দিন খান
সহযোগিতায়ঃ আল মুয়াম্মাল কালচারাল ফাউন্ডেশন,কোম ইরান এবং শহীদ আল্লামা বাকের সাদর (রহ.)বিশ্ব সম্মেলন কমিটি,কোম,ইরান।
প্রকাশকঃ আমার দেশ বাংলাদেশ সোসাইটি (সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান)
প্রকাশকালঃ ২১ রমজান,১৪৩০ হিজরী,১২ সেপ্টেম্বর,২০০৯ খৃষ্টাব্দ
Shia probanata o islam, Author: Shaheed Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, Translator: Muhammad Munir Hossain Khan, Editor: Muhammad Ashrafuddin Khan, Sponsored: Al-Mu’ ammal Cultural Foundation and Muzes fee Usule Din of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, qum, Iran. Published by: Amar desh Bangladesh Society. ৩২/১, T.B Cross Road, Khulna, Bangladesh.
সম্মেলন কমিটির বক্তব্য
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী আত-তাহেরীন।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে ছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। যার পরিণতিতে বিচ্যুত,অবনতি আর জড়তার আধার উম্মাকে ছেয়ে ফেলেছিল। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুসলিম উম্মার পুনর্জাগরণ শুরু হয়। ইমাম খোমেইনীর (রহ.)নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে তা পরিপুর্ণতা অর্জন করে,ইসলামী শক্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়।দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী ও অত্যাচারীদের হাতে শোষিত হওয়ার পর উম্মার ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার সে শক্তি সঞ্চয় করেছে,মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। মুসলিম উম্মার এ পুনর্জাগরণ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে,উপনিবেশবাদী লোলুপ দৃষ্টি পোষণকারীদের আশা আকাঙ্ক্ষার কবর রচনা করেছে।
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মার মধ্যে আজ যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে ইমাম খোমেইনী(রহ.)মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি চিন্তাগত ও তত্ত্বগত দিক থেকে উম্মার মধ্যে যে জোয়ার এসেছে সেক্ষেত্রে শহীদ আল্লামা বাকের সাদর নিঃসন্দেহে মৌলিক অবদান রেখেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন নজিরবিহীন। তার চিন্তাধারা ও লেখনি একদিকে যেমন চিন্তার জগতে নব-দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে অপরদিকে গভীরতা ও ব্যপকতার দিক থেকেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন চিন্তাধারার পারস্পরিক সংঘাতময় পরিবেশেও তিনি বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদদের মহলে ব্যাপকভাবে ইসলামী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।
শহীদ আয়াতুল্লাহ বাকের সাদর তার নজিরবিহীন ব্যক্তিত্ব,অসাধারণ যোগ্যতা ও গতিশীল ইসলামী চিন্তাধারার মাধ্যমে আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদেরকে অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। বস্তুবাদী সভ্যতার তত্ত্বগত ভিত্তিহীনতা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি সবাইকে চিন্তাগত দাসত্বের শৃঙ্খল,(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের)অন্ধ অনুকরণ ও খোদাবিমুখতা থেকে ফিরিয়ে রাখেন। বাস্তব জীবনে মানব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের যে নজিরবিহীন ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন আধুনিক বিশ্ব যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাহলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকুলের সৌভাগ্য রচিত হবে,মানব সমাজ কল্যাণ লাভ করবে।
শহীদ আল্লামা বাকের সাদর অত্যন্ত গতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তার চিন্তাধারা কোন বিশেষ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলনা,বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি,তুলনামূলক দর্শন (ইসলামী ও পশ্চাত্য দর্শন),আধুনিক যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সাম্প্রতিককালে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেছেন এবং নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। উসূল ও ফেকাহশাস্ত্র,দর্শনশাস্ত্র,যুক্তিবিদ্যা,কালামশাস্ত্র,তাফসীর,ইতিহাস ইত্যাদি ক্লাসিক বিষয়েও পদ্ধতিগত ও বিষয়-বস্তুগত উভয় দিক থেকে নতুন নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং চিন্তাগত বিপ্লব ঘটিয়েছেন।
আল্লামা বাকের সাদরের শাহাদতের পর দু’ দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে,কিন্তু আজও পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে তার চিন্তাধারার প্রভাব অটুট রয়েছে। যে কোন বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তার রেখে যাওয়া রচনাবলী,বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন তা সবার জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকবে।
এ দৃষ্টিকোণ থেকেই শহীদ আল্লামা বাকের সাদর বিশ্ব সম্মেলন পরিচালনা কমিটির প্রধান দায়িত্ব হবে চিন্তাগত ও জ্ঞানগত বিভিন্ন বিষয়ে তার রেখে যাওয়া মূল্যবান রচনাবলীর পুনরুজ্জীবন ও উপযুক্ত সংরক্ষণ। যেহেতু তার রচনাবলী অত্যন্ত ব্যাপক তাই এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনের ক্ষেত্রে দু’ টি দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবেঃ
প্রথমতঃ অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও সূক্ষ্ণ দৃষ্টিসহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এগুলোর অনুবাদ এবং প্রকাশ।
দ্বিতীয়তঃ অত্যধিকবার প্রকাশিত হওয়া এবং উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে তার প্রকাশিত অনেক বই যেগুলো আংশিকভাবে বিকৃত হযেছে সেগুলোকে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং সংশোধন করা।
সবশেষে আমরা আল্লামা বাকের সাদরের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের,বিশেষ করে তার স্বনামধন্য পুত্র জনাব সাইয়্যেদ জাফর সাদর(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)-এর অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লামা বাকের সাদরের বিভিন্ন রচনাবলী প্রকাশ ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ সম্মতি প্রদান করেছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
পরিচালনা কমিটি
শহীদ আল্লামা বাকের সাদর বিশ্ব সম্মেলেন
ভূমিকা
ইসলামে শিয়াদের ইতিহাস রক্ত আর অশ্রুর ইতিহাস। শিয়া ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিজীবি মহলে শিয়া মতবাদকে ভূলভাবে বুঝা হয়ে থাকে এবং তাই তার ভূল ব্যাখ্যা দেয়া হয়। শীর্ষস্থানীয়দের সামান্যতম কু-ধারণা কালক্রমে জনতার কাছে বিপদজনক আকার ধারণ করে। পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের মাঝে সামান্যতম মতপার্থক্য বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ উপমহাদেশের স্বণামধন্য ব্যক্তিগণ তথা নবাব সিরাজউদ্দৌলা,টিপু সুলতান,হাজী মুহাম্মদ মুহসীন,তীতুমীর প্রমূখ জা’ ফরী ফিকাহ (শিয়া মাজহাব)এর অনুসারী হওয়া স্বত্বেও এবং এ দেশে আগত অনেক পীর-কামেল ইমাম হযরত আলী (আ.)এর ধারার অনুসারী হওয়ার পরও এ‘ মাযহাব’ বিরুদ্ধবাদীদের বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতবিক্ষত। এর অন্যতম কারণ বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এ সম্পর্কে তেমন কোন বাংলা বই পুস্তক ও কিতাবাদি ছিল না এবং বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে দ্বীনের দাওয়াতী ও প্রচারমূলক কর্মকান্ডও তেমন লক্ষণীয় ছিল না।
“ আন-নাশআ-তুশ-শীয়া” মহান মনীষী ও গবেষক শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহ.)-এর আরবী ভাষায় লিখিত একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শীয়া মতবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলে এ‘ মাযহাব’ সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর ফলে সার্বিকভাবে উপকৃত হবে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ।
এ বইটি মূল আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের দেশের বিশিষ্ট গুণীজন ও অনুবাদক জনাব মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান এক অনবদ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট আলেম জনাব মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন খান। তাদের উভয়কে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করায় জনাব আলী নেওয়াজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি অনুবাদে সহযোগিতা করায় শহীদ আল্লামা বাকের সাদর (রহ.)বিশ্ব সম্মেলনে কমিটি,কোম, ইরান এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
অবতরণিকা
কিছু কিছু আলোচক ও পর্যালোচক মুসলিম উম্মাহ্ বহির্ভূত এক সম্প্রদায় হিসেবে“ শিয়া মাযহাব” সর্ম্পকে আলোচনা করে থাকেন । তাঁরা এ মাযহাবটিকে মুসলিম উম্মাহর এমন এক অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন যার উদ্ভব কালক্রমে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সামাজিক ঘটনা ও পরিবতর্নের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে,এ সব ঘটনা প্রবাহ ও পরিবর্তনসমূহ মুসলিম উম্মাহর সেই অংশ-বিশেষের (শিয়া মাযহাব) চিন্তাগত ও মাযহাবী অস্তিত্বের এক বিশেষ রূপরেখা প্রদান করেছে । অতঃপর ধীরে ধীরে সেই অংশটি (সম্প্রদায়টি) বিকাশ লাভ করতে থাকে ।
এসব আলোচক ও পর্যালোচক (শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি সংক্রান্ত) এ ধরনের ধারণা পোষণ করার পাশাপাশি ঐ সব ঘটনা ও পরিবর্তন সর্ম্পকেও যথেষ্ট মতপার্থক্য পোষণ করে থাকেন যা শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ । এসব আলোচক ও পর্যালোচকের মধ্যে কারো কারো ধারণা হচ্ছে এই যে,‘‘ আবদুলাহ্ বিন সাবা ” ও তার কল্পিত রাজনৈতিক তৎপরতাই শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির মূল কারণ । ১ আবার কোন কোন পর্যালোচক ইমাম আলী (আ.)-এর খেলাফত কাল এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে ‘‘ শিয়া মাযহাবের ” উৎপত্তি সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন । ২ আবার কোন কোন আলোচক মনে করেন যে, ইমাম আলী (আ.)-এর খেলাফত-কালোত্তর মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের মাঝেই নিহিত রয়েছে শিয়া মাযহাবের উৎপত্তির কারণ । ৩
আমার দৃষ্টিতে যে কারণে এসব আলোচকের অনেকেই শিয়া মাযহাবকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বহিরাগত (অনুপবেশকারী) এক সম্প্রদায় হিসেবে ধারণা করছেন,তা হল এই যে,শিয়া সম্প্রদায় ইসলামের শুরু থেকেই মুসলিম উম্মাহর এক সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ বই আর কিছুই ছিল না।
আর এ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,শিয়া না হওয়া ছিল সে সময়কার মুসলিম সমাজে প্রচলিত একমাত্র নিয়ম । আর শিয়া হওয়াটাই ছিল সেই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম এবং (মুসলিম) উম্মাহ্ বহির্ভূত এমন বিষয় বা ঘটনা যার উৎপত্তির কারণসমূহ (তৎকালীন) প্রচলিত অবস্থার বিপক্ষে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ক্রমবিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ।
অথচ সংখ্যাধিক্য এবং আপেক্ষিক সংখ্যালঘুতকে নিয়ম ও ব্যতিক্রম নির্ণয় বা মূল-অমূলের পার্থক্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় । তাই সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে শিয়া বহির্ভূত ইসলামকে মৌলিকত্ব প্রদান এবং সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে শিয়া ইসলামকে অমূলক ও ইসলাম বহির্ভূত বলে বিবেচনা করাটাও এক মারাত্মক ভুল । কেননা এটা বিশ্বাস-কেন্দ্রিক বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি বিরোধী । কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমরা একই রিসালতের অবকাঠামোর মধ্যে বিশেষ কোন বিশ্বাস-কেন্দ্রিক বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকি যা উক্ত রিসালতের কতিপয় চিহ্ন ও নিদর্শনের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান মতপার্থক্যভিত্তিক । আবার কখনো কখনো দু‘ টি আদর্শিক (বিশ্বাস-কেন্দ্রিক) সম্প্রদায় যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে সমান নয়,তবুও সমানভাবে বিতর্কিত ঐ রিসালতটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে । যেমনভাবে ইসলামী রিসালতের অবকাঠামোর আওতায়‘‘ শিয়া” তত্ত্বের উৎপত্তির বিষয়টি একটি পরিভাষা এবং মুসলমানদের মধ্যকার একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের এক বিশেষ নাম হিসেবে শিয়া বা তাশাইয়ু শব্দের সাথে জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না,তদ্রুপ সংখ্যাগত দিক থেকে শিয়া অশিয়া-এ দু’ ভাগে ইসলামী রিসালতের অবকাঠামোর ভিতরে আদর্শিক বিভক্তি সংক্রান্ত আমাদের ধারণাও কোনক্রমে সঠিক হবে না । কারণ শাব্দিক নাম ও পরিভাষাসমূহের উৎপত্তি এক জিনিষ আর অন্তর্নিহিত মূল নির্যাস বা বিষয়,সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি এবং (পান্ডিত্যপূর্ণ)তত্ত্বের উৎপত্তি আরেক জিনিষ। তাই মহানবীর জীবদ্দশায় বা তাঁর তিরোধানের পর প্রচলিত ভাষায় আমরা“ শিয়া” শব্দের অস্তিত্ব যদি খুজে নাও পাই তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে না যে,(মহানবীর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতোত্তর কালে) শিয়া তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না ।
সুতরাং এ মানসিকতার আলোকে শিয়া বা তাশাইয়ু (শিয়া প্রবণতা) সম্পর্কে আলোচনা এবং নিম্নোক্ত প্রশ্ন দু’ টির উত্তর দেয়া জরুরী । প্রশ্ন দু’ টি :
১ । শিয়া প্রবণতার(تشیع ) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে?
২ । শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে?
তাশাইয়ু বা শিয়া প্রবণতার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে?
v ভবিষ্যতের দাওয়াতের বিষয়ে নেতিবাচব পদক্ষেপ ।
v শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে মহানবীর (সা.) খলিফা নির্ধারণের ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
v সরাসরি বাছাই ও প্রত্যক্ষ মনোনয়নের ভিত্তিতে মহানবীর (সা.) উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করণের ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ শিয়া প্রবণতা বা তাশাইয়ুর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? আমরা এতদসংক্রান্ত চিন্তা করে বলতে পারি যে,তাশাইয়ু হচ্ছে পবিত্র ইসলাম ধর্মেরই এক স্বাভাবিক পরিণতি এবং সেই তত্ত্বেরই বাস্তব রূপ যা একমাত্র দাওয়াত বা ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সুষ্ঠু বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম । তাই এ প্রচার কার্যক্রম কর্তৃক তা অর্জিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । আর মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব,কার্যক্রমের গঠন-প্রকৃতি এবং তাঁর (সা.) সমসাময়িক পরিস্থিতি ও অবস্থার কারণেই দিয়েছিলেন । আর এ ইসলাম প্রচার কার্যক্রম থেকেই সরাসরি এ তত্ত্ব অর্থাৎ শিয়া মাযহাবের তত্ত্ব যুক্তিপূর্ণভাবে নির্ণয় করা সম্ভব ।
কারণ মহানবী (সা.) বৈপ্লবিক প্রচার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিতেন এবং তিনি সমাজ, সামাজিক রীতি-নীতি,প্রথা-ব্যবস্থা এবং চিন্তা ও ভাবধারায় বাস্তবে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেছেন । আর এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি ক্ষণস্থায়ী কোন প্রক্রিয়া ছিল না বরং তা ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক যা জাহেলিয়াত (অন্ধকার যুগ) ও ইসলাম ধর্মের মধ্যকার বিরাজমান আধ্যাত্মিক ব্যবধান ও পার্থক্যের মতই দীর্ঘ ও ব্যাপক । তাই যে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম মহানবী (সা.) তাঁর নিজ জীবদ্দশায় পরিচালনা করেছেন,কথা ছিল যে,তা জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগের অজ্ঞ,বর্বর মানুষকে এক নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবে এবং তাকে (আদর্শ) ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে,যে বিশ্ববাসীর কাছে নতুন আলোর বার্তা পৌঁছে দিবে এবং জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করবে ।
মহানবী (সা.) সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিস্ময়কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । আর উচিৎ ছিল যে,এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম প্রক্রিয়া এমনকি মহানবীর (সা.) ওফাতের পরও অব্যাহতভাবে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করবে । মহানবী (সা.) তাঁর ওফাতের কিছুকাল আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে,তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অতি নিকটবর্তী,তাই তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় বিদায় হজ্বেও ব্যক্ত করেছিলেন ।৪ আর মৃত্যুও তাঁর কাছে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়নি । এর অর্থ দাঁড়ায় যে,তিনি তাঁর ওফাতের পরে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন । এমনকি যদি এক্ষেত্রে আমরা অদৃশ্য জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক ঐশী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে রিসালতের সরাসরি সংরক্ষণ করার বিষয়টি আদৌ বিবেচনায় না আনি।
অতএব,এ আলোচনার আলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে,মহানবী (সা.)-এর সামনে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কেবলমাত্র তিনটি পথই উন্মুক্ত ছিল:
প্রথমতঃ নেতিবাচক পথ বা পদক্ষেপ।
দ্বিতীয়তঃ শূরা বা পরামর্শভিত্তিক ইতিবাচক পথ বা পদক্ষেপ এবং
তৃতীয়তঃ সরাসরি বাছাই,মনোনয়ন এবং নিযুক্তি ।
আর এক্ষেত্রে তিনটি আলোচনা রয়েছে ।
ভবিষ্যতের দাওয়াতের বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান
প্রথম পথ : খেলাফত বা মহানবীর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া এবং অবহেলা প্রদর্শন করা ।
আর এর অর্থ হল ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর নেতিবাচক পদক্ষেপ এবং কেবলমাত্র তাঁর নিজ জীবদ্দশায় ইসলামী প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বদান ও পথ-প্রদর্শনই যথেষ্ট মনে করা এবং ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কর্মকান্ডের ভবিষ্যৎকে অজ্ঞাত, অজানা পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং আকস্মিকতার হাতে ছেড়ে দেয়া ।
এ ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে মোটেও ভাবা যায় না । কারণ দু’ টি বিষয় থেকে এ ধরনের নেতিবাচকতার উৎপত্তি । আর এ দু’ টি বিষয় মহানবীর ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও চিন্তা করা যায় না (অর্থাৎ এ দু’ টি বিষয় মহানবী (সা.)-এর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না) ।
প্রথম বিষয় : এ ধরনের বিশ্বাস করা যে,খেলাফত বা মহানবীর উত্তরাধিকার ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন ভবিষ্যতে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের উপর মোটেও প্রভাব ফেলবে না এবং ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের আশু দায়িত্বভার গ্রহণকারী মুসলিম উম্মাহ্ নিজেই প্রচার কাজের সহায়ক যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিচ্যুতির হাত থেকে তা রক্ষা করতেও সক্ষম ।
আসলে এ ধরনের বিশ্বাসের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই । বরং প্রকৃত বাস্তবতা এর বিপক্ষে । কারণ তিনি ইসলাম প্রচার কার্যক্রমকে সূচনালগ্ন থেকেই এক বৈপ্লবিক সংস্কারমূলক কর্মকান্ড হিসেবে একটি জাতি গঠন এবং সব ধরনের জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার মূলোৎপাটন করার ব্রত ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন । আর এ প্রচার কার্যক্রম চরম বিপদের সম্মুখীন হবে যখন তা নেতা ও নেতৃত্ববিহীন হয়ে যাবে এবং তা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রূপরেখা ছাড়াই চলতে থাকবে । তাই এক্ষেত্রে বহু বিপদ রয়েছে । আর এসব বিপদ হচ্ছে :
প্রথমতঃ (ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যের) কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ও রূপরেখা না থাকার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা মোকাবেলা করার গতি-প্রকৃতি এবং মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের কারণে উদ্ভূত ব্যাপক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই পদক্ষেপ গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্ট বিপদসমূহ । কারণ মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন না করেই যদি ময়দান ত্যাগ করেন তাহলে প্রথম বারের মত এবং শীঘ্রই নেতাবিহীন অবস্থায় প্রচার কাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যা মোকাবেলা করার গুরুদায়িত্ব উম্মাহর উপরই বর্তাবে ।
আর এ ব্যাপারে উম্মাহর কোন পূর্ব-ধারণা ও অভিজ্ঞতাই নেই । সমস্যার ভয়াবহতা যতই তীব্র হোক না কেন এক্ষেত্রে উম্মাহর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ও অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যাশা করতে হবে । কেননা এ ধরনের শূন্যাবস্থা চলতে দেয়া যায় না । উম্মাহর প্রাণহানিকর এ ক্ষতির মুহূর্তে উম্মাহকে দ্রুত এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে । কারণ এমতাবস্থায় উম্মাহ্ অনুভব করতে পারে যে,তারা তাদের মহান নেতাকে হারিয়েছে । আর সেই সাথে মহান নেতাকে হারানোর প্রচন্ড আঘাত ও ক্ষতিটাও উম্মাহ্ উপলব্ধি করতে পারে যা মানুষের চিন্তাশক্তিকে প্রচন্ডভাবে স্থবির ও লন্ড-ভন্ড করে দেয়,এমনকি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রচন্ড আঘাত জনিত কারণেই ঘোষণা করতে থাকেন যে,“ মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবেনও না।” ৫ সুতরাং উম্মাহ্ কর্তৃক গৃহীত এ ধরনের পদক্ষেপ ও আচরণ হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক । আর এর পরিণতি কখনো শুভ হবে না ।
দ্বিতীয়তঃ রিসালতের দায়িত্ব পালনে মুসলমানদের যোগ্যতার অভাব এবং অপরিপক্কতা জনিত কারণে সৃষ্ট বিপদ ও সংকটসমূহ । আর এ রিসালতী যোগ্যতা ও পরিপক্কতা যে মাত্রায় আগেই মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের রিসালতী কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিশ্চয়তা বিধান করেছিল এবং যার ফলে তিনি (সা.) মুহাজির-আনসার,কুরাইশ-অকুরাইশ অথবা মক্কা-মদীনা কেন্দ্রিক শ্রেণী-বিভক্তির কারণে মুসলমানদের অন্তরে লুক্কায়িত বৈষম্য ও চাপা ক্ষোভ মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিক সেই মাত্রায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না ।
তৃতীয়তঃ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারী একটি গোষ্ঠী যারা সর্বদা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত তাদের থেকে উদ্ভূত বিপদাপদ ও সংকটসমূহ । আর এ গোষ্ঠীটিকে পবিত্র কোরানে মুনাফিক নামে অভিহিত করা হয়েছে।৬ আর এদের সাথে যদি আরো বিরাট সংখ্যক জনগণকে যোগ করি যারা মক্কা বিজয়ের পর বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করে কিন্তু সত্য গ্রহণের মানসিকতা না নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল,তাহলে আমরা এ সকল দল ও গোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট বিপদাপদ ও আশঙ্কার ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারব । আর এ সকল চক্র নিশ্চয়ই ময়দানে নেতার অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট বিরাট শূন্যাবস্থায় ব্যাপক অপতৎপরতা চালানোর এক মোক্ষম সুযোগও লাভ করে থাকবে ।
তাই মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর খলীফা বা উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের সীমাহীন গুরুত্ব শুধুমাত্র সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নয়,আদর্শিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এমন যে কোন নেতার কাছেই গোপন থাকা একেবারে অসম্ভব ।
আর হযরত আবু বকর যদি খেলাফত ও শাসন সংক্রান্ত সতর্কতা অবলম্বনের অজুহাতে প্রশাসনের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা বিধান করতে গিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ময়দান ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন৭ এবং যখন ঘাতকের হাতে আহত হওয়ার পর জনসাধারণ হযরত উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল,“ হে আমীরুল মুমেনীন,আপনি যদি কাউকে আপনার পরে খলিফা মনোনীত করতেন ?” ৮ আর মহানবী(সা.)-এর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রম যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সৃষ্টি করেছিল তা সত্ত্বেও এসব কিছুই ছিল খলীফার অবর্তমানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার আশঙ্কায় । আর জনসাধারণ খলীফা বিহীন অবস্থায় যে বিপদাপদের আশঙ্কা করেছিল খলীফা উমর সে আশঙ্কা ও অনুভূতির প্রতি সাড়া দিয়ে যখন পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করার জন্য ছয় জনের ব্যাপারে অসিয়ত করেছিলেন,৯ আর হযরত উমর যখন সকীফা দিবসে প্রথম খলিফা নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়াই হযরত আবু বকরের খেলাফত ও শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা ও প্রতিক্রিয়ার কথা উপলব্ধি করে বলেছিলেন,“ হযরত আবু বকরের বাইআত ছিল আকস্মিক ঘটনা তবে মহান আল্লাহ এ ঘটনার অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন ।” ১০ আর যখন হযরত আবু বকর ত্বরা করে শাসনভার গ্রহণ করার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছিলেন যে,তিনি খলীফা নিযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপক গুরুত্ব এবং যে কোন উপায়ে (মহানবীর ওফাতের পরে নেতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্ট সংকট ও সমস্যা) সমাধান করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,(আর তিনি শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য মৃদু নিন্দা ও ভৎসনারও শিকার হয়েছিলেন)“ মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন জনগণ জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগ থেকে সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ তারা নব্য মুসলমান) । তাই আমি ভয় পেলাম যে,তারা (নব্য মুসলমানরা) মহানবীর অবর্তমানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে । আর বন্ধুরাও আমার উপর জোর করেই খেলাফতের দায়িত্ব চাপিয়ে দিল ।” ১১ আর এসব কিছুই যদি সত্য হয় তাহলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের কর্ণধার এবং নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে নেতিবাচক পদক্ষেপের (অর্থাৎ মহানবীর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের পরিচালনা ও নেতৃত্ব দানের জন্য একজন খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত মনোনীত না করা) কুফল ও বিপদ ইতিবাচক পদক্ষেপের বাস্তবতার আলোকে এবং স্বয়ং হযরত আবু বকরেরও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগ থেকে সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী উম্মাহর আমূল সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের নিরিখে সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছিলেন এবং সবার চেয়ে বেশী অনুধাবন করেছিলেন ।
দ্বিতীয় বিষয় (স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি): দ্বিতীয় বিষয়টি যা সম্ভবতঃ নেতার মৃত্যুর পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতার নেতিবাচক পদক্ষেপের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারে তা হল যে,এ ধরণের নেতিবাচক পদক্ষেপের কুফল ও বিপদ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নেতা ঐ বিপদের মোকাবেলায় প্রচার কাজের সঠিক সংরক্ষণের জন্য কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাননি । কেননা তিনি প্রচার কার্যক্রমকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে দেখেন ও বিবেচনা করেন । তাই যে পর্যন্ত তিনি জীবিত আছেন কেবলমাত্র সে পর্যন্ত এ প্রচার কার্যক্রম থেকে লাভবান হওয়ার জন্যই উক্ত প্রচার কার্যক্রমটিকে টিকিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করাই হচ্ছে তার (নেতার) একমাত্র ব্রত ও উদ্দেশ্য । আর তার মৃত্যুর পরে দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তার কোন চিন্তা-ভাবনাই নেই ।
এ ধরনের ব্যাখ্যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য নয়,এমনকি যদি আমরা নবুওয়াত ও রিসালত সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে মনে নাও করি এবং তাঁকে অন্যান্য মিশনারী নেতার মত নিছক একজন মিশনারী নেতা হিসেবে বিবেচনা করি । কারণ জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম-ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা মহানবী (সা.) প্রদর্শন করেছেন তার কোন নজীর মিশনারী নেতাদের জীবনেতিহাসে বিদ্যমান নেই । তাঁর (সা.) পুরো জীবন থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত । তাই মহানবী (সা.) মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে এবং তীব্র অসুস্থতার মাঝেও এমন এক যুদ্ধের কথা চিন্তা করেছিলেন যার পরিকল্পনা তিনি নিজেই প্রণয়ন করেছিলেন এবং রণাঙ্গনে প্রেরণের জন্য তিনি নিজেই হযরত উসামা বিন যায়েদের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত ও সজ্জিত করেছিলেন । এ কারণেই তিনি (সা.) অসুস্থতা সত্ত্বেও বলেছিলেন,“ উসামার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কর- উসামার সেনাবাহিনীকে রণাঙ্গনে প্রেরণ কর ।” আর তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন আর কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর মূর্ছা ও যাচ্ছিলেন১২ । অতএব,কোন এক সামরিক বিষয়ে মহানবী (সা.) মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায়ও যদি এতবেশী উদ্বিগ্ন ও উৎকন্ঠিত থাকেন এবং উক্ত যুদ্ধের ফলাফল হাতে আসার আগেই যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তা তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়টি (অর্থাৎ উসামার নেতৃত্বে উক্ত সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করা) থেকে মোটেও বিরত না হন,আর আমরা এটাও দেখতে পাই যে,শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তেও মহানবী (সা.) ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছেন,তাহলে আমরা কিভাবে ভাবতে পারি যে,মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না বা কোন চিন্তা-ভাবনাও করবেন না এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার যাতে করে তাঁর ওফাতের পরে নানা প্রকার কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত সংকট,সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে সেজন্য তিনি কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও রূপরেখাও দিয়ে যাবেন না ?!!
আর সবশেষে মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ অসুস্থতায়ও তাঁর আচরণের মধ্যে এমন এক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যা প্রথম পদক্ষেপটিকে (নেতিবাচক পদক্ষেপ) সর্বৈব মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট । আর এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে,বিপদাশঙ্কা না করা বা বিপদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত না হওয়ার কারণে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে মহানবী (সা.) অনেক দূরে ছিলেন ।
শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে মুসলমানদের সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থে মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় মহানবীর যে আচরণের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে তা হল যখন মহানবী (সা.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হল এবং ঘরে অনেক লোক ছিল আর তাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন তখন তিনি (সা.) বললেন,“ কাগজ ও কলম নিয়ে এসো । আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে যাব যার পরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।” ১৩
মহান নেতার পক্ষ থেকে আন্তরিক এ প্রচেষ্টা যার বর্ণনা ও সত্যতা সম্পর্কে সকলেরই ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,মহানবী (সা.) প্রচার কার্যের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করতেন । আর বিকৃতি,বিচ্যুতি ও বিলুপ্তির হাত থেকে মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইসলাম প্রচার কার্যক্রম সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা ও রূপরেখা প্রণয়ন করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । তাই যে কোন অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর পক্ষে নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ধারণা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব এবং মোটেও যুক্তিসংগত নয় ।
শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে খলীফা নির্ধারণের ইতিবাচক পদক্ষেপ
দ্বিতীয় পথ : সম্ভাব্য দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হচ্ছে যে,হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ওফাতের পরে দাওয়াত বা ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার ভিত্তিতে তিনি ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব এ উম্মাহরই প্রথম আদর্শিক প্রজন্ম অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অতএব,উম্মাহর প্রতিনিধিত্বকারী এ প্রজন্মটিই হবে সরকার বা প্রশাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে ধাবমান ইসলাম-প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বধারার কেন্দ্রবিন্দু ।
তবে বাস্তবতা,মহানবী (সা.)-এর ইসলাম প্রচার কার্যক্রম এবং প্রচারকদের স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল সর্বসাধারণ অবস্থার কারণে সম্ভাব্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত অনুমান ও ধারণা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় । আর এর পাশাপাশি মহানবী (সা.) যে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে অগ্রগামী প্রজন্ম অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের সাথেই তাঁর ওফাতের পরে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব-ধারাকে জুড়ে দিয়েছেন- এতদসংক্রান্ত সকল অনুমান এবং জল্পনা-কল্পনারও অবসান হয়ে যায় । নিম্নোল্লেখিত কিছু কিছু বিষয় থেকেও উপরোক্ত বক্তব্যের একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা ও জোরালো সমর্থন পাওয়া যায় ।
১-শূরা পদ্ধতির জন্য উম্মতের প্রস্তুতি ছিলনা : মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচার কার্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনা করেই তাঁর ওফাতের পরে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা থেকে সরাসরি উৎসারিত নেতৃত্ব-ধারার সাথে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব-ধারাকে জড়িত করার লক্ষ্যে বাস্তবে যদি কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েই থাকতেন তাহলে এ ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য যে সব বিষয় অপরিহার্য ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয়টি নিঃসন্দেহে এই হত যে,তিনি (সা.) পরামর্শ ব্যবস্থা এবং এর সার্বিক আইনগত পরিসীমা ও দিক সম্পর্কে সমগ্র উম্মাহ্ এবং প্রচারকদেরকে অবশ্যই অবহিত করতেন এবং এ ব্যবস্থাটি মেনে নেয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহকে মানসিক ও চিন্তাগতভাবে প্রস্তুতও করতেন । এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজটি ছিল কতিপয় গোত্রের সমষ্টি । আর এ সব গোত্র ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্পরিক পরামর্শ বা শূরাভিত্তিক কোন রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় বসবাস করতে একদম অভ্যস্ত ছিল না, শুধু তাই নয় বরং তারা গোত্রপতিদের কঠোর নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করত; সেখানে পেশীবল,ধনবল এবং বংশগৌরবই বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করত। (দ্রঃ- ডঃ আব্দুল আযীয আদ্-দাওরী প্রণীত আন্ নুযমু আল ইসলামিয়াহ্ পৃঃ ৭,নাজীব প্রেস,বাগদাদ ১৯৫০ সালে মুদ্রিত,ডঃ সুবহী আস্-সালেহ্ প্রণীত আন্ নুযম আল ইসলামিয়াহ্ পৃঃ ৫০,দারুল ইল্ম লিল্ মালাঈন কর্তৃক ১৯৫০ সালে মুদ্রিত)
অতএব,আমরা বেশ সহজেই বুঝতে পারছি যে,মহানবী (সা.) শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার সমুদয় আইনগত ব্যাখ্যা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার সাথে মুসলিম উম্মাহকে পরিচিত করার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি । অথচ এ ধরণের পদক্ষেপ যদি বাস্তবে নেয়া হত তাহলে তা স্বভাবতঃই মহানবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী বা হাদীসসমূহে বর্ণিত হত এবং মুসলিম উম্মাহর চিন্তার-চেতনায় অথবা অন্ততঃপক্ষে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে মুসলিম উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতায় অবশ্যই প্রতিফলিত হত । আর এটাই ছিল স্বাভাবিক । কিন্তু আমরা মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার কোন আইনগত সুস্পষ্ট চিত্রই খুজে পাই না ।
এরপর আমরা উম্মাহর মানসিকতায় অথবা উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের ধ্যান-ধারণায়ও এ ধরনের পরিচিতিকরণ প্রক্রিয়ার কোন ইঙ্গিত অথবা সুস্পষ্ট প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করি না । অথচ এ প্রজন্মটির মাঝে দু’ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা বিদ্যমান ছিল । যার একটির নেতৃত্বে ছিলেন মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইত (আ.) আর অন্যটির পুরোধায় ছিল সকীফার ঘটনা এবং খেলাফতের সমর্থক । আর খেলাফত ও সকীফার ঘটনার উৎপত্তি হয়েছিল কার্যতঃ মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পরেই ।
তবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে,প্রথম ভাবধারাটি অসিয়ত ও ইমামতে বিশ্বাস এবং মহানবী (সা.)-এর কুরাবাহ বা আত্মীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করত । আর শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন বিশ্বাসই এর মাঝে পরিলক্ষিত হত না ।
দ্বিতীয় ভাবধারাটির উৎপত্তি,বিকাশ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণাদি থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে,এ ভাবধারাটিও শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না এবং উক্ত পরামর্শ ব্যবস্থার ভিত্তিতে বাস্তবে এর কোন কর্মতৎপরতাই ছিল না । আর ঠিক এই একই জিনিস আমরা মহানবী (সা.) এর ওফাতকালীন সময়ের মুহাজির ও আনসার প্রজন্মের সবার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি ।
আর তখনই বিষয়টির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি যে,হযরত আবু বকরের অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি হযরত উমরকে তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা মনোনীত করলেন এবং হযরত উসমানকে তা লিখারও নির্দেশ দিলেন। আর হযরত উসমান অসিয়তে লিখেছিলেন,“ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে । আর এটা হচ্ছে মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফা আবু বকরের প্রতিজ্ঞা পত্র । তোমাদের উপর সালাম । আমি তোমাদের সমীপে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি । আমি তোমাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করলাম। তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে ।” (দ্রঃ- ইবনে মানযূর প্রণীত মুখতাসার তারীখে দিমাশ্ক ১৮তম খণ্ড,পৃঃ ৩১০,তারীখুত তাবারী ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫২)
আব্দুর রহমান ইবনে আওফ হযরত আবু বকরের কাছে এসে বললেন,“ হে মহান রসুলের খলীফা! আপনি কেমন আছেন? ” হযরত আবু বকর বললেন, “ আমি আমার মৃত্যুর পর খলীফা নিযুক্ত করেছি । যখন তোমরা দেখতে পেলে যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে আমি খলীফা মনোনীত করেছি আর তখনই তোমরা আমার যা হয়েছে তা আরো বাড়িয়ে দিলে । তোমাদের সবারই নাসিকা ফুলে মোটা হয়ে গেছে । কেননা তোমরা সবাই তোমাদের নিজেদের জন্য খেলাফত প্রত্যাশা করছ । ”
(দ্রঃ- তারীখুল ইয়া’ কুবী ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৬, তারীখ ইবনে আসাকির ১৮তম খণ্ড পৃঃ ৩১০, তারীখুত তাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২)
এ ধরনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং এতদসংক্রাস্ত বিরোধিতার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,খলীফা শূরা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতেন না । আর তিনি মনে করতেন যে,খলীফা মনোনীত করাটা তাঁর অধিকার । আর এ ধরনের নিযুক্তি ও মনোনয়নের কারণে নতুন খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যায় । তাই খলীফা আবু বকর তাদেরকে নতুন খলীফার কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন । সুতরাং খলীফার এ উক্তি কেবলমাত্র সাদামাটা প্রস্তাব বা নিছক স্মরণ করিয়ে দেয়ার ঘটনাই ছিল না;বরং তা ছিল নিযুক্তি,বাধ্যবাধকতা এবং আদেশ । আমরা আরো লক্ষ্য করি যে,খলীফা উমর মনে করতেন মুসলমানদের জন্য নতুন খলীফা মনোনীত করা তাঁর দায়িত্ব ও অধিকার । তাই তিনি খলীফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে অন্য সকল মুসলমানের প্রকৃত ভূমিকা অস্বীকার করে কেবলমাত্র ছয় জনের মাঝেই খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি স্থির করেছিলেন । আর এর অর্থ দাঁড়ায় যে,ঠিক যেমনভাবে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে প্রথম খলীফার অনুসৃত প্রক্রিয়ায় শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার কোন প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি ঠিক তেমনি এ ব্যবস্থার কোন যৌক্তিকতাও উত্তরাধিকারী বা খলীফা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলীফার অনুসৃত পদ্ধতিতে আদৌ প্রতিফলিত হয়নি ।
জনগণ হযরত উমরের কাছে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন,“ যদি আমি দু’ জনের একজনকে জীবিত পেতাম তাহলে এ বিষয়টি (ফতঅর্থাৎ খেলা) তার জন্য স্থির করে দিতাম এবং এক্ষেত্রে তার উপর আস্থা স্থাপন করতাম । দু’ জনের একজন আবু হুযাইফার দাস সালেম এবং অন্যজন আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ । আর যদি সালেম জীবিত থাকত তাহলে খেলাফতের ব্যাপারে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ নিযুক্ত করতাম না ।” ১৪
হযরত আবু বকর মৃত্যূ শয্যায় শায়িতাবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে বলেছিলেন,“ আমি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে,(মহানবীর পরে) কে খলীফা হবে অর্থাৎ খেলাফত কার হবে? যার ফলে এ বিষয়ে আর কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবে না ।১৫ … ..তবে আনসারগণ যখন সকীফায় সা’ দ বিন উবাদাকে খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করার জন্য মিলিত হয়েছিল তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলেছিল : কোরাইশ বংশীয় মুহাজিরগণ যদি তা মেনে না নিয়ে বলে যে : আমরাই মুহাজির এবং আমরাই মহানবীর জ্ঞাতি-গোত্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আর এরপরও যদি তাদের মধ্য থেকে কোন দল এ কথা বলে যে : আমাদের মধ্য থেকে একজন নেতা ও তোমাদের মধ্য থেকে একজন নেতা হবে তবুও আমরা এ ব্যাপারে তাদের (কোরাইশদের) প্রস্তাবটি কখনোই মেনে নিব না ।” ১৬
হযরত আবু বকর তখন বক্তৃতায় বলেছিলেন,“ আমরা (মুহাজির) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছি আর এক্ষেত্রে সকল জনগণ আমাদের পিছনে (অর্থাৎ তারা আমাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে) । আমরা মহানবীর জ্ঞাতি-গোত্র এবং আরবদের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ।” ১৭
আর যখন আনসারগণ তাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে খেলাফত পর্যায়ক্রমিক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন হযরত আবু বকর তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,“ মহানবী (সা.) যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন তখন পিতৃধর্ম ত্যাগ করা আরবদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়েছিল । তাই তারা তাঁর (সা.) বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল । মহান আল্লাহ তাঁর গোত্রের মধ্য থেকে প্রথম দিককার মুহাজিরগণকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এরং তাঁকে মেনে নেয়ার বিশেষ তৌফিক দিয়েছিলেন । আর তারাই প্রথম যারা পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করেছিল । তারাই ছিল তাঁর বন্ধু এবং রক্তজ জ্ঞাতি-গোত্র । সুতরাং তাঁর (সা.) পরে খেলাফতের ব্যাপারে তাদেরই অধিকার অন্য সকলের চেয়ে বেশী । একমাত্র জালেম ব্যতীত আর কেউ খেলাফতের ব্যাপারে তাদের সাথে দ্বন্দ্ব করতে পারে না।১৮ যখন হাব্বাব বিন মুনযির আনসারদেরকে খেলাফত দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল এবং বলছিল,“ তোমরা নিজেদের হাতের ক্ষমতা ধরে রাখ। জনগণ নিঃসন্দেহে তোমাদের দলে এবং ছায়ায় রয়েছে। যদি এরা (মুহাজিরগণ) অস্বীকার করে তাহলে আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে আর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন আমীর হবে।” তখন হযরত উমর তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,“ দূর হোক,দূর হোক,একই খাপে কখনও দু’ টি তলোয়ার থাকতে পারে না । হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজত্ব ও প্রশাসনে একমাত্র মিথ্যাবলম্বী,পাপাশ্রয়ী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অভাগা ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি আমাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চায় ? অথচ আমরাই তাঁর বন্ধু,জ্ঞাতি ও নিকট আত্মীয়।” ১৯
খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার অনুসৃত পদ্ধতি,ঐ পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের আপত্তি ও অভিযোগ না থাকা এবং সকীফা দিবসে প্রথম প্রজন্মের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের (মুহাজির ও আনসার) যুক্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারী দলীয় মানসিকতা, কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও শাসন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা এবং প্রশাসনে আনসারদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার মানসিকতা সম্বলিত মুহাজিরদের দৃষ্টিভঙ্গি,মহানবীর জ্ঞাতি-গোত্রকে তাঁর উত্তরাধীকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য আরবদের তুলনায় অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে-এমন সব বংশীয় কারণের উপর গুরত্বারোপ,আনসারদের অনেকেরই দু’ জন আমীরের অস্তিত্ব (একজন আনসারদের মধ্য থেকে অন্যজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে) মেনে নেয়ার মানসিকতা এবং মহানবীর পরে খলীফা কে হবে-এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন না করার কারণে (সকীফার দিবসে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকারী) হযরত আবু বকরের আফসোস ও পরিতাপ-এসব কিছু থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে,মুসলিম উম্মাহর এই অগ্রগণ্য প্রজন্মটি (যাদের মধ্যে সেই অংশটিও রয়েছে যাঁরা মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পরে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন) কখনো শূরা ব্যবস্থার কথা চিন্তাও করত না এবং এ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণাও তাদের ছিল না । অতএব,আমরা কিভাবে ভাবতে পারি যে,মহানবী (সা.) বিধিসম্মত ও চিন্তাগতভাবে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং আনসার-মুহাজির প্রজন্মকে এ ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাঁর ওফাতের পরে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন? অতঃপর উক্ত আনসার-মুহাজির প্রজন্মের কাছে শূরা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অথবা সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ আমরা খুঁজে পাই না । অন্যদিকে আমাদের পক্ষে ভাবা মোটেও সম্ভব নয় যে,মহানবী (সা.) নিজেই এ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন এবং আইনগত ও ভাবগতভাবে তা সুনির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যাও করেছেন । পরিশেষে,তিনি (সা.) এ ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে মোটেও সচেতন ও পরিচিত করে যাননি ।
অতএব,এখানে যা বর্ণনা করা হল তা থেকে প্রমাণিত হয় যে,মহানবী (সা.) উম্মাহর কাছে একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে“ শূরা” ব্যবস্থাটি উত্থাপন করেননি । কারণ শূরার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার কথা উত্থাপন,অতঃপর সকল মুসলমানের কাছে সবদিক থেকে তা গোপন ও অখ্যাত থেকে যাওয়া স্বভাবতঃই সম্ভব নয় ।
আর যে বিষয়টি থেকে এ সত্যটির সর্বাধিক ব্যাখ্যা আমরা পেতে পারি তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে:
প্রথমতঃ যে পরিবেশে মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে কোন রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবে প্রবর্তিত হয়নি সে পরিবেশে শূরা ব্যবস্থা স্বভাবতঃই একটি নতুন ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হয়ে থাকবে । অতএব,যেমনভাবে আমরা বর্ণনা করেছি ঠিক তেমনিভাবে এ ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি প্রগাঢ় ও সুগভীর সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক ।
দ্বিতীয়তঃ চিন্তামূলক ক্ষেত্রে শূরা হচ্ছে একটি দুর্বোধ্য বিষয় যা অতি সাধারণভাবে আলোচিত হওয়া যথেষ্ট নয় । কারণ শূরার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে । আর যে পর্যন্ত শূরার সমুদয় খঁটিনাটি বিষয়,বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন এবং শূরা বা পরামর্শ সভায় মতপার্থক্য দেখা দিলে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রদানের মাপকাঠি ও নিয়মাবলীর বিশদ বিবরণ না দেয়া হবে,সে পর্যন্ত কেবলমাত্র এভাবে অতি সাদামাটাভাবে তা (শূরা) আলোচিত হওয়া যথেষ্ট নয় । আর এক্ষেত্রে সংখ্যা ও পরিমাপের ভিত্তিতে,নাকি গুণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এ মাপকাঠিসমূহের মান নির্ধারিত হবে ?
এ ধরনের যা কিছু শূরার সীমারেখা সংক্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে এবং মহানবীর ওফাতের সাথে সাথে তা বাস্তবায়নযোগ্য করে তা সবকিছুই বর্ণিত হওয়া আবশ্যক ছিল ।
তৃতীয়তঃ নিঃসন্দেহে আমরা পরামর্শ ব্যবস্থা থেকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক পারস্পরিক পরামর্শ এবং প্রশাসনের ভাগ্য নির্ধারণের দ্বারা যে কোন ভাবে শাসন ক্ষমতার বাস্তবায়নের একটি ব্যাখ্যা পেতে পারি । তাই এটা হচ্ছে এক ধরনের দায়িত্ব যা বিরাট সংখ্যক লোকের সাথে জড়িত যারা শূরা বা পরামর্শ পরিষদের আওতাধীন । আর এর অর্থ দাঁড়ায় যে, শূরা ব্যবস্থা যদি শরয়ী হুকুম বা বিধানই হত যা মহানবীর ওফাতের পরপরই কার্যকর করা ওয়াজিব তাহলে তা অবশ্যই ঐ সকল লোকের (যারা শূরার আওতাধীন) অধিকাংশের কাছে উত্থাপিত হওয়া আবশ্যক হয়ে যেত । কারণ শূরার ব্যাপারে তাদের মনোভাব ইতিবাচক আর তাদের প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে কিছু না কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে । আর এসব বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে,উম্মাহর কাছে মহানবী কর্তৃক তাঁর ওফাতের পরে তাঁরই বিকল্পস্বরূপ শূরা ব্যবস্থা উত্থাপন করা ছিল অত্যন্ত জরুরী বিষয়।
আর সেজন্য তাঁর করণীয় ছিল (এ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে) বিপুল হারে, গভীরভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে সাধারণ মানসিক প্রস্তুতি নেয়া,সব ধরনের ফাঁক-ফোঁকড়, রন্ধ্র ও ছিদ্র বন্ধ করা এবং শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা । আর এ পর্যায়ে,মহানবী (সা.) কর্তৃক জনসমক্ষে ব্যাপক ও গভীরভাবে পরামর্শ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার উত্থাপন এবং এরপর মহানবীর ওফাতের সময় পর্যন্ত তাঁর সমসাময়িক সকল মুসলমানের কাছে এ ধারণার যাবতীয় আলামত ও নিদর্শন বিস্মৃত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ।
আবার কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে,মহানবী (সা.) শূরা ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণাটি অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে কাঙ্খিত মাত্রায় এবং মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় পরিসরেই উত্থাপন করেছিলেন । তবে হঠাৎ করে উদ্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অন্যান্য কারণে প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা ঢাকা পড়ে গেছে । আর এর ফলে জনগণ শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় খুটি-নাটি বিধি-বিধান ও বিবরণ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিল তা গোপন করতে বাধ্য হয়েছে ।
কিন্ত এ ধারণাটি আদৌ বাস্তবসম্মত নয় । কেননা ঐ সকল রাজনৈতিক চাপ ও কারণ সম্পর্কে যত কিছুই বলা হোক না কেন তা সাধারণ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত করে না যারা মহানবীর ওফাতের পরপরই রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সকীফার পিরামিড (খেলাফত) নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন আবদানই রাখেনি । তাদের ভূমিকাও ছিল নিতান্ত গৌণ । যতই রাজনৈতিক নিষ্পেষণ ও আগ্রাসনের শিকার হোক না কেন এ ধরনের লোকেরাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে থাকে ।
অতএব,শূরা ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণা যদি কাঙ্খিত মাত্রায় মহানবী (সা.) কর্তৃক উত্থাপিত হত তাহলে শূরা সংক্রান্ত মহানবীর স্পষ্ট উক্তি শোনার পর বিষয়টি কেবলমাত্র কতগুলো রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের সমর্থকদের মাঝেই সীমিত থাকত না । বরং বিভিন্ন স্তরের জনতা তা শুনে থাকত এবং যেভাবে ইমাম আলী (আ.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী এবং প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাহী ক্ষমতা সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহ কার্যতঃ বিভিন্ন সাহাবী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে শূরা সংক্রান্ত মহানবীর হাদীসসমূহও সর্বসাধারণ সাহাবা কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই বর্ণিত হত । হযরত আলী (আ.)-এর মর্যাদা,গুণাবলী,প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাহী ক্ষমতা(وصایة ) এবং প্রামাণিক কর্তৃত্ব(مرجعیت ) সম্পর্কে মহানবী (সা.) থেকে সাহাবীদের সূত্রে বর্ণিত শত শত হাদীস রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের প্রবল বাঁধা ও চাপ এবং তৎকালীন বহুল প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে কিভাবে পৌঁছাল? অথচ শূরা ব্যবস্থা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের উল্লেখযোগ্য কোন অংশই কেন আমাদের কাছে পৌঁছাল না?!!আর এমনকি যারা প্রচলিত প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করত,তারাও বহুলাংশে গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য করত । এমনকি এক দলের বিরুদ্ধে আরেক দলের শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার শ্লোগান তোলার ফায়দা থাকা সত্ত্বেও আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি যে,কোন দল মহানবী (সা.) থেকে শোনা একটি বিধান হিসেবে শূরা ব্যবস্থার ধুঁয়ো তুলেছে । উদাহরণস্বরূপঃ হযরত আবু বকর যখন হযরত উমরকে খলীফা মনোনীত করলেন তখন এ মনোনয়নের বিপক্ষে হযরত তালহা নীতি-অবস্থান গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ ও তাঁর অসন্তুষ্টিও ব্যক্ত করেছিলেন।২০ এতদসত্ত্বেও হযরত তালহা খলীফা আবু বকরের এ মনোনয়নের বিরুদ্ধে“ শূরা কার্ড” (ورقة الشوری )ব্যবহার করার কথা মোটেও ভাবেননি । তিনি খলীফা আবু বকরের এ পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে মোটেও চিন্তা করেননি যে,খলীফা আবু বকর মহানবী (সা.) বর্ণিত শূরা ব্যবস্থা এবং নির্বাচন পরিপন্থী কাজ করেছেন ।
২-উম্মাকে ( আগামী প্রজন্মকে ) চিন্তাগতভাবে মিশনারী দায়িত্বের জন্য সংগঠিত না করা :
মহানবী (সা.) যদি মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে অগ্রগামী প্রজন্ম মুহাজির ও আনসার সাহাবাদেরকে তাঁর ওফাতের পরে দাওয়াত বা ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং আমূল সংস্কার প্রক্রিয়া পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণই করতেন তাহলে তাঁর করণীয় ছিল এ প্রজন্মটিকে চিন্তামূলকভাবে ও মিশনারী দায়িত্ববোধ সহকারে সর্বদিক থেকে গড়ে তোলা যাতে তারা ইসলামী মতাদর্শ পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে এবং এ মতাদর্শের আলোকে পূর্ণ আন্তরিকতা ও সচেতনতার সাথে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজও সম্পন্ন করতে পারে । আর এর ফলে এ কার্যক্রম বিরামহীন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধানও রেসালতী আদর্শের আলোকে তারা দিতে সক্ষম হবে । বিশেষতঃ তখনই যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি যে,মহানবী যিনি পারস্য সম্রাট খসরু এবং রোমান সম্রাট কায়সারের পতনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন;২১ তিনি জানতেন যে,অচিরেই ইসলাম প্রচার কার্যক্রম ব্যাপক সাফল্য অর্জন করবে এবং অতি শীঘ্রই পৃথিবীর নতুন নতুন জাতি,দেশ ও রাজ্য মুসলিম উম্মাহর করায়ত্তে আসবে । আর তখনই ইসলামের সাথে বিজিত জাতিসমূহকে পরিচিত করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে । মুসলমানদের সাথে বিজিত জাতি ও জনপদসমূহের সংমিশ্রণের সমূহ বিপদাপদ এবং অনিষ্ট থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং বিজিত জনপদ ও দেশসমূহে ইসলামী শরীয়ত ও আইন কানুন বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও উক্ত প্রজন্মের উপরই বর্তাবে । মুসলিম উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম নিঃসন্দেহে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব প্রজন্ম লাভ করেছিল তন্মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও কলুষতামুক্ত এবং ত্যাগ ও কোরবানীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন । তা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত সমূদয় প্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত গভীর ও ব্যাপক শিক্ষাদানের কোন নিদর্শনই আমরা খুজে পাই না । আর বাস্তবে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান কার্যক্রমের কোন নিদর্শন না থাকার বিষয়টি সমর্থন করে এমন সব দলীল-প্রমাণের সংখ্যা প্রচুর যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্ত করা সম্ভব নয় । আর এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে,শরয়ী বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাহাবাসূত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস বা ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণের সংখ্যা কয়েকশোর বেশী হবে না । অথচ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের মতে মহানবীর সাহাবা সংখ্যা ১২০০০ (বার হাজার)-এর অধিক ছিল ।২২ আর যেখানে মহানবী (সা.) তাঁর হাজার হাজার সাহাবার সাথে একই শহরে একই মসজিদে কত সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছেন সেখানে এ সংখ্যাগুলোর মাঝেও কি বিশেষ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান কার্যক্রমের সামান্য নিদর্শন খুজে পাওয়া সম্ভব নয়?!!
মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রীতি এটাই ছিল যে,তাঁরা মহানবী (সা.)-কে প্রথমেই প্রশ্ন শুরু করতেন না বা এ থেকে বিরত থাকতেন এমনকি তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মদীনার বাইরে থেকে কোন আরব বেদুঈনের আগমনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন,যে নাকি এসে মহানবীকে প্রশ্ন করবেন আর এ সুযোগে তিনি ঐ প্রশ্নটার উত্তর মহানবীর কাছ থেকে শুনে নিবেন ।২৩ তাঁরা (সাহাবাগণ) মনে করতেন যে,যে সব বিষয় সংঘটিত হয়নি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা বাহুল্য বই আর কিছুই নয় যা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত । আর এ কারণেই হযরত উমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,“ মহান আল্লাহর শপথ,যে বিষয় বা ব্যাপার সংঘটিত হয়নি সে সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে,তাহলে আমি তার উপর কঠোরতা আরোপ করব । কারণ মহান আল্লাহ যা ঘটে বা ঘটছে অবশ্যই তা বর্ণনা করেছেন।” ২৪ তিনি আরো বলেছেন,“ যা ঘটেনি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা কারো জন্য বৈধ হবে না । কারণ মহান আল্লাহ যা ঘটে বা ঘটবে সে বিষয়ে অবশ্যই ফয়সালা দিয়েছেন।” ২৫ একদিন এক ব্যক্তি ইবনে উমরের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে ইবনে উমর তাকে বলেছিলেন,“ যে জিনিস ঘটেনি তা জিজ্ঞেস করো না । কারণ আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে যে জিনিস ঘটেনি সে বিষয়ে প্রশ্নকর্তাকে অভিসম্পাত দিতে শুনেছি।” ২৬ এক ব্যক্তি উবাই ইবনে কা’ বকে কোন সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন,“ হে বৎস,যে বিষয়টা সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ তা ঘটেছে কি?” তখন ঐ লোকটি বলেছিল-“ না ।” তখন তিনি বললেন,“ অতএব,তা ঘটা পর্যন্ত তুমি আমাকে সময় দাও ।” ২৭
একদিন হযরত উমর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতটিতে পৌঁছলেন,“ অতঃপর আমরা তথায় শস্যবীজ, আঙ্গুর, ইক্ষু, জলপাই, খেজুর, উদ্যানরাজি, ফল এবং দুর্বাঘাস( اب ) সৃষ্টি করেছি । ” ২৮ তখন তিনি বলতে লাগলেন “ এ সব কিছুই তো বুঝলাম । কিন্তু “ اب ” কি? ” এরপর তিনি বললেন, “ খোদার কসম আসলেই এটা একটা কষ্টদায়ক ব্যাপার । তাই তোমাদের জানা ওয়াজিব হবে না যে, “ اب ” শব্দের অর্থ কি । পবিত্র কোরানের যে অংশের অর্থ তোমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে কেবল সেটুকর অনুসরণ কর এবং তদনুযায়ী আমল (কাজ) কর । আর কোরানের যা কিছু তোমরা জান না তা তার প্রভুর কাছে সঁপে দাও । ” ২৯
আর এভাবে আমরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার এক সার্বিক প্রবণতা সাহাবাদের মধ্যে দেখতে পাই । আর এ প্রবণতাই হচ্ছে মহানবী (সা.) থেকে সাহাবাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের সংখ্যা খুব কম হওয়ার মূল কারণ । আর এ স্বল্পতার কারণেই পরবর্তী কালে (খুটি-নাটি বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধান প্রণয়ন করার জন্য) ইস্তেহসান ও কিয়াসের মত পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ বহির্ভূত অন্যান্য উৎসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । আর এই ইস্তেহসান ও কিয়াস হচ্ছে ঐ ধরনের ইজতিহাদ যাতে মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিরুচির উপস্থিতি ও প্রভাব রয়েছে । আর এ কারণেই শরয়ী বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চিন্তাধারা সমেত তার ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে যায় । আর এ প্রবণতাটি রিসালতী দায়িত্ব ও সচেতনতাবোধ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষিত করার বিশেষ কার্যক্রমের ধ্যান-ধারণা থেকে যে বহু দূরে তা বলার অপেক্ষা রাখে না । আর এ বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হত অগ্রগণ্য ঐ প্রজন্মটিকে (মুহাজির-আনসারগণ) ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রশিক্ষিত করা ।
ঠিক যেমনভাবে সাহাবাগণ মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থেকেছেন ঠিক তেমনভাবে ইসলামী বিধি-বিধানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হওয়া সত্ত্বেও মহনবীর হাদীস ও সুন্নাহ্ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকেছেন । বলা বাহুল্য যে,লিখন প্রক্রিয়াই হচ্ছে বিলুপ্তি ও বিকৃতির হাত থেকে হাদীস ও সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করার একমাত্র পন্থা । উদাহরণস্বরূপ হিরাভী‘ যাম্মুল কালাম’ গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া বিন সা’ দের সূত্রে আব্দুল্লাহ্ বিন দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন,“ সাহাবাগণও হাদীস লিপিবদ্ধ করেননি আর তাবেয়ীগণও তা করেননি । তাঁরা কেবল হাদীসগুলোর শাব্দিক বর্ণনা করতেন এবং হিফয বা মুখস্তকরণ প্রক্রিয়ায় হাদীস গ্রহণ করতেন।৩০ তবে দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব- তাবাকাতে ইবনে সা’ দের বর্ণনানুসারে- মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্ সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বোত্তম কোন্ পন্থা নেয়া যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। দীর্ঘ একমাস চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনি মহানবীর হাদীস ও সুন্নাহ্ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেন।৩১ আর এ নিষেধাজ্ঞার কারণে মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ-যা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের পর ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস তা অদৃষ্টের হাতে ১৫০ বছরের জন্য ছেড়ে দেয়া হল,যার ফলে মহানবীর অগণিত হাদীস ও সুন্নাহ বিস্মৃতি ও বিকৃতির শিকার হল এবং হাদীসের অসংখ্য হাফেজের মৃত্যুতে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল ।
এর ব্যতিক্রম হচ্ছে আহলে বাইতের দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত পদক্ষেপ । তাঁরা প্রথম শতক থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন । আহলে বাইতের ইমামদের থেকে মুস্তাফিজ*সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে যে,আহলে বাইতের ইমামগণের কাছে হযরত আলীর হস্তে লিখিত মহানবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণীর (হাদীসের) একটি বিশাল গ্রন্থ আছে যাতে সংরক্ষিত রয়েছে মহানবীর সমূদয় সুন্নাহ ।৩২
(*মুস্তাফিজ রেওয়ায়েত : মশহুর ও মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতের মাঝামাঝি অর্থাৎ মশহুর অপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের এবং মুতাওয়াতিরের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের- অনুবাদক) খোদার শপথ, বাস্তবিকই যদি ব্যাপারটি অতি সাদামাটাই হয়ে থাকে তাহলে,ঐ সরল দৃষ্টিভঙ্গি যা কোন ঘটনা ঘটার আগে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় এবং মহানবীর পবিত্র সুন্নাহ্ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে,তা সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমণের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নতুন রিসালতের নেতৃত্বদানের জন্য কি উপযুক্ত ও যথেষ্ট ?
মহানবী (সা.) তাঁর সুন্নাহ্ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ না করেই ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে চলে যাবেন অথচ তিনিই আবার কিভাবে তাঁর সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য সবাইকে আদেশ করবেন ?৩৩
মহানবী (সা.) যদি শূরা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন অধিকারের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা করেই যেতেন তাহলে মহানবী কর্তৃক শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার যাবতীয় বিধি-বিধান সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করার কি প্রয়োজন ছিল না ? যাতে শূরা ব্যবস্থা একটি স্থায়ী নির্দিষ্ট পথে চলতে পারে এবং কারো প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত না হয় সেজন্য মহানবী (সা.) অবশ্যই তাঁর সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ।
আর মহানবী (সা.)-এর গৃহীত এ পদক্ষেপের একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা কি এটাই নয় যে, তিনি ইমাম আলীকে তাঁর ওফাতের পরে সমূদয় ধর্মীয় বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রামাণিক উৎস ও বৈধ কতৃপক্ষ (المرجعیة ) এবং ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত করেছেন । আর তাঁর (সা.) সমূদয় সুন্নাহ্ তাঁর (আলী) কাছে আমানত রেখেছেন এবং জ্ঞানের এক হাজার দুয়ার তাঁর কাছে উন্মোচিত করেছেন ।৩৪
মহানবী (সা.)-এর ওফাত-পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে,অনেক বড় বড় সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান সংক্রান্ত কোন জ্ঞান ও শিক্ষা আনসার ও মুহাজির প্রজন্মের ছিল না । মহানবীর ওফাতের পরে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম এসব সমস্যার সম্মুখীন হবে,সে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ধারণা করা হয়েছিল । এমনকি মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিরাট বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ সংক্রান্ত শরয়ী বিধি-বিধান,মুহাজিরদের মধ্যেই কি তা বন্টন করতে হবে নাকি সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্য তা ওয়াক্ফ করা হবে,এতদসংক্রান্ত কোন সুস্পষ্ট ধারণা খলীফা ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছিল না।৩৫ অতএব,আমরা কি ধারণা করতে পারি যে,মহানবী (সা.) যেখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলতেন,তারা শীঘ্রই পারস্য সম্রাট খসরু এবং রোমান সম্রাট কায়সারের সাম্রাজ্য জয় করবে এবং ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়াভিযানের দায়িত্ব আনসার-মুহাজির প্রজন্মের হাতে তিনি অর্পণ করবেন, সেখানে তিনি অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের অগ্রযাত্রা ও বিজয়াভিযানের মাধ্যমে অর্জিত পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদেরকে (মুহাজির-আনসার প্রজন্ম ও সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে) বিন্দুমাত্র অবহিত করেননি?!!
বরং এর চেয়ে আরো মারাত্মক যে বিষয়টি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হল,মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক (মুহাজির-আনসার) প্রজন্মের এমনকি নিছক ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রেও স্বচ্ছ জ্ঞান ও ধারণা ছিল না । উল্লেখ্য যে,মহানবী (সা.) এসব বিষয় সাহাবাদেরকে শত শত বার বাস্তবে করে দেখিয়েছেন । উদাহরণস্বরূপঃ এ প্রসঙ্গে আমরা জানাযার নামাযের কথা উল্লেখ করতে পারি । জানাযার নামায ছিল একটি ইবাদত যা মহানবী (সা.) মুসল্লী ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের উপস্থিতিতে শত শত বার আদায় করেছেন । কিন্তু এতদসত্ত্বেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন সাহাবারা যে পর্যন্ত মহানবী (সা.) জানাযার নামায আদায় করেছেন সে পর্যন্ত তারা কেবলমাত্র মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং এ ইবাদতটি শেখার প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করেননি। আর এ জন্যই মহানবীর ওফাতের পর জানাযার নামাযে কয়টা তাকবীর আছে সে ব্যাপারেও সাহাবাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইব্রাহীমের সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন : মহানবী যখন ইন্তেকাল করলেন তখন জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল । তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলেছিল,‘‘ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পাঁচবার তাকবীর বলতে শুনেছি।” আবার কোন কোন ব্যক্তির বক্তব্য ছিল,‘‘ মহানবী (সা.)-কে চারবার তাকবীর বলতে শুনেছি ।” আর এ ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ হযরত আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে । অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব যখন খলীফা হলেন তখন জানাযার নামাযের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য তাঁর জন্য পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল । তাই তিনি মহানবীর কতিপয় সাহাবীকে পত্র লিখে বলেছিলেন,“ হে মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ,আপনারা যতক্ষণ সাধারণ মুসলিম জনতার সামনে মতপার্থক্য করে যাবেন ততক্ষণ তারাও আপনাদের পর মতপার্থক্য জিইয়ে রাখবে । আর যখন আপনারা তাদের সামনে ঐকমত্য পোষণ করবেন তখন তারাও ঐক্যবদ্ধ থাকবে । সুতরাং আপনারা যে সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন কেবলমাত্র সে সব বিষয়েই আপনাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।” উমর ইবনুল খাত্তাব যেন তাদেরকে জাগ্রত করলেন । অতঃপর তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন,“ হে আমীরুল মুমেনীন,আপনি যা মনে করেন তাই উত্তম।” ৩৬
আর এভাবে আমরা দেখতে পাই যে,সাহাবাগণ মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় প্রধানতঃ তাঁর উপরই নির্ভর করতেন । আর যতদিন মহানবী (সা.) জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁরা (সাহাবাগণ) শরয়ী বিধি-বিধান ও ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন ও বুৎপত্তি লাভ করার প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করেননি ।
কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে,সাহাবাদের যে চিত্রটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতার যে সব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মহানবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যাপক সাফল্য এবং তিনি (সা.) যে এক অতি উন্নত মিশনারী প্রজন্মের জন্ম দিয়েছিলেন সে সংক্রান্ত আমাদের ধারণা ও কিয়াসের পরিপন্থী ।
এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে আমরা মহানবী (সা.)-এর ওফাতকালীন সময়ের সেই বিশাল প্রজন্মটির (মুহাজির-আনসার প্রজন্ম) প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছি । আর এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছেন সেটার ইতিবাচক মূল্যায়ন-পরিপন্থী কোন কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি । কারণ আমরা যে মুহূর্তে বিশ্বাস করি যে,মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল এক উন্নত ঐশ্বরিক আদর্শ এবং যুগে যুগে নবুওয়াতী কর্মধারার ইতিহাসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক রিসালতী মিশন,ঠিক সে মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই যে,এ ব্যাপারে বিশ্বাস এবং এ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফলের একটা যথার্থ মূল্যায়নে উপনীত হওয়া আসলে উক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে ফলাফলকে আলাদা করে কেবলমাত্র তা পর্যবেক্ষণ করার উপরই যেমনভাবে নির্ভরশীল নয়,ঠিক তেমনিভাবে পরিমাণের উপরও নির্ভরশীল নয়,যা গুণ ও মান বিবর্জিত । এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে একটি উপমা উল্লেখ করব । মনে করি যে,একজন শিক্ষক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়ে থাকেন । আমরা যদি তাঁর শিক্ষকতার দক্ষতার একটি মূল্যায়ন করতে চাই তাহলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কি পরিমাণ জ্ঞান ও তথ্য এ সব ছাত্র-ছাত্রীর অর্জিত হয়েছে কেবলমাত্র তা যাচাই করে দেখলে চলবে না;বরং ইংরেজী ভাষা কোর্সের সময়কাল,কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ববর্তী অবস্থা,ইংরেজী ভাষা ও পরিবেশের সাথে তাদের পরিচিতির,নৈকট্য ও দূরত্বের মাত্রা,ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা এবং এ শিক্ষা কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং স্পষ্ট করে তা বর্ণনা করতে হবে । আর এর পাশাপাশি পাঠদানের বিভিন্ন অবস্থার সাথে উক্ত ভাষা-শিক্ষকের পাঠদানের সর্বশেষ অবস্থার ফলাফলের সম্পর্কটাও নির্ণয় করতে হবে ।
সুতরাং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিত:
(ক) মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সময়কাল ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। কেননা মহানবী (সা.)-এর স্বল্পসংখ্যক প্রবীণ সাহাবীগণ যারা ইসলাম প্রচার কালের শুরু থেকে তাঁর সাথে ছিল তাদের ক্ষেত্রেও ঐ সময়কাল দু’ যুগের বেশী হবে না । আর এ একই সময়কাল বিরাট সংখ্যক আনসার সাহাবাদের ক্ষেত্রে একযুগের বেশী হবে না । আর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের ক্ষেত্রে তিন-চার বছরের বেশী হবে না ।
দ্বিতীয়তঃ মহানবী (সা.)-এর সমাজ-সংস্কার কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা শুরু করার আগে চিন্তামূলক,মানসিক,ধর্মীয় এবং আচার আচরণগত দিক থেকে মুহাজির,আনসার ও তৎকালীন আরবদের ইসলাম পূর্বাবস্থা,সাদামাটা ও সহজ-সরল জীবন যাপন,চিন্তা,আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে বিরাজমান শূন্যতা এবং স্বতঃস্ফুর্ত মনোবৃত্তি ।
আমি এ বিষয়টির আর বাড়তি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না । কারণ এগুলো হচ্ছে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট । কেননা পবিত্র ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র সমাজের বাহ্যিক অবস্থার সংস্কারই করেনি বরং তা হচ্ছে সমাজের আমূল সংস্কার প্রক্রিয়া এবং একটি নতুন উম্মাহর বৈপ্লবিক ভিত্তি । আর এর অর্থই হচ্ছে ইসলাম-পূর্ব অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান রয়েছে,যা লক্ষ্য করেই মহানবী (সা.) উম্মাহর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন ।
তৃতীয়তঃ মহানবী (সা.)-এর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা এবং বহুমুখী রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের বিভিন্ন রূপ যা মহানবী ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি ও ধরনকে হযরত ঈসা (আ.) ও তদীয় শিষ্যদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি ও ধরন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে । তাই মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মত নয় । তবে তা হচ্ছে এমনই এক সম্পর্ক যা একজন প্রশিক্ষক,সেনাপতি এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবীর অবস্থা ও মর্যাদার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ।
চতুর্থত: আদর্শিক-সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি যা মুসলিম উম্মহকে মোকাবেলা করতে হয়েছে কারণ এভাবে বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসার কারণে এবং নতুন ধর্মীয় প্রচার কার্যক্রমের পূর্ববর্তী ধর্মীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষায় দীক্ষিত শত্রুগণ কর্তৃক ময়দানে পরিচালিত অপতৎপরতা লাগাতার উদ্বেগ-উৎকন্ঠা এবং উত্তেজনার কারণ হয়েছিল । আর আমরা সবাই জানি যে,এ ধরনের অপতৎপরতা পরবর্তীকালে এমন এক ইস্রাঈলী (ইহুদীদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্বলিত) চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল যা আপনা-আপনি অথবা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।৩৭ এই প্রতি-বিপ্লবী ইস্রাঈলী চিন্তাধারার ব্যাপকতা এবং তা খণ্ডন করার ব্যাপারে ঐশী মনোযোগ ও দৃষ্টির মাত্রা নির্ণয় করার জন্য পবিত্র কোরানে সামান্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট ।৩৮
পঞ্চমত : যে সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মানবতার মহান পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যাপক ও সর্বসাধারণ পরিসরে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সাধনা করেছেন তা ছিল ঐ পর্যায়ে একটি সৎ ও জনপ্রিয় গণফোরামের প্রতিষ্ঠা । আর এ প্লাটফর্ম বা গণফোরামের সাথে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতোত্তর রিসালতী মিশনের নতুন নেতৃত্বধারা হবে পূর্ণ সংগতিশীল এবং এর মধ্য দিয়েই তা (নতুন নেতৃত্বধারা) সমুদয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও অর্জন করবে । এখানে উল্লেখ্য যে,এ নেতৃত্বধারার শীর্ষে উম্মাহর উত্তরণেরও ছিল না পর্যায়ভিত্তিক কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । কারণ এ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন রিসালত ও নবুওয়াতী মিশন সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞান,দ্বীন ও শরীয়তের বিধি বিধান সংক্রান্ত ব্যাপক-গভীর বুৎপত্তি এবং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার সাথে সুগভীর নিরঙ্কুশ সংবদ্ধতা ও সংযুক্তি। আর তৎকালীন মুসলিম উম্মাহ্ এ সব কিছুর অধিকারী ছিল না । আর ঐ পর্যায়ে পূর্বোল্লেখিত মানে রিসালতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ছিল এক সর্বৈব যুক্তিসংগত ব্যাপার যা (মহানবী কর্তৃক পরিচালিত) সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি থেকেও সুনির্দিষ্ট ও অবধারিত হয়ে যায় । কারণ,নিছক কতগুলো বাস্তব ইতিবাচক সম্ভাব্যতার আলোকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা মোটেও যুক্তিসংগত হবে না । ইসলাম তৎকালীন জাহেলী অনগ্রসর বর্বর আরব সমাজে যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে,ঠিক সে রকম পরিস্থিতির ন্যায় যে কোন পরিস্থিতিতে যদি কোন বাস্তব সম্ভাব্যতা থেকেও থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র আমাদের উল্লেখিত সীমারেখার মধ্যেই রয়েছে । কেননা নতুন রিসালত ও ধর্ম (ইসলাম) এবং আরবের তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত জাহেলী দূর্নীতি পরায়ণ বাস্তব সামাজিক অবস্থার মধ্যকার আদর্শিক,চিন্তাগত এবং আধ্যাত্মিক গুণ ও মানগত পার্থক্যটাই এ রিসালত বা ইসলাম ধর্মের নেতৃত্বের পর্যায়ে উম্মাহর উত্তরণের পথে সার্বিকভাবে এক বিরাট অন্তরায় ছিল ।
ষষ্ঠতঃ মহানবী (সা.)-এর রেখে যাওয়া উম্মতের এক বিরাট অংশই ছিল বিজিতআত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ তারা মহানবীর মক্কা বিজয় এবং আরব উপদ্বীপে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়,সাফল্য ও নেতৃত্ব লাভ করার পর এ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।৩৯ বিজয়ের পর কেবলমাত্র অতি সীমিত ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবং অল্প সময়ের জন্য মহানবী (সা.) এসব নব দীক্ষিত মুসলমানদেরকে পবিত্র ইসলামের সাথে পরিচিত এবং তাদের সাথে ইসলামী প্রশিক্ষণের কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন । এদের সাথে মহানবীর অধিকাংশ আচার-আচরণ ও সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রজার সাথে শাসকের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের মত। আর মুআল্লাফাতুল কুলব সংক্রান্ত ধারণার উন্মেষও এ পর্যায়েই হয়েছিল । (মুআল্লাফাতুল কুলব ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে বলা হয় যাদের অন্তঃকরণ ধন-সম্পদ ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে) । আর তা ইসলামের যাকাত-বিধান৪০ এবং অন্যান্য নির্বাহী ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব লাভ করেছিল । এখানে উল্লেখ্য যে,উম্মাহর এ অংশটি (মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীরা) অপরাপর অংশ থেকে কখনোই পৃথক ও বিচ্ছিন্ন ছিল না;বরং তাদের সাথে এরা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তারা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হত (অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর যারা মুসলমান হয়েছিল তারা এবং উম্মাহর অন্যান্য অংশ একে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে) ।
অতএব,এ ছ’ টি বিষয়ের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে,মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এক বিরাট ফলাফলের জন্ম দিয়েছিল,এক অনন্য সাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং রিসালতী প্রচার কার্যক্রমের নতুন অভিজ্ঞতার নেতৃত্বধারাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত হওয়ার লক্ষ্যে সৎ জনপ্রিয় গণ-প্লাটফর্ম গঠনের সত্যিকার যোগ্যতাসম্পন্ন একটি সৎ প্রজন্মেরও উদ্ভব ঘটিয়েছিল । এ কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ করি যে,যতদিন মহানবী (সা.)-এর কর্তৃত্বে সুপথপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্যন্ত এই প্রজন্মটি সৎ জনপ্রিয় গণপ্লাটফর্ম হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছে । আর এই সুপথপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থার যদি মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর ঐশী পথ পরিক্রমণ করা সম্ভব হত তাহলে উক্ত জনপ্রিয় গণ-প্লাটফর্মটি তার সঠিক ভূমিকা পালন করে যেত । তবে এ কথার অর্থ কস্মিনকালেও এটা হতে পারে না যে,উক্ত গণ-প্লাটফর্মটি কার্যতঃ এ নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং স্বয়ং নিজেই এ নতুন নবুওয়াতী প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ছিল উপযুক্ত ও প্রস্তুত । কারণ এ ধরণের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন রিসালত বা নবুওয়াতী মিশনের সাথে আত্মিক ও ঈমানীভাবে একীভূত হওয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের সংবদ্ধতা ও সংযুক্তি । আর সেই সাথে প্রয়োজন রিসালতের সমুদয় বিধি-বিধান,ধ্যান-ধারণা এবং মানবজীবন সংক্রান্ত রিসালতের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত ব্যাপক-পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এবং মুনাফিক,অনুপবেশকারী শত্রু এবং মুআল্লাফাতুল কুলবদের থেকে রিসালতী প্রচার কার্যক্রমের সকল স্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিশুদ্ধি । আর এসব গোষ্ঠী (মুনাফিক,অনুপবেশকারী শত্রু এবং মুআল্লাফাতুল কুলব) উক্ত প্রজন্মের একটা অংশ হিসেবে তখনও বিদ্যমান ছিল যাদের ছিল সংখ্যাগত গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক অবস্থান ও ভূমিকা ।
তারা প্রচুর নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ারও অধিকারী ছিল । কারণ,পবিত্র কোরানে মুনাফিক গোষ্ঠী এবং তাদের চক্রান্ত ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত প্রচুর আয়াত রয়েছে ।৪১ উক্ত প্রজন্মের মাঝে হযরত সালমান,হযরত আবুযার,এবং হযরত আম্মার (রা.)-এর মত এমন লোকজনও বিদ্যমান ছিলেন যাঁদেরকে মহানবী (সা.) নবুওয়াতী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে অতি উন্নত নবুওয়াতী দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করে গঠন করেছিলেন এবং তাঁদেরকে রিসালতী বা নবুওয়াতী মিশনের আদর্শের সাথে পরিপূর্ণরূপে একাকার করে দিয়েছিলেন ।
আমি বলতে চাই যে,ঐ মহান প্রজন্মের মাঝে (আম্মার,সালমান,আবুযার প্রমুখ ব্যক্তিদের মত) এসব ব্যক্তিদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয় না যে,সম্পূর্ণ প্রজন্মটি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল বলেই শূরা ভিত্তিক ব্যবস্থার আলোকে রিসালতী কার্যক্রমের গুরুদায়িত্বভার তাদের (উক্ত প্রজন্মের) উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল । এমনকি এসব ব্যক্তি যাঁরা উক্ত প্রজন্মের মাঝে রিসালতী মিশনের অতি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন তাঁদের তীব্র নিষ্ঠা এবং ইসলামের প্রতি গভীর আবেগ-অনুরাগ এবং ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও চিন্তামূলক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবুওয়াতী প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা তাঁদের ছিল না । এর কারণ ইসলাম কোন মানবরচিত তত্ত্ব নয় যা অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব এবং এর যাবতীয় ধ্যান-ধারণা নিখাদ অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে । ইসলাম হচ্ছে মহান আল্লাহর রিসালত যার সমূদয় বিধি-বিধান এবং ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ও নির্ধারিত হয়েছে । রিসালতী কর্মকান্ড ও কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সমূদয় সাধারণ অনুশাসন ও নীতিমালা সহকারে আধ্যাত্মিকভাবে এ ধর্মটিকে সজ্জিত ও উপস্থাপিত করা হয়েছে । অতএব,ইসলামের যাবতীয় সীমা-পরিসীমা খুঁটি-নাটি বিষয় এ ধর্মের রিসালতী ও নবুওয়াতী কার্যক্রমের নেতৃত্বকে আবশ্যিকভাবে নখদর্পণে রাখতে হবে । আর এমনটি যদি না হয় তাহলে উক্ত নেতৃত্বকে আবশ্যিকভাবে ও বাধ্য হয়েই তখন জাহেলী চিন্তাধারা এবং গোত্রীয় ধ্যান-ধারণা,প্রীতি এবং সমর্থনের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে হবে এবং এ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে । আর এভাবে রিসালতী ও নবুওয়াতী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার ধারায় ফাটল ধরবে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে । বিশেষ করে যেখানে ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী রিসালত যা সর্বযুগে টিকে থাকবে এবং সকল প্রকার সময়ভিত্তিক,আঞ্চলিক এবং জাতিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে । আর যেহেতু সর্বকালে এ ধর্মের টিকে থাকার মূলভিত্তিকে একমাত্র এর নেতৃত্ব ধারাই সৃষ্টি করে থাকে তাই তা (ইসলামের নেতৃত্বধারা) কখনো কখনো ভুল করবে আবার কখনো কখনো নির্ভুল ও সঠিক হবে- এধরনের ভ্রান্তি ও নির্ভুলতার অভিজ্ঞতার ক্রীড়নকে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা যা কখনো ভুলও হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে তাতে ভুলের পর ভুল স্তূপিকৃত হতে থাকবে এবং কিছুকাল এভাবে চলতে থাকলে এমন এক ভয়াবহ ফাটল বা রন্ধ্রের সৃষ্টি হবে যা রিসালতী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে ধ্বংস ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে ।
যা আলোচনা করা হল তা থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে,মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সর্বসাধারণ পর্যায়ে যে সচেতনতাবোধের অনুশীলন ও চর্চা করেছিলেন তা রিসালতী ও নবুওয়াতী প্রচার কার্যক্রম এবং সংস্কার-প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতের আদর্শিক,চিন্তামূলক এবং রাজনৈতিক সচেতন নেতৃত্বধারা তৈরি করার জন্য যে মাত্রায় থাকা প্রয়োজন ঠিক সে মাত্রায় বিদ্যমান ছিল না । বরং তা ছিল যে মাত্রায় নবুওয়াতী প্রচার কার্যক্রমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত সচেতন গণ-প্লাটফর্ম সৃষ্টি করা যায় ঠিক সেই মাত্রার সচেতনতাবোধ ।
অতএব,মহানবী (সা.) তাঁর ওফাতের পর ইসলামী রিসালতী প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়-দায়িত্ব সরাসরি আনসার ও মুহাজির প্রজন্মের হাতে অর্পণ করার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন বলে যে ধারণা পোষণ করা হয় তা থেকে সবকিছুর অগোচরে সংস্কার কার্যক্রমের ইতিহাসে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মিশনারী নেতা অভিযুক্ত হয়ে যান যে, তিনি প্রচার কার্যক্রমের জননন্দিত প্লাটফর্ম পর্যায়ের কাঙ্খিত সচেতনতাবোধ এবং প্রচার কার্যক্রমের আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব-পর্যায়ের কাঙ্খিত সচেতনতাবোধের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম ।
৩-উম্মাহ্ তখনও জাহেলী রীতি - নীতি হতে মুক্ত হয়নি : প্রচার কার্যক্রমই হচ্ছে সংস্কার প্রক্রিয়া এবং মানব জীবনের নয়া পদ্ধতি । আর এটা হচ্ছে একটি উম্মাহকে নতুন করে গড়ে তোলা এবং এর জীবন থেকে জাহেলীয়াতের সকল শিকড় এবং খাদ ও তলানী পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার দৃঢ় সংকল্পস্বরূপ । সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ বড় জোর এক যুগ মহানবীর এ সংস্কার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে । স্বাভাবিকভাবে আদর্শিক রিসালতী যৌক্তিকতার আলোকে এ সংক্ষিপ্ত সময়কাল যথেষ্ট নয় । অর্থাৎ এ সময়কাল যে প্রজন্মটি প্রচার কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে মাত্র দশ বছর অতিবাহিত করেছে সেই প্রজন্মটির সচেতনতা,বস্তুনিষ্ঠতা অতীতের সকল জাহেলী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি এবং নতুন প্রচার কার্যক্রমের অবদানসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যা ঐ প্রজন্মটিকে রিসালতের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব এবং প্রচার কার্যক্রমের সমূদয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ এবং নেতা ছাড়াই সংস্কার প্রক্রিয়াকে চালিয়ে নেয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলবে । বরং আদর্শিক রিসালতী যৌক্তিকতা ও দর্শন থেকে অবধারিত হয়ে যায় যে,উক্ত কাঙ্খিত অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধায়কের পর্যায়ে উত্তরণের জন্য উম্মাহকে বেশ সুদীর্ঘ সময়কাল আদর্শিক তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে চলতে হবে ।
আর এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যা কেবলমাত্র আমরাই গবেষণা করে বের করেছি । বরং এটা এমন এক বাস্তবতাকে নির্দেশ করে যা মহানবী (সা.)-এর ওফাতোত্তর ঘটনা-প্রবাহ থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় । আর এ নিগুঢ় বাস্তবতা অর্ধশতাব্দী বা তার চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে আনসার-মুহাজির প্রজন্ম কর্তৃক ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা করার মাধ্যমে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠে । কারণ এ তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের বয়সকাল ২৫ বছর গত হতে না হতেই খেলাফতে রাশেদাহ্ (সুপথ প্রাপ্ত খিলাফত) এবং ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রম যার নেতৃত্ব এবং পরিচালনার ভার আনসার-মুহাজির প্রজন্ম গ্রহণ করেছিল তা ইসলামের আদি শত্রুদের তীব্র আক্রমণ ও আঘাতের মুখে ভেঙ্গে পড়ে । তবে এটা ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অবকাঠামোর ভিতর থেকেই হয়েছিল,বাইরে থেকে নয়। কারণ ইসলামের আদি শত্রুরা ধীরে ধীরে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রভাব-কেন্দ্রসমূহে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং অসচেতন নেতৃত্ব থেকে ফায়দা হাসিল ও স্বার্থোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল । তারপর তারা ঐ নেতৃত্বকেই চরম নির্লজ্জতার সাথে এবং কঠোরভাবে জবরদখল করে অগ্রগামী বরেণ্য প্রজন্মসহ মুসলিম উম্মাহকে নিজ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের আসন থেকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। আর এরই ফলশ্রুতিতে,ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বধারা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল । আর এ রাজতন্ত্র মুমিন-মুসলমানদের মান-মর্যাদা হানি করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করত না,পূণ্যাত্মাদেরকে ঠান্ডামাথায় হত্যা করত,জনসাধারণের ধনসম্পদ লুন্ঠন করত,শরীয়তের দন্ডবিধি প্রয়োগ করত না এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান বন্ধ করে দিয়েছিল এবং জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলত । তখন ফাই (যেসব ভূমি যুদ্ধ ছাড়াই চুক্তির ভিত্তিতে রসুলের হস্তগত হয়) এবং সওয়াদ (গ্রাম-গ্রামাঞ্চল) কোরাইশদের উদ্যানে পরিণত হয়েছিল । খেলাফত ও উমাইয়া বংশীয় অর্বাচীন তরুণ ও যুবকদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল।৪২
অতএব,মহানবীর ওফাতোত্তর অভিজ্ঞতা এবং ২৫ বছর পরে লব্ধ ফলাফলসমূহ থেকে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায় । যা থেকে সবিশেষ গুরুত্বের সাথে স্পষ্ট হয়ে যায় যে,মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পরই আনসার-মুহাজির প্রজন্মের হাতে সরাসরি আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃতার্পণ আসলেই হবে এক অপরিপক্ক ও অদূরদর্শী এবং সঠিক সময়ের আগেই নেয়া পদক্ষেপ । আর এ কারণেই মহানবী (সা.) যে এ ধরনের অপরিপক্ক ও কাঁচা কাজ করতে পারেন তা পুরোপুরি অযৌক্তিক এবং অমূলক ।
প্রত্যক্ষ মনোনয়নের মাধ্যমে মহানবীর খলীফা নিযুক্তকরণের ইতিবাচক পদক্ষেপ
তৃতীয় পথ : এ পদ্ধতিই প্রকৃত ইতিবাচক পদক্ষেপ । এ পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহকে পথ-প্রদর্শন ও পরিচালনা করবেন তাকে প্রস্তুত ও নিযুক্ত করা হয় । একমাত্র এ পদ্ধতিটিই প্রকৃত বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিশীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের প্রচারকদের অবস্থা এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসৃত রীতি-নীতি ও পন্থার আলোকেও অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ । আর এ পদক্ষেপটি হচ্ছে এই যে,মহানবী (সা.) তাঁর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবশ্যই কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকবেন । তাই তিনি মহান আল্লাহর আদেশে এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন যাঁর অস্তিত্ব ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের মাঝে আকন্ঠ নিমজ্জিত । আর তাঁর অস্তিত্বের এ সুগভীরতা তাঁকে বিশেষভাবে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত করে তুলবে । সুতরাং মহানবী (সা.) এই ব্যক্তিকেই মিশনারী (রিসালতী) ভাবধারায় এবং বিশেষভাবে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তাঁর (অর্থাৎ মহানবীর মনোনীত ব্যক্তিটির) মধ্যে ইসলাম প্রচার কাজের আদর্শিক প্রামাণ্য উৎস ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার যোগ্যতা এবং এ প্রচার কার্যক্রমের রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হবে । আর এটা হতেই হবে এ কারণে যে,উক্ত ব্যক্তিটিই মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর আনসার-মুহাজির প্রজন্মের সচেতন জনপ্রিয় প্লাটফর্মের সাহায্য নিয়ে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বধারা এবং তাদেরকে আদর্শিকভাবে সুগঠিত করার প্রক্রিয়াকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দেবে যা উম্মাহকে নেতৃত্বের গুরু-দায়িত্ব বহন করার জন্য উপযুক্ত করবে ।
আর এভাবে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে,এটাই (সরাসরি মনোনীতকরণ) হচ্ছে একমাত্র (সঠিক) পদ্ধতি যা ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের প্রকৃত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং প্রগতির পথে এ কার্যক্রমের নব অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনাসূত্রে প্রমাণিত যে,তিনি (সা.) একজন প্রচারককে মিশনারী এবং আদর্শিকভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর ওফাতের পর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবধান এবং মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেছেন । আর এটাই হচ্ছে তৃতীয় পদ্ধতি সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর অনুসৃত রীতি-নীতিরই প্রমাণস্বরূপ যা বাস্তবতার আলোকে অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির নিরিখেও সমর্থিত হয়ে যায় । ইতোমধ্যে আমরা এ ব্যাপারে অবগত হয়েছি ।
আর এ সুমহান নবুওয়াতী মিশনের নেতৃত্বদানের যোগ্য ও ন্যায্য দাবিদার এবং ভবিষ্যৎ ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি স্বয়ং আলী ইবনে আবু তালেব ছাড়া আর কেউ নন । ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের সাথে তাঁর অস্তিত্বের সু-গভীর একাত্মতা তাঁকে এ কার্যক্রমের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করে। শুধু তাই নয়,তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম-ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম মুজাহিদ । আর একইভাবে তাঁর অস্তিত্ব মহানবীর জীবনের সাথে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল । এই আলী ছিলেন মহানবীর হাতে লালিত-পালিত,তাঁর শিয়রেই তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম চোখ খোলেন এবং পৃথিবীর আলো প্রত্যক্ষ করেন । তিনি মহানবীর হাতেই বড় হয়েছেন । আর এ কারণেই হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করেছেন । তাঁর জীবনে পড়েছে মহানবীর পূর্ণ প্রভাব । তিনি মহানবীর নীতি,আদর্শ এবং পথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন । এসব কিছু অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি ।
হযরত মুহম্মদ (সা.) যে হযরত আলীকে রিসালতী মিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ও যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন তার অগণিত দলীল ও সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বয়ং তাঁর (সা.) ও ইমাম আলীর জীবনে বিদ্যমান রয়েছে । তাই ইমাম আলী (আ.) যখন মহানবীকে প্রশ্ন শুরু করতেন তখনই মহানবী (সা.) ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রম এবং এর নিগুঢ় তাৎপর্য বর্ণনা করতেন এবং ইমাম আলীর প্রশ্ন করার কারণেই মহানবী (সা.) আদর্শিক-চিন্তামূলক বিষয়াদি এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কিত সঠিক ইসলামী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি জনসমক্ষে পেশ করতেন।৪৩ তিনি (সা.) ইমাম আলী (আ.)-এর সাথে দিবা-রাত্রি ঘন্টার পর ঘন্টা একান্ত নিভৃতে কাটাতেন এবং রিসালত সংক্রান্ত সঠিক ও গভীর জ্ঞান,এ পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমুদয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম আলী (আ.)-এর অন্তঃদৃষ্টির উন্মেষ ঘটিয়েছেন ।
আবু ইসহাক থেকে সনদ সহকারে“ আল-মুস্তাদরাক” গ্রন্থে আল-হাকেম বর্ণনা করেছেন,আবু ইসহাক বলেন,“ আমি কাসেম বিন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম : হযরত আলী কিভাবে মহানবী (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন?” তিনি বললেন,“ কারণ তিনি (আলী) আমাদের সবার আগে মহানবীর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মহানবীর সাথে থাকতেন অর্থাৎ তাঁকে সঙ্গ দিতেন।” ৪৪
হুলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : তিনি বলতেন,“ মহানবী (সা.) হযরত আলীর কাছে ৭০টি প্রতিজ্ঞা (আহ্দ) করেছিলেন যা তিনি আলী ব্যতীত অন্য কারো কাছে করেননি।” (দ্র: হুলইয়াতুল আউলিয়া আবু নাঈম প্রণীত ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮; দারুল কিতাব আল আরাবী কতৃর্ক মুদ্রিত ১৪০৫ হি:) ।
ইমাম নাসাঈ আল-খাসায়েস গ্রন্থে ইমাম আলী থেকে বর্ণনা করেছেন,ইমাম আলী (আ.) বলতেন,“ মহানবীর কাছে আমার এমন এক মর্যাদা ছিল যা সৃষ্টিকুলের আর কারো ছিল না । আমি প্রতি রাতেই মহানবীর কাছে যেতাম । যদি তিনি নামাযরত থাকতেন,তাহলে নামাযান্তে তসবীহ পাঠের সময় আমি তাঁর কাছে যেতাম । আর যখন তিনি নামায পড়তেন না তখন তিনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম ।” ইমাম নাসাঈ ইমাম আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : ইমাম আলী (আ.)বলেছেন,“ মহানবী (সা.)-এর খেদমতে আমার উপস্থিত হওয়ার দু’ টি সময় ছিল । একটি রাতে অন্যটি দিনে । (দ্র: আস-সুনান আল-কুবরা আল-খাসায়েস ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৪০,হাদীস নং ১/৮৪৯৯ এবং পৃ: ১৪১)
ইমাম আলী (আ.) থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন : ইমাম আলী (আ.) বলতেন,‘‘ আমি যখনই মহানবীকে প্রশ্ন করতাম তখনই আমি সে প্রশ্নের জবাব পেতাম । আমি যদি চুপচাপ থাকতাম তিনিই কথা বলা শুরু করতেন ।” (প্রাগুক্ত ৫ম খণ্ড পৃ: ১৪২) আল-হাকেম তাঁর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে এই একই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন,“ হাদীসটি শায়খাইনের শর্ত মোতাবেক সহীহ ।” [শায়খাইনঃ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম-এ দুই হাদীসবেত্তা] (দ্র: আল-মুস্তাদরাক ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৫৩,হাদীস ৪৬৩০,মুস্তাফা আব্দুল কাদের আতা কর্তৃক গবেষণাকৃত,দারুল কুতব আল-ইলমিয়াহ,বৈরুত থেকে ১৪১১ হিজরীতে মুদ্রিত)
হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন : তিনি (উম্মে সালামাহ্) বলেছেন,“ নিশ্চয় মহানবীর কাছে প্রতিশ্রুতি ও বন্ধুত্বের দিক থেকে সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিই ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (আ.) ।” উম্মে সালামাহ্ বলেছেন,“ মহানবী (সা.) যে দিন ইন্তেকাল করলেন সেদিন প্রভাতে হযরত আলী (আ.)-কে ডেকে পাঠালেন । আমার মনে হয় যে,তিনি আলীকে কোন প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন । এরপর তিনি (সা.) বলতে থাকেন : আলী এসেছে কি? এ কথা তিনি তিনবার বললেন । আলী (আ.) সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসলেন । তিনি ফিরে আসলে আমরা বুঝতে পারলাম যে,আলীর সাথে মহানবী (সা.)-এর বিশেষ প্রয়োজন আছে । তাই আমরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম । সেদিন আমরা হযরত আয়েশার হুজরায় মহানবীর সান্নিধ্যে ছিলাম । আমি সবার শেষে হুজরা থেকে বের হলাম এবং দরজার পিছনে বসে পড়লাম । আমি অন্য সকলের চেয়ে দরজার খুব নিকটেই বসে ছিলাম । আলী (আ.) মহানবীর পবিত্র বুকে ঝুঁকে রয়েছিলেন । তিনি ছিলেন মহানবীর কাছে প্রতিশ্রুতির দিক থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি । এ সময় মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)-এর সাথে গোপনে কথা বলতে থাকেন।” (দ্র: ইমাম নাসাঈর আস-সুনান আল-কুবরা ৫ম খণ্ড,পৃ:-১৫৪, অধ্যায়:৫৪ । এই একই হাদীস ইবনে আসাকির প্রণীত মুখতাসারাত তারীখে বর্ণিত হয়েছে ১৮তম খণ্ড, পৃ: ২১) ।
ইমাম আলী (আ.) তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণ আল-খুতবাহ্ আল-কাসেআহ্’ য় মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর অসাধারণ সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মহানবীর বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, “ ঘনিষ্ঠ আত্মিয়তার দিক থেকে ও বিশেষ অবস্থানের কারণে মহানবীর কাছে আমার যে মর্যাদা রয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা সবাই অবগত আছ । তিনি আমাকে আমার শৈশব-কালে তাঁর কোলে বসাতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তিনি আমাকে তাঁর নিজ বিছানায় শোয়াতেন । তাঁর পবিত্র দেহ আমার দেহকে স্পর্শ করত । তিনি আমার ঘ্রাণ নিতেন । তিনি খাদ্য চিবিয়ে তা আমাকে খাওয়াতেন । তিনি আমাকে কখনো কোন কথায় মিথ্যা বলতে দেখেননি । উষ্ট্রশাবক যেমনভাবে তার মাকে অনুসরণ করে ঠিক তেমনিভাবে আমি তাঁকে (সা.) অনুসরণ করতাম । তিনি আমাকে প্রতিদিন তাঁর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী থেকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন এবং আমাকে তা পালন করার নির্দেশ দিতেন । তিনি প্রতি বছর হেরা পর্বতের গুহায় মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন । একমাত্র আমি তাঁকে সেখানে দেখতে যেতাম । আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে সেখানে দেখতে যেত না । মহানবী (সা.) ও হযরত খাদীজা (রা.)-এর গৃহ ব্যতীত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আর কোন গৃহ বা পরিবার সেদিন পৃথিবীর বুকে ছিল না । আর আমি ছিলাম উক্ত পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি । আমি ওয়াহী ও রিসালতের জ্যোতি (নূর) প্রত্যক্ষ করতাম এবং নবুওয়াতের সুঘ্রান পেতাম । (দ্র: ডঃ সুবহী সালেহ কর্তৃক সম্পাদিত নাহজুল বালাগাহ্,ভাষণ নং- ১৯২)
এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং আরো অগণিত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বের পর্যায় সম্পর্কে ইমাম আলী (আ.)-কে সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য মহানবী (সা.)- এর যে বিশেষ মিশনারী (রিসালতী) প্রস্তুতিও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়েছিলেন তার একটি চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে । মহানবীর ওফাতের পর ইমাম আলী (আ.)-এর জীবনে এত প্রচুর ও অগণিত তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে,মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ইমাম আলীর জন্য বিশেষ আদর্শিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন যার ফলাফল ও প্রভাবসমূহ পরবর্তীকালে মহানবীর ওফাতের পর প্রত্যক্ষ করা গেছে । মহানবীর ওফাতের পর ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গের কাছে যেসব সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দূরূহ বা অসাধ্য ছিল তা সমাধান করার একমাত্র যোগ্য উৎস ছিলেন ইমাম আলী (আ.) । (আস-সুয়তী প্রণীত তারীখুল খুলাফা পৃ: ১৭০-১৭২,হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলতেন,“ এমন কোন সমস্যায় আল্লাহ্পাক যেন আমাকে জীবিত না রাখেন যেখানে আবুল হাসান আলী নেই ।” ইবনে হাজর প্রণীত আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা,পৃ: ১২৭)
ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে খুলাফা-ই রাশেদার যুগে এমন কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই যেক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যার সমাধান পদ্ধতি জানার জন্য ইমাম আলী (আ.) অন্য কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়েছিলেন । অথচ আমাদের জানামতে এমন অনেক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে যার সমাধানের জন্য তদানীন্তন ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ এ বিষয়ে রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আলী (আ.)-এর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ।
মহানবী (সা.) ইমাম আলী (আ.)-কে তাঁর তিরোধানের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্বদান ও পরিচালনা করার জন্য যে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন সে সংক্রান্ত্ দলীল-প্রমাণাদি যখন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে তখন মহানবী (সা.) কর্তৃক এ মহা-পরিকল্পনা ঘোষণা করা এবং ইমাম আলীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্পণ করা সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণাদিও নিঃসন্দেহে ওগুলো থেকে কম হবে না । উদাহরণস্বরূপঃ হাদীসু-ইয়াওমুদ্দার৪৫ (দ্র: তাফসীরুল খাযেন ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৭১,দারুল মারেফাহ,বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত) হাদীসে সাকালাইন,৪৬ হাদীসে মানযিলাহ,৪৭ হাদীসে গাদীর৪৮ এবং মহানবীর (সা.) অগণিত হাদীসে এ বিষয়টি আমরা প্রত্যক্ষ করি ।৪৯
আর এভাবেই ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের অবকাঠামোর মধ্যেই তাশাইয়ু বা হযরত আলীর অনুসারী হওয়ার প্রবণতার উন্মেষ ঘটে যা মহানবীর নবুওয়াতী পরিকল্পনার সীমার মধ্যেই বিকশিত হতে থাকে। আর স্বয়ং মহানবী (সা.) নিজেই এ পরিকল্পনার ভিত মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন ।
আর এভাবেই,ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে প্রমাণিত হয় যে,তাশাইয়ু দ্বীন-বহির্ভুত কোন অবস্থা বা ঘটনা ছিল না;বরং তা ছিল প্রচার কার্যক্রমের গঠন প্রকৃতি,এর মৌলিক প্রয়োজনাদি এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অর্থাৎ ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের গঠন-প্রকৃতি,মৌলিক প্রয়োজনাদি এবং অবস্থাসমূহ ইসলামের সীমারেখার মধ্যে হযরত আলীর অনুসারী হওয়ার প্রবণতার উদ্ভবের বিষয়টিকে অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী করেছে । অন্য অর্থে বলা যায়,ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের গঠন-প্রকৃতি,মৌলিক চাহিদা এবং পরিবেশ পরিস্থিতিই ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের প্রথম নেতার উপর এ কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় নেতাকে প্রস্তুত করার বিষয়টিকে অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী করে দেয় । আর এ দ্বিতীয় নেতা ও তাঁর উত্তরসুরীদের হাতেই ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের বৈপ্লবিক বিকাশ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে । এর ফলে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অতীত জাহেলীয়াতের সকল প্রকার বিদ্যমান প্রভাব,চিহ্ন ও নিদর্শনের পূর্ণ মূলোৎপাটন করবে এবং দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের যাবতীয় চাহিদা,প্রয়োজন এবং দায়িত্বশীল পর্যায়ে একটি নতুন উম্মাহ্ গঠনের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সংস্কারমূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে থাকবে ।
কিরূপে শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি ঘটল ?
v মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী) জীবদ্দশায় দু’ টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ।
v নবীর আহলে বাইতই (আ.) আদর্শিক এবং নেতৃত্বদানকারী কর্তৃপক্ষ ।
v শিয়া মাযহাবে আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহ ।
আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে,কিভাবে তাশাইয়ু বা হযরত আলীর অনুসারী হওয়ার প্রবণতার উৎপত্তি হয়েছে । কিন্তু এখন আমরা কিভাবে শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে এর ফলে কিভাবে মুসলিম উম্মাহ্ শিয়া ও সুন্নী- এ দু’ দলে বিভক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব ঃ
মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় দু’ টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ
মহানবীর জীবদ্দশায় মুসলিম উম্মাহর জীবনের প্রাথমিক পর্যায় গবেষণা ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব যে,প্রথম বছরগুলো থেকেই উম্মাহর বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি এবং ইসলামী দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার শুভ সূচনার সাথে সাথে দু’ টি প্রধান ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একই সাথে বিকাশ লাভ করেছে এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত মুসলিম উম্মাহর অবকাঠামোর মধ্যেই অবস্থান করেছে । আর এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্যই মহানবীর ওফাতের পর (মুসলিম উম্মাহর মাঝে) সরাসরি আদর্শিক ও ফিকাহভিত্তিক বিভক্তির জন্ম দেয় এবং মুসলিম উম্মাহকে প্রধান দু’ দলে বিভক্ত করে ফেলে । সর্বসাধারণ ইসলামী অবকাঠামোর আওতায় এ দু’ দলের একটি শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিজ প্রভাবাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং অপর দলটিকে শাসনক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং বিরোধীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য হয় । আর উম্মাহর এ সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটিই হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায় ।
(আর এখানে তিনটি আলোচনা রয়েছে)
একদম শুরু থেকেই যে দুই প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলামী উম্মাহর বিকাশ লাভের পাশাপাশি বিকাশ লাভ করেছিল তা হলঃ
প্রথমতঃ ধর্মীয় কৃচ্ছসাধনায় নিবিষ্টতা,ধর্মীয় দৃঢ়তা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণে বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি ।
দ্বিতীয়তঃ ঐ দৃষ্টিভঙ্গি,যা বিশ্বাস করে যে,ধর্মে বিশ্বাস কেবলমাত্র ইবাদত ও অদৃশ্য জগতের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ভক্তি,আনুগত্য ও নিবিষ্টতার মাঝেই সীমাবদ্ধ এবং প্রাগুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কল্যাণ,স্বার্থ ও সুবিধানুসারে ধর্মীয় বিধি-বিধানের পরিবর্তন ও ভারসাম্যপূর্ণ করণের ভিত্তিতে ইজতিহাদ এবং যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করা বৈধ ও সম্ভব ।
সাহাবাগণ মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসী ও গৌরবোজ্জ্বল অগ্রগামী প্রজন্ম হিসেবে মুসলিম উম্মাহর বিকাশের সর্বোত্তম উৎস হওয়া সত্ত্বেও এমনকি মানব ইতিহাসে মহানবীর নিজ হাতে গড়া প্রজন্মের চেয়ে অধিকতর উত্তম,সম্ভ্রান্ত এবং পবিত্র কোন আদর্শিক প্রজন্ম না দেখা গেলেও আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই এমন এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার অস্তিত্ব মেনে নেয়ার আবশ্যিকতা প্রত্যক্ষ করি যা কল্যাণকামিতা ও সুবিধার আলোকে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করার চাইতে ইজতিহাদ এবং পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা বা সুবিধা ভোগ করার বিষয়টিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক । আর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার কারণেই মহানবী (সা.)-কে অনেক ক্ষেত্রে এমনকি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েও তিক্ততা সহ্য করতে হয়েছে । সামনে এতদসংক্রান্ত আরো বর্ণনা ও বিবরণ আসবে । তবে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতা ছিল যা ধর্মীয় দৃঢ়তা,ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত আত্মসমর্পণবোধ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধানের নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্যে বিশ্বাসী ।
মুসলমানদের মাঝে ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার প্রসার লাভের অন্যতম একটি কারণ হয়তো এটাও হতে পারে যে,এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি,যে স্বার্থ-সুবিধা বা কল্যাণ মানুষ উপলব্ধি ও পরিমাপ করতে সক্ষম তদনুসারে যথেচ্ছা ভোগ করার প্রবণতার সাথে পূর্ণ সংগতিসম্পন্ন। পক্ষান্তরে যে বিধানের মর্মার্থ বা সারবত্বা সে উপলব্ধি করতে অক্ষম তা পালন করা তার স্বভাব ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী । আর বড় বড় সাহাবার মাঝে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের মত কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বকারী । হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব মহানবীর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শরয়ী দলীল-প্রমাণের বিপক্ষে ইজতিহাদও করেছেন । যে পর্যন্ত তিনি (হযরত উমর) প্রত্যক্ষ করতেন যে,ফায়দা বা কল্যাণকামিতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইজতিহাদে ভুল করেননি (অর্থাৎ তাঁর ইজতিহাদ ফায়দা বা কল্যাণ পরিপন্থী নয়) সে পর্যন্ত তিনি এমনকি নাস বা স্পষ্ট শরয়ী দলীল-প্রমাণের বিপক্ষেও ইজতিহাদ করার বৈধতায় বিশ্বাস করতেন । আর এতদপ্রসঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে তাঁর আচরণ ও নীতি অবস্থান৫০ এবং এ সন্ধির বিপক্ষে তাঁর যুক্তি প্রদানের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি । একইভাবে আযানের ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও আযান থেকেحی علی خیر العمل বাদ দেয়া এবং যখন মহানবী (সা.) মুত’ আতুল হজ্ব৫১ বা হজ্বে তামাত্তুর বিধান দেন তখন মহানবীর এ বিধানের ব্যাপারে নীতি অবস্থান ইত্যাদি সব কিছুই ছিল নাস বা স্পষ্ট শরয়ী দলীল- প্রমাণের মোকাবেলায় তাঁর গৃহীত ইজতিহাদী পদক্ষেপ ।৫২
আর এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয় মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষভাগে কোন এক দিনে তাঁরই সামনে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেছেন,“ মহানবীর ওফাত তথা মৃত্যু নিকটবর্তী হলে একদিন ঘরে অনেক লোক উপস্থিত ছিল।আর তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন,তখন মহানবী (সা.) বললেন,“ এসো আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিব যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।” তখন হযরত উমর বলে উঠলেন,“ মহানবীর উপর রোগযন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করেছে । আর তোমাদের কাছে তো কোরানই রয়েছে । আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কোরানই যথেষ্ট । হযরত উমরের এ কথায় ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হল । তারা ঝগড়া করতে লাগল । তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলল,“ তোমরা তাঁর নিকটবর্তী হও । নবী (সা.) তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবেন যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।” আবার কেউ কেউ হযরত উমর যা বলেছিলেন তাই বলল । এর ফলে মহানবীর সান্নিধ্যে বাক-বিতন্ডা,অযথা কথা-বার্তা,হট্টগোল,ঝগড়া-বিবাদ এবং মতপার্থক্য চরম আকার ধারণ করলে মহানবী (সা.) তীব্র অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বললেন,“ আমার কাছ থেকে তোমরা সবাই বের হয়ে যাও।” ৫৩ প্রাগুক্ত ঘটনাটি ঐ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের ব্যাপকতা এবং এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পার্থক্যের মাত্রা নিরূপণ ও প্রমাণ করার জন্য একাই যথেষ্ট ।
এ ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক,ক্ষোভ ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা উপরোক্ত ঘটনার সাথে যোগ করতে পারি । এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল । যার ফলে মহানবী (সা.) অসুস্থাবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে জনসমক্ষে ভাষণ দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন,“ হে লোক সকল উসামাকে সমরাধিনায়ক নিযুক্ত করার ব্যাপারে তোমাদের কারো কারো কথা (আপত্তি,ক্ষোভ,অসন্তোষ) আমার কাছে পৌঁছেছে । আর উসামাকে আমি সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে ব্যাপারে তোমরা যদি কটাক্ষ ও তিরষ্কার করতে থাক তাহলে তো তোমরা এর আগেও তার পিতাকে সমরাধিনায়ক নিযুক্ত করার ব্যাপারেও আমাকে কটাক্ষ ও নিন্দা করেছিলে। আল্লাহর শপথ,নিশ্চয়ই যায়েদ সেনাপতি হওয়ার যোগ্য এবং তার পুত্র উসামাও তারপর আমীর বা সেনাপতি হওয়ার যোগ্য ।” ৫৪
মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য তাঁর (সা.) তিরোধানের পরও ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব সংক্রান্ত মুসলমানদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহেও ব্যাপকাকারে প্রতিফলিত হয়েছে । তাই যারা ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত অনুসরণ (تعبد ) সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বকারী তারা কোন ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা এবং ভারসাম্যকরণ প্রক্রিয়া ছাড়াই মহানবীর হাদীসে এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার যথাযথ কারণও খুজে পেয়েছেন ।
তবে ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টিতে তখনই মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত পদ্ধতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এর পক্ষে সম্ভব যখন এ দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা মতে ইজতিহাদী প্রক্রিয়া এমন এক পদ্ধতি পেশ করবে যা উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে মহানবীর প্রদত্ত পদ্ধতি অপেক্ষাও অধিকতর সংগতিসম্পন্ন হবে ।
আর এভাবে আমরা দেখতে পাই যে,মহানবীর ওফাত বা তিরোধানের সময় থেকেই শিয়া মাযহাবের প্রত্যক্ষ উৎপত্তি হয়েছে । তখন ঐ সকল মুসলমানই“ শিয়া” বলে পরিচিত হয়েছে যারা কার্যতঃ ইসলামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের তত্ত্ব মেনে নিয়েছিল । আর এ তত্ত্বটিকে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর ওফাতের পরপরই সরাসরি বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন । আর শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি,ইমাম আলীর নেতৃত্ব ও ইমামত সংক্রান্ত তত্ত্বটি নিষ্ক্রিয় ও বানচাল করে শাসন-কর্তৃত্ব অন্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করার ব্যাপারে সকীফা বনী সায়েদার চত্বরে যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে । আব্বান বিন তাগলীব থেকে আল্লামা তাবারসী ইহতিজাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,আব্বান বলেছেন,“ আমি ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ আস-সাদেক (আ.)-কে বললাম,“ আপনার জন্য আমার প্রাণ কোরবান (উৎসর্গ) হোক । মহানবীর সাহাবাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত আবু বকরের শাসন কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?” তিনি (আ.) বললেন,“ যারা হযরত আবু বকরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা ছিলেন সংখ্যায় ১২ জন । মুহাজিরদের মধ্য থেকে খালিদ বিন সাঈদ বিন আবিল আস,সালমান আল-ফারেসী,আবুযার গিফারী,মিকদাদ বিন আসওয়াদ,আম্মার বিন ইয়াসির,বুরাইদাহ আল-আসলামী এবং আনসারদের মধ্যে আবুল হাইসান ইবনে আত্-তিহান,উসমান ইবনে হুনাইফ,খুযাইমাহ বিন সাবিত যুশ-শাহাদাতাইন,উবাই বিন কাব এবং আবু আইয়ুব আল-আনসারী । (দ্র: আল্লামা আত্-তাবারসী প্রণীত আল-ইহতিজাজ ১ম খণ্ড,পৃ: ৭৫ ও ১৮৬,মুআস্সাসাহ আল-আ’ লামী,বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত/১৯৮৩;তারীখুল ইয়াকুবী,২য় খণ্ড পৃ: ১০৩)
কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে,শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নিছক একনিষ্ঠা সহকারে শরয়ী দলীল-প্রমাণ অনুসরণ করার বাস্তব নমুনা । আর এ শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে রয়েছে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি যা ইজতিহাদের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে । আর এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে,শিয়া মাযহাব ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যানকারী এবং শিয়া মতাবলম্বীগণ ইজতিহাদ করার অনুমতি দেয় না । অথচ আমরা দেখতে পাই যে,এরাই (শিয়া মতাবলম্বীগণ) আবার শরীয়তের খুঁটি-নাটি বিষয়ে সর্বদা ইজতিহাদের চর্চা অব্যাহত রেখেছে !!!
উত্তর : যে ইজতিহাদের চর্চা শিয়ারা করে এবং যা শিয়াদের দৃষ্টিতে শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিবে কেফায়াহ তা হল শরয়ী দলীল থেকে শরয়ী বিধি-বিধান (হুকুম-আহকাম) প্রণয়ন করা। আর তা মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিমত ও অভিরুচি অনুসারে শরয়ী দলীল অথবা মুজতাহিদের কল্পিত (অনুমিত) কোন ফায়দা বা কল্যাণকামিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইজতিহাদ নয় । কারণ এ ধরনের ইজতিহাদ অবৈধ । আর শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি এতদ অর্থে ইজতিহাদের যে কোন ধরনের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে ।
ইসলামের একদম প্রাথমিক যুগ থেকেই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে,উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের একটি হচ্ছে শরয়ী দলীল অনুসরণের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি হচ্ছে ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি । আর এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অর্থ হচ্ছে শরয়ী দলীল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ইজতিহাদ ।
যে কোন ব্যাপক সংস্কারপন্থী রিসালত বা মিশন যা একদম গোঁড়া থেকেই সকল দূনীতি,বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায়ের আমূল সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালায় তার ছত্রছায়ায় উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের উদ্ভব একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা । কেননা এ ধরনের মিশন পূর্ব হতে থেকে যাওয়া জাহেলী ধ্যান-ধারণাসমূহ,নতুন রিসালত বা মিশনের প্রতি প্রতিটি ব্যক্তির একাত্মতার মাত্রা এবং তার ভক্তি ও ভালবাসার পর্যায়ানুসারে বিভিন্ন হারে বা মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে থাকে । আর এভাবে আমরা জানতে পারি যে,শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা প্রদর্শনকারী দৃষ্টিভঙ্গিই আসলে রিসালত বা মিশনের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের একাত্মতা,পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও উৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে । এ দৃষ্টিভঙ্গি শরয়ী দলীলের সীমারেখার মধ্যে ইজতিহাদ এবং তা থেকে শরয়ী বিধি-বিধান প্রণয়ণ করার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কখনোই অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে না । এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া জরুরী । আর তা হচ্ছে যে,শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিবিষ্টতার অর্থ কখনোই নিষ্ক্রিয়তা, স্থবিরতা (বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার অবসান) এবং বুদ্ধিহীনতা নয় যা মানব জীবনের বিবর্তন, বিকাশ,উন্নতি এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যকারণ ও সমুদয় প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিপন্থী । কেননা শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিবিষ্টতা বা তা’ আব্বুদের অর্থই হচ্ছে ধর্ম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা এবং আংশিকভাবে নয় বরং পূর্ণরূপে দ্বীন বা ধর্মকে আঁকড়ে ধরা । আর এ দ্বীন বা ধর্মের ভিতরেই আছে নমনীয়তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় মৌল ও উপাদান,যুগের সাথে চলার শক্তি এবং সবধরনের সংস্কার ও বিবর্তনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় মৌল ও উপাদান ধারণ করার ক্ষমতা (সামর্থ) । তাই ধর্ম ও শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতার অর্থই হচ্ছে ঐ সকল মৌল বা উপাদানের মধ্যে যা কিছুরই সৃজনশীলতা,উদ্ভাবনী শক্তি এবং সংস্কারকামিতা রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা । (দ্র: আল-মাআলিমুল জাদীদাহ লিল উসূল পৃ: ৪৮০) । এ সব কিছুই হচ্ছে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অবকাঠামোর মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে“ তাশাইয়ু” শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিছু সর্বসাধারণ লেখ বা চিত্র ।
নবীর ( সা .) আহলে বাইতই আদর্শিক ও নেতৃত্বদানকারী কর্তপক্ষ :
আহলে বাইত এবং ইমাম আলীর ইমামত যা উক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে তা আসলে দু’ ধরনের নেতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়:
একটি হচ্ছে চিন্তামূলক (আদর্শিক) নেতৃত্ব এবং অন্যটি হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আর এ উভয় প্রকার নেতৃত্বই মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছিল । আমরা ইতোমধ্যে যে সব পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি তদনুসারে মহানবী (সা.) তাঁর ওফাতের পরে তাঁর এমন এক যোগ্য ও উপযুক্ত নেতৃত্বধারার অস্তিত্বের ব্যাপারে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবেন যা উভয় প্রকার নেতৃত্বের অধিকারী হবে । এর ফলে আদর্শিক নেতৃত্ব ঐ সকল আদর্শিক শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হবে যা কখনো কখনো মুসলমানদের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এছাড়াও তা (চিন্তামূলক নেতৃত্ব) জীবন ও মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে নবোদ্ভূত সমস্যা ও বিষয়াদি সংক্রান্ত সঠিক ব্যাখ্যা দিতেও সক্ষম হবে । আর রাজনৈতিক,সামাজিক নেতৃত্ব ও ইসলাম প্রচার কার্যক্রম এবং ইসলমী উম্মাহর পথ-পরিক্রমাকে সঠিক সামাজিক খাতে পরিচালিত করবে ।
আমরা যে সব পরিবেশ-পরিস্থিতি আলোচনা করেছি সেগুলোর কারণেই মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের মাঝে উপরোক্ত নেতৃত্বদ্বয়ের সুসমাবেশ ঘটেছিল । আর এ বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপকারী অগণিত হাদীস মহানবী (সা.) থেকে সবসময়ই বর্ণিত হয়েছে । মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত চিন্তামূলক (আদর্শিক) নেতৃত্বের হাদীস-ভিত্তিক দলিল-প্রমাণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে হাদীসুস্ সাকালাইন (حدیث الثقلین ) । মহানবী (সা.) উক্ত হাদীসে বলেছেন:
‘‘ মহান প্রভূ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে অচিরেই আহবান (তলব) করা হবে । আর আমাকে সেই আহবানে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে । আর আমি তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি দু’ টি ভারী বস্তু:একটি আল্লাহর গ্রন্থ আল-কোরান যা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত রজ্জু (রশি) এবং অন্যটি আমার রক্তজ বংশধর (ইতরাত) আমার আহলে বাইত । সর্বজ্ঞানী সর্বসুন্দর মহান আল্লাহু আমাকে জানিয়েছেন যে,এ দুই ভারী বস্তু আমার কাছে হাউযে কাওসারে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না । অতএব,সাবধান! সাবধান! আমার পর এ দুই ভারী বস্তু বা সাকালাইনের ক্ষেত্রে তোমরা কেমন আচরণ কর!” ৫৫
সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংক্রান্ত হাদীসভিত্তিক দলীল-প্রমাণের সবচেয়ে বড় আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে গাদীরে খুমের হাদীস । আল্লামা তাব্রানী হযরত যায়েদ বিন আরকাম থেকে এমন এক সনদসহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার সত্যতা সম্পর্কে ইজমাবা সবার ঐকমত্য রয়েছে । তিনি (যায়দ ইবনে আরকাম) বলেছেন, মহানবী (সা.) খুমের জলাশয়ের কাছে গাছের নীচে ভাষণ দানকালে বলেছিলেন, ‘‘ হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমাকে মহাপ্রভূ আল্লাহর তরফ থেকে ডাকা হবে এবং আমাকে সে আহবানে সাড়া দিতে হবে । নিশ্চয় আমাকে যেমনিভাবে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও তোমাদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে । অতএব, তখন তোমরা কি বলবে? ” তখন উপস্থিত জনতা বলল, ‘‘ আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি ইসলাম প্রচার করেছেন, জিহাদ করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন । অতএব, মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন । ” এরপর মহানবী (সা.) বললেন, ‘‘ তোমরা কি সাক্ষ্য দেবে না যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ (রসুল) । বেহেশত সত্য । নরক (জাহান্নাম) সত্য । মৃত্যু সত্য । মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য । কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । মহান আল্লাহ সেদিন কবরে শায়িতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন ? ” ৫৬ তখন তারা সবাই বলল, ‘‘ হ্যাঁ, আমরা সবাই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব । ” মহানবী (সা.) তখন বললেন, ‘‘ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো । ” এরপর তিনি বললেন, ‘‘ হে জনতা, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার প্রভূ (মওলা) । আর আমি প্রতিটি মুমিনদের মওলা (অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক কতৃপক্ষ) । আমি তাদের (মুমিনদের) চেয়েও তাদের জীবনের উপর অধিকতর কর্তৃত্বশীল । অতএব আমি যার তত্ত্বাবধায়ক, কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষ ( مولی ) এই আলীও তার তত্ত্বাবধায়ক, কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষ । হে আল্লাহ! যে তাকে (আলীকে) ভালোবাসবে তাকে তুমিও ভালবাসো, আর যে তার সাথে শত্রুতা করবে তুমিও তার সাথে শত্রুতাকরো । ” ৫৭
আর এভাবে মহানবী (সা.) এ দু’ টি হাদীস (হাদীসে সাকালাইন এবং গাদীরে খুমের হাদীস) এবং উক্ত হাদীসদ্বয়ের মত অগণিত হাদীসে তাঁর আহলে বাইতের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার নেতৃত্বের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন । পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মহানবীর বর্ণিত হাদীস ও রিওয়ায়েতসমূহ অনুসরণ করার ব্যাপারে বিদ্যমান ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিটি হাদীসে সাকালাইন এবং গাদীরে খুমের হাদীসকে গ্রহণ করেছে এবং আহলে বাইতের উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করেছে । আর এটাই হচ্ছে আহলে বাইতের অনুসারী মুসলমানদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি ।
আর প্রত্যেক ইমামের সামাজিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অর্থ যদি ঐ ইমামের জীবদ্দশায় তাঁর শাসন-কার্য পরিচালনা করাই হয়ে থাকে,তাহলে আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব (المرجعیة الفکریة ) হবে এমনই এক স্থায়ী,অপরিবর্তিত বাস্তবতা যা কোন শর্তাধীন হবে না এবং ইমামের আয়ুষ্কালের গন্ডির মধ্যেও সীমাবদ্ধ করা যাবে না । সুতরাং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ ইসলাম এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান,হারাম-হালাল বিধান এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে ততদিন পর্যন্ত তারা সর্বদা মহান আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত আদর্শিক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকবে । আর এই আদর্শিক নেতৃত্ব প্রথমতঃ মহান আল্লাহর গ্রন্থ পবিত্র কোরানে বিধৃত এবং দ্বিতীয়ঃ মহানবীর পবিত্র সুন্নাহ্ এবং তাঁর নিষ্পাপ রক্তজ বংশধর তাঁরই আহলে বাইতের মাঝে প্রতিফলিত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে । মহানবী (সা.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে,তাঁর আহলে বাইত (আ.) কখনোই পবিত্র কোরান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না । কিন্তু পবিত্র কোরান ও হাদীস একনিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করার পরিবর্তে ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা মহানবী (সা.)-এর ওফাতের সময় থেকেই শাসনকার্য পরিচালনাকারী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কতকগুলো পরিবর্তনশীল ও গতিশীল নীতিমালার আলোকে মুহাজিরদের কিছু গণ্য-মান্য ব্যক্তির কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল । আর এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই মহানবীর ওফাতের পর সকীফা বনী সায়েদার চত্বরে সীমিত পরিসরে যে পরামর্শ করা হয়েছিল তদনুযায়ী হযরত আবু বকর সরাসরি শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন ।৫৮ অতঃপর হযরত আবু বকরের পক্ষ থেকে এক প্রত্যক্ষ অসিয়তের ভিত্তিতে হযরত ওমর (হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর) খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।৫৯ এরপর হযরত ওমরের পক্ষ থেকে পরোক্ষ অসিয়তের ভিত্তিতে হযরত ওসমান তাঁদের উত্তরাধিকারী হন ।৬০ আর খলীফা নিযুক্ত করার এ ধরনের অনুশীলন ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে মহানবী (সা.)-এর ওফাতের ৩০ বছরের মধ্যেই তালিক বা মহানবী (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয় দিবসে সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত কুরাইশদের সন্তানরা প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রসমূহে অধিষ্ঠিত হয়ে যায় । অথচ এরাই মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম,মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছে । যা কিছু এতক্ষণ বর্ণনা করা হল আসলে তা শাসনকার্য পরিচালনাকারী (রাজনৈতিক) নেতৃত্বের সাথেই সংশিষ্ট । তবে আদর্শিক (আধ্যাত্মিক ও চিন্তামূলক) নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বলতে হয় যে,আহলে বাইতের কাছ থেকে রাজনৈতিক-সামাজিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার পর ইজতিহাদ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে মহান আহলে বাইতের আদর্শিক (আধ্যাত্মিক ও চিন্তামূলক) নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা এবং মেনে নেয়া সুকঠিন ব্যাপার । কারণ মহান আহলে বাইতের (আ.) আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করার অর্থই হচ্ছে এমন বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব করা যার ফলে তাঁরা (আহলে বাইত) শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন এবং প্রাগুক্ত দু’ ধরনের নেতৃত্বকে নিজের মুঠোয় ফিরিয়ে আনতে পারবেন । ঠিক তেমনিভাবে শাসনকার্য পরিচালনাকারী খলিফার আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা এবং মেনে নেয়াও বেশ কঠিন । কেননা আদর্শিক নেতৃত্বের জন্য যে সব শর্ত থাকা অপরিহার্য তা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা থেকে ভিন্ন । অতএব,শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য কোন ব্যক্তিকে যোগ্য বলে মনে করার অর্থ কখনোই এটা নয় যে,ঐ ব্যক্তিকে আদর্শিক ইমাম বা নেতা হিসেবে এবং পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর পর তত্ত্বজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রামাণিক উৎস হিসেবে নিযুক্ত করা সম্ভব । কারণ এ ধরণের আদর্শিক নেতৃত্বের জন্য অতি উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃতি,কৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত চূড়ান্ত পারদর্শিতা এবং পারঙ্গমতা অপরিহার্য । আর এটাও দিব্য পরিষ্কার এবং প্রমাণিত সত্য যে,এ ধরণের যোগ্যতা একমাত্র আহলে বাইত (আ.) ব্যতীত এককভাবে আর কোন সাহাবার মাঝে বিদ্যমান ছিল না ।
এ কারণেই আদর্শিক নেতৃত্বের মাপকাঠি বেশ কিছুকাল দোদুল্যমান থেকে যায় । তাই বহুক্ষেত্রে খলিফাগণ ইমাম আলী (আ.)-এর সাথে তাঁরই আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে অথবা তাঁর আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অতি নিকটবর্তী অন্য কোন নীতি-মালার ভিত্তিতে আচরণ করেছে । এমনকি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরও বহুবার বলেছেন,‘‘ আলী যদি না থাকত তাহলে উমর ধ্বংসই হয়ে যেত । আমাকে আল্লাহ এমন কোন সমস্যায় জীবিত না রাখেন যেখানে (অর্থাৎ যা সমাধান করার জন্য) আবুল হাসান (আলী) উপস্থিত নেই।” ৬১ তবে কালক্রমে,মহানবীর ওফাতের পর মুসলমানগণ ধীরে ধীরে আহলে বাইত (আ.) এবং ইমাম আলী (আ.)-কে দোষগুণ সম্পন্ন সাধারণ মানুষ হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । আর এর ফলে আহলে বাইতের আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা একেবারে অনুভব না করা এবং এই আদর্শিক প্রামাণিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে আহলে বাইত (আ.) ছাড়াও অন্য কোন যথার্থ ও উপযুক্ত বিকল্পের উপর আরোপ করাও নিতান্ত সহজ ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । আর এই বিকল্প স্বয়ং খলিফা নিজেও নন বরং সাহাবা-ই কেরাম । এভাবেই আহলে বাইতের ধর্মীয় প্রামাণিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বদলে সামগ্রিকভাবে সাহাবা-ই কেরামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের তত্ত্বকে ধীরে ধীরে দাঁড় করানো হয় । আর সাহাবা-ই কেরামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং প্রামাণিকতা এমনই এক মোক্ষম বিকল্প যা পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ বিধৃত প্রামাণিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উপেক্ষিত হওয়ার পর সাধারণ মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী ও যথার্থ বলে বিবেচিত হয় । কেননা এরাই (সাহাবাগণ) হচ্ছে ঐ প্রজন্ম যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছে,মহানবীর জীবনাদর্শ ও অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন যাপন করেছে এবং তাঁর সুন্নাহ ও হাদীসকে অনুধাবন করেছে ।
আর এভাবেই,আহলুল বাইত (আ.) কার্যতঃ মহান আল্লাহ প্রদত্ত তাঁদের বিশেষত্বটি হারিয়ে সাহাবা হিসেবে আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বধারার একটি মাত্র অংশ হিসেবে পরিগণিত হন । সাহাবা-ই কেরামের মধ্যকার তীব্র মতবিরোধ ও পারস্পরিক বৈপরিত্যসমূহ অনেক সময় বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সূত্রপাত করেছে এবং এর ফলে একদল মুসলমান অন্যদলের রক্ত ঝরানো এবং মানসম্ভ্রমহানি করাকে বৈধ বলে মনে করেছে । একদল অন্যদলকে বিচ্যুত ও বিশ্বাসঘাতক বলে অপবাদও দিয়েছে ।৬২ আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বধারার বিভিন্ন গ্রুপ ও শ্রেণীর মধ্যকার এসব মতপার্থক্য এবং পারস্পরিক দোষারোপের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন প্রকার আদর্শিক এবং আকীদাগত মতপার্থক্য ও পারস্পরিক বৈপরীত্যের উদ্ভব হয় । আসলে এসব মতপার্থক্য এবং পারস্পরিক দোষারোপ প্রকৃতপক্ষে ইজতিহাদ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃক উদ্ভাবিত আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বধারার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের বাস্তব প্রতিফলন ।
শিয়া মাযহাবে আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক দিকসমূহ:
আমি এখানে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই আমার বিবেচনায় যার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে । আর তা হল যে কতিপয় গবেষক দু’ ধরনের তাশাইয়ু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তাশাইয়ু এবং রাজনৈতিক তাশাইয়ু-এর মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আধ্যাত্মিক তাশাইয়ু রাজনৈতিক তাশাইয়ু অপেক্ষা প্রাচীনতর । ইমামীয়া শিয়া মাজহাবের ইমামগণ যাঁরা ইমাম হুসাইনের বংশধর ছিলেন তাঁরা কারবালায় লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের পর নিজেদেরকে রাজনীতি ও পার্থিব কর্মকান্ড থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় উপদেশ দানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন ।
আর এটাও সত্য যে,জন্মলগ্ন থেকেই তাশাইয়ু কখনো নিছক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতারই অধিকারী ছিল না বরং মহানবীর ওফাতের পর আদর্শিক,সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সমানভাবে উম্মাহকে ইমাম আলী (আ.) কর্তৃক নেতৃত্ব দানের পরিকল্পনাস্বরূপ ইসলামের ক্রোড়েই তাশাইয়ুর উৎপত্তি হয়েছে । আর আমরা ইতোমধ্যে তাশাইয়ুর উৎপত্তি ও বিকাশের পরিস্থিতি বর্ণনা করার সময় এ বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি । ঠিক যেমনভাবে ইসলামের রাজনৈতিক দিক থেকে এর আধ্যাত্মিক দিককে পৃথক করা সম্ভব নয় ঠিক তেমনভাবে তাশাইয়ুর উৎপত্তির কারণ হিসেবে যে সব পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অবস্থা উল্লেখ করেছি সেগুলোর আলোকে রাজনৈতিক তাশাইয়ূ থেকে আধ্যাত্মিক তাশাইয়ুকেও পৃথক করা সম্ভব নয়।
সুতরাং তাশাইয়ুকে কোনক্রমেই বিভাজিত করা যাবে না । তবে যদি মহানবীর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পরিকল্পনাস্বরূপ তাশাইয়ু তার নিজস্ব অর্থ ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে তাহলে তখন তা হবে অন্য কথা (অর্থাৎ সেক্ষেত্রেই কেবল তাশাইয়ুকে আধ্যাত্মিক তাশাইয়ু ও রাজনৈতিক তাশাইয়ু এবং আরো নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাবে) আর মহানবীর তিরোধানের পর দাওয়াত বা ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যে ঠিক সমভাবেই মুখাপেক্ষী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই । শাসনকার্য বা খেলাফত পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন খলীফার ভূমিকা অব্যাহতভাবে চালিয়ে নেয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে সর্বসাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইমাম আলী (আ.)-এর প্রতি ব্যাপক গণসমর্থন ও জনপ্রিয়তা বিদ্যমান ছিল । আর এই ব্যাপক গণসমর্থনই তাঁকে (আলীকে) খলীফা উসমানের নিহত হওয়ার ঠিক পরপরই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল ।৬৩ তবে এই জনসমর্থন না ছিল আধ্যাত্মিক,না ছিল রাজনৈতিক । কারণ তাশাইয়ু ইমাম আলীকে তিন খলীফার বিকল্প এবং মহানবীর প্রত্যক্ষ খলীফা হিসেবেই বিশ্বাস করে । তাই ইমাম আলীর প্রতি মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপের ব্যাপক সমর্থনটা ছিল প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ তাশাইয়ু অপেক্ষাও ব্যাপকতর । আর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক তাশাইয়ুও এই ব্যাপক জনসমর্থনের অবকাঠামোর মাঝেই যদি বিকাশ লাভ করে থাকে তাহলেও এটাকে বিভাজিত তাশাইয়ুর উদাহরণ বলে বিবেচনা করা সম্ভব হবে না । যেহেতু ইমাম আলী (আ.) খলীফা আবু বকর ও খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে হযরত সালমান,হযরত আবু যার এবং হযরত আম্মারের মত বড় বড় প্রবীণ সাহাবীর আত্মিক ও নৈতিক (মনস্তাত্বিক) সমর্থন পেয়েছিলেন সেহেতু এ থেকেও বোঝা যায় না যে,আধ্যাত্মিক তাশাইয়ু রাজনৈতিক দিক বিবর্জিত। বরং এটা ছিল মহানবীর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার কার্যক্রমে ইমাম আলীর আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি ঐ সব সাহাবার আস্থা ও ঈমানেরই পরিচায়ক । ইমাম আলীর নেতৃত্বের আদর্শিক দিকের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস যেমনভাবে তাদের প্রাগুক্ত আত্মিক ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক তদ্রুপ খলীফা আবু বকরের খেলাফত এবং যে দৃষ্টিভঙ্গিটি ইমাম আলীর হাত থেকে শাসনকর্তৃত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করার জন্য দায়ী সেটার বিরোধিতা করার মাধ্যমে ইমাম আলীর নেতৃত্বের রাজনৈতিক দিকের প্রতিও তাদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে ।৬৪
আসলে রাজনৈতিক তাশাইয়ু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আধ্যাত্মিক তাশাইয়ুকে উপস্থাপন সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিটি একদল শিয়া মুসলমানের মন-মানসিকতায় এমনিতেই অর্থাৎ বিনা কারণে উৎপন্ন হয়নি । বরং রূঢ় বাস্তবতার কাছে তার আত্মসমর্পণ ও নতিস্বীকার,মুসলিম উম্মাহকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী নেতৃত্বকে প্রস্তুতকরণ এবং মহানবীর হাতে গড়ে উঠা ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা হিসেবে তাশাইয়ুর জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ তার অন্তরে নিভে যাওয়া এবং কিছু নিছক প্রাণহীন আকীদা-বিশ্বাসে তাশাইয়ুর রূপান্তরিত হওয়ার পরপরই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে । উল্লেখ্য যে,এ নিছক আকীদা-বিশ্বাস এমনই যে,মানুষ তার নিজ হৃদয়কে এর সাথে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে এবং এ থেকে সে তার নিজ জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দ এবং আশা-আকাঙ্খা পেতে চায় ।
এখন ঐ কথা প্রসঙ্গে আসা যাক যা ব্যক্ত করে যে,আহলুল বাইতের ইমামগণ যাঁরা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন এবং পার্থিব কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন । কিন্তু ইসলামের নেতৃত্বধারাকে অব্যাহতভাবে গতিশীল ও সচল রাখার ফর্মুলা স্বরূপ তাশাইয়ুকে অনুধাবন করার পর ইসলামী নেতৃত্ব বলতে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর গঠন পরিপূর্ণ করার জন্য মহানবী (সা.) যে সংস্কার কর্মকান্ড চালিয়েছিলেন ঠিক সেটাই যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে তাশাইয়ু মতাদর্শ বর্জন না করা ব্যতীত রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে ইমামদের সরে আসা কস্মিনকালেও সম্ভব নয় । তবে যে বিষয়টি রাজনৈতিক নেতৃত্বদান করা থেকে ইমামদের নির্লিপ্ত ও দূরে থাকার ধারণাটিকে শক্তিশালী করেছে তা হল প্রতিষ্ঠিত অবস্থার বিরুদ্ধে ইমামগণের সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্যোগ না নেয়া। অথচ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থ কেবলমাত্র এ ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম ও পদক্ষেপ গ্রহণের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ ।
ইমামদের থেকে বেশ কিছু দলীল রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,যুগের ইমাম সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন যদি তিনি সাহায্যকারীদের অস্তিত্ব এবং ঐ সংগ্রামের ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও সামর্থ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন ।৬৫
আমরা যদি শিয়া আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে,আহলুল বাইতের ইমামগণ কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করতেন না । ইসলামের নির্দেশিত পথে সংস্কার-কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হবে না যে পর্যন্ত না এই প্রশাসন (অর্থাৎ ইমাম-প্রশাসন ও সরকার) জনপ্রিয় সচেতন গণভিত্তি দ্বারা সমর্থিত হবে । আর এ ধরনের সচেতন জনপ্রিয় গণভিত্তিসমূহই ইমামদের প্রশাসনের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথার্থভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং শাসনকার্য সংক্রান্ত ইমাম-প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ণ আস্থাবান ও বিশ্বাসী হবে । এসব গণভিত্তি ইমাম-প্রশাসনকে সর্বদা সমর্থন করে যাবে। ইমাম জনগণের কাছে প্রশাসনের যাবতীয় পদক্ষেপ ও নীতি অবস্থান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং সব ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে স্থির,অবিচল ও অটল থাকবেন ।
মহানবীর ওফাতের পর অর্ধশতাব্দী ধরে শিয়া নেতৃত্বধারা শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিশ্বাস করত সেসব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে সরকার ও প্রশাসনকে নিজের আয়ত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছে। কারণ শিয়া নেতৃত্বধারা ঐ সময় সচেতন জনপ্রিয় গণভিত্তিসমূহের অস্তিত্বে অথবা মুহাজির-আনসার এবং তাবেয়ীদেরকে বদান্যতার সাথে সচেতন করার মাধ্যমে শাসন-কর্তৃত্ব নিজের আয়ত্বে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও বিশ্বাস করত । তবে অর্ধশতাব্দী পরে এবং উক্ত জনপ্রিয় গণভিত্তির আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকার পর এবং বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে তরলমনা প্রজন্মসমূহের বিকাশের কারণে শিয়া-আন্দোলন কর্তৃক নিছক প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করাটাই সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়নি । কারণ সচেতনতাবোধ ও আত্মত্যাগের স্পৃহাসম্পন্ন সেই জনপ্রিয় গণভিত্তিসমূহ তখন আর বিদ্যমান ছিল না। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র দু'টি কাজ করারই সুযোগ রয়েছে । আর তা হল ঃ
প্রথমতঃ ভবিষ্যতে শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য ঐ সচেতন জনপ্রিয় গণভিত্তিকে পুনরায় গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করা ।
দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মাহর বিবেক ও ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা এবং উম্মাহর জাগ্রত ইসলামী বিবেক ও ইচ্ছাকে এমনভাবে প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত রাখা যার ফলে উম্মাহ্ বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট শাসকদের সামনে নিজ ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা পাবে । আর প্রথম কাজটিই স্বয়ং ইমামগণ (আ.) নিজেরাই আঞ্জাম দিয়েছেন । আর দ্বিতীয় কাজটি হযরত আলীর বিপ্লবী বংশধরদের হাতে সম্পন্ন হয়েছে । তাঁরা (আলী বংশীয় বিপ্লবীগণ) তাঁদের বীরত্বব্যাঞ্জক আত্মত্যাগ ও কোরবানীর মাধ্যমে ইসলামী বিবেকবোধ ও সংকল্প চিরঞ্জীব রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন । আর তাঁদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান (মুখলেস) ছিলেন তাঁদেরকে আহলে বাইতের ইমামগণ সমর্থন করেছেন ।
ইমাম আলী ইবনে মুসা আর রেযা (আ.) শহীদ যায়েদ ইবনে আলী সম্পর্কে আব্বাসীয় খলীফা মামুনকে একবার বলেছিলেন,“ তিনি (হযরত যায়েদ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর আলেমদের মধ্যে অন্যতম । তিনি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে (প্রচলিত পরিস্থিতি ও অবস্থার ব্যাপারে) ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত জিহাদ করে গিয়েছেন । আমার পিতা মুসা ইবনে জাফর আমাকে বলেছেন,আমি আমার পিতা জাফর বিন মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি,মহান আল্লাহ আমার চাচা যায়েদের প্রতি করুণা করুন । কারণ তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রিয় (ইমামের) প্রতি (জনগণকে) আহবান করেছিলেন । যদি তিনি বিজয়ী ও সফল হতেন তাহলে তিনি যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে অবশ্যই পূর্ণ নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন ।
যায়েদ বিন আলী নিঃসন্দেহে যা সত্য নয় সে দিকে দাওয়াত দেননি । তিনি এ ব্যাপারে মহান আল্লাহকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী ভয় করতেন । তিনি বলতেন,আমি তোমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহলে বাইতের সন্তুষ্টির প্রতি আহবান জানাচ্ছি ।” ৬৬
অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে,ইমাম জাফর আস্-সাদেক (আ.)-এর সমীপে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে যাঁরা (তদানীন্তন স্বৈরাচারী জালিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র) সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করা হলে তিনি (আ.) বলেছিলেন,“ আমি এবং আমার শিয়ারা এখনও উত্তম অবস্থায় রয়েছি । মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ বিদ্রোহ করেনি । আর তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে,মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ বিদ্রোহ করুক এবং তার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার হোক ।” ৬৭ সুতরাং বিচ্যুত শাসকদের বিরুদ্ধে ইমামদের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা না করার অর্থ এটা নয় যে,ইমামগণ তাঁদের নেতৃত্বের রাজনৈতিক দিকটি পরিহার করে কেবলমাত্র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন । অথচ ইমামদের সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ না হওয়াটাই সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ার অবয়বগত যে পার্থক্য ও ভিন্নতা আছে তারই পরিচায়ক । আর বিভিন্ন ধরনের বস্তুনিষ্ঠ অবস্থায় সমাজ-সংস্কার প্রক্রিয়ার অবয়ব ও ধরনকে সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে থাকে । এ ছাড়াও ইমামদের এ ধরনের আচরণ (প্রত্যক্ষ শসস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত না হওয়া) সমাজ সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি এবং তা বাস্তবায়নের স্বরূপ সংক্রান্ত তাঁদের সুগভীর জ্ঞান ও অনুভূতিরই পরিচায়ক ।
তথ্যসূত্রঃ
১. তন্মধ্যে মুহাম্মদ রশিদ রেজা তার (আসসুন্নাহ ওয়াশ শিয়া) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার আলোচনায় এটি উল্লেখ করেছেন।
২. তারিখুল ইমামিয়া ওয়া আসলাফিহীম মিনাশ শিয়া গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠা পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৩.প্রাগুক্ত।
৪.সহীহ মুসলিম,৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা:-১৮৭৪ এবং মুখতাসারে তারিখে ইবনে আসাকির, ১৮ তম খণ্ড,পৃষ্ঠা:-৩২।
৫. তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:-২০১-২০২।
৬.সূরা নিসা,আয়াত নং-১৩৮-১৪৬;সূরা তওবা,আয়াত নং-৬৪-৬৮;সূরা আহযাব,আয়াত নং-১২-১৫;সূরা মুনাফেকুন,আয়াত নং-১-৪ ও আরো অনেক আয়াত।
৭.তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪২৮,মুখতাসারে ইবনে আসাকির,১৮তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩০৮-৩০৯।
৮. তারিখে তাবারী,৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা-২২৮।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২০৫।
১১. শারহে নাহ্জুল বালাগ্বা,ইবনে আবিল হাদীদ,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪২।
১২. আল কামিল ফিততারিখ ইবনুল আসির,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩১৮;তাবাকাতে ইবনে সা’ দ,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৪৯ ।
১৩. মুসনাদে আহমাদ,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩৫৫;সহী মুসলিম,৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৭৬; আত-তাবাকাতুল কুবরা,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৪২;সহী বুখারী,১ম খণ্ড,কিতাবুল ওয়াসিয়া অধ্যায়,পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৮ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৬১ ।
১৪. তাবাকাতে ইবনে সা’ দ,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩৪৩ ।
১৫. তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৩১ ।
১৬. তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২১৮-২১৯ ।
১৭. শারহে নাহজুল বালাগ্বা,ইবনে আবিদ হাদীদ,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা-৭ ।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯ ।
২০.তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৩৩ ।
২১.তারিখে তাবারী,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৫৬৯ । (খন্দক খননের সময় রাসূলের হাদীস)।
২২.ইবনে হাজার তার“ আল ইছাবাহ্ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ গ্রন্থে নবীর (সা.) সাহাবা সংখ্যা ১২২৬৭ জন বলেছেন।
২৩.ডঃ সুবহি সালিহ্ নাহাজুল বালাগ্বার উপর গবেষণা গ্রন্থের ৩২৭ পৃষ্ঠাষ্ঠায় হযরত আলীর (আ.) ২১০ নং খূৎবার আলোচনায় এটি উল্লেখ করেছেন ।
২৪.সূনানে দারেমী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৬৩,হাদীস নং-১২৪ ।
২৫.আল গাদীর,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৯৩ ।
২৬.প্রাগুক্ত।
২৭.সূনানে দারেমী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮,হাদীস নং-১৪৯ ।
২৮.সূরা আবাসা,আয়াত নং-২৭-৩১ ।
২৯. আল ইতক্বান ফি উলুমিল কুরআন,আল্লামা সূয়ূতি,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪ ।
৩০.সুনানে দারেমী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৩০ ।
৩১.আত তাবাকাতুল কুবরা,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৮৭ ।
৩২.উসূলুল কাফী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৪১-২৪২ ।
৩৩.কানযুল উম্মাল,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৭২ । (কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরার নির্দেশ)।
৩৪.কানযুল উম্মাল,১৩তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১১৪,হাদীস নং-৩৬৩৭২।আত্ তাফসীরুল কবির,৮ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-২১ ان الله اصطفی آدم এই আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য ।
৩৫.আহকামুল কুরআন,৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৭৭৮,সুরা হাশর দ্রষ্টব্য ।
৩৬.শারহে মায়ানিয়েল আসার,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৯৫-৪৯৬,জানাযার তাকবিরের সংখ্যা অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।
৩৭.ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবীর আল ইসরাঈলিয়াত ফিত্ তাফসীর ওয়াল হাদীস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৩৮.দেখুন সূরা মায়েদা,আয়াত নং-১৫-১৯ এবং সূরা আলে ইমরান,আয়াত নং-৬০ ও পরবর্তী আয়াত সমূহ ।
৩৯.সুরা নাসরের তাফসীর দেখুন।
৪০.সুরা তওবা,আযাত নং-৬০ দ্রষ্টব্য।
৪১.সুরা মুনাফেকুনের তাফসীর দেখুন।
৪২.আন্-নেযা ওয়াত্তাখাছুম বাইনা বানি হাশিম ওয়া বানি উমাইয়া গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৪৩.সুনানুল কুবরা,আনসারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৪২,হাদীস নং-৮৫০৪,৮৫০৫, ৮৫০৬। আস-সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ,পৃষ্ঠা-১২৮,হাদীস নং-১১।
৪৪.আল-মুস্তাদরাক আল সহীহাইন ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-১২৫।
৪৫.মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা. ১৭৮,হাদীস নং-৮৮৫।
৪৬.হাদীসে সাকালাইন: সিহাহ,সুনান এবং মাসানীদ রচয়িাতগণ কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ।(দ্র:-সহীহ মুসলিম ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৮৭৩,সহীহ আত তিরমিযী, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৫৯৬ কামাল আল হুত কর্তৃক গবেষণাকৃত,দারুল ফিকর থেকে মুদ্রিত)
৪৭.হাদীসুল মানযিলাহ: মুসার কাছে হারূনের যেরূপ মর্যাদা সেরূপ তুমি আমার কাছে……( দ্র: সহীহ আল– বুখারী,তাবুকের যুদ্ধ,৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৮১,অধ্যায় ৩৯,সুনানে তিরমিযী,৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৫৯৯,হাদীস নং-৩৭৩১)।
৪৮.হাদীসে গাদীর : (দ্র:সুনানে ইবনে মাজাহ ভূমিকা:অধ্যায় ১১,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৪৩,হাদীস নং-১১৬)মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল,৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৮১,দারুস সাদির বৈরুত থেকে মুদ্রিত।
৪৯.আত্ তাজুল জাম’ লিল উসুল,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:৩৩০-৩৩৭।
৫০.সিরাতুননাবাবী,ইবনে হিশাম,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:৩১৬-৩১৭।
৫১.মুসনাদে আহমাদ,৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৫৯০,হাদীস নং-১৯৩৪০;আত্ তাজুল জামে লিল উসুল,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:১২৪।
৫২.মুস্তাদরাক আলাস-সাহীহাইন,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৬৯;সহীহ বুখারী,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:২৫২;আননাছ ওয়াল ইজতিহাদ-আল্লামা শরাফুদ্দিন,২০৮ পৃষ্ঠার পর দেখুন।
৫৩.সহীহ বুখারী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৩৭,কিতাবুল ইলম অধ্যায় এবং ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা:১৩৭-১৩৮।
৫৪.আত-তাবাকাতুল কুবরা,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৪৯-২৫০।
৫৫.কানযুল উম্মাল,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৮৬,হাদীস নং-৯৪৪,সুনানুত্ তিরমিযি,৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৬২২,হাদীস নং-৩৭৮৮।
৫৬.আল-মুস্তাদরাকুস সহীহাইন (আল-হাকেম আন নিসাবুরী প্রণীত) ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:১১৯;আল-হাকেম বলেছেন: শায়খাইন অর্থাৎ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসে সাকালাইন সহীহ হাদীস। সহীহ মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৮৭৪;সহীহ তিরমিযী,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৩০;আস-সুনান আল-কুবরা(ইমাম নাসাঈ প্রণীত)৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:৬২২;মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা:২১৭,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৪-১৭;সুনানে আদ-দারেমী ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৩২, পবিত্র কোরানের ফযীলত বা মর্যাদা অধ্যায়,দার ইহয়া ইসসুন্নাহ আন-নাবাবীয়াহ কর্তৃক মুদ্রিত।
৫৭.আল্লামা আমিনী প্রণীত আল-গাদীর গ্রন্থ,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩১-৩৬;সুনানে ইবনে মাজাহ,১ম খণ্ড,ভূমিকা,১১তম অধ্যায়;মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা:২৮১ এবং ৩৬৮ দারুস সাদর কর্তৃক মুদ্রিত।হাদীসে গাদীর শিয়া ও সুন্নি উভয় সূত্রে মুস্তাফিজ হাদীস হিসেবে পরিগণিত। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ গাদীরের হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবার সংখ্যা শতাধিক,তাবেয়ীনের সংখ্যা আশির অধিক এবং দ্বিতীয় শতাব্দির হাদীস বর্ণনাকারী ও রেজালশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ষাটের মত বলে উল্লেখ করেছেন । আল্লামা আমিনীর আল– গাদীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।
৫৮.তারিখুত তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২০৩ হতে পরবর্তী অংশ।
৫৯.তারিখুত তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪২৮ হতে পরবর্তী অংশ।
৬০.তারিখুত তাবারী,৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২২৭-২২৮।
৬১.যাখায়েরুল উকবাহ,পৃষ্ঠা.৮২,মানাকিবুল খাওয়ারেজমী,পৃষ্ঠা:৮১,আত্ তাবাকাতুল কুবরা,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:৩৩৯।
৬২.তারিখে তাবারী,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৮০।
৬৩.নাহজুল বালাগ্বা,পৃষ্ঠা-৪৯,খুতবা নং-৩,(খুতবায়ে শিক শিকিয়া),তারিখে তাবারী,২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৬৯৬।
৬৪.আল ইহতিজায,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৮৬।
৬৫.উসুলে কফি,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৪২,মুমিনদের সংখ্যা স্বল্পতার অধ্যায়।
৬৬.ওয়াসায়েলুশ শিয়া,১৫তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৫৩,বাব-১৩,হাদীস নং-১১।
৬৭.ইবনে ইদ্রিস প্রণীত আস-সারায়ের,৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা ৫৬৯ এবং ওয়াসায়েলুশ শিয়া,১৫তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৫৪,হাদীস নং-১২।
গ্রন্থসূচী
১-আল্ ইতকান ফি উলুমিল কোরআন,জালাল উদ্দীন সূয়তী,আররাজী প্রকাশনা,কোম ।
২-আল্ ইহতিজাজ,আহমাদ ইবনে আবি তালিব আততাবরাসী,উসভে প্রকাশনা,তেহরান ।
৩-আহ্কামুল কোরআন,মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী,ঈসা আল বাবী আল হালাবী প্রকাশনী,লেবানন ।
৪-আল ইসরাঈলীয়াত ফিত তাফসীর ওয়াল হাদীস,ডক্টর মুহাম্মদ হুসেইন আযযাহাবী, দারুল ঈমান প্রকাশনী,দামেস্ক ।
৫-আল ইয়বাহ্ ফি তাময়ীয়িছ ছাহাবা,আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী।
৬-আত-তাজুল কামে লিল উছুল,শেইখ মানসুর আলী নাসিফ,দারু ইহ ইয়াউত তুরামিল
আরাবী ।
৭-তারিখুল ইমামীয়া ওয়া আসলাফিহিম মিনাশ শিয়া,ডক্টর আব্দুল্লাহ্ ফাইয়ায,আসআদ
প্রকাশনী,বাগদাদ ।
৮-তারিখুত তাবারী,মুহাম্মদ ইবনে জারির আততাবারী,গবেষনা মুহাম্মদ আবিল ফাজল ইব্রাহীম,রাওয়াঈত তুরাসুল আরাবী প্রকাশনা,মিশর ।
৯-তারিখুল ইয়াকুবী,আহমাদ ইবনে আবি ইয়াকুব আলইয়াকুবী,আল-আল আ’ লামী প্রকাশনী,বৈরুত ।
১০-আততাফসীরুল কাবির,ফাখরুর রাবী,দারুল কুতব আল ইলমিয়াহ্,তেহরান ।
১১-হুলইয়াতুল আউলিয়া,আল হাফিজ আবু নাঈম আল ইসফাহানী,দারুল কিতাবিল আরাবী।
১২-খাসায়িসু আমিরিল মুমিনীন,নাসায়ী আশশাফিয়ী,নাইনাওয়া প্রকাশনা,তেহরান ।
১৩-যাখায়িরুল উকবা,আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ মুহিবুদ্দীন আততাবারী,দারুল মা’ রিফা প্রকাশনী,তেহরান ।
১৪-আর রিযাদ্বুন নাদ্বরাহ্,আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ মুহিবুদ্দীন তাবারী,কায়রো ।
১৫-সুনানে ইবনে মাজা,ইবনে মাজা কাযভীনি,দারুল ফিকর ।
১৬-সুনানুত তিরমিযী,মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সুরা,দারু ইহইয়ায়ুত তুরাসুল আরাবী ।
১৭-আস্ সুনানুল কোবরা,আহমাদ ইবনে শুয়াইব আননাসায়ী,দারুল কুতুবুল ইলমিয়া,বৈরুত।
১৮-সুনানুদ দারেমী,আব্দুল্লা হ্ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আদদারেমী,দারুল
কিতাবিল আরাবী ।
১৯-আস্ সিরাতুন নাবাভীয়া,আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম,দারুল ভীফাক,বৈরুত ।
২০-শারহু মায়ানীয়িল আসার,আবু জা’ ফার আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আততাহাভী,
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ।
২১-শারহে নাহ্জল বালাগা,আব্দুল হামিদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিল হাদীদ
আল মু’ তায়িলী,দারুল কুতুবিল আরাবিয়াতিল কুবরা,মিশর ।
২২-সাহীহুল বুখারী,মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল জো’ ফী আল বুখারী,দারুল ফিকর,বৈরুত।
২৩-সহীহ মুসলিম,মুসলিম ইবনেল হাজ্জাজ আলকুশাইরী,মুহাম্মাদ আলী ছাবিহ্ প্রকাশনী,কায়রো ।
২৪-আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ,আহমাদ ইবনে হাজার,দারুল কুতুবুল ইলমিয়া,বৈরুত ।
২৫-আত- তাবাকাতুল কুবরা,মুহাম্মদ ইবনে সা’ দ আয-যুহাইরী,দারুল কুতবলু
ইলমিয়া,বৈরুত ।
২৬-আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা,আল্লামা সাইয়েদ মুরতাজা আল-আসকারী,আত-তাওহীদ
প্রকাশনী ।
২৭-আল-গাদীর,আল্লামা আব্দুল হুসেইন আহমাদ আল আমিনী,দারুল কুতুবুল
ইসলামীয়া,তেহরান ।
২৮-আল কাযী,মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল কুলাইনী,দারুল কুতুবল ইসলামীয়,তেহরান ।
২৯-আল কামিল ফিত তারিখ,ইবনুল আমির,দারু সাদের প্রকাশনী,বৈরুত ।
৩০-কানযুল উম্মাল,আলাউদ্দীন আল মুত্তাকী আল হিন্দী,আর-রিসালাহ্ প্রকশানী ।
৩১-মুখতাছারে তালিখে ইবনে আসাকির ইবনে মানযুর আল আফিকি,দারুল ফিকির,দামেস্ক।
৩২-আল মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন,আল হাকিম আন নিশাবুরী,দারুল মা’ রেফা,বৈরুত।
৩৩-মুসানাদুল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল,দারুসাদের,বৈরুত ।
৩৪-আল মানাকিব,আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল মাক্কী আল খাওয়ারিযমী,কোম হতে প্রকাশিত ।
৩৫-আল মুয়াভা,মালিক ইবনে আবাস,দারুল ফিকর,বৈরুত ।
৩৬-আননেযা ওয়াততাখাছুম বাইনা বানি হাশিম ওয়া বানি উমাইয়া,তাকীউদ্দীন মাকরিযী,মানশুরাতুশ শারিফ আররাদ্বী ।
৩৭-নাহজুল বালাগা,শারহে ডক্টর সুবহী সালিহ্ ।
৩৮-ওয়াসায়িলুশ শিয়া,আল হুররুল আমিলী,আলুল বাইত প্রকাশনী,কোম ।
৩৯-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাহ্,আল কাজযী আল হানাফী,মানুশুবাতু মুয়াস সাসাতিল আ’ লামী, বৈরুত ।
সূচীপত্র
অবতরণিকা. ৮
তাশাইয়ু বা শিয়া প্রবণতার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ? ১১
ভবিষ্যতের দাওয়াতের বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান ১৩
শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে খলীফা নির্ধারণের ইতিবাচক পদক্ষেপ ১৯
প্রত্যক্ষ মনোনয়নের মাধ্যমে মহানবীর খলীফা নিযুক্তকরণের ইতিবাচক পদক্ষেপ.. ৪৫
কিরূপে শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি ঘটল ? ৫২
মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় দু’টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ৫২
নবীর (সা.) আহলে বাইতই আদর্শিক ও নেতৃত্বদানকারী কর্তপক্ষ ৫৯
শিয়া মাযহাবে আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক দিকসমূহ : ৬৫
তথ্যসূত্রঃ... ৭১
গ্রন্থসূচী ৭৬