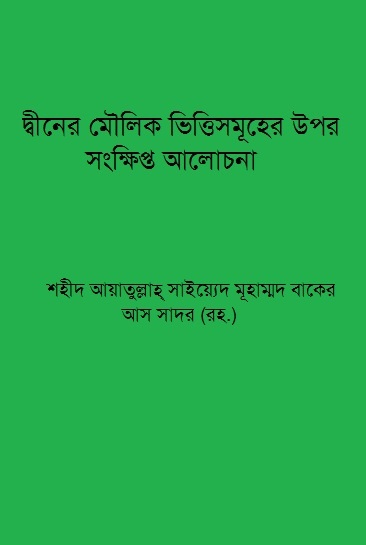দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা
মূল : শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মূহাম্মদ বাকের আস সাদর (রহ.)
অনুবাদ : মোঃ মাঈনুদ্দিন তালুকদার
প্রকাশকাল :
১৪ই আশ্বিন,১৪০৮ বঙ্গাব্দ
১০ই রজব,১৪২২ হিজরী
২৯ সেপ্টেম্বর,২০০১ ইংরেজি
প্রকাশনায় :
শহীদ আল্লামা বাকের সাদর (রহঃ) বিশ্ব সম্মেলন কমিটি,কোম-ইরান।
DINER MAULIK VITTI SAMUHER UPAR SANKHIPTA ALOCHANA
Originated From ‘MUZES FEE USULE DIN’ Of Shahid Sayyed Baqer As-Sadr,Traslated Into Bangla By Md. Mainuddin,Published By Kongre-E Shahid Sadr.
সম্মেলন কমিটির বক্তব্য
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী আত-তাহেরীন।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে ছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। যার পরিণতিতে বিচ্যুত,অবনতি আর জড়তার আধার উম্মাকে ছেয়ে ফেলেছিল। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুসলিম উম্মার পুনর্জাগরণ শুরু হয়। ইমাম খোমেইনীর (রহ.)নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে তা পরিপুর্ণতা অর্জন করে,ইসলামী শক্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়।দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী ও অত্যাচারীদের হাতে শোষিত হওয়ার পর উম্মার ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার সে শক্তি সঞ্চয় করেছে,মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। মুসলিম উম্মার এ পুনর্জাগরণ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে,উপনিবেশবাদী লোলুপ দৃষ্টি পোষণকারীদের আশা আকাঙ্ক্ষার কবর রচনা করেছে।
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মার মধ্যে আজ যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে ইমাম খোমেইনী(রহ.)মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি চিন্তাগত ও তত্ত্বগত দিক থেকে উম্মার মধ্যে যে জোয়ার এসেছে সেক্ষেত্রে শহীদ আল্লামা বাকের সাদর নিঃসন্দেহে মৌলিক অবদান রেখেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন নজিরবিহীন। তার চিন্তাধারা ও লেখনি একদিকে যেমন চিন্তার জগতে নব-দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে অপরদিকে গভীরতা ও ব্যপকতার দিক থেকেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন চিন্তাধারার পারস্পরিক সংঘাতময় পরিবেশেও তিনি বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদদের মহলে ব্যাপকভাবে ইসলামী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।
শহীদ আয়াতুল্লাহ বাকের সাদর তার নজিরবিহীন ব্যক্তিত্ব,অসাধারণ যোগ্যতা ও গতিশীল ইসলামী চিন্তাধারার মাধ্যমে আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদেরকে অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। বস্তুবাদী সভ্যতার তত্ত্বগত ভিত্তিহীনতা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি সবাইকে চিন্তাগত দাসত্বের শৃঙ্খল,(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের)অন্ধ অনুকরণ ও খোদাবিমুখতা থেকে ফিরিয়ে রাখেন। বাস্তব জীবনে মানব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের যে নজিরবিহীন ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন আধুনিক বিশ্ব যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাহলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকুলের সৌভাগ্য রচিত হবে,মানব সমাজ কল্যাণ লাভ করবে।
শহীদ আল্লামা বাকের সাদর অত্যন্ত গতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তার চিন্তাধারা কোন বিশেষ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলনা,বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি,তুলনামূলক দর্শন (ইসলামী ও পশ্চাত্য দর্শন),আধুনিক যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সাম্প্রতিককালে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেছেন এবং নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। উসূল ও ফেকাহশাস্ত্র,দর্শনশাস্ত্র,যুক্তিবিদ্যা,কালামশাস্ত্র,তাফসীর,ইতিহাস ইত্যাদি ক্লাসিক বিষয়েও পদ্ধতিগত ও বিষয়-বস্তুগত উভয় দিক থেকে নতুন নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং চিন্তাগত বিপ্লব ঘটিয়েছেন।
আল্লামা বাকের সাদরের শাহাদতের পর দু ’ দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে,কিন্তু আজও পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে তার চিন্তাধারার প্রভাব অটুট রয়েছে। যে কোন বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তার রেখে যাওয়া রচনাবলী,বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন তা সবার জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকবে।
এ দৃষ্টিকোণ থেকেই শহীদ আল্লামা বাকের সাদর বিশ্ব সম্মেলন পরিচালনা কমিটির প্রধান দায়িত্ব হবে চিন্তাগত ও জ্ঞানগত বিভিন্ন বিষয়ে তার রেখে যাওয়া মূল্যবান রচনাবলীর পুনরুজ্জীবন ও উপযুক্ত সংরক্ষণ। যেহেতু তার রচনাবলী অত্যন্ত ব্যাপক তাই এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনের ক্ষেত্রে দু ’ টি দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবেঃ
প্রথমতঃ অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও সূক্ষ্ণ দৃষ্টিসহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এগুলোর অনুবাদ এবং প্রকাশ।
দ্বিতীয়তঃ অত্যধিকবার প্রকাশিত হওয়া এবং উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে তার প্রকাশিত অনেক বই যেগুলো আংশিকভাবে বিকৃত হযেছে সেগুলোকে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং সংশোধন করা।
সবশেষে আমরা আল্লামা বাকের সাদরের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের,বিশেষ করে তার স্বনামধন্য পুত্র জনাব সাইয়্যেদ জাফর সাদর(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)-এর অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লামা বাকের সাদরের বিভিন্ন রচনাবলী প্রকাশ ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ সম্মতি প্রদান করেছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
পরিচালনা কমিটি
শহীদ আল্লামা বাকের সাদর বিশ্ব সম্মেলেন
দীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের উপর
সংক্ষিপ্ত আলোচনা
ভূমিকা
v ১-প্রেরক
v ২-প্রেরিত
v ৩-রিসালাত
ভূমিকা
কোন কোন বিশিষ্ট আলেম,আমার অনেক ছাত্র এবং অন্যান্য মুমিন আমার নিকট কামনা করেছেন যে,পূর্ববতী আলেমগণের অনুসরণে ও তাঁদের মহান কীর্তির উপর নির্ভর করে উত্তরোত্তর যে বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়টির উপর একটি ভূমিকা লিখব। আর সে বিষয়টি হলো : পূর্ববর্তী আলেমগণ সাধারণত তাঁদের গবেষণাপত্রের প্রারম্ভে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও দীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের প্রমাণের জন্য কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে আবার কখনো বা বিস্তৃতরূপে ভূমিকা লিখতেন। কারণ তাঁদের গবেষণাপত্রসমূহ ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে থাকে,যার জন্য পবিত্র ও মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবীকে জগতের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আর এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে এ মূল ভিত্তিসমূহের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। অতএব,প্রেরক আল্লাহ,প্রেরিত নবী এবং তাঁর রিসালাত-যার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন-তার প্রতি বিশ্বাস থেকেই বিধি-নিষেধ ও এর প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা রূপ পরিগ্রহ করে।
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশায় এবং এ আলোচ্য বিষয়ের অতীব গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের এ আহ্বানে আমি সাড়া প্রদান করলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো : আমি কোন্ পদ্ধতিতে এ ভূমিকা লিখব? আমি কি ফতুয়ায়ে ওয়াযিয়ার মতো যথাসম্ভব সহজ-সরল প্রক্রিয়ায় এ ভূমিকা লিখার চেষ্টা করব,যা ‘ ফতুয়ায়ে ওয়াযিহার ’ মতো সর্বসাধারণের জন্য ঐরূপ বোধগম্য হবে যেরূপ কারো জন্য ইসলামী বিধানের কোন হুকুম সহজবোধ্য হয়? তবে লক্ষ্যণীয় যে,প্রকৃতপক্ষে এ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ও ‘ আল ফতুয়াতুল ওয়াযিহার ’ মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ ফতুয়া কোন প্রকার দলিল উপস্থাপন ব্যতীত কেবল গবেষণালব্ধ ও আবিষ্কৃত বিধিকে তুলে ধরে,অথচ আমাদের আলোচ্য ভূমিকাটির উপস্থাপনই যথেষ্ট নয়,বরং দীনের মৌলিক ভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনের বিধিগত আবশ্যকতার জন্য আমরা এর সপক্ষে যুক্তির অবতরণা করতে বাধ্য। এছাড়া আমাদের এ ভূমিকার উদ্দেশ্যই হলো দীনের ভিত্তি ও মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রতিষ্ঠা করা। আর যুক্তি বা দলিল উপস্থাপন ব্যতীত তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে যুক্তি প্রদর্শনেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই,এমনকি সরলতম ও প্রাথমিক স্তরসমূহও (স্ব স্ব ক্ষেত্রে) গ্রাহককে পরিপূর্ণরূপে তুষ্ট করে থাকে। যদি মুক্ত ও নিষ্কলুষ বিবেকের মানুষ হয়,তবে সরলতম ও প্রাথমিক স্তরের দলিলই প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে তার জন্য যথেষ্ট। বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে কোরআনের এ প্রশ্নই তাকে তুষ্ট করে :
أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمُ الخاَلِقُونَ
“ উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হইয়াছে,না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা? ”
(সূরা তূর : ৩৫)
কিন্তু গত দু ’ শতাব্দীতে নব নব (জটিল) চিন্তার ফলে মুক্ত ও নির্মল বিবেক আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ কারণেই যারা ঐ সকল চিন্তার সংস্পর্শে এসেছে ও ঐগুলো কর্তৃক তাদের বিবেক পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের জন্য সরলতম ও প্রাথমিক পর্যায়ের দলিল প্রযোজ্য নয়। তবে যাদের বিবেক এগুলো থেকে মুক্ত তাদের জন্য সরলতম দলিলই যথেষ্ট। অতএব,আমাদেরকে দু ’ টি পথের একটি নির্বাচন করতে হবে-হয় তাদেরকে বিবেচনা করে লিখতে হবে যাদের বিবেক এখনও উল্লিখিত জটিল চিন্তা থেকে মুক্ত এবং সরলতম যুক্তিতেই যারা তুষ্ট হয়। তখন আমাদের বর্ণিত বিষয়বস্তু অধিকাংশ সুস্পষ্ট ফতুয়ার মতোই সহজবোধ্য হবে অথবা তাদের কথা বিবেচনা করে লিখব,যাদের চিন্তা-ভাবনা জটিল বা জটিলতার সীমারেখায় যাঁরা পড়াশুনা করেছেন এবং স্রষ্টা সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান ও চিন্তার পর্যায় ভিন্ন।
অতএব,আমরা দেখতে পাই যে,আমাদের জন্য দ্বিতীয়টিই উত্তম।
তবে সাধারণত যাতে আমার লেখা বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বোধগম্যতার মধ্যে থাকে,সে চেষ্টাই করেছি। আর এ জন্যই যথাসম্ভব পরিভাষা ও গাণিতিক জটিল শব্দসমূহ পরিহার করার চেষ্টা করেছি। আর সে সাথে চেষ্টা করেছি দূরদর্শী পাঠকবর্গের জন্য বিষয়বস্তুর মানও বজায় রাখার। ফলে কিছু জটিল বিষয়েরও অবতারণা করতে হয়েছে। অতঃপর আরো বিস্তারিত জানার জন্য (যারা আগ্রহী তাদের জন্য) আমাদের অন্যান্য পুস্তকসমূহ পাঠ করার আহবান রইল। তদুপরি,সাধারণ পাঠকবর্গের অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে এ পুস্তক থেকে তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও চেতনার প্রবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হন,যা তাঁদের জন্য তুষ্টকারী দলিলও বটে।
অতএব,প্রথম ধাপ হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক ও আরোহ যুক্তি পদ্ধতি,যাতে সাধারণ পাঠকবর্গের জন্য সুস্পষ্ট ও যথার্থ দলিল উপস্থাপন করা যায় ।
যাহোক,আমরা প্রথমত প্রেরক (আল্লাহ),দ্বিতীয়ত প্রেরিত (রাসূল) এবং তৃতীয়ত রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করব।
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
প্রেরক
(আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা)
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
আল্লাহর গুণসমূহ
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে। এমনকি দার্শনিক চিন্তা অথবা যুক্তিতত্ত্বকে অনুধাবনের পূর্বেই সে একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। সে স্বীকার করে নিয়েছিল তার সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব। আর তখন থেকেই সে অনুভব করত মহান প্রভুর সাথে তার এক গভীর সম্পর্কের কথা।
প্রভুর প্রতি মানুষের এ বিশ্বাস কোন শ্রেণিবৈষম্যের ফল ছিল না,ছিল না কোন সুবিধাবাদী জালিমের চাতুর্যের ফলও-শোষণের পথকে সুগম করাই যার অভিপ্রায়। তার এ বিশ্বাস না ছিল কোন নিপীড়িত,নিগৃহীত জনপদের জীবনাবসাদের ফলশ্রুতিও যে,এ বিশ্বাস স্থাপন করে তারা কষ্টাক্লিষ্ট জীবন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কারণ মানুষের এ বিশ্বাস (স্রষ্টায় বিশ্বাস) বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এ ধরনের যে কোন বৈষম্য ও সংঘাতের চেয়েও প্রাচীন।
অনুরূপভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের এ লালিত বিশ্বাস কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বস্তুজগৎ ও প্রকৃতিজগতের বৈরিতা থেকে উৎসারিত ভয়-ভীতির ফলও ছিল না। কারণ দ্বীন যদি ভয়-ভীতির ফল হতো,তবে মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষই-তা যে কোন ধর্মীয় মতাদর্শেরই হোক-সবচেয়ে ভীতু মানুষ হিসাবে পরিগণিত হতো। কিন্তু আমরা জানি যে,যুগ যুগ ধরে যারা ধর্মের আলোকবর্তিকা ধারণ করে সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছিলেন,তারাই সর্বাপেক্ষা দৃঢ় মনোবল ও মানসিক শক্তির অধিকারী মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিল।
অতএব,মানুষের এ বিশ্বাস তার অন্তরের গভীরে প্রোথিত।
স্রষ্টার প্রতি তার ভালোবাসা,অনুরাগ এবং অবিচলিত বিবেকবোধও আত্মশক্তিরই পরিচায়ক। তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সে মহান প্রভু ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাথে তার নিজ সম্পর্ককে অনুধাবন করে।পরবর্তীকালে মানুষের মাঝে দার্শনিক মনোবৃত্তির বিকাশ হলে তার পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুসমূহ থেকে সে সামগ্রিক ধারাণাসমূহ,যেমন অনিবার্যতা,সম্ভাব্যতা ও অসম্ভবত্ব,একত্ব ও বহুত্ব,যৌগিকত্ব ও সরলত্ব,অংশ ও সমগ্র,অগ্রবর্তিতা ও উত্তরবর্তিতা এবং কারণ ও ফলাফল আবিষ্কার করেছিল। এ ধারণাগুলোকে সে তার নিজস্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছিল যা প্রভুর প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও ঈমানের সমর্থক ও সহায়ক হয়েছে। আর এভাবে সে এ ঈমানকে দর্শনের মাধ্যমে বর্ণনা এবং দার্শনিক আলোচনা ও পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছিল ।
ইতোমধ্যে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ আসল। অতঃপর মানুষ এগুলোকে জ্ঞানার্জন ও পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করল। কারণ চিন্তাবিদগণ উপলব্ধি করলেন যে,শুধু সামগ্রিক ধারণাই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সত্য,প্রকৃত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিদ্যমান রহস্যসমূহ উদ্ঘাটনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং তাঁরা ধারণা করলেন যে,পরীক্ষা-নিরীক্ষা,পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই হলো বিদ্যমান নিয়ম-শৃঙ্খলা ও রহস্য উদ্ঘাটনের প্রকৃত মাধ্যম। এ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও অবগতির পূর্ণতা এবং বিস্তৃতির পথে গুরুত্বপূর্ণ।
এ শ্রেণির চিন্তাবিদগণ এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে,ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো জ্ঞানার্জনের পথে দু ’ টি বিশেষ মাধ্যম।
মানুষের জ্ঞান এবং পরিচিতি স্বীয় পথে এগুলোর দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য। তদুপরি মানুষ এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রয়োগ করে,তার পরিপার্শ্বে বিদ্যমান সামগ্রিক বিন্যাস ব্যবস্থা,বাস্তবতা ও রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে লাভবান হতে চায়। মানুষের উচিত তার চিন্তালব্ধ ফলাফলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা। যেমন গ্রীক চিন্তাবিদ এরিস্টটল ঘরের এক কোণে বসে মুক্তাঙ্গনে বস্তুর গতি এবং গতিশক্তি সম্পর্কে চিন্তা করার পর বিশ্বাস স্থাপন করলেন যে,গতিশীল বস্তু তখনই স্থিরাবস্থায় পৌঁছে যখন গতিশক্তি লীন হয়ে যায়। অপরদিকে গ্যালিলিও,গতিশীল বস্তুকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং এ পর্যবেক্ষণকে পুনঃপুন অনুধাবন করলেন। অতঃপর গতিশক্তি এবং বস্তুর গতির মধ্যে একটি সম্পর্ক উদ্ভাবন করলেন যে, “ যখন গতিশক্তি কোন বস্তুকে গতিশীল অবস্থায় আনে,ঐ গতিশীল বস্তু স্থিরাবস্থায় আসবে না,যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপরীত কোন শক্তি গতিশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তাকে বাধাগ্রস্ত করে। ”
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি গবেষকমণ্ডলীকে এবং মহাবিশ্বের পদার্থসমূহের যাবতীয় বস্তুনিচয়ের (বিদ্যমান) নিয়মগুলো আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আর তা দু ’ টি পর্যায়ে বা ধাপে অর্জিত হয় :
১। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা,পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণ।
২। বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় অর্থাৎ প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাসকরণ যাতে করে গ্রহণযোগ্য সামগ্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
অতএব,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি কোন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অনির্ভরশীল নয়।
কোন প্রকৃতিবিজ্ঞানী বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মহাবিশ্বে বিদ্যমান রহস্যসমূহ থেকে কোন রহস্যের উদ্ঘাটন অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির সম্পর্ক অবধারণ করতে পারেননি। কারণ প্রথম ধাপে যা অর্জিত হয় তা হলো গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ। আর দ্বিতীয় ধাপে আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি,এ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিরূপণ করে এবং এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এমন কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার কথা আমাদের জানা নেই যা দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে। কারণ প্রথম ধাপের বিষয়গুলো হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় ধাপের বিষয়গুলো হলো প্রামাণ্য ও বিবেচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা (এ ধাপে) ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। যেমন নিউটন দু ’ টি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান আকর্ষণ বলকে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অনুভব করেননি যে, “ এ আকর্ষণ বল ঐ দু ‘ টি বস্তুর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং ঐ বস্তুদ্বয়ের ভরদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক। ” বরং যা তিনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জেনেছেন তা ছিল এই যে,প্রস্তরখণ্ডকে যদি উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়,তবে তা ভূমিতে ফিরে আসে;চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং গ্রহসমূহ সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনরত। নিউটন তাঁর এ পর্যবেক্ষণগুলোকে পরস্পর বিশ্লেষণ করলেন এবং গবেষণা করলেন। সে সাথে তিনি আকষর্ণকারী বস্তু অভিমুখে গতিশীল আকর্ষিত বস্তুর গতি বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্ত গ্যালিলিওর সূত্রটি এবং ভূপৃষ্ঠের উপর পতনশীল ও তীর্যক তলসমূহের উপর গড়িয়ে যাওয়া বস্তুসমূহের সুশৃঙ্খল দ্রুতি সংক্রান্ত গ্যালিলিওর তত্ত্বসমূহ এবং গ্রহসমূহের গতি সংক্রান্ত ক্যাপলারের সূত্রসমূহেরও সাহায্য নিলেন। ক্যাপলারের এক সূত্রে বলা হয়েছে যে, ‘ সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনরত প্রতিটি গ্রহের পরিক্রমণ কালের বর্গফল,সূর্য ও উক্ত গ্রহের মধ্যকার দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক ’ । অতঃপর নিউটন মহাকর্ষ সূত্র অবিষ্কার ও বর্ণনা করলেন যে,দু ’ টি বস্তুকণার মধ্যে বিদ্যমান আকর্ষণ বল উক্ত বস্তুদ্বয়ের ভরদ্বয় এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলের সমানুপাতিক।
প্রাকৃতিক বিন্যাস ব্যবস্থার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৃষ্টিকর্তার প্রতি সুস্পষ্টরূপে বিশ্বাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে একটি নতুন অবলম্বন হতে পারে। কারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা মহাবিশ্বে যে বিভিন্ন ধরনের সামঞ্জস্য,ঐকতান,নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রজ্ঞা ও কৌশলের নিদর্শনাদি আবিষ্কার করেছে তা প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। তবে প্রকৃতিবিজ্ঞানিগণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে এ বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ করার ব্যাপারে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না যা এখনও মানব জ্ঞান ও পরিচিতি এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সমস্যাবলীর প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে একটি দার্শনিক বিষয় বলে গণ্য হচ্ছে। আর খুব শীঘ্রই বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রের বাইরে এমন সব দার্শনিক ও যুক্তিবিদ্যাগত ঝোঁক ও প্রবণতার উদ্ভব হলো যা এ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে (ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি) দার্শনিক ও যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর প্রয়াস চালালো এবং ঘোষণা করল যে,পরিচিতি ও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ই হলো একমাত্র মাধ্যম। যেখানেই ইন্দ্রিয় অপারগতা প্রকাশ করে সেখানেই মানব পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ও কোনভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যার উপর অসম্ভব,তা প্রমাণ করতে মানুষও সম্পূর্ণরূপে অপারগ।
আর এভাবেই ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভুর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করেছে। ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক মতবাদের অনুসারীদের মতে খোদা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নন,তাঁকে দেখাও অসম্ভব এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বকে অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার এবং তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন পথই বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে অনস্তিত্বশীল প্রমাণ করার জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও পরিচিতিকে মাধ্যমরূপে নির্ধারণ শুরু হয়েছে দার্শনিকদের পক্ষ থেকে-সে সকল মনীষীর পক্ষ থেকে নয় যাঁরা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এক বিশেষার্থে সফলতায় পৌঁছিয়েছেন। এটা দার্শনিকদেরই কাজ ছিল যাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে দর্শন ও অপযুক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।
কিন্তু এ ধারা ও বিশ্বাস পর্যায়ক্রমে স্ববিরোধিতার জালে আটকা পড়েছে। দার্শনিক দিক থেকে এ বিশ্বাস ও ধারা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে,আমরা যে বিশ্বে বাস করি তার অস্তিত্বকেই অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতাকে আংশিক বা পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বসেছিল। এ ধারার প্রবক্তারা বলেন, “ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া আমাদের অধিকারে কোন অবলম্বন নেই এবং একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিই কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে যেভাবে আমরা তা দেখি এবং উপলব্ধি করি ঠিক সেভাবে। ” কিন্তু এ দেখা বা উপলব্ধি করা যথার্থ এবং মৌলিক নয়। কারণ কখনো কখনো কোন কিছুকে উপলব্ধি করি এবং সম্ভবত এর সত্তাকে আমাদের অনুভূতিতে গুরুত্বারোপ করি,কিন্তু লক্ষ্য করতে পারি যে,এর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার আওতায় পড়ে না। অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। ফলে ইন্দ্রিয়ানুভূতিও ঐগুলোকে প্রমাণের মাধ্যম হতে পারে না। যেমন আমরা আকাশে চাঁদ দেখি এবং আমাদের এ চাঁদ দেখার মাধ্যমে এর অস্তিত্বের প্রতি কেবল গুরুত্বারোপ করতে পারি বৈ কি।
আর ঐ মুহূর্তে একে উপলব্ধিও করতে পারি। কিন্তু সত্যিই কি চাঁদ আকাশে বিদ্যমান? চোখ খোলা এবং এর প্রতি তাকানোর পূর্বেও কি তা বিদ্যমান ছিল?
অতএব,ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম-এ মতবাদের অনুসারিগণ পরিপূর্ণরূপে কোন কিছুকে প্রমাণ ও গুরুত্বারোপ করতে পারে না।
যেমন যার চোখ টেরা সে বস্তুকে দেখে এবং তার এই দেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে,কিন্তু ঐ বস্তুর সত্যিকারের অস্তিত্বের (অবস্থানের) প্রতি গুরুত্বারোপ বা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। আর এভাবেই ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক মতবাদের অনুসারিগণ অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,ইন্দ্রিয় হলো জ্ঞান ও পরিচিতির অন্যতম মাধ্যম। আর তা জ্ঞান ও পরিচিতির মাধ্যম হওয়ার পরিবর্তে এর চূড়ান্ত সীমায় পর্যবসিত হয়েছে। এভাবেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও পরিচিতি এমন এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে,আমাদের উপলব্ধি ও মনোজগতের বাইরে যার স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই।
তাই উক্ত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি ‘ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ’ -এর প্রবক্তারা উল্লেখ করেছেন তা হলো প্রতিটি বাক্য বা উদ্ধৃতিই-যার অন্তর্নিহিত অর্থকে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না ও তার উপর গুরুত্বারোপ সম্ভব হয় না,তবে তা হলো অনর্থক বাক্য-কতগুলো এলোমেলো বর্ণমালার মতোই তা থেকেও কোন অর্থ লাভ করা সম্ভব নয়। আবার যে সকল বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এবং যার উপর গুরুত্বারোপ করা সম্ভব তা হলো অর্থবোধক বাক্য। সুতরাং যদি ইন্দ্রিয় বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকৃত অবস্থা অনুসারে অনুধাবন করে ও গুরুত্বারোপ করে,তবে ঐ বাক্য সত্য হবে;আর যদি তার অন্যথা হয় তবে তা হবে মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় : ‘ বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় ’ তবে এ বাক্যটি হলো একটি অর্থবোধক বাক্য এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও সত্য। যদি বলা হয় : ‘ শীতকালে বৃষ্টি হয় ’ তবে তা একটি অর্থবোধক বাক্য বটে,কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো মিথ্যা। আবার যদি বলা হয় : কদরের রাত্রে এমন কিছু বর্ষিত হয় যা দেখা ও অনুভব করা যায় না,তবে বাক্যটির অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য সত্য বা মিথ্যা হওয়া তো দূরের কথা,বরং এর কোন অর্থই নেই। কারণ ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সত্যতা বা অসত্যতা যাচাই করা যায় না। অনুরূপ যদি কেউ বলে : ‘ দাইয কদরের রাত্রে অবতরণ করে ’ ,তবে সত্যি কথা বলতে কি,এর যেমন কোন অর্থ নেই,তেমনি প্রাগুক্ত বাক্যটিরও অর্থ নেই। এভাবে যদি বলি, ‘ খোদা অস্তিত্বশীল ’ তবে এটি উপরিউক্ত বাক্যে যে ‘ দাইয (অনর্থক শব্দ) অস্তিত্বশীল ’ যার কোন অর্থ নেই,তার মতোই। কারণ খোদার অস্তিত্বকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় না। এ ধরনের ব্যাখ্যাও যা বাহ্যত যৌক্তিক,স্বয়ং পারস্পরিক বিরোধিতায় নিমজ্জিত। কারণ যে সর্বজনীন উক্তিতে বলা হয়েছে যে, ‘ যে সকল বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যারূপে আখ্যায়িত করা যায় না সে সকল বাক্য হলো অর্থহীন ’ তা-ও স্বয়ং এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সত্যতা বা অসত্যতা ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা যায় না। অতএব,ঐ বাক্যটিও অর্থহীন। অর্থাৎ যে যৌক্তিক বাক্যের মাধ্যমে বলা হয় ‘ প্রতিটি বাক্যই-যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায় না-তা অর্থহীন ’ ,তা-ও ঐ সর্বজনীন উক্তির আওতাভুক্ত। কারণ ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আংশিক এবং সীমাবদ্ধতা ছাড়া সংঘটিত হয় না।
অতএব,এ যুক্তি পারস্পরিক বিরোধিতা সৃষ্টি করে। ফলে এটাকে আর সর্বজনীনতা দেয়া সম্ভব না এবং একটি সর্বজনীন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিও এ থেকে প্রতিভাত হয় না। এ যুক্তির ফলে সৃষ্টি সম্পর্কে মহান মনীষিগণ যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তার সবগুলোই একাধারে ভুল পর্যবসিত হয়। কারণ ইন্দ্রিয় ‘ সর্বজনীনতা ’ কে উপলব্ধি করতে পারে না;শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই যা সীমাবদ্ধ তাকেই প্রমাণ ও উদ্ঘাটন করতে পারে।১
সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞান তার নিরন্তর ক্রমবিকাশের পথে কখনই এ ধরনের প্রবণতার প্রতি আকর্ষিত হয়নি। বিজ্ঞান সর্বদা এ বিশ্বচরাচরে প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার ও গবেষণার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অতঃপর বিজ্ঞান এ আবিষ্কার প্রক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রবণতাসমূহ যে সকল সংকীর্ণ সীমারেখা আরোপ করেছিল তা থেকে মুক্ত করেছে। এর ফলে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চ ও বিষয়াদি বিন্যস্তকরণ,সেগুলোকে সর্বজনীন নিয়ম-নীতির অবয়বে স্থাপন এবং এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।
তবে বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদসমূহের উপর এ চরমপন্থি ইন্দ্রিয়বাদী প্রবণতাসমূহের দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রভাব দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে গিয়েছে । আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন-দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা হচ্ছে যার প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী-তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে এ সকল ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক প্রবণতাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতঃ নিজেকে প্রথম ধাপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক অভিজ্ঞতার সীমা রেখা এবং এমনকি দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করার অধিকারও প্রদান করে। আর এখানে উল্লেখ্য যে,বিজ্ঞানীরা এ ইন্দ্রিয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে তার গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড শুরু এবং প্রাগুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে তার ইতি টানেন। কারণ বিজ্ঞানী প্রথম ধাপে অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে তুলনা করে একটি সর্বজনীন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ আবিষ্কার করে এবং যে সকল সম্পর্ক এই অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে কল্পনা বা ধারণা করা সম্ভব,তা প্রকাশ করে।
এদিক থেকে বস্তুবাদীদের উত্তরসূরি,দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা চরমপন্থী ইন্দ্রিয়বাদী এ ধারার মতে ‘ অদৃশ্য ও অলৌকিকতায় ’ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা দ্বান্দ্বিক চিন্তার কলেবরে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটি সাধারণ মতবাদ ব্যক্ত করে থাকেন।
বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মবাদী (الهيون ) উভয়েই এ ব্যাপারে একমত যে,ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমানা অতিক্রম করা উচিত এবং জ্ঞান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে দু ’ টি ধাপ অতিক্রম করাই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত।
প্রথমধাপ : ইন্দ্রিয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল সংগ্রহকরণ।
দ্বিতীয়ধাপ : সংগৃহীত ফলাফলগুলোর তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ।
বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা,বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে মতভেদ;অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপে। বস্তুবাদী দর্শন এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যার মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়। অপরপক্ষে,অধ্যাত্মবাদী দর্শন বিশ্বাস করে যে,ঐ সকল (১ম ধাপে) সংগৃহীত তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাবান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সন্তোষজনক হবে না।
অতএব,প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার নিমিত্তে নিম্নোল্লিখিত দু ’ প্রকারে যুক্তি উপস্থাপন করব। উভয় প্রকার যুক্তির ক্ষেত্রেই প্রথম ধাপে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ এবং দ্বিতীয় ধাপে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত উপাত্তগুলোকে ব্যবহার করব। অতঃপর এ উপসংহারে পৌঁছব যে,বিদ্যমান এ বিশ্বকে এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। দু ’ প্রকারের যুক্তি হলো :
১. বৈজ্ঞানিক বা আরোহী যুক্তি পদ্ধতি ( Inductive Reasoning ) ।
২. দার্শনিক যুক্তি পদ্ধতি ( Philosophical Reasoning )
বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দলিল বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করছি।
যে সকল যুক্তি ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাবনা তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল আরোহ যুক্তি পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কোন কিছুকে প্রমাণ করে তাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে। অতএব,স্রষ্টার সত্তাকে প্রমাণ করার জন্য আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক যুক্তি পদ্ধতি যা সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত।২
এজন্য খোদার সত্তাকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আমরা ‘ আরোহ যুক্তি ’ রূপে নামকরণ করেছি।
পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।
বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণঃ
ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে,স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি আরোহ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল যা স্বয়ং সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুক্তি প্রদর্শনের পূর্বে উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করাটা সমীচীন বলে মনে করছি । অতঃপর এ পদ্ধতির একটা মূল্যায়ন করব। এর ফলে আমরা এ পদ্ধতি কতটা গ্রহণযোগ্য এবং সত্য উদ্ঘাটন ও কোন কিছু শনাক্তকরণ বা জানার ক্ষেত্রে কতখানি নির্ভরযোগ্য তা জানতে পারব।
আরোহ যুক্তি পদ্ধতি যা সম্ভাবনা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত,তা একটি অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল ভাষ্য সম্বলিত পদ্ধতি,যার জন্য গভীর মনোযোগের প্রয়োজন। আর আরোহ যুক্তি পদ্ধতির মূলনীতিসমূহ এবং সম্ভাবনা তত্ত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমেই এ পদ্ধতির একটা সর্বাঙ্গীণ সূক্ষ্ম (গভীর) মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে আমরা এ পদ্ধতির জটিল ভাষ্যসমূহ এবং দুর্র্বোধ্য বিশ্লেষণ পরিহার করার চেষ্টা করব।
এ কারণে আমাদেরকে দু ’ টি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে হচ্ছে। যথা :
১. পদ্ধতির সংজ্ঞা উপস্থাপন (যা স্বয়ং প্রমাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে) এবং এর সরল ও সংক্ষিপ্তরূপে ব্যাখ্যা প্রদান।
২. এ পদ্ধতির মূল্যায়ন এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সীমারেখা নির্দিষ্টকরণ। তবে তা যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং যুক্তিবিদ্যা ও গাণিতিক ভিত্তিমূলসমূহের অনুসন্ধানের মাধ্যমে নয়-যার উপর এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। কারণ এর অর্থ হবে জটিল,জটিল বিষয়ে পদার্পণ করা যার জন্য গভীর মনোযোগের প্রয়োজন,বরং যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করতে চাই যা শুধু সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। আর এ জ্ঞানের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি সকলের বিশ্বাস অর্জিত হবে। তাই বলব,সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যে পদ্ধতির উপর আমরা নির্ভর করব তা অনুরূপ পদ্ধতিই যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কিছুকে প্রমাণ করতে বা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগে।
অতএব,আমরা দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কারণেই কোন সত্যকে প্রমাণ করতে বা কোন বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে যে পদ্ধতির পদচারণা করি সে পদ্ধতিই হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এখানে আমাদের মনোনীত পদ্ধতি। তবে এ পদ্ধতি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে উপমা (Analogie) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নতুবা স্বয়ং মহান প্রভুই এ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব প্রদান করেন।
উদাহরণস্বরূপ,আপনার দৈনন্দিন জীবনের কোন এক সময় ডাকের মাধ্যমে একটি চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠিটি পড়েই বুঝতে পারেন যে,তা আপনার ভাইয়ের নিকট থেকে প্রেরিত হয়েছে। যদি কোন চিকিৎসক রোগসমূহ নিবারণে সফল হন,তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে,তিনি একজন দক্ষ চিকিৎসক।
অনুরূপ,অসুস্থ অবস্থায় যদি আপনাকে কয়েকটি পেনিসিলিন ইনজেকশন দেয়া হয়,আর প্রতিবারই যদি কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়,তবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,পেনিসিলিন আপনার দেহে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।
উপরিউক্ত প্রতিটি উদাহরণের ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে আপনি সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ যুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানিগণও তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যখন সূর্যের নির্দিষ্ট কোন বিশেষত্বকে সৌরমণ্ডলে পরিলক্ষণ করেন,তবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে,উক্ত গ্রহসমূহ সূর্যেরই অংশবিশেষ ছিল যেগুলো তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
বিজ্ঞানিগণ নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কারের পূর্বে গ্রহসমূহের পরিক্রমণ পথ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে,নেপচুন নামক একটি গ্রহ সৌরমণ্ডলে বিদ্যমান।
অনুরূপ,অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বেই কতগুলো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও ঘটনার আলোকে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।
প্রকৃতি বিজ্ঞানিগণ উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ যুক্তি পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছেন। আর এটা সে পদ্ধতিই যে পদ্ধতিকে আমরা প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্যবহার করব। তখন আমরা এর অর্থ স্পষ্টরূপে অনুধাবন করব।
১ .আরোহ পদ্ধতির সংজ্ঞা এবং এর মূলনীতিসমূহ :
এখন আমরা সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ পদ্ধতিকে সুস্পষ্ট ও সরলরূপে উপস্থাপন করতে চাই । এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় উপস্থাপন করব :
ক . ইন্দ্রিয় গ্রাহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় অনেক ঘটনা বা বিষয় পরিলক্ষিত হয়।
খ . পর্যবেক্ষণ ও এ সকল ঘটনাকে সমবেত করার পর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর্যায়ে পৌঁছব। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য এমন কতগুলো কল্পনা নির্ধারণ করতে হবে যেগুলো পরীক্ষালব্ধ বিষয়গুলোর অনুরূপ এবং আমাদের ইপ্সিত ব্যাখ্যাগুলোর জন্য উপযুক্ত হবে। উপযুক্ত হওয়ার অর্থ হলো এই যে,এ কল্পনাগুলো যখন প্রমাণিত হবে,তখন ঐ পরীক্ষালব্ধ বিষয়গুলো উপপাদ্যসমূহের (প্রমাণিত কল্পনা) অন্তর্গত বা ঐগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।
গ . যদি এ সকল কল্পনা প্রকৃতপক্ষেই সঠিক ও চূড়ান্ত না হয়,তবে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলো এবং ঐগুলোর উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলো হবে দুর্বল। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে,এ কল্পনা বা প্রকল্প সঠিক নয়,তাহলে এ সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অনস্তিত্বের সম্ভাবনা অথবা এগুলোর মধ্যে অন্তত একটির অনস্তিত্বের সম্ভাবনার সাথে এগুলোর অস্তিত্বের সম্ভাবনার অনুপাত অত্যন্ত ক্ষীণ হবে। যেমন শতকরা এক ভাগ অথবা এক হাজার ভাগের এক ভাগ।
ঘ . এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে,কল্পনাটি সত্য। আর তা সত্য হওয়ার দলিল হচ্ছে ঐ সকল বিষয়ের অস্তিত্ব যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে প্রথম ধাপেই নিশ্চিত হয়েছি (অর্থাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছি)।
ঙ . পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলোর প্রমাণের মাত্রা গ-তে উল্লিখিত নীতির বিপরীত। কারণ সেখানে আমরা বলেছিলাম যে,ফলাফলগুলোর উপস্থিতির সম্ভাবনা কল্পনাগুলোর অসত্যতার ভিত্তিতে তাদের অনুপস্থিতির সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এ সম্পর্ক যত কম হবে প্রমাণের মাত্রা তত দৃঢ় হবে,এমনকি অনেক সময় কল্পনাগুলোর সঠিকতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত প্রমাণরূপে প্রতিভাত হয়।
এ বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে সম্ভবনার মূল্যমানের জন্য সঠিক মানদণ্ড বা স্কেলস্বরূপ যেগুলো স্বয়ং সম্ভাবনাভিত্তিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ অভ্যাসবশত ও ফেতরাতগত কারণেই এ মানদণ্ডগুলোকে প্রায় সঠিকভাবেই প্রয়োগ করে থাকে। এ জন্য আমরা এখানে শুধু সম্ভাবনা মানের ফেতরাতগত মূল্যায়নই যথেষ্ট মনে করব এবং যুক্তিবিদ্যা ও গণিতভিত্তিক জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা পরিহার করব।
এটা এমন এক পদ্ধতি যা প্রতিটি সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ পদ্ধতি-কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে,কি গবেষণা ও অনুসন্ধানে,কি প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণে প্রযোজ্য যুক্তি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করে থাকি।
২ .আরোহ পদ্ধতির মূল্যায়ন :
ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে,এই পদ্ধতিকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব এবং প্রথমেই দৈনন্দিন জীবন থেকে এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। পূর্বে আমরা বলেছিলাম,একটি চিঠি আপনার নিকট আসল এবং আপনি তা পড়লেন;বুঝতে পারলেন যে,চিঠিটি আপনার ভাই ব্যতীত অন্য কারো (যার সাথে চিঠিপত্র বিনিময় হয়) কাছ থেকে প্রেরিত হয়নি। এখানে আপনি সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত-এ বিষয়টি যখন আপনার কাছে স্পষ্ট হলো,তখন প্রকৃতপক্ষে তা এমন একটি প্রতিপাদ্য বিষয় যা আরোহ যুক্তি ও আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এখানে কিছু বিষয় লক্ষ্যণীয় :
প্রথম ধাপ : আপনি এখানে কিছু ঘটনার মুখোমুখী হয়েছিলেন। যেমন :
-চিঠিটিতে একটি নাম আছে যা আপনার ভাইয়ের নামের অনুরূপ।
-চিঠির লেখাগুলোর ধরন আপনার ভাইয়ের লেখার মতো।
-শব্দ,অক্ষর এবং শব্দসমূহের মধ্যবর্তী ব্যবধান,বর্ণনা-পদ্ধতি ও চিঠির ভাষা সেরকমই যেরকম আপনার ভাই লিখে থাকেন।
-বর্ণনার ভাবভঙ্গি ঠিক সেরকম যেরকমটি আপনার ভাইয়ের লিখায় ইতোপূর্বে দেখেছেন।
-লেখার পদ্ধতি ও অক্ষরগুলোর মাত্রা যেরকমটি আপনার ভাইয়ের লেখায় সাধারণত দেখা যায় সেরকম।
-চিঠিতে উল্লিখিত বিষয় সেগুলোই যেগুলো আপনার ভাই জানেন।
-সাধারণত আপনার ভাই আপনার কাছে যা আকাঙ্ক্ষা করেন,পত্র-লেখক ও তা-ই করেছেন।
-বিষয়বস্তুতে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি আপনার ভাইয়ের মতোই।
অতএব,এগুলোই হলো ঘটমান বিষয়সমূহ।
দ্বিতীয় ধাপ : নিজের কাছে আপনি প্রশ্ন করেন যে,সত্যিই কি এ চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত না আপনার ভাইয়ের মতো নামের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত। এখানেই আপনার জন্য কিছু কল্পনার (পরিভাষাগত) অবতারণা হবে যা ঐ ঘটমান বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত হয়,তবে প্রথম ধাপে যে সব তথ্য আপনি পর্যবেক্ষণ করেছেন তা পরিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।
তৃতীয় ধাপ : নিজেকে প্রশ্ন করুন : মনে করি এ চিঠিটি আমার ভাই কর্তৃক প্রেরিত না হয়ে অন্য কারো কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে,তাহলেও কি প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে বর্ণিত বিষয়গুলো ঘটতে পারে না? এর জবাব অনেকগুলো কল্পনার উপর নির্ভর করে। কারণ তখন আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে,এ নামে অন্য এক ব্যক্তি আছে,যার লেখার পদ্ধতি,হাতের লেখা,বর্ণনার ধরন,ভাষা শৈলী,অনুরূপ জ্ঞান,চাহিদা ও অন্যান্য বিষয়ে আমার ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্য আছে। এ সমস্ত বিষয়ের আলোকে আমরা দেখতে পাব যে,ঐ ধরনের বিষয়গুলোর উপস্থিতির সম্ভাবনা (অন্য কারো ক্ষেত্রে) কম। আর এ বিষয়গুলোর (যেগুলোর উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল) পরিমাণ যত বেশি হবে,এ ধরনের সম্ভাবনাও তত বেশি হ্রাস পাবে।
অনুসন্ধানের জন্য মৌলিক যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে শিখায় যে,কিভাবে সম্ভাবনাকে অনুমান করব;কিভাবে এ সম্ভাবনা দুর্বল ও ভিত্তিহীন হয়ে যায় এবং কেনইবা উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিস্তৃতির সাথে সাথে তাদের সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দুর্বলতর হতে থাকে? তবে এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি না। কারণ সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর জন্য এটা অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সৌভাগ্যবশত এ ‘ সম্ভাবনার দুর্বলতা ’ বিষয়টির ব্যাখ্যা অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমনি করে উপর থেকে মানুষের নীচে পড়ে যাওয়া অভিকর্ষ বল ও অভিকর্ষ সূত্রের উপর,মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না।
অতএব,আপনার ভাইয়ের সদৃশ এক ব্যক্তির (যিনি সমস্ত উল্লিখিত বিষয়ে আপনার ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্যমান) অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব-এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। যেমন কোন ব্যাংক এ সম্ভাবনার পরিমাণ অনুসন্ধানের জন্য (যে ব্যাংকের সকল গ্রাহক উক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা থেকে খরচ নির্বাহ করে) যুক্তিবিদ্যার মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। কারণ এমনটি ঘটার সম্ভাবনা সত্যিই দুর্বল। তবে এক বা একাধিক ব্যক্তির এমনটি করার সম্ভাবনা আছে।
চতুর্থ ধাপ : যখন চিঠিটির এ সকল বিষয় (শুধু কিছুটা দুর্বল সম্ভাবনা ব্যতীত যে,চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত নয়-অন্য করো থেকে এসেছে) আপনি পর্যবেক্ষণ করবেন,তখন বাহ্যিক বিষয়বস্তুর সঠিকতার আলোকে বুঝতে পারবেন যে,চিঠিটি প্রকৃতই আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে।
পঞ্চম ধাপ : চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত-এ চতুর্থ ধাপটিকে প্রাধান্য দেয়া এবং তৃতীয় ধাপের অপর সম্ভাবনাটি দুর্বল হওয়া প্রসঙ্গে এক পক্ষের প্রাধান্য দানের মাত্রা যত বেশি হবে,অন্য পক্ষের মাত্রা তত বেশি দুর্বলতর হবে। অতএব,আমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে,চিঠিটি অবশ্যই আপনার ভাইয়ের। অর্থাৎ এ দু ’ ধাপের মধ্যে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে,প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়টি ও দুর্বল সম্ভাবনাময় বিষয়টির মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান।
অতএব,সম্ভাবনার মাত্রা যতটা কম হবে প্রাধান্যের মাত্রা ততটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং চিঠিটি আপনার ভাইয়ের-এর সঠিকতার বিরোধী কোন নিদর্শন যখন পাওয়া যাবে না তখন এ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যে,চিঠিটি আপনার ভাই কর্তৃক প্রেরিত-পঞ্চম ধাপে প্রামাণ্য বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটবে।
উপরিউক্ত উদাহরণটি ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে নেয়া। এখন অপর একটি উদাহরণ কোন মতবাদকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের যুক্তি প্রদর্শনের পদ্ধতি থেকে বর্ণনা করব। যেমন গ্রহসমূহের উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন,কোটি কোটি বছর পূর্বে এ ন ’ টি গ্রহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডরূপে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সকল বিজ্ঞানীই এ মতবাদের উপর একমত রয়েছেন। তবে কিরূপে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে-এ ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে থাকেন। যাহোক,মূল মতবাদ যার উপর সকলেই একমত তা নিম্নোক্ত ধাপসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় :
প্রথম ধাপ :বিজ্ঞানিগণ এ ধাপে কিছু বিষয়কে ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে নিম ্ন ক্রম অনুসারে লক্ষ্য করেছেন :
১. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন আপন অক্ষে সূর্যের ঘূর্ণনের সাথে মিল রয়েছে এবং উভয়ই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তিত হয়।
২. আপন অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন সূর্যের ঘূর্ণনের মতোই। অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে।
৩. সূর্যের বিষুব রেখার সাথে সমান্তরাল অক্ষরেখার উপর পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয় যেন সূর্য হলো যাঁতাকলের অক্ষ আর পৃথিবী হলো ঐ যাঁতাকলের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু।
৪. যে সকল উপাদান থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সে সকল উপাদান সূর্যেও মোটামুটি বিদ্যমান।
৫. সূর্য ও পৃথিবীতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরিমাণগত অনুপাত সমান ও একই। যেমন পৃথিবী ও সূর্য উভয়েরই দাহ্য মৌলিক উপদান হচ্ছে হাইড্রোজেন।
৬. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতিবেগ ও আপন অক্ষের উপর এর গতিবেগ এবং আপন অক্ষের উপর সূর্যের গতিবেগের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।
৭. ব্যবহারিক হিসাব নিরূপণ ও গণনার ভিত্তিতে পৃথিবী এবং সূর্যের আয়ুষ্কালের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান।
৮. পৃথিবীর কেন্দ্র উত্তপ্ত ও অগ্নিসদৃশ,যা প্রমাণ করে যে,সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে অগ্নিসদৃশ ছিল।
উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো হলো বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত কয়েকটি বিষয়,যেগুলো তাঁরা প্রথম ধাপে হস্তগত করেছেন।
দ্বিতীয় ধাপ : এখানে মনীষিগণ একটি কল্পনাকে ৩ নির্বাচন করেছেন যার মাধ্যমে এ সমস্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ যদি কল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে সত্য হয়, তবে তা উল্লিখিত বিষয়গুলোকে সত্যায়িত ও ব্যাখ্যায়িত করবে। কল্পনাটি নিম্নরূপ :
‘ পৃথিবী সূর্যেরই অংশ,যা কোন কারণে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ ।
অতএব,উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে (যা প্রথম ধাপে উল্লিখিত হয়েছে) আমাদের পক্ষে উল্লিখিত কল্পনাটির ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়েছে।
১. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের দিক আপন অক্ষে সূর্যের ঘূর্ণনের দিক সদৃশ। অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এ সাদৃশ্যের কারণ কল্পনাটির সাথে নিম্নরূপে প্রমাণিত হয়। যদি কোন গতিশীল বস্তু থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে,তবে নিত্যতার সূত্র অনুসারে তা মূল বস্তুর গতির দিকের অনুরূপ দিকে গতি বজায় রাখে (যেমন রশির মাধ্যমে কোন বস্তুকে আবর্তিত করলে তা থেকে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হলে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ গতির অনুরূপ দিকই বজায় রাখে)।
২. আপন অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন আপন অক্ষে সূর্যের ঘূর্ণনের সদৃশ এবং উভয়েই পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে। উল্লিখিত কল্পনাটি এটাও ব্যাখ্যা করে। কারণ যদি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূর্ণায়মান কোন বস্তু থেকে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়,তবে নিত্যতার সূত্র অনুসারে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশও একই দিকে গতি বজায় রাখবে।
৩. এ ক্ষেত্রেও ২-এর অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।
৪ ও ৫. পৃথিবীতে বিদ্যমান উপাদানসমূহ এবং সূর্যে বিদ্যমান উপাদনসমূহের মধ্যে পরিমাণ ও অবস্থাগত দিক থেকে সাদৃশ্য ও আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। উল্লিখিত কল্পনাটির মাধ্যমে এদেরও ব্যাখ্যা করা যায়। (বলা যায়,যেহেতু পৃথিবী সূর্যের একটি অংশ,সেহেতু যে সকল উপাদান অংশে বিদ্যমান,অবশ্যই সেগুলো সমগ্রেও বিদ্যমান থাকবে।)
৬. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতিবেগ আপন অক্ষের উপর এর গতিবেগ এবং আপন অক্ষের উপর সূর্যের গতিবেগের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। ‘ পৃথিবী সূর্য থেকে পৃথক হয়েছে ’ -এ কল্পনার মাধ্যমে এটা ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি সূর্যের গতি থেকেই উৎসারিত।
৭. সূর্য এবং পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সামঞ্জস্যকেও ‘ পৃথিবী সূর্য্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।
৮. এ পর্যায়েও পূর্বের মতোই আমরা বলতে পারি যে,সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ‘ পৃথিবী সূর্য থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাকেই সত্যায়িত করে।
তৃতীয় ধাপ : ‘ পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাটি যদি সঠিক না হয়,তবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেমনি অসম্ভব তেমনি এর অধীনে বিষয়গুলোকে একত্র করাও অসম্ভব। কারণ যে কল্পনাটির অসত্যতা ধারণা করা হয়েছে তার অধীনে কতগুলো অপরাপর বিচ্ছিন্ন বিষয়কে আকস্মিকভাবে একত্র করতে পারার সম্ভাবনা প্রকৃতই দুর্বল। কারণ কল্পনাটির অসত্যতার সম্ভাবনার ফলে আমাদের অপর এক শ্রেণির কল্পনার দ্বারস্থ হতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব। যেমন :
সূর্যের নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের সাথে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ এবং উক্ত ঘূর্ণন ও প্রদক্ষিণ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হওয়ার যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে ঐ শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমদেরকে ধরে নিতে হবে যে,পৃথিবী সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত একটি অংশ,যা হয় নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়েছে অথবা অন্য কোন নক্ষত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ সৌর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একই সাথে ধরে নিতে হবে যে,পৃথিবী যখন অপন কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল তখন সূর্যের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত কোন বিন্দুতে প্রবেশ করেছিল। ফলে,পশ্চিম থেকে পূর্বে পরিক্রমণ করছে। কারণ যদি সূর্যের পূর্বে অবস্থিত কোন বিন্দুতে প্রবেশ করত,তাহলে অবশ্যই পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তিত হতো।
আপন অক্ষের উপর এবং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে যে অভিন্নতা বিদ্যমান,সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে,অন্য কোন নক্ষত্র বিদ্যমান যা থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং যা পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘূর্ণনরত।
সূর্যের বিষুব রেখার সাথে সমান্তরাল অক্ষরেখার উপর পৃথিবী পরিক্রমণ করছে,এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে,সূর্যের বিষুব রেখার উল্লম্ব৪ অবস্থানে অন্য কোন নক্ষত্র বিদ্যমান যা থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
সূর্য এবং পৃথিবীর উপাদানসমূহের অভিন্নতার ক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে,একই উপাদানসম্বলিত সূর্য ভিন্ন অন্য কোন নক্ষত্র বিদ্যমান যা থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং যা উপাদানসমূহের অনুপাতের ক্ষেত্রেও সূর্যের অনুরূপ।
সূর্যের পরিপার্শ্বে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের দ্রুতি,আপন অক্ষে তার দ্রুতি এবং আপন অক্ষে সূর্যের দ্রুতির মধ্যকার বিদ্যমান শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে,অন্য কোন নক্ষত্র বিদ্যমান যা পৃথিবীকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে যে,সূর্যের গতিবেগের অনুপাতে এর গতিবেগ বজায় থাকে।
সূর্য এবং পৃথিবীর আয়ুষ্কাল এবং সৃষ্টির আদিতে এর তাপমাত্রার ক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে,পৃথিবী এমন এক নক্ষত্র (সূর্য ভিন্ন) থেকে বিছিন্ন হয়েছে যা সূর্যের আয়ুষ্কালের সম আয়ুষ্কালবিশিষ্ট এবং তার তাপমাত্রাও এ সূর্যের তাপমাত্রার মতোই।
অতএব,আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ‘ পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাটি যদি সত্য না হয়,তবে প্রাগুক্ত সমুদয় সম্ভাবনা ও কল্পনাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এবং এ সকল শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যতা যে আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে,তা-ও বিশ্বাস করতে হবে। আর উপরিউক্ত কল্পনার বিপরীতে এ সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার আকস্মিকভাবে উদ্ভব ও সমবেত হওয়ার সম্ভাবনাও সত্যিই ক্ষীণ। অপরপক্ষে,গৃহীত কল্পনাটিই (সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে) সমস্ত পরীক্ষালব্ধ বিষয়কে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।
চতুর্থ ধাপ : যেহেতু ‘ সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাটি অসত্য মনে করলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বিষয়গুলোর উপস্থিতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে সেহেতু এটা মনে করাই শ্রেয় যে,উল্লিখিত কল্পনাটি সত্য,যা সমগ্র পরিলক্ষিত বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে। অতএব, ‘ পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ’ -এ কল্পনাটিই অপর পক্ষের উপর প্রাধান্য পাবে।
পঞ্চম ধাপ : চতুর্থ ধাপে বর্ণিত প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয় (অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছে) এবং তৃতীয় ধাপে বর্ণিত ক্ষীণ সম্ভাবনাময় বিষয়ের (সমস্ত পরিলক্ষিত বিষয় সূর্য ভিন্ন অন্য কোন নক্ষত্র থেকে প্রাপ্ত )মধ্যে তুলনা করব। এখানে আমরা দেখতে পাব যে,চতুর্থ ধাপের উপসংহার তৃতীয় ধাপের উপসংহারের উপর প্রকৃতই প্রাধান্য পাওয়ার দাবি রাখে।
আর এর ভিত্তিতেই আমরা ‘ সূর্য থেকে পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ’ সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করব এবং বিজ্ঞানীরা এ পদ্ধতির মাধ্যমেই উক্ত কল্পনাকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করতে পেরেছেন।
আরোহ পদ্ধতিকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে কিরূপে প্রয়োগ করব?
আমরা ইতোপূর্বে সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ যুক্তি পদ্ধতির সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং এ পদ্ধতিকে পূর্বের সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন করেছি। এখন আমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করব।
প্রথম ধাপ : এখানে আমরা লক্ষ্য করব যে,কতগুলো শৃঙ্খলিত বিষয় এবং জীবন্ত এক অস্তিত্ব হিসাবে মানুষের নির্ভরশীলতা বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে,অন্য কোন বিষয় এর বিকল্প হতে পারে না। কারণ তাহলে মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে ও মানুষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিম্নে এ ধরনের কিছু বিষয়ের উল্লেখ করব :
পৃথিবী সূর্য থেকে কিছু তাপ গ্রহণ করে যা জীবন নির্বাহের জন্য এবং প্রাণবন্ত অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। এ তাপের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জীবনের যাত্রাপথ বিঘ্নিত হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যদি এ দূরত্ব অধিক হয় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পৃথিবীতে পৌঁছবে না। আবার যদি এ দূরত্ব হ্রাস পায়,তবে তাপ বৃদ্ধি পাবে। ফলে পৃথিবীতে জীবন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে।
লক্ষ্য করব যে,ভূপৃষ্ঠকে ভূমি এবং পানি ৪ঃ ৫ অনুপাতে দখল করে আছে (বিভিন্ন যৌগরূপে) যা অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।
এছাড়া নিয়ত অক্সিজেনের রাসায়নিক রূপান্তর সত্ত্বেও মুক্ত বাতাসে এর মোট পরিমাণ অপরির্তিত থেকে যায় যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং জীবন ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল জীবই অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। যদি বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন নিঃশেষ হতে থাকে (র্অথাৎ যদি মূল পরিমাণ কমতে থাকে) তবে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরো লক্ষ্য করব যে,মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনের অনুপাতে বিদ্যমান। বাতাস ২১% অক্সিজেন এবং ৭৯% অন্যান্য গ্যাস নিয়ে গঠিত। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ তা অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়,তবে পরিবেশ ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে সার্বক্ষণিক অগ্নিকাণ্ড দেখা দেবে। আবার যদি এর চেয়ে কম হয়,তবে ভূপৃষ্ঠে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে পড়বে। ফলে মানুষ জ্বালানী কাজে অক্সিজেন এবং আগুন ব্যবহার করতে পারবে না,যা তার জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
প্রকৃতিতে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং লক্ষ-কোটি বছর ধরে এ পুনরাবৃত্তি হয়েছে,এমন একটি বিষয় হলো প্রয়োজন অনুপাতে অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখার প্রক্রিয়া। মানুষ (সাধারণ অর্থে প্রাণী) শ্বাস নেয়ার সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বাতাসে বিদ্যমান অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বসন গ্রক্রিয়া চালায়। রক্তের মাধ্যমে এ অক্সিজেন শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে প্রবেশ করে এবং খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় এবং প্রশ্বাসের মাধ্যমে বা কথা বলার ফলে মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে মানুষ এবং পশু সর্বদা এ গ্যাস(CO ২ ) উৎপন্ন করে,যা উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে।
এ অক্সিজেন পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যবহৃত হয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে এ আদান-প্রদানের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ ও সম্ভব হয়।
এ বিনিময় হাজারো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলস্বরূপ যা একে অপরের হাতে হাত দিয়ে সম্পাদন করেছে এবং জীবনের চাহিদাসমূহের যোগান দিয়েছে। যদি এ বিনিময় এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকত,তবে জীবন ধারণের উপাদানগুলো (যেমন অক্সিজেন) অল্প অল্প করে কমতে থাকত এবং মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত।
লক্ষ্য করব যে,নাইট্রোজেন একটি ভারী গ্যাস এবং প্রায় জমাটবদ্ধতার কাছাকাছি। নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বাতাসে অবস্থান করে,যার ফলে হালকা হয় এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহারের উপযোগী হয়। লক্ষ্যণীয় যে,যে পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে সর্বদা অবস্থান করে তা নাইট্রোজেনের পরিমাণের সাথে আনুপাতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। অর্থাৎ নাইট্রোজেনকে হালকা করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সর্বদা বিদ্যমান। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বা নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়,তবে প্রয়োজন অনুসারে হালকা করণের এ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।
লক্ষ্য করব যে,বাতাস এক নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করে। কখনো এ পরিমাণ পৃথিবীর উপাদান ও কণিকাসমূহের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেও বৃদ্ধি পায় না। এ পরিমাণ মানুষের জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যদি বিদ্যমান বাতাসের পরিমাণ কম বা বেশি হয়,তবে মানুষের জীবন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদি বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়,তবে মানুষের দেহের উপর চাপও বৃদ্ধি পাবে যাতে করে সে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি হারাবে। আবার যদি বাতাসের পরিমাণ কম হয়,তবে বাতাস আকাশে বিদ্যমান উল্কাসমূহকে বাধা দিতে পারবে না,ফলে ভূপৃষ্ঠে সহজেই উল্কাপাত ও অগ্নিকাণ্ড দেখা দেবে।
লক্ষ্য করব যে,ভূপৃষ্ঠ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন আকর্ষণ করে যেন সমস্ত গ্যাস এতে শোষিত না হয়। যদি ভূপৃষ্ঠ সমস্ত গ্যাস শোষণ করে নিত,তবে জীবনের জন্য কোন গ্যাস অবশিষ্ট থাকত না। ফলে মানুষ,পশু ও বৃক্ষসমূহ জীবন ধারণ করতে পারত না।
লক্ষ্য করব যে,পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব নির্দিষ্ট,যা মানুষ এবং অন্যান্য জীবের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ যদি চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটবর্তী হতো,তবে সাগরসমূহের জোয়ার এমনভাবে বৃদ্ধি পেত যেন পাহাড়সমূহকে উপড়ে ফেলবে।
আমরা প্রাণীর মধ্যে অনেক ধরনের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি। যদিও এ সব প্রবৃত্তির অলৌকিক ভাবার্থ আছে যা বাহ্যত দেখা যায় না। তবে এ সব প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটে তা আমাদের কাছে গোপনীয় নয়,বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সকল প্রবৃত্তিই দর্শনোপযোগী। আর মানুষ তার স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা হাজার হাজার প্রবৃত্তিকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে যা তার জীবন যাপন প্রক্রিয়াকে সহজ এবং তাকে রক্ষা করে। আমরা এ সব প্রবৃত্তির অনেকগুলোকেই সঠিকভাবে চিনি না এবং শনাক্তও করতে পারি না। যখন আমরা এ সব প্রবৃত্তিকে প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভক্ত করব তখন আমরা বুঝতে পারব যে,প্রতিটি শ্রেণিই বিশেষ এক শৃঙ্খলার সাথে মানব জীবনকে সাহায্য ও সুরক্ষা বিধান করছে। মানুষের মধ্যে শারীরিক গঠনসমূহ কোটি কোটি অগণিত প্রাকৃতিক ঘটনার উদ্ভব ঘটায় যেগুলোর প্রতিটিই মানুষকে তার জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখন উদাহরণস্বরূপ যে সকল বাহ্যিক কারণ ও বিষয় প্রাণীর দেখার সাথে সরাসরি জড়িত এবং কোন কিছুর দর্শনানুভূতিতে মানুষকে সহায়তা করে সেগুলোকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করব। চক্ষুলেন্স বস্তুর চিত্র অক্ষিপটে প্রতিফলিত করে। এ অক্ষিপট স্বয়ং ন ’ টি স্তরে গঠিত। সবর্শেষ স্তরটি কোটি কোটি স্তম্ভাকৃতি ও কোণাকৃতির কোষের সমন্বয়ে গঠিত যা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। অপরদিকে এ অংশটি চক্ষুলেন্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ‘ কোন বস্তুর দর্শন ’ এ পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বস্তু প্রকৃতপক্ষেই বহির্জগতে বিদ্যমান যার উপর দৃষ্টি প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়ে থাকে এবং অপরটি হলো বস্তুর প্রতিচ্ছবি যা উল্টাকারে অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দর্শন এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়,বরং কেটি কেটি স্নায়ুকোষ অক্ষিপটে প্রতিফলিত উল্টা প্রতিবিম্বকে সোজা (প্রকৃত) করার কাজ সম্পাদন করে এবং একে মানুষের মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। আর এ পর্যায়েই দর্শন সংগঠিত হয় যা মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে জড়িত।
এমনকি সৌন্দর্য,কমনীয়তা ও সুগন্ধির মতো প্রাকৃতিক বিষয়-বস্তুসমূহের প্রতিটিই স্ব স্ব স্থানে মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সাথে জড়িত।
যদি ফুলের পরাগায়ণে কীটপতঙ্গের ভূমিকাকে পর্যবক্ষেণ করি,তবে দেখতে পাব যে,ফুলের সৌন্দর্য,কমনীয়তা ও সুগন্ধ এর একটি বিশেষ কারণ। ফুলের এ উপাদানসমূহই নিজের প্রতি কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে এবং পরাগায়ণের কাজটি সহজীকরণ করে। ফুলের প্রস্ফুটনে পরাগায়ণের জন্য বাতাস যে কার্য সম্পাদন করে এবং কীটপতঙ্গ যে কার্য সম্পাদন করে এ দু ’ টি আলাদাভাবে চিহ্নিত হয় না।
প্রজননের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে নারী ও পুরুষের গঠনে (হোক প্রাণী অথবা উদ্ভিদ) এবং পারস্পরিক জীবন ধারণ ও অস্তিত্বের অব্যাহত গতির জন্য প্রকৃতি ও প্রাণীর পারস্পরিক বিনিময়ের সাথে পূর্ণরূপে সমন্বিত।
পবিত্র কোরানে এ ব্যপারে বলা হয়েছে :
و اِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُحصُوها اِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيم
“ এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ” (নাহল,১৮)
যাহোক,উপরিউক্ত পর্যায়গুলো ছিল প্রথম ধাপের অন্তর্ভুক্ত।
দ্বিতীয় ধাপ : এ ধাপে আমরা দেখতে পাব যে,প্রকৃতি এবং জীবনের মধ্যে এই যে শতধা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক তা একটি কল্পনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কল্পনাটি হলো :
‘ এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান,যিনি এ পৃথিবী ও বস্তুসমূহকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং তাঁর এ সৃষ্টির পেছনে একটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান। ’
অতএব,উল্লিখিত সকল সম্পর্ক এবং বিষয়কে উপরিউক্ত কল্পনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়।
তৃতীয় ধাপ : যদি প্রকৃতই প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা না থাকে বলে মনে করা হয়,তবে সৃষ্টি ও প্রাণীর জীবনের অগ্রযাত্রা ও সুখ-সমৃদ্ধির পথে এই যে পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক,কোন উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্ভাবনা কতটুকু হতে পারে? এটা পরিষ্কার যে,এর সম্ভাবনা অর্থাৎ এ সকল ঘটনা কোন এক মহাসংঘর্ষের ফল,এমনটি ঘটার সম্ভাবনা খুবই দুর্বল। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে,ভাই ভিন্ন অন্য কারো কর্তৃক চিঠিটি প্রেরিত হলে সকল বিষয় ভাইয়ের সদৃশ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই দুর্বল। কারণ শত শত বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। অতএব,কিরূপে এ ধারণা করা যায় যে,আমাদের আবাসস্থল এ পৃথিবীর সকল বিষয় শুধু বস্তু ও বস্তুগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কোন উদ্দেশ্য ব্যতীতই সংগঠিত হয়েছে? অপরদিকে এ ঘটনাগুলো এমন এক সৃষ্টিকর্তাকে প্রকাশ করে,যিনি প্রজ্ঞাবান এবং যিনি কোন উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করেন।
চতুর্থ ধাপ : অতএব,নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ধাপে বর্ণিত কল্পনাটি প্রাধান্য পায় যে,প্রজ্ঞাবান,চিন্তাশীল ও জ্ঞানী এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান।
পঞ্চম ধাপ : প্রাধান্য প্রাপ্ত বিষয়টি এবং দুর্বল সম্ভাবনাময় বিষয়টির মধ্যে তুলনা করব। যত বেশি সংখ্যক সাংঘর্ষিক ঘটনা বা আকস্মিক বিষয়ের ধারণা করা হবে,তৃতীয় ধাপে বর্ণিত ধারণার সঠিকতার সম্ভাবনা তত বেশি দুর্বলতর হতে থাকবে। কারণ এ কল্পনাটি (সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই) তাত্ত্বিক নিয়মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সাংঘর্ষিক ও আকস্মিক বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে অপারগ।
অতএব,এ ধরনের সম্ভাবনাময় ‘ কল্পনা ’ একান্তভাবেই নির্ভরশীল হতে পারে না।৫ এভাবে আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছব যে,বিদ্যমান এ জগতের জন্য প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকাটা আবশ্যকীয়।
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :
سَنُريهِم اَيَاتِنا في الافَاق وَ في اَنفُسِهِم حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُم اَنَّهُ الحَقّ اَوَلَم يَكفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ
“ নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব, এমনকি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা নিশ্চিত সত্য। ইহাই কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক? ” (সূরা ফুসসিলাত : ৫৩)
اِنَّ في خَلقِ السَّمَاواتِ و الاَرضِ و اختِلافِ اللّيلِ و النَّهارِ و الفُلكِ الّتي تَجري في البَحرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ و ما اَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ من مَاءٍ فَاَحيَا به الاَرضَ بَعدَ مَوتِهَا و بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ و تَصرِيفِ الرِّياحِ و السَّحَابِ المسخرِ بينَ السَّماءِ و الارضِ لاياتٍ لِقَومٍ يَعقِلونَ
“ নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ যাহা সমূদ্রে এমন দ্রব্যাদি লইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা যাহা আল্লাহ্ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন, যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ও উহাতে যাবতীয় জীব- জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিরাজমান বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে, যাহারা বিচার- বুদ্ধি খাটায়। ” (সূরা বাকারা : ১৬৪)
فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَرَى مِن فُطُورِ ثُمَّ ارجِعِ البصَرَ()كرَّتَين يَنقَلِب اِلَيكَ البَصَر خَاسئا و هو حَسِير
“ অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবন্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি- বিচ্যুতি দেখিতে পাও? অতঃপর তুমি পুনঃপুন দৃষ্টি নিবন্ধ কর,( পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। ” (সূরা মুলক : ৩ ও ৪)
দার্শনিক যুক্তি
খোদার অস্তিত্ব প্রমাণে দার্শনিক যুক্তি (الدليل الفلسفي ) সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে দার্শিনিক যুক্তি কী এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাথে দার্শনিক যুক্তির পার্থক্য কী? যুক্তি কত প্রকার ও কী কী?
যুক্তি তিন ভাগে বিভক্ত : গাণিতিক যুক্তি,বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং দার্শনিক যুক্তি।
গাণিতিক যুক্তি হলো যা বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র ও গঠন যুক্তিবিদ্যায় (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয়شكل ) ব্যবহৃত হয়। বৈপরীত্যহীনতা (عدم تناقض ) অর্থাৎ ‘ বৈপরীত্যের জোট অসম্ভব ’ -এ বিষয়টিই হচ্ছে সর্বদা এ যুক্তির ভিত্তিমূল। যেমন আমরা বলতে পারি ‘ ক ’ হলো ‘ ক ’ -এর সমান এবং এ কথার ভিত্তিতে আমাদের পক্ষে এটা বলা অসম্ভব যে, ‘ ক ’ , ‘ ক ’ -এর সমান নয়। অতএব,যে সকল যুক্তি প্রত্যক্ষভাবে বৈপরীত্যহীনতার সাথে জড়িত তাকেই গাণিতিক যুক্তি বলা হয়। আর এ ধরনের যুক্তি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট।
বৈজ্ঞানিক যুক্তি হলো যে সকল যুক্তি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। এ যুক্তি যে সকল জ্ঞাত বিষয়কে ইন্দ্রিয় ও গাণিতিক যুক্তিভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব তার উপর নির্ভরশীল।
দার্শনিক যুক্তি হলো যা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাত৬ বিষয়ের সাহায্যে এবং গাণিতিক যুক্তির মূলনীতির আলোকে বাস্তবজগতের কোন বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ এ নয় যে,দার্শনিক যুক্তি একান্তভাবেই ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞাত বিষয়কে অনুমোদন করে না;বরং এর অর্থ এই যে,উক্ত বিষয়ের অনুমোদনের পাশাপাশি কোন মনোনীত বিষয়ের প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাত বিষয়ের গণ্ডিতেও কাজ করে।
অতএব,দার্শনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো বৈজ্ঞানিক যুক্তির ক্ষেত্রে ‘ গাণিতিক যুক্তির মূলনীতি ’ অন্তর্ভুক্ত নয়।
দার্শনিক যুক্তির অর্থ বুঝাতে যা বলেছি তার ভিত্তিতে প্রশ্ন হতে পারে যে,অনুভূতি,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের সাহায্য ছাড়া কি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাত বিষয়ের (অর্থাৎ যে সকল চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রবেশ করে) উপর নির্ভর করা সম্ভব?
এর উত্তর হ্যাঁ-বোধক। কারণ কিছু জ্ঞাত বিষয় আছে যেগুলো সর্বজনস্বীকৃত,(যেমন বৈপরীত্যহীনতার মূলনীতি-যার উপর বিশুদ্ধ গণিত নির্ভরশীল) বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতেই আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য বলে পরিগণিত হয়েছে-ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নয়।
আর আমাদের এ দাবির পশ্চাতে যুক্তি হলো উক্ত মূলনীতির উপর আমাদের বিশ্বাসের মাত্রা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এর অর্থ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করার জন্য সমতার হিসাব থেকে একটি সহজ উদাহরণ আনব। যেমন : ২+২=৪ এ সরল বিনিময়ের সঠিকতার উপর আমাদের বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংখ্যাধিক্যের সমমানে প্রতিষ্ঠিত নয় ;কারণ এর অন্যথা আমরা গ্রহণ করতে পারি না অর্থাৎ বলতে পারি না যে,২ এবং ২ এর যোগফল কোন বিজোড় সংখ্যা,যেমন ৩ অথবা ৫ হবে। অতএব,এ ধরনের ফলাফলের অসত্যতার উপর আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয়। যদি তাই হতো,তবে ইতিবাচকতা বা নেতিবাচকতা এ ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলত। অর্থাৎ ২+২ = ৪ বা ২ = ৪-২ বা ৪-২ = ২ সকল ক্ষেত্রেই ফলাফল অপরিবর্তিত। এখন যেহেতু ঐন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও উল্লিখিত সত্যটির উপর আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি সেহেতু স্বভাবতঃই বিশ্বাস করব যে,বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাতব্যের (যার সপক্ষে দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপিত হয়) উপর নির্ভর করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়,দার্শনিক যুক্তিকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা যে, ‘ যেহেতু দার্শনিক যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাতব্যের উপর নির্ভর করে,যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্ক রাখে না ’ প্রকৃত পক্ষে তা গাণিতিক যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। কারণ গাণিতিক যুক্তিও বৈপরীত্যহীনতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয় নি।
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তির একটি নমুনা :
দার্শনিক যুক্তি তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত :
ক. স্বতঃসিদ্ধ বিষয় : প্রতিটি সৃষ্ট বিষয়েরই একটি অস্তিত্ব প্রদানকারী কারণ রয়েছে। এ বিষয়টিকে মানুষ তাৎক্ষণিক ও ফেতরাতগত কারণেই অনুধাবন করে থাকে এবং পুনঃপৌনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এর অনুমোদন দেয় এবং একে সমর্থন করে।
খ . ঐ সকল বিষয় যাতে বলা হয় প্রতিটি অস্তিত্ববান সত্তারই একটি ক্ষীণ পর্যায় ও একটি তীব্র পর্যায় রয়েছে। তবে এটা মনে করা যাবে না যে,ক্ষীণ পর্যায় এর তীব্র ও পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ের কারণ। যেমন তাপের তীব্র ও ক্ষীণ পর্যায় বিদ্যমান।
অনুরূপ,পরিচিতি এবং আলোকেরও তীব্র ও ক্ষীণ পর্যায় রয়েছে। অর্থাৎ কোন কোনটির চেয়ে কোন কোনটি তীব্রতর ও পূর্ণতর। অতএব,কল্পনা করা যাবে না যে,তীব্র তাপ ক্ষীণ তাপ থেকে জন্ম নেয়। যে ব্যক্তি ইংরেজি জানে না বা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচিত নয়,সে ব্যক্তির নিকট থেকে কেউ ইংরেজি ভাষার উপর পূর্ণ দখল অর্জন করতে পারে না। অনুরূপ ক্ষীণ আলোক থেকে তীব্র আলোকের আশা করা যায় না। কারণ প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ও তীব্র পর্যায়েরই অস্তিত্ব ও গুণগত দিক থেকে ক্ষীণ পর্যায়ের উপর “ এক প্রকরণগত আধিক্য ও প্রাচুর্য ” রয়েছে এবং এ প্রকরণগত প্রাচুর্য ক্ষীণ পর্যায় থেকে অর্জিত হতে পারে না যা স্বয়ং প্রাচুর্যহীন। সংক্ষেপে বলা যায়,আপনি এমন কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে পারেন না যাতে আপনার মোট সম্পত্তি বা অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
গ . বস্তু এর অব্যাহত ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার বিবর্তনের মাত্রানুসারে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন এক বিন্দু পানি বস্তু-রূপসমূহের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে;জীবনের একক প্রোটোপ্লাজম যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় তা বস্তু-রূপের অপেক্ষাকৃত উন্নত অস্তিত্বের অধিকারী হয়েছে;এককোষী প্রাণী এ্যামিবা বস্তু-রূপসমূহের মধ্যে একটিকে পরিগ্রহ করে যা বহু পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অবশেষে প্রাণবন্ত এবং অনুভূতি ও সচেতন অস্তিত্ব মানুষও হলো বস্তু-রূপের এক উন্নত পর্যায়।
নিম্নোক্ত প্রশ্নটি অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা কি শুধু পরিমাণগত (অংশ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে যান্ত্রিকযোগ সাজস্য) নাকি প্রকরণগত ও অবস্থাগত যা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাত্রা ও পর্যায় অনুসারে ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করে? অন্য কথায় মাটি ও মানুষের (মাটি থেকে সৃষ্ট) মধ্যে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্য কি পরিমাণগত,না অস্তিত্ব ও পূর্ণতার শ্রেণি (যেমন আলোকের তীব্রতা ও ক্ষীণতার পার্থক্য) অনুসারে?
যখন মানুষ নিজেকে এ প্রশ্নটি করে তখন ফেতরাতগত কারণেই নিজের মাঝে খুঁজে পায় যে,এ বিবিধ রূপসমূহ হলো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তীব্রতা ও ক্ষীণতা এবং পূর্ণতার স্তরসমূহের ফল। অর্থাৎ প্রাণের অস্তিত্ব হলো অনুভূতিহীন খাঁটি বস্তুর অস্তিত্বেরই পূর্ণ ও তীব্রতম পর্যায়। আর প্রাণ যত বেশি নূতন কিছু নিজের মধ্যে সংযোজন করতে থাকবে তত বেশি পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। এ অবস্থায়ই প্রাণ এক অনুভূতি ও সচেতন অস্তিত্ব হিসাবে উদ্ভিদের চেয়ে ঐশ্বর্যময় ও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু বস্তুবাদী চিন্তা এক শতাব্দীরও কিছু পূর্বে উপরিউক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল এবং অস্তিত্বশীল জগতের ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক মতবাদের উপস্থাপনা করল। যান্ত্রিক মতবাদটি নিম্নরূপ :
বাস্তবজগৎ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও পরস্পর সমাকৃতিক বস্তুশ্রেণি থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্র অনুসারে কোন এক ব্যাপক শক্তি এ বস্তুসমূহের উপর প্রভাব ফেলে। এর ফলশ্রুতিতে কিছু বস্তু অপর কিছু বস্তুকে গতিশীল করে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে চালিত করে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের এ সূত্র অনুসারে বস্তুর অংশসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে একীভূত হয় অথবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরীভূত হয়। আর এভাবেই বস্তু-রূপের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রময়তা অর্জিত হয়।
উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক বস্তুবাদ বিবর্তন ও গতিকে মহাশূন্যে বস্তু ও বস্তুকণাসমূহের স্থানান্তর গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং পদার্থের বিভিন্ন রূপকে এরূপে ব্যাখ্যা করে। তবে এ প্রক্রিয়ায় বস্তুদেহের একীভূত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে যাতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নূতন কোন কিছুর উদ্ভব ঘটে না। অতএব,বস্তু এর অস্তিত্ব ও বিবর্তনের মাঝে কোন বিকাশ ও উন্নয়ন লাভ করে না। যেমন আপনার হাতে কিছু খামির (মাখানো ময়দা) আছে যাকে আপনি বিভিন্ন আকৃতি দিতে পারেন। কিন্তু এর ফলে এতে খামির ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যাবে না।
এ কল্পনাটি হলো যান্ত্রিক বিজ্ঞানের বিকাশজাতক এবং তা প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থায় নিরঙ্কুশরূপে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিদ্যমান ছিল। এর কারণ ছিল এর মাধ্যমে যান্ত্রিক গতির সূত্র আবিষ্কার এবং সাধারণ বস্তুদেহের গতি ও মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের গতির ব্যাখ্যা প্রদান।
কিন্তু বিজ্ঞানের অব্যাহত বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈচিত্রতা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে তার বিস্তৃতির ফলে ইতোমধ্যে এ কল্পনাটির অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ দেখা গিয়েছে যে,এ কল্পনাটি সকল প্রকারের স্থানান্তর গতিকে যান্ত্রিকরূপে ব্যাখ্যা করতে অপারগ। অপরদিকে এ কল্পনাটি বস্তুসমূহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়াকে যান্ত্রিক গতির আলোকে একীভূতও করতে পারেনি। বিজ্ঞান গুরুত্বারোপ করে যে,মানুষ ফেতরাতগতভাবে বস্তুর রূপ-বৈচিত্র থেকে যা অনুধাবন করে তা শুধু বস্তুসমূহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের যান্ত্রিক গতি থেকে নয়,বরং তাদের গুণগত ও অবস্থাগত বিবর্তন ও বিকাশের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে,বস্তুসমূহের কোন প্রকার সংখ্যাগত ও গুণগত বিন্যাস ও আকৃতিই অনুভূতি,চিন্তা ও প্রাণের অধিকারী হতে পারেনি।
তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাই যে,এ বিষয়টি যান্ত্রিক বস্তুবাদী কল্পনার সাথে কতটা বিরোধ সৃষ্টি করে! কারণ প্রাণ ও অনুভূতি বা উপলব্ধিই হলো পদার্থের প্রকৃত বিকাশ এবং অস্তিত্বের স্তরে গুণগত বিবর্তন ও পরিবর্তনের জাতক-হোক এ বিবর্তনের ধারক সর্বোস্তরের বস্তু অথবা অবস্তুগত কিছু।
এখানে তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :
১. প্রতিটি সৃষ্টিশীল (حادث )৭ বস্তুই একটি অস্তিত্ব দানকারী কারণের উপর নির্ভরশীল।
২. নিম্ন পর্যায়ের বস্তু কখনই উচ্চ পর্যায়ের বস্তুর অস্তিত্ববিধায়ক কারণ হতে পারে না।
৩. এ জগতে বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের স্তরের পার্থক্য এবং অস্তিত্বশীলসমূহের রূপের যে বৈচিত্র তা হলো গুণগত (সংখ্যাগত ও পরিমাণ গত নয়)।
উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে,বস্তুর বিভিন্ন বিবর্তিত রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে পদার্থ অপেক্ষা এক প্রকার বিকাশ,পূর্ণতা এবং একটা কিছুর প্রাচুর্য উপস্থিত। তাহলে “ প্রতিটি সৃষ্টিশীল বিষয়ই একটি অস্তিত্বদানকারী কারণের উপর নির্ভরশীল,যা ঐ বিষয়ের পূর্বসূরী ” এর আলোকে প্রশ্ন করা যায় যে,এ ‘ প্রাচুর্য ’ কোথা থেকে অর্জিত হয়েছে এবং কিরূপে এর আবির্ভাব ঘটেছে?
প্রথম জবাব : এ ‘ প্রাচুর্য ’ স্বয়ং পদার্থ থেকেই অর্জিত হয়েছে। চিন্তা,অনুভূতি ও প্রাণহীন পদার্থই বিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যমে চিন্তা,অনুভূতি ও প্রাণের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পদার্থের সরলতম রূপই হলো পদার্থের পূর্ণাঙ্গ রূপের অস্তিত্ব দানকারী কারণ।
কিন্তু এ জবাবটি পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় বিষয়টির ( অর্থাৎ নিম্ন পর্যায়ের বস্তু কখনও উচ্চ পর্যায়ের বস্তুর অস্তিত্বগত কারণ হতে পারে না) সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করুন : মৃত পদার্থ যা স্বয়ং প্রাণের অধিকারী নয় তা নিজের জন্য এবং অপর পদার্থের জন্য অনুভূতি,অনুধাবন ও প্রাণের সঞ্চার করে যা ইংরেজি না জানা ব্যক্তির ইংরেজি শিখানো কিংবা ক্ষীণ আলোক থেকে তীব্র আলোকের উৎপত্তি অথবা সম্পদহীন বা দরিদ্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করার মতোই।
দ্বিতীয় জবাব : পদার্থের উপর এ প্রাচুর্য এমন এক স্থান থেকে অর্জিত হয় যা এ ‘ প্রাচুর্যের ’ অধিকারী অর্থাৎ প্রাণ চিন্তা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। আর তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। অতএব,একমাত্র মহান আল্লাহই তাঁর প্রজ্ঞা,পরিচালনা ও প্রতিপালনের মাধ্যমে পদার্থের বিকাশ ও বিবর্তন পদার্থের মাঝে অর্পণ করেন।
পবিত্র কোরআনে আমরা দেখতে পাই :
وَ لَقَدْ خَلَقْنا الاِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ المُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْناَ العِظاَمَ لَحْماً ثُمَّ أنْشَأناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَباَرَكَ اللهُ أحْسَنُ الخاَلِقِينَ.
“ এবং আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর আমরা তাহাকে সংস্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে; অতঃপর আমরা সেই শুক্র বিন্দুকে এক আঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঠালো জমাট রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, অতঃপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম। সুতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী। ” (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)
সুতরাং একমাত্র এ জবাবটির মাধ্যমেই আমরা পূর্বোল্লিখিত তিনটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠা এবং এ বিশ্বে বস্তুরূপের বিকাশ ও পূর্ণতার যুক্তিসংগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি।
পবিত্র কোরআন তার কিছু আয়াতে মানুষের সহাজাত প্রবৃত্তি (ফেতরাত) ও বিবেককে (عقل ) উদ্দেশ্য করে বলে :
اَفَرَئيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أأنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ
“ তোমরা ( নারীগর্ভে) যে বীর্যপাত কর, উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ? তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা উহার সৃষ্টিকর্তা? ” (সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ৫৮-৫৯)
اَفَرَئيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أأنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
“ তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা ক্ষেতে বপণ কর? তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা উহার উৎপাদনকারী? ” (সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ৬৩ ও ৬৪)
اَفَرَئيْتُمْ النَّارَ الَّتي تُورُونَ * أأنْتُمْ أنْشَأْتُمْ شَجَرَتهَاَ أمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ
“ তোমরা কি সেই আগুন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা জ্বালাইয়া থাক? তোমরাই কি উহার ( জন্য) বৃক্ষকে উৎপন্ন করা, না আমরা ( উহার) উৎপাদনকারী? ” (সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ৭১ ও ৭২)
وَمِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقًكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
“ এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি ( নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ, তোমরা মানুষরূপে ( সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ। ” (সূরা রূম : ২০)
দার্শনিক যুক্তির সম্মুখে বস্তুবাদের অবস্থানঃ
যান্ত্রিক বস্তুবাদ এ যুক্তির মোকাবিলায় কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। কেননা আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে,যান্ত্রিক বস্তুবাদ প্রাণ,অনুভূতি ও চিন্তাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে,এ বিষয়গুলো বস্তুদেহসমূহের বিচ্ছিন্নতা ও একীভূতি থেকে অর্জিত হয়েছে-কোন প্রাচুর্য থেকে নয়। অতএব,এ বিচ্ছিন্নতা ও একীভূতির মাধ্যমেই যান্ত্রিক শক্তি অনুসারে অংশসমূহের গতি নামক নূতন কিছু অর্জিত হয়েছে।
কিন্তু নব্য বস্তুবাদ ‘ বস্তুর প্রকরণগত ও অবস্থাগত বিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যমে বস্তু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে ’ -এ বিশ্বাস হেতু উক্ত যুক্তির সম্মুখে সমস্যায় পতিত হয়। তবে এ প্রতিষ্ঠান গুণগত বা অবস্থাগত বিবর্তনকে এমন এক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে যা পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় বিষয়টির (অর্থাৎ নিম্ন পর্যায়ের বস্তু উচ্চ পর্যায়ের বস্তুর অস্তিত্বগত কারণ হতে পারে না) সাথে সমন্বয় রক্ষা করে এবং একমাত্র পদার্থকেই এ অবস্থাগত বা গুণগত বিবর্তনের জন্য যথেষ্ট মনে করে। অর্থাৎ পদার্থই এ অবস্থাগত ও গুণগত বিবর্তন ও বিকাশের উৎস। আর এটি ‘ বিত্তহীন ব্যক্তির আপন সম্পদের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ’ পূর্বোল্লিখিত এ উদাহরণের মতো;দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে বৈপরীত্য প্রদর্শন করে না।৮
বরং এ ব্যাখ্যাটি এরূপ যে,প্রতিটি বিকশিত ও বিবর্তিত রূপ এবং এর ধারণকৃত উপাদানসমূহ পদার্থের মধ্যে সৃষ্টির আদি থেকেই বিদ্যমান। যেমন ডিমের মধ্যে মুরগী এবং পানির মধ্যে গ্যাস সৃষ্টির আদিতেই উপস্থিত ছিল। কিন্তু কিরূপে পদার্থ সমসাময়িককালে ডিম,আবার মুরগী;কিংবা গ্যাস আবার পানিও হতে পারে? দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এর জবাব নিম্নরূপে প্রদান করে :
এটা হলো পারস্পরিক বৈপরীত্য যা প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিয়ম। প্রতিটি পদার্থই স্বয়ং তার বিপরীত উপাদানের অধিকারী এবং এ দু ’ পরস্পর বিপরীত উপাদানের মধ্যে এক প্রকার নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব বিরাজমান। এ দ্বন্দ্বের ফলেই পদার্থের বিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন যখন ডিমের খোলস ভেঙ্গে যায় তখন একটি মুরগীর বাচ্চা তা থেকে বের হয়ে আসে। আর এভাবেই পদার্থ সর্বদা পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। কারণ পারস্পরিক বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের ফলে যে বৈপরিত্য (نقيض ) অর্জিত হয়েছে তা পরবর্তী দু ’ বৈপরীত্যের একটি হিসাবে কাজ করে।
অতএব,আমরা বলতে পারি নব্য বস্তুবাদ এ পদ্ধতির দ্বারা বুঝাতে চায় যে,প্রতিটি পদার্থ স্বয়ং তার বিপরীতেরও ধারণকারী। সুতরাং নিম্নলিখিত যে কোন একটি অর্থ উদ্দিষ্ট হতে পারে :
১. তবে কি ডিম এবং মুরগীর বাচ্চা পরস্পর বিরোধী বস্তু এবং ডিমই কি মুরগীকে অর্জন করে ও প্রাণ নামক বিশেষ গুণকে এর মধ্যে অস্তিত্বে আনে? অর্থাৎ মৃত বস্তু জীবন ও অস্তিত্ব সৃষ্টি করে এবং প্রাণ ও জীবন দান করে। তাহলে তো তা দরিদ্র ও বিত্তহীন ব্যক্তির সম্পদহীন অবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করার মতোই যা উল্লিখিত ভূমিকার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে।
২. অথবা এর অর্থ হলো ডিম বাচ্চাকে অস্তিত্বে আনে না,বরং তার অপ্রকাশিত অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। কারণ প্রতিটি বস্তুরই নিভৃতে তার বিপরীত বস্তুও বিদ্যমান। অর্থাৎ ডিম যে অবস্থায় ডিম সে অবস্থায় বাচ্চাও বটে। যেন সে ছবির মতো-এক দিক থেকে একরকম আবার অন্য দিক থেকে বিভিন্ন রকম।
তাহলে এটা পরিষ্কার যে,ডিম যে অবস্থায় ডিম আবার সে অবস্থায়ই যদি বাচ্চাও হয়,তবে পূর্ণতার জন্য কোন কার্য সম্পাদিত হয়নি (অর্থাৎ পূর্ণতা অর্জিত হয়নি)। কারণ যা এখন বিদ্যমান তা প্রথম থেকেই অস্তিত্ববান ছিল। যেমন কোন ব্যক্তি তার পকেট থেকে টাকা বের করল এবং তাতে অতিরিক্ত কোন টাকা সংযোজিত হয়নি। কারণ এ টাকা পূর্ব থেকেই তার পকেটে ছিল। যদি তাই হয়,তবে পূর্ণতার গতি (حركت تكاملي ) যা নতুন বস্তু সৃষ্টি করে,তার অর্থ কি?
অতএব,এর যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আমাদেরকে বলতে হবে যে,ডিম,বাচ্চা বা মুরগী ছিল না,বরং সেটার জন্য যোগ্য ছিল-যা বাচ্চায় পরিণত হয়েছে। আর এভাবে ব্যাখ্যা করেই আমরা ডিমকে প্রস্তরখণ্ড থেকে পৃথক করতে পারি। কারণ প্রস্তরখণ্ড কখনই মুরগী হতে পারবে না। অপরদিকে মুরগীর ডিমের এ সম্ভাবনা আছে যে,উপযুক্ত পরিস্থিতি ও শর্ত সাপেক্ষে তা মুরগীর বাচ্চায় পরিবর্তিত হতে পারবে। সর্বোপরি কথা হলো সৃষ্টি ও সংগঠনের জন্য শুধু সম্ভাবনাই যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ যদি কখনও ডিম বাচ্চায় পরিণত হয়,তবে শুধু সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে না।
অপরদিকে বস্তুর এ রূপান্তর যদি অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফল হয়,তবে উক্ত রূপান্তরকেও অবশ্যই এ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ভিত্তেতে ব্যাখ্যা করা উচিত। মুরগীর ডিমের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য অবশ্য পানির অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ ডিমের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফল হলো মুরগী,আর পানির অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফল হলো গ্যাস। এ কল্পনার উপর ভিত্তি করে সহজেই বস্তুর শেষ রূপান্তর থেকে বস্তুর গাঠনিক একক (অর্থাৎ ইলেকট্রন,প্রোটন ও নিউট্রন) পর্যন্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
প্রোটন একটি অসমস (ضد ),ইলেকট্রন অপর একটি অসমস ( ضد )। তাহলে নিউট্রন কি? প্রতিটি বস্তুই কি এ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ভিত্তিতে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে? অর্থাৎ প্রোটন বস্তুর অভ্যন্তরে বিদ্যমান এবং পরবর্তীতে গতি ও পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে কি মুরগী ও ডিমের মতো প্রকাশিত রূপ লাভ করে?
যদি তাই হয়,তবে বস্তুর রূপান্তরকে কিরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি? কারণ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের যুক্তি অনুসারে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে,বস্তসমূহ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে পরস্পর পৃথক। অর্থাৎ বস্তুসমূহের অভ্যন্তরীণ মৌলিক সত্তা পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান বস্তুর মৌলিক সত্তাগত অভিন্নতায় বিশ্বাসী। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বস্তুসমূহের অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ বা মৌলিক সত্তাসমূহ অভিন্ন এবং তারা যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তা তাদের এ অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের (যারা সর্বদা এক ও অভিন্ন) ভিত্তিতে হতে পারে না।
তবে প্রোটন নিউট্রনে বা নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ বস্তুর বাহ্যিক রূপ (পরমাণু ও মৌলিক সত্তাগত অভিন্নতা বিবেচনা না করলে) পরিবতির্ত হতে পারে। কিন্তু বস্তুর অভ্যন্তরীণ মৌলিক সত্তা সর্বদা একই থাকে যদিও তাদের রূপসমূহ বিভিন্ন। অতএব,কিরূপে এ ধারণা করা যায় যে,অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য ও বস্তুর অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের পার্থক্যের কারণে বস্তুসমূহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে?
মুরগী ও এর ডিমের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে উপস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন ডিম বিভিন্ন বাচ্চায় পরিণত হয়। তাহলে ‘ বস্তুসমূহের বিভিন্ন রূপের কারণ হলো তাদের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য ’ -এ ধারণার উপর ভিত্তি করে বলতে হয় যে,এ ডিমগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ গঠনেও পরস্পর বিভিন্ন ধরনের। অতএব,মুরগীর ডিম এবং অন্য কোন পাখির ডিম দু ’ টি ভিন্ন বাচ্চা অর্থাৎ মুরগী এবং অন্য পাখিতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি উভয়েই একই প্রকারের অর্থাৎ মুরগীর ডিম হয়,তবে বলা যাবে না যে,ডিম দু ’ টির অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের কারণেই দু ’ টি ভিন্ন রূপে পরিণত হয়েছে।
অতএব,দেখা যায় যে, ‘ বস্তুরূপের বৈসাদৃশ্য,অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের কারণ ’ -নব্য বস্তুবাদের এ ব্যাখ্যা এবং অধুনা বিজ্ঞানের বস্তুর অভ্যন্তরীণ মৌলিক সত্তার অভিন্নতায় যে বিশ্বাস তা দু ’ টি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।
৩. অথবা এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভবত বুঝানো হয়েছে যে,স্বয়ং মুরগীর ডিম দু ’ টি অসমস বা দুটি স্বাধীন বিপরীত সত্তার ধারক যেখানে প্রতিটিই একটি বিশেষ অস্তিত্বের অধিকারী।
তাদের একটি হলো : জীবন একক (نطفه ) যার কারণ স্বয়ং মুরগীর ডিমের অভ্যন্তরে রূপ লাভ করে এবং অপরটি হলো : যা মুরগীর ডিমের অন্যান্য উপাদানে সমন্বিত। এ দু ’ টি অসমস ডিমের অভ্যন্তরে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়,যার ফলে তাদের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশ লাভ করে অর্থাৎ জীবন একক (نطفه ) জয়ী হয় এবং ডিম মুরগীর বাচ্চা আকারে প্রকাশিত হয়। অসমসদের (اضداد ) মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব সর্বদা মানুষের জীবনে বিদ্যমান ছিল এবং দার্শনিক চিন্তায় তো বটেই,এমনকি মানুষের দৈনন্দিন চিন্তায়ও তা আদিকাল থেকে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কেন ডিমের অভ্যন্তরস্থ জীবন একক ও ডিমের প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পারস্পরিক বৈপরীত্য (تناقض ) নামকরণ করব? কেন বীজ,মাটি ও বাতাসের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পারস্পরিক বৈপরীত্য বলব? এবং কেনইবা মাতৃগর্ভে ভ্রুণ এবং তা যে সকল খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পারস্পরিক বৈপরীত্য নামকরণ করব? প্রকৃতপক্ষে এগুলো নিছক নামকরণ ছাড়া আর কিছুই না এবং এটাই বলা শ্রেয় যে,তাদের (অসমসদ্বয়) একটি অপরটিতে বিগলিত হয় বা অপরটির সাথে একীভূত হয়।
ধরা যাক,একে আমরা পারস্পরিক বৈপরীত্য নামকরণ করব। অতএব,যদবধি আমরা বলব যে,দু ’ টি অসমসের মধ্যে বিশেষ দ্বন্দ্বই বিকশিত নূতন বস্তুর আবির্ভাবের কারণ যা পূর্বের অসমসদ্বয়ের উপাদনাসমূহের সমষ্টি অপেক্ষা বেশি,তদবধি এটা দ্বারা আমাদের সমস্যা দূরীভূত হয় না। কারণ এ বেশি অংশ কোথা থেকে এসেছে? দু ’ টি অসমসের (যাদের প্রতিটিই তৃতীয় কোন বিষয়ের ঘাটতিযুক্ত) পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলেই কি এ বেশি অংশটুকু উদ্ভাবিত হয়েছে? এ ব্যাখ্যা পূর্বোল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের দ্বিতীয়টির (নিম্ন পর্যায়ের বস্তু উচ্চ পর্যায়ের বস্তুর কারণ হতে পারে না) ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
অসমস এবং দু ’ টি অসমসের মধ্যকার সংঘর্ষই প্রকৃত বিকাশ ও বিবর্তনের কারণ-এ ধরনের কোন উদাহরণ কি আমরা প্রকৃতিতে পেতে পারি? কিরূপে এক অসমস পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিজের বিপরীতের বিকাশ ও বিবর্তনে সাহায্য করতে পারে যেখানে অসমতা বা দ্বন্দ্বের অর্থ হলো প্রতিরোধ বা কোন কিছু গ্রহণে আপত্তি এবং প্রতিটি প্রতিরোধই আপন শক্তির বিপরীতকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ বিপরীতের বিকাশ ও পূর্ণতার বিরোধী?
আমরা সকলেই জানি যে,সাঁতারু যখন সমুদ্রতরঙ্গের সম্মুখীন হয় তখন সমুদ্রতরঙ্গ তাকে সম্মুখে এগুতে বাধাগ্রস্ত করে এবং সাঁতারুকে গতিশীল করার পরিবর্তে তার অগ্রসর হওয়ার শক্তিকে হরণ করে। যদি অসমসদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ (যে কোন অর্থেই হোক না কেন) ডিমের বিকাশ এবং এর মুরগীতে বিবর্তিত হওয়ার মূলে বিদ্যমান থাকে,তবে যে বিকাশ অসমসমূহের দ্বন্দ্বের ফলে পানিকে গ্যাসে পরিণত করে বা গ্যাস পানিতে পরিণত হয়,তা কোথায়?
প্রকৃতি আমাদেরকে ঐ সকল অসমসের সাথে পরিচয় করায় যাদের মধ্যকার সংঘর্ষ,এমনকি সম্পৃক্তি,বিবর্তন ও বিকাশের কারণ তো নয়ই,বরং বিনাশ ও ধ্বংসের কারণ হয়। ধনাত্মক প্রোটন পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রন উক্ত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করে। যদি এ দু ’ টি বিপরীতধর্মী সত্তা পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়,তবে পরমাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ফলশ্রুতিতে উক্ত পদার্থ প্রকাশিত অবস্থা থেকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে।
মোটকথা পদার্থ (এর বহির্ভূত) কোন বাহ্যিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃত বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করতে এবং উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। বিশেষ করে,পদার্থ কখনই স্বয়ং পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবন,অনুভূতি ও অনুধাবনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না যদি না মহান আল্লাহ পদার্থকে এ সকল বিশেষত্ব অর্জনে সাহায্য করে। বিকাশ ও বিবর্তনের কার্যক্রমে পদার্থের ভূমিকা শুধুমাত্র জীবন,অনুভূতি ও উপলব্ধির বিশেষত্বকে গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ততা অর্জন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেমন কোন শিশু তার শিক্ষকের কাছে জ্ঞান নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।
অতএব,বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ অতীব বরকতময়।
মহান আল্লাহর গুণসমূহ
এখন যেহেতু প্রজ্ঞা ও কৌশল অনুযায়ী সৃষ্টিকারী,প্রতিপালনকারী এবং জগতের শৃঙ্খলা বিধানকারী হিসাবে মহান আল্লাহর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি স্বভাবতঃই তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্টের মাধ্যমে তাঁর গুণাবলীর সাথেও আমরা পরিচিত হব এবং এ সৃষ্টসমূহের সাহায্যে তাঁর গুণাবলীকে পর্যালোচনা করব। যেমনি করে আমরা একজন প্রকৌশলীকে তাঁর তৈরিকৃত ইমারতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিংবা একজন লেখককে তাঁর লিখিত বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে অথবা একজন শিক্ষককে তাঁর শিক্ষার্থীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সঠিকভাবে চিনতে পারি।
এরূপে আমরা মহান স্রষ্টার কতিপয় গুণ,যেমন তাঁর জ্ঞান,প্রজ্ঞা,জীবন,ক্ষমতা,দর্শন ও শ্রবণ সম্পর্কে অবগত হতে পারব। কারণ এ সৃষ্টিজগৎ সুনিপুণতা ও সূক্ষ্ম কার্যে পরিপূর্ণ (যার জন্য গভীর মনোযোগের প্রয়োজন),যা আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এ সুনিপুণ বিন্যাস ব্যবস্থার গভীরে এমন সব শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে যারা তাঁর ক্ষমতা ও আধিপত্যকে প্রদর্শন করে। এছাড়া বিচিত্র রূপ,বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিও বিদ্যমান যা মহান আল্লাহর জীবন ও উপলব্ধিকে বর্ণনা করে। জগতের এ বিন্যাস ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এক বিশেষ সমন্বয় ও সুসংগতি প্রতিষ্ঠিত যা সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রমাণ বহন করে। আর সে সাথে প্রমাণ করে তাঁর জ্ঞানের একত্বকেও যা থেকে এ মহাজগৎ সৃষ্ট ও সিদ্ধি লাভ করেছে।
ন্যায়পরায়ণতা (عدل )ও দৃঢ়তা (استقامت ) :
আমরা প্রত্যেকেই (ফেতরাতগত ও তাৎক্ষণিকভাবে) আমাদের জীবন ব্যবস্থায় এক শ্রেণির সাধারণ মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এ মূল্যবোধ গুরুত্বারোপ করে যে,ন্যায়পরায়ণতা সত্য ও কল্যাণকর;জুলুম বা অত্যাচার মিথ্যা ও অকল্যাণকর। ন্যায়পরায়ণ পৃথিবীতে সম্মান ও পরকালে পুরস্কারের উপযুক্ত। আর অত্যাচারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী পৃথিবীতে নিন্দিত ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য। এ মূল্যবোধসমূহ স্বভাবজাত ও ফেতরাতগতভাবেই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা প্রদানের মূল,তবে যখন অজ্ঞতা ও সুবিধাবাদীতার মতো কোন প্রতিকূলতা না থাকে। অতএব,যদি কোন মানুষ সত্য ও মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে অথবা বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকে এবং যখন ব্যক্তিগত কোন বাধা ও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য তাকে এ মূল্যবোধসমূহ থেকে বিচ্যুতিতে বাধ্য না করে,তবে সে সত্যকে মিথ্যা এবং বিশ্বস্ততাকে বিশ্বাসঘাতকতার উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ যে এমন কারো উপর নির্ভরশীল নয়,যে তাকে এ সকল মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করতে পারে অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য যাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অত্যাচারের পথে পরিচালিত না করতে পারে,সে ব্যক্তির সাথে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মতো আচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ ঠিক সেরকম আচরণ যা মহান আল্লাহর জন্যই সঠিক এবং তিনিও ঐ ধরনের ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণই করে থাকেন। এ সমস্ত মূল্যবোধ মহান আল্লাহরই আওতাধীন এবং আমরা যা ফেতরাতগত জ্ঞানের দ্বারা অনুধাবন করতে পারি। কারণ মহান আল্লাহই আমাদেরকে এ জ্ঞান দান করেছেন এবং ঐ অবস্থায় মহান প্রভু তাঁর মহাপরাক্রম ও জগতের সর্বত্রব্যাপী বিরাজমান শক্তি ও আধিপত্য এবং সকল পূর্ণতাব্যঞ্জক গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে কোন কিছু থেকে লাভবান হওয়ার মুখাপেক্ষী নন। এখানেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব যে,মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ এবং তিনি কাউকেই অত্যাচার করার অনুমতি প্রদান করেন না।
মহান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা প্রতিদানের প্রমাণবহ :
ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে,যে সকল মূল্যবোধে আমরা বিশ্বাসী সে সকল মূল্যবোধ আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা,দৃঢ়তা,বিশ্বস্ততা,সততা,প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও অন্যান্য সৎ গুণের দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐগুলোর বিরোধী কোন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে। এ মূল্যবোধসমূহ শুধু আমাদেরকে কিছু গুণের প্রতি আকৃষ্ট বা কিছু গুণের প্রতি বিকর্ষিতই করে না,বরং এগুলোর বিনিময়ে যথোপোযুক্ত প্রতিদানও যাঞ্ছা করে থাকে। ফেতরাতগত জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই অনুধাবন করে যে,অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি পাওয়া উচিত এবং ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসী,যে ন্যায়,বিশ্বাস ও সততার পথে নিজেকে উৎসর্গ করে তার পুরস্কৃত হওয়া উচিত। অবশ্য আমাদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্বের গভীরে এমন একটি অবস্থা বিরাজমান যা অত্যাচারী সীমা লঙ্ঘনকারীকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে;আর ন্যায়পরায়ণ ও সৎ কর্মপরায়ণকে উৎসাহ ও স্বীকৃতি দান করে। এরূপ প্রতিক্রিয়ার অনুপস্থিতির কারণ,হয় কোন ব্যক্তির সঠিক অবস্থান গ্রহণে অক্ষমতা অথবা তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকার বহিঃপ্রকাশ।
যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করব যে,মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ এবং যথাযথ প্রতিদান প্রদানে মহাপরাক্রমশালী;কোন কিছুই ঐ সকল মূল্যবোধের জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদান প্রদানে তাঁকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না এবং তিনি সৎ কর্মপরায়ণ ও দুষ্কর্ম পরায়ণের প্রত্যেককেই তাদের সঠিক প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে অতীব শক্তিধর,ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবতঃই আমরা বিশ্বাস করব যে,মহান আল্লাহ পুণ্যবানকে তাঁর পুণ্য অনুসারে পুরস্কৃত করেন;আর অত্যাচারিতের প্রাপ্য অত্যাচারীর নিকট থেকে আদায় করেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে,এ প্রতিদানগুলোর অধিকাংশই মহান আল্লাহর আওতাধীন হওয়া সত্ত্বেও এ পৃথিবীতে কার্যকর হয় না।
অতএব,আমাদের পূর্বোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে,প্রতিদানের জন্য এক আসন্ন দিবসের অস্তিত্ব রয়েছে-যেদিন কোন এক অখ্যাত ব্যক্তি,যে নিজেকে এক মহান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন,কিন্তু তাঁর এ ত্যাগের ফল পার্থিব জীবনে আহরণ করতে পারেননি এবং যে অত্যাচারী তার শাস্তি প্রাপ্তি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল,শত অত্যাচারিতের রক্তের উপর দিয়ে আপন পথ রচনা করেছিল,হরণকৃত সম্পদের বিনিময়ে সুখের নীড় গড়েছিল-তাদের প্রত্যেকেই ন্যায়-নীতির পরাকাষ্ঠে যথাযথ প্রতিদান লাভ করবে। আর এ আসন্ন দিবসটিই হলো কিয়ামত বা পরকাল। সেদিন এ মূল্যবোধসমূহের প্রতিটিই মূর্তরূপে প্রতীয়মান হবে এবং এমন একটি দিবস ব্যতীত প্রাগুক্ত মূল্যবোধসমূহই অর্থহীন।
প্রেরিত
(রাসূল)
v নবুওয়াতের সাধারণ আলোচনা
v বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত
নবুওয়াতের সাধারণ আলোচনা
এ মহাবিশ্বে বিরাজমান সকল কিছুই মহান আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীন। কোন অবস্থায়ই কোন কিছুই এ নিয়মের গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এ নিয়মের অধীনেই সৃষ্ট বিষয়সমূহ পরিচালিত এবং বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হয়। অতএব,শষ্যবীজ এক বিশেষ নিয়মের অধীন যা উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে বৃক্ষে পরিণত হয়;জীবন এককও এক বিশেষ নিয়মের অধীন যা তাকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে। নক্ষত্র থেকে প্রোটন পর্যন্ত এবং নক্ষত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহসমূহ থেকে প্রোটনকে কেন্দ্র করে ভ্রমণকারী ইলেকট্রনসমূহ পর্যন্ত সবকিছুই এ নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয় এবং নিজ নিজ বিশেষ সম্ভাবনাসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিকশিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।
মহান প্রভু কর্তৃক প্রণীত এ কর্মসূচী সর্বজনীন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা এ মহাবিশ্বের সকল পর্যায়ে এবং সকল বিষয়ে বিস্তৃত।
বিদ্যমান এ বিশ্বে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা। মানুষ এক স্বাধীন (ঐচ্ছিকভাবে) ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন অস্তিত্ব অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য আছে এবং তার সমস্ত কর্ম ঐ উদ্দেশ্যের পথেই সম্পন্ন করে। সে মাটি খনন করে যাতে পানি পেতে পারে,খাদ্যসমূহ রান্না করে যাতে সুস্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং প্রাকৃতিক বিষয়সমূহকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাতে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হতে পারে। ঐ সকল প্রাকৃতিক বিষয়েরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান এবং তারা সকলেই একই রেখায় নিজ নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসরমান। তবে তাদের ক্রিয়াকলাপ কেবল জীবন ও জীবন ধারণ নয়,বরং এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরবৃত্তিক (Physiological)। যেমন ফুসফুস,পাকস্থলী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শারীরিক কাজকর্মের জন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হয়। কিন্তু এ উদ্দেশ্য নিজ বিশেষ সহজাত ও শারীরিক ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে নয়,বরং তা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। যেহেতু মানুষ এক উদ্দেশ্যসম্পন্ন অস্তিত্ব সেহেতু তার সকল কর্মতৎপরতার পেছনে যে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে তা ঐ কর্মসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে এমন নয় যে,সর্বদা সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতি বজায় রেখে কাজ করে (যেমন এক বিন্দু পানি মহাকর্ষ নিয়মের ফলে নীচে পতিত হয়)। কারণ যদি তা-ই হতো তবে মানুষের অন্তরে এমন কোন উদ্দেশ্য বিরাজ করত না যার দিকে সে ধাবিত হতে পারে। এখন মানুষ হলো উদ্দেশ্যসম্পন্ন অস্তিত্ব যে স্বাধীন এবং সে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব,মানুষের কর্মক্ষেত্র ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক হলো একটি নিয়ম যা তার ইচ্ছাকে প্রতীয়মান করে। কারণ উদ্দেশ্য নিজেই অবচেতনভাবে বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আপন উদ্দেশ্যকে তার নিজস্ব কল্যাণচিন্তা,প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা অনুসারে বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ করে। আবার স্থান-কাল ও পরিবেশ যা মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট তা তার এ চাওয়া-পাওয়া,লক্ষ্য ও অভ্যাসসমূহের সীমা নির্ধারণ করে। কিন্তু এ সকল পারিপার্শ্বিক নিয়ামক ও প্রভাবক যেগুলো মানুষকে তার লক্ষ্যপানে ধাবিত করে সেগুলো আসলে বায়ুপ্রবাহের মতো নয় যা বৃক্ষ পত্রকে আন্দোলিত করে,বরং স্বীয় লক্ষ্যপানে ধাবিত হওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের কল্যাণচিন্তা থেকেই উৎসারিত। কারণ বায়ুপ্রবাহ এবং পত্ররাজির আন্দোলনে স্বকীয় উদ্দেশ্য নামক কোন বিষয়ের ভূমিকা নেই।
অতএব,উল্লিখিত নিয়ামকসমূহ অর্থাৎ স্থান-কাল-পরিবেশ বাধ্যগতভাবেই মানুষকে তার কল্যাণচিন্তার উপলব্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন নির্দিষ্ট কাজে প্ররোচিত করে। তবে প্রতিটি কল্যাণচিন্তাই মানুষকে প্ররোচিত করে না,বরং তার সহজাত কল্যাণচিন্তাই এ স্থানে ভূমিকা রাখে। কল্যাণচিন্তা(مصالح ) দু ’ প্রকারের। কোন কোন কল্যাণচিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন এক উদ্দেশ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে দ্রুত সময়ে ফল দান করে। আবার কোন কোন কল্যাণচিন্তা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটা সমাজকে বা জনগোষ্ঠীকে সুফল দিয়ে থাকে এবং প্রায়শঃই ব্যক্তিগত কল্যাণচিন্তার সাথে সামাজিক কল্যাণচিন্তার বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অতএব,আমরা দেখতে পাই যে,মানুষ প্রায়ই কল্যাণচিন্তা ও ইতিবাচক মূল্যবোধের কারণে কর্মে লিপ্ত হয় না,বরং যতটুকু থেকে সে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারবে,ঠিক ততটুকু কার্য সম্পাদনেই উদ্যোগী হয়। অপরদিকে সমাজের কল্যাণচিন্তা অনুসারে মানব উন্নয়নের জন্য নিয়ামকসমূহের ভূমিকা মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য শর্ত এবং তার সফলতাও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর ভিত্তিতে সমাজকল্যাণে মানুষের প্রাসঙ্গিক আচরণ ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তার জীবন পদ্ধতি ও জীবন যাপন যা অপরিহার্য করে তা,আর তার ব্যক্তিগত প্রবণতা,সহজাত প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা-এ দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয়।
অতএব,একান্ত বাধ্যগতভাবেই এ বিরোধের অবসান এবং যে সকল নিয়ামক ও কারণ মানুষকে সমাজের কল্যাণার্থে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকার জন্য মানুষকে একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। (আর তা হলো নবুওয়াত)।
নবুওয়াত মানব জীবনের জন্য একটি ঐশী বিষয় যা প্রাগুক্ত বিরোধের সমাধান দেয়। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণকে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যক্ত করে যা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। আর তা এ আহ্বানের মাধ্যমে রূপ লাভ করে যে,মৃত্যুর পরও মানব জীবন অব্যাহত থাকবে এবং মানুষকে প্রতিদান লাভের জন্য সত্য ও ন্যায়বিচারের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। মানুষই হলো সে সৃষ্টি যে আপন কর্মের ফল দেখতে পাবে। পবিত্র কোরআনের আয়াত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ
“ তখন কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পুণ্যকর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে এবং কোন ব্যক্তি এক অনু পরিমাণও মন্দ কর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে। ” (সূরা যিলযাল : ৭ ও ৮)
সুতরাং এক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিকল্যাণে রূপান্তরিত হয়।
অতএব,যা এ বিরোধের অবসান ঘটায় তা হলো এক নির্দিষ্ট মতবাদ এবং এর ভিত্তিতে প্রদত্ত বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি। আর উক্ত মতবাদ হলো পুনরুত্থান দিবস বা কিয়ামত সম্পর্কিত মতবাদ যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সুফলদায়ক হয়। এ মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঐশী পদ্ধতিতে হয়ে থাকে এবং ঐশ্বরিক সাহায্য ব্যতীত তা অসম্ভব। কারণ এ কার্যক্রম পরকাল বা অদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল যা ঐশী বাণী (وحي ) অর্থাৎ নবুওয়াত ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।
মোদ্দাকথা,নবুওয়াত ও পুনরুত্থান দিবস এ দুই পরস্পর জড়িত বিষয়ই মানব জীবনে উল্লিখিত বিরোধের সমাধান দিয়ে থাকে এবং মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতাভিত্তিক আচরণের বিকাশ সাধন ও প্রকৃত মানবকল্যাণের দিকে তাকে উন্নীতকরণের জন্য মৌলিক শর্তসমূহের আয়োজন করে।
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রমাণঃ
যেমন করে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আরোহ যুক্তি পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়েছে তেমনি মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতও বৈজ্ঞানিক ও আরোহ যুক্তির মাধ্যমে এবং যে পদ্ধতি নিজেদের জীবনে কোন বাস্তবতাকে প্রমাণ করতে প্রয়োগ করা হয় সে পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়। এ উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদাহরণ ভূমিকারূপে তুলে ধরব :
মনে করুন কোন ব্যক্তি কোন এক নিকটাত্মীয় গেঁয়ো কিশোর (যে প্রথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে) কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি পেলেন। ঐ ব্যক্তি দেখতে পেল যে,উল্লিখিত চিঠিটি সর্বোচ্চ সাহিত্যমান,চূড়ান্ত ভাষাশৈলী,পূর্ণ অভিব্যক্তি ও সুন্দর চিন্তাসম্বলিত,নির্ভুল ও নূতন ভাষায় লিখিত। যখন কোন ব্যক্তি এ ধরনের একটি চিঠি পায় তখন দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে,কোন এক সুশিক্ষিত,বহুমুখী জ্ঞান ও সুন্দর লেখার অধিকারী ব্যক্তি এ চিঠিটি উক্ত কিশোরকে লিখে দিয়েছে অথবা ঐ কিশোর অন্য কোন উপায়ে কারো নিকট থেকে ভাষাগুলো শিখে নিয়েছে।
যদি আমরা উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তবে দেখতে পাব যে,ঐ ঘটনাটিকে পত্রপ্রাপক নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করেছেন :
ক . পত্রলেখক হলো এক গেঁয়ো কিশোর যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে।
খ . পত্রখানি এক চূড়ান্ত বাগ্মিতা,আকর্ষণীয় ও মিষ্টি-মধুর এবং সুন্দর ও দক্ষ প্রকাশভঙ্গিতে জ্ঞানগর্ভমূলক ভাষায় লিখিত হয়েছে।
গ. অনুরূপ অবস্থাসমূহের মধ্যে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে,একজন কিশোরের (ক-তে উল্লিখিত) পক্ষে এ ধরনের (খ-তে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসহকারে) একটি পত্র লিখা সম্ভব নয়।
ঘ . উপসংহারে বলা যায় পত্রটি অন্য কারো চিন্তা ও ভাষা থেকে রচিত হয়েছে। অতঃপর তা কোনভাবে উক্ত কিশোরের হাতে এসেছে এবং সে তা থেকে লাভবান হয়েছে।
অপর উদাহরণটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতি থেকে নেয়া হয়েছে-যার মাধ্যমে বিজ্ঞানিগণ ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে থাকেন। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :
কোন এক বিজ্ঞানী এক প্রকারের আলোক রশ্মির উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং অনুরূপ প্রকারের বিশেষ রশ্মিকে একটি বদ্ধ টিউবের মধ্যে উৎপাদন করেছেন। অতঃপর ঘোড়ার নাল আকৃতির একটি চুম্বক উক্ত টিউবের মাঝ বরাবর স্থাপন করলেন। এ সময় লক্ষ্য করলেন যে,উক্ত বিশেষ রশ্মি চুম্বকের ধনাত্মক মেরুর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল এবং ঋণাত্মক মেরু থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। এ নিরীক্ষণটিকে বিভিন্ন অবস্থা,সময় ও স্থানে পুনরাবৃত্তি করলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে,এ বিশেষ রশ্মি চুম্বকের সাথে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ক্রিয়া প্রদর্শন করে।
উক্ত বিজ্ঞানী তাঁর পর্যবেক্ষণকে অন্যান্য আলোক রশ্মির ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন যে,এ আলোক রশ্মিসমূহ চুম্বক কর্তৃক প্রভাবিত হয় না অথবা তার দিকে আকৃষ্ট হয় না। অতএব,তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে,চুম্বকের চৌম্বকশক্তি আলোকরশ্মিকে আকর্ষণ করে না,বরং আলোক রশ্মির অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশেষ সত্তাসমূহকে আকর্ষণ করে এবং উক্ত সত্তাসমূহ নির্দিষ্ট এক প্রকারের রশ্মিসমূহে বিদ্যমান যা চুম্বকের ধনাত্মক মেরুর দিকে ধাবিত হয়। এ বিষয়টিকে জ্ঞাত ধারণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অতএব,তিনি বুঝতে পারলেন যে,আলোক রশ্মিসমূহে অন্য কোন সত্তা বিদ্যমান। অর্থাৎ এ রশ্মিসমূহ ঋণাত্মক ধর্মবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণিকার সমন্বয়ে গঠিত যা সকল প্রকারের পদার্থে উপস্থিত রয়েছে। এ অতি ক্ষুদ্র কনিকাসমূহকে ইলেকট্রন নামকরণ করা হলো।
উপরিউক্ত দু’টি উদাহরণে যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে,জ্ঞাত উপাত্তসমূহের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পর্যালোচনা এবং অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে ঐ জ্ঞাত উপাত্তসমূহের অনুসন্ধানমূলক পর্যবেক্ষণ স্বয়ং ঐ নির্দিষ্ট ঘটনাসংশ্লিষ্ট নয়। আর এটা অপ্রত্যাশিত অপর এক বিষয়ের উপস্থিতি প্রমাণ করে যা উল্লিখিত ঘটনার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ধরে নিতে হয়।
অন্যভাবে বলা যায়,যখন অনুরূপ অবস্থাসমূহের মধ্যে অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখা যায় যে,বিদ্যমান জ্ঞাত উপাত্তসমূহ অপেক্ষা বৃহত্তর কোন ফল পাওয়া যায়,তবে তা জ্ঞাত উপাত্তসমূহের নেপথ্যে অপর এক বিষয়ের উপাস্থিতি প্রমাণ করে যা তদোবধি আমাদের চিন্তায় ছিল না। আর এটা তা-ই যা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের এবং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক বিশ্ববাসীর জন্য ঘোষণাকৃত ঐশীবাণীর প্রমাণ বহন করে।
এ উপসংহার নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অতিক্রমণান্তে প্রমাণিত হয় :
ক . এ ব্যক্তি যিনি তাঁর রিসালাতকে (প্রেরিত বাণী) একক প্রভু কর্তৃক প্রেরিত বলে বিশ্ববাসীদেরকে আহবান জানাচ্ছেন তিনি ছিলেন সভ্যতা,সংস্কৃতি,চিন্তা,রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ স্থান আরব উপদ্বীপের অধিবাসী। বিশেষ করে হেজায নামক এ উপদ্বীপের একটি স্থান যা এমনকি শত শত বছর পূর্বের প্রাথমিক সভ্যতার সাথেও ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত ছিল না,তিনি সে স্থানের অধিবাসী ছিলেন। হেজায পরিপূরক সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছুই জানত না এবং সমসাময়িক সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে বিন্দুমাত্র লাভবান হয়নি। এমনকি বিশ্বের অন্যান্য স্থানের উন্নত সভ্যতা,সংস্কৃতি ও চিন্তার মতো উল্লেখযোগ্য কোন কিছুর উপস্থিতি হেজাযের অধিবাসীদের কবিতা ও সাহিত্যকর্মেও ছিল না। হেজাযের অধিবাসীরা বিশ্বাসগত দিক থেকে শিরক (অংশীদারিত্ব) এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সমাজে সত্যিকার অর্থে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম বিরাজ করছিল এবং একমাত্র সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক বিধানই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। এভাবে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় (قبيله ) ও দলে বিভক্ত ছিল। এ অবস্থার কারণে তাদের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব,সংঘাত ও লুটতরাজ লেগেই থাকত। যে শহরে নবী (সা.) বড় হয়েছেন সেখানেও শুধু গোত্রভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোন শাসন-ব্যবস্থা ছিল না এবং এর বাসিন্দারা গ্রোত্রপতি ছাড়া কউকে চিনত না। এমনকি পড়ালেখার মতো সভ্যতা-সংস্কৃতির এ সাধারণ কাজগুলোতেও তারা কালেভদ্রে বা কদাচিৎ হাত দিয়েছিল। অর্থাৎ এ সমাজ ছিল সামগ্রিকভাবে মূর্খ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :
هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الاُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُو مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ.
“ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রাসূল আবির্ভূত করিয়াছেন যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ” (সূরা জুমু’আ : ২)
স্বয়ং রাসূল (সা.) উক্ত সমাজের ব্যক্তিসকলের নিরক্ষর অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোন লেখা-পড়াই করেননি। পবিত্র কোরআনের ভাষায় :
وَ ماَ كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَ لاَ تَخُطُُّهُ بِيَمِينِكَ اِذاً لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
“ এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব আবৃত্তি কর নাই এবং তোমার ডান হাতে ইহা লিখও নাই, যদি এই রূপ হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদিগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত। ”(সূরা আনকাবুত : ৪৮)
পবিত্র কোরআনের এ অকাট্য ভাষ্য নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক অবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ প্রমাণটি,এমনকি যারা কোরআনের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাসী নয় তাদের জন্যও অকাট্য প্রমাণ। কারণ তা এমন এক অকাট্য ভাষ্য যা নবী (সা.) তাঁর নিজ গোত্রের নিকট ঘোষণা করেছিলেন এবং যারা নবীর জীবনেতিহাস ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিল তাদের সম্মুখে বর্ণনা করেছিলেন;তা সত্ত্বেও কেউই এ বক্তব্যের বিরোধিতা করতে পারেনি;বরং তারা জানত যে,রাসূল (সা.) এমনকি নবুওয়াতের পূর্বেও তদানিন্তন তাঁর গোত্রে প্রচলিত কবিতা বা প্রশংসাগীতির মতো কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতেন না এবং চারিত্রিক বিষয়,যেমন বিশ্বস্ততা,সচ্চরিত্র,সততা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বাসনা তাঁর আচরণে পরিলক্ষিত হয়নি।
তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর আপন গোত্রের মাঝে অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীদের চেয়ে উল্লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে অগ্রাধিকার দেননি। অনুরূপ তিনি তাঁর জীবনে ঐ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন,যা চল্লিশ বছর প্রকাশ লাভ করেছে তার কোন ইঙ্গিত ও চি হ্ন তাঁর প্রাকনবুওয়াত জীবনে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের বাণী স্মরণযোগ্য :
قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ اَدْراَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أفَلاَ تَعْقِلُونَ
“ তুমি বল, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না। নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ সময় ধরে জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক- বুদ্ধি খাটাইবে না ও অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে না? ” (সূরা ইউনুস : ১৬)
মহানবী (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে দু’টি ছোট সফর ছাড়া আরব উপদ্বীপের বাইরে যাননি। এ দু’টি সফরের একটি ছিল তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাল্য বয়সে জীবনের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে এবং অপরটি ছিল তাঁর জীবনের তৃতীয় দশকের শুরুতে হজরত খাদিজা (সা.)-এর ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে।
অতএব,নবী (সা.) যেহেতু পড়তে ও লিখতে অপারগ ছিলেন,সেহেতু ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের কোন উৎস থেকে কিছুই পড়তে ও শিখতে পারেননি। অপরদিকে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেও এ ধরনের কিছু পাননি। কারণ মক্কা তখন চিন্তা ও আচরণগত দিক থেকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল এবং খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদীবাদের কোন চিন্তা-চেতনা সেখানে পৌঁছেনি। আবার নীতিগতভাবে ‘ হোনাফা’( الحنفاء )বলে পরিচিত যে সকল ব্যক্তি মূর্তিপূজাকে নিষেধ করতেন তাঁরাও খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদীবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না।
এমনকি ইহুদীবাদ ও খ্রিষ্টবাদের চিন্তার কোন প্রতিফলনই কেস ইবনে সাদাত (قس ابن سعادة ) এবং অন্যান্য হোনাফা অর্থাৎ দীনে হানীফের অনুসারীদের কবিতা ও সাহিত্যকর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না।
এছাড়া রাসূল (সা.) যদি ইহুদী ও খ্রিষ্টবাদের উৎসসমূহ থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টাও করতেন,তবে তা ঐ রকম এক সহজ-সরল পরিবেশে এবং ইহুদীবাদ ও খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ সমাজে তাঁর আচার-আচরণে প্রকাশ পেত এবং এর ফলশ্রুতিতে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারত না।
খ . যে রিসালাত (ঐশী বাণী) ইসলামের নবী (সা.) বিশ্ব-মানুষের কাছে ঘোষণা করেছেন এবং যা কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধানের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করেছে তা অনেক বিশেষত্বে পরিপূর্ণ ছিল :
ইসলামী রিসালাত মহান আল্লাহ্,তাঁর গুণাবলী,জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসমূহ সংক্রান্ত এক অভূতপূর্ব ঐশী দিকনির্দেশনা আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা মানব জাতির পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নবিগণের ভূমিকা এবং তাঁদের বার্তা ও বাণীর মধ্যকার ঐক্য,তাঁদের অতুলনীয় আদর্শিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টান্তসমূহকেও অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছে। এ রিসালাত নবিগণের সাথে প্রভুর আচরণ,সত্য ও মিথ্যা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যকার অবিরাম দ্বন্দ্ব,সংঘাত ও সংগ্রাম সম্পর্কেও আলোচনা করেছে। যারা অত্যাচারিত,লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত তাদের সাথে ঐশী রিসালাতের যে গভীর সম্পর্ক আছে তা এবং সকল ঐশী রিসালাত যে,যারা অবৈধ স্বার্থ ও লেনদেনের মাধ্যমে অন্যদেরকে ঠকিয়ে সুবিধা ভোগ করে তাদের বিরোধী-এ বিষয়টিও ইসলামী রিসালাতে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে।
ঐশী এ রিসালাত শুধু র্শিক ও মূর্তিপূজা কবলিত চিন্তা ও ধর্মের তুলনায়ই মহান ও শ্রেষ্ঠ নয়,বরং সকল ধর্ম-যেগুলো ঐ সময় পর্যন্ত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল সেগুলোর চেয়েও শ্রেয়তর। এমনকি তাদের যে কোন প্রকারের তুলনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে,ইসলাম এসেছে অতীতের সকল ধর্মের ক্রটি-বিচ্যুতিকে পরিশুদ্ধ করতে এবং ঐগুলোক মানবীয় ফেতরাত ও সুষ্ঠু যুক্তি ও জ্ঞানের দিকে প্রত্যাবর্তন করাতে।
আর এ বিষয়গুলোর সবই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এমন এক সমাজে রূপ লাভ করেছে যে সমাজ বিকাশ ও পূর্ণতার পর্যায় তো দূরের কথা,সমসাময়িক কালের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় পুস্তকসমূহের সাথেও যার কোন পরিচয় ছিল না।
মোট কথা,যে সকল বৈশিষ্ট্য ইসলামী বিধানে পরিদৃষ্ট হয়েছে তা ছিল মূলত নৈতিক মূল্যবোধ,জীবন যাপন জ্ঞান,মানুষ,তার কর্ম ও সামাজিক সম্পর্ক এবং ইসলামী বিধানে এ মূল্যবোধসমূহ ও ভাবার্থসমূহের যথাযথ রূপদান। এ ভাবার্থ ও মূল্যবোধসমূহ এবং বিধি-বিধানসমূহ,এমনকি যে একে ঐশী বলে বিশ্বাস করে না তার দৃষ্টিতেও মানব জাতির ইতিহাসে যত সভ্যতা ও সামাজিক মূল্যবোধ ও বিধি-বিধানের পরিচয় দেয়া হয়েছে সেগুলোর সকলের চেয়েও সুন্দরতম ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ।
“ গোত্রীয় সমাজের সন্তান দাঁড়িয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের চূড়ায়
বিশ্বমানবতাকে জানায় আহবান সম্প্রীতির ছায়ায়। ”
যে সমাজ আত্মীয়-স্বজন ও বংশ অহমিকা আর সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করত,সে সমাজেরই সন্তান এ মিথ্যা অহমিকা আর বর্ণ বৈষম্যের সূতিকাগারকে ধ্বংস করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বের সকল মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো পরস্পর সমান। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন :
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقاَكُمْ.
“ নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদা- ভীরু। ” (সূরা হুজুরাত : ১৩)
তিনি এ স্লোগানকে বাস্তব রূপ দান করেছিলেন যাতে করে মানুষ শোষণের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে। নারীকে তার মর্যাদার আসনে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং মনুষ্যত্বের মর্যদার ক্ষেত্রে নারীকে পূরুষের মতোই এক আসনে বসিয়ে ছিলেন।
মরুর যে সন্তান শুধু নিজ সমস্যা ও ক্ষুধা নিবারণ ব্যতীত কোন কিছু চিন্তা করতে পারত না,অহংকার বলতে যে শুধু গোত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না সে সন্তানই আত্মপ্রকাশ করেছিল মানব সমাজের বৃহত্তর বোঝা কাঁধে নিতে,বিশ্বের মুক্তিদাতারূপে মানব সমাজের নেতৃত্ব দিতে এবং সারা বিশ্বের অত্যাচারিত জনতাকে কাইজার আর বাদশাহী স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি দিতে। সুদ,ঘুষ আর মজুতদারীতে পরিপূর্ণ এক সমাজ-যার ছিল সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিকে বাধা-বিপত্তি,ঘাটতি ও অপ্রতুলতা সে সমাজেরই এক সন্তান উঠে দাঁড়িয়েছিল সে বাঁধা-বিপত্তিকে দূর করে ঐ ঘাটতি ও অপ্রতুলতাকে পূরণ করতে। এক দারিদ্র্য-নিপীড়িত সমাজকে মানবিক মূল্যবোধের প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করতে এবং আপন ধর্মের বিধানকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারে প্রবেশ করাতে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন ঘুষ,মজুতদারী ও সুদ থেকে ঐ সমাজকে মুক্ত করতে,সম্পদকে ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করতে এবং এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমাজের শক্তি ও সরকার ধনাঢ্য আর সম্পদশালীদের হাতে না থাকে। সর্বোপরি,এক সর্বজনীন দায়িত্বশীলতা ও সামাজিক নিশ্চয়তা বিধানের মূলনীতিসমূহ ঘোষণা করতেই তাঁর উদয় হয়েছিল এ পৃথিবীতে। এগুলো সে সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টা ও গবেষণা শেষে সমাজ বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে।
এ ব্যাপক পরিবর্তন সামাজিক বিকাশ নামে প্রকৃতপক্ষে এক ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানে বাস্তব রূপ লাভ করেছিল।
মোটকথা,ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র দিক হলো পবিত্র কোরআনে পূর্বের শরীয়তসমূহ,নবিগণের ইতিহাস এবং তাঁদের উম্মত ও উম্মতগণের উপর যা কিছু ঘটেছে সেগুলো সম্পর্কে বহু বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। একটি শির্ক কবলিত ও নিরক্ষর পরিবেশ,যেখানে নবী (সা.) ঐ সময়ে বসবাস করতেন তিনিও এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলেন না। এমনকি ইহুদী ও খ্রিষ্টান আলেমগণও অনবরত রাসূল (সা.)-কে বিতর্কে আহবান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁদের ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কথোপকথন করতে চেয়েছিলেন। মুহম্মাদ (সা.) বীরত্বের সাথেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ সকল ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু জানার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও কোরআন থেকে তিনি আহলে কিতাবের আলেমগণ যা জানতে চেয়েছিলেন তার জবাব দিয়েছিলেন।
وَ ماَ كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِّي اِذْ قَضَيْناَ اِلىَ مُوسى الْاَمْرَ وَماَ كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدينَ
“ এবং তুমি ( তুর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে ( নবুওয়াতের) দায়িত্ব অপর্ণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না। ” (সূরা কাসাস : ৪৪)
وَ لَكِنَّا اَنْشَأناَ قُرُوناً فَتَطاَوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
“কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ” (সূরা কাসাস : ৪৫)
وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً في اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياَتِناَ وَ لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
“ তুমি মাদ্য়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রাসূল প্রেরণকারী। ”(সূরা কাসাস : ৪৫)
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطّورِ اِذْ نَادَيْناَ وَ لَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ماَ أتاَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .
“ এবং তুমি তখনও তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা ( মূসাকে) ডাকিয়াছিলাম। বস্তুত এ সবকিছু তোমার প্রভুর নিকট হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। ” (সূরা কাসাস : ৪৬)
অতএব,স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে,কোরআনে বর্ণিত সত্য কাহিনীসমূহ বাইবেলের পুরাতন বিধান (The Old Testament ) এবং নূতন বিধান (The New Testament ) থেকে উদ্ধৃত ও বর্ণিত হতে পারে না,এমনকি যদি মনেও করা হয় যে,পুরাতন ও নূতন বিধানসমূহের বিষয়বস্তু ও চিন্তাসমূহ ইসলামের নবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ উদ্ধৃতি ও বর্ণনাকরণ নেতিবাচক ভূমিকা রাখে অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে দান করে। কিন্তু এ কাহিনীগুলো বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আর যা নূতন ও পুরাতন বিধানসমূহে বর্ণিত হয়েছে তার পরিশুদ্ধি ও ভারসাম্য বিধান করে এবং নবী ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও ইতিহাসসমূহকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জটিলতাসমূহ যা ফেতরাত,তাওহীদ ও ধর্মীয় নির্ভুল প্রমাণসমূহের সাথে কোন প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক রাখে না তা থেকে পরিশুদ্ধ করে।
সাহিত্যমানের দিক থেকে কোরআন চূড়ান্ত বাগ্মিতা ও এক নব ভাষাশৈলী ও অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। এমনকি যারা কোরআনের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস করে না তাদের কাছেও কোরআন উল্লিখিত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বস্তুত কোরআনের বাগ্মিতা ও নব ভাষাশৈলিতা আরবী ভাষার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ(ايام جاهلية ) ও ইসলামী যুগের (ايام جاهلية -এর পরবর্তী যুগ) পার্থক্য নির্দেশক সীমারেখারূপে এবং এ ভাষার সার্বিক বিকাশ ও শাব্দিক রীতিসমূহের মূলনীতিরূপে পরিচিত।
যে সকল আরব নবী (সা.)-এর নিকট থেকে কোরআন শুনেছে তারা অনুধাবন করেছে যে,এ বাক্যসমূহ চূড়ান্ত ভাষাশৈলী ও অভিব্যক্তিতে পূর্ণ এবং তদোবধি যত ভাষা তারা শুনেছে তার যে কোনটির সাথেই অতুলনীয়। আর এ কারণেই তাদের একজন যখন কোরআন শুনেছিল তখন বলেছিল : “ খোদার শপথ,এমন ভাষা শুনলাম যা না কোন মানুষের ভাষা,না কোন জ্বীনের,যে ভাষা মিষ্টি-মধুর প্রাঞ্জল। যার বাহ্যে রয়েছে ফল ও প্রাচুর্য,আর গভীরে রয়েছে সমৃদ্ধি;সবকিছুকেই যা ছাড়িয়ে যায়,কোন কিছুই যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না,যার বাগ্মিতা আর প্রাঞ্জলতার কাছে সকল কথা-সকল ভাষাই ম্লান হয়ে যায়। ” ৯
তৎকালীন আরবরা কোরআন তাদেরকে প্রভাবিত করবে-এ ভয়ে তা শ্রবণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখত। কোরআন শোনার ফলে তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে-তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে-এ ভয়ে তারা কোরআন শোনা থেকে দূরে থাকত। এটা কোরআনের অভিব্যক্তি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি উত্তম প্রমাণ যে,তৎকালীন সময়ে প্রকাশভঙ্গি ও সাহিত্য শৈলীর ক্ষেত্রে কোরআনের সমকক্ষ কিছুই ছিল না। যারাই নবী (সা.)-কে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে আহবান করত তারাই সর্বদা তাঁর বক্তব্য ও যুক্তির কাছে হার মানত। কোরআন ঘোষণা করেছিল,যদি সমস্ত মুশরিক ও ইসলামের শত্রুরা একত্র হয়েও চেষ্টা করে তবু কোরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না। দ্বিতীয়বার ঘোষণা করেছিল,এমনকি দশটি সূরাও আনতে পারবে না এবং তৃতীয়বার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল,এমনকি কোরআনের মতো একটি সূরাও তারা দেখাতে পারবে না। নবী (সা.) এ বিষয়টিকে এক বাকপটু,তার্কিক ও আপন মহিমাগীতিতে পটু সমাজের কাছে (যারা ইসলামের ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারত না) অনবরত ঘোষণা করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও ঐ সমাজ (যেখানে সাহিত্যিক দিক থেকে এতটা বিতর্কের আহবান ছিল) কোরআনের মোকাবিলায় দাঁড়ানোর কোন চেষ্টাই করেনি। কারণ তারা দেখেছিল যে,কোরআনের সাহিত্যিক মান তাদের শাব্দিক,সাহিত্যিক ও কৌশলগত পারঙ্গমতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এটাই সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় যে,যিনি এ কোরআনের বাহক তিনি চল্লিশ বছর আপন গোত্রের মাঝে বসবাস করেছিলেন এবং কোন প্রকার বিতর্ক ও বাকযুদ্ধে কখনই অংশগ্রহণ করেননি। এছাড়া বাকপটুতায়ও তাঁর কোন প্রকার কৃতিত্ব তৎপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি।
এগুলো হলো নবী (সা.) কর্তৃক আনিত রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কয়েকটি।
গ . এ ধাপটি জনপদসমূহের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং তার উপর নির্ভরশীল। খ-তে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বলিত রিসালাতের বিষয়গুলো স্পষ্টতঃই ক-তে বর্ণিত উপাদান ও বিষয়গুলো অপেক্ষা শ্রেয়। ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে আমরা এ ধরনের বহু ঘটনা দেখতে পাই যে,কোন ব্যক্তি আপন সমাজের শীর্ষে আরোহণ করেছে এবং উক্ত সমাজকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোন সমাজের ক্ষেত্রেই বর্ণিত সমাজের মতো এরকম বিপরীত অবস্থা,এরকম প্রতিকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই এক বিস্ময়কর সর্বজনীন অগ্রগতি ও বিকাশ জীবনের সর্বাবস্থায় মূল্যবোধ ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে সঞ্চারিত হয়েছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ছাড়াও উক্ত সমাজকে এক উজ্জ্বলতর এবং উন্নত ও শ্রেয়তর পথে পরিচালিত করেছে। গোত্রীয় সমাজ-ব্যবস্থা নবী (সা.) কর্তৃক বিশ্বাসের পথে এবং এক মানবিক ও বিশ্বজনীন সমাজ গঠনের পথে অগ্রগতি লাভ করেছিল। মূর্তিপূজারী এ সমাজও নির্মল একত্ববাদের পথে পূর্ণতা লাভ করেছিল। উপরন্তু পূর্বের সকল ঐশী ধর্মকে পরিশুদ্ধ করেছিল এবং সকল উদ্ভট গল্প ও কাহিনী ঐ সব ধর্ম থেকে দূরীভূত করেছিল। তাৎপর্য ও মূল্যবোধশূন্য এক সমাজকে তাৎপর্য ও মূল্যবোধে পরিপূর্ণ করেছিল,এমনকি ঐ সমাজকে এমন এক সমাজে রূপান্তরিত করেছিল যে,বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্বের মশাল হস্তে ধারণ করেছিল।
অপরদিকে কোন সমাজের সার্বিক বিকাশ ও বিবর্তন যদি উল্লেখযোগ্য কোন কিছূর প্রভাব থেকে উৎসারিত হয়,তবে তা সূচনাবিহীন ও আকস্মিক হতে পারে না। কারণ একান্তভাবেই এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য সূচনালগ্নের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং নানাবিধ প্রভাব এ পরিবর্তনের পথে ক্রিয়াশীল হয়। এভাবে সর্বদা মানসিক ও চিন্তাগত পূর্ণতা ও প্রকৃষ্টতা লাভ করে এবং পথ প্রদর্শনের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্ব ঐ সমাজ থেকে উদ্ভাবিত হয় যাতে করে সঠিক উন্নতির পথে ঐ সমাজ যাত্রা শুরু করতে পারে।
বিভিন্ন সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির কারণসমূহের উপর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখা যায় যে,প্রথমে কোন সমাজে ছড়ানো-ছিটানো বীজের মতো বিভিন্ন চিন্তাগত উৎকর্ষ সূচিত হয়েছিল। অতঃপর এ বীজগুলো পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছিল এবং চিন্তামূলক এক তরঙ্গমালার আকৃতি ধারণ করেছিল।
এভাবে পর্যায়ক্রমে এ তরঙ্গের প্রভাবসমূহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ফলে ঐ সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্ব পরিপক্বতা লাভ করেছিল। তখন সমাজের বিভিন্ন আংশিক পর্যায়ে এ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সাথে বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছিল। পুরাতন ও নূতনের এ সংঘর্ষের মাধ্যমে চিন্তামূলক তরঙ্গধারা সমাজের বিভিন্ন ধাপে ছড়িয়ে পড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।
অপরদিকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘটনাগুলো ছিল এর ব্যতিক্রম। এ শিকলের কোন বলয়ই মুহাম্মদ (সা.)-এর নব রিসালাতের ইতিহাসে বিরাজমান ছিল না এবং এ চিন্তামূলক তরঙ্গের সাথে এর কোন সাদৃশ্যও ছিল না। নবী (সা.) কর্তৃক ঘোষিত এ ধরনের চিন্তা,মূল্যবোধ ও ভাবার্থের কোন বীজই তাঁর সামাজিক পরিমণ্ডলে বপন করা ছিল না। যে জোয়ার নবী (সা.)-এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল এবং যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিশেষত্ব ছিল,প্রকৃতপক্ষে তা কেবল এ নব রিসালাত ও ইসলামের নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ এমনটি ছিল না যে,বিশ্বনবী উক্ত চিন্তামূলক জোয়ার-তরঙ্গে রিসালাত অর্জিত হয়েছিল এবং তখন নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। এদিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে,মহানবী (সা.)-এর অর্জিত বিষয়সমূহ এবং বর্ণিত সংস্কারকগণের অর্জিত বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য নব তরঙ্গে বিদ্যমান বিন্দুসমূহের পার্থক্যের মতো ছিল না,বরং এ পার্থক্য ছিল মৌলিক এবং অবর্ণনীয়। আর এটাই প্রমাণ করে যে,মুহাম্মদ (সা.) কোন তরঙ্গের অংশ ছিলেন না,বরং উক্ত (চিন্তামূলক ) তরঙ্গ ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর রিসালাতের অংশ।
ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে,কোন নব বিপ্লবে সামাজিক,আদর্শিক এবং চিন্তামূলক নেতৃত্ব যখন কোন নির্দিষ্ট চিন্তামূলক ও সামাজিক বিকাশের মধ্যে একক কেন্দ্রবিন্দুর পরিপার্শ্বে কেন্দ্রীভূত হয় তখন ঐ কেন্দ্রবিন্দু হয় এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বেরই নেতৃত্ব। অনুরূপ তার ক্রমাগত অগ্রগতিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে তা পরিপক্বতা লাভ করে এবং তাকে ঐ অগ্রগতির ধারায় উক্ত তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়।
কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনার ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে। স্বয়ং নবী (সা.) আদর্শিক,চিন্তামূলক এবং সামাজিক নেতৃত্বকে হাতে তুলে নিয়েছেন যেখানে তিনি তাঁর জীবনেতিহাসে একজন উম্মী মানুষ (যিনি লেখা পড়া শিখেননি) হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি না কোন সমসাময়িক সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতেন,না কোন অতীত ধর্ম সম্পর্কে। আর এ নেতৃত্ব হাতে নেয়ার পূর্বে পরিবেশে কোন ভূমিকারই উপস্থিতি ছিল না (অর্থাৎ ঐ সমাজের কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না)।
ঘ . উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বিচার-বিশ্লেষণের শেষ ধাপে উপনীত হব। এখানেই আমরা এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা বিশ্লেষণের জন্য শুধু একটি সংশ্লিষ্ট নির্বাহীর (عامل ) ধারণা পেতে পারি যা উক্ত ঘটনা ও বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আর তা হলো নবুওয়াতের ধারণা যা পার্থিব বিষয়ের উপর ঐশী প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রদান করে।
وَكَذَلِكَ اَوْحَيْناَ اِلَيْكَ رُوحاً مِنْ اَمْرِناَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَ اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
“ এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশ- বাণী ওহী করিয়াছি। তুমি জানিতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমরা ইহাকে ( বাণীকে) আলোকস্বরূপ করিয়াছি যদ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহি হেদায়েত দিই এবং নিশ্চয় তুমি ( লোকদিগকে) সরল সুদৃঢ় পথেপরিচালিত করিতেছ। ” (সূরা শুরা : ৫২)
অপর কার্যকর নির্বাহীসমূহের ভূমিকা :
উপরিউক্ত আলোচনার অর্থ এটা নয় যে,আমরা অন্যান্য নির্বাহী ও কার্যকর কারণসমূহকে অগ্রাহ্য করে রিসালাতকে শুধু ওহী ও ঐশী সাহায্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করব এবং এ নির্বাহী ও কার্যকর নিয়ামকসমূহ,যেমন স্থান-কাল-পাত্রের ইতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করব,বরং প্রকৃতপক্ষে এদের প্রভাব বিশ্বের নিয়ম-ব্যবস্থায় এবং সাধারণ সমাজের নিয়মে বিদ্যমান যদিও এ প্রভাব শুধু ঘটনাক্রম এবং যথাস্থানে রিসালাত প্রকাশিত হওয়ার জন্য সাহায্য করে অথবা বিরত রাখে। অতএব,রিসালাত এর বিষয়বস্তুর মতোই প্রকৃতপক্ষে ঐশী। অর্থাৎ তা বস্তুগত শর্তাবলীর ঊর্ধ্বে। কিন্তু তা ঘটনা প্রবাহের পরিবর্তন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরির্বতনের পথে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে অবতীর্ণ হয়েছে।
অতএব,কথিত আছে যে,যখন আরবের লোকরা নিজেদের তৈরিকৃত প্রতিমাসমূহকে অথবা তার মতো বৃহত্তর কোন প্রস্তর খণ্ডকে পূজা করত এবং ক্রোধ ও রাগের সময় তারা সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলত অথবা মিষ্টি বস্তুর তৈরি খোদাকে ক্ষুধার সময় খেয়ে ফেলত তখন এ নূতন রিসালাতের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল।
অথবা কথিত আছে যে,হতভাগ্য আরব সমাজ যা অত্যাচার,বিচ্যুতি,সুদ ও মুনাফাখোরে পরিপূর্ণ ছিল,এ নব আন্দোলনের বানে তা দূরীভূত হয়েছিল এবং ন্যায়পরায়ণতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ও একটি সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথবা বলা হয়ে থাকে যে,গোত্রীয় প্রভাব এ রিসালাত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল-হোক তা স্থানীয় প্রভাব,যেমন কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বিরোধীদের মোকাবিলায় নবী (সা.)-এর বংশীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি অথবা হোক তা গোত্রীয় প্রভাব,যেমন দক্ষিণ আরবের মোকাবিলায় উত্তর আরবের গোত্র প্রভাব।
অথবা বলা হয়ে থাকে যে,তদানিন্তন সময়ের পৃথিবীর অবস্থা এ রিসালাতের বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল। তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বিরাজমান ছিল। ফলে পারস্য ও রোমান সাম্রাজের প্রভাব আরব উপদ্বীপে এ রিসালাতের প্রাতিষ্ঠায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।
এ ধরনের বক্তব্য বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কখনো কখনো গ্রহণযোগ্যও বটে। তবে এটা শুধু ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে,কিন্তু স্বয়ং রিসালাতকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
রিসালাত
ইসলামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্য
ফাতুয়াতুল ওয়াযিহাত
যে রিসালাত জগতের জন্য রহমতস্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো ইসলাম।
প্রকৃতপক্ষে ইসলামে সর্বাগ্রে প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ক ও তার পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
অতএব,প্রথমত একক ও সত্যপ্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ক (যিনি মানুষকে সহজাত প্রকৃতি দান করেছেন) এবং প্রভুর একত্বের উপর কঠোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ ইসলামের সকল কিছু তাওহীদের বাণীلااله الا الله ( আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই) এ মূল নীতিবাক্যের উপর নির্ভর করে গঠিত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত পুনরুত্থানের সাথে মানুষের সম্পর্ক। কারণ এর মাধ্যমে পরাক্রমশালী একক প্রভু পার্থিব অসামঞ্জস্যগুলোকে১০ দূর করেন এবং তাঁর ন্যায়বিচার বাস্তব রূপ লাভ করে।
ইসলামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যঃ
ইসলামের রিসালাত এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই অন্যান্য ঐশী রিসালাত হতে স্বতন্ত্র। কারণ তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ঐকান্তিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই।
নিম্নে এ সকল বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :
১. এ রিসালাত কোরআনের অকাট্য ভাষ্যসম্বলিত,পবিত্র ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান এবং কোন প্রকার ত্রুটি,ভ্রম এতে প্রবেশ করতে পারেনি। অপরদিকে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ ক্রটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং আপন সত্য বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন :
اِناَّ نَحْنُ نَزَّلنْاَ الْذِّكْرَ وَ اِناَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ .
“ নিশ্চয় আমরাই এ কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই উহার রক্ষাকারী। ” (সূরা হিজর : ৯)
যেহেতু ইসলামের রিসালাত তার বিশ্বাসগত ও বিধানগত বিষয়বস্তু থেকে বিস্মৃত হয়নি সেহেতু তা প্রশিক্ষণ ও (আধ্যাত্মিক) পরিচর্যার ক্ষেত্রে আপন ভূমিকাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। কারণ যে রিসালাত আপন বিষয়বস্তু থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতির মাধ্যমে দূরে সরে যায় তা খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা হারায়। কারণ এ সম্পর্ক শুধু নামকরণের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়,বরং প্রকৃতপক্ষে রিসালাতের মূল বিষয়বস্তুর প্রতিফলন এবং চিন্তা পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে তার রূপদানের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এ দিক থেকে ইসলামের রিসালাতের সঠিকতা ও নির্ভুলতা কোরআনের বিষয়বস্তুর নির্ভুলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যাতে করে আপন উদ্দেশ্য ও মতবাদকে প্রতিপাদন করতে পারে।
২. কোরআনের রুহ (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত) অবিকৃত থাকায় তা কোরআনের ঐশ্বরিকতা প্রমাণের জন্য উত্তম হাতিয়ার। কারণ কোরআন এবং তা হতে উদ্বৃত বিধানসমূহ ও রিসালাতের বিষয়বস্তু হলো পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসারে মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাত ও নবুওয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আরোহ যুক্তি। যদবধি কোরআন থাকবে তদোবধি এ দলিলও থাকবে,যা অন্যান্য নবুওয়াত ও রিসালাতের ব্যতিক্রম,যার প্রমাণ স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ও বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং যা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। যেমন অন্ধকে আলো দান এবং কুষ্ঠ রোগীকে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তিদান। কারণ এ ঘটনাগুলো শুধু সমসাময়িক কালের মানুষই উপলব্ধি ও অবলোকন করেছিল এবং সময় ও কালের ধারায় তা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল,এমনকি স্বয়ং ঐ ঘটনাগুলোও হারিয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণেই মানুষ এ সকল ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে এবং তার তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ করতে অপারগ। যে সকল নবুওয়াত ও রিসালাতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব মহান আল্লাহ সে সকল রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও ঐগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য কোন দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেননি। কারণ :
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً اِلاّ مَا آتاَهاَ
“ মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন নাই,একমাত্র তাহা ব্যতীত যাহা তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে। ”
কিন্তু এখন আমরা পূর্বের নবী-রাসূলগণের প্রতি এবং তাঁদের মু ’ জেযার প্রতি কোরআনের তথ্য ও সংবাদ অনুসারে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।
৩. ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে,কালের প্রবাহে ইসলামের রিসালাতের মৌলিক যুক্তির তো কোন প্রকার ঘাটতি হয়ইনি,বরং তা মানব সভ্যতার বিবর্তন ও বিকাশের ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে এ মৌলিক যুক্তিকে এক নবসংযোগ প্রদান করেছে। শুধু তা-ই নয়,কোরআন স্বয়ং এ সমস্ত বিষয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এ যুক্তিসমূহকে ও পার্থিব বিভিন্ন ঘটনাকে প্রজ্ঞাবান প্রভুর সাথে সম্পর্কিত করেছে এবং মানুষকে এ রহস্য সম্পর্কে অবগত করেছে। এমনকি মানুষ এমন অনেক বিষয় সম্পর্কে আজ জানতে পেরেছে যা শত শত বছর পূর্বেই এ কোরআনে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের একজন উম্মী ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আজনিয়ারী(اجنيري ) নামক আরবী ভাষার এক অধ্যাপক বলেছিলেন:
“ প্রকৃতপক্ষে ফুল-ফলের পরাগায়ণে বাতাসের ভূমিকা সম্পর্কে উটের মালিকেরা (আরবরা) ইউরোপে এর আবিষ্কারের বহু পূর্বেই জানতে পেরেছিল। ” ১১
৪. এ রিসালাত জীবনের প্রতিটি স্তরের সাথে সমন্বিত। আর এর ভিত্তিতে জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে-একীভূত করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একসূত্রে-সম্পর্ক স্থাপন করেছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে।
৫. প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আনয়নকৃত এ রিসালাতই একমাত্র ঐশী রিসালাত যা মানব জীবনে প্রয়োগ ক্ষেত্রে এক বিরাট সফলতা লাভ করেছে। সর্বোপরি,এ রিসালাত মানব জীবনের বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করেছে।
৬. এ রিসালাত তার প্রায়োগিক পর্যায়ে এসে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। কারণ এর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এক সমাজ যারা গ্রহণ করেছে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। এ রিসালাত এক ঐশী রিসালাত যা পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছে এবং যা সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে অদৃশ্য অজড় জগতের সাথে যা অলৌকিক ও ধারণাতীত।
আর এ ক্ষেত্রেই আমরা ভুল করি। আমরা শুধু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করি অথবা শুধু বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা ইতিহাসকে বিচার করি। যার ফলে এ
বস্তুগত বোধ মানুষের সাথে ঐশী বিষয়কে সম্পর্কিত করতে পারে না। অনুরূপ পারে না এ রিসালাতকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে। যেমন এ রিসালাত ঐশী হওয়ার সত্যতা অনুধাবন করতে বা এর ইতিহাস বুঝতে অপারগতা প্রকাশ করে।
৭. এ রিসালাত তার কার্যকারিতাকে শুধু এক বিশেষ সমাজের জন্য সীমাবদ্ধ করেনি,বরং অন্যান্য সমাজেও তার বিস্তৃতি রয়েছে। এর প্রভাব পরিব্যপ্ত করেছে সাড়া বিশ্বজগতকে-সকল যুগকে। এমনকি ইউরোপীয় মনীষীরাও এর প্রভাবের অধীন। যার ফলে অধুনা ইউরোপীয় মনীষিগণ স্বীকার করেছেন যে,ইসলাম তার যাত্রাপথে ঘুমন্ত ইউরোপকে জগ্রত করেছে এবং এক নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।
৮. প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) যিনি এ রিসালাতের বাহক,পূর্ববর্তী সকল নবীর মতোই ঐশী সম্পর্কের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যে পদ্ধতিতে তিনি তাঁর রিসালাত বা ধর্মবাণী প্রচার করেছেন সে দিক থেকে এটা স্বতন্ত্র। এটা এ কারণে যে,তাঁর আনয়নকৃত রিসালাতই হচ্ছে সর্বশেষ রিসালাত। আর এ কারণেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে,তিনিই সর্বশেষ নবী। নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির পশ্চাতে দু ’ টি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত না-বোধক তাৎপর্য-যার মাধ্যমে অন্য কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত হ্যাঁ-বোধক তাৎপর্য-যার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত এ নবুওয়াতের স্থায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।
নবুওয়াতের সমাপ্তির না-বোধক তাৎপর্যের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে,ইসলামের প্রবর্তনের চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এর তাৎপর্য বাস্তবের সাথে সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যতদিন সময়ের গতি অব্যাহত থাকবে ইসলামের এ বৈশিষ্ট্যও অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ অন্য কোন নবুওয়াতের আবির্ভাব না ঘটলেও মানব সভ্যতায় মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের মৌলিক ভূমিকার কোন অপনোদন ঘটবে না। কারণ শেষ নবুওয়াত পূর্ববর্তী নবুওয়াতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী রিসালাতসমূহের সকল মূল্যবোধকে ধারণ করেছে এবং ক্ষণস্থায়ী ও অস্থায়ী মূল্যবোধসমূহকে দূরে রেখেছে। এভাবে এ রিসালাত তার গতিশীলতায় সকল প্রকার বিবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরী।
وَاَنْزَلْناَ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ
“ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি সত্যগ্রন্থ, যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং ঐগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। ” (সূরা ময়েদাহ্ : ৪৮)
৯. প্রভুর যে প্রজ্ঞার কারণে ইসলামের রিসালাতের সাথে সাথে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটে সে প্রজ্ঞাই নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তিতে উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সৃষ্টিকর্তা কতৃর্ক কাউকে নির্বাচনেরও দাবি করে। আর এ প্রতিনিধিগণই হলেন বারো জন ইমাম,যাঁদের সংখ্যা প্রত্যক্ষ প্রমাণসহকারে সঠিক হাদীসসমূহে নবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর সত্যতা ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।
এ ইমামগণের প্রথম হলেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। তারপর ইমাম হাসান (আ.),তারপর ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তারপর তাঁর (হুসাইন) সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়জন ইমাম। তাঁদের নাম যথাক্রমে আলী ইবনিল হুসাইন আস্ সাজ্জাদ (আ.),মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকির (আ.),জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস্ সাদিক (আ.),মূসা ইবনে জাফর আল কাযেম (আ.),আলী ইবনে মূসা আর-রেযা (আ.),মুহাম্মদ ইবনে আলী আল জাওয়াদ (আ.),আলী ইবনে মুহাম্মদ আল হাদী (আ.),হাসান ইবনে আলী আল আসকারী (আ.) এবং সর্বশেষে মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আল মাহ্দী (আ.)।
১০. সর্বশেষ ইমামের অনুপস্থিতিতে (গাইবাত) ইসলাম ফকীহ্গণের হাতে মানুষের দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং ইজতিহাদের (অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ উদ্ধৃত করার জন্য গভীর অনুসন্ধান করা) দ্বারকে খুলে দিয়েছে।
ফাতুয়াতুল ওয়াযিহাত
‘ ফাতুয়াতুল ওয়াযিহাত ’ সেই ইসলামী বিধানের একটি গবেষণামূলক বক্তব্য যে ইসলামী বিধান সর্বশেষ নবীর (সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক তাঁর এবং তাঁর পবিত্র বংশধরগণের উপর) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।
যখন এ পুস্তিকার শেষ চরণগুলো লিখছিলাম তখন এক নিদারুণ বেদনা ও শ্বাসরুদ্ধকর কষ্ট আমাদের হৃদয়ের নিভৃতে অবস্থান করছিল। কারণ এমন একটি সময়ে অবস্থান করছিলাম যখন ইসলামের বীর সন্তান,অমর শহীদ ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণ হৃদয়ে বিরাজমান যিনি এমনই এক সময়ে আল্লাহ,রাসূল ও তাঁর রিসালাতের পথে দৃঢ় ও অনড় থাকার জন্য স্বীয় অমূল্য শোণিত উৎসর্গ করেছিলেন। এ রিসালাতকে অটুট রাখার জন্যই নিজেকে এবং স্বীয় অতুলনীয় নির্ভীক সঙ্গীদেরকে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। সর্বকালে ও সর্বস্থলে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা ও বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতাকে সাহায্য করার জন্য এবং অত্যাচারীর হস্ত গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কিছু সন্তান ও সাহাবীকেও জালিমের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আপামর মুসলিম জনতার অস্তিত্বে বিদ্যমান যে প্রত্যয় ও অনুভূতিকে স্বৈরাচারীরা নিস্তব্ধ ও স্থবির করে দিতে চেয়েছিল শহীদের পিতা ইমাম হুসাইন (আ.) আপন শোণিতপ্রবাহ দিয়ে তাকে গতিশীল করেছিলেন;আর সে সাথে এ শোকাবহ ঘটনাপ্রবাহে তাঁর দৃঢ়তা ও রুধীর ধারায় মুসলিম জনতার অন্তরাত্মায় সংযোজন করেছিলেন এক মহান অনুভূতি।
সুতরাং,হে আমার মহান নেতা! হে আবা আবদাল্লাহ্! এ পুস্তিকার সকল ছওয়াব তোমাকেই উৎসর্গ করলাম। তোমার পবিত্র রক্তের লোহিত ধারায় বেঁচে থাকুক এ সকল দৃঢ় চিন্তা ও চেতনা। তোমার প্রতিবাদধ্বনি ও শহীদের রক্তধারায় এবং তোমার ও তোমার পবিত্র সন্তানগণের রক্তের বিনিময়েই ইতিহাসের পাতা সিক্ত করে নির্ভেজাল রিসালাতের সুগন্ধ আমাদের নিকট পৌঁছেছিল।
তথ্যসূত্র
১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের প্রবক্তাগণ তাঁদের দেয়া সূত্রে “ প্রতিটি ” বা ‘ যে সকল ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন যা সর্বজনীনতাকে তুলে ধরে। কিন্তু তাঁদের ভাষ্যকে সত্য ধরতে হলে তাঁদের এ উক্তির সর্বজনীনতা থাকে না। কারণ সর্বজনীনতাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না।
২। যুক্তি প্রদর্শনের ‘ পদ্ধতি ’ যুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু। যেমন মনীষিগণের বর্ণনা থেকে আমরা যুক্তি প্রদর্শন করি যে,সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর। এখানে যে,পদ্ধতিতে আমরা যুক্তি উপস্থাপন করেছি তা হলো মনীষীদের মতবাদের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি। কখনোবা স্বপ্ন দেখা থেকে যুক্তি প্রদর্শন করব যে,ঐ ব্যক্তি মারা যাবে। দেখা গেল যে,লোকটি মারা গেছে। এখানে পদ্ধতিটি হলো স্বপ্নকে সত্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তি বলে মনে করা। আবার কখনোবা যুক্তি প্রদর্শন করি যে,পৃথিবী ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু ’ টি বৃহত্তম চৌম্বক মেরুতে বিভক্ত এবং দিকদর্শন যন্ত্রের চৌম্বক সূচকটি সর্বদা উত্তর মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানে অনুসৃত পদ্ধতিটি হলো ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা পদ্ধতি। তবে প্রতিটি যুক্তির সঠিকত্ব নির্ভরশীল পদ্ধতির সঠিকত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।
৩. ‘ কল্পনা ’ এখানে পরিভাষাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. সমকোণের অভিলম্বের উপর অবস্থিত বিন্দু।
৫. এখানে দু ’ টি বিষয় রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন :-
ক. ‘ বিকল্প ’ বা ‘ বাদিল ’ -যা প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় এবং যা আরোহ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে তা এ অর্থে যে,জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির নিমিত্তে প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুসমূহ বা বহির্জগতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান তা অনৈচ্ছিক বা অবচেতনভাবেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক,অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক বৈপরীত্য এবং সত্তাগত ও প্রকৃতিগত কর্তৃত্বই হলো এ সকল ঘটনার কারণ ও উৎস।
আরোহ যুক্তি পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণার ‘ বিকল্প ’ -এর (بديل ) ’ উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ আরোহ যুক্তি পদ্ধতি প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার
অস্তিত্বের ধারণা ছাড়া আর কিছুই প্রদর্শন করে না,যেখানে ‘ বিকল্প ’ যা বস্তুর অনৈচ্ছিক বা অবচেতন ক্রিয়াকলাপের ফল-স্বয়ং অনেকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা,অলোচনার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। এ কারণে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার ‘ বিকল্প ’ অনেক বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অতএব,এর প্রতি জোড়া পরস্পরকে অকার্যকর ও বিনাশ করে। আর এ অকার্যকর করা তখনই সঠিক হতে পারে যখন প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা অধিকাংশ বিষয় বা ঘটনার রক্ষাকারী ও ধারণকারী হিসাবে না থাকবেন। (কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত। কারণ প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণার মাধ্যমে বিশ্বের সকল ঘটনা বা বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়।) অতএব,ঘটনার সংখ্যা অনুসারে অনুরূপ সংখ্যক জ্ঞান ও শক্তির উপর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে দেখতে পাব যে,যত সংখ্যক পরিমাণ জ্ঞান ও মূল্যমান এ কল্পনাটিকে (সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান) প্রমাণ করে তা যা প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার ‘ বিকল্প ’ (অর্থাৎ বস্তুর অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ফল) তার সমান । সুতরাং একটির উপর অপরটির প্রাধান্য কিরূপে পরি গণিত হবে?
এ প্রশ্নের উত্তর হলো,এ প্রাধান্য বস্তুর অবচেতনতা,অবিন্যস্ততা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন,স্বতন্ত্র ও বিযুক্ত ঘটনার জন্য অন্য কোন ঘটনার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং এ বিষয়টি সম্ভাবনার হিসাবে একটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে পরিগণিত হয়।
কিন্তু যে জ্ঞান ও মূল্যমান প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বাঞ্ছিত সেগুলো (ঘটনা বা বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের আলোচনার বিষয়) একে অপর থেকে পৃথক নয়। কারণ প্রতিটি ঘটনা সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে এমন এক জ্ঞান ও শক্তিকে চায় যা স্বয়ং অপর এক জ্ঞান ও শক্তিকে যাঞ্ছা করে। অতএব,পৃথকভাবে এ শক্তি ও জ্ঞানের কোন অংশকে ধারণা করা সঠিক নয়;বরং এক বৃহদাকারে মাধ্যমিকতা ও সম্পর্ককে যাঞ্ছা করে এবং এ শর্ত হলো সম্ভাবনাভিত্তিক। অর্থাৎ এ শক্তি ও জ্ঞানের সমষ্টির প্রতিটিই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের মধ্যকার সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট।
যখন সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে এ জ্ঞান ও শক্তিকে জড় বস্তুসমূহ থেকে অর্জিত ফলাফলের সাথে মূল্যায়ন করতে চাই,তখন আমরা সম্ভাবনাভিত্তিক নির্ধারিত হিসাব বিজ্ঞানের ‘ সম্ভাবনার গুণ ’ পদ্ধতির অনুসরণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ একটি সমষ্টির প্রতিটি এককের সম্ভাবনার মূল্যমানকে অপর সমষ্টির মূল্যমান দিয়ে গুণ করব এবং এভাবে একটি তালিকার প্রতিটি বিষয়কে অপর তালিকার প্রতিটি বিষয়ের সাথে তুলনা ও মূল্যায়ন করব। তবে এ কর্মের ফলে একটি তালিকার প্রতিটি প্রকার অপর তালিকার অনুরূপ প্রকারসমূহকে নিস্ক্রিয় বা অকার্যকর করবে এবং গুণের মান যত কম হবে,অকার্যকর বা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা তত কম হবে। শর্তযুক্ত সম্ভাবনা এবং শর্তহীন সম্ভাবনার হিসাবে গুণের পদ্ধতি গণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রামাণ করে যে,শর্তযুক্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিটি সদস্যের মূল্যমান অপর সদস্যের মূল্যমানের সাথে গুণ হবে এ হিসাবে যেন এটা প্রথম তালিকারই সদস্য এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুড়ান্ত বা চুড়ান্তের কাছাকাছি। এছাড়া এ গুণ প্রক্রিয়া ঐ সদস্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অথবা ক্ষীণ মাত্রায় হ্রাস করে না। কিন্তু শর্তহীন সম্ভাবনা এর বিপরীত। এ ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রতিটিই অন্যের সম্ভাবনার বিপরীতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হিসাবে পরিলক্ষিত হয় এবং গুণ প্রক্রিয়া এখানে মূল্যমানসমূহের মধ্যে বড় রকমের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এভাবেই একটি কল্পনার উপর অপরটির প্রাধান্য সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয়।
খ. ‘ পূর্বসম্ভাবনা ’ -এর সংজ্ঞা আরোহ পদ্ধতিতে সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ব্যাখ্যা দেয়ার নিমিত্তে ‘ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণে আরোহ পদ্ধতি ’ এবং পূর্বল্লোখিত ‘ চিঠিটি তার ভাইয়ের ’ এ দু ’ য়ের মধ্যে একটি তুলনা দাঁড় করাবো। ঐ ব্যক্তি চিঠিটি পড়ার পূর্বেই এ আশংসা করে যে,তা তার ভাই কর্তৃক প্রেরিত। আর এই যে পড়ার পূর্বেই যে আশংসা একে আমরা ‘ পূর্ব সম্ভাবনা ’ নামকরণ করেছি। যেমন ঐ ব্যক্তি চিঠিটি খোলার পূর্বে ৫০% আশংসিত হয় যে,চিঠিটি ভাই কর্তৃক প্রেরিত এবং চিঠি পড়ার পর ও আরোহ পদ্ধতির পাঁচটি ধাপ (পূর্বোল্লিখিত) অতিক্রম ও বিচার-বিশ্লেষণ করার পর বিশ্বাস স্থাপন করে যে,তার ধারণা সঠিক।
কিন্তু পূর্বেই যদি এ ধারণা (সম্ভাবনা) করে যে,চিঠিটি তার ভাই কর্তৃক প্রেরিত নয় (যেমন বেশিরভাগ আশংকা করে যে,তার ভাই মারা গিয়েছে) তবে,একমাত্র তুলনা,বিচার-বিশ্লেষণ ও আরোহ পদ্ধতির পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করার পর ও জোরালো নিদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে,চিঠিটি ভাই কর্তৃক প্রেরিত। অতএব,কিভাবে আমরা ‘ পূর্ব সম্ভাবনা ’ -এর অনুমান থেকে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?
প্রকৃতপক্ষে পবিত্র সৃষ্টিকর্তা সম্ভাব্য বিষয় নয়,বরং ফেতরাতগত বিবেক প্রসূতভাবে গুরুত্বারোপিত ও সুনিশ্চিত বিষয়। কিন্তু যদি মনে করি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব একটি সম্ভাব্য বিষয় এবং আরোহ যুক্তি পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁকে প্রমাণ করতে চাই,তবে ‘ পূর্ব সম্ভাবনা ’ কে আমরা নিম্নরূপে মূল্যায়ন করতে পারি :
আমরা প্রথমে একটি বস্তুকে আলোচনার বিষয়রূপে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করব এবং দেখতে পাব ঐ বস্তুর উপর দু ’ টি সম্ভাবনা রয়েছে। উভয় সম্ভবনার মাধ্যমেই আমরা বস্তুটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রথমটি হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণা এবং দ্বিতীয়টি হলো ‘ বস্তুর আবশ্যকীয় জড়তার ’ ধারণা। এ অবস্থায় একটির উপর অপরটিকে প্রাধন্য দেয়ার মতো কোন ব্যাখ্যাই আমাদের কাছে নেই। অতএব,আমাদের ১০০% নিশ্চয়তাকে প্রতিটি সম্ভাবনার জন্য সমান দু ’ ভাগে ভাগ করব। অর্থাৎ স্বীকার করে নেব যে,প্রতিটি ৫০% নিশ্চিত বা সঠিক। কিন্তু যেহেতু ‘ প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের'বিষয়ে সম্ভাবনাটি শর্তযুক্ত এবং ‘ বস্তুর আবশ্যকীয় জড়তার ’ বিষয়ে সম্ভাবনাটি শর্তহীন ও স্বাধীন সেহেতু গুণ করার সময় সর্বদা শেষোক্তটি দুর্বল ও অকার্যকারিতার দিকে ধাবিত হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি (বস্তুর আবশ্যকীয় জড়তার ধারণা) সর্বদা নিম্নক্রম এবং প্রথম সম্ভাবনাটি (সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বের ধারণা) সর্বদা ঊর্ধ্বক্রমে যেতে থাকবে।
অতএব,গবেষণা ও নিরলস প্রচেষ্টার পর আমরা পেলাম যে,সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে আরোহ যুক্তি পদ্ধতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের (যেমন রাসেল) কাছে নিগৃহীত হওয়ার কারণ হলো উল্লিখিত দু ’ টি বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের অপারগতা। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য এবং আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার জন্য মৌলিক আরোহ যুক্তিবিদ্যার দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে।)
৬. বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞাত বিষয় হলো সেগুলো যেগুলোকে প্রমাণ করার জন্য ইন্দ্রিয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই।
৭। সৃষ্টিশীল (حادث ) -এর পরিভাষাগত অর্থ হল যার সূচনা কাল আছে। অর্থাৎ এমন একসময় ছিল যে,তা ছিল না। অন্য ভাবে বলা যায় বস্তু সম্ভাব্য অবস্থায় ছিল এবং এক অস্তিত্বদানকারী কারণের (علّة الوجودي ) ফলে তা বিশেষ সম্ভাব্য (امكان خاص অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব তার জন্যে সমান ) অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে অস্তিত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে । যা এ বস্তুটিকে “ সম্ভাব্য অবস্থা ” থেকে “ অস্তিত্বে ” এনেছে,তাকে অস্তিত্বদানকারী কারণ (علّة الوجودي ) বলে। এবং যে বস্তুটি সম্ভাবনার পর ‘ হওয়া ’ অবস্থায় পৌঁছেছে তাকে সৃষ্ট বস্তু (شيء حادث ) নামকরণ করা হয়েছে।
৮. কারণ এখানে বিবর্তন পরিমাণগত নয়,বরং গুণগত।
৯.কথিত আছে যে,এ উক্তিটি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আসবাবে নুযূল : ২৯৫,সূরা মুদ্দাস্সির এবং এ ’ লামুল ওয়ারা,১ : ১১০-১১২ দ্রষ্টব্য।
১০. পুণ্যবান ব্যক্তি সারা জীবন কষ্ট করে। অত্যাচারী মহা অনন্দে দিন যাপন করে। এক ব্যাক্তি পাঁচটি খুন করে,কিন্তু একটি খুনের সাজা (অর্থাৎ একবার মৃত্যুদণ্ড) ছাড়া বাকীগুলোর বিচার করা যায় না।
১১. এটা মহান আল্লাহর সে বাণীকেই উদ্ধৃত করে যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন و ارسلنا الرياح لواقح এবং আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি।
সূচীপত্র
প্রেরক ১১
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ১২
বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণঃ. ২১
আরোহ পদ্ধতিকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে কিরূপে প্রয়োগ করব? ৩৪
দার্শনিক যুক্তি. ৪১
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তির একটি নমুনা ৪৪
দার্শনিক যুক্তির সম্মুখে বস্তুবাদের অবস্থানঃ. ৫০
মহান আল্লাহর গুণসমূহ ৫৬
ন্যায়পরায়ণতা. ৫৬
মহান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা প্রতিদানের প্রমাণবহ ৫৮
প্রেরিত ৬০
নবুওয়াতের সাধারণ আলোচনা ৬১
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রমাণঃ. ৬৫
অপর কার্যকর নির্বাহীসমূহের ভূমিকা. ৭৯
রিসালাত ৮১
ইসলামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যঃ. ৮৩
ফাতুয়াতুল ওয়াযিহাত ৮৮
তথ্যসূত্র ৮৯