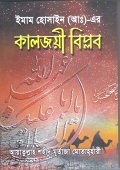ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কালজয়ী বিপ্লব
3য় খণ্ড
মূল : আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী
সংকলনে: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

শিরোনামঃ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কালজয়ী বিপ্লব
মূলঃ শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
সংকলেনঃ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
তত্ত্বাবধানঃ মোহাম্মদ আওরায়ী কারিমী
কালচারাল কাউন্সেলর,ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস-ঢাকা,বাংলাদেশ
প্রকাশনাঃ কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস-ঢাকা প্রকাশকাল : দ্বিতীয় মুদ্রণ (সংযোজিত অংশসহ),ডিসেম্বরর 08,মহররম 1431হিঃ,পৌষ 1416 বঃ
সংখ্যা : 2000
Title: Imam Hossain (A.) Er Kaljoie Biplob
Writer: Ayatullah Shahid Murtaza Motahhari
Translator: Abdul Quddus Badsha
Supervisor: Mohammad Oraei Karimi
Cultural Counsellor
Embassy of the I.R.of Iran-Dhaka
Publication Date: 2nd Edition (with addition),
December 2008
Circulation: 2000
ভূমিকা
বিসিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন,‘‘ যদি মুহাম্মাদ (সা) এর ধর্ম আমার নিহত হওয়া ছাড়া টিকে না থাকে তাহলে,এসো হে তরবারী! নাও আমাকে।’’ নিঃসন্দেহে কারবালার মর্ম বিদারী ঘটনা হলো মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। এটা এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা,যার সামনে বিশ্বের মহান চিন্তাবিদরা থমকে দাড়াতে বাধ্য হয়েছেন,পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে স্তুতি-বন্দনায় মুখিরত হয়েছেন এই নজিরবিহীন আত্মত্যাগের। কারণ,কারবালার কালজয়ী বিপ্লবের মহানায়করা‘‘ অপমান আমাদের সয়না” -এই স্লোগান ধ্বনিত করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যায় হাতে গোনা জনাকয়েকটি হওয়া সত্ত্বেও খোদায়ী প্রেম ও শৌর্যে পূর্ণ টগবেগ অন্তর নিয়ে জিহাদ ও শাহাদাতের ময়দানে আবির্ভূত হন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অধঃজগতকে পেছনে ফেলে উর্দ্ধজগতে মহান আল্লাহর সনে পাড়ি জমান। তারা স্বীয় কথা ও কাজের দ্বারা জগতবাসীকে জানিয়ে দিয়ে যান যে,‘‘ যে মৃত্যু সত্যের পথে হয়,তা মধূর চেয়েও সুধাময়।’’
বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের জীবনপটে যেমন,তেমনি তাদের পবিত্র বিশ্বাসের পাদমূলে আশুরার সঞ্জীবনী ধারা বাহমান। কারবালার আন্দোলন সুদীর্ঘ চৌদ্দশ’ বছর ধরে-সুগভীর বারিধারা দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে এসেছে প্রাণসমূহের। আজও অবধি মূল্যবোধ,আবেগ,অনুভূতি,বিচক্ষণতা ও অভিপ্রায়ের অযুত-অজস্র সুক্ষ্ণ ও স্থুল বলয় বিদ্যমান যা এই আশুরার অক্ষকে ঘিরে আবর্তনশীল। প্রেমের বৃত্ত অঙ্কনের কাটা-কম্পাস স্বরূপ হলো এ আশুরা।
নিঃসন্দেহে এই কালজয়ী বিপ্লবের অন্তঃস্থ মর্মকথা এবং এর চেতনা,লক্ষ্য ও শিক্ষা একটি সমৃদ্ধশালী,নিখাদ ও প্রেরণাদায়ক সংস্কৃতি গঠন করে। প্রকৃত ইসলামের সুবিস্তৃত অঙ্গনে এবং আহলে বাইেতর সুহৃদ ভক্তকুল,ছোট-বড়,জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সর্বদা এই আশুরা সংস্কৃতির সাথেই জীবন যাপন করেছে,বিকিশত হয়েছে এবং এ জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছে। এই সংস্কৃতির চর্চা তাদের জীবনে এত দূর প্রসারিত হয়েছে যে জন্মক্ষণে নবজাতেকর মুখে সাইয়্যেদুশ শুহাদার তুরবাত (কারাবালার মাটি ) ও ফোরাতের পানির আস্বাদ দেয় এবং দাফনের সময় কারবালার মাটি মৃতের সঙ্গে রাখে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু অবিধও সারাজীবন হোসাইন ইবনে আলী (আ.) এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করে,ইমামের শাহাদাতের জন্য অশ্রুপাত করে। আর এই পবিত্র মমতা দুধের সাথেই প্রাণে প্রবেশ করে আর প্রাণের সাথেই নিঃসিরত হয়ে যায়।
কারবালার আন্দোলন সম্পর্কে অদ্যাবিধ অসংখ্য রচনা,গবেষণা এবং কাব্য রচিত হয়েছে। সুক্ষ্ণ চিন্তা ও ক্ষুরধার কলমের অধিকারী যারা,তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নানান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই কালজয়ী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করেছেন। এই সকল রচনাকর্ম যদি এক করা হয় তাহলে তা পরিণত হবে এক মহাগ্রন্থাগারে। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে নব নব গবেষণা ও ভাবনার অঙ্গন এখনো উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কবি‘ সায়েব’ এর ভাষায়ঃ
‘‘ এক জীবন ধরে করা যায় (শুধু) বন্ধুর কোকড়া চুলের বর্ণনা
এই চিন্তায় যেওনা যে ছন্দ ও স্তবক ঠিক থাকলো কি-না’’
বক্ষমান বইখানি মহান দার্শনিক ও রুহানী আলেম আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারীর এই কালজয়ী বিপ্লব সম্পর্কিত বক্তৃতামালা ও রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ। ফার্সী ভাষায়‘ হেমাসা-এ হোসাইনী’ শিরোনামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই থেকে আরো 6টি কলাম যোগ করে বাংলাভাষায় বর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় বারের মতো প্রকাশিত হলো‘‘ ইমাম হোসাইন (আ.) এর কালজয়ী বিপ্লব’’ । ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক বইটি প্রকাশ করে বাংলাদেশের আহলে বাইত (আ.) এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হল যাতে তাদের আল্লাহ অভিমুখে পূর্ণযাত্রার পথে আলোকবর্তিকা হয় ইনশাআল্লাহ।
আশা করা যায়,বইটি পবিত্র আহলে বাইত (আ.) এর ভক্তকূল,যারা অন্তরে ইমাম হোসাইন (আ.) এর প্রেমভক্তি লালন করে এবং তারই সমুন্নত আদর্শের সামনে মাথা নোয়ায়,তাদের জন্য উপকারী হবে।
কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস,ঢাকা।
হোসাইনী আন্দোলনে অন্যতম উপাদান“ তাবলীগ”
‘ তাবলীগ’ -এর তাৎপর্য
মানুষের উক্তির মধ্যে যেমন সহজ অথবা দুর্বোধ্য হওয়া অর্থাৎ সরলভাবে একটিমাত্র অর্থপ্রকাশক কিম্বা বহুমাত্রিক ও একাধিক অর্থ প্রকাশক হওয়ার দিক থেকে পার্থক্য থাকে,তদ্রুপ মানুষের আন্দোলন ও বিপ্লবসমূহও একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের উক্তি দু’ প্রকারের হতে পারেঃ যে উক্তির একটিমা অর্থ থাকে আর যে উক্তির একাধিক অর্থ বা দিক থাকতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ। কোরআন তার আয়াতমালাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেঃ আয়াতে মুহকামাত তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত আর আয়াতে মুতাশাবিহাত তথা দ্ব্যর্থক আয়াত। প্রথম প্রকারের আয়াত হলো যার একটিমাত্র অর্থ থাকে। অর্থাৎ উক্ত ভাষা বা শব্দ থেকে একটার বেশী অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত থেকে একই সময়ে কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে আমরা যাতে সদৃশ্য অর্থাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির কবলে না পড়ি এজন্যে মুহকাম আয়াতগুলোকেই মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করতে হবে। কারণ সেগুলোই হলো‘‘ উম্মুল কিতাব’’ তথা কিতাবের মূল স্বরূপ।
মানুষের আন্দোলনসমূহ এবং বিপ্লবসমূহও ঠিক তদ্রুপ। কোনো আন্দোলনের একটি মাত্র অর্থ বা লক্ষ্য থাকতে পারে আবার একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিতও হতে পারে। অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে আন্দোলন পরিচালিত হয় আবার যেন সে সবগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিণতিতে একটি মূল লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তিত হয়। এভাবে একটি আন্দোলন একই সময়ে বিভিন্ন দিক ও মাত্রা সম্বলিত হতে পারে।
ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর আন্দোলন হলো এরূপ একটি বহু মাত্রা এবং বহু দিক সম্বলিত আন্দোলন। এই যে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর আন্দোলনকে ঘিরে নানান ব্যাখ্যা আর নানান মত,এর কারণ হলো এর মধ্যে একাধিক উপাদানের সমান্তরাল উপস্থিতি। আমরা যখন কিছু কিছু উপাদান এবং নিয়ামকের দিক বিবেচনায় এ আন্দোলনের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচার ও শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দাবীর বিপরীতে কেবলই প্রতিবাদী দৃঢ়তা এবং একগুয়েমী অবাধ্যতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আন্দোলনটি হলো এক নাকচ ঘোষণা এবং আত্ম-সমর্পণ না করা। আমরা সকলে জানি যে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এবং ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহণ আর এ উদ্দেশ্যে যতসব চক্রান্ত চালানো হয় তারপর ইয়াযিদ অপরিহার্য মনে করলো যে ইসলামী বিশ্বের কতিপয় ব্যক্তিত্ব যাদের সর্বাগ্রে ছিলেন ইমাম হোসাইন (আঃ),যাকে নিয়ে ইয়াযিদের হিসাব নিকাশ ছিল সবচেয়ে বেশী,এদের থেকে বাইয়াত আদায় করা। তাহলে জনসাধারাণও সবাই চুপ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হবে।
মুয়াবিয়ার মৃত্যু পর ইয়াযিদ কালক্ষেপণ না করে একটি চিঠি মদীনার গভর্ণর,তারই চাচাতো ভাই ওয়ালীদ ইবনে উতবা ইবনে আবি সুফিয়ানের কাছে প্রেরণ করে। তার মাধ্যমে সে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ এবং নিজের ক্ষমতারোহনের কথা তাকে অবগত করে। আর আলাদা একটি চিরকুটে সে কয়েক জনের নাম লিখে পাঠায় যাদের শিরোনামে ছিল ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নাম,তাদের কাছ থেকে অবশ্যই বাইয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ দান করে। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) বাইয়াত করতে রাজি হলেন না। তারপর আরো কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করার পর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এরা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়,তখন স্বীয় আহল পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর পবিত্র নিরাপদ ঘরের অভিমুখে রওনা হন। অর্থাৎ রজব মাসের শেষ ভাগে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর মদীনায় পৌছে এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট বাইয়াতের দাবী জানায়।
সম্ভবত 27 রজব ইমাম হোসাইন (আঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং 3রা শাবান তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেদিন তার জন্ম দিবসও ছিল। 8ই জিলহজ্ব অবধি তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তবে কোনো অবস্থাতেই তিনি তার কাছে যে দাবী জানানো হয়েছিল তার প্রতি সাড়া দিতে রাজি হননি। এই নাকচ করে দেয়াটা হলো একটি উক্তি । যে উক্তি এই আন্দোলনকে এক বিশেষ প্রাণ দান করে। এ প্রাণসত্তাটি হলো যুগের শাসন ক্ষমতা দখলকারী এক স্বৈরাচারী দাবীর বিরুদ্ধে‘ না’ বলা এবং আত্মসমর্পণ না করা।
এই আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী আরেকটি উপাদান হলো‘‘ সৎকাজের আদেশ আর অন্যায় কাজে নিষেধ’’ -এই নীতিটি । ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (আঃ)-এর বক্তব্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে। এমর্মে সাক্ষ্য প্রমাণও অনেক রয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে তার কাছে বাইয়াতের দাবী নাও করতো তাহলেও তিনি নীরব থাকতেন না।
আরেকটি উপাদান হলো হুজ্জাত তথা প্রমাণ পূর্ণ করা এবং চরম পত্র প্রদান করা। তৎকালে মুসলিম জাহানের তিনটি বড় কেন্দ্র ছিলঃ মদীনা-যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের ভূমি নামে পরিচিত ছিল,শ্যাম-যা খেলাফতের ভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং পূর্বে আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) এর দারুল খেলাফত ছিল। এছাড়া এটা ছিল একটি নতুন শহর যা মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সময়ে স্থাপিত হয়েছিল এবং একে ইসলামী সৈন্যদের সেনানিবাসও বলা হতো। আর একারণে একে শ্যামের সমান বলে তুলনা করা হতো। এই শহরের অর্থাৎ মুসলিম সেনানিবাসের জনগণ যখন অবগত হলো ইমাম হোসাইন (আঃ) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করতে রাজি হননি তখন তাদের নিকট থেকে প্রায় আঠারো হাজার চিঠি এসে পৌঁছে ইমামের কাছে। চিঠি গুলোকে কেন্দ্রে পাঠায় এবং ঘোষণা করে যে আপনি যদি কুফায় আসনে তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। এখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) ইতিহাসের দুই রাস্তার মোড়ে এসে উপনীতঃ যদি তাদের আহবানের প্রতি সাড়া না দেন তাহলে অনিবার্যভাবে ইতিহাসের রায়ে তিনি নিন্দিত হবেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস তখন বিচার করে বলবে যে অভাবনীয় একটি অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন নি। অথবা তিনি চাননি কিম্বা তিনি ভয় পেয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি অপব্যাখ্যা। ইমাম হোসাইন (আঃ) যাতে এই লোকগুলো যারা এভাবে সাহায্যের হাত তার দিকে প্রসারিত করেছে,তাদের কাছে হুজ্জাত তথা প্রমাণকে চুড়ান্ত করতে পারেন এজন্যে তাদের আহবানে সাড়া জানান। ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে। এপর্যায়ে এই আন্দোলন আরেক সত্তা এবং আরেক রূপ ও বর্ণ ধারণ করে।
এই আন্দোলনের আরো একটি মাত্রা বা দিক হলো এর তাবলীগ তথা প্রচারের দিক। অর্থাৎ,এই আন্দোলন একই সাথে যেমন সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ এবং একইসাথে যেমন প্রমাণ চুড়ান্তকরণ (ও যুগের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ না করার ঘোষণা) তদ্রুপ এটা একটি প্রচার এবং বার্তাবাহীও বটে। ইসলামকে পরিচিত করা এবং চিনিয়ে দেবার এক আন্দোলনও বটে।
আলোচনার শুরুতে‘‘ তাবলীগ’’ এর সঠিক অর্থকে আগে ব্যাখ্যা করার দরকার। বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ-এই নীতির সাথে এর পার্থক্য কি সেটা নির্ধারণ করতে হবে যাতে বুঝা যায় যে,হোসাইনী আন্দোলনে‘ তাবলীগ’ উপাদানটি‘ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ উপাদান থেকে ভিন্ন ।
‘ তাবলীগ’ এমন একটি শব্দ যা পবিত্র কোরআনে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোরআন নবীগণের ভাষায় বর্ণনা করে যে,
) يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ(
‘‘ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাস না।’’ (আ’ রাফঃ 79)
কিম্বা নবীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেঃ
) مَا عَلَي الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ(
‘‘ রসুলের উপর কোনো দায়িত্ব নেই কেবল পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া।’’ (মায়িদাঃ 99)
মোদ্দকথা হলো,‘‘ বালাগ’’ ,‘‘ তাবলীগ’ ,‘‘ ইউবাল্লিগুনা’’ ইত্যাদি শব্দগুলো পবিত্র কোরআনে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের অর্থ কি? দুর্ভাগ্যেরকথা হলো বর্তমানে এই শব্দটি একটি করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। অর্থাৎ এক অশুভ এবং ঘৃণ্য অর্থ লাভ করেছে। এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে আজ (উদাহরণস্বরূপ ফার্সী ভাষাভাষীদের কাছে তাবলীগ বলতে বুঝায় সত্য মিথ্যার তেলেসমাতি করা এবং প্রকৃতপক্ষে ঠগবাজি ও বোকা বানিয়ে মানুষের হাতে কোনো পন্য ধরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ বোকা বানানোর অর্থেই এখন এর প্রয়োগ। আর একারণেই দেখা যায় যখন কেউ বলতে চায় যে এসবের কোনো ভিত্তি নেই তখন বলে দেয় যে জনাব,এসব কিছুই আসলে তাবলীগ,সবকিছুই মিথ্যা আর ধোকাবাজি। এজন্যে দেখতে পাই অনেকে ধর্মীয় ব্যাপারে এ শব্দটি প্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। কিন্তু কথা হলো যদি কোনো শব্দের সঠিক অর্থ থাকে আর সেই সঠিক অর্থ পবিত্র কোরআন এবং নাহজুল বালাগার মধ্যে প্রয়োগ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত শব্দের অর্থ বিভ্রান্ত ঘটার অপরাধে সেটাকে শাস্তি দেয়া আমাদের উচিত হবে না। বরং সবসময় এর সঠিক অর্থটিই মানুষের কাছে বলা আমাদের কর্তব্য ।
تبلیغ (তাবলীগ) কথাটিوصول (উসুল) এবংایصال (ইসাল) কথা দুটির সাথে খুব নিকটবর্তী অর্থ বহন করে। আরবী ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু সূক্ষ্ণও নিখুঁত কাজ থাকে যা অন্য ভাষায় (এমনকি ফার্সীর মতো মিষ্টি ও সমৃদ্ধ ভাষাতেও) দেখা যায় না। আরবী ভাষায় একটি শব্দ হলোایصال (ইসাল) এবং আরেকটি শত্রুহলোابلاغ (ইবলাগ)।ایصال (ইসাল) এর অর্থ কি? যেমন ধরুন,আমি কোনো এক কাপড়কেایصال (ইসাল) করেছি। এর অর্থ হবে আমি ওটাকে পৌছে দিয়েছি।ابلاغ (ইবলাগ) ফার্সী ভাষায় কি অর্থ দেয়? যদি বলা হয় যে অমুক জিনিসটাকেابلاغ (ইবলাগ) করেছি,সে ক্ষেত্রে ও বলি যে এর অর্থ হলো পৌছে দিয়েছি। ফার্সী ভাষায় এ উভয়ের বলোয়‘ পৌছানো’ এবং‘ পৌছে দেয়া’ অর্থে ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আরবী ভাষায়ایصال (ইসাল) কেابلاغ (ইবলাগ) এর স্থলে প্রয়োগ করা যায় না। তদ্রুপابلاغ (ইবলাগ) কেওایصال (ইসাল) এর স্থলে প্রয়োগ করা যায় না।ایصال (ইসাল) শব্দটি সচরাচর কোনো জিনিসকে কারো হাত দ্বারা অথবা কারো আয়ত্বাধীনে পৗছানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ জড়বস্তুগত বিষয়ে। কেউ যদি একটি পার্সেলকে কারো নিকটে পৌছাতে চায়,এ ক্ষেত্রেایصال (ইসাল) শব্দকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিম্বা কেউ যদি আপনার কাছে কোনো আমানত (বস্তুগত) রেখে থাকে এবং আপনি সে আমানতকে তার কাছে পৌছে দিতে চান,এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমানতকে তার মালিকের নিকটایصال (ইসাল) করেছে।
কিন্তুابلاغ (ইবলাগ) কথা কোনো চিন্তা কিম্বা বার্তাকে পৌছে দেবার সময় বলা হয়। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে কারো মন,মানস,চিন্তা ও অন্তরে পৌছে দেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একারণেابلاغ (ইবলাগ) এর বিষয়বস্তু কোনো জড়বস্তু হতে পারে না। অবশ্যই তা কোনো অজড় এবং আধ্যাত্মিক কিছু হতে হবে। একটি চিন্তা অথবা একটি অনুভব। অন্যকথায়,সাধারণতঃ কোনো বার্তা,সালাম বা অনুরূপ কোনো কিছু প্রেরণের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। বলা হয় সালামابلاغ (ইবলাগ) করেছে,বার্তাابلاغ (ইবলাগ) করেছে। যখন বার্তাابلاغ (ইবলাগ) করে তখন কোনো চিন্তাকে অন্যদের কাছে পৌছায়। আর যখন সালামابلاغ (ইবলাগ) করে তখন আবেগ ও ভক্তিকে পৌছায়। এরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রেইابلاغ (ইবলাগ) বাتبلیغ (তাবলীগ) কথাটি ব্যবহৃত হয়। আর পবিত্র কোরআন এই শব্দকে রেসালাত তথা বার্তাসমূহের বেলায় প্রয়োগ করেছে।
সুতরাং,تبلیغ (তাবলীগ) হলো কোনো বার্তাকে একজনের নিকট থেকে আরেক জনের নিকটে পৌছানো। ফার্সী ভাষায় যে পয়গম্বর (বা বার্তাবাহক) কথা এসেছে তা‘ রাসুল’ শব্দের অনুবাদ। এর অর্থ হলো রেসালাতের মুবাল্লিগ তথা বার্তা প্রচারক।‘ রেসালাত’ শব্দ এমন একটি শব্দ যা শুভ পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য আমরা রেসালাহ বলতে যেসব জিনিসকে বুঝি তা কোরআনে ব্যবহৃত‘ রেসালাত’ এর থেকে ভিন্ন । আমরা সাধারনত কিছু লিখিত কাগজের সেট যার সমষ্টি একটি পুস্তকের মতো নয় সেটাকে রেসালাহ বলে থাকি। যদিও উক্ত রেসালাহ’ র বিষয়বস্তুর বার্তার সাথে কোনো সম্পর্ক নাও থাকে। যেমন ধরুন,কেউ একটি পুস্তিকা লিখলো কোনো ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে,ফার্সী কিম্বা আরবীর। তখন বলা হয় যে অমুক লোক অমুক বিষয়ে একটি রেসালাহ লিখেছে। যদিও এ নামটি উক্ত বিষয়বস্তুর ( যেমন ভাষার ব্যাকরণ) সাথে সঙ্গতিশীল নয়।‘ রেসালাহ’ কে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে কোনো বার্তা থাকবে। কিন্তু কেউ যদি কোনো জ্ঞানগত বা ভাষাগত সমস্যার সমাধান করে থাকে তাহলে সে কারো জন্য কোনো বার্তা আনেনি। এক্ষেত্রে এশব্দটি প্রয়োগ সঙ্গত নয়। কিন্তু সম্প্রতি‘ রেসালাত’ শব্দটি ফার্সী ভাষায় ব্যাবহার করা হচ্ছে । যেমন বলা হয় অমুকের সমাজের প্রতি‘ রোসালাত’ রয়েছে। অর্থাৎ,বর্তমানে যার সম্পর্কে অনুভব করা হয় যে স্বীয় সমাজের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব রয়েছে যা তার পালন করা উচিত,তার ক্ষেত্রে বলা হয় যে,তার একটা রেসালাত রয়েছে। এই ভাষাটি কোরআনে রেসালাতকে যে ভাষায় প্রয়োগ করা হয়েছে তার সাথে যদি অনুরূপ নাও হয়,খুবই কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ,এই অর্থটি কোরআনে ব্যবহৃত রেসালাত’ র অর্থের খুবই কাছাকাছি। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا اللهُ(
‘‘ সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। (আহযাবঃ 39)
এটা হলো বার্তাবাহকের জন্য সবচেয়ে বড় পূর্বশর্ত।
যখন প্রতিপন্ন হলো যেابلاغ (ইবলাগ) এবংتبلیغ (তাবলীগ) এর অর্থ হলো বার্তা পৌছে দেয়া তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে,تبلیغ (তাবলীগ) যা কোরআনে এসেছে আর‘ আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার’ -সেটাও যে কোরআনে এসেছ-এ দুটি আলাদা বিষয়। যদিও একে অপরের সাথে জড়িত,তবে বিষয় দুটি।
তাবলীগ হলো পরিচিত করার এবং উত্তমভাবে পৌছানোর পর্যায়। সুতরাং এটা হলো জানা বা পরিচিতর স্তর। কিন্তু আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের পর্যায়টি হলো কার্যকর এবং বাস্তবায়নের পর্যায়। তাবলীগ নিজেই একটি সার্বজনীন কর্তব্য সকল মুসলমানের জন্য । যেমনভাবে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারও এক সার্বজনীন কর্তব্য । তাবলীগের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যে কর্তব্য রয়েছে সেটা হলো তার মধ্যে যেন এমন অনুভূতি কাজ করে যে তার স্থান থেকে সে যেন ইসলামের বার্তা বহন করে। কিন্তু যে কর্তব্যটি‘ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর রয়েছে তা হলো তার মধ্যে যেন এই অনুভূতি কাজ করে যে সেও একজন বাস্তবায়নকারী এবং সমাজে এই বার্তা বাস্তবায়নকারী শক্তির সেও একটি অংশ। একারণেই আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার হলো এক বিষয়,আর তাবলীগ হলো ভিন্ন আরেকটি বিষয়। তাই হোসাইনী আন্দোলনে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ র মাত্রা তথা দিক ছাড়াও আরেকটি মাত্রা তথা দিক রয়েছে। আর সেটা হলো তাবলীগ। এই মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থক এবং বহুমাত্রিক আন্দোলন যে কাজটি করেছে তা হলো ইসলামের স্বরূপকে ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই পরিচিত করেছে। ইসলামের বার্তাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত ও উত্থাপিত করেছে। তাও আবার কতো দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে! ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে উক্তি দু’ প্রকারেরঃ মুহকাম তথা দ্ব্যর্থহীন আর মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থক। আরেকটি বিচারেও উক্তি দু’ প্রকারের হয়। যথাঃ স্বচ্ছ ও পরিণত উক্তি আর অস্বচ্ছ ও অপরিণত উক্তি ।
মুসলিম পণ্ডিতরা কিছু কিছু বাচনকে বিশুদ্ধ ও পরিণত বলে থাকেন। বিশুদ্ধ ও পরিণত বচন হলো সেটাই যা বক্তার মনোভাব ও উদ্দেশ্যকে উত্তম ও যথার্থভাবে শ্রোতার মন ও অনুভূতিতে পৌছাতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এমন উক্তি যা প্রকৃতই বক্তার উদ্দেশ্যকে পৌছে দিতে পারে।
আন্দোলনও এরূপ। স্বচ্ছ আন্দোলন যেমন রয়েছে,অস্বচ্ছ আন্দোলনও তেমনি রয়েছে। স্বচ্ছ আন্দোলন হলো সেটা,যা,যে বার্তাকে মনসমুহ,চিন্তাসমূহ এবং অনুভূতিসমুহের কাছে পৌছাতে চায়,তাকে ভালোভাবে পৌছে দিতে সক্ষম হয়। এই দিক থেকে যখন তাকাই তখন দেখি যে,হোসাইনী আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর,পরিণত এবং পৌছে দিতে সক্ষম কোনো আন্দোলনই খুজে পাওয়া যাবে না। এটা এমন এক আন্দোলন যা একদিক থেকে দেখা যায় যে স্থানিক ব্যপ্তির বিবেচনায় তা বিশ্বময় বিস্তৃতি লাভ করেছে। আবার কালের বিবেচনায় প্রায় চৌদ্দশ’ বছর পেরিয়ে এসেও আজ তার প্রভাব ও পৌছে দেবার শক্তি শুধু কমে যায়নি,তা নয়,বরং বলীয়ান হয়েছে। অসাধারণ শক্তিশালী এক আন্দোলন।
এপর্বে খোদ তাবলীগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক যাতে ইমাম হোসাইন (আঃ) এর আন্দোলনে‘ তাবলীগ’ উপকরণ কে সঠিকভাবে চিনতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারি। তাবলীগ এর অর্থ ও তাৎপর্য ইতিপূর্বে অবগত হয়েছি। দেখা গেছে যে পবিত্র কোরআন তাবলীগ শব্দটির ওপর নির্ভর করেছে। নবীগেণর প্রেরণের দর্শন সম্পর্কে নাহজুল বালাগায় প্রসিদ্ধ একটি বাক্য রয়েছে। বাক্যটিতে বলা হয়েছেঃ
فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، وَ وَاتَرَ اِلَيْهِمْ اَنْبِيَائَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَآّکرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ—
আল্লাহ নবীগণকে একের পর এক প্রেরণ করলেন। কি জন্যে ? প্রথমতঃ এজন্যে যে আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে মানুষের স্বভাবে প্রতিশ্রুতি নিহিত রেখেছেন। (বলতে চান যে দীন কোনো চাপিয়ে দেয়া বিষয় নয় যে মানুষের ওপর আরোপ করা হবে,বরং মানুষের সহজাত আহবানের প্রতিই সাড়া দেয়া। আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তা কোনো কাগজের নয়। অক্ষর,ধ্বণি কিম্বা বাইয়াতের মাধ্যমে নয়,বরং তকদীরের কলম দ্বারা,মানবের স্বভাব ও আত্মার গহীনে)। বলছেন যে,নবীগণ এসেছেন একথা বলতে যে,হে মানব! তোমরা তোমাদের সহজাত স্বভাব ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে অস্বীকারবদ্ধতা হয়েছে,আমরা তোমাদের সে প্রতিশ্রুতি পালন দেখতে চাই। অন্য কিছু নয়।
وَ يُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ অর্থাৎ নবীরা হলেন স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ।
وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ আর আল্লাহর বার্তাকে মানুষের কাছে পৌছে দেন যাতে এর মাধ্যমে মানুষের জন্য হুজ্জাত বা দলীলকে পূর্ণ করেন।
وَ يُثيِرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ
(কি অদ্ভুত বাক্যগুলো!)অর্থাৎ বলেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরে তথা বিবেক ও আত্মার মধ্যে গুপ্ত ধন লুকিয়ে রয়েছে। তাদের মগজে নিহিত রয়েছে চিন্তার গুপ্তধন। কিন্তু এসব গুপ্তধনকে ঢেকে ফেলেছে ধুলা ময়লার আস্তরণ। নবীগণ এসেছেন এসব ধুলা ময়লাকে ঝেড়ে ফলতে এবং মানুষের নিজের মধ্যে যেসব গুপ্তধন রয়েছে সেগুলো তাকে দেখিয়ে দিতে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের মন ও আত্মার ঘরের ভেতর মূল্যবান গুপ্তধনের অধিকারী রয়েছে কিন্তু সে তা থেকে বেমালুম বেখবর। নবীগণ মানুষকে তার এই মূল্যবান গুপ্তধনের সন্ধান দিতে চান যাতে প্রত্যেকে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তার গুপ্তধন বের করে আনার কাজে ব্রতী হয়।( উদ্ধৃত বাণীটির জন্য দেখুন নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খুতবা 1 , অংশ 36 , পৃষ্ঠা 33 )
তাবলীগের এই যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো নবীগণ ছিলেন সে অর্থে মুবাল্লিগ। কিন্তু সকলে শরীয়ত প্রবর্তক ছিলেন না। একারণে আল্লাহর নবীগণ ছিলেন দুই শ্রেণীরঃ এক শ্রেণীর নবী হলেন যারা মুবাল্লিগ এবং শরীয়তেরও প্রবর্তক। আর আরেক শ্রেণীর নবী যারা শুধুই মুবাল্লিগ। শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী হলেন আইন ও বিধান প্রণয়ণকারী নবী যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। তাদের মোট সংখ্যা হলো পাঁচজন। যথাঃ হযরত নূহ,ইব্রাহীম,মূসা,ঈসা আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কিন্তু সকল নবীই ঐশী বার্তার মুবাল্লিগ তথা প্রচারক। যেমনভাবে তারা আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার কারীও বটে। এই যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এসেছেন,প্রত্যেক নবীই মানুষের জন্যে আইন নিয়ে আসেননি। যারা আইন নিয়ে এসেছেন তারা সীমিত। অবশিষ্ট নবীরা সেই বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব পালন করতেন যা শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবীগণ নিয়ে এসেছেন। এরা হলেন তাবলীগের নবী। আর শেষনবীর পরে যেমন কোনো শরীয়তের নবীও আসবেন না তদ্রুপ কোনো তাবলীগের নবীও আসবেন না। কিন্তু মুবাল্লিগ থাকতে হবে। কিভাবে? যেহেতু শেষ যুগ হলো মানুষের প্রাপ্ত বয়স্ক ও পরিপূর্ণতার যুগ। এসময়ে ঐ যে দায়িত্ব এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী (পাঁচজন ব্যতীত) পালন করতেন অর্থাৎ তাবলীগের কাজ (যদিও প্রকৃত অর্থে স্বয়ং আল্লাহই তা করতেন অর্থাৎ নবীদেরকে একাজ পালন করার জন্যে প্রেরণ করতেন),সেকাজ এখন সাধারণ মানুষকে পালন করতে হবে। অ-নবীরাই এখন সেকাজ পালন করবে,আলেম এবং অ-আলেমরাই এখন তা পালন করবে। আর এজন্যেই ইসলামের প্রকৃত মুবাল্লিগরা হলেন নবীদের নবী। অর্থাৎ,নবীদের বার্তাকে তারা মানুষের কাছে পৌছায়।
তবে,একটি বার্তার সফলতার পূর্বশত কি? ইসলাম নিজে কি একটি সফল বার্তা ছিল? যদি উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে এই সফলতার পেছনে রহস্য কি ছিল? একটি বার্তা সফল হওয়ার চারটি শর্ত রয়েছে। যদি সে শর্ত চারটি একত্রে জমা হয় তাহলেই উক্ত বার্তার সফলতা শতভাগ নিশ্চিত হবে। কিন্তু যদি তা একত্রে জমা না হয় তাহলে তখন বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে।
একটি বার্তা সফল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া এবং এর বিষয়বস্তুর শক্তিদীপ্ত হওয়া। অর্থাৎ উক্ত বার্তা মানুষের জন্যে কি নিয়ে এসেছ এবং মানুষের যুগ জিজ্ঞাসা স্মরণে কত সামঞ্জস্যশীল এবং কিভাবে তা পূরণ করতে সক্ষম হবে? মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। মানিসক,চিন্তাগত,আবেগ অনুভূতিগত,ব্যবহারিক,সামাজিক,বস্তুগত ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি বার্তা শুধু যে মানুষের চাহিদার বিরুদ্ধ হবে না তাই নয়,বরং,সে চাহিদাগুলোর অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক বার্তার প্রথম কথাই হলো তাকে যুক্তিসিদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ,মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিশীল। তা এমন হবে যেন মানুষের বুদ্ধির আকর্ষণ ক্ষমতাকে সে নিজের দিকে টেনে আনে। কেননা,কোনো বার্তা যদি মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির পরিপন্থি হয় এমনকি যদি আবেগপ্রসূতও হয় তাহলে তার স্থিতিকাল খুব সামান্যই থাকে। চিরকাল তা টিকতে পারে না। একারণে কোরআন সর্বদা চিন্তা ও অনুধ্যানের ওপর জোরারোপ করে থাকে। কোরআন কখনোই বুদ্ধি ও যুক্তিকে পরিত্যাগ করেনি। বরং,যুক্তি ও বুদ্ধিকে সব সময় নিজের জন্য একটি খুঁটি হিসাবে কাজে লাগিয়েছে এবং মানুষকে বুদ্ধি খাটানোর জন্যে আহবান জানিয়েছে।
তদ্রুপ,একটি বার্তা যাতে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয় এজন্য তাকে মানুষের আবেগের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। মানুষের একটি দিক রয়েছে যা তার বুদ্ধি ও চিন্তার দিক থেকে ভিন্ন । যার নাম‘ আবেগ’ এবং যাকে উপেক্ষা করার জো নেই। বার্তাকে মানুষের এই আবেগের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলোর উন্নত ও সূক্ষ্ণগুলোকে একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিতৃপ্ত করা এবং মানুষের জীবনের বাস্তব প্রয়োজন সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া হলো ঐ বার্তার বিষয়বস্তুর বলীয়ান হওয়ার মূলকথা। যদি কোনো বার্তা মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদাসমূহের বিরুদ্ধ হয় তাহলে সফল হতে পারবে না।
একটি হাদীস রয়েছে,ফেকাহ’ র মধ্যেও যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ,ইসলামই বিজয়ী হয় এবং অন্যের ওপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,কোনো কিছুই ইসলামের ওপর বিজয়ী হয় না।( নাহজুল ফাসাহা , পৃষ্ঠা 214 , হাদীস নং 1056 )
এটা হলো এমন একটি হাদীস যা ইসলামের সকল শ্রেণীর আলেমবৃন্দ সমান দৃষ্টিতে যার মূল্যায়ন করেছেন। ফেকাহর আলেমগণ যারা সবকিছুকেই ফেকহী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পছন্দ করেন,তারা এই হাদীসের থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইসলামে সামাজিক বিধি বিধানে এমন কোনো বিধান নেই যা পরিণামে অমুসলমানদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয়ী করবে। ইসলাম এধরনের বিধানকে অনুমোদন করে না। উদাহরণস্বরূপ,ইসলামী সমাজে একজন আহলে যিম্মা (যেমন ইহুদী,খৃষ্টান কিম্বা যরথুষ্ট্রীয়) কি এমন মর্যাদা বা অবস্থায় উপনীত হতে পারে যে সে-ই শাসক হবে আর একজন মুসলমান হবে তার শাসনাধীন? কিম্বা একজন মুসলমানকে তার নিজের এখতিয়ারে নিয়ে নিবে? ফকীহবৃন্দ উত্তরে বলেন,:
الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ ইসলামের হাত সব সময় উপরে থাকতে হবে। ইসলাম নীচের হাতকে কখনো মেনে নেয় না। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে কতিপয় বিধান নিঃসরণ করে থাকেন।
কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ আবার বিষয়টিকে দেখেন অন্যভাবে। তারা কালাম শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর দিকে তাকান। (যেহেতু তাদের কাজ হলো যুক্তি প্রমাণ আর দলীল দস্তাবেজ নিয়ে একারণে) তারা বলেন যে,:الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ এর অর্থ হলো ইসলামের যুক্তি-প্রমাণ অন্য সব যুক্তি প্রমাণের চেয়ে শ্রেয়তর। যুক্তি-প্রমাণের ময়দানে ইসলামের যুক্তি প্রমাণই জয়যুক্ত হবে। এটা হলো উক্ত হাদীসের আরেক ধরনের ব্যাখ্যা । আবার যারা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবিষটি মূল্যায়ন করেছেন তারা বলেনঃالْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ,কার্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা ইসলামেরই। কারণ,ইসলামের বিধি বিধান অন্য যে কোনো বিধি বিধানের চেয়ে মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে তার পথকে বাস্তবক্ষেত্রে সহজতর করে তোলে।
কেউ যখন স্বীয় প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমগুলোর দিকে তাকায়,উন্নত কলা-কৌশল,দক্ষ জনবল,ব্যাপক পরিকল্পনা,বিশাল বাজেট এবং সর্বোপরি তাদের ব্যাপকতা দেখে বলে ওঠে যে,তাদের প্রোপাগাণ্ডার এতসব কিছুর পরেও কি ইসলাম টিকে থাকতে পারে? সত্যিই আজব ব্যাপার! যখন আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই তখন দেখি,তাবলীগের উপায় উপকরণের দিক দিয়ে আমরা একবারে শুন্যের কোঠায় রয়েছি। পৃথিবীর কোনো ধর্মই তাবলীগের উপকরণ আর মুবাল্লিগের দিক থেকে ইসলামের চেয়ে দুর্বল নয়। এমনকি ইহুদীরা যাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়,কিন্তু তাদের কোমর শক্ত করে বাধা। কিছু না হলেও অন্তত বিকৃতির দ্বারা। তাদের ইতিবাচক কিছু নেই যা দ্বারা মানুষদেরকে ইহুদীবাদের প্রতি আহবান জানাতে পারে। কিন্তু তাদের বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রবল অন্য ধর্মগুলোকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য । একজন ইহুদী তার জীবনভর ইসলামের কোনো একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা চালায়। তার লক্ষ হলো কোনো একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি আসন দখল করা। আর ঐ আসনে বসেই সে তার কাজ সেরে ফেলে। এমন একটি বই লিখবে এবং উক্ত বইয়ের মধ্যে সে তার নিজ চিন্তার প্রসার ঘটাবে। আপনারা কি জানেন যে বিশ্বে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর নববই শতাংশেরও বেশি চেয়ার ইহুদীদের দখলে রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বে ইসলামের এক্সপার্টরা হলো সব ইহুদী! তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের আঘাত শক্তি কতো জোরদার। ঐ হলো খৃষ্টানদের কথা আর এই হলো ইহুদীদের কথা।
কিন্তু এতসব কিছু সত্বেও,বিশ্বে কি হারে মানুষ মুসলমান হচ্ছে পত্র পত্রিকা খুললেই চোখে পড়বে। এটা কোন তাবলীগের জোরে? কোনো মুবাল্লিগও ছিল না। বড়জোর একটা রেডিও থেকে মাঝে মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের অনুষ্ঠান শুনেছে হয়তো। আমি (ওস্তাদ মুতাহহারী) ইউরোপ ফেরত একজন খোঁজ-খবর রাখা ব্যক্তির সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। ভদ্রলোকটি যিনি বহু বছর ধরে ইউরোপে থাকেন তিনি লোমণ্ড সংবাদপত্রে বিগত কয়েক বছরে 14 মিলিয়ন লোকের মুসলমান হওয়া মর্মে প্রকাশিত খবরের প্রসঙ্গে জনৈক খৃষ্টান ব্যক্তির অভিমত তুলে ধরে বলেন যে ঐ খৃষ্টান লোকটি বলেছিল,লোমণ্ড-এর তথ্য ভুল। আসলে বিগত বছরগুলোতে মুসলমান হওয়া লোকের সংখ্যা পচিশ মিলিয়ন। লোকটি আরো বলে যে আফ্রিকায় দুইটি শক্তি ক্রমবর্ধমানঃ ইসলাম এবং কম্যুনিজম। খৃষ্টবাদ যতই তৎপরতা চালাক,উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেনি। যদিও তাদের প্রচার মাধ্যমসমূহ শক্তিশালী এবং ব্যাপক;পক্ষান্তরে ইসলামের প্রচারমাধ্যম দুর্বল। এর পার্থক্য হলো দুটোর বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটির বিষয়বস্তু শক্তিশালী এবং যুক্তিনির্ভর,আর অপরটির বিষয়বস্তু আবেগ নির্ভর। আবেগের দৃষ্টিতে তা খুবই শক্তিশালী। এর বিষয়বস্তু বাস্তবমুখী এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনাচার কেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে অন্যটির বিষয়বস্তু হলো চাপিয়ে দেয়া। ইসলামের প্রথম কথাটি একজন পিপাসার্তের গলায় পানির মতো পরম আগ্রহে গলাধঃকরণ হয়। ইসলাম বলে, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আল্লাহ ও তার একত্ববাদকে প্রমাণিত করতে হবে। কিন্তু খৃষ্টবাদের প্রথম কথাই হলো বুদ্ধিবৃত্তিকে বিদায় করে ত্রিত্ববাদের কথা বলতে হবে।
মহররম ও আশুরাকে ঘিরে আলোচনা এতাটা বিস্তারিত করার উদ্দেশ্য হলো হোসাইনী বার্তাকে মানুষের কাছে পৌছানো। অতঃপর ব্যাখ্যা প্রদান করবো যে কিভাবে এ আন্দোলন ইসলামের বার্তা বহনকারী ছিল। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আঃ) কিভাবে ইসলামের বার্তাকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন।
ইমাম হোসাইন (আঃ) 8ই জিলহাজ্ব তারিখে যখন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে হাজীরা দলে দলে মক্কায় প্রবেশ করছিল,আর ঠিক যে দিনটাতে তাদের আরাফাত ও মিনার দিকে যাত্রা করতে হয়,তখন তিনি মক্কা থেকে প্রস্থান করলেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেন এবং ইবনে তাউসের মারফত বর্ণিত সেই বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন। এক মঞ্জিল অতিক্রম করে অন্য মঞ্জিলে পৌছিলেন এবং একসময় ইরাকের সীমান্তের নিকটবর্তী হলেন। কুফায় তখনও কি সংবাদ আল্লাহ মাবুদই ভালো জানেন। সেখানে হযরত মুসলিম ইবনে আকিলের ওপর নির্যাতনের করুণ কাহিনী ঘটে গেছে। ইমাম হোসাইন (আঃ) পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলেন কুফার দিক থেকে আসছে। ইমাম ক্ষণিক যাত্রাবিরিত করলেন তার সাথে কথা বলার জন্যে । বলা হয় যে,ঐ লোকটি ইমাম হোসাইন (আঃ) কে চিনতো। অপরদিকে সে কুফার করুণ ঘটনার খবর রাখতো। কাজেই সে বুঝতে পারলো যে যদি ইমাম হোসাইন (আঃ) এর নিকটে যায় তাহলে ইমাম নিশ্চয় তাকে কুফার সংবাদ জিজ্ঞাসা করবেন। তখন তাকে ঐ দুঃসংবাদের কথা জানাতে হবে। সে উক্ত খবর ইমামকে বলতে চাইলো না। অগত্যা নিজের রাস্তা ঘুরিয়ে দিলো এবং অন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হলো। বিন আসাদ গোত্রীয় দুইজন লোক যারা হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় ছিল এবং ইতিমধ্যে তাদের হজ্জ পালন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল,যেহেতু তারা ইমামকে সহযোগিতা করার মনস্থ করেছিল একারণে দ্রুততার সাথে পেছন থেকে রওনা হয়েছিল ইমাম হোসাইন (আঃ) এর কাফেলায় যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ।
এরা প্রায় এক মঞ্জিল পিছিয়ে ছিল। দেখা হয়ে গেল ঐ লোকটির সাথে যে কুফা থেকে আসছিল। পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার পর সালাম বিনিময়ের পরে আরবের প্রথা অনুযায়ী ইন্তিসাবের খবর জানতে চাইলো অর্থাৎ কে কোন গোত্রভূক্ত তার পরিচয় জানতে চাইলো। লোকটি বললো,আমি বনি আসাদ গোত্রের। তারা বললো,অবাক ব্যাপার! আমরাও তো বনি আসাদ গোত্রের! তাহলে বলো দেখি তোমার বাবা কে আর দাদা কে? সে উত্তর দিল। তারাও নিজেদের পরিচয় দিল। তখন মদীনা থেকে আসা লোক দুজন বললো,কুফার সংবাদ কি? সে বললোঃ সত্যি বলতে কি কুফার অবস্থা আসলে খুবই দুঃখজনক। ইমাম হোসাইন (আঃ) মক্কা থেকে কুফার দিকে যাচ্ছেন এবং পথিমধ্যে আমাকে দেখে তিনি থেমে যান কুফার সংবাদ নেবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু আমি এ দুঃসংবাদ তাকে বলতে পারবো না বলে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি। তারপর সে কুফার সব ঘটনা এ দুজনকে খুলে বললো।
তারা দুজন চলতে চলতে ইমামের কাফেলায় পৌছে যায়। প্রথম মঞ্জিলে পৌছে তারা এ ব্যাপারে মুখ খুললো না। তারা অপেক্ষা করলো যতক্ষণ না ইমাম আরেকটি মঞ্জিলে অবতরণ করলেন এবং গতকাল তারা কুফার যে লোকটির সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাত করেছিল তখন থেকে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। ইমাম তাবুর ভেতরে একদল সঙ্গী সাথী নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় সে দুজন লোক সেখানে প্রবেশ করলো এবং আরজ করলো,হে ইমাম! আমাদের কাছে একটি সংবাদ রয়েছে। সেটাকে এখানেই সকলের সম্মুখে বলার অনুমতি দান করবেন নাকি আড়ালে শুনবেন? তিনি বললেন,আমি আমার সঙ্গীদের থেকে কিছুই গোপন করবো না। যে সংবাদই হোক এখানেই সকলের সামনে তা বলো। দু’ জনের একজন বললো,হে ইমাম! আমরা গতকাল যে লোকটি আপনাকে দেখে না থেমে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল তার সাথে সাক্ষাত করেছি। সে একজন আস্থাশীল লোক। আমরা তাকে চিনি। আমাদেরই স্বগোত্রীয় বনি আসাদের লোক। আমরা তাকে কুফার সংবাদ জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে খুব খারাপ সংবাদ দিল। বললো,আমি কুফা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়েছি যখন নিজের চোখে দেখেছি যে মুসলিম ইবনে আকিল এবং হানি ইবনে উরওয়াকে শহীদ করা হয়েছে। আর তাদের লাশকে পায়ে রশি বেঁধে গলিতে আর বাজারে টেনে বেড়ানো হচ্ছিল। ইমাম হযরত মুসলিমের শাহাদাতের সংবাদ শুনলেন। তার দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। সাথে সাথে তিনি এই আয়াতখানি পাঠ করলেনঃ
) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(
অর্থাৎ,মুমীনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (আহযাবঃ 23)
এমন অবস্থায় ইমাম কিন্তু বললেন না যে,কুফাকে যেহেতু কব্জা করে নিয়েছে আর মুসলিম ও হানীকে যেহেতু শহীদ করে ফেলেছে কাজেই আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা পরাজিত হয়ে গেছি। কাজেই এখান থেকেই ফিরে যাই। বরং তিনি এমন এক বাক্য বললেন যা প্রতিপন্ন করে যে ব্যাপারটা অন্য কিছু । উপরোক্ত আয়াতটি সম্ভবতঃ আহযাবের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম বোঝালেন যে মুসলিম ইবনে আকিল তার কর্তব্য পালন করেছেন। এখন আমাদের পালা। কবির ভাষায়ঃ
کاروان شهيد رفت از پيش |
وان ما رفته گير و مي انديش |
‘‘ শহীদের কাফেলা আগই গেছে চলি
আমরা এখনো বেধে আছি চিন্তার খাতা খুলি’’
ইমামের একথা শুনে যারা দুর্বল চিত্তের ছিল এবং পার্থিব আশা নিয়ে ইমামের সঙ্গী হয়েছিল তারা প্রস্থান করে। (যেমনটা সব আন্দোলনেই দেখা যায়)।
لَمْ يَبْقَ مَعَهُ اِلَّا اَهْلَ بَيْتِهِ وَ صَفْوَتِهِ
অর্থাৎ তার সাথে অবিশষ্ট থেকে গেল কেবল তার আহলে বাইত ও নিষ্ঠাবান সঙ্গীদল। যাদের সংখ্যা সে সময়ে খুবই কিঞ্চিত ছিল। (খোদ কারবালায় এসে কিছুসংখ্যক লোক যারা প্রথমে ধোকার শিকার হয়েছিল এবং ওমর ইবনে সা’ দের দলে যোগ দিয়েছিল তারা একজন একজন করে জাগ্রত হয়ে ইমামের সাথে এসে যোগদান করেছিল)। হয়তো বা বড়জোর কুড়ি জনের বেশী হবে না তারা। এমন অবস্থাতেই হযরত মুসলিম ইবনে আকিল এবং হানী ইবনে উরওয়ার মর্মান্তিক শাহাদাতের খবর এসে পৌছে।‘ লিসানুল গাইব’ গ্রন্থের লেখক বলেন,কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন,ইমাম হোসাইন (আঃ) যেহেতু কোনো কিছুকেই তার সঙ্গীদের কাছে গোপন করছিলেন না,কাজেই এই খবরটি শোনার পরে সমীচিন ছিল শিশু ও নারীদের তাঁবুতেও গিয়ে মুসলিমের সংবাদটা তাদেরকে প্রদান করা যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলো হযরত মুসলিমের পরিবার,তার ছোট শিশুরা,ছোট ভাইয়েরা,বোনেরা এবং আরো কতিপয় চাচাতো বোনেরা।
এখন কিভাবে ইমাম তাদেরকে এ সংবাদ জানাবেন। হযরত মুসলিমের ছোট একটি মেয়ে ছিল। ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন বসলেন তাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে বসালেন এবং আদর করতে শুরু করলেন। কন্যাটি বুদ্ধিমতী ছিল। সে বুঝতে পারলো এ আদর কোনো সাধারণ আদর নয়। পিতৃসুলভ আদর। একারণে সে জিজ্ঞেস করলো,চাচাজী! যদি আমার বাবা মারা যান তাহলে আমাদের কি হবে? ইমাম তার একথায় বিগলিত হলেন। বললেন,মা আমার,আমি তোমার পিতার জায়গায় আছি। তার অবর্তমানে আমিই তোমার বাবার জায়গায় থাকবো। ইমাম পরিবারে কান্নার রোল পড়ে গেল। আকিলের সন্তানদের প্রতি উদ্দেশ্য করে ইমাম ঘোষণা দিলেন,হে আকিলের সন্তানেরা! তোমরা একজন মুসলিমকে উৎসর্গ করেছো। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট । এখন তোমরা চলে যেতে চাইেল চলে যেতে পারো। তারা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলো,হে ইমাম! আমরা এতক্ষণ কোনো মুসলিমকে শহীদ দান করিনি তখন আপনার সাথে ছিলাম। আর মুসলিমকে দান করে এখন আমরা ছেড়ে যাব? কক্ষনোই তা হতে পারে না। আমরা আপনার খেদমতে থেকে যাবো যতক্ষণ না মুসলিমের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমাদের ভাগ্যেও তা ঘটে।
বার্তা পৌঁছানোর উপকরণাদি ও মাধ্যমসমূহ
একটি বার্তার সফলতা নির্ভর করে চারটি শর্তের উপর। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো খোদ বার্তার বিষয়সার। অর্থাৎ বার্তা হতে হবে সমৃদ্ধ ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান। কোরআনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় হক্কানী তথা সত্যনিষ্ঠ বার্তা। এটা হলো এমন একটা শর্ত যা বার্তা বাহকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর এই যে খোদ বার্তার সত্যনিষ্ঠ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক,মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই,তদ্রুপ দীনি এবং মযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। পবিত্র কোরআন এ দিকটির ওপর নির্ভর করে যে,একটি বিষয় যদি সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তব হয় তাহলে খোদ ঐ বাস্তবসত্য হওয়াটাই তার স্থায়িত্বের কারণ হয়। পক্ষান্তরে কোনো বার্তার অন্তসারশুন্য হওয়া বা মিথ্যা ও বাতিল হওয়াটাই তার ধ্বংসের কারণ হয় যা তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে ফেলে। পবিত্র কোরআনে এ সংক্রান্ত একটি উপমা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) نزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الْأَمْثَالَ(
অর্থাৎ,তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্লোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর,স্লোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে এবং অলঙ্কার ও তৈজসপত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে,তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব ফেনা তো শুকিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। (রাদ : 17)
এ আয়াতে প্রথমে বৃষ্টি নামার এবং পানির ঢলে বান ডাকার বর্ণনা দেবার পর এবং সে বানের তোড়ে ছোট-বড় সব গর্ত-নালা প্রত্যেকে তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পানিতে পূর্ণ হওয়া এবং পানির স্লোত বয়ে চলা কালে কিভাবে তার ওপর ফেনার আস্তরণ জমে যায় যে আস্তরণ কখনো কখনো পানির উপরিভাগকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করে ফেলে ইত্যাদি বর্ণনা তুলে ধরার পর বলেঃ কিন্তু ফেনা অবশেষে বিদুরিত হয়। আর যা কিছু মানুষের জন্য লাভজনক ও উপকারী অর্থাৎ মূল পানিগুলোই শুধু অবশিষ্ট রয়ে যায়। অতঃপর বলেঃ এ উপমাটি হলো হক ও বাতিলের উপমা।
একটি বার্তা সফল হওয়ার আরো অনেক নিয়ামক রয়েছে যেগুলো অবশ্য খোদ বার্তার সারবস্তুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। একটি বার্তা যখন চায় এক আত্মা থেকে আরেক আত্মায় পৌছবে এবং জনমানুষের আত্মাগুলিতে প্রবেশ করবে,একটি সমাজকে স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করবে তখন নিঃসন্দেহে বার্তাবাহকদের দরকার রয়েছে,যারা সে বার্তাকে পৌছে দেব। একারণে,বার্তাবাহকদের মধ্যে যেসব গুণবৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বা নিয়ামক হলো সেই সব উপকরণ এবং মাধ্যম,বার্তা পৌছাবার জন্যে যেগুলোকে ব্যাবহার করা হয়। একজন বার্তাপ্রবাহকের নিঃসন্দেহে কি উপকরণ এবং হাতিয়ার ও মাধ্যমের দরকার য দ্বারা সে যে বার্তা পৌছে দেবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছে সেটা জনগণের কাছে (ইবলাগ) বা পৌছাতে সক্ষম হয়। আর চতুর্থ কারণ তথা নিয়ামক হলো বার্তাপ্রবাহকের Method বা পদ্ধতি এবং কৌশল ও অভিরুচি। অর্থাৎ কি উপায়ে সে বার্তা পৌছাবে। সুতরাং যে চারটি নিয়ামক কারণ একটি বার্তার সফলতা বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো যথাঃ
1. বার্তার বিষয়সার (অর্থাৎ তা সমৃদ্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া)
2. বার্তাবাহকের নিজস্ব বিশেষ ব্যক্তিত্ব
3. বার্তা পৌছানোর উপকরণাদি
4. বার্তা পৌছানোর কলা-কৌশল
এখানে‘ বার্তা পৌছানোর উপকরণাদি’ বিষয়ে আলোচনাটি ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক। একটি বার্তা যদি মানুষের কাছে পৌছতে চায় তাহলে নিঃসন্দেহে উপায় উপকরণাদির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ,উপকরণ ছাড়া একস্থানে বসে থেকে কখনো আরেক জনের অন্তরে কোনো বার্তাকে অঙ্কিত করে দেয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে নূন্যতম যে উপকরণ কাজে না লাগালে নয় তা হলো বাকশক্তি এবং কথার মাধ্যম। শব্দ উচ্চারণ করে কিম্বা বক্তৃতা করে অথবা কবিতা আবৃতির মাধ্যমে অথবা কোনো প্রবন্ধ লিখে। মোটকথা কোনো না কোনো উপকরণ দরকার। একজন বক্তার জন্য তার আসনটি (মেম্বার) একটি উপকরণ,তদ্রুপ মাক্রোফোনটিও একটি উপকরণ ইত্যাদি শত সহস্র উপকরণের কথা থাকতে পারে একটি বার্তা পৌছানোর জন্য ।
তবে একটি কথা রয়েছে। সেটা হলো পৌছে দেবার বার্তাটি যদি হয় ঐশী বার্তা তাহলে সেক্ষেত্রে যে কোনো উপকরণকেই কাজে লাগানো যাবে না। অর্থাৎ যাতে ঐশী বার্তা পৌছানো হয় এবং যেহেতু উদ্দেশ্যও পুত-পবিত্র কাজেই আমাদের এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে উপকরণ যা-ই হোক না কেন আমরা একাজে তা ব্যাবহার করতে পারবো। চাই সে উপকরণ বৈধ হোক আর অবৈধ। বলা হয়ে থাকে যে اَلْغَايَةُ تُبَرِّرُ الْمَبَادِي অর্থাৎ,‘‘ ফলাফলসমূহ উপকরণাদিকে বৈধ করে দেয়।’’ অর্থাৎ উদ্দেশ্য সঠিক হলেই আর উপকরণের বাছবিচার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এহেন নীতি পরিত্যাজ্য । আমরা যদি একটি পবিত্র কাজের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহলে একটি পবিত্র উপকরণ কিম্বা কমপক্ষে একটি বৈধ উপকরণকে কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু যদি অবৈধ হয় তাহলে তার আশ্রয় নেয়া যাবে না। আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই যে কিছু কিছু লক্ষ্য যেগুলো নিজে বৈধ এবং ন্যায়নীতিপূর্ণ,কিন্তু সেগুলোর জন্যে এমনসব উপকরণ ব্যাবহার করা হয় যেগুলো নীতিবিরুদ্ধ এবং অবৈধ। এর থেকে বুঝা যায় যে যারা দেখাতে চায় যে আমাদের এমন এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে আর এগুলো হলো তার উপকরণ,আসলে ঐ উপকরণগুলোই তাদের লক্ষ্য । উদাহরণ হিসাবে বলা যায়,আগেকার যুগে একটি বিষয় ছিল যাকে বলা হতো‘ শাবিহখানি’ । তেহরানে এটা বেশি বেশি ছিল। এটা হলো কারবালার ঘটনাবলীর উপর একটি কার নাট্যাভিনয়। কারবালার ঘটনাবলী নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার মূল বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম যে আস্তে আস্তে মূল শাবিহখানির বিষয়টিই মানুষের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। যেন তখন আর ইমাম হোসাইন (আঃ) এবং কারবালার কাহিনী তুলে ধরা বা সে সব হৃদয়বিদারক ঘটনাকে চিত্রায়িত করা কাজ ছিল না। শাবিহখানির মধ্যে তখন শত সহস্র বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে যেগুলো আর যাই হোক,কারবালার ঘটনাবলীর সাথে অন্তত মিলতো না। কত যে খেয়ানত,কত যে মিথ্যাচার,ধোকাবাজি আর রিপুচর্চা এসব শাবিহখানির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল যে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় কখনো কখনো সেগুলো হারাম কাজ হয়ে যেত! কোনো নিয়মনীতির প্রতিই যেন তার দায়বদ্ধতা নয়। আর এটা নিয়ে বিজ্ঞ দীনি আলেমবর্গের সাথে একটা বিরোধ লেগেই থাকতো। তারা এগুলোকে বরদাশত করতেন না। এমনকি পবিত্র কোম শহরেও শাবিহখানির নামে এসব উপহাসমূলক কল্পকাহিণী চালু হয়ে পড়ে। আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দীর মারজাইয়্যাত লাভের প্রথমদিকে যখন তার অসাধারণ প্রতাপ ছিল তখন একবার মহররমের আগে তাকে জানানো হলো যে আমাদের শাবিহখানির অবস্থা এরকম। তিনি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রত্যেক হেইয়্যাত তথা আযাদারী দলের নেতারা তার আমন্ত্রণে আসলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,আপনারা কার তাকলীদ করেন? সকলে উত্তর দিল যে আমরা আপনারই তাকলীদ করি। তিনি বললেন,যদি আমার তাকলীদ করে থাকেন তাহলে আমার ফতোয়া হলো এই যে শাবিহখানিকে আপনারা এই অবস্থায় পরিণত করেছেন,এটা হারাম কাজ। তখন তারা খুবই স্পষ্টরূপে আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দীকে জানিয়ে দিল যে,মুহতারাম,আমরা সারা বছর আপনারই তাকলীদ করি বটে;কিন্তু এই তিন চারটে দিন কোন ক্রমে আপনার তাকলীদ করবো না!! তারা একথা বলেই সেখান থেকে প্রস্থান করলো এবং তাদের মারজায়ে তাকলীদের কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলো না। তাহলে বোঝা গেল যে এখানে উদ্দেশ্য ইমাম হোসাইন (আঃ) বা ইসলাম নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো ঐ নাট্যাভিনয় যা থেকে তাদের অন্য কোনো ফায়দা রয়েছে। কিম্বা কমপক্ষে মজা তো উপভোগ করতে পারে! এটা ছিল এর পুরাতন রূপ।
আর এর আধুনিক রূপ হলো আমরা বর্তমানে যেটা দেখতে পাই কোনো সুফী দরেবেশর জন্য কিছূকাল অন্তর অন্তর একটা বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত করা দেশের অভ্যন্তরে কিম্বা বাইরে,কোনো বড় দরেবশ যেমন মাওলানা রুমির নামে। দেখতে পাই যে কি একটা বলে যা তাদের ভাষায়‘‘ সামা’’ যদিও খোদ এই সামা নিয়েও অনেক কথা রয়েছে। ঐ সামা’ র মজিলস বৈধ নাকি অবৈধ আমি সে বিষয়ে কথা বলতে চাই না। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে উক্ত সামা’ র মজিলস এরূপ ছিল না যে গোটা কতেক নাচনে আর ঢুলি যাদের মাথায় ইরফানের মরমী অর্থই বোধগম্য নয়,তারা সেখানে অংশগ্রহণ করবে! পরবর্তিতে আমরা দেখতে পাই যে (তৎকালীন শাহ সরকার কর্তৃক) মাওলানা রুমীর 700তম জন্মবার্ষিকী পালনের নামে যে কংগ্রেসের আয়াজন করেছে সেখানে যে একটিমাত্র কাজ করা হয় তাহলো একদল নাচনে কে এনে তথাকথিত সামা’ র মজিলস অনুষ্ঠিত করা,একটি রিপুচর্চার মজলিস তাও আবার মাওলানা রুমির শানে।
উদ্দেশ্য যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে উপায় উপকরণও বৈধ হতে হবে। অপরদিকে আবার একদল রয়েছে যাদেরকে বৈধ উপকরণ ব্যবহারের জন্য হাজার কষ্ট করেও রাজি করানো যায় না। এই মাইক্রোফোনের কথাই ধরুন। যখন প্রথম এটা তৈরী হয় তখন কতইনা এর বিরোধিতা করা হয়! যদিও শব্দের জন্যে মাইক্রোফোন হলো চোখের জন্য চশমার তুল্য কিম্বা কানের জন্য ইয়ার-ট্রাম্পেট তুল্য। যদি মানুষের কান ভার থাকে তাহলে এক ইয়ার-ট্রাম্পেট স্থাপন করে। এর অর্থ হলো আগে শুনতো না,এখন শুনতে পায়। আগে কোরআনকে শুনতে পেত না,এখন কোরআনকে ভালোমতো শুনতে পায়। গালিগালাজকেও আগে শুনতো না,এখন গালিগালাজকেও ভালোমতো শুনতে পায়। কিন্তু এটা তো ইয়ার-ট্রাম্পেট এর সাথে সম্পর্কিত না। মােইক্রোফোনের বেলায়ও সেই একই কথা। মাইক্রোফোন তো আর হারাম কাজের বিশেষ উপকরণ নয়। সেই উপকরণই ব্যাবহার করা হারাম যার দ্বারা কেবল হারাম কাজ ছাড়া আর কিছুই সাধিত হয় না। যেমন‘‘ ক্রুশ’’ চিহ্নটি । যা দ্বারা শিরকের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। মূর্তিও তদ্রুপ। কিন্তু যেসব জিনিস দ্বারা হারাম কাজও করা যায় আবার হালাল কাজও করা যায় সেগুলো হারাম হবে কেন?
জনৈক ওয়াজকারী বলতেন,মাইক আবিস্কার হওয়ার প্রথমদিকের একটি ঘটনা। আমরাও নতুন নতুন মাইকে কথা বলা শুরু করেছি। (সত্যি বলতে কি এই মাইক ওয়াজকারীদের ওপর আসলেই অনেক দাবীদার। যদি ত্রিশবছর আগে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখা যাবে যে সত্তর বছর বয়স হয়েছে এমন ওয়াজকারী খুবই কম ছিল। বেশীরভাগ ওয়াজকারীই চল্লিশ-পঞ্চাশবছর বয়সেই কোনো একভাবে মৃত্যুবরণ করতেন। আর এর পেছনে একটি কারণ ছিল এই মাইক না থাকা। ফলে তাদের অনেক জোরে জোরে কথা বলতে হতো। তখন গাড়ীঘোড়াও তো ছিল না যে তারপর গাড়ীতে চেপে বসবে। গাধা বা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হতেন। আর শীতের সময় এটা তাদের জন্য খুব খারাপ হতো। ফলে তাদের অধিকাংশই যুবক বয়সেই মৃত্যুর কবলে পড়তেন। এক্ষমতাবস্থায় মাইক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে) কিন্তু তখনো মাইক প্রচলন লাভ করেনি। কথা ছিল আমি এক বৃহৎ মজলিসে বক্তব্য রাখবো। সেখানে মাইকও রাখা হয়েছিল। আমার আগে জনৈক বক্তা মেম্বারে ওঠেন। মেম্বারে উঠেই তিনি বললেন,এই শয়তানের গোরটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। শয়তানের গোরটাকে সরিয়ে ফেলা হলো। আমি দেখলাম যদি সহ্য করি এবং কথা না বিল তাহলে এই শয়তানের গোরটাকে তো নিয়ে গেছে,পরবর্তিতেও একে আর ব্যাবহার করা যাবে না। তিনি বলেন যে,আমি যেইমাত্র মেম্বারে আরোহণ করলাম,বললাম,ঐ শয়তানের জীনটাকে আনা।
মোটকথা,এধরনের নিরেট মন-মানসিকতা আর শুস্ক চিন্তা-ভাবনা অবান্তর। মাইকের কোনো দোষ নেই। রেডিও,টেলিভিশন,ফিল্ম ইত্যাদি নিজ পরিসরে কোনো দুষ্ট নয়। এর বিষয়সার কি হবে? রেডিওতে যা বলা হবে সেটা কি হবে? টেলিভিশনে যা দেখানো হবে তা কি হবে? ফিল্মে যা দর্শন করা হবে তা কি হবে? এ ক্ষেত্রে মানুষের আর শুস্কতার পরিচয় দেয়া উচিত নয় এবং যে জিনিস নিজ পরিসরে হারাম নয় বরং বৈধ,সেটাকে একটা অবৈধ হিসাবে প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। ইসলামের ইতিহাসে তৎকালীন যুগে যেসব উপকরণ ছিল সেগুলোর কেমন ব্যাবহার হয়েছে এবং সেসব উপকরণ ইসলামের বার্তা পৌছানোর কাজে কি অসাধারণ অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে জানতে হলে এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ প্রদান করতে হবে। কখনো কি পবিত্র কোরআন মজিদের আয়াতমালার বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা,এগুলোর প্রঞ্জলতা এবং আকর্ষণীয়তার ব্যাপারে চিন্তা করেছেন? কোরআন দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীঃ একটি হলো এর বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ হক্কানী তথা সত্যনিষ্ঠতা। আর দ্বিতীয়টি হলো সৌন্দর্যময়তা।
কোরআন তার অর্ধেক সফলতা এপথ ধরেই অর্জন করেছে। সৌন্দর্যময়তা ও শিল্পশৈলিতা। কোরআনের বিশুদ্ধতা রয়েছে যা মানবের উর্দ্ধে । কোরআনের এই প্রভাব-প্রতাপ তার সৌন্দর্যের দান। কোনো উক্তির বিশুদ্ধতা এবং সৌন্দর্যই সেই উক্তি কে অপরের কাছে পৌছে দেবার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। স্বয়ং কোরআনও তার এই বিশুদ্ধতা এবং সৌন্দর্যকে নিয়ে কতই না গর্ব করে এবং এ ব্যাপারে কতই না কথা বলে! আসলে কোরআনের আয়াতমালার প্রভাব সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনেই কতো আলোচনা এসেছে! এই প্রভাব হলো কোরআনের রীতি পদ্ধতি সম্পর্কিত অর্থাৎ এর বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য।
) اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّـهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ(
অর্থাৎ,আল্লাহ কিতাব তথা উত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন,যা সামঞ্জস্যপূর্ণ,পুনঃ পুনঃ গঠিত। এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে ওঠে চামড়ার উপর,যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। ( যুমারঃ 23)
এই যে একটি হাকিকত তথা সারসত্য বিষয় যা বিদ্যমান ছিল এবং বিদ্যমান রয়েছে,কোরআন সে ব্যাপারে বর্ণনা করছে। উক্তি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সুন্দরতম হলো-মাছানি কিতাব। (মাছানির অর্থ যাই হোক না কেন) تَقْشَعِرُّ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ,যাদের অন্তরে প্রতিপালকের ভয় থেকে একটি অনুভূতি রয়েছে,যখন তারা কোরআনকে শ্রবণ করে তখন কাঁপতে শুরু করে। তাদের শরীরের চামড়া মুষড়ে পড়ে,
) ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اِلَي ذِآکرِ اللهِ(
আরেকটি আয়াতে এসেছেঃ
) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُآکرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَاناً وَ عَلَي رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ(
অর্থাৎ,যারা ঈমানদার তারা এমন যে,যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম,তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (আনফাল 2)
অথবা কিছু আয়াতে সেসকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা কোরআনের আয়াত শোনার সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ।
) يَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّداً(
অর্থাৎ,তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। (ইসরাঃ 107)
কিম্বা কিছু খৃষ্টানদের ব্যাপারে বর্ণনা করে যেঃ
) إذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَي الرَّسُولِ تَرَي اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ(
অর্থাৎ,তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে,তা যখন শুনে,তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (মায়িদা 83)
আসলে হাবাশার বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হয়? হাবাশার বিপ্লবের সূচনা হয় কি থেকে? হাবাশা মুসলমান হয়ে যায় কেন এবং এই ইসলামের উৎপত্তি হয় কোত্থেকে? কোরআন এবং এর সৌন্দর্য ছাড়া কি অন্য কিছু ছিল? সেদিনকার সে ঘটনায় হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব হাবাশায় ঐ সভায় প্রবেশ করলেন,রাজকীয় গাম্ভীর্যতা চারপাশে,তিনি শুরু করলেন পবিত্র কোরআন (সুরা তাহা) থেকে তেলাওয়াত করতে। মুহুর্তেই গোটা আসর বিস্ময়ে জেগে উঠলো। এ জাগরণের কারণ কি ছিল?! কোরআন বিশুদ্ধতা ও বর্ণনা শক্তি এবং প্রঞ্জলতা ও আকর্ষণীয়তা আর প্রভাব ক্ষমতার দিক থেকে এমনভাবে রচিত যে অন্তরসমূহের উপরে এরূপে প্রভাব বিস্তার করে।
আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) এর জনগণের মাঝে সফলতার একটি কারণ হলো তার ভাষার বিশুদ্ধতা।‘ নাহজুল বালাগা’ -আজ যা সংকলনের এক সহাস্রাব্দকাল অতিক্রান্ত হতে চলেছে অর্থাৎ গ্রন্থাকারে রূপলাভ করার সময় থেকে এক হাজার বছর কেটে গেছে,আর মূল খোতবাসমূহ উচ্চারিত হওয়ার পর থেকে প্রায় চৌদ্দশ’ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন আমলেও কি আর বর্তমান যুগেও কি,তার শীর্ষ স্থান বজায় রেখেছে। আমি এক সময় একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলাম। দেখতে পাই যে স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন (আঃ) এর যুগ থেকে অদ্যাবধি আরবের সকল সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আমিরুল মুমিনীন (আঃ)-এর বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ভাষার সামনে কুর্ণিশ জানিয়ে এসেছে ।
বলা হয় যে,মিশরে কয়েকবছর আগে‘ শাকিল আরসেলান’ যাকে‘‘ আমিরুল বাইয়্যান’’ তথা বাগ্মী সম্রাট বলে আখ্যায়িত করা হতো-তার সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়াজন করা হয়েছিল। এ সভায় বক্তাদের মধ্যে একজন তার বক্তৃতায় শাকিল আরসেলানের প্রশংসা তুলে ধরতে গিয়ে এক পর্যায়ে তাকে হযরত আলী (আঃ)-এর সাথে তুলনা করে বলে যে,শাকিল আরসেলান হলেন আমাদের যুগের আমিরুল বাইয়্যান যেমনভাবে আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন তার যুগের আমিরুল বাইয়্যান অর্থাৎ বাগ্মী সম্রাট। যখন স্বয়ং শাকিল আরসেলান বক্তৃতা মঞ্চে আরোহন করলেন,প্রচণ্ড ক্ষুধা অবস্থায় বললেন,এসব আজগুবি কথাবার্তা বলা হচ্ছে কেন?! আমাকে আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে তুলনা করছেন?! আমি আলীর জুতোর ফিতার সমানও হতে পারবো না। আমার বয়ান কোথায় আর হযরত আলীর বয়ান কোথায়?! আমাদের যুগেও এমন এমন লোক দেখি নির্মল পবিত্র অন্তরের অধিকারী,যখন হযরত আলীর বক্তৃতা শ্রবণ করে,মনের অজান্তে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এটা তাহলে কি? বক্তৃতার সৌন্দর্য থেকেই। স্বয়ং হযরত আলীর জামানায় এধরনের নজীর অনেক পাওয়া যায়।
হযরত আলী (আঃ) এর‘‘ খুতবাতুল গাররা’’ তথা দীপ্ত ভাষণটি যা দৃশ্যতঃ মরুভূমিতে উচ্চারিত হয়েছিল,সে সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে,যখন ভাষণ শেষ হয় তখন সমবেত সবাই সেভাবেই অশ্রু ঝরিয়ে যাচ্ছিল।‘‘ হাম্মাম’’ নাম্মী জনৈক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমীরুল মুমিনীনের কাছে আবেদন জানালেন যে,মুত্তাকী লোকদের পরিচয় কি আমাকে ব্যাখ্যা দিন। প্রথমে ইমাম এড়িয়ে যেতে চাইলেন এবং দু-তিনটি বর্ণনা দিয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু হাম্মাম তুষ্ট হলেন না। বললেন,আরো জানতে চাই। আপনি পরিপূর্ণভাবে মুত্তাকীর চিত্র আমার জন্য চিত্রায়িত করুন। এবার হযরত আলী (আঃ) ঐ মজলিসেই শুরু করলেন মুত্তাকীদের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে;মুত্তাকীরা তাদের রাত অতিবাহিত করে এভাবে,তাদের দিন কাটে এভাবে,তাদের বস্ত্র এরূপ,লোকজনের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে তারা এরূপ,তাদের কোরআন পড়া এরূপ। আমি (ওস্তাদ শহীদ মুতাহহারী) একবার গণনা করে দেখেছিলাম,চল্লিশটি বাক্যের মাধ্যমে মুত্তাকীদের একশ’’ ত্রিশটি গুণবৈশিষ্ট্য ঐ মজলিসে ব্যাখ্যা করেন। ঐ লোকটি এই বর্ণনা যতই শুনছিলেন ততই তার আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতঃপর একসময় জোরে চিৎকার করে ওঠেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। আমিরুল মুমিনীন বললেন : هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِاَهْلِهَا - অর্থাৎ বক্তৃতা যদি বিশুদ্ধ হয় আর অন্তর যদি গ্রহী হয় তাহলে এরূপ করে থাকে।( নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খোতবা নং 184 , খোতবা - ই হাম্মাম নামে প্রসিদ্ধ , পৃষ্ঠা - 618 )
দোয়া দরুদের কথাও বলা যায়। দোয়াসমূহের মধ্যে মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলে থাকে। নিছক শব্দ বা উক্তির কোনো প্রভাব থাকে না। কিন্তু আমাদের দোয়াসমুহ পরিপূর্ণতম বিশুদ্ধতা এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। কেন? কারণ,দোয়ার ঐ সৌন্দর্য যেন একটা মাধ্যম হয় যাতে দোয়ার বিষয়বস্তুকে মানুষের অন্তরে পৌছাতে সক্ষম হয়। কেন বলা হয় যে মুয়াজ্জিন সুকন্ঠের হওয়া মুস্তাহাব? এটা তো ইসলামী ফেকাহর কথা।‘‘ আল্লাহু আকবার’’ কে সুকন্ঠে বলা হোক আর কর্কশ কণ্ঠে বলা হোক-অর্থ তো আর বদলে যায় না। কিম্বা‘‘ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ কে সুকন্ঠে বলা হোক আর কর্কশ কন্ঠে বলা হোক-অর্থ তো আর পরিবর্তন হয়না। কিন্তু মানুষ যখন‘‘ আল্লাহু আকবার’’ কে কোনো কর্কশ কন্ঠ থেকে না শুনে বরং কোনো সুললিত কন্ঠ থেকে শ্রবণ করে তখন তার অন্তরে অন্যরূপে প্রভাব ফেলে।
শেখ সাদী এক কাহিনী বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেন যে এক শহরে একজন মুয়াজ্জিন ছিল খুবই কর্কশ গলার। সে ঐ কর্কশ কন্ঠে আযান দিচ্ছিল। একসময় তাকিয়ে দেখলো যে এক ইহুদী তার জন্যে উপেঢৗকন নিয়ে উপস্থিত হলো এবং বললো এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করবে? মুয়াজ্জিন বললোঃ কেন? সে বললোঃ কারণ,তুমি আমার বড় একটি উপকার করেছ। মুয়াজ্জিন বললোঃ কি উপকার! আমি তো কোনোই উপকারই তোমার জন্যে করিনি। ইহুদী তখন বললোঃ আমার একটি কন্যা রয়েছে যে ইদানীং ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছিল। কিন্তু তুমি যখন আযান দিচ্ছিলে তখন তোমার মুখ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে এখন সে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। তাই আমি তোমার জন্যে এই উপহারটি নিয়ে এসেছি। কারণ আমার মেয়েকে মুসলমান হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে তুমি আমার বড়ই উপকার করেছ।
মোটকথা এ বিষয়টি নিজেই একটি বিষয়।
ইবনে সীনা তার‘‘ মাকামাতুল আরেফীন’’ গ্রন্থে মানুষের জন্য আত্মিক সংযুতি কখন সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে খুবই উত্তম ও সুক্ষ্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং এর কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো যথাঃ اَلْكَلامُ الْوَاعِظُ مِنْ قَائِلٍ زَآکيٍّ অর্থাৎ উপদেশ বাণী যখন কোনো পবিত্র বক্তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ প্রথম কথা হলো স্বয়ং উপদেশদাতা (ওয়াজকারী) কে শুদ্ধ ও পবিত্র অন্তরের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর বলেনঃ بِعِبَارَةٍ بَلِيغَةٍ وَ نَغْمَةٍ رَخِيمَةٍ অর্থাৎ উক্ত ওয়াজকারীর কন্ঠ হতে হবে সুললিত,সুকন্ঠ । যাতে শ্রোতার মনে উত্তমরূপে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়। ওয়াজকারীর কথা বিশুদ্ধ হতে হবে তাহলে শ্রোতার অন্তরে প্রভাব ফেলবে। স্বয়ং বক্তার চেহারা সুরতও এ প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ আলোচনা করার উদ্দেশ্য একটাই। আর তাহলো যাতে বুঝা যায় যে অর্থ পৌছানো,নিজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলো হলো উপকরণ তথা মাধ্যম,এগুলোই বৈশিষ্ট্য আর পদ্ধতি। এই উপকরণ ও মাধ্যমগুলোই বার্তাকে চতুর্দিকের ব্যক্তি তথা জনতার কাছে পৌছে দেবে।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে হয়। স্বয়ং কোরআন পড়ার বিষয়টি কিরূপ? অবশ্য কোরআন আযানের মতো নয়। আযানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে একজন আযান দেবার জায়গায় আরোহণ করবে এবং আযান প্রদান করবে। আর তাকে সুকন্ঠের অধিকারী হতে হবে। কিন্তু কোরআনকে সবাই পড়ে। যারাই কোরআন পড়ে তাদের কর্তব্য হলো যথাসম্ভব সুন্দরভাবে পড়া। এতে যেমন স্বয়ং কারীর অন্তরে উত্তম প্রভাব ফেলে,তদ্রুপ শ্রোতার অন্তরেও। কোরআনে এই যে নির্দেশ এসেছেঃ
) وَ رَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتِيلاً(
অর্থাৎ, কোরআন আবৃত্তি করুন তারতীল তথা সুবিন্যস্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে। (মুযযাম্মিলঃ 4)-এর অর্থ কি? অর্থাৎ যখন কোরআন পড়বেন তখন যেন শব্দাবলীকে এমন দ্রুততার সাথে পড়বেন না যে সেগুলো পরস্পর জোড়া লেগে যায়। আবার এমন বিরিত দিয়ে পড়বেন না যে এক শব্দ আরেকটি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এমনভাবে সেগুলো পড়তে হবে যেন কেউ বলে দিচ্ছে আর আপনি তা শুনে শুনে পাঠ করছেন। কিম্বা আপনি যেন নিজের সাথে নিজে কথা বলছেন। আরফগণের ভাষায়,মানুষের উচিত কোরআনকে সবসময় এমনভাবে পাঠ করা যে সে যেন মনে করে বক্তা হলেন আল্লাহ আর শ্রোতা সে নিজে। সে স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি একথাগুলো শুনছে এবং গ্রহণ করছে।
আল্লামা ইকবাল লাহোরী বলেন,আমার পিতা আমাকে একটি কথা বলেন যা আমার ভাগ্য গড়ার কাজে অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বর্ণনা করেন যে একিদন আমি আমার কক্ষে বসে কোরআন পাঠ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় আমার পিতা সে কক্ষের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে থেমে গেলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ মুহাম্মাদ! কোরআনকে এমনভাবে পাঠ করো যেন স্বয়ং তোমার উপরেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তখন থেকে আমি যখনই কোরআন খুলে বসি এবং আয়াতগুলোকে পাঠ করি তখনই আমি মনে করি যে,এ হলেন আমার আল্লাহ যিনি আমার সাথে অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে কথা বলছেন।
এক হাদীসে রয়েছেঃ
تَغَنَّوْا بِالْقُرْآنِ
অর্থাৎ কোরআনকে গানে গানে ( সূরে সূরে) পাঠ করো।( বিহারুল আনায়ার , খণ্ড 92 , পৃষ্ঠ - 191 ; জামেউল আখবার , অধ্যায় 23 , পৃষ্ঠা - 57 ) এমর্মে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেটা নিশ্চিত করে বলা যায় তাহলো এর বক্তব্য-তোমরা কোরআনকে খুবই সুরেলা কন্ঠে পাঠ করো। অবশ্য সেসব সুর যেগুলো আনন্দ ফুর্তির আসরের গান বাজনা সদৃশ্য এবং যৌন সুড়সুড়িকর সেগুলো তো অবধারিতভাবে হারাম এবং শরীয়ত বিরোধী। কিন্তু যেসব সুর মানুষের আত্মিক অবস্থার সাথে সমঞ্জস্যশীল তেমন সুরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্মরণ রাখতে হবে যে পবিত্র কোরআনের অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে সুর ধারণ করার ক্ষেত্রে । এটাও কোরআনের এক মুজিজা। তবে সে সুর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। কোনো যৌন সুড়সুড়িকর সুর নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেবেন কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ।
আব্দুল বাসেতের কোরআন তেলাওয়াত কেন দেশ দেশ এত জনপ্রিয়? কারণ,আব্দুল বাসেত তার মোহনীয় কন্ঠে সুললিত সুরে এবং তেলাওয়াতের যথাযথ নিয়ম কানুন মেনে যে সূরাকে যেমন সুরে পড়তে হবে ঠিক সেভাবে পড়তে জানেন এবং পড়ে থাকেন। আমাদের মাসুম ইমামগণের সম্পর্কেও বিশেষ করে ইমাম যয়নুল আবেদীন এবং ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ) সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তারা যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন,সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক কন্ঠে ,তখন সে আওয়াজ গলিপথে ছড়িয়ে পড়তো। আর যারা সে পথে চলাচল করতো তারা সে সুর শুনে বিমোহিত হয়ে পড়তো। থেমে যেত তাদের পথ চলা। ইমাম (আঃ) এর দরজা পাশে ভীড় জমে যেত আর সে ভীড়ে পথ বন্ধ হয়ে যেত। এমনকি যারা পানি সরবরাহ করতো (সে আমলে চলন ছিল কিছু কিছু লোক মশক কাঁধে নিয়ে কুপ থেকে পানি তুলে মানুষের ঘরে ঘরে সরবরাহ করতো। মদীনায় শুধুই কুপ ছিল। পানির নহর ছিল না।) এবং সংখ্যায়ও নিতান্ত কম ছিল না,তারা কাঁধে পানির মশক নিয়েই যখন ইমাম (আঃ) এর বাড়ীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে যেত,তখন ইমাম (আঃ) এর সুমধুর কন্ঠ শুনে তাদের পা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলতো। ঐ পানি ভরা ভারী মশকগুলো কাঁধে নিয়েই তারা দাড়িয়ে দাড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণে নিমগ্ন হয়ে যেত যতক্ষণ না ইমাম (আঃ) এর তেলাওয়াত শেষ হতো। এসব কিছু থেকে কি বেরিয়ে আসে? ঐশী বার্তা পৌছানোর জন্যে বৈধ উপকরণ বা মাধ্যমকে কাজে লাগানো। ইমাম (আঃ) কেন কোরআনকে এভাবে সুমধুর সুরে তেলাওয়াত করতেন? কারণ তিনি চেয়েছিলেন এই মাধ্যম দ্বারা তাবলীগের কাজ করতে। কোরআনকে মানুষের কাছে পৌছাতে। কেউ যখন ইসলামের ব্যাপারে কবিতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করে তখন অদ্ভুত বিষয়াদি দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কবিতার সাথে লড়াইও করেছেন আবার কবিতাকে প্রচলনও করেছেন। সেই সব কবিতার সাথে লড়াই করেছেন যেগুলো আজকের ভাষায় প্রতিশ্রুতিশীল ছিল না। অর্থাৎ সেগুলো কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বলিত কবিতা ছিল না। নিছক কল্পনা আর খেয়াল,সময় কাটানোর মাধ্যম,মিথ্যাচারে ভরা। যেমন কেউ কবিতা আবৃত্তি করতো কারো বল্লমের প্রশংসায় কিম্বা কারো ঘোড়ার প্রশংসায়। কেউ বা আবার কবিতা আবৃত্তি করতো প্রেয়সীর তিলকের প্রশংসায় অথবা ধনীলোকের প্রশংসা করতো তার অর্থের আশায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে এজাতীয় কবিতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বলেছেনঃ
لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِيَ شِعْراً
অর্থাৎ যদি মানুষের পেট বমি দ্বারা ভরা থাকে সেটাও বরং ভালো ফালতু কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে।( নাহজুল ফাসাহা , পৃষ্ঠা 470 , হাদীস নং 2215 ) কিন্তু আবার তিনিই বলেছেনঃ
اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً
অর্থাৎ কিছু কিছু কবিতা রয়েছে প্রজ্ঞাপূর্ণ।( আল গাদীর , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 9 ) সব কবিতাকে ফালতু বলা হয়নি। বরং কিছু কিছু কবিতা রয়েছে বাস্তবতা সমৃদ্ধ ।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সভাসদদের মধ্যে কয়েকজন কবিকেও রেখেছিলেন। তাদের মেধ্যে একজন হলেন হাসসান বিন সাবিত। দুই প্রকার কবিতার মধ্যে প্রভেদকরণ শুধু কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসেই আসেনি। বরং পবিত্র কোরআনেও এ ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ(
-অর্থাৎ,বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে,তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে,তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে।( শুআরা 224 - 227 ) এমনও কবি ছিল যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অথবা পবিত্র ইমামগণ (আঃ) ঊৎসাহিত করতেন। কিন্তু কোন ধরনের কবিরা? যারা কবিতার সুন্দর আভরণে ইসলামের বার্তাকে এবং এর সারত্তাকে জনগণের কাছে তুলে ধরতো। নিঃসন্দেহে কবিতা যে কাজ করতে পারে,একটি প্রবন্ধ দ্বারা তা করা যায় না। কারণ,কবিতা হলো যুগের চেয়ে সৌন্দর্যময়। কবিতার ছন্দ থাকে,থাকে অন্তরাত্মা যা সূর ধারণ করতে সক্ষম। মস্তিস্ক তা মুখস্ত করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় সভাসদের একজন হাসসান বিন সাবিতকে বললেনঃ
لَا تَزَالُ مُؤَيِّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ ، مَا ذَبَبْتَ عَنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ
অর্থাৎ,পবিত্র আত্মা তোমাকে ততক্ষণ অবিধ সমর্থন করে যাবে যতক্ষণ তুমি যে পথে (অর্থাৎ আহলে বাইত) রয়েছ তা থেকে বিপথগামী না হবে।( আল - গাদীর , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 34 ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথাগুলো বলেন একজন কবি সম্পর্কে।
মাসুম ইমামদের (আঃ) সময়কার কবিরা কতই না অবদান রেখেছেন! আমাদের ইসলামের ইতিহাসে আরবী,ফার্সী ও অন্যান্য ভাষায় অনেক বীরত্বগাঁথা ও একত্ববাদী কবিতা রয়েছে। অসাধারণ উপদেশময় সেসব কবিতা। এগুলো সবই হলো ইসলামী সংস্কৃতির ফলস্বরূপ। কবিতার যে প্রভাব রয়েছে,যুগের তা নেই। আর নাহজুল বালাগার বিস্ময় হলো এটাই যে গদ্য,কিন্তু বিশুদ্ধতা আর সৌন্দর্যতায় কবিতার সমকক্ষ বা তার চেয়েও বেশী। ফার্সী ভাষায় আপনি এক পৃষ্ঠাও লেখা খুজে পাবেন না যা শেখ সাদীর এক পৃষ্ঠা কবিতার সমকক্ষ হবে। যদিও মানোর্ত্তীর্ণ লেখা বহু রয়েছে। যেমন,খাজা আব্দুল্লাহ আনসারীর কালেমাতে কেসার কিম্বা সাদীর কথা-সাহিত্য । মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি তার ঐ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা সত্বেও যখন তার ওয়াজের মজলিসে যাবেন,দেখবেন যে তার কবিতার তুলনায় কথার বয়ানগুলো কিছুই না। আরবী ভাষায়ও এমন কোনো গদ্য রীতির লেখা নেই যার মধ্যে নাহজুল বালাগার মতো অসাধারণ শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করা যায়। কবিতা তার নিজ আদলে অনেক অবদানই রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং অনেক অবদান রাখতে সক্ষম। আবার মন্দ কবিতাও খুবই মন্দ হতে পারে যেমনভাবে ভালো কবিতাও অনেক ভালো হতে পারে। হিকমতের কবিতা,তৌহিদের কবিতা,পরকালের কবিতা,নবুওয়াতের কবিতা,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসার কবিতা,মাসুম ইমাগণ এবং পবিত্র কোরআনের প্রশংসায় কবিতা,শোক-মার্সিয়ার কবিতা ইত্যাদি কবিতাসমূহ যদি ইমামদের যুগের কবিতার মতো ভালো হয় তাহলে তা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।
আল্লামা ইকবাল লাহোরী প্রকৃতই একজনবান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইসলামের ক্ষেত্রে নিজের জন্যে এক রেসালাত তথা দায়িত্ব অনুভব করতেন। আর এ রেসালাত পৌছানোর জন্যে তিনি যে উপকরণকে কাজে লাগিয়েছিলেন তা হলো কবিতা। ফার্সী ভাষার কবিদের মধ্যে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছেন এমন কবি হিসাবে নিঃসন্দেহে আল্লামা ইকবালের কোনো জুড়ি নেই। কবিতা যদি কবির জন্যে মাধ্যম হয়ে থাকে তার লক্ষ্যের জন্যে ,তাহলে তার কোনো তুলনা হয় না। আল্লামা ইকবাল যেখানে সঙ্গীতের প্রয়োজন ছিল সেখানে সঙ্গীত রচনা করতেন। তার বিখ্যাত যে সঙ্গীতটি আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে সেটা উর্দুতেই তিনি রচনা করেছিলেন। এখন ফার্সী ভাষায়ও তা অনুবাদ করা হয়েছে। কি অসাধারণ সঙ্গীত খানি। আমি (ওস্তাদ মুতাহহারী) নিজে একাধিকবার এটি শুনে ক্রন্দন করেছি,অনেককে কাদতেও দেখেছি। আমরা সঙ্গীতকে কাজে লাগাবো না কেন? এগুলো সবই হলো মাধ্যম। এসব মাধ্যম থেকে উদাসীন থাকা আজ আর চলে না। আধুনিক যুগে এমন সব মাধ্যম আবিস্কৃত হয়েছে যা আগের আমলে ছিল না। শুধু আগেকার যুগের উপকরণ নিয়ে আমরা ক্ষান্ত থাকবো কেন? আমাদের কেবল দেখতে হবে যে কোন উপকরণটি শরীয়ত স্বীকৃত আর কোনটি শরীয়ত স্বীকৃত নয়।
স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আঃ) ঐ উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে স্বীয় বার্তাকে পৌছানোর জন্য এবং ইসলামের বার্তাকে পৌছানোর জন্য যে যে উপকরণ এবং মাধ্যমকে ব্যাবহার করা সম্ভব ছিল তার সবগুলোই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। ইমামের মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত এবং কারবালায় প্রবেশ করার পর থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত তার ভাষণসমূহ অসাধারণ অনুপ্রেরণাদায়ক,আবেগময় এবং অসাধারণ সৌন্দর্যময় আর সাবলীল ও বিশুদ্ধ ভাষা সমৃদ্ধ । এদিক থেকে কেবলমাত্র যে ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) এর প্রতিদ্বন্দী তিনি হলেন ইমাম হোসাইন (আঃ)। এমনকি কেউ কেউ বলে থাকেন যে আশুরার দিনের ইমাম হোসাইন (আঃ) এর ভাষণসমুহ আমিরুল মুমিনীনের ভাষণসমূহের চেয়েও ঊৎকৃষ্টতর। তিনি যখন মক্কা ছেড়ে বের হয়ে আসতে চাইলেন তখন লক্ষ্য করুন কি উৎকৃষ্ট ভাষা আর কি সুন্দর ও বিশুদ্ধ বাচনের মাধ্যমে তিনি স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরলেন।
মানুষকে আরবী ভাষা শিখতে হবে;তবেই কেবল পবিত্র কোরআন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণীমালায়,মাসুম ইমামগণের ভাষণে এবং খোতবা আর দোয়া-কালামের মধ্যে নিহিত এই অপরূপ সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে পারবে। ইমামের এসব ভাষণগুলো অনুবাদ করলে যথার্থ রূপে অর্থ প্রকাশ করে না। তিনি বলছেনঃ মৃত্যু হলো মানুষের গলায় অলঙ্কারের ন্যায়। একজন মানুষের জন্যে মৃত্যু ততখানি সৌন্দর্যময় যেমনটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে যুবতীর গলায় অলঙ্কার পরিধান করলে। হে লোক সকল! আমি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করেছি,আমি আত্মত্যাগের নেশায় মত্ত ,আমি আমার পূর্বসূরীদের সাক্ষাতে ততটাই আসক্ত যতটা আসক্ত ছিলেন নবী ইয়াকুব তার ইউসুফকে সাক্ষাতের জন্য । অতঃপর তিনি যে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং কেউ যেন মনে না করে যে তিনি দুনিয়ার বাহ্যিক বিজয় লাভ করার আশায় চলেছেন,না বরং তিনি ভবিষ্যতকে সচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন যে ঐ মরু মাঝে কিভাবে মানুষরূপী নেকড়েগুলো সারি বেধেছ এবং কিভাবে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে,এ বিষয়টি জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ
رِضَي اللهِ، رِضَانَا اَهْلُ الْبَيْتِ
অর্থাৎ,আমরা আহলে বাইত আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট হন তাতেই সন্তুষ্ট থাকি।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড 44 , পৃষ্ঠা 367 ; মাকতালু মুকাররাম , পৃষ্ঠা 193 , আল লুহুফ , পৃষ্ঠা 25 , কাশফুল গুম্মাহ , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 29 ) এটা হলো সেই রাস্তা যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তিনি পছন্দ করেছেন। সুতরাং আমরা এ পথকেই বেছে নেব। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের সন্তুষ্টি । কেবলমাত্র তিন চার লাইনের বেশী নয়। কিন্তু একটি বইয়ের চেয়েও বেশী প্রভাব ফেলে। শেষ মুহুর্তে তিনি মানুষের কাছে ইবলাগ করতে (তথা পৌছে দিতে) চান যে আমি কি বলতে চাই আর তোমাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করি। তাই তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি বুকের রক্তকে আমাদের পথে উৎসর্গ করতে তৈরী আছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করার সংকল্প রাখে সে যেন প্রস্তুত থাকে। আগামীকাল সকালে আমরা রওনা হব। আশুরার রাতে পবিত্র তেলাওয়াতের মুগ্ধকর সুর শুনতে পাই,মৌমাছির গুঞ্জরণের মতো দোয়া মোনাজাতের গুনগুনানী ভেসে আসে যা শত্রুর অন্তরকেও বিমোহিত করে দেয় এবং তাদেরকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে। যে সাহাবীদল মদীনা থেকে ইমামের সঙ্গে এসেছিলেন তাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। হয়তো কুড়ি জন হতে পারে। কেননা একদল তো পথিমধ্যে আলাদা হয়ে চলে যায়। বাহাত্তর জন শহীদের অনেকেই কারবালায় এসে যোগদান করেছিলেন। অনেকে আবার ইবনে সা’ দের দল থেকে পৃথক হয়ে ইমামের বাহিনীতে যোগ দেয়। এদের মধ্যে একদল হলো তারা,যারা আশুরার রাতে এসব খিমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের কানে ভেসে আসছিল মিষ্টি মধুর গুঞ্জরণের ধ্বনি,কোরআনের তেলাওয়াত,সিজদা আর রুকুর যিকির, সুরা হামদ। এই ধ্বনিই তাদেরকে আকৃষ্ট করে এবং তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার সাহাবীবগ যে প্রকার মাধ্যমকেই অধিকতর কাজে লাগোনো সম্ভব ছিল তার সবগুলোকেই কাজে লাগিয়েছেন। অন্যান্য মাধ্যম ও উপকরণের কথায়ও যাব। স্বয়ং দৃশ্যগুলোকেও ইমাম এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যে মনে হবে যেন কোনো ঐতিহাসিক দৃশ্যকে মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যেই এভাবে সাজিয়েছেন যাতে কিয়ামত অবধি এক শিহরণ জাগানো দৃশ্য হিসাবে ইতিহাসে অক্ষয় থেকে যায়।
ইতিহাসে লেখা রয়েছে যে,যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবীরা বেঁচে ছিলেন,এমনকি তাদের একজন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ও আহলে বাইতের তথা ইমাম হোসাইন (আঃ) এর সন্তানবর্গ,ভাই-ভাতিজা প্রমুখের কোনো একজনকেও ময়দানে যেত দেননি। তাদের কথা ছিল,হে ইমাম! আমাদের দায়িত্বকে আগে পালন করার সুযোগ দিন। তারপর আমরা যখন থাকবো না তখন আপনি যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করবেন। অপরদিকে নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতও অপেক্ষায় ছিলেন কখন তাদের পালা আসবে। ইমামের সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি যখন শহীদ হন তখন নবী পরিবারের যুবকদের মধ্যে সহসা উলুধ্বণি পড়ে গেল। সবাই স্ব স্ব জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লেন। লেখা রয়েছে যেঃ
فَجَعَلَ يُودَعُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً
অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছিলেন,এক অপরের গলায় হাত রেখে পরস্পরের মুখে চুম্বন করছিলেন।
আহলে বাইতের যুবকদের মধ্যে সর্ব প্রথম যিনি ইমামের নিকট থেকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন তিনি হলেন তার যুবক পুত্র হযরত আলী আকবার। যার ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আঃ) সাক্ষ্যদান করেছেন যে দেহের গড়ণ,চেহারা-চিরত্র আর চলায় বলায় আলী আকবার ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অধিকতর সদৃশ। তিনি যখন কথা বলতেন মনে হতো যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা বলছেন। এত বেশী মিল ছিল যে ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজে বলেন,হে আল্লাহ! তুমিই ভালো জানো যে যখন আমরা নবীজীকে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়তাম তখন এই যুবকের দিকে তাকাতাম। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবির দর্পণ। এবার সেই যুবকই এলেন পিতার সম্মুখে।
বললেন,বাবা! আমাকে অনুমতি দিন। অনেক সাহাবী বিশেষ করে যুবকদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তারা যখন অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইমামের কাছে উপস্থিত হচ্ছিলেন তখন ইমাম কোনো না কোনো ভাবে তাকে নিঃরত করার জন্য ব্যাখ্যা তুলে ধরছিলেন। যেমন হযরত কাসিমের কাহিনী যা সকলের জানা রয়েছে। কিন্তু যখন হযরত আলী আকবার উপস্থিত হলেন তখন তিনি শুধুই কেবল স্বীয় মাথাকে নীচু করলেন। যুবক পুত্র ময়দানে রওনা হয়ে যায়। বর্ণিত রয়েছে যে ইমামের চক্ষুদ্বয় যখন অর্ধ নির্মিলিত অবস্থায় ছিলঃ
ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ نَظَرَ آئِسٍ
অর্থাৎ তিনি তার দিকে তাকালেন এমন ভঙ্গিতে যেভাবে একজন নিঃরাশ ব্যক্তি তার যুবক পুত্রের দিকে তাকায়।( আল - লুহুফ , পৃষ্ঠা 47 )
ইমাম নিঃরাশার সাথে তার যুবক পুত্রের দিকে তাকালেন,কয়েক ধাপ তার পিছে পিছেও এগিয়ে গেলেন। আর ঠিক এই সময়ে তিনি বলে ওঠেনঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো যে এমন এক যুবক আজ এদের বিরুদ্ধে রওনা হয়েছে যে ছিল তোমার নবীর চেহারার সাথে সবচেয়ে বেশি সদৃশ । অতঃপর তিনি ওমর ইবনে সা’ দকেও একটি কথা বলেন। উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে বললেন যেন ইবনে সা’ দ বুঝতে পারে। বললেনঃ
يَابْنَ سَعْدٍ قَطَعَ اللهُ رَحِمَكَ
অর্থাৎ,হে ইবনে সা’ দ! আল্লাহ যেন তোমার বংশকে নির্বংশ করে যেমনভাবে আমার এই সন্তান থেকে আমাকে নির্বংশ করলে।( আল - লুহুফ , পৃষ্ঠা 47 , মাকতালু আলী আকবার - মুকাররাম , পৃষ্ঠা 76 , মাকতালুল হোসাইন - মুকাররাম , পৃষ্ঠা 321 , মাকতালুল হোসাইন - খরাযমী , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 30 , বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড 45 , পৃষ্ঠা 43 )
ইমাম হোসাইন (আঃ) এর এই বদ্দোয়ার পর দুই তিন বছরের বেশী দেরী হয়নি,এর মধ্যেই মোখতার,ওমর ইবনে সা’ দকে হত্যা করেন। এমন সময়ে যখন ওমর ইবনে সা’ দের পুত্র মোখতারের দরবারে এসেছিল তার পিতার জন্য সুপারিশ করতে। ওমর ইবনে সা’ দের মস্তককে একটি কাপড়ে ঢেকে সভায় আনা হয় এবং মোখতারের সামনে রাখা হয়। তখনই তার পুত্র এসেছিল পিতার জন্য সুপারিশ করতে। একসময় বলা হলো যে মস্তকটি এখানে রাখা আছে সেটাকে তুমি কি চেন? যখন কাপড় সরিয়ে ফেলা হলো দেখতে পেল যে তারই বাবার মাথা। মনের অজান্তেই কখন সে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগলো। সাথে সাথে মোখতার নির্দেশ দিলেন,ওকেও ওর বাবর সাথে যুক্ত করে দাও।
এভাবেই হযরত আলী আকবার ময়দানে যাত্রা করেন। ঐতিহাসিকগণ সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন যে হযরত আলী আকবার অতুলনীয় সাহসিকতা আর বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। কিছু যুদ্ধ করার পর তিনি ফিরে আসনে তার মহান পিতার নিকটে যা ইতিহাসে একটি চিরন্তন ধাঁ ধাঁ হয়েই থাকবে যে কি কারণে তিনি ফিরে এসেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্যকি ছিল? এসে বললেন,বাব! বড়ই পিপাসা। পিপাসা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে । এই অস্ত্রের ভারও আমাকে পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে। এক কাতরা পানি যদি আমার গলায় স্পর্শ করে তাহলে আমি শক্তি সঞ্চার করে পুনরায় আক্রমণ চালাতে পারবো। এই কথাগুলো ইমামের কলিজায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি বলেন, পুত্র আমার! দেখ,আমার মুখ তোমার মুখের চাইেতও শুস্ক । তবে আমি তোমাকে ওয়াদা দিলাম যে শীঘ্রই তুমি তোমার নানা নবীর হাতে পানি পান করবে। এই যুবক আবারো চলেন ময়দানে এবং লড়াই চালিয়ে যান।
হামিদ ইবনে মুসলিম নাম্মী জৈনক ব্যক্তি ছিল হাদীসের রেওয়ায়েতকারী। কারবালার ময়দানে সে উপস্থিত ছিল একজন সংবাদদাতার মতো। অবশ্য যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেনি। তবে বেশিরভাগ ঘটনাবলীকে সে বর্ণনা করেছে। তার বর্ণনায় এসেছ যে,আমি এক ব্যক্তির পাশে ছিলাম। যখন আলী আকবার আক্রমণ করছিলেন তখন সবাই পালিয়ে যাচ্ছিল। এ দেখে লোকটি অসন্তুষ্ট হলো কারণ সে নিজেও একজন বীর। শপথ করে বললো,যদি ঐ যুবক আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে আমি ওর পিতাকে পুত্র হারানোর শোক বেদনায় নিমজ্জিত করবই। আমি তাকে বললাম,তোমার এতে কি কাজ। ছেড়ে দাও,শেষ পর্যন্ত তো তাকে হত্যা করা হবেই। সে বললো,না। আলী আকবার যখন অগ্রসর হলেন তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় লোকটি গুপ্ত হামলার মতো বর্শা দ্বারা এমন সজোরে আঘাত করলো যে আলী আকবার নিশ্চল হয়ে পড়লেন। হাতদুটি ঘোড়ার গলায় জড়িয়ে ধরে নিজের ভারসাম্য রাখার প্রচেষ্টা করলেন। এমন সময় চিৎকার করে বলে উঠলেন,
يَا اَبَتَاه هَذَا جَدِّي رَسُولِ اللهِ
অর্থাৎ,হে বাবা! এখনই আমি নানা রসূলকে মনের চোখ দ্বারা দেখতে পাচ্ছি পানি পান করছি।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড 45 , পৃষ্ঠা 44 , মাকতালুল হোসাইন খরাজমী , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 31 )
ঘোড়া হযরত আলী আকবারকে এমনভাবে শত্রুদের মাঝে নিয়ে গেল (যেহেতু বাস্তবে ঐ ঘোড়ার আর কোনো সওয়ারী ছিল না) যে এখানে এসে অদ্ভুত একটি কথা লেখা রয়েছে :
فَاحْتَمَلَهُ الْفَرَسُ اِلَي عَسْكَرِ الْاَعْدَاءِ فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ اِرْباً ارْباً
অর্থাৎ,অতঃপর ঘোড়া তাকে বহন করে নিয়ে গেল শত্রু সেনার অভ্যন্তরে। আর তারা তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছাড়ে।( মাকতালুল হোসাইন - মুকাররাম , পৃষ্ঠা 324 , মাকতালুল আওয়াসিম , পৃষ্ঠা 95 , বিহারুল আনোয়ার খণ্ড 45 , পৃষ্ঠা 44 , মাকতালুল হোসাইন - খরাজমী , খণ্ড 2 , পৃষ্ঠা 242 )
তাবলীগ (বা প্রচার) পদ্ধতি প্রসঙ্গে
হোসাইনী আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি দিক হচ্ছে এর তাবলীগ তথা প্রচারমূলক দিক। এখানে‘ তাবলীগ’ শব্দটি তার প্রকৃত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে,বর্তমান যুগে প্রচলিত অর্থে নয়। তাবলীগ বা প্রচার মানে জনগণের নিকট প্রচারকের নিজের বাণীকে পৌঁছে দেয়া এবং‘ ইসলাম প্রচার’ মানে স্বয়ং ইসলামকে পৌঁছে দেয়া। অন্যকথায়,মানুষের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়া। এবার দেখা দরকার যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার এ আন্দোলনে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন,বিশেষ করে যার তাবলীগি গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথেষ্ট প্রচারমূলক গুরুত্ব রয়েছে যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) এ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে স্বীয় লক্ষ্যকে এবং তার কন্ঠ থেকে ইসলামের যে প্রকৃত ফরিয়াদ বেরিয়ে আসছিলো তা সর্বোত্তমভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দেন।
এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আজকের দিনে যাকে‘ পদ্ধতি’ (method) বা‘ কর্মপদ্ধতি’ বলা হয়-যা আসলে এক বিদেশী পরিভাষা,সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।
বস্তুতঃ যে কোনো কাজে সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্বাচন। উদাহরণস্বরূপ,আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে,চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান,কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ বা আস্ত্রোপাচারকারীগণ পরস্পর থেকে পৃথক বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের কারো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অন্যদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে অধিকতর সাফল্যের অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান এর সন্ধিকাল সম্পর্কিত এক আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে,কালের একটি অধ্যায়কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে পুরনো বা প্রাচীন ও নতুন বা আধুনিক নামে অভিহিত করা চলে না,তবে একটি যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন বা আধুনিক যুগ বলে নামকরণ করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে ,জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগের সাথে এর আধুনিক যুগের পার্থক্য কী? আধুনিক যুগে বিজ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ও অবিশ্বাস্য ভাবে উন্নতি করেছে। মনে হচ্ছে যেন সহসাই বিজ্ঞানের চাকার সামনে থেকে একটি বাধাকে অপসারণ করা হয়েছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পথ চলতে শুরু করেছে,অথচ প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গতি ছিলো মন্থর। কিন্তু আধুনিক যুগে এরূপ দ্রুত গতির কারণ কী? তা কি এই যে,লুই পাস্তুর প্রমুখ আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীগণ বোক্বরাত (বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী),জালিনুস (বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী),ও ইবনে সীনার ন্যায় প্রাচীন বিজ্ঞানীগণের তুলনায় অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন? অন্যকথায়,এর কারণ কি এই যে,আধুনিক বিশ্বে এমন সব অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে প্রাচীন কালে যে ধরনের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে নি? না,মোটেই তা নয়। হয়তোবা আজকের দিনে এমন একজন লোকও পাওয়া যাবে না যে দাবী করবে যে,পাস্তুর বা অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানীর প্রতিভা এরিষ্টোটল,প্লোটো,ইবনে সীনা,বোক্বরাত,জালিলুস বা খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী’ র তুলনায় বেশী। তবে তা সত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাজের ও সাফল্যের গতি অনেক বেশী। এর রহস্য কী?
বলা হয়,এর রহস্য এই যে,বিজ্ঞানীদের কাজের পদ্ধতি সহসাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের গবেষণার পদ্ধতি যখন পরিবর্তিত হয়ে গেলো তখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির গতি বেড়ে গেলো। বস্তুতঃ কাজের পদ্ধতি সাফল্যের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এমনটাও হতে পারে যে,আপনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও সুচতুর কর্মঠ ব্যক্তির হাতে একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। কিন্তু তিনি সে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাফল্যের অধিকারী হলেন না। অতঃপর একই প্রতিষ্ঠানে এমন এক ব্যক্তিকে তার স্থলে নিয়োগ করলেন যিনি স্মরণশক্তি ,সচেতনতা,প্রতিভা ও কোনো কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সমপর্যায়ের নন,কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকতর উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলেন। এর কারণ এই যে,তার কাজের পদ্ধতি অধিকতর উত্তম।
এ প্রসঙ্গে আমরা অধিকতর সুস্পষ্ট উদাহরণ দিতে পারি। আমরা এ ধরনের বহু লোককে দেখেছি যাদের সচেতনতা,মেধা-প্রতিভা ও স্মরণশক্তি অনেক বেশী। কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের মাত্রা কম। অথচ এমন অনেক লোক শেখার ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের অধিকারী যাদের সচেতনতা,স্মরণশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রথমোক্তদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে,এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিদের কাজের পদ্ধতি অধিকতর উত্তম। উদাহরণস্বরূপ,একজন লোক প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী এবং তিনি দিনরাতে ষোল ঘন্টা পরিশ্রম করেন। কিন্তু তার কাজের ধরন কী? তিনি একটি গ্রন্থকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং এরপর সাথে সাথেই তিনি আরেকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অথচ এই প্রথম গ্রন্থটি এক বিষয়ের এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি ভিন্ন এক বিষয়ের। এরপর তিনি অন্য একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং পরে অন্য একটি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি এভাবে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেন। অন্য দিকে এক ব্যক্তি হয়তো আট ঘন্টার বেশী পড়াশুনা করেন না। কিন্তু তিনি যখন কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তখন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন;তাড়াহুড়া করে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি কোনো পঠণীয় বিষয়কে একবার পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। তিনি আরো একবার গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করেন। তিনি যে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছেন তার বিষয়বস্তু তার মস্তিস্কে প্রবেশ না করা পর্যন্তি তিন অন্য কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। তিনি অবশ্য এখানেই থেমে থাকেন না,বরং তিনি এ গ্রন্থে যে সব বিষয় অধ্যয়ন করেছেন তার মধ্যে যে সব বিষয়কে তিনি খুব ভালো জিনিস বলে দেখতে পেয়েছেন ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন সেগুলোকে কাগজের বুকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার অর্জিত জ্ঞানকে লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন যার ফলে সারা জীবনে তিনি যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই তাতে চোখ বুলালে বিষয়গুলো তার পুরোপুরি স্মরণ হবে। এভাবে তিনি একটি গ্রন্থের অধ্যয়ন ও তা থেকে নোট করার কাজ সমাপ্ত করার পর একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বিভিন্ন গ্রন্থ একই নিয়মে অধ্যয়ন করেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু দিন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ বিষয়ে অধিকতর অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন হয়ে যান। এরপর তিনি অন্য একটি বিষয়ের ওপরে গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের কাজ শুরু করেন।
এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আজ এ গ্রন্থ ,কাল ঐ গ্রন্থ ও পরশু অপর একটি বিষয়ের অধ্যয়ন করেন তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি খাবার খেতে এসে এখান থেকে এক লোকমা,ওখান থেকে এক লোকমা,অন্য এক ধরনের খাবার থেকে চার লোকমা,চতুর্থ এক ধরনের খাবার থেকে পাঁচ লোকমা ভক্ষণ করে। এভাবে সে তার পাকস্থলীকে ধ্বংসঠিকরে ফেলে। এতে তার কোনো ফায়দাই হয় না। বস্তুতঃ এ বিষয়টি কর্মপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
এভাবেই সঠিক ও প্রকৃত অর্থে তাবলীগ মানে জনগণের নিকট কোনো বাণী পৌঁছে দেয়া ও তাদেরকে বিষয়টির সাথে পরিচিত করে তোলা। তাদেরকে বাণীটির ব্যাপারে ওয়াকেফহাল করা,এতে বিশ্বাসী করে তোলা,তাদের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ তৈরী করা ও এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোনো বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কারণ,কেবল সঠিক পন্থার অনুসরণ করা হলেই একটি বাণীর প্রচার সফল হওয়া সম্ভব। সঠিক পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে যে ইতিবাচক ফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে শুধু তা-ই নয়,বরং তার বিপরীত ফল পাওয়া যাবে। মানুষ যখন কোনো বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং এরপর এ বিষয় সম্পর্কিত কোরআন মজীদের আয়াতের সন্ধান করে এবং এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে চিন্তাগবেষণা করে তখন সে দেখতে পায় যে,কোরআন মজীদের আয়াত থেকে এ সংক্রান্ত কী কী বিষয় ( POINTS) পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি প্রযোজ্য ,যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাবলীগ বা প্রচার।
পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোরআন মজীদ যে সব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেاَلْبَلَاغُ الْمُبِينُ (আল-বালাগুল মুবীন ) কথাটির ব্যবহার। অর্থাৎ অত্যন্ত সুক্ষ্ণ ভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হবে। এ পরিভাষায় যে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? এর লক্ষ্য হচ্ছে বাঞ্চিতভাবে,সহজ-সরলভাবে ও দুর্বোধ্যতা ছাড়াই বাণীটিকে পৌঁছে দিতে হবে যাতে শ্রোতা খুব সহজেই তা বুঝতে পারে।
কঠিন,জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা,অনেক বেশী পরিভাষা ব্যবহার করা এবং এমন সব বাক্য ব্যবহার করা যা বুঝার জন্য বছরের পর বছর পড়াশুনা করতে হবে-এটা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রচার পদ্ধতিতে ছিলো না। তিনি এমনই সহজ-সরল ও সুস্পষ্টভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরতেন যে,তা বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষীগণ যেমন বুঝতে পারতেন তেমনি নিরক্ষর লোকেরাও‘ তাদের অনুধাবন ক্ষমতা অনুযায়ী’ তা সঠিকভাবেই বুঝতে পারতো। (এটা বলছি না যে,সকলে একই মাত্রায় বুঝতে পারতো।)
যে মুবাল্লিগ বা দীন প্রচারক নবী-রাসূলগণের (আঃ) ভাষায় কথা বলতে চান এবং তাদের পথে পথ চলতে চান তার প্রচার অবশ্যই‘ বালাগুল মুবীন’ হতে হবে। এ হচ্ছে‘ মুবীন’ -এর তাৎপর্যের একটি দিক। তবে এখানে আরো কয়েকটি সম্ভাবনাও রয়েছে। (আর সম্ভবতঃ এ সম্ভাবনাগুলোর সবগুলোই সঠিক।) এ সম্ভাবনাগুলোর অন্যতম হচ্ছে‘ মুবীন’ মানে কোনোরূপ রাখঢাক না করে কথা বলা। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ (আঃ) কঠিন ও জটিল ভাষায় কথা বলতেন না শুধু তা-ই নয়,বরং লোকদের সাথে খোলাখুলি কথা বলতেন ও কোনোরূপ রাখঢাক না করে তাদের কাছে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তারা আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতেন না। তারা যদি মনে করতেন যে,কোনো বিষয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন তাহলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়ই তা তুলে ধরতেন। যেমন,তারা বলতেনঃ–
) اَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ(
‘‘ তোমরা কি সেই জিনিসের উপাসনা করছো যাকে নিজেরাই তৈরী করেছো?’’ (সূরা আস-সাফ্ফাতঃ 95)
প্রচারের ক্ষেত্রে কোরআন মজীদ দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কোরআনের নিজের ভাষায় তা হচ্ছেنُصْح (নুছহ)। আমরা সাধারণতঃ‘ নুছহ’ কে‘ কল্যাণ কামনা’ অর্থে অনুবাদ করি। অবশ্য এ অর্থটাও সঠিক। কিন্তু দৃশ্যতঃ‘ কল্যাণ কামনা’ ‘ নুছহ’ -এর আক্ষরিক অর্থ নয়,বরং‘ নুছহ’ শব্দের অর্থটির আবশ্যিক অনুষঙ্গ । দৃশ্যতঃنُصْح (নুছহ) শব্দটিغَشّ (গ্বাশ) শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আপনি কারো কাছে দুধ বিক্রি করতে চান। হয়তো আপনি তাকে খাঁটি দুধ সরবরাহ করবেন। অথবা,খোদা না করুন,পানি মেশানো দুধ সরবরাহ করবেন। অথবা আপনি কাউকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চান;এ ক্ষেত্রে হয়তো আপনি তাকে খাঁটি স্বর্ণের মুদ্রা দেবেন (যাতে খাদের পরিমাণ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্র মাত্রায় থাকে)। অথবা,খোদা না করুন,হয়তো অনেক বেশী খাদ মেশানো (গ্বাশ্যুক্ত ) স্বর্ণের মুদ্রা দেবেন।‘ নুছহ’ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত‘ নাছেহ’ (নুছহকারী) যে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার অধিকারী।‘ তাওবাতুন নাছুহ’ মানে খালেছ তওবা। মুবাল্লিগ ( প্রচারক) কে নাছেহ,খালেছ ও মোখেলছ (একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার অধিকারী) হতে হবে। অর্থাৎ তিনি যখন দীনের দাওয়াত দেবেন তখন তার অন্তরে শ্রোতার কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না।
আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সততার পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা। বলা হয়েছেঃ
اَلنَّاسُ کُلُّهُمْ هَالِکُونَ اِلَّا الْعَالِمُونَ وَ الْعَالِمُونَ هَالِکُونَ اِلَّا الْعَامِلوُنَ وَالْعَامِلُونَ هَالِکُونَ اِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَی خَطَرٍ عَظِيمٍ.
‘‘ সকল মানুষই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র আলেমগণ ছাড়া,আলমদের সকলেই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র আমলকারীগণ ছাড়া,আমলকারীদের সকলেই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র মোখলেছ (একনিষ্ঠ) গণ ছাড়া,আর মোখলেছগণ বিরাট ঝুকির মধ্যে রয়েছে।’’
বর্ণিত হয়েছে যে,মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দী (আল্লাহ তার মকামকে উচ্চতর করুন) যখন শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়েন (যার দু’ একিদন পরে তিনি ইন্তেকাল করেন) তখন যারা তার কাছে ছিলেন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেনঃ‘‘ আপনার নিজের স্মরণের জন্য এবং অন্যদের নিছহতের জন্য কিছু বলুন।’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ জনাব,গেলাম কিন্তু কিছুই করলাম না,আর স্তুপীকৃত করলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে জমা করি নি।’’ উপস্থিত ব্যক্তিদের একজন মনে করলেন যে,তিনি এটা বিনয় বশতঃ বলছেন,তাই তিনি বললেনঃ‘‘ হুজুর,আপনি এ কথা কেন বলছেন?’’ তারপর তিনি বলতে লাগলেন যে,আল– হামদুলিল্লাহ আপনি এই করেছেন,সেই করেছেন,মসিজদ তৈরী করেছেন,মাদ্রাসা তৈরী করেছেন,দ্বীনী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন ইত্যাদি। তিনি একথা বললে আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দী উপস্থিত সকলের দিকে ফিরে নিম্নোক্ত হাদীছটি পাঠ করলেন এবং নীরব হলেনঃ
خَلِّصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ
‘‘ তোমার আমলকে নির্ভেজাল করো, কারণ সমালোচক সেই রকেমর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ।’’ ( মাওয়ায়িযুল আদিদাহ , পৃষ্ঠাঃ 124 )
বস্তুতঃ ইখলাছ (একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা) কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে দৃশ্যতঃ সকল নবী-রাসূলের (আঃ) জবানীতেই বলা হয়েছেঃ
) مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ(
‘‘ আমি এর ( দ্বীনের দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাই না।’’ (সূরা সোয়াদঃ 86) অর্থাৎ যেহেতু আমি তোমাদের কল্যাণকামী সেহেতু এ কারণেই তোমাদের নিকট দ্বীনের প্রচার করছি। বস্তুতঃ নাছেহ বা কল্যাণকামীর জন্য পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা (ইখলাছ) থাকা অপরিহার্য।
অন্য একটি বিষয় হচ্ছে মোতাকাল্লেফ (مُتَکَلِّفْ ) না হওয়া।تَکَلُّفْ (তাকাল্লুফ ) শব্দটি (যা থেকেمُتَکَلِّفْ শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষেتَکَلُّفْ -এর অর্থ নিজের সাথে বাঁধা বা জড়িত করা। অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো কিছুকে জোর করে নিজের সাথে বাঁধে তখন সে কাজকেتَکَلُّفْ বলা হয়। এটা কথা বা বক্তব্য সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়। কোনো লোক যখন সহজ-সরল ও গতিশীল তথা প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলার পরিবর্তে কঠিন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলী ব্যবহার করে তখন তাকে মোতাকাল্লেফ বলা হয়।
হাদীছে আছে,এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে কথা বলতে গিয়ে কঠিন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলী ব্যবহার করছিলো। তখন রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ
اَنَا وَ اَتْقِيَاءُ اُمَّتِی بُرَآءٌ مِنَ التَّکَلُّفِ
‘‘ আমি ও আমার উম্মাতের মধ্যকার মুত্তাকী লোকেরা তাকাল্লুফ থেকে মুক্ত ।’’
মূলতঃ তাকাল্লুফ ও ফাছাহাত (فَصَاحَتْ -প্রঞ্জলতা) সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রকৃতপক্ষে ফাছাহাত মানেই হচ্ছে ভাষার গতিশীলতা-যার দাবী হচ্ছে এই যে,তা কঠিনতা,দুর্বোধ্যতা ও জড়তা থেকে মুক্ত হবে। দ্বীন প্রচার সম্পর্কে কোরআন মজীদে নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর জবানীতে এরশাদ হয়েছেঃ
) مَا اَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِينَ(
‘‘ আমি মোতাকাল্লেফদের (যারা কথার ফুলঝুরি ছুটায়) অন্তর্ভুক্ত নই।’’ (সূরা সোয়াদঃ 86)
মুফাসসিরগণের ভাষ্য অনুযায়ী,এ বাকে বাহ্যতঃ এটা বলতে চাওয়া হয় নি যে,আমি কথা বলার ক্ষেত্রে মোতাকাল্লেফ নই। বরং এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে,আমি যা বলছি তার ব্যাপারে মোতাকাল্লেফ নই অর্থাৎ আমি এমন নই যে,যে বিষয়ে জানি না জোর করে সে বিষয়ে জানার ভান করে কথা বলবো। আমার কাছে সুস্পষ্ট নয় এমন কোনো বিষয়ে মানুষের সামনে কথা বলছি না।
উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর-গ্রন্থ‘‘ মাজমা‘ উল বায়ান’’ -এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ উদ থেকে বর্ণিত হয়েছে,তিনি বলেনঃ
اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ.
‘‘ হে লোক সকল! যে ব্যক্তি যা জানে সে যেন তা বলে,আর যা জানে না সে ব্যাপারে যেন বলেঃ আল্লাহই অধিকতর অবগত। নিঃসন্দেহে এ-ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত,যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে বলবে যে,আল্লাহই অধিকতর অবগত।’’ অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ
) قُلْ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِينَ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলুন,আমি এর ( দ্বীনের দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি মোতাকাল্লেফদের (যারা কথার ফুলঝুরি ছুটায়) অন্তর্ভুক্ত নই।’’ ( মাজমাউল বাইয়্যান , খণ্ড 8 , পৃষ্ঠা 486 )
এ থেকে সুস্পষ্ট যে,হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ উদ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করেন যে,যা জানেন তা লোকেদেরকে বলবেন এবং যা জানেন না তা বলবেন না। বরং বলবেন যে,এ বিষয়ে জানি না।
বিখ্যাত সুবক্তা ইবনে জওযী একবার তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বারে বসা ছিলেন। এ সময় একজন মহিলা এসে তাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। ইবনে জওযী জবাবে বললেনঃ‘‘ আমি জানি না।’’ মহিলা বললেনঃ‘‘ তুমি যখন জানো না তখন তিন ধাপ উপরে উঠেছো কেন?’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ এই তিন ধাপ উপরে উঠেছি সেই সব বিষয়ে বলার জন্য যেগুলো আমি জানি কিন্তু আপনি জানেন না। আর যে সব বিষয়ে আমি জানি না সেগুলোর জন্য যদি মিম্বার তৈরী করা হতো তাহলে তা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।’’
শেখ আনছারী ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের অন্যতম। তিনি একদিকে যেমন ফিকাহ ও উছুলের ক্ষেত্রে প্রকৃতই একজন মোহাক্কেক (গবেষক) ও প্রথম শ্রেণীর আলেম ছিলেন,তেমনি ছিলেন তাকওয়ার অধিকারী। এ কারণে অনেকে তার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অতিশয়োক্তি করে ফেলতেন। যেমন,বলা হতোঃ হুজুরের কাছে যা কিছুই জিজ্ঞেস করো না কেন,তা-ই তার জানা আছে;এটা অসম্ভব যে,কোনো বিষয়ে তিনি জানবেন না। (তিনি ছিলেন শুশ্তারের অধিবাসী। কথিত আছে যে,তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খুযেস্থানের আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলতেন।) তাকে যে সব শারয়ী বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো তিনি মুজতাহিদ হওয়া সত্বেও কোনো কোনো সময় তার কোনো বিষয় তার মনে থাকতো না। যখনই কোনো প্রশ্নের উত্তর তার মনে না থাকতো তখন তিনি অত্যন্ত জোরে বলতেনঃ‘‘ জানি না।’’ এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে,শ্রোতাগণ ও তার শিষ্যগণ যাতে বুঝতে পারেন যে,কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে তা স্বীকার করার মধ্যে লজ্জার কোনো কারণ নেই। অন্য দিকে তাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো সে সম্পর্কে জানা থাকলে তিনি আস্তে জবাব দিতেন এবং তার কন্ঠস্বর কেবল ততটুকু উচু হতো যাতে প্রশ্নকর্তা বুঝতে পারে। কিন্তু জানা না থাকলে জোরে জোরে বলতেনঃ‘‘ জানি না,জানি না,জানি না।’’
কোরআন মজীদ নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে অপর যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তা হচ্ছে বিনয় (যা অহঙ্কারের বিপরীত)। যে ব্যক্তি লোকদের কাছে কোনো বাণী পৌঁছাতে চান,বিশেষ করে মহান আল্লাহ বাণী পৌঁছাতে চান তার অবশ্যই পুরোপুরি বিনয়ী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ তার জন্যে আমিত্বের অহঙ্কার বর্জন করা এবং লোকেদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। তাকে বিনয়ের মূর্ত প্রতীক হতে হবে। কোরআন মজীদে হযরত (আঃ)-এর জবানীতে তার কওমের একদল লোককে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ .
) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ ( .
‘‘ এটা কি তোমাদেরকে বিস্মিত করছে যে,তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ওপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যিকর (আল্লাহর বাণী) এসেছে?’’ ( সূরা আ ’ রাফঃ 61 )
উপরোক্ত আয়াতে‘‘ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে’’ (مِنْ رَبِّکُمْ ) কথাটির ব্যবহার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । এ কথাটির ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে,হযরত (আঃ)‘‘ আমার প্রতিপালক’’ বলতে চান নি। কারণ,এরূপ বললে তার মধ্যে এমন এক ভাব প্রকাশ পেতো যে,তিনি তার প্রতিপালকের দিকে অন্যদেরকে আহবান করছেন। অন্য কথায়,তারা এমন তুচ্ছ লোক যে‘‘ প্রতিপালক’’ কে‘‘ তোমাদের প্রতিপালক’’ বলা চলে না। এরপর তিনি বলেন‘‘ তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ওপর’’ عَلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ অর্থাৎ আমি নিজেও তোমাদেরই একজন।
আপনারা লক্ষ্য করুন এ আয়াতে একজন নবীর কতখানি বিনয়ের পরিচয় রয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يوُحَی اِلَیَّ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলুন,অবশ্যই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ,তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয়।’’ অর্থাৎ তোমাদের মতো একজন মানুষের ওপরই এ ওহী নাযিল হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ
) أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (
‘‘ অবশ্যই তোমোদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ । অতএব,যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন উত্তম কর্ম সম্পাদন করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’’ ( সূরা কাহাফঃ 110 )
দীন প্রচারের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হচ্ছে বন্ধু সুলভ ও নম্র আচরণ করা এবং রূঢ়তা পরিহার করা। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কোনো বাণী পৌঁছাতে চায়,বিশেষ করে যে মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে চায় এবং কামনা করে যে,তারা তা পছন্দ করুক ও এর ওপর ঈমান আনুক,তাকে অবশ্যই নম্র ভাষী হতে হবে এবং নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।
বস্তুতঃ বস্তুগত সামগ্রীর ন্যায় কথাও নরম ও শক্ত হতে পারে। কোনো কোনো সময় মানুষ কোনো বক্তব্য সহজভাবেই গ্রহণ করে ঠিক যেভাবে কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য সহজেই গলাধঃকরণ করতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ একটি বক্তব্য গ্রহণ করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়;এটা যেন কোনো কাঁটাযুক্ত বস্তু গলাধঃকরণের ন্যায়। কথা যদি খুবই কর্কশ হয় বা তাতে যদি বহু রকমের আকার-ইঙ্গিত থাকে তাহলে লোকদের পক্ষে তা গ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।
মহান আল্লাহ যখন হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) কে ফেরাউনের নিকট পাঠালেন তখন তাদেরকে যেসব নির্দেশ দান করেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলো দাওয়াতের পদ্ধতি। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (
‘‘ আর তার সাথে নরমভাবে কথা বলো,হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’’ (সূরা তা হাঃ 44) অর্থাৎ যদিও ফেরাউন সার্বিক অর্থেই একজন উদ্ধত অহঙ্কারী লোক তথাপি তার সামনেও এবং এ ধরনের যে কোনো লোকের সামনেই নম্রভাবে কথা বলতে হবে এবং নম্র ভাষায় আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে হবে। কারণ,এমনও হতে পারে যে,সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তার প্রতিপালককে ভয় করবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) ফেরাউনের নিকট সেভাবেই নম্রতার সাথে দাওয়াত পেশ করেন,কিন্তু ফেরাউন সে দাওয়াত গ্রহণ করার মতো লোক ছিলো না।
মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ
) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(
‘‘ আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি নম্র । আর আপনি যদি তাদের প্রতি কঠোরহৃদয় হতেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব,আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমার আবেদন করুন। আর (সামষ্টিক) কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন,অতঃপর যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন;নিঃসন্দেহে আল্লাহ (তার ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’’ (সূরা আল ইমরানঃ 159)
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে নম্র ভাবে কথা বলতেন। তার আচরণ ও কথা উভয়ই ছিলো নম্র এবং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি রূঢ়তা পরিহার করে চলতেন। তার কথা বলার ধরন সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে,তিনি কীভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে রূঢ়তা পরিহার করে চলতেন। কথা ও আচরণে এ নম্রতার গুরুত্ব এতই বেশী যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র কোরআন মজীদের বাহক,এত সব মু‘ জিযা ও অন্য সকল গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘ আলা বলছেন যে,আপনি নম্রতার অধিকারী না হলে ও কঠোর হৃদয় হলে লোকেরা আপনার চারদিক থেকে সরে যেতো;বস্তুতঃ আপনার নম্রতা দীনের প্রচার ও লোকদের হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে-তাদের আল্লাহর পরিচয় লাভ ও ঈমান আনয়নে বিরাট প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
শেখ সা‘ দী বলেনঃ
درشتی و نرمی بهم در به است |
چو رَگزن که جرّاح و مرهم نه است |
‘‘ কঠোরতা ও নম্রতার একত্র সমাবেশই উত্তম
শিঙ্গা লাগাতে যখম করে যে মলমও লাগায় সে।’’
অবশ্য এখানে আমরা কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। এ দ্বিপদীটি এ কারণে উদ্ধৃত করেছি যে,এ আমাদের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি। নম্রতার সাথে কঠোরতা থাকারও কি প্রয়োজন নেই? বস্তুতঃ রূঢ়তা ও সহিংসতা এবং কঠোরতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ঝর্ণাধারার তলেদেশে যেসব নুড়ি পাথর পড়ে আছে তার ওপর দিয়ে বছরের পর বছর প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং এগুলোকে ক্ষয় করে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যখন ঝর্ণার তলদেশ থেকে এরূপ নুড়ি পাথর হাতে তুলে নেয় সে দেখতে পায় যে,সেগুলো আগের মতোই শক্তও কঠিন,কিন্তু মসৃণ-যা ধরলে মানুষের হাতে সামান্যতম কষ্টও অনুভূত হয় না। শুধু তা-ই নয়,বরং মনে হবে যে,নিজের গায়ের জামার ওপরে হাত বুলালে যত কর্কশতা অনুভূত হয় এসব নুড়ি পাথরের ওপর হাত বুলালে তত কর্কশতাও অনুভব করে না। যে তলোয়ারকে রেত দিয়ে অনেক বেশী ঘষা হয়েছে তাতেও এক ধরনের নম্রতা ও মসৃণতা আছে,এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এরূপ তলোয়ারকে স্পিং-এর ন্যায় বাঁকা করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কঠিন বটে কঠোরতার অধিকারী হওয়া,দৃঢ়তার অধিকারী হওয়া,বীরত্বের অধিকারী হওয়া ও আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করা কর্কশতা ও সহিংসতা থেকে ভিন্ন বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিকে যেমন লোকদের সাথে আচরণ ও কথা বলার ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন,অন্য দিকে স্বীয় পথের ব্যাপারে ছিলেন আপোসহীন। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতেন না।
দীন প্রচারকের আরেকটি গুণ হচ্ছে সাহসিকতা। দীন প্রচারকদের এ গুণ সম্পর্কে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ
) اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا الله( .
‘‘ যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয় ও তাকে ভয় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করে না।’’ (সূরা আহযাবঃ 39) বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে ভয় করেন বলেই তার বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক করেন না এবং তাতে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করেন না,সত্য পথ থেকে বঞ্চিত হন না। কিন্তু দীন প্রচারকের একটি গুণ যে,
) لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا الله(
(আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করে না।)-এ বৈশিষ্ট্য এখন খুব কম লোকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।
নবী-রাসূলগণ (আঃ) কর্তৃক দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে,তারা বলতেনঃ দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। তারা বলতেনঃ আমরা আল্লাহর বান্দা,আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর বাণীর বাহক। যাজকরা যেমনটি করতেন-এবং সম্ভবতঃ এখনো করেন-নবী-রাসূলগণ (আঃ) সেভাবে লোকেদেরকে সরাসরি বেহেশত বা দোযখের সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য আগমন করেন নি। তারা এ ধরনের সনদ দান করতেন না যদিও তাদের নবী-রাসূল হওয়ার ব্যাপারে তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। বরং তারা সাধারণভাবে বিষয়াদি তুলে ধরতেন। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করতো যে,আমার শেষ পরিণতি কেমন হবে? তাহলে তারা জবাব দিতেনঃ আল্লাহ জানেন। গুপ্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেও তারা বলতেনঃ আল্লাহ জানেন;তোমার শেষ পরিণতি কী হবে স্বয়ং আল্লাহ তা‘ আলাই ভালো জানেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী ওসমান বিন মায‘ উন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরেতর পর পরই তিনিও হিজরত করেন। তিনি ছিলেন মদীনায় ইন্তেকালকারী প্রথম মুহাজির। তার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জান্নাতুল বাকী‘ তে দাফন করার জন্য নির্দেশ দেন এবং সেদিন থেকেই জান্নাতুল বাকী‘ গোরস্থানে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান বি মায‘ উনকে খুবই ভালোবাসতেন এবং সকলেরই তা জানা ছিলো।
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ)‘‘ নাহজুল বালাগ্বা’’ য় এরশাদ করেনঃ
کَانَ لِی فَبِمَا مَضَی اَخٌ فِی اللهِ، وَ کَانَ يُعَظِّمُهُ فِی عَيْنِی صِغَرُ الدُّنْيَا فِی عَيْنِهِ.
‘‘ অতীতে আমার একজন দীনী ভাই ছিলো আর যে জিনিস তাকে আমার চোখে মহান করে তুলে ধরে তা হচ্ছে ,তার চোখে এ দুনিয়াটা ছিলো খুবই তুচ্ছ।’’ ( নাহজুল বালাগা , হিকমাতঃ 281 , পৃষ্ঠাঃ 1225 )
‘‘ নাহজুল বালাগ্বা’’ র ভাষ্যকারগণ বলেছেন,এখানে হযরত আমীরুল মু’ মিনীন তার দীনী ভাই বলতে ওসমান বি মায‘ উনকে বুঝিয়েছেন। হযরত আমীরুল মু’ মিনীনের পুত্রদের একজনের নাম ওসমান। তার নামকরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি জন্ম গ্রহণ করলে হযরত আমীরুল মু’ মিনীন বলেনঃ আমি আমার ভাই ওসমান বি মায‘ উ-এর নামে তার নামকরণ করবো। এভাবে তিনি ওসমান বি মায‘ উ-এর স্মৃতিকে সদাজাগ্রত রাখতে চান।
এরূপ একজন ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তখন একজন আনসারের গৃহে জীবন যাপন করতেন। সে গৃহে একজন মহিলা ছিলেন যিনি তার খেদমত করতেন যার নাম ছিলো উম্মে‘ আলা;সম্ভবতঃ তিনি তার আনসার ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান বি মায‘ উ-এর নামাযে জানাযা পড়ার জন্য এলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই সব কাজ করেন যা তিনি তার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বেলায় করতেন। সহসা উম্মে‘ আলা ওসমান বি মায‘ উন-এর লাশের দিকে মুখ করে বললেনঃ هَنِيّاً لَکَ الْجَنَّةُ ’‘ বেহেশত তোমার জন্য উপভোগ্য হোক।’’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে‘ আলার দিকে ফিরে কঠোর কণ্ঠে বললেনঃ‘‘ কে তোমার নিকট এহেন অঙ্গীকার করেছে?’’ উম্মে‘ আলা বললেনঃ‘‘ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আপনার সাহাবী। যেহেতু আপনি তাকে এত ভালোবাসতেন এ কারণে আমি এ কথা বলেছি।’’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ
) قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا اَدْرِی مَا يُفْعَلُ بِی وَ لَا بِکُمْ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলে দিন,আমি নতুন ধরনের কোনো রসূল নই;আমি জানি না আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে।’’ (সূরা আহকাফঃ9) এর তাৎপর্য অত্যন্ত সুগভীর। অনুরূপভাবে সূরা আল-জিন-এর শেষ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ
) قُلْ اِنِّی لَا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرّاً وَ لَا رَشَداً. قُلْ اِنِّی لَنْ يُجِيرَنِی مِنَ اللهِ اَحَدٌ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ( .
‘‘ (হে রাসূল!) বলে দিন,তোমাদের ক্ষতি করার বা কল্যাণ করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। বলে দিন,আল্লাহর মোকাবিলায় কেউই আমাকে আশ্রয় দান করতে সক্ষম হবে না এবং আমি তার নিকটে ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাবো না।’’ ( সূরা জিনঃ 21 - 22 )
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রচার পদ্ধতির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লোকদের অবস্থার পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা। জাহেলিয়াতের যুগে আরব জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের শ্রেণীপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। তখন এমনকি দরিদ্রদেরকেও মানুষ বলে গণ্য করা হতো না,দাস-দাসীদের মানুষ গণ্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তৎকালীন অভিজাত লোকেরা-কোরআন মজীদে যাদেরকে মালা’ (مَلأ ) বলা হয়েছে,তারা নিজেদেরকে সব কিছুর মালিক-মোখতার ও অধিকারী বলে মনে করতো এবং যাদের কিছুই ছিলো না তাদের কিছু পাবার অধিকার আছে বলে মনে করতো না। শুধু তা-ই নয়,তারা এটা মনে করতো না এবং স্বীকার করতো না যে,তারা এ দুনিয়ার বুকে সব কিছুর অধিকারী হলেও এবং অন্যরা কিছুরই অধিকারী না হলেও পরকালীন জীবনে হয়তো এর বিপরীত অবস্থা হতে পারে। বরং তারা বলতো যে,দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের অবস্থার নিদর্শন;যেহেতু দুনিয়ার জীবনে আমরা সব কিছুর অধিকারী,সেহেতু তা এটাই প্রমাণ করে যে,আমরা আল্লাহ তা‘ আলার প্রিয়;আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং এ কারণেই আমাদেরকে সব কিছু দিয়েছেন। অতএব,আখরাতের অবস্থাও এমনই হবে;তোমরাও আখরাতে এ রকম অবস্থারই সম্মুখীন হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে হতভাগ্য সে পরকালীন জীবনেও হতভাগ্য ।
আরবের অভিজাত লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতোঃ তোমার কাজে ত্রুটি কোথায় জানো? তুমি জানো,কেন আমরা তোমার রিসালাতের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত নই? এর কারণ হলো এই যে,তুমি নীচ স্তরের ও ইতর শ্রেণীর লোকেদেরকে তোমার চারদিকে জমায়েত করেছো। এদেরকে দূরে সরিয়ে দাও,তখন আমরা অভিজাত লোকেরা তোমার কাছে চলে আসবো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন,
) وَ مَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ( .
‘‘ আমি মু’ মিনদেরকে বিতাড়নকারী নই।’’ (সূরা শুআরাঃ 114) অর্থাৎ আমি এমন লোক নই যে,এই লোকেরা আমার ওপর ঈমান আনা সত্ত্বেও কেবল দরিদ্র ও ক্রীতদাস হওয়ার কারণে আমি তাদেরকে আমার কাছ থেকে বিতাড়িত করবো। আল্লাহ তা‘ আলা অন্য এক আয়াতেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ .
) وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَ الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.(
‘‘ (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সকাল-বিকাল তাকে ডাকে।’’ (সূরা আনআমঃ 52) অর্থাৎ এতে অভিজাত লোকেরা যদি আপনার কাছ থেকে সরে যায় তো যাক;ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে অবশ্যই তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতে হবে।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রবর্তিত এবং তার নিজের জীবনে আচরিত একটি নিয়ম ছিলো এই যে,প্রথমতঃ তার মজলিসে বসার ক্ষেত্রে মর্যাদাগত উুঁচু-নীচু অবস্থার অস্তিত্ব ছিলো না;সাধারণতঃ তার মজলিসে আগমনকারীরা গোল হয়ে বসতেন। ফলে মর্যাদাগত উঁচু-নীচু অবস্থার সৃষ্টি হতো না। দ্বিতীয়তঃ তিনি মজলিসে প্রবেশ করলে লোকেদেরকে তার সম্মানার্থে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন যে,এটা আ‘ জামীদের অর্থাৎ অনারবদের রীতি। তিনি আরো বলতেনঃ যে ব্যক্তি যখনই মজলিসে প্রবেশ করবে সে যে জায়গাই খালি পাবে সেখানেই বসে পড়বে;লোকেরা যেন কাউকে সম্মানজনক জায়গায় তথা মর্যাদাগত বিচারে উচ্চতর বিবেচিত স্থানে,যেমনঃ সামনে,বসতে দেয়ার জন্যে তাদের জায়গা থেকে সরে বসতে বাধ্য না হয়। কারণ,এটা ইসলামের রীতি নয়।
একবার ইসলাম গ্রহণকারী একজন অভিজাত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে বসে ছিলেন। এ সময় জীর্ণবাস পরিহিত একজন গরীব লোক মজলিসে প্রবেশ করলেন এবং উক্ত অভিজাত ব্যক্তির পাশে খালি জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দরিদ্র ব্যক্তি সেখানে বসে পড়ার সাথে সাথেই অভিজাত ব্যক্তি জাহেলিয়াত যুগের অভ্যাস অনুযায়ী নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে বসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন;তিনি অভিজাত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি এরূপ করলে কেন? তুমি কি এ ভয়ে সরে গেলে যে,তোমার ধনসম্পদ থেকে কিছুটা তার গায়ে লেগে যাবে? অভিজাত ব্যক্তি জবাব দিলেনঃ না,হে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তুমি কি এ ভয় করেছো যে,তার দারিদ্রের কিছুটা তোমার গায়ে লেগে যাবে? অভিজাত ব্যক্তি বললেনঃ না,হে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি এমন করলে কেন? তখন অভিজাত ব্যক্তি বললেনঃ আমি ভুল করেছি;অন্যায় করেছি। এ ধরনের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ আমি আপনার এই মজলিসেই আমার সমস্ত ধন সম্পদের অর্ধেক আমার এই মুসলমান ভাইকে দান করলাম। তখন উপস্থিত লোকেরা তার দরিদ্র মু’ মিন ভাইকে বললেনঃ এবার তোমার সম্পদ নিয়ে নাও। জবাবে দরিদ্র ব্যক্তি বললেনঃ না,নেবো না। উপস্থিত লোকেরা বললেনঃ তোমার তো ধন সম্পদ নেই,তাহলে নেবে না কেন?
তিনি বললেনঃ ভয় করছি যে,তা গ্রহণ করলে একদিন হয়তো এই ব্যক্তির ন্যায় অহঙ্কারী হয়ে পড়বো।
দীন প্রচারের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হচ্ছে ধৈর্য-স্থৈর্য ও দৃঢ়তা। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) فَاصْبِرْلِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ( .
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনি আপনার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করুন এবং সেই মাছওয়ালার (ইউনুসের) ন্যায় হবেন না।’’ (সূরা নূন ওয়াল কালামঃ 48) আল্লাহ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন :
) فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ.(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনি দৃঢ়তার অধিকারী রাসূলগণের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করুন।’’ ( সূরা আহকাফঃ 35 ) আরো এরশাদ হয়েছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ( .
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে অবিচল থাকুন।’’ ( সূরা হূদঃ 112 ) . فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ . কথাটি দুটি সূরায় এসেছেঃ সূরা আশ্-শূরায় এবং সূরা-হূদে কথাটি এভাবে এসেছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি নিজে এবং আপনার সঙ্গী-সাথী তাওবাকারীগণ অবিচল থাকুন।’’ ( সূরা হূদঃ 112 ) আর সূরা আশ-শূরায় কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে এ আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি এরশাদ করেছেনঃ
شَيَّبَتْنِی سُورَةُ هُودٍ
‘‘ সূরা হূদ আমার দাড়িকে সাদা করে দিয়েছে।( মাজমাউল বায়ান , খণ্ড 5 , পৃষ্ঠা 140 ) যেখানে বলা হয়েছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি নিজে এবং আপনার সঙ্গী-সাথী তাওবাকারীগণ অবিচল থাকুন।’’ তবে কেবল আমাকেই বলা হয়নি,বরং স্বয়ং আমার ও অন্যদের কথা বলা হয়েছে;বলা হয়েছেঃ তাদেরকেও অবিচল রাখো।’’
এবার আমরা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) প্রসঙ্গে ফিরে যাবো এবং তার প্রচার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দেবো।
আবু আব্দুল্লাহ হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার আন্দোলন ও সংগ্রামে এমন কতগুলো কাজ করেন যেগুলোকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা চলে। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা রণাঙ্গনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। অবশ্য এটা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে যে,মহররমের নবম দিবস (তাসূ‘ আ) উপলক্ষে হযরত আবুল ফজল আব্বাস (সালামুল্লাহি আলাইহ)কে স্মরণ করা হয়।
হযরত আবুল ফাজল আব্বাস-এর মর্যাদা অত্যন্ত। আমাদের নিস্পাপ ইমামগণ বলেছেনঃ
. اِنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَغْبَطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ.
‘‘ অবশ্যই আল্লাহর নিকট আব্বাসের মর্যাদা এমন যে,সমস্ত শহীদ তাতে গর্ব করবে।’’ ( আবসারুল আইন ফি আনসারিল হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ 27 ; বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড 44 , পৃষ্ঠা 29 ; আমালী সাদুক , মজিলসঃ 70 , নম্বরঃ 10 ) দুঃখের বিষয় এই যে,ইতিহাস এ মহান শহীদ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে নি। অর্থাৎ কেউ যদি তার জীবন কাহিনী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করতে চায় তাহলে তিনি যথেষ্ট তথ্য খুজে পাবেন না। কিন্তু অনেক বেশী তথ্যের প্রয়োজন কী? ক্ষেত্রবিশেষে একজন মানুষের জীবনের একটি দিন বা দু’ টি দিন বা পাঁচ দিনের ঘটনাবলী-যার পূর্ণ বিবরণ হয়তো পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হবে না,এমনই প্রোজ্জ্বল হতে পারে যে,যা সেই ব্যক্তির এমন মর্যাদার পরিচায়ক যার গুরুত্ব কয়েক ডজন খণ্ড সম্বলিত জীবনী গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশী। আর হযরত আবুল ফজল আব্বাস ছিলেন এ ধরনেরই একজন ব্যক্তি ।
কারবালার ঘটনার সময় আবুল ফজল আব্বাসের বয়স ছিলো প্রায় 45 বছরের মতো। তিনি ছিলেন কয়েক জন সন্তানের পিতা;এদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব যিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে,একিদন হযরত ইমাম যায়নুল আবদীন (আঃ) তাকে দেখলেন;তখন কারবালার ঘটনাবলী তার মনে পড়ে গেলো এবং ইমামের’ চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। .
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ)-এর শাহাদাতের সময় আবুল ফজল আব্বাস ছিলেন চৌদ্দ বছরের কিশোর।‘‘ নাসেখুত তাওয়ারীখ’’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,আবুল ফজল আব্বাস সিফফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর ছিলেন (মোটামুটি বারো বছরের ছিলেন,কারণ,আমীরুল মু’ মিনীনের শাহাদাতের প্রায় তিন বছর আগে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়),সেহেতু আমীরুল মু’ মিনীন তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেন নি। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে,সিফফীনের যুদ্ধের সময় যদিও তিনি বালক মাত্র ছিলেন তথাপি তিনি এক কালো রঙ্গের ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিলেন। এর বেশী কিছু জানা যায় না। তবে এ বিষয়টি অনেকেই লিখেছেন। যুদ্ধ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে যে,আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) এক সময় তার ভাই‘ আক্বীলকে বলেনঃ‘‘ আমার জন্য এমন একজন স্ত্রী নির্বাচন করে দাও যে বীর বংশধর জন্ম দেবে।’’ ‘ আক্বীল ছিলেন নসবনামা (বংশধারা শাস্ত্রীয়) বিশেষজ্ঞ । আর এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর দক্ষতার অধিকারী। তিনি লোকদের গোত্র পরিচয় ও পিতা-মাতা সম্বন্ধে এবং কখন কোথায় সংশ্লিষ্ট গোত্রের উদ্ভব ঘটে সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত ছিলেন। তাই আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তার সহায়তা চাইলে সাথে সাথেই তিনি বলেনঃ
. عنَیِّ لَکَ بِاُمِّ الْبَنِينَ بِنْتِ خَالِدٍ
‘‘ আমি তোমার জন্য উম্মুল বানীন বিনতে খালেদ-এর প্রস্তাব দিচ্ছি ।’’
উল্লেখ্য ,‘‘ উম্মুল বানীন’’ মানে‘ কয়েক জন পুত্রের জননী’ । তবে এটা‘‘ উম্মে কুলসুম’’ -এরই অনুরূপ;বর্তমানে আমরা এর দ্বারা নাম রেখে থাকি। ইতিহাসে আছে যে,উম্মুল বানীন-এর পূর্ববর্তী বংশধারায় তার পরদাদী বা আরো পূর্ববর্তী কারো নাম ছিলো উম্মুল বানীন;হয়তো তার কথা স্মরণ করেই এর নাম উম্মুল বানীন রাখা হয়েছিলো।
যা-ই হোক,আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) উম্মুল বানীনকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে চারজন পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে,তিনি কোনো কন্যা সন্তান জন্ম দেননি। এভাবে তিনি শুধু নামে নয়,কার্যতঃও উম্মুল বানীন বা কয়েক জন পুত্র সন্তানের মাতা হিসেবে প্রমাণিত হন।
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) আরো কয়েক জন বীর সন্তানের অধিকারী ছিলেন। প্রথমতঃ স্বয়ং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) উভয়ই ছিলেন বীরপুরুষ। বিশেষ করে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) যে কত বড় সাহসী ছিলেন কারবালায় তিনি তার প্রমাণ রাখেন। প্রমাণিত হয় যে,তিনি তার পিতার সাহসিকতা ও বীরত্ব উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছেন। দ্বিতীয় আমীরুল মু’ মিনীনের আরেক পুত্র মুহাম্মাদ বিন হানাফীয়াও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি আবুল ফজলের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তিনি জঙ্গে জামালে (উটের যুদ্ধে ) অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী,খুবই শক্তিশালী ও শৌর্যের অধিকারী। বলা হয় যে,আমীরুল মু’ মিনীন (আঃ) তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী কারবালার রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার থেকে সর্ব প্রথম যিনি শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত আলী আকবর,আর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের পূর্বে সর্বশেষ যিনি শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত আবুল ফজল আব্বাস। অর্থাৎ আবুল ফজল যখন শহীদ হন অতঃপর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পুরুষ সঙ্গীসাথী ও অনুসারীদের মধ্যে একমাত্র তার অসুস্থ পুত্র হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিলেন না।
বর্ণিত হয়েছে,আবুল ফজল আব্বাস রণাঙ্গনে যাবার আগে এ জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইতে আসনে এবং বলেনঃ‘‘ প্রিয় ভাইজান! আমাকে রণাঙ্গনে যাবার অনুমতি দিন। আমি বেঁচে থাকাতে খুবই অশান্তি বোধ করছি।’’
আবুল ফজল আব্বাস নিজে রণাঙ্গনে যাবার আগে তার তিন সহোদর ভাইকে (যাদের সকলেই বয়সে তার চেয়ে ছোট ছিলেন) রণাঙ্গনে পাঠান। তিনি তাদেরকে বলেনঃ‘‘ ভাইেয়রা! তোমারা যাও;আমি আমার ভাইদের বিপদের (শাহাদাতের) বিনিময়ে পুরস্কার পেতে চাই।’’ তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে,তার তিন সহোদর ভাই তার আগেই শহীদ হয়েছেন এবং তিনি মনস্থ করেছিলেন যে,এরপরই তিনি তাদের সাথে যুক্ত হবেন।
এই হলো উম্মুল বানীন ও তার চার পুত্রের ঘটনা। তবে আশূরার সময় উম্মুল বানীন কারবালায় ছিলেন না। তিনি তখন মদীনায় ছিলেন। যারা মদীনায় ছিলেন তারা কারবালার ঘটনার কোনো খবরই রাখতেন না। চারটি পুত্র সন্তানের জননী এই মহিলার গোটা জীবন বলতে তার এই পুত্রগণই ছিলেন। তার নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে,তার চার সন্তানই কারবালায় শহীদ হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একজন পূণ্যবতী মহিলা। তিনি ছিলেন একজন বিধবা,যার একমাত্র সম্বল ছিলো তার এই পুত্রগণ,কিন্তু তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি অনেক সময় মদীনা থেকে কুফা অভিমুখী পথের পাশে বসে তার সন্তানদের স্মরণে শোকগাঁথা গাইতেন।
ইতিহাসে লেখা হয়েছে যে,এই মহিলা স্বয়ং ছিলেন বনি উমাইয়্যার প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক বিলষ্ঠ প্রচার। যে কেউ ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতো সে-ই থমকে থেমে যেতো এবং তার শোকগাঁথা শুনে অশ্রু বিসর্জন করতো। এমন কি আহলে বাইতের ঘোরতর দুশমনদের অন্যতম মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন মদীনার আমীর (গভর্ণর) ছিলো,সে যখনই ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন উম্মুল বানীনের শোকগাঁথা শুনে নিজের মনের অজান্তই বসে পড়তো এবং উম্মুল বানীনের বিলাপের সাথে সাথে ক্রন্দন করতো।
উম্মুল বানীন বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে একটি কবিতায় তিনি বলেনঃ
لَا تَدْعُونِی وَيْکَ اُمَّ الْبَنِينِ |
تُذَکِّرِينِی بِلُيُوثِ الْعَرِينِ |
|
کَانَتْ بَنُونَ لِی اُدْعَی بِهِمْ |
وَ الْيَوْمَ اَصْبَحْتُ وَ لَا مِنْ بَنِينٍ |
‘‘ হে আর আমাকে ডেকো না উম্মুল বানীন বলে
এ ডাক তাজা করে দেয় বেদনার স্মৃতি মোর
ছিলো মোর ক’ টি পুত্র,ডাকা হতো তাই এই নামে মোরে
আজ আমি আছি শুধু মোর কোনো পুত্র নেই।’’
(মুন্তাহাল আমাল,খণ্ড 1,পৃষ্ঠা 386)
উম্মুল বানীনের জৈষ্ঠ পুত্র ছিলেন হযরত আবুল ফজল আব্বাস। তাই তিনি বিশেষভাবে আবুল ফজলের স্মরণে এক মর্মবিদারক শোকগাঁথা রচনা করেন। এতে তিনি বলেনঃ
يَا مَنْ رَأَی الْعَبَّاسَ کَرَّ عَلَی جَمَاهِيرِ النَّقَدِ
وَ وَرَاهُ مِنْ اَبْنَاءِ حَيْدَرَ کُلُّ لَيْثٍ ذِی لَبَدٍ
اُنْبِئْتُ اَنَّ ابْنِی اُصِيبَ بِرَأْسِهِ مَقْطُوعَ يَدٍ
وَيْلِی عَلَی شِبْلِی اَمَالَ بِرَأْسِهِ ضَرْبُ الْعَمَدِ
لَوْ کَانَ سِيْفُکَ فِی يَدَيْکَ لِمَا دَنَی مِنْهُ اَحَدٌ
‘‘ হে,যে জন দেখেছো আব্বাসকে নীচ গোষ্ঠীর মোকাবিলায়
আর তার পশ্চাতে ছিলো হায়দারের পুত্রগণ প্রত্যেকেই সিংহ দৃঢ়পদ
আমাকে জানানো হলো,আমার কর্তিতহস্ত পুত্রের শিরোপরি আপতিত হলো
আফসোস তবু সে সিংহ শাবকের শিরে স্বেচ্ছায় হেনেছে আঘাত
হায়! তোমার হাতে থাকলে তরবারী কেউই আসতো না তার কাছে।’’ (প্রাগুক্ত)
উম্মুল বানীন জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আমার পুত্র সাহসী বীরপুরুষ আব্বাস কীভাবে শহীদ হলো? বস্তুতঃ হযরত আবুল ফজল আব্বাসের সাহসিকতা ও বীরত্বের বিষয় ইতিহাসের অকাট্য বিষয় সমূহের অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দর। এ কারণে শৈশব কালেই তাকে‘‘ ক্বামারে বানী হাশেম’’ (বনি হাশেমের পূর্ণচন্দ্র ) বলা হতো যিনি বনি হাশেমের মাঝে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুদ্ভাসিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী। অনেক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী,তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হতেন তখন রেকাব থেকে পা বের করে ঝুলিয়ে দিলে তার পায়ের আব্দুল ভূমি স্পর্শ করতো। তার বাহুও ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও শক্তিশালী এবং বক্ষ ছিলো খুবই প্রশস্ত। উম্মুল বানীন বলতেন যে,এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার পুত্র নিহত হবেন না। উম্মুল বানীন লোকদের জিজ্ঞেস করেন,তার পুত্রকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিলো? তাকে জানানো হয় যে,প্রথমে তার হাত দু’ টি কেটে ফেলা হয়,এরপর তাকে হত্যা করা হয়। একথা শুনে উম্মুল বানীন এ নিয়ে মার্সিয়া (শোকগাঁথা) রচনা করেন। তিনি বলতেনঃ‘‘ হে কারবালা প্রত্যক্ষকারী নয়নগুলো! হে কারবালা থেকে আগত লোকেরা! তোমরা তো আমার আব্বাসকে দেখেছো যে,সে শৃগালদের দলের ওপর হামলা করেছিলো এবং দুশমন পক্ষের লোকেরা শৃগালের মতো তার সামনে থেকে পলায়ন করছিলো।’’ তিনি বলেনঃ
يَا مَنْ رَأَی الْعَبَّاسَ کَرَّ عَلَی جَمَاهِيرِ النَّقَدِ
وَ وَرَاهُ مِنْ اَبْنَاءِ حَيْدَرَ کُلُّ لَيْثٍ ذِی لَبَدٍ
‘‘ হে,যে জন দেখেছো আব্বাসকে নীচ গোষ্ঠীর মোকাবিলায়
আর তার পশ্চাতে ছিলো হায়দারের পুত্রগণ প্রত্যেকেই সিংহ দঢ়পদ।’’
তিনি তার শোকগাঁথায় বলেনঃ‘‘ আলীর অন্যান্য পুত্র তার পিছনে দাড়িয়ে ছিলো;তারা সিংহের পিছনে সিংহের ন্যায় আব্বাসের পিছনে দাড়িয়ে ছিলো। আফসোস! আমাকে জানানো হয়েছে,তোমার নরিসংহ পুত্রের শরীরে লৌহশলাকা ঢুকানো হয়েছিলো। আব্বাস! প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার! আমি জানি,তোমার শরীরে যদি হাত থাকতো তাহলে কেউই তোমার সামনে আসতে সাহসী হতো না।’’
হোসাইনী আন্দোলনের প্রচার পদ্ধতিসমূহ
দীন প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার পর এবার আমরা বিশেষভাবে হোসাইনী আন্দোলনের প্রচার পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করবো। তবে হযরত ইমাম হোসাইন অনুসরণ করেন তার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলা প্রয়োজন।
ইসলামের ইতিহাসে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত ও হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের মধ্যে কালগত ব্যবধান পাঁচ দশকের। এ সময়ের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বরং অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজতত্ত্বের মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন গবেষকগণ এসব ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (point) লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ‘ আলায়েলী আহলে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়টির প্রতি অন্য সকলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
আব্দুল্লাহ‘ আলায়েলী বলেনঃ সকল আরব গোত্রের (কুরাইশ ও অ-কুরাইশ নির্বিশেষে) বিপরীতে বনি উমাইয়্যা কেবল এক বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠিমাত্র ছিলো না। বরং তারা ছিলো এমন এক বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি যাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মতৎপরতা ছিলো এক রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি ও কর্ম তৎপরতার অনুরূপ । অর্থাৎ তারা এক বিশেষ ধরনের সামাজিক চিন্তাধারা পোষণ করতো যা প্রায় আমাদের যুগের ইয়াহুদীদের অনুরূপ-যারা তাদের গোটা ইতিহাস জুড়ে এমন একটি বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি যারা একটি বিশেষ চিন্তা ও বিশেষ মতাদর্শের অধিকারী এবং সে মতাদর্শ ভিত্তিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে জনগোষ্ঠির সকল সদস্যের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে শুধু তা-ই নয়,বরং এ জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বনি উমাইয়্যাকে একটি ধুর্ত ও শয়তানী বৈীমষ্ট্যের অধিকারী বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর বর্তমানে তাদের সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ করা হয় যে,বনি উমাইয়্যা হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠি,ইসলামের অভ্যুদ্যয়ের কারণে অন্য যে কোনো জনগোষ্ঠির তুলনায় যারা অনেক বেশী বিপদ অনুভব করে এবং ইসলামকে নিজেদের জন্য বিরাট মুছিবত বলে গণ্য করে। এ কারণে তারা সর্বশক্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতঃপর হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে,ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রামে আর কোনোই লাভ হবে না। এ কারণে তারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে।‘ আম্মার ইয়াসিরের ভাষায়ঃ .
.. مَا اَسْلَمُوا وَ لَکِنْ
‘‘ তারা ইসলাম গ্রহণ করে নি,তবে........।
আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাদের সাথে‘‘ মুআল্লাফাতু কুলুবিহিম’’ (অর্থাৎ যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত থেকে প্রদান করার নিয়ম রয়েছে) নীতি অনুযায়ী আচরণ করতেন। অর্থাৎ তারা এমন লোক যারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিন্তু ইসলাম তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নি।
হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) (বনি উমাইয়্যার ইসলাম গ্রহণের পর) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বনি উমাইয়্যার ওপর কোনো মৌলিক কাজের দায়িত্বই অর্পণ করেন নি। কিন্তু তার ওফাতের পর ক্রমান্বয়ে বনি উমাইয়্যা ইসলামী প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ও এতে প্রবেশলাভ করে। আর হযরত ওমর বিন খাত্তাবের শাসনামলে যে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতি ভুল করা হয় তা হচ্ছে ,আবু সুফিয়ানের পুত্রদের অন্যতম ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে শামের প্রশাসক (গভর্ণর) নিয়োগ করা হয় এবং তার পরে মু‘ আবিয়া শামের প্রশাসক হন ও হযরত ওসমানের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত বিশবছর যাবত সেখানে রাজত্ব করেন। ফলে সেখানে বনি উমাইয়্যার পা রাখার জন্য একটি জায়গা তৈরী হয়ে যায় এবং তা ছিলো কতই না বড় একটি‘ পা রাখার জায়গা’ !
এরপর হযরত ওসমান খলীফা হলেন। মনে হচ্ছে ,মন-মানসিকতার দিক থেকে বনি উমাইয়্যার অন্যান্য লোকের সাথে তার পার্থক্য ছিলো। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রম;আবু সুফিয়ানের মতো ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উমাইয়্যা বংশের লোক বৈ ছিলেন না। হ্যাঁ,তার যুগে ইসলামী প্রশাসনে বনি উমাইয়্যার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পদ,যেমনঃ মিসর,কুফা ও বসরার মতো বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গার প্রাদেশিক হুকুমত বনি উমাইয়্যার কুক্ষিগত হলো। এমনকি স্বয়ং খলীফা ওসমানের মন্ত্রীর পদও মারওয়ান ইবনে হাকামের হাতে পড়লো। বনি উমাইয়্যার লক্ষ্য হাসিলের পথে এটা ছিলো এক বিরাট পদক্ষেপ। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে শামের আমীর মু‘ আবিয়া দিনের পর দিন স্বীয় অবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে লাগলেন।
হযরত ওসমানের শাসনামল পর্যন্ত বনি উমাইয়্যা শুধু দু’ টি শক্তির অধিকারী ছিলো। এক ছিলো রাজনৈতিক পদ ও রাজনৈতিক শক্তি ,অপর ছিলো বায়তুল মাল তথা আর্থিক শক্তি। হযরত ওসমানের নিহত হওয়ার পর মু‘ আবিয়া আরো এক শক্তি হস্তগত করলেন। তা হচ্ছে ,তিনি নিহত খলীফার মযলুম অবস্থার বিষয়টিকে কাজে লাগাতে লাগলেন। খলীফা ওসমানের মযলুম অবস্থায় নিহত হবার কাহিনী প্রচার করে তিনি বহু জনগোষ্ঠির (অন্ততঃ শামে) ধর্মীয় অনুভূতিকে নিজের পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হন। তিনি বলতেনঃ খলীফাতুল মুসিলমীন,খলীফাতুল ইসলাম মযলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন। আর
مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً
‘‘ (আল্লাহ বলেনঃ) যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দান করেছি।’’ অতএব,খলীফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ফরয;এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে।’’
মু‘ আবিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের অনুকূলে এভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের-হয়তো বা নিযুত নিযুত সংখ্যক লোকের-সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আল্লাহই ভালো জানেন মু‘ আবিয়ার এ প্রচারের ফলে লোকেরা হযরত ওসমানের কবরের ওপর কী পরিমাণ অশ্রুপাত করেছিলো। আর এসব ঘটানো হয় আমীরুল মু‘ মিনীন হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফত কালে।
হযরত আলী (আঃ)-এর শাহাদাতের পর মু‘ আবিয়া মুসলমানদের ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হলেন। ফলে সকল ক্ষমতাই তার হস্তগত হলো। এখানে তার পক্ষে চতুর্থ আরেকটি শক্তিকেও নিজের অনুকূলে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। তা হচ্ছে ,তিনি দীনী ব্যক্তিবর্গকে (এ যুগের পরিভাষায়,সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে) ভাড়া করেন। তখন থেকে হঠাৎ করেই হযরত ওসমানের প্রশংসায়,এমন কি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের প্রশংসায়ও,মিথ্যা হাদীছ রচনা শুরু হলো। কারণ,মু‘ আবিয়া তাদের মর্যাদাকে অনেক বেশী উচ্চে তুলে ধরাকে তার নিজের জন্য লাভজনক ও হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। আর এ কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) তার বিভিন্ন উক্তিতে বনি উমাইয়্যা যে ইসলামের জন্য এক বিরাট বিপদ সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার এক ভাষণের শুরুর দিকে খারেজীদের ওপর আলোকপাত করেন এবং তাদের শেষ পরিণতির কথাও উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেনঃ
-فَاَنَا فَقَّأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ
‘‘ অতঃপর আমি ফিৎনার চোখ উৎপাটন করলাম।’’ ( নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খোতবাঃ 92 , পৃষ্ঠাঃ 273 ) এরপর সহসাই তিনি তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং বলেনঃ .
اَلَا وَ اِنَّ اَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَيْکُمْ، فِتْنَةُ بَنِی اُمَيَّةَ فَاِنِّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءٌ مُظْلِمَةٌ
‘‘ সাবধান! আমি আমার সামনে তোমাদের জন্য একটি ফিৎনার আগমনের ভয় করছি,তা হচ্ছে বনি উমাইয়্যার ফিৎনা। নিঃসন্দেহে তা হবে ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন সর্বগ্রাসী ফিৎনা।’’ ( প্রাগুক্ত ) অর্থাৎ বনি উমাইয়্যার ফিৎনা হবে খারেজীদের ফিৎনার চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ।
বনি উমাইয়্যার ফিৎনা সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ)-এর অনেক উক্তি রয়েছে। তিনি বনি উমাইয়্যার যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ,ইসলামের সাম্যনীতি তাদের দ্বারা পুরোপুরি পদদলিত হবে এবং ইসলাম যে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে সমান গণ্য করেছে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তখন লোকেরা কর্তা ও গোলাম-এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে এবং তোমরা (জনগণ) কার্যতঃ তাদের গোলামে পরিণত হবে। তার এ ধরনের একটি উক্তিতে তিনি বলেনঃ .
حَتَّی لَا يَکُونَ انْتِصَارُ اَحَدِکُمْ مِنْهُمْ اِلَّا کَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ
‘‘ এমনকি তাদের সাথে তোমাদের কারো আচরণই স্বীয় মনিবের সাথে দাসের আচরণের ন্যায় বৈ হবে না।’’ ( প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠাঃ 274 ) মোদ্দা কথা,তাদের সকলেই হবে মালিক আর তোমরা হবে তাদের সকলেরই দাস সমতুল্য । এ ব্যাপারে হযরত আলী (আঃ)-এর আরো অনেক উক্তি রয়েছে।
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ)-এর উক্তিতে দ্বিতীয় একটি বিষয় এসেছে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে এবং পরে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে,তার যুগের পরে সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত মহল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেনঃ
عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خُصَّتْ بَلِيَّتُهَا.
‘‘ এর মুছিবত হবে সর্বজনীন,তবে এর প্রতি আপতিত হবে শ্রেণী বিশেষের ওপর।’’ ( প্রাগুক্ত ) তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেনঃ
وَ اَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ اَبْصَرَ فِيهَا وَ اَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِیَ عَنْهَا
‘‘ এই মুছিবত চক্ষুষ্মানদের ওপর আপতিত হবে এবং এ মুছিবতের দ্বারা তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা এ ব্যাপারে অন্ধ ।’’ ( প্রাগুক্ত ) অর্থাৎ যে কেউই দৃষ্টিশক্তি তথা দূরদৃষ্টির অধিকারী হবে,আজকের পরিভাষায় বলা যায়,যে কেউই চিন্তাশীল বা বুদ্ধিজীবী হবে এ ফিৎনা তাকেই গ্রাস করবে। কারণ,ওরা চায় না সমাজে তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকের অস্তিত্ব থাকুক। আর ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে,বনি উমাইয়া দ্বারা ঐ যুগের বুদ্ধিজীবি ও দূরদর্শীদেরকে ঠিক পাখী যেমন খাদ্যদানা গুলোকে এক এক করে জমা করে,তেমনি করে তাদেরকে জমা করতো এবং গর্দান দিত। আর এভাবে তারা কি নৃশংসতাই না চালিয়েছে!
তৃতীয় বিষয়টি হলো ঐশ্বরিক মর্যাদা সমূহকে ক্ষুন্ন করা।
لَا يَدْعُوا لِلَّهِ مُحَرَّماً اِلَّا اسْتَحْلُوهُ وُلَا عَقْداً اِلَّا حَلُّوهُ
অর্থাৎ,আর কোনো হারাম বাকী থাকবে না যা তারা করবে না আর ইসলামের আর কোনো বন্ধন বাকী থাকবে না যা তারা তুলে ফেলবে না।( নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খোতবা নং 97 , পৃষ্ঠা নং 290 ) চতুর্থ কথাটি হলো ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বরং প্রকাশ্যে কার্যত : তারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। আর যাতে জনগণকে উল্টিয়ে ফলতে পারে এজন্য ইসলামকেই উল্টিয়ে দেয়।
لُبِسَ الْاِسْلاَمُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً
অর্থাৎ, ইসলামকে জনগণের শরীরে এমন ভাবে পরিয়ে দিল যেভাবে পশমী পোশাককে উল্টিয়ে পরানো হয়।( নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খোতবা নং 107 পৃষ্ঠা নং 324 )
পশমী কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হলো এটা গরম করে এবং এর পশমের মধ্যে সৌন্দর্যময় বৈচিত্র বাহার থাকে। আর সেটা তখনই প্রকাশ পায় যখন সেটা ঠিকভাবে পরিধান করা হবে। কিন্তু এটাকে যদি উল্টিয়ে পরা হয় তাহলে এতে তো কোনো গরম উৎপাদন হবেই না;উপরন্তু এমন এক ভয়াল আতঙ্কজনক দৃশ্যের অবতারণা করবে যা ঠাট্রা বিদ্রুপেরও খোরাক যোগাবে বটে। আলী (আঃ) যখন শহীদ হয়ে গেলেন তখন মুআবিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী যে নিহত হওয়ার মাধ্যমে আলীর সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে এর বিপরীতে বরং তিনি একটি প্রতীক হিসাবে সমাজে জীবিত হলেন। যদিও একজন ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিহত হয়েছেন। অর্থাৎ আলীর চিন্তাধারা তার মৃত্যুর পরে আরো বেশী বিস্তার লাভ করে। এরপরে শিয়ারা উমাইয়্যা দলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলো। ফলে চিন্তা চেতনায় ঐক্যতান সৃষ্টি হলো এবং মূলতঃ তখন থেকেই আলী (আঃ) এর শিয়ারা একটি সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।
মুআবিয়া নিজ শাসনামলে আলীর চিন্তার সাথে বহু লড়াই চালিয়ে যান। মেম্বারের উপরে বসে আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও অভিশাপ বর্ষণ করা হতো। রাষ্ট্রীয় ভাবে অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল যেন ইসলামী সম্রাজ্যের সর্বত্র মসজিদে মসজিদে জুমআর নামাজের মধ্যে আলীকে অভিসম্পাত করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আলী (আঃ) একটি শক্তি ও প্রতীক হিসাবে মানুষের আত্মার মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাস হিসাবে জীবিত ছিলেন। একারণে,মুআবিয়া এর বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংঘটিত করে,কাউকে বিষক্রিয়ায় হত্যা করে,কারো শিরোচ্ছেদ করে কাটা শির বর্শার মাথায় তোলে ইত্যাদি। এগুলো তো ছিলই উপরুন্তু মুআবিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য বাহ্যিক বেশভূষায় কিছুটা মেনে চলতো। কিন্তু ইয়াযীদের সময় আসার সাথে সাথে সম্পূর্ণ রূপে মুখোশ খুলে পড়ে যায়। তাছাড়া অদক্ষ ইয়াযীদ এতদিনের উমাইয়া রাজনীতিকেও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। বরং সে এমন কিছু করে যাতে উমাইয়াদের গোপনীয়তার পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর এমনই পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় আন্দোলনের সূচনা করেন। এবার ইমামের এ আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। পবিত্র কোরআনের আয়াত মালার এক বৈশিষ্ট্য হলো বিচিত্র ধরনের সুর ধারণের ক্ষমতা। ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও প্রঞ্জলতা ছাড়াও সূর ধারণ করার এই অভাবনীয় ক্ষমতার কারণে কোরআনের আয়াতসমুহ অনায়াসে অন্তরে অন্তরে জায়গা করে নেয়ার একটি অন্যতম কারণ হয়েছে। তদ্রুপ মানুষ যখন আশুরার ঘটনার ইতিহাসকে দেখে তখন তার দ্বারা‘ শাবিহ’ তৈরী করার উপযোগীতা খুজে পায়। কোরআন যেমন সূর ধারণের জন্যে তৈরী হয়নি কিন্তু এরূপ আছে তেমনি কারবালার ঘটনাও শাবিহ তৈরীর জন্য সংঘটিত হয়নি,তবে এরূপ আছে।
জানি না,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) হয়তো এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। অব বিষয়টা আমরা সঠিক বলেও রায় দিচ্ছি না,আবার প্রত্যাখ্যানও করছি না। কারবালার কাহিনী এখন থেকে বারোশ’ বছর আগে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমন এক সময় তা লিপিবদ্ধ করা হয় যখন কারো পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিলো না যে,এ কাহিনী এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। এ ঘটনার ইতিহাস মূলতঃ এক নাটক আকারে লিখিত হয়েছিলো বলে মনে হয়;নাটকের সাথে এর খুবই মিল লক্ষ্য করা যায়। মনে হচ্ছে যেন কেউ তা মঞ্চায়নের উপযোগী করে লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা ইতিহাসে অনেক মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা লক্ষ্য করি,কিন্তু প্রশ্ন জাগে,এ ঘটনা যে ধরনের তা কি ঘটনাক্রমে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব? হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) কি বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন নি? জানি না,কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমনটাই ঘটলো এবং বিশ্বাস করতে পারছি না যে,তা ইচ্ছাকৃত নয়।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট ইয়াযীদের অনুকূলে বাই‘ আত দাবী করা হয়। এর তিনদিন পর তিনি মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন,তথা পারিভাষিক দৃষ্টিতে,হিজরত করেন। তিনি আল্লাহ তা‘ আলার হারামে-আল্লাহ যাকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন,সেখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বীয় তৎপরতা শুরু করেন। প্রশ্ন হচ্ছে ,কেন তিনি মক্কা গেলেন? তিনি কি এ কারণে মক্কা গিয়েছিলেন যে,মক্কা হচ্ছে আল্লাহ তা‘ আলা কর্তৃক নিরাপদ ঘোষিত হেরেম শরীফ? তিনি কি বিশ্বাস করতেন যে,বনি উমাইয়্যা মক্কার প্রতি সম্মান দেখাবে? অর্থাৎ তিনি কি বনি উমাইয়্যা সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে,তাদের রাজনীতির দাবী যদি এই হয় যে,তারা তাকে হত্যা করবে তথাপি তারা মক্কার সম্মানার্থে এ কাজ থেকে বিরত থাকবে? নাকি অন্য কিছু ?
প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর মদীনা থেকে মক্কায় হিজরতের পিছনে প্রথমতঃ উদ্দেশ্য ছিলো এই যে,স্বয়ং এই হিজরতই ছিলো বনি উমাইয়্যার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি যদি মদীনায় থেকে যেতেন এবং বলতেন যে,আমি বাই‘ আত হবো না,তাহলে তার এ প্রতিবাদী কণ্ঠ ইসলামী বিশ্বে অতখানি পৌঁছতো না। এ কারণে তিনি একদিকে যেমন ঘোষণা করেন যে,আমি বাই‘ আত হবো না,অন্য দিকে প্রতিবাদ স্বরূপ আহলে বাইতকে নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং মক্কায় চলে আসেন। এর ফলে তার কণ্ঠ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বুঝতে পারে যে,হোসাইন বিন আলী (আঃ) বাই‘ আত হতে রাযী হননি এবং এ কারণে তিনি মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেছেন। আমাদের এ ধারণা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তার এ পদক্ষেপ ছিলো জনগণের নিকট স্বীয় লক্ষ্য ও বাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এক ধরনের প্রচারমূলক পদক্ষেপ।
এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) 3রা শা‘ বান মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি পুরো শা‘ বান,রামাযান,শাওয়াল ও যিলক্বাদ মাস এবং যিলহজ্ব মাসের আট তারিখ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অর্থাৎ যে দিনগুলোতে ওমরা করা মুস্তাহাব এবং যখন চারদিক থেকে লোকেরা মক্কায় ছুটে আসে তখন তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। এরপর হজ্বের দিনগুলো এসে গেলো এবং শুধু চারদিক ও আশপাশ থেকেই নয়,এমনকি খোরাসানের মতো তৎকালীন ইসলামী জাহানের দূরতম প্রান্তবর্তী ভূখণ্ড থেকেও লোকেরা মক্কায় ছুটে এলো। এরপর এলো 8 যিলহজ্ব-যেদিন লোকেরা হজ্বের উদ্দেশ্যে নতুন ইহরাম পরিধান করে অর্থাৎ আরাফাত ও মিনায় যাবার জন্য তথা হজ্ব সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন সহসাই ইমাম হোসাইন (আঃ) ঘোষণা করেনঃ আমি ইরাকের দিকে যাবো,আমি কুফার দিকে যাবো। অর্থাৎ এমনি এক সময় ও পরিস্থিতিতে তিনি কা‘ বার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন,হজ্বের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিবাদ জানান। তিনি এভাবেই,এ পন্থায়ই প্রতিবাদ,সমালোচনা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে,কা‘ বা তো এখন বনি উমাইয়্যার কুক্ষিগত;যে হজ্ব পরিচালিত হবে ইয়াযীদের দ্বারা মুসলমানদের জন্য সে হজ্ব অর্থহীন।
এমন একটি দিনে কা‘ বা ও হজ্বের অনুষ্ঠানাদির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন এবং ঘোষণা দান যে,আমি আল্লাহ তা‘ আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদের দিকে মুখ ফিরাচ্ছি ও হজ্বের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি,আমর বিল মা‘ রুফ ওয়া নাহি‘ আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি ও হজ্বের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি-এর তাৎপর্য সীমাহীন;এটা কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার ছিলো না। এখানে এসে তার পদক্ষেপের প্রচারমূলক গুরুত্ব এবং কাজের পদ্ধতি তুঙ্গে উপনীত হয়।
এ পর্যায়ে এসে ইমাম হোসাইন (আঃ) এমন এক সফরের সিদ্ধান্ত নেন যাকে‘ বুদ্ধিমান’ লোকেরা (অর্থাৎ যারা সব কিছুকেই পার্থিব স্বার্থের মানদণ্ডে বিচার করেন) হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর জন্য ব্যর্থতা ডেকে আনবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অর্থাৎ তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে,তিনি এ সফরে নিহত হবেন। আর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে সঠিক বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ আমি নিজেও এটা জানি।
তার এ কথার পরে তারা বলেনঃ তাহলে নারী ও শিশুদেরকে কেন সাথে নিয়ে যাচ্ছেন ?
তিনি বললেনঃ তাদেরকেও সাথে নিয়ে যেতে হবে।
বস্তুতঃ ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর আহলে বাইত কারবালার মঞ্চে উপস্থিত থাকায় সে মঞ্চ হয়ে ওঠে অধিকতর উত্তপ্ত ,অধিকতর মর্মান্তিক। প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইন (আঃ) এমন একদল মুবাল্লিগ (প্রচারক)কে সাথে নিয়ে যান তার শাহাদাতের পরে যাদেরকে দুশমনের হুকুমতের হৃদপিণ্ডে অর্থাৎ শামে পৌঁছে দেয়া হয়। আসলে এটা ছিলো এক বিস্ময়কর কৌশল ও একটি অসাধারণ কাজ। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, কণ্ঠস্বর যেন যত বেশী সম্ভব বিশ্বের বিভিন্ন পৌঁছে যায়,বিশেষ করে যেন তৎকালীন ইসলামী জাহানের সর্বত্র পৌঁছে যায় এবং ইতিহাসের অনেক বেশী দিককে ও কালের অনেক দিককে উম্মুক্ত করে দেয়,আর এর পথে যেন কোনোরূপ বাধাবিঘ্ন না থাকে।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) পথিমধ্যে যে সব কাজ সম্পাদন করেন তাতেও ইসলামের প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামের মহানুভবতা ও মানবতা এবং ইসলামের চেতনা ও সত্যতা প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটিরই নিজস্ব গুণ রয়েছে। এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। চলার পথে একটি মনযিলে উপনীত হবার পর তিনি বেশী করে পানি নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ যত মশক আছে তার সবগুলোই পূর্ণ করে নাও এবং লাগাম হাতে ধরে পায়ে হেটে তোমাদের বাহনগুলোকে এগিয়ে নাও এবং তাদের পিঠে পানি তুলে নাও। বস্তুতঃ এ ছিলো এক ভবিষ্যদ্বাণী।
চলার পথে হঠাৎ ইমামের জনৈক অনুসারী চীৎকার দিয়ে বললেনঃ‘‘ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ।’’ অথবা বললেনঃ‘‘ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।’’ অথবা‘‘ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে‘ উন।’’ মনে হলো তিনি যেন উচ্চৈঃরে যিকর করছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী? তিনি বললেন,আমি এ ভূখণ্ডের সাথে ভালোভাবে পরিচিত। এটা এমন একটি ভূখণ্ড যেখানে কোনো খেজুর বাগান নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দূরে খেজুর বাগান দেখা যাচ্ছে ;খেজুর গাছের ডাগরের মতো চোখে পড়ছে। লোকেরা বললো,খুব ভালো করে দেখো।’’ যাদের দৃষ্টি শক্তি অনেক বেশী প্রখর তারা ভালো করে দেখে বললো,না জনাব! খেজুর বাগান নয়;ওগুলো পতাকা। দূর থেকে মানুষ আসছে,ঘোড়া আসছে। অন্যরা বললো,হয়তো ভুল দেখছো। তখন স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আঃ) দেখলেন এবং বললেন,ঠিক বলেছো। তারপর তিনি সঙ্গীসাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের বামবিক একটি পাহাড় আছে;তোমরা ঐ পাহাড়কে তোমাদের পিছনে প্রতিরক্ষা দেয়াল স্বরূপ গ্রহণ করো।
হুর এসে হাযির হলেন,সাথে এক হাজার সৈন্য । বস্তুতঃ এখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার জন্য তার হাতে সুযোগ ছিলো। কিন্তু তিনি কাপুরুষতার আশ্রয় নেন নি;এ সুযোগ কাজে লাগান নি,ঠিক যেভাবে তার মহানুভব পিতা হযরত আলী (আঃ) শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বরং তার দৃষ্টিতে,এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামী মহানুভবতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। তাই হুর ও তার লোকজন এসে পৌঁছার সাথে সাথেই ইমাম হোসাইন (আঃ) বললেন,ঐখান থেকে পানি নিয়ে এসো এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাও,লোকদেরকেও পানি পান করাও। স্বয়ং তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন যে,তাদের ঘোড়াগুলোর পুরোপুরি পিপাসা নিবৃত্তি হয়েছে কিনা। এক ব্যক্তি বলেন,আমার কাছে একটি মশক দেয়া হলো,কিন্তু আমি মশকটির মুখ খুলতে পারলাম না। তখন হযরত এসে নিজের হাতে মশকটির মুখ খুলে আমার কাছে দিলেন। এমনকি ঘোড়াগুলো যখন পানি পান করছিলো তখন তিনি বলেন,এগুলো যদি ক্ষুধার্ত থেকে থাকে তাহলে এক বারে পিপাসা নিবৃত্তি করে পানি পান করবে না। তাই এগুলোকে দুই বার বা তিন বার পানি পান করতে দাও। তেমনি তিনি কারবালাতেও যুদ্ধ শুরু না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।
অন্য একটি বিষয় এমন যে ব্যাপারে আমি সম্মানিত লেখক শহীদ জাভীদের সাথে একমত হতে পারি নি। আমি তাকে বলেছিলাম,ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন কুফার লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন এবং যখন পরিস্কার হয়ে গেলো যে,কুফা পুরোপুরি ইবনে যিয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে,আর মুসলিমও নিহত হয়েছেন,এর পর কেন তার ভাষণগুলো অধিকতর কড়া হয়েছিলো? কেউ হয়তো বলতে পারে যে,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সামনে তো আর ফিরে যাওয়ার পথ খোলা ছিলো না!
মানলাম,তার জন্য ফিরে যাওয়ার পথ খোলা ছিলো না। কিন্তু আশূরার রাতে তিনি যখন তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন যে,আমি তোমাদের ওপর থেকে আমার বাই‘ আত তুলে নিলাম,আর তারা বললেন,না,আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবো না,তখন তিনি বলেন নি যে,এখানে থাকা তোমাদের জন্য হারাম;কারণ,তারা আমাকে হত্যা করতে চায়;তোমাদের সাথে তাদের কোনো সমস্যা নেই। তোমরা যদি এখানে থেকে যাও তাহলে অযথাই তোমাদের রক্তপাত হবে,আর তা হারাম হবে। কেন তিনি তা বলেন নি? কেন তিনি বলেন নি যে,এখান থেকে চলে যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয? বরং তারা যখন তাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার ঘোষণা দিলেন তখন ইমাম হোসাইন (আঃ) তাদের এ অবস্থানকে পুরোপুরি মেনে নেন এবং এর পরই তাদের নিকট সেই সব রহস্য তুলে ধরেন যা এর আগে কখনো প্রকাশ করেন নি।
আশূরার রাতে অর্থাৎ নয়ই মহররমের সূর্যাস্তের পর এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে,পরিদন কী হতে যাচ্ছে । এ সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন (আঃ) হাবীব বিন মাযাহারকে বনি আসাদ গোত্রের লোকদের কাছে পাঠান যাতে সম্ভব হলে তিনি তাদের মধ্যে থেকে কতক লোককে নিয়ে আসেন। বুঝাই যাচ্ছিলো যে,তিনি নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছিলেন। কারণ,শহীদদের রক্ত যত বেশী পরিমাণে প্রবাহিত হবে তার এ আহবান তত বেশী বিশ্বের ও বিশ্ব বাসীর কাছে পৌঁছে যাবে।
আশূরার দিন হুর তওবা করলেন এবং এরপর ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট চলে এলেন। ইমাম (আঃ) বললেন,ঘোড়া থেকে নেমে এসো। হুর বললেন,না,হুজুর,অনুমতি দিন,আমি আপনার পথে আমার রক্ত ঢেলে দেবো। তখন ইমাম হোসাইন (আঃ) বললেন না যে,আমার পথে তোমার রক্ত ঢেলে দেবে এ কথার মানে কী? এর মানে কি এই যে,তুমি নিহত হলে আমি মুক্তি পেয়ে যাবো? এর ফলে আমি তো মুক্তি পাবো না। তিনি এ জাতীয় কোনো কথাই বললেন না।
এসব বিষয় এটাই প্রমাণ করে যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) চাচ্ছিলেন কারবালার ময়দান যত বেশী পরিমাণে সম্ভব রক্তাক্ত হোক। বরং বলা চলে যে,তিনি নিজেই এ রণাঙ্গনকে রঞ্জিত করেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে,আশূরার আগে এক বিস্ময়কর দৃশ্যপটের অবতারণা হয়। মনে হয় যেন,তিনি স্বেচ্ছায় ও পরিকল্পিতভাবে তার অবতারণা করেছিলেন যাতে তিনি যা বলতে ও বুঝাতে চাচ্ছেন তা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়,তার অধিকতর প্রদশর্নী ঘটে। এ কারণেই এ ঘটনা অনুরূপ ঘটনার জন্য প্রেরণায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী পরিমাণে বেড়ে যায়।
মরহুম আয়াতী তার‘‘ বার্রাসিয়ে তারীখে আশূরা’’ (আশূরার ইতিহাস পর্যালোচনা) গ্রন্থে একটি বিষয়ের ওপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেনঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রক্তের রং হচ্ছে সর্বাধিক স্থায়িত্বের অধিকারী রং। ইতিহাসে ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে যে রং কখনোই মুছে যায় না তা হচ্ছে লাল রং,রক্তের রং। আর হোসাইন বিন আলী (আঃ) এ উদ্দেশ্য পোষণ করতেন যে,স্বীয় ইতিহাসকে এ স্থায়ী ও অমোচনীয় রং দ্বারা লিপিবদ্ধ করবেন;স্বীয় বাণীকে তার নিজের খুন দ্বারা লিখে যাবেন।
শোনা যায়,এমন কতক লোক ছিলো যারা তার আগে নিজের রক্তের দ্বারা স্বীয় বক্তব্য লিখে গেছে,বাণী লিখে গেছে। বুঝাই যায়,কেউ যখন নিজের রক্ত দ্বারা কোনো কথা বা কোনো বাণী লিখে তার এক বিশেষ প্রভাব থাকে। জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি নিয়ম ছিলো এবং কখনো কখনো এমন ঘটতো যে,দু’ টি গোত্র এমন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে চাইতো যা কখনো ছিন্ন হবে না। তখন তারা একটি পাত্রে রক্ত নিয়ে আসতো (অবশ্য তাদের নিজেদের রক্ত নয়) এবং তার মধ্যে হাত ডুবাতো। তারা বলতো,এ চুক্তি আর কখনো ভঙ্গ করার নয়;এটা রক্তের চুক্তি,আর রক্তের চুক্তি ভঙ্গ করার মতো নয়।
মনে হচ্ছে ,ইমাম হোসাইন (আঃ) যেন আশূরার দিনকে রং দিয়ে রঞ্জিত করতে চাচ্ছিলেন,তবে তা ছিলো রক্তের রং। কারণ,ইতিহাসে যে রং সবচেয়ে বেশী স্থায়ী তা হচ্ছে এই রক্তের রং। তাই তিনি তার ইতিহাসকে রক্তের দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন।
অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাই বা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাই,অনেক রাজা-বাদুশা এবং এ ধরনের পদবীর অধিকারীরা নিজেদের নাম ইতিহাসের বুকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে এখন থেকে শত শত বছর পূর্বে ধাতব বা পাথরের ফলকে খোদাই করে লিখিয়ে রেখে গেছেনঃ‘ আমি অমুক,অমুকের পুত্র ,অমুক দেবতাদের বংশধর’ ;‘ আমি হচ্ছি ঐ ব্যক্তি যার সামনে অমুক ব্যক্তি যার সামনে এসে হাটু গেড়ে বসেছিলো’ ...। প্রশ্ন হচ্ছে ,তারা ধাতব বা প্রস্তর ফলকে তাদের নাম খোদাই করাতেন কেন? কারণ,তা যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়,তা যেন টিকে থাকে। আমরা যে সব নিদর্শন পাচ্ছি তাতে যেমন দেখতে পাচ্ছি ,ইতিহাস তাদেরকে মাটির স্তুপের নীচে চাপা দিয়েছে;কেউই তাদের খবর রাখতো না। অতঃপর হাজার হাজার বছর পরে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণ এলেন এবং মাটি খনন করে সেগুলোকে উদ্ধার করে আনলেন। হ্যাঁ,সেগুলোকে মাটির নীচ থেকে বের করে আনা হয়েছে ঠিকই,তবে তাতে কিছু আসে-যায় না। এটা কোনো ব্যাপারই নয়। কারণ,তাদেরকে কেউ তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। কারণ,তারা তাদের কথাগুলো পাথরের ওপর লিখে রেখে গেছেন;মানুষের হৃদয় পটে লিখে রেখে যেতে পারেন নি।
ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় বাণীকে না পাথরের ওপর রং-কালি দিয়ে লিখেছেন,না খোদাই করে রেখে গেছেন। তিনি যা কিছু বলেন তা বাতাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং লোকদের কানে ঝঙ্কৃত হয়। তবে তা লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে রেকর্ড হয়ে যায় যে,কখনোই তা হৃদয়পট থেকে মুছে যায় নি। আর তিনি এ সত্যের ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তিনি তার সম্মুখস্থ ভবিষ্যতকে সঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। তা হচ্ছে ,অতঃপর আর কেউ হোসাইনকে হত্যা করতে পারবে না এবং তিনি আর কখনোই নিহত হবেন না।
আপনারা লক্ষ্য করুন,এসব কী? এসব কি ঘটনাক্রমে ঘটে থাকতে পারে? ইমাম হোসাইন (আঃ) আশূরার দিন ঐ সময়,ঐ শেষ মুহুর্তগুলোতে আল্লাহ তা‘ আলার নিকট সাহায্যয্যের জন্য দো‘ আ করেন। অর্থাৎ এই বলে দো‘ আ করেন যে,তার জন্য এমন সাহায্যকারীরা আসুক যারা নিহত হবে; এই বলে দো‘ আ করেন নি যে,সাহায্যকারীরা আসুক এবং তাকে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করুক। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) চান নি তার নিহত হওয়ার পর তার সঙ্গী-সাথীরা,তার ভাইয়েরা ও তার পুত্র-ভ্রাতুস্পুত্ররা বেঁচে থাকুক। তা সত্ত্বেও তিনি সাহায্য ও সাহায্যকারী চাচ্ছিলেন;চাচ্ছিলেন যে,সাহায্যকারীরা আসুক ও নিহত হোক। ইমাম হোসাইন (আঃ) যে বলছিলেনঃ
هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنِی
‘‘ এমন কোনো সাহায্যকারী আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে?’’
এটাই ছিলো তার এ আবেদনের প্রকৃত তাৎপর্য।
ইমাম হোসাইন (আঃ) এর এ আবেদন তাঁবুগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিলো,আর নারীরা বিলাপ করছিলেন;তাদের বিলাপের শব্দ উচ্চকিত হচ্ছিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তার ভাই আব্বাস ও অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন,বললেন,যাও,নারীদেরকে নীরব হতে বলো। তারা গেলেন এবং নারীদেরকে নীরব হতে বললেন;নারীরা নীরব হলো। এরপর তারা দু’ জন ইমামের তাঁবুতে ফিরে এলেন।
এ সময় হযরত ইমামের (আঃ) দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এনে তার কোলে দেয়া হলো। ইমাম হোসাইনের (আঃ) বোন হযরত যায়নাব (আঃ) শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে তার ভাইয়ের কোলে দিলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে নিলেন। তিনি বললেন না,প্রিয় বোন! এ মুছিবতের মধ্যে-যেখানে কোনোরূপ নিরাপত্তা নেই এবং অপর পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে ,আর দুশমন ওৎ পেতে আছে,এহেন পরিবেশে এ শিশুকে নিয়ে এলে কেন? বরং তিনি তার শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। আর ঠিক তখনই দুশমনদের দিক থেকে তীর ছুটে এলো এবং নিস্পাপ শিশুর পবিত্র গলদেশে বিদ্ধ হলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তখন কী করলেন? দেখুন রং করার কাজ কী ধরনের। এভাবে শিশু শহীদ হলে তিনি তার হাতে শিশুর রক্ত নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। যেন তিনি বলছেনঃ হে আসমান! দেখো এবং সাক্ষী থাকো।
ইমাম হোসাইন (আঃ) এর জীবনের শেষ সময়;আঘাতে আঘাতে তার পবিত্র শরীর জর্জরিত। তিনি আর দাড়িয়ে থাকতে পরলেন না;মাটিতে পড়ে গেলেন। ঐ অবস্থায় তিনি হাঁটুতে ভর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেন,তারপর পড়ে গেলেন। তিনি আবার উঠে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করলেন;এ সময় তীর এসে তার গলায় বিদ্ধ হলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,তিনি পুনরায় তার হাতে রক্ত নিলেন এবং তার চেহারায় ও মাথায় মাখালেন এবং বললেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি ।
এগুলো হচ্ছে কারবালার হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। এগুলো হচ্ছে এমন ঘটনা যা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর বাণীকে দুনিয়ার বুকে চিরদিনের জন্য স্থায়ী ও টেকসই করে দিয়েছে।
নয়ই মহররমের বিকালে যখন দুশমনরা হামলা করে তখন হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার ভাই আব্বাসকে দুশমনদের কাছে পাঠান এবং তাকে বলেন,আমি আজ রাতে আমার প্রতিপালকের সাথে একান্ত আলাপন করবো,নফল নামায আদায় করবো,দো‘ আ ও ইস্তেগফার করবো। তুমি যেভাবেই পারো এদেরকে বুঝিয়ে আজ রাতের জন্য-কাল সকাল পর্যন্ত তাদেরকে হামলা থেকে বিরত রাখো। আমি কাল এদের সাথে যুদ্ধ করবো। শেষ পর্যন্ত শত্রুরা ঐ রাতের জন্য হামলা থেকে বিরত থাকে।
ইমাম হোসাইন (আঃ) নয়ই মহররম দিবাগত রাতে অর্থাৎ আশূরার রাতে কয়েকটি কাজ আঞ্জাম দেন যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সে রাতে তিনি যে সব কাজ আঞ্জাম দেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,তিনি তার সঙ্গী সাথীদেরকে (বিশেষ করে যারা এ কাজে সুদক্ষ ছিলেন) নির্দেশ দেনঃ‘‘ তোমরা আজ রাতের মধ্যেই তোমাদের তলোয়ার ও বর্শাগুলোকে (যুদ্ধের জন্য ) প্রস্তুত করো।’’ আর তিনি নিজেই তাদের কাজ তদারক করতে লাগলেন। জুন নামে এক ব্যক্তি অস্ত্র মেরামত ও ধারালো করার কাজে সুদক্ষ ছিলেন;হযরত ইমাম (আঃ) নিজে গিয়ে তার কাজ তদারক করেন।
ইমাম হোসাইন (আঃ) সে রাতে অপর যে কাজ করেন তা হচ্ছে,ঐ রাতের মধ্যেই তাঁবুগুলোকে খুব কাছাকাছি এনে খাটানোর নির্দেশ দেন-এতই কাছাকাছি যাতে এক তাঁবুর রশি বাধার খুটা অন্য তাঁবুর রশির আওতায় পোঁতা হয় এবং দুই তাঁবুর মাঝখান দিয়ে যেন একজন লোক অতিক্রম করার মতোও ফাঁক না থাকে। এছাড়া তিনি তাঁবুগুলোকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে স্থাপনের এবং সে রাতের মধ্যেই তাঁবুগুলোর পিছনে সুগভীর পরীখা খনসনের নির্দেশ দেন-এমন আয়তন ও গভীরতা বিশিষ্ট্য পরীখা যাতে ঘোড়ার পক্ষে তা লাফ দিয়ে ডিঙ্গানো সম্ভব না হয় এবং শত্রু যাতে পিছন দিক থেকে হামলা করতে না পারে। এছাড়া তিনি মরুভূমি থেকে শুকনো আগাছা এনে তার পিছন দিকে স্তুপীকৃত করে রাখার ও আশূরার দিন সকালে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন যাতে যতক্ষণ আগুন জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুশমনরা তাঁবুগুলোর পিছন দিক থেকে হামলা করতে না পারে। তিনি ডান,বাম ও সামনের দিক থেকে দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এভাবে তিনি পিছন দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) ঐ রাতে অপর যে কাজ করেন তা হচ্ছে,তিনি তার সকল সঙ্গীসাথীকে এক তাঁবুতে সমবেত করেন এবং শেষ বারের মতো হুজ্জাত (হুজ্জাত মানে অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।হুজ্জাত পুর্ণ করার মানে হচ্ছে কোনো বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য এমনভাবে তুলে ধরা যাতে শ্রোতার কাছে তার সত্যতার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে,তা বাহ্যতঃ শ্রোতা তা স্বীকার করুক বা না-ই করুক এবং মানুক বা না-ই মানুক। এখানে হযরত ইমাম হোসেন (আঃ) কর্তৃক হুজ্জাত পূর্ণ করার মানে হচ্ছে তার সঙ্গী সাথীদের শহীদ হওয়ার বিষয়টির পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ততা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ কেউ যেন এভাবে জীবন দেয়াকে অর্থহীন মনে করেও কেবল ইমামের প্রতি বাই‘ আতের খাতিরে জীবন না দেন) পরিপূর্ণ করেন। তিনি প্রথমে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান যার ভাষা ছিলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও যার তাৎপর্য ছিলো খুবই সুগভীর। তিনি যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি,তেমনি তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এরপর বলেন,আমি আমার আহলে বাইতের চেয়ে উত্তম কোনো আহলে বাইতের এবং আমার সঙ্গী সাথীদের তুলনায় অধিকতর আনুগত শীল সঙ্গী সাথীর কথা জানি না। এতদসত্ত্বেও তিনি বলেন,তোমরা সকলেই জানো যে,ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ছাড়া আর কারো ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের লক্ষ্য কেবল আমি। তারা আমাকে হাতে পেলে তোমাদের কাউকে নিয়েই মাথা ঘামাবে না। তোমরা চাইলে রাতের আধারকে কাজে লাগিয়ে সকলেই চলে যেতে পারো।
এরপর তিনি বলেন,তোমাদের প্রত্যেকেই এই শিশুদের ও আমার পরিবারের একেক জন সদস্যকে সাথে নিয়ে চলে যেতে পারো। তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই চারদিক থেকে সকলেই বলতে শুরু করলেন,হে আবু আব্দুল্লাহ ! আমরা তা করবো না। সকলের আগে যিনি একথা বললেন তিনি হলেন হযরত ইমামের (আঃ) মহান ভ্রাতা আবুল ফজল আব্বাস।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 44 , পৃষ্ঠাঃ 393 , ইরশাদ - শেখ মুফীদ , পৃষ্ঠঃ 231 , এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ 235 )
এ পর্যায়ে এসে বাস্তবিকই আমরা ঐতিহাসিক ও নাট্যসুলভ কথাবার্তা শুনতে পাই। প্রত্যেকেই তার মতো করে কথা বলেন। একজন বলেন,আমাকে যদি হত্যা করা হয় এবং আমার শরীরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়,আর তার ভস্ম বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়,তারপর আবার আমাকে জীবন্ত করা হয় এবং এভাবে সত্তর বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়,তাহলেও আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। আমার এ তুচ্ছ জীবন তো আপনার জন্য উপযুক্ত কুরবানীও নয়। আরেক জন বলেন,আমাকে যদি হাজার বার হত্যা করা ও জীবন্ত করা হয় তথাপি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। কেবল পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও ইখলাছের অধিকারী লোকেরাই যাতে তার সাথে থেকে যান সে জন্য যা কিছু করা দরকার হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার সব কিছুই করলেন।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে আশূরার সে দিনগুলোতেই খবর এলো যে,তার পুত্র অমুক কাফেরদের হাতে বন্দী হয়েছে। বন্দী একটি যুবক ছেলে বৈ নয়;তার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছিলো তা নিশ্চিত করে বলার উপায় ছিলো না। ছেলের খবর শুনে তিনি বললেন,আমি চাই নি যে,আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলের ভাগ্যে এমনটা ঘটবে।
ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে,আপনার অমুক সঙ্গীর ছেলে কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। ইমাম (আঃ) তাকে ডাকালেন এবং তিনি এলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন ও তার অতীতের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণ করলেন,তারপর বললেন,তোমার পুত্র বন্দী হয়ে আছে। কারো না কারো টাকা-পয়সা ও উপঢৌকনাদি নিয়ে সেখানে যাওয়া দরকার যাতে তাদেরকে তা দিয়ে বন্দীকে মুক্ত করতে পারে। সেখানে কিছু মালামাল ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিলো যা বিক্রি করে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তাকে বললেন,তুমি এগুলো নিয়ে অমুক জায়গায় গিয়ে বিক্রি করো,তারপর প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে যাও তোমার ছেলেকে মুক্ত করো। ইমাম হোসাইন (আঃ) এ কথা বলার সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বললেনঃ
اَکَلَتْنِی السِّبَاعُ حَيّاً اِنْ فَارَقْتُک
অর্থাৎ হিংস্র পশুরা আমাকে জীবন্ত ভক্ষণ করুক যদি আমি আপনাকে ছেড়ে যাই।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 44 , পৃষ্ঠাঃ 394 ) তার কথা হলো,আমার পুত্র বন্দী হয়ে আছে;থাকুক না। আমার পুত্র কি আমার কাছে আপনার তুলনায় অধিকতর প্রিয়?
ইমাম হোসাইন (আঃ) কর্তৃক হুজ্জাত পূর্ণ করার পর যখন সকলেই এক জায়গায় ও এক বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ঘোষণা দিলেন এবং বললেন যে,আমরা কখনো আপনাকে ছেড়ে চলে যাবো না,তখন সহসাই পট পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ইমাম (আঃ) বললেন,ব্যাপার যখন এই,তখন সকলেই জেনে রাখো যে,আমরা নিহত হতে যাচ্ছি । তখন সকলে বললো,আল-হামদুলিল্লাহ-আল্লাহ তা‘ আলার প্রশংসা করছি যে,তিনি আমাদেরকে এ ধরনের তাওফীক দান করেছেন। এটা আমাদের জন্য এক সুসংবাদ,একটি আনন্দের ব্যাপার। ইমাম হোসাইন (আঃ) এর মজলিসের এক কোণে একজন কিশোর বসে ছিলেন;বয়স বড় জোর তেরো বছর হবে। এ কিশোরের মনে সংশয়ের উদয় হলোঃ আমিও কি এ নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবো? যদিও ইমাম বলেছেন‘ তোমরা এখানে যারা আছা তাদের সকলে’ ,কিন্তু আমি যেহেতু কিশোর ও নাবালেগ,সেহেতু আমার কথা হয়তো বলা হয় নি। কিশোর ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর দিকে ফিরে বললেনঃ
؟ يَا عَمَّاه وَ اَنَا فِی مَنْ قُتِلَ؟
অর্থাৎ,চাচাজান! আমিও কি নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবো? এ কিশোর ছিলেন হযরত ইমাম হাসান (আঃ)-এর পুত্র কাসেম। ইতিহাস লিখেছে,এ সময় হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) স্নেহশীলতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমে জবাব দানে বিরত থাকেন,এরপর কিশোরকে জিজ্ঞেস করেন,ভাতিজা! প্রথমে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও,এরপর আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো। তুমি বলো,তোমার কাছে মৃত্যু কেমন;মৃত্যুর স্বাদ কী রকম? কিশোর জবাব দিলেন,আমার কাছে মধুর চেয়েও অধিকতর সুমিষ্ট । আপনি যদি বলেন যে,আমি আগামী কাল শহীদ হবো তাহলে আপনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন। তখন ইমাম হোসাইন (আঃ) জবাব দিলেন,হ্যাঁ,ভাতিজা! কিন্তু তুমি অত্যন্ত কঠিন কষ্ট ভোগ করার পর শহীদ হবে। কাসেম বললেনঃ আল্লাহর শুকরিয়া,আল-হামদুলিল্লাহ-আল্লাহর প্রশংসা যে,এ ধরনের ঘটনা ঘটবে।
এবার আপনারা ইমাম হোসাইন (আঃ) এর এ ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করে দেখুন যে,পরদিন কী বিস্ময়কর এক বাস্তব নাটকের দৃশ্যের অবতারণা হওয়া সম্ভব!
হযরত আলী আকবরের শাহাদাতের পর এই তেরো বছরের কিশোর হযরত ইমাম হাসানের পুত্র ইমাম হোসাইন (আঃ) এর নিকট এগিয়ে এলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন নাবালেগ কিশোর,তার শরীরের বৃদ্ধি তখনো সম্পূর্ণ হয় নি,তাই তার শরীরে অস্ত্র ঠিকভাবে খাপ খাচ্ছিলো না;কোমরে ঝুলানো তলোয়ার ভূমি স্পর্শ করে কাত হয়ে ছিলো। আর বর্মও ছিলো বড়,কারণ বর্ম পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের জন্য তৈরী করা হয়েছিলো,কিশোরদের জন্য নয়। লৌহ টুপি বড়দের মাথার উপযোগী,ছোট বাচ্চাদের উপযোগী নয়। কাসেম বললেন,চাচাজান! এবার আমার পালা। অনুমতি দিন আমি রণাঙ্গনে যাই।
এখানে উল্লেখ্য যে,আশূরার দিনে ইমাম হোসাইন (আঃ) এর সঙ্গী সাথীদের কেউই তার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে রণাঙ্গনে যান নি। প্রত্যেকেই তার নিকট এসে তাকে সালাম করেন এবং এরপর অনুমতি চান;বলেনঃ‘‘ আস-সালামু‘ আলাইকা ইয়া আবা আবদিল্লাহ । আমাকে অনুমতি দিন।’’
ইমাম হোসাইন (আঃ) সাথে সাথেই কাসেমকে অনুমতি দিলেন না। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কাসেম ও তার চাচা পরস্পরকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ইতিহাসে লেখা হয়েছেঃ
. فَجَعَلَ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَ رِجْلَیه
অর্থাৎ,অতঃপর তিনি (কাসেম) তার (ইমাম হোসাইনের) হাত ও পা চুম্বন করতে শুরু করলেন।‘‘ মাক্কাতিল’’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছেঃ
فَلَمْ يَزَلِ الْغُلَامُ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ حَتَّی اَذِنَ لَهُ.-
‘‘ তাকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিশোর তার (ইমাম হোসেনের) হাত ও পা চুম্বন অব্যাহত রাখেন।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 34 এবং মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 27 )
এ ঘটনার অবতারণা কি এ উদ্দেশ্যে হয়নি যাতে ইতিহাস পুরো ঘটনাকে অধিকতর উত্তম রূপে বিচার করতে পারে? কাসেম অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করেন আর ইমাম হোসাইন (আঃ) অনুমতি দানে বিরত থাকেন। ইমাম মনে মনে চাচ্ছিলেন কাসেমকে অনুমতি দেবন এবং বলবেন,যদি যেতে চাও তো যাও। কিন্তু মুখে সাথে সাথেই অনুমতি দিলেন না। বরং সহসাই তিনি তার বাহুদ্বয় প্রসারিত করে দিলেন এবং বললেন,এসো ভাতিজা! এসো,তোমার সাথে খোদা হাফেযী করি।
কাসেম ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কাঁধের ওপর তার হাত দুটো রাখলেন এবং ইমামও কাসেমের কাঁধের ওপর স্বীয় হস্তদ্বয় রাখলেন। এরপর উভয়ে ক্রন্দন করলেন। ইমামের সঙ্গী সাথীগণ ও তার আহলে বাইতের সদস্যগণ এ হৃদয় বিদারক বিদায়ের দৃশ্য অবলোকন করলেন। ইতিহাসে লেখা হয়েছে,উভয়ে এতই ক্রন্দন করলেন যে,উভয়ই সন্ধিৎহারা হয়ে পড়লেন। এরপর এক সময় তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং কিশোর কাসেম সহসাই তার ঘোড়ায় আরোহণ করলেন।
ইয়াযীদী পক্ষের সেনাপতি ওমর ইবনে সা‘ দের সেনাবাহিনীর মধ্যে অবস্থানকারী বর্ণনাকারী বলেন,সহসাই আমরা একটি বালককে দেখলাম ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে যে তার মাথায় টুপির (ধাতব) পরিবর্তে একটি পাগড়ী বেধেছে। আর তার পায়ে যোদ্ধার বুট জুতার পরিবর্তে সাধারণ জুতা এবং তার এক পায়ের জুতার ফিতা খোলা ছিলো; আমার স্মৃতি থেকে এটা মুছে যাবে না যে,এটা ছিলো তার বাম পা। তারপর বর্ণনাকারী বলেনঃ
کَاَنَّهُ فَلْقَهُ الْقَمَرِ
সে যেন চাঁদের একটি টুকরা।( মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব , খণ্ডঃ 4 , পৃষ্ঠাঃ 106 , এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ 242 , আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 48 , বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 35 , ইরশাদ - শেখ মুফিদ , পৃষ্ঠাঃ 239 , মাকতালু মুকাররাম , পৃষ্ঠাঃ 231 , তারীখে তাবারী , খণ্ডঃ 6 , পৃষ্ঠাঃ 256 ) একই বর্ণনাকারী আরো বলেন,কাসেম যখন আসছিলো তখনো তার গণ্ড দেশে অশ্রুর ফোটা দেখা যাচ্ছিলো।
সবাই অনুপম সুন্দর এ কিশোর যোদ্ধাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো এবং ভেবে পাচ্ছিলো না যে,এ ছেলেটি কে! তৎকালে রীতি ছিলো এই যে,কোনো যোদ্ধা রণাঙ্গনে আসার পর প্রথমেই নিজের পরিচয় দিতো যে,আমি অমুক ব্যক্তি । উক্ত রীতি অনুযায়ী কাসেম প্রতিপক্ষের সামনে এসে পৌঁছার পর উচ্চৈঃস্বরে বললেনঃ
اِنْ تَنْکُرُونِی فَاَنَا ابْنُ الْحَسَن |
سِبْطُ النَّبِیِّ الْمُصْطَفَی الْمُؤْتَمَنَ |
|
هَذَا الْحُسَيْنُ کَالْاَسِيرِ الْمُرْتَهَنِ |
بَيْنَ اُنَاسٍ لَاسُقوا صُوبَ الْمَزَنِ |
যদি না চেনো আমাকে জেনো আমি হাসান তনয়
সেই নবী মুস্তাফার নাতি যার ওপর ঈমান আনা হয়
ঋণে আবদ্ধ বন্দী সম এই যে হোসাইন
প্রিয়জনদের মাঝে,পানি দেয়া হয় নি যাদের উত্তম রীতি মেনে।’’
(বিহারুল আনোয়ার,খণ্ডঃ 45,পৃষ্ঠাঃ 34)
কাসেম রণাঙ্গনে চলে গেলেন,আর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার ঘোড়াকে প্রম্তুত করলেন এবং ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলেন। মনে হচ্ছিলো যে তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্য যথা সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। জানি না তখন হযরত ইমামের মনের অবস্থা কেমন ছিলো। তিনি অপেক্ষমান;তিনি কাসেমের কণ্ঠ শোনার জন্য অপেক্ষমান। সহসাই কাশেমের কণ্ঠে‘‘ চাচাজান!’’ ধ্বনি উচ্চকিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন,আমরা বুঝতে পারলাম না ইমাম হোসাইন কত দ্রুত গতিতে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং রণাঙ্গনের দিকে ছুটে এলেন। তার এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) এক শিকারী বায পাখীর ন্যায় রণাঙ্গনে পৌঁছে যান।
ইতিহাসে লিখিত আছে,কাসেম যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান তখন শত্রুপক্ষের প্রায় দুই শত যোদ্ধা তাকে ঘিরে নেয়। তাদের একজন কাশেমের মাথা কেটে ফলেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তারা যখন দেখলো যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) আসছেন তখন তাদের সকলেই সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি কাশেমের মাথা কাটতে চাচ্ছিলো সে তাদের ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট হলো। যেহেতু তারা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো সেহেতু তারা তাদের বন্ধুর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক লোক একবারে ঘোড়া চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো;কেউ কারো দিকে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছিলো না। মহা কবি ফেরদৌসীর ভাষায়ঃ
ز سم ستوران در آن پهن دشت
زمين شد شش و آسمان هشت
‘‘ সেই বিশাল প্রান্তরে কঠিন ক্ষুরের ঘায়ে
ধরণী হলো ছয় ভাগ আর আসমান আট।’’
কেউ বুঝতে পারলো না যে,কী ঘটে গেলো। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে সৃষ্ট ধুলার কুণ্ডলী যখন বসে গেলো এবং হাওয়া কিছুটা স্বচ্ছ হলো তখন সবাই দেখতে পেলো যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) কাসেমকে কোলে নিয়ে আছেন। আর কাসেম তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছিলেন এবং যন্ত্রণার তীব্রতার কারণে মাটিতে পা আছড়াচ্ছিলেন। এ সময় শোনা গেলো,ইমাম হোসাইন (আঃ) বলছেনঃ
يَعِزُّ وَ اللهِ عَلَی عَمِّکَ اَنْ تَدْعُوهُ فَلَا يَنْفَعُکَ صَوْتُهُ.
‘‘ আল্লাহর শপথ,এটা তোমার চাচার জন্য কতই না কষ্টকর যে,তুমি তাকে ডাকলে কিন্তু তার জবাব তোমার কোনো কাজে এলো না।’’ ( মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব , খণ্ডঃ 4 , পৃষ্ঠাঃ 107 , এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ 243 , আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 48 , বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 35 , ইরশাদ - শেখ মুফিদ , পৃষ্ঠাঃ 239 , মাকতা মুকাররাম , পৃষ্ঠাঃ 232 , তারীখে তাবারী , খণ্ডঃ 6 পৃষ্ঠাঃ 25 । )
হোসাইনী আন্দোলনের প্রচারে আহলে বাইতের নারীদের ভূমিকা
হোসাইনী আন্দোলন ও ইসলাম প্রচারে সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সম্মানিত আহলে বাইতের তথা তার পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার আগে দু’ টি ভূমিকা পেশ করা প্রয়োজন। প্রথম ভূমিকা হচ্ছে এই যে,বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী এবং আমরা যারা ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ইমামতের আক্কীদা পোষণ করি তাদের আক্কীদা অনুযায়ী,তিনি প্রথম দিন থেকেই যত কাজ সম্পাদন করেছেন তার সব কিছুই গভীর চিন্তাভাবনা ও নিখুঁত হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে করেছেন। তিনি বিনা চিন্তাভাবনা ও হিসাব-নিকাশে এবং বিনা কারণে কোনো অযৌক্তিক কাজ সম্পাদন করেন নি। অর্থাৎ আমরা একথা বলতে পারি না যে,তার সাথে সংশ্লিষ্ট অমুক ঘটনাটি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছিলো। বরং সব কিছুই সুচিন্তিতভাবে ও হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছিলো। আর এ বিষয় যে ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট শুধু তা-ই নয়,যুক্তি ,বিচার বুদ্ধি ,প্রাপ্ত রেওয়ায়েত সমূহ এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ইমামতের প্রতি আমাদের আক্কীদাও তা সমর্থন করে।
আশূরার ঘটনাবলী প্রসঙ্গে যে সব প্রশ্নে ইতিহাসবিদগণও আলোচনা করেছেন এবং দীনী সূত্রের রেওয়ায়েতও উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার এ বিপজ্জনক সফরে তার আহলে বাইত (পরিবার-পরিজন)কে সাথে নিয়ে গেলেন কেন? এ সফর যে এক বিপজ্জনক সফর হবে সে ব্যাপারে সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অর্থাৎ এ সফর বিপজ্জনক হওয়ার বিষয় এমনকি সাধারণ লোকদের জন্যও ভবিষ্যদ্বাণী করার উর্ধ্বে ছিলো না। এ কারণে তার রওনা হবার আগে যারাই তার কাছে এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই বাস্তবতার আলোকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং পরিবার-পরিজনদের তার সাথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্তকে মঙ্গল চিন্তার (مصلحت ) সাথে সাংঘর্ষিক বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ তারা তাদের সাধারণ জ্ঞানস্তরের হিসাব-নিকাশ ও বুদ্ধির ভিত্তিতে এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার পরিবার-পরিজনের প্রাণরক্ষার মানদেণ্ডের আলোকে সকলে প্রায় সর্বসম্মতভাবে বলেন,হচ্ছে ইমাম! আপনার এ যাত্রা আপনার নিজের জন্যও বিপজ্জনক,অতএব,এ সফর বাঞ্চনীয় নয়। অর্থাৎ এ সফরে আপনার নিজের জীবনই হুমকির সম্মুখীন হবে;পরিবার-পরিজন নিয়ে যাবার তো কোনোই যৌক্তিকতা নেই। ইমাম হোসাইন (আঃ) জবাব দেন,না-আমাকে অবশ্যই তাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়া তার জন্য অপরিহার্য বলে তিনি জানিয়ে দেন।
তিনি তাদেরকে এমন দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন যে,এরপর আর তাদের পক্ষে কোনো কথা বলা সম্ভব ছিলো না। তিনি তাদের সামনে ঘটনার আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেন। আপনারা শুনেছেন যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) বার বার তার স্বপ্নের কথা বলেছেন যা ছিলো আল্লাহ তা‘ আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি অকাট্য ইলহাম। তিনি বলেন, স্বপ্নের জগতে আমার নানা আমাকে বলেছেনঃ
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاکَ قَتِيلاً
নিশ্চয় আল্লাহ চান যে,তুমি নিহত হবে।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 44 , পৃষ্ঠাঃ 364 , মাকতালুল হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ 195 )
বলা হলো,যদি তা-ই হয়,তো পরিবার-পরিজন ও শিশুদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন যে,এদেরকে নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে;বললেনঃ
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا
নিশ্চয় আল্লাহ চান যে,তারা বন্দিনী হবে।( প্রাগুক্ত )
এখানে সংক্ষেপে একটি ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে ,এখানে ;
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا বা اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاکَ قَتِيلاً
বাক্য দু’ টির প্রকৃত তাৎপর্য কী?
এর প্রকৃত তাৎপর্য যা,নিঃসন্দেহে ঐ সময় ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত সকলেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। আজকে যেমন অনেকে এ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত তাৎপর্য সন্ধান করেন তার বিপরীতে প্রকৃত পক্ষে এতে কোনো প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত তাৎপর্য ছিলো না। কারণ কোরআন মজীদে আল্লাহ তা‘ আলার‘ মাশিয়্যাত’ বা‘ ইরাদাহ’ শব্দ দু’ টির প্রতিটিই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি অর্থকে পারিভাষিকভাবে‘ ইরাদায়ে তাকভীনী’ (সৃষ্টি-ইচ্ছা) বলা হয়,আর অপরটি হচ্ছে‘ ইরাদায়ে তাশরী‘ য়ী’ (শরয়ী ইচ্ছা)।
‘ ইরাদায়ে তাকভীনী’ বলতে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ যখন চান যে,কোনো কাজ অবশ্যই সংঘটিত হোক সে ক্ষেত্রে এর মোকাবিলায় কারো কিছুই করার থাকে না। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আল্লাহর‘ ইরাদায়ে তাশরী‘ য়ী’ র মানে হচ্ছে এই যে,আল্লাহ পছন্দ করেন যে,বান্দা এ কাজটি করুক,কিন্তু তিনি বান্দাকে এ কাজটি সম্পাদনে বাধ্য করেন না। উদাহরণস্বরূপ,মহান আল্লাহ যখন রোযা সম্বন্ধে বলেনঃ
) يُرِيدُ اللهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ( .
‘‘ আল্লাহ তোমোদের জন্য সহজ করতে চান,কঠিন করতে চান না।’’ ( বাক্বারাঃ 185 ) অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গে,যেমনঃ যাকাত প্রসঙ্গে বলেনঃ
) يُرِيدُ لِيُطَهِّرَکُمْ(
‘‘ তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।’’ ( মায়িদাঃ 6 ) এখানে মহান আল্লাহর ইরাদা বা চাওয়া মানে হচ্ছে তিনি এরূপ আদেশ দিয়েছেন তথা এ কাজের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। অতএব,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ইচ্ছা করেন বা চান মানে হচ্ছে আল্লাহ তার শহীদ হওয়া পছন্দ করেন,তেমনি তার পরিবার-পরিজনের বন্দী হওয়ার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। বস্তুতঃ আল্লাহ যে কাজে সন্তুষ্ট তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে ব্যক্তি ও মানবতার পূর্ণতা।
যা-ই হোক,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর জবাবের পর আর কেউ কোনো কথা বললেন না। অর্থাৎ কারো পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব ছিলো না। সকলের নীরব মন্তব্য যেন এই যে,প্রকৃত ব্যাপার যখন এই যে,আপনার নানা অবস্তুগত জগতে এসে আপনাকে জানিয়েছেন যে,আপনার নিহত হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাহলে এর বিপরীতে আমাদের আর কিছুই বলার নেই।
যারাই ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর এ উক্তি দুটো শুনেছেন তাদের সকলেই এভাবেই বর্ণনা করেছেন;কেউই বলেন নি যে,তিনি বলেছেন,মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিহত হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেছে,অতএব তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজেও স্বপ্নে শ্রুত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তিটির এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেন নি। তেমনি পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন নি যে,এ ব্যাপারে আমার কিছু করা বা না করার এখিতয়ার নেই,কারণ,এটাই নির্ধারিত হয়ে আছে। বরং তিনি বলেন যে,স্বপ্নে আমাকে যে ইলহাম করা হয়েছে তা থেকে আমি এ তাৎপর্যই গ্রহণ করেছি যে,তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়াটাই আল্লাহর পছন্দ এবং তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমি আমার নিজ এখতিয়ারের সাহায্যে এ কাজ সম্পাদন করছি-পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি ,তবে আমি তার ভিত্তিতেই এ কাজ করছি যা থেকে আমি এর কল্যাণময়তার উপসংহারে উপনীত হয়েছি।
এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে,অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সকলে এক রকম ধারণা পোষণ করতেন,কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন;আর তার ধারণা ছিল অত্যন্ত উচু স্তরের। সবাই যেখানে অভিন্ন অভিমতে উপনীত হতেন সেখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) ভিন্ন অভিমতে উপনীত হতেন এবং বলতেন যে,বিষয় এ রকম নয়;আমি অন্যভাবে পদক্ষেপ নেবো।
এ থেকে সুস্পষ্ট যে,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কাজকর্ম ছিলো সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ণ ও নির্ভুল হিসাব-নিকাশি ভিত্তিক। তিনি তার ওপরে অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করছিলেন। তেমনি তিনি তার পরিবার-পরিজনকে স্বীয় পোষ্য হিসেবে সাথে নিয়ে যান নি। তিনি এরূপ চিন্তা করেন নি যে,আমি যখন যাচ্ছি তখন আমার পরিবার-পরিজনকে কী করবো,কোথায় কার কাছে রেখে যাবো? তার চেয়ে বরং সাথে নিয়ে যাওয়াই ভালো।
ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউই স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যান নি। বস্তুতঃ কোনো ব্যাক্তি যখন কোনো বিপজ্জনক সফরে যায় তখন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে যায় না। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তার সাথে নিয়ে গেলেন। তবে এ চিন্তা থেকে তাদেরকে সাথে নিয়ে যান নি যে,আমি যখন যাচ্ছি তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী! (উদ্দেশ্য,ইমাম হোসাইন (আঃ) মদীনায় বসবাস করতেন;মক্কায় তার কোনো বাড়ীঘর ছিলো না।) বরং তিনি কেবল এ কারণে তাদেরকে সাথে নিয়ে যান যে,তাদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।
এই হলো একটি ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকাটি হচ্ছে‘ ইতিহাসে নারীর ভূমিকা’ প্রসঙ্গ। প্রশ্ন তোলা হয় যে,মূলগতভাবেই ইতিহাস বিনির্মাণে নারীর কোন ভূমিকা আছে, নাকি নেই ? আসলে নারীর পক্ষে কি ইতিহাসে কোনো ভূমিকা পালন করা সম্ভব ? তাদের কি ইতিহাস বিনির্মাণে কোনো কোনো ভূমিকা পালন করা উচিৎ,নাকি উচিৎ নয়? তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে কীভাবে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করা হবে?
ইতিহাসে সব সময়ই নারী একটি ভূমিকার অধিকারী ছিলো এবং এখনো রয়েছে;কেউই নারীর এ ভূমিকা অস্বীকার করে নি। তা হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টিতে নারীর পরোক্ষ ভূমিকা। বলা হয়,নারী পুরুষকে তৈরী করে আর পুরুষ ইতিহাস তৈরী করে। এর মানে হচ্ছে নারীকে গড়ে তোলার ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষকে গড়ে তোলার ব্যাপারে নারীর ভূমিকা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা বড় ধরনের প্রশ্ন যে,পুরুষ নারীর চেতনা,মন-মানস ও ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দেয় কি না,তা মা হিসেবেই হোক বা স্ত্রী হিসেবেই হোক? নাকি নারীই তার সন্তানদেরকে,এমনকি স্বামীকে গড়ে তোলে? বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, স্বামীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকা বেশী,নাকি স্ত্রীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বামীর ভূমিকা বেশী? বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে,ইতিহাস গবেষণা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে ,নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে পুরুষের ভূমিকা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে তুলনায় পুরুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নারীর ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইতিহাস সৃষ্টিতে নারীর পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারী যে পুরুষকে গড়ে তুলেছে এবং পুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেল তা হবে এক সুদীর্ঘ আলোচনা।
এবার আমরা দেখবো যে,ইতিহাস দৃষ্টিতে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা কী ধরনের এবং কী ধরনের হওয়া উচিৎ ও কী ধরনের হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে একটি অবস্থা হতে পারে এই যে,মূলগতভাবেই ইতিহাস দৃষ্টিতে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকতে পারে অর্থাৎ নারীর ভূমিকা পুরোপুরি নেতিবাচক হতে পারে। বিশ্বের অনেক মানব সমাজে সন্তান জন্মদান,লালন-পালন ও গৃহের অভ্যন্তরের বিষয়াদি পরিচালনা ছাড়া নারীর পালনীয় আর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করা হয় না। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজে নারীর কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই,কেবল পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। অতএব,এরুপ সমাজে নারীর ভূমিকা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ আর পরিবারে গড়ে ওঠা পুরুষের ভূমিকা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নারী অনেক সমাজেই পুরুষের মাধ্যমে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা ছাড়া সমাজে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ ভূমিকার অধিকারী নয়।
কিন্তু এ ধরনের সমাজ সমূহে নারী যে ইতিহাস ও সমাজ গঠনে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ ভূমিকার অধিকারী ছিলো না,শুধু তা-ই নয়,বরং নিঃসন্দেহে এবং এ ব্যাপারে পরিচালিত প্রচারের বিপরীতে নারী একটি মূল্যবান জিনিস রূপে অস্তিত্বমান থাকতো। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হিসেবে সে খুবই সামান্য ভূমিকার অধিকারী ছিলো,কিন্তু সে ছিলো একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। আর সে এভাবে মূল্যবান জিনিস হবার কারণেই পুরুষের ওপর তার ভূমিকার প্রভাব ছিলো। সে এমন সস্তা ছিলো না যে পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকবে এবং তার থেকে সুবিধা হাসিলের জন্য শত সহস্র পাবলিক প্লেস বা উদ্যান থাকবে। বরং কেবল পারিবারিক জীবনের বৃত্তের মধ্যেই তার কাছ থেকে সুবিধা লাভ করা সম্ভব ছিলো। অতএব,অনিবার্যভাবেই পরিবারের পুরুষ সদস্যের জন্য সে ছিলো একটি অত্যন্ত মূল্যবান অস্তিত্ব । কারণ,সে ছিলো একমাত্র অস্তিত্ব যে পুরুষের যৌন ও স্নেহ-মমতার প্রয়োজন পূরণ করতো। অতএব,অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কার্যতঃ পুরুষ তার খেদমতে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু নারী ছিলো একটি জিনিস,একটি মূল্যবান জিনিস,ঠিক যেমন হীরা একটি মূল্যবান রত্ন। তবে সে ব্যক্তি ছিলো না,সে ছিলো একটি জিনিস একটি মূল্যবান জিনিস।
ইতিহাসে নারীর অন্য এক ধরনের ভূমিকাও ছিলো এবং প্রাচীন সমাজে নারীর এ ধরনের ভূমিকা অনেক দেখা যায়। তা হচ্ছে ,নারী ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী এক উপাদান রূপে ভূমিকা পালন করেছে। সে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে এবং ব্যক্তি হিসেবে এ ভূমিকা পালন করেছে,জিনিস হিসেবে নয়। কিন্তু সে ছিলো মূল্যহীন ব্যক্তি-যার ও পুরুষের মধ্যকার সম্মানার্হ দেয়াল (حریم ) তুলে নেয়া হয়েছিলো। সুক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে,নারীকে প্রিয় করে তোলা ও রাখার জন্য তার মনস্তাত্ত্বিক গঠনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ণভাবে পরিকল্পনা করে তৈরী করা হয়েছে। আর যখনই এ সীমারেখা উঠে গেছে এবং এ সম্মানার্হ দেয়াল পুরোপুরি ধ্বসে পড়েছে তখনই সম্মান,মর্যাদা ও সম্ভ্রমের বিচারে নারীর ব্যক্তিত্ব নীচে নেমে এসেছে। অবশ্য অন্য কোনো দিক থেকে তার ব্যক্তিত্ব উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকতে পারে,যেমনঃ সে শিক্ষিতা হয়েছে,সে জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞানী হয়েছে,কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের কাছে সে যেরূপ মহামূল্য অস্তিত্ব ছিলো অতঃপর আর তা থাকে নি।
অন্যদিকে নারী নারী না হয়ে পারে না। নারীর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে,সে পুরুষের জন্য অত্যন্ত মহামূল্য হবে। আর নারীর প্রকৃতি থেকে এ বৈশিষ্ট্যটি যদি বিলুপ্ত করে দেয়া হয় তাহলে নারীর গোটা চেতনাই বিলুপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসাবে নারীকে নিজের এখতিয়ারে পাওয়া;নারী তার জন্য একটি মহামূল্য অস্তিত্ব বিধায় নিজেকে তার এখতিয়ারে সোপর্দ করা পুরুষের লক্ষ্য নয়। অন্য দিকে নারীর প্রকৃতিতে যা নিহিত তা এটা নয় যে,পুরুষ তাকে একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসাবে স্বীয় এখতিয়ারে নিয়ে নিক। বরং তার প্রকৃতির দাবী হচ্ছে এই যে,একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসেবে সে-ই পুরুষকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে।
নারী যখন তার বিশেষ অবস্থা থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হলো (এজন্য প্রচলিত বিবাহ প্রথা পরিত্যাগ অপরিহার্য নয়),অর্থাৎ নারী যখন সস্তা হয়ে গেলো,তাদেরকে প্রকাশ্য জায়গাগুলোতে ব্যাপকভাবে দেখা গেলো,সস্তা পুরুষদের দ্বারা তাদেরকে ব্যবহারের জন্য হাজারো উপায় উদ্ভাবিত হলো,রাস্তাঘাট ও অলি গলি নারীর প্রদর্শনীস্থলে পরিণত হলো যেখানে নারী নিজেকে পুরুষের কাছে প্রদর্শন করতে পারে এবং পুরুষ নারীর শরীরের যৌন আকর্ষণীয় অঙ্গ– প্রত্যঙ্গসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করার ও তাকিয়ে দেখার,নারীর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর শোনার ও তাকে স্পর্শ করার সুযোগ পেলো এবং এভাবে তাকে সস্তায় সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের সুযোগ পেলো তখন নারী তার মূল্য-পুরুষের কাছে তার যে মূল্য থাকা উচিৎ ছিলো সে মূল্য-হারিয়ে ফেললো। অর্থাৎ অতঃপর আর নারী পুরুষের কাছে মহামূল্য অস্তিত্ব নেই,যদিও হতে পারে যে,সে অন্য অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে,উদাহরণস্বরূপ,সে শিক্ষিতা হয়েছে,পড়াশুনা করেছে,সে শিক্ষিকা হতে পারে,ক্লাস নিতে পারে,সে ডাক্তার হয়ে থাকতে পারে। সে এর সব কিছুই হতে পারে,কিন্তু এ অবস্থায় অর্থাৎ সে যখন সস্তা হয়ে যায়,তখন একজন নারীর প্রকৃতিতে যে মূল্য নিহিত রয়েছে সে মূল্য আর তার থাকে না। প্রকৃত পক্ষে এহেন অবস্থায়ই নারী পুরুষ সমাজের কাছে ভিন্ন এক ধরনের খেলনায় পরিণত হয়,কিন্তু পুরুষ সমাজের একজন সদস্যের কাছে তার যে মর্যাদা ও সম্মান থাকা উচিৎ তা আর থাকে না।
ইউরোপীয় সমাজ এদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ সেখানে একদিকে যেমন নারীর জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি কতগুলো মানবিক প্রতিভা ও সম্ভাবনার বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে ব্যক্তিত্ব প্রদান করা হয়েছে,অন্য দিকে তার মূল্যও গুরুত্বের বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।
এ দুই অবস্থার বাইরে একটি তৃতীয় অবস্থারও অস্তিত্ব রয়েছে। তা হচ্ছে,নারী একজন‘ মহামূল্যবান ব্যক্তি’ হিসেবে গড়ে উঠবে। সে একদিকে যেমন হবে ব্যক্তি অন্যদিকে একই সাথে হবে মহামূল্য । অর্থাৎ একদিকে সে চৈন্তিক,নৈতিক ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে,জ্ঞান,সচেতনতা ইত্যাদি আত্মিক ও মানিবক পূর্ণতার অধিকারী হবে। বলা বাহুল্য যে,জ্ঞান ও সচেতনতা নারীর ব্যক্তিত্বের অন্যতম স্তম্ভ এবং স্বাধীন এখতিয়ারের অধিকারী হওয়া,ইচ্ছার অধিকারী থাকা,শক্তিশালী মনের অধিকারী হওয়া ও সাহসী হওয়া তার ব্যক্তিত্বের অপর একটি স্তম্ভ। সৃজনশীলতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের মানসিক ব্যক্তিত্বের আরেকটি স্তম্ভ। ইবাদতকারিনী হওয়া,স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকা ও তার অনুগত থাকা,তার সাথে এমনকি অত্যন্ত উচু স্তরের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকা-যে স্তরের সম্পর্ক ছিলো নবী-রাসূলগণের (আঃ)-এ সব হচ্ছে সেই সব বৈশিষ্ট্য যা নারীকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে। অন্যদিকে নারী সামাজিক অঙ্গনে অশ্লীলভাবে উপস্থিত হবে না ও অশ্লীলতার কারণ হবে না। অর্থাৎ কোনো কোনো সমাজে নারীর ওপরে যে কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে তার ওপর সে সীমাবদ্ধতা যেমন থাকা উচিৎ নয়,তেমনি তার জন্য পুরুষের সাথে মিশে যাওয়াও উচিৎ নয়। না নারীর জন্য কঠোর সীমাবদ্ধতা থাকবে,না অবাধ মেলামেশা থাকবে,বরং উভয়ের মাঝে এক সম্মানার্হ সীমারেখা থাকবে। সম্মানার্হ সীমারেখা (حریم ) হচ্ছে নারীর ওপরে কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা-এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ একটি অবস্থা।
আমরা যখন এ ব্যাপারে ইসলামী সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখতে পাই যে,ইসলাম নারীর ব্যাপারে যা চায় তা হচ্ছে ,সে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে তেমনি সে হবে মহামূল্য । তার এই ব্যক্তিত্ব ও মহামূল্যতার কারণেই ইসলামী সমাজে লজ্জাশীলতা ও শালীনতা বিরাজ করে এবং মনগুলো নির্মল ও সুস্থ থাকে,সমাজের বুকে পরিবার রূপ সংগঠনগুলো টিকে থাকে এবং সব দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষ গড়ে ওঠে।
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মহামূল্য হওয়ার মানে হচ্ছে এই যে,ইসলাম তার ও পুরুষের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা উভয়ের জন্যেই সম্মানার্হ। অর্থাৎ ইসলাম এর অনুমতি দেয় না যে,পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে অর্থাৎ সমাজের মঞ্চে নারীর কাছ থেকে পুরুষের সুবিধা গ্রহণ তথা যৌন আস্বাদনের সুযোগ থাকবে,তা সেটা পুরুষ কর্তৃক নারীর শরীর ও যৌন উদ্দীপক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতই হোক,বা তার শরীর স্পর্শ করাই হোক,তার শরীরের সুবাস গ্রহণই হোক বা তার পায়ের ধ্বনি (প্রচলিত কথায় যা উচ্ছাস সৃষ্টিকারী) শুনেই হোক। ইসলাম এগুলোকে অনুমোদন দেয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে,জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা,এখতিয়ার ও ইচ্ছাশক্তি,ঈমান ও ইবাদত,শিল্পকলা,সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম কী বলে? হ্যাঁ,এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে কতগুলো কাজকে হারাম করেছে,কিন্তু যে সব কাজ হারাম করে নি তা কারো জন্যই হারাম করে নি। বস্তুতঃ ইসলাম নারীর জন্য ব্যক্তিত্ব চায়, তবে তার জন্য অশ্লীলতা চায় না।
অতএব,ইতিহাস গঠনে কেবল পুরুষের ভূমিকা ছিলো অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক ভূমিকা ছিলো-এ বিষয়টির তিনটি রূপ পাওয়া যেতে পারে। একটি হচ্ছে এই যে,ইতিহাস মানেই পুরুষের ইতিহাস অর্থাৎ যে ইতিহাস সরাসরি পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে-যাতে নারীদের কোনোই ভূমিকা নেই।
আরেকটি ইতিহাস হচ্ছে নারী ও পুরুষের যৌথভাবে গড়ে তোলা ইতিহাস,তবে সেখানে নারী ও পুরুষ সংশ্রিত;সেখানে পুরুষ তার অক্ষের সীমারেখার মধ্যে থাকবে এবং নারী তার অক্ষের সীমারেখার মধ্যে থাকবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তা এমন এক ইতিহাস যেখানে এসে এ ছন্দের পতন ঘটেছে। পুরুষরা নারীর বৃত্তে অবস্থান নিয়েছে এবং নারীরাও পুরুষের বৃত্তে অবস্থান নিয়েছে। আমরা যদি বর্তমান যুগের কতক ছেলে ও মেয়ের বা নারী ও পুরুষের পোশাকের ধরনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই কীভাবে তারা পরস্পরের জায়গাকে বদল করেছে।
আর তৃতীয় ধরনের ইতিহাস হচ্ছে নারী ও পুরুষের ইতিহাস যে ইতিহাস একদিকে যেমন পুরুষের হাতে গড়ে উঠেছে,তেমনি তা নারীর হাতেও গড়ে উঠেছে। তবে পুরুষ তার অক্ষের সীমারেখার ভিতরে থেকেছে এবং নারীও তার অক্ষের সীমারেখার ভিতরে থেকেছে। আমরা যখন কোরআন মজীদে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে,পবিত্র কোরআন ধর্মের ইতিহাসকে যেভাবে তুলে ধরেছে তা নারী ও পুরুষের এক যৌথ ইতিহাস,সে ইতিহাসে নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণ নেই,বরং পুরুষ নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ভূমিকা পালন করেছে এবং নারী তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ভূমিকা পালন করেছে।
কোরআন মজীদ তার নির্বাচিত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একই সাথে ইতিহাসের সত্যপন্থী ও পবিত্র পুরুষদের কথা বলেছে এবং ইতিহাসের সত্যপন্থী ও পবিত্র নারীদের কথা বলেছে। হযরত আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীর কাহিনীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য মনে করি।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয় যে,খৃষ্টানরা বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে অত্যন্ত ভুল একটি ধারণা প্রবিষ্ট করিয়েছে যা প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য । [আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিবাহ না করার যুক্তিতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের বিবাহ বর্জন ও কৌমার্য ব্রত গ্রহণ এ ধারণাকে শক্তিশালী করেছে।] খৃষ্টানদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এরূপ ধারণা তৈরী হয়ে যায় যে,মূলগতভাবেই নারী হচ্ছে পাপ ও প্রতারণার হাতিয়ার তথা ছোট শয়তান। পুরুষ লোক নিজে নিজেই তথা স্ব-উদ্যোগে পাপকার্যে লিপ্ত হয় না,বরং নারী হচ্ছে ছোট শয়তান-যে সব সময় পুরুষকে কুমন্ত্রণা দেয় ও তাকে পাপকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। তারা বলে যে,মূলতঃ আদম ও হাওয়ার ঘটনা এভাবে শুরু হয় যে,শয়তান আদমেক প্রভাবিত করতে পারছিলো না,তাই সে হাওয়ার কাছে এসে তাকে প্রতারিত করে এবং হাওয়া আদমকে প্রতারিত করেন। আর মানব জাতির গোটা ইতিহাস জুড়ে সব সময়ই এমনই ঘটেছে যে,বড় শয়তান নারীকে ও নারী পুরুষকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে।
বস্তুতঃ খৃষ্টানদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী এভাবেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদ এর বিপরীত কথা বলে,আর যারা তা জানে না তাদের কাছে তা বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে।
কোরআন মজীদ যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করে তখন কাহিনীর মূলনায়ক হিসেবে হযরত আদম (আঃ)কে তুলে ধরেছে এবং হযরত হাওয়া (আঃ) কে দেখিয়েছে তার অনুসরণকারী হিসেবে। মহান আল্লাহ প্রথমে বলেন যে,আমি তাদের উভয়কে (শুধু আদমকে নয়) বললাম যে,তোমরা বেহেশতে বসবাস করো,তবে
) لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ(
‘‘ তোমরা দু’ জন এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না।” ( বাক্বারাঃ 36 ) (সে বৃক্ষটি যে বৃক্ষই হোক না কেন তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।) এরপর আল্লাহ বলেনঃ .
) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ(
‘‘ অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিলো।’’ ( আ ‘ রাফঃ 19 )
এখানে কোরআন বলেনি যে,শয়তান তাদের একজনকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো এবং তিনি অপর জনকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলেন। অতঃপর কোরআন বলেঃ
) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ(
‘‘ এরপর সে উভয়ের নিকট প্রতারণা মূলক যুক্তি উপস্থাপন করলো।’’ ( আ ‘ রাফঃ 21 ) এখানে দ্বিবচন বাচকهما সর্বনামটির ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য অর্থাৎ সে যা বলে প্রতারণা করতে চাচ্ছিলো তা উভয়ের সামনে উপস্থাপন করেছিলো।
আর قَاسَمَهُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ “ সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বললো যে,অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের কল্যাণকামীদের অন্যতম।’’ ( আ ‘ রাফঃ 20 ) এখানেও‘ তাদের উভয়ের’ (هُمَا ) ও‘ তোমাদের উভয়ের’ (کما ) সর্বনামের ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য । এ থেকে সুস্পষ্ট যে,এ ব্যাপারে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়ের বিচ্যুতির পরিমাণ সমান।
এ ঘটনার ধর্মীয় ইতিহাসে যে ভ্রান্ত চিন্তা স্থান দেয়া হয়েছে এবং যে মিথ্যা রচনা করা হয়েছে ইসলাম তাকে অপসারিত করেছে এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে,মহান আল্লাহর নিষেধ না মানার ঘটনা এমন নয় যে,শয়তান নারীকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে আর নারী পুরুষকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে,অতএব,নারী মানে পাপের হাতিয়ার। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন মজীদ মহান পবিত্র পুরুষদের কথা উল্লেখের পাশাপাশি মহান পবিত্রা নারীদের কথা উল্লেখ করেছে এবং তাদের সকলেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে পবিত্র পুরুষ ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত সারাহ (আঃ) কে কতই না প্রশংসিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে! হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেভাবে ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের অধিকারী ছিলেন এবং তাদেরকে দেখতে পেতেন ও তাদের কথা শুনতে পেতেন হযরত সারা (আঃ) ও একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ফেরেশতা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে বললো যে,আপনাদের প্রতিপালক আপনাদেরকে সন্তান দিতে ইচ্ছা করেছেন তখন হযরত সারা তা একইভাবে শুনতে পেলেন এবং বিস্মিত হয়ে বললেনঃ
) اَ اَلِدُ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِی شَيْخاً( .
‘‘ আমাদের কি সন্তান হবে যখন আমি বন্ধ্যা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ !’’ ( হুদঃ 72 ) ফেরেশতা তখন হযরত সারা (আঃ) কে সম্বোধন করে জবাব দেয়,হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে সম্বোধন করে নয়,বলেঃ
) اَ تَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ الله(
‘‘ আপন কি আল্লাহর কাজে বিস্মিত হচ্ছেন?’’ ( হুদঃ 73 ) একইভাবে মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন বলেনঃ
) وَ اَوْحَيْنَا اِلَی اُمِّ مُوسَی اَنْ اَرْضِعِيه(
‘‘ আর আমরা মূসার মাকে ওহী করলাম যে,তাকে (মূসাকে) দুধ পান করাও।’’ ( আল - ক্বাছাছঃ 7 ) আল্লাহ তা‘ আলাও হযরত মূসা (আঃ)-এর মাকে সম্বোধন করে ওহী মারফত আরো বলেনঃ
) فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِی وَ لَا تَحْزَنِی اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْکَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ( .
‘‘ আর তুমি যখন তার ব্যাপারে ভয় করবে তখন তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও আর তার ব্যাপারে ভয় করো না ও দুশ্চিন্তা করো না;নিঃসন্দেহে আমরা তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো। আর অবশ্যই আমরা তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছি।’’ ( প্রাগুক্ত আয়াত )
কোরআন মজীদ হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর কাহিনী বলতে গিয়ে বিস্ময়কর সব তথ্য উপস্থাপন করেছে। নাবীগণ (আঃ) পর্যন্ত এ মহীয়সী নারীর মর্যাদার কাছে শ্রদ্ধায় নতজানু হন। তার খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ) যখন তার কাছে আসনে তখন দেখতে পান যে,মাইয়ামের কাছে এমন সব নে‘ আমত (তাজা ফলমূল) রয়েছে যা সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের কোথাও পাওয়া যায় না। তাই তিনি বিস্মিত হন। কোরআন মজীদ বলে,মারইয়াম যখন মেহরাবে ইবাদতে রত ছিলেন তখন ফেরেশতারা এসে তার সাথে কথা বলে।
) اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللهَ يُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَی بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ(
‘‘ ফেরেশতারা যখন বললোঃ হে মারইয়াম! অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ থেকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম ঈসা মসী ইবনে মারইয়াম-যিনি এই দুনিয়ায় ও পরকালে অত্যন্ত সম্মানিত এবং তিনি (আল্লাহ তা‘ আলার) নৈকট্যের অধিকারীদের অন্যতম।’’ ( আল ‘ ইমরানঃ 45 )
এখানে দেখা যাচ্ছে যে,ফেরেশতারা সরাসরি হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর সাথে কথা বলছে। হযরত মারইয়াম (আঃ) কে নবী হিসেবে পাঠানো হয় নি। আল্লাহ এ নিয়ম করেন নি যে,একজন নারীকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন। তাই হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর এত বড় মর্যাদা সত্ত্বেও তাকে নবী হিসেবে পাঠানো হয় নি,কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক নবীর (আঃ) চেয়ে উচ্চতর। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে,হযরত যাকারিয়া (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও এবং হযরত মারইয়াম (আঃ) নবী না হওয়া সত্ত্বেও মারইয়াম (আঃ)-এর মর্যাদা যাকারিয়া (আঃ)-এর চেয়ে বেশী ছিলো।
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সম্বোধন করে হযরত ফাতেমা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআন মজীদে এরশাদ করেনঃ
) اِنَّا اَعْطَيْنَاکَ الْکَوْثَرَ(
‘‘ অবশ্যই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি।’’ ( আল - কাওছারঃ 1 )
বস্তুতঃ একজন নারীর মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাকে‘‘ কাওছার’’ হিসেবে অভিহিত করার চেয়ে উন্নততর আর কোনো পরিভাষা পাওয়া যেতে পারে না। যে দুনিয়ায় নারীকে নিরঙ্কুশ অনিষ্ট বলে গণ্য করা হতো এবং তাকে প্রতারণা ও পাপের হাতিয়ার মনে করা হতো সেই দুনিয়ায় কোরআন মজীদ একজন নারী সম্পর্কে বলছে,না,সে কল্যাণের আকর;সে শুধু কল্যাণের আকরই নয়,বরং সে হচ্ছে‘ কাওছার’ -বিপুল কল্যাণের আকর;দুনিয়াজোড়া কল্যাণের উৎস।
এ প্রসঙ্গে আসুন আমরা ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর সেই প্রথম দিনেই দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেনঃ হযরত আলী (আঃ) ও হযরত খাদীজা (আঃ)। তাদের উভয়ই ইসলামের ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের দেড়শ’ বছর পরে ইবনে ইসহাক যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তিনি হযরত খাদীজার মর্যাদা এবং নবী করীম (সাঃ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভূমিকা,বিশেষ করে তার সান্তনাদায়ক ভূমিকা তুলে ধরেছেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন,হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর-যে বছর হযরত আবু তালেবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন,সত্যি সত্যিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য দুনিয়া সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) যখনই হযরত খাদীজার নাম উল্লেখ করতেন তখনই তার পবিত্র চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে যেতো। হযরত আয়শা বলেনঃ‘‘ একজন বৃদ্ধার গুরুত্ব তো এত বেশী নয়;কী ব্যাপার!’’ জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ‘‘ তুমি কি মনে করছো যে,আমি খাদীজার শরীরের জন্য কান্না করছি? কোথায় খাদীজা,আর কোথায় তুমি ও অন্য সকলে!’’
আপনারা যদি ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে,ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে নারী-পুরুষের ইতিহাস। তবে এ ইতিহাসে পুরুষ তার অক্ষের চারদিকে এবং নারী তার অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যেমন পুরুষ সাহাবী ছিলেন তেমনি নারী সাহাবীও ছিলেন। এখন থেকে হাজার বছর পূর্বে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে যেমন পুরুষ বর্ণনাকারীর (راوی ) বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত নেয়া হয়েছে তেমনি নারী বর্ণনাকারীর (راوی ) বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত রয়েছে। আমাদের কাছে এমন বিপুল সংখ্যক হাদীস ও রেওয়ায়েত এসেছে যার বর্ণনাকারী নারী। একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যার নাম“ বালাগ্বাতুন নেসা” যাতে নারীদের প্রাঞ্জল ও সুউচ্চ সাহিত্যিক মানসম্পন্ন ভাষণ স্থানলাভ করেছে। বাগদাদী হিজরী 250 সালের দিকে-হযরত ইমাম হাসান‘ আসকারী (আঃ)-এর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি সংকলিত করেন। (স্মর্তব্য ,ইমাম হাসান আসকারী হিজরী 260 সালে শহীদ হন।) বাগদাদী তার এ গ্রন্থে যে সব ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে ইবনে যিয়াদের মজলিসে ইয়াযীদের মসজিদে প্রদত্ত হযরত যায়নাব (আঃ)-এর ভাষণ এবং হযরত আবু বকরের খেলাফতের শুরুর দিকে মসজিদে নববীতে প্রদত্ত হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ আঃ)-এর ভাষণ অন্যতম।
সাম্প্রতিক কালে হযরত মা‘ ছূমা (আঃ) (হযরত ফাতেমা মা‘ ছূমা (আঃ) ছিলেন হযরত ইমাম মূসা কাযেম (আঃ)-এর কন্য ও হযরত ইমাম রেযা (আঃ)-এর বোন। ইরানের দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্র কোম নগরীতে তার মাযার রয়েছে এবং তার মাযারকে কেন্দ্র করেই কোম ইরানের অন্যতম জ্ঞান নগরীতে পরিণত হয়েছে)-এর মাযারের জন্য যে নতুন রেলিং তৈরী করা হয়েছে তার ওপর যেসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সবগুলোর বর্ণনাকারীই হচ্ছেন নারী-যেসব হাদীসের বর্ণনা হযরত নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখানে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে,এজন্য কেবল সেই সব হাদীস বেছে নেয়া হয়েছে যেগুলোর বর্ণনাকারীদের সকলের নামই ফাতেমা এবং তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন। বর্ণনার ধারাক্রম এরূপ যে,অমুকের কন্যা ফাতেমা অমুকের কন্যা ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি অমুকের কন্যা ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে তা ফাতেমা বিনতে মূসা ইবনে জা‘ ফর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর এর ধারাবাহিকতা এগিয়ে চলে ফাতেমা বিনতে হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালেব এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত নবী-তনয়া হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে।
এ থেকেই বুঝা যায় যে,নারীদের হাদীস শ্রবণ ও জ্ঞান আহরণের বিষয়টি কতখানি প্রচলিত ছিলো। কিন্তু তারা কখনোই অবাধ মেলামেশা করতেন না। অনেক বর্ণনাকারীই হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের কাছ থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ই হাদীস শ্রবণ করেছেন। তবে নারীরা এক পাশে বসতেন এবং পুরুষরা আরেক পাশে বসতেন;কখনোবা নারীরা একটি কক্ষে এবং পুরুষরা অন্য একটি কক্ষে বসতেন। তারা এজন্য আসতেন না যে,এমনভাবে চেয়ার পাতা হবে যে,একজন নারী ও একজন পুরুষ পাশাপাশি বসবে এবং নারী এমনভাবে মিনি স্কার্ট পরিধান করবে যে,তার উরুর উর্ধাংশ পর্যন্ত দেখা যাবে। হ্যাঁ,বলা হয় যে,মহিলা জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছেন। বুঝাই যায় যে,বাইরে এক ও ভিতরে অন্য কিছু । এর বিপরীতে ইসলাম জ্ঞানার্জনের কথা বলে। বলে,এমন পরিবেশে জ্ঞানচর্চা করতে হবে যার সাথে প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করার সংযোগ থাকবে না, প্রতারণা থাকবে না,থাকবে ব্যক্তিত্বের পরিচয়।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) ও হযরত আলী (আঃ)-এর মধ্যে বিবাহ হওয়ার পর তারা তাদের সংসারের কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা চাচ্ছিলেন যে,রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তা ভাগ করে দিবেন। কারণ,এটা তাদের কাছে আনন্দজনক হবে বলে তারা মনে করছিলেন। তাই তারা তার কাছে গেলেন এবং বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মন চায় যে,আপনি আমাদের সংসারের কাজগুলো আমাদের দু’ জনের মধ্যে ভাগ করে দিন;বলে দিন কে কোন কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরের বাইরের কাজগুলো হযরত আলীর জন্য এবং ঘরের ভিতরের কাজগুলো হযরত ফাতেমার জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) বলেন,তোমরা জানো না যে,আমার পিতা বাইরের কাজগুলোর দায়িত্ব থেকে আমাকে রেহাই দেয়ায় আমি কত খুশী হয়েছি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী নারী এমনই যিনি লোভ বা ঈর্ষা করবেন না।
এবার লক্ষ্য করুন এই যে হযরত ফাতেমা যাহরা,তার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিলো? তার ভিতরে নিহিত সম্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ কী ধরনের ছিলো? তার জ্ঞান কোন পর্যায়ের ছিলো? তার ইচ্ছা শক্তি কেমন ছিলো? তার ভাষণ ও বক্তব্যে প্রঞ্জলতা কেমন ছিলো?
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) খুব কম বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করেন। আর ঐ সময় তার দুশমনের সংখ্যা ছিলো অনেক। এ কারণে তার জ্ঞানসম্পদের খুব কমই পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলো। তার আয়ুস্কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিতর্ক আছে। ইন্তেকালের সময় তার বয়স আঠারো থেকে সর্বোচ্চ সাতাশ বছর ছিলো বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ বয়সে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি যে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী) ভাষণ দেন। সৌভাগ্যক্রমে তা পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের কাছে পৌছেছে। আর এটা কেবল শিয়া মাযহাবের সূত্রেই বর্ণিত হয় নি,বরং হিজরী তৃতীয় শর্তাব্দীতে বাগদাদী তার গ্রন্থে এ ভাষণটি উদ্ধৃত করেছেন। তার এই একটি ভাষণই এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে,মুসলিম নারী পুরুষের কাছ থেকে নিজের মর্যাদার সীমারেখা সংরক্ষণ করেও এবং নিজেকে পুরুষদের কাছে প্রদর্শন না করেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত উচুঁস্তরে উঠতে পারেন এবং সমাজের কাজকর্মে নারী অংশ নিলে তা কতখানি হওয়া উচিৎ।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ)-এর ভাষণে তাওহীদের আলোচনা রয়েছে এবং তা‘ নাহজুল বালাগ্বা’ র সম পর্যায়ের অর্থাৎ তা এমনই উচুঁ স্তরের যে,দার্শনিকগণ পর্যন্ত সে স্তরে উপনীত হতে সক্ষম নন। তিনি যখন আল্লাহর সত্তা ও তার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন মনে হয় যে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকগণের অন্যতম। এমনকি ইবনে সীনার মতো এত বড় দার্শনিকের পক্ষেও এ ধরনের ভাষণ দান করা সম্ভব ছিলো না। এরপর সহসাই তিনি শারয়ী আহকামের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেনঃ আল্লাহ তা‘ আলা নামাযকে এজন্য ফরয করেছেন,রোযাকে এ কারণে ফরয করেছেন,হজ্ব কে এজন্য ফরয করেছেন,আমর বিল মা‘ রুফ ওয়া নাহি‘ আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ) ফরয হবার কারণ এই,যাকাতকে অমুক কারণে ফরয করা হয়েছে ইত্যাদি। এরপর তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব গোত্রসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করতে শুরু করেন এবং ইসলাম তাদের জীবনে কী পরিবর্তন এনে দিয়েছে তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে,তোমরা আরবরা এই রকম ছিলে,ঐ রকম ছিলে ইত্যাদি। ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের বস্তুগত ও নৈতিক-আত্মিক অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বস্তুগত ও নৈতিক-আত্মিক অবস্থায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) মসজিদে নববীতে হাজার হাজার লোকের সামনে তার এ ভাষণ পেশ করেন। কিন্তু তিনি আত্ম প্রদর্শনীর জন্য মিম্বারে ওঠেন নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত একটি রীতি ছিলো এই যে,মজলিসে নারী ও পুরুষরা আলাদা বসতেন এবং তাদের মাঝখানে একটি পর্দা টানিয়ে দেয়া হতো। হযরত ফাতেমা যাহরা’ (সাঃ আঃ) পর্দার আড়াল থেকে তার পুরো ভাষণ পেশ করেন এবং মজলিসে উপস্থিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই অভিভূত করে ফেলেন।
এর মানে হচ্ছে এই যে,ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি,মুসলিম নারী একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী অন্য দিকে লজ্জাশীলতারও অধিকারী,যেমন পবিত্রতার অধিকারী তেমনি স্বীয় মর্যাদার সীমারেখাকে মেনে চলেন;কখনো নিজেকে পুরুষদের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে পেশ করেন না। কিন্তু মুসলিম নারী এমন কোনো হস্তপদ বিহীন অর্থব সত্তা নয় যার মাথায় কিছুই ঢোকে না এবং দুনিয়ার কোনো কিছুরই খবর রাখে না।
কারবালার ইতিহাস হচ্ছে নারী-পুরুষের ইতিহাস। এ হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা ছিলো,কিন্তু পুরুষরা স্বীয় অক্ষের চারদিকে এবং নারীরাও স্বীয় অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয়েছেন। এগুলো হচ্ছে ইসলামের মু’ জিযা। ইসলাম চায় আজকের দুনিয়া ও ভবিষ্যত দুনিয়া এগুলোকে গ্রহণ করুক;জাহান্নাম গ্রহণ না করুক।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যান। কারণ,তিনি চাচ্ছিলেন যে,তারা কাফেলার নেত্রী হযরত যায়নাব (আঃ)-এর নেতৃত্বে স্বীয় অক্ষের সীমারেখা থেকে বাইরে না এসেও এ বিরাট ইতিহাসে একটি বড় ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন-এ ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন।
আশূরার দিন বিকালে হযরত যায়নাব স্বমহিমায় সমুদ্ভাসিত হলেন। এর পরবর্তী দায়িত্ব তার ওপরে অর্পিত হয়েছিলো। তিনি হলেন কাফেলার নেত্রী। কারণ,এ কাফেলার একমাত্র পুরুষ সদস্য ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) এ সময় গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং এ কারণে তার নিজেরই সেবাশুশ্রূষার প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য ইবনে যিয়াদের সাধারণ নির্দেশ ছিলো এই যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যই যেন জীবিত না থাকেন। তদনুযায়ী ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে হত্যা করার উদ্দেশ্য শত্রুরা বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছিলো। কিন্তু তারা তার অবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেঃ‘‘ নিঃসন্দেহে সে নিজেই সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 61 ; এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ 246 ; ইরশাদ - শেখ মুফীদ , পৃষ্ঠাঃ 242 ) অর্থাৎ তিনি তো এমনিতেই মারা যাচ্ছেন।
বস্তুতঃ এ ছিলো মহান আল্লাহর কল্যাণ-ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে,এভাবে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) বেঁচে থাকুন এবং তার মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পবিত্র বংশধারা টিকে থাকুক।
হযরত যায়নাব (আঃ) এ সময় যে সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর সেবা-শুশ্রূষা।
11ই মহররম বিকালে বন্দীদেরকে বাহনে (উটের বা খচ্চরের বা উভয়ের পিঠে) সওয়ার করানো হলো। এগুলোর জিন ছিলো কাঠের তৈরী। বন্দীদেরকে মানসিক কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনের ওপরে কাপড় বিছাতে বাধা দেয়া হয়। রওয়ানা হওয়ার আগে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ জানানো হয় এবং সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়।
قُلْنَ بِحَقِّ اللهِ اِلَّا مَا مَرَرْتُمْ بِنَا عَلَی مِصْرَعِ الْحُسَيْنِ.
‘‘ তারা (বন্দী নারীরা) বললেনঃ আল্লাহর দোহাই,আমাদেরকে হোসাইনের শাহাদাতস্থল ছাড়া অন্য কোনো জায়গা দিয়ে নিয়ে যেয়ো না।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 58 ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 55 , মাকতালু হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ 396 , মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 39 )
শেষ বারের মতো শহীদগণকে খোদা হাফেযী করার উদ্দেশ্যেই তারা তাদেরকে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতস্থল হয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।
বন্দীদের মধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) খুবই অসুস্থ ছিলেন বিধায় বাহনের ওপর ঠিকভাবে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। এ কারণে তার পা বাহনের পেটের নীচে বেঁধে দেয়া হয়। অন্য সকলেই বাহনের ওপর মুক্তভাবে বসে যান। তারা যখন শাহাদাতস্থলে পৌঁছিলেন তখন সকলেই নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন এবং বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এরপর হযরত যায়নাব হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পবিত্র লাশের নিকট পৌঁছে গেলেন। তিনি তাকে এমন এক অবস্থায় দেখলেন যেরূপ ইতিপূর্বে কখনো কাউকে দেখেন নি। ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর লাশ মাথা বিহীন অবস্থায় পড়ে ছিলো। তিনি তার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে থাকেন,তাদের পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কথা বলতে থাকেন। অন্তরে যত বেদনা ছিলো তার সবই ঢেলে দেন। আর তিনি এতই বিলাপ করেন যে,বর্ণনাকারী বলেনঃ
فَأَبْکَتْ وَ اللهِ کُلَّ عَدُوٍّ وَ صِدِّيقٍ.
‘‘ আল্লাহর শপথ,তিনি দুশমন ও বন্ধু নির্বিশেষে প্রত্যেককেই কাঁদালেন।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 59 ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 56 , মাকতা মুকাররম , পৃষ্ঠাঃ 396 )
বস্তুতঃ সর্ব প্রথম যিনি ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতে শোকানুষ্ঠান করেন তিনি হলেন হযরত যায়নাব (আঃ)। কিন্তু এ সময়ও তিনি তার মূল দায়িত্ব বিস্মৃত হন নি। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব ছিলো তারই। তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে,এ অবস্থা দেখে ইমামক সহ্য করতে পারেছন না,মনে হচ্ছিলো যেন তার প্রাণ দেহের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। হযরত যায়নাব (আঃ) সাথে সাথে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর লাশ রেখে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর নিকট চলে এলেন। তিনি বললেনঃ‘‘ ভাতিজা! তোমার এ অবস্থা কেন যে,মনে হচ্ছে তোমার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে ?’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ ফুফুজান! এটা কী করে সম্ভব যে,প্রিয়জনদের লাশ দেখে কষ্ট না পাবো?’’ তখন হযরত যায়নাব (আঃ) তাকে সান্তনা দিতে শুরু করেন।
ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে সান্তনা দিতে গিয়ে হযরত যায়নাব (আঃ) তাকে উম্মে আইমান থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনান। উম্মে আইমান ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের একজন সম্মানিতা মহিলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী। যতটা জানা যায়,প্রথমে তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা (আ):-এর ক্রীতদাসী যাকে পরে মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু মুক্ত হওয়ার পরেও নবী-পরিবারের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহে হযরত খাদীজা (আঃ)-এর খেদমতে ও তার ইন্তেকালের পরে হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর খেদমতে থেকে যান। তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
দীর্ঘ বহু বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে অবস্থানকারী এ মহিলা পরবর্তী কালে হযরত যায়নাব (আঃ)-এর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যেহেতু হাদীসটি ছিলো আহলে বাইতের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাই হযরত যায়নাব (আঃ) একদিন তার পিতা হযরত আলী (আঃ)-এর খেদমতে এ হাদীসটি পেশ করে এর বক্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার প্রচেষ্টা করেন। তিনি পুরো হাদীসটি পেশ করলে তা শোনার পর হযরত আলী (আঃ) বললেনঃ উম্মে আইমান ঠিকই বলেছেন।
কারবালার ঐ পরিস্থিতিতে হযরত যায়নাব (আঃ) উম্মে আইমান থেকে শোনা এ হাদীস ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে শোনালেন। বস্তুতঃ এ হাদীসের মধ্যে একটি বিশেষ দর্শন নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে,কেউ যেন মনে না করে যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের ফলে সব শেষ হয়ে গেলো। হযরত যায়নাব (আঃ) বললেনঃ‘‘ ভাতিজা! আমাদের নানা (রাসূলুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,এখন যেখানে হোসাইনের লাশ দেখতে পাচ্ছো সেখানে কাফন পরানো ছাড়াই তার লাশ দাফন করা হবে এবং এখানে হোসাইনের কবর যিয়ারতগাহে পরিণত হবে।’’ কবি বলেনঃ
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
که زيارتگه رندان جهان خواهد بود.
‘‘ আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে যখন হিম্মত চাহো
কারণ তা একদিন বিশ্বের আধ্যাত্মবাদীদের যিয়ারতগাহ হবে।’’
হযরত যায়নাব (আঃ) তার ভ্রাতুস্পুত্রকে জানিয়ে দেন যে,একদিন হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদতগাহ ইখলাছের অধিকারী মুসলমানদের যিয়ারতগাহে পরিণত হবে।
11ই মহররম বিকালে বন্দীদের কাফেলাকে পুনরায় রওয়ানা করানো হয়। অন্যদিকে ইয়াযীদী বাহিনীর সেনাপতি ওমর ইবনে সা‘ দের নেতৃত্বে তার সৈন্যরা তাদের নিহত সহযোদ্ধাদের দাফন করার জন্য থেকে যায়। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার সঙ্গীসাথী শহীদগণের লাশ রণাঙ্গনেই পড়ে থাকে।
বন্দীদের কাফেলাকে প্রথমে কারবালা থেকে 12 ফারসাখ (36 মাইল) দূরবর্তী নাজাফে নিয়ে আসা হয়। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে,ঢাক-ঢোল ও বাশী বাজিয়ে এবং বিজয় পতাকা উড়িয়ে আনন্দ-উৎসব সহকারে 12ই মহররম বন্দীদেরকে কুফায় প্রবেশ করানো হবে। তারা এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আহলে বাইতের ওপর সর্বশেষ আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিলো।
হযরত যায়নাব (আঃ) সম্ভবতঃ 9ই মহহরম থেকে মোটেই ঘুমাননি। এহেন এক অবস্থায় বন্দীদেরকে কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। শহীদগণের পবিত্র শিরগুলো আগেই নিয়ে যাওয়া হয়। সূর্যদয়ের দুই-তিন ঘন্টা পরে বন্দীদেরকে কুফায় প্রবেশ করানো হয়। আদেশ দেওয়া হলো যে,বন্দীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেন শহীদদের পবিত্র কর্তিত শিরগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন এমন এক বিস্ময়কর মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার বর্ণনা প্রদান বর্ণনাশক্তির উর্ধ্বে। কুফা নগরীর প্রবেশদ্বারে পৌঁছার পর ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কন্যা ফাতেমা স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হলেন। এ সাহসী বীর নারী স্বীয় নারীসুলভ মর্যাদা বজায় রেখেই সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।
বর্ণনাকারীগণ বলেন,এ পর্যায়ে এক বিশেষ সময়ে হযরত যায়নাব (আঃ) পরিস্থিতিকে তার নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত গণ্য করলেন এবং সকলের প্রতি নীরব হওয়ার জন্য ইশারা করলেন। ইতিহাসের উক্তি এরূপঃ
وَ قَدْ اَوْمَأَتْ اِلَی النَّاسِ اَنْ اُسْکُتُوا فَارْتَدَّتِ الْاَنْفَاسُ، وَ سَکَنَتِ الْاَجْرَاسُ.
‘‘ (সেই গোলযোগ ও হৈ চৈ পূর্ণ পরিস্থিতিতে) তিনি লোকদের প্রতি ইশারা করে নীরব হতে বললেন,ফলে নিঃশ্বাসগুলো (তাদের বুকের মধ্যে ) আটকে গেলো এবং (বাহনগুলো দাড়িয়ে যাওয়ায় তাদের গলায় বাধা) ঘন্টাগুলো নীরব হয়ে গেলো।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 108 ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 42 , মাকতালু মুকাররম , পৃষ্ঠাঃ 402 ; মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 40 ) এরপর হযরত যায়নাব (আঃ) সকলের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ
وَلَمْ اَرَ وَ اللهِ خَفِرَةً قَطُّ اَنْطَقَ مِنْهَا
‘‘ আল্লাহর শপথ, এমন আর কোনো লজ্জাশীলা নারীকে কখনো এমন ভাষণ দিতে দেখিনি।’’ ( প্রাগুক্ত ) এখানে বর্ণনাকারীর ব্যবহৃতخَفِرَةً শব্দটি খুবই গুরুত্বের অধিকারী। কারণ,এ থেকে সুস্পষ্ট যে,তিনি ছিলেন একজন লজ্জাশীলা মহিলা। তিনি কোনো নির্লজ্জ নারীর ন্যায় ভাষণ দিতে আসেন নি। হযরত যায়নাব (আঃ) অত্যন্ত শৌর্যপূর্ণ ও বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ দেন। কিন্টতু তা সত্ত্বেও তার দুশমন পক্ষের বর্ণনাকারীরাও বলতে বাধ্য হনঃ‘‘ আল্লাহর শপথ,এমন আর কোনো লজ্জাশীলা নারীকে কখনো এমন ভাষণ দিতে দেখি নি।’’ অর্থাৎ তিনি নারীসুলভ লজ্জাশীলতা সহকারেই লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তার ভাষণে হযরত আলী (আঃ)-এর বীরত্ব আর নারীসুলভ লজ্জাশীলতা সংমিশ্রি ত হয়েছিলো।
বিশ বছর আগে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী (আঃ) যখন তৎকালীন মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন তখন তিনি কুফায় ছিলেন। কুফা ছিলো তার রাজধানী। তিনি প্রায় পাঁচ বছর খলীফা ছিলেন। এ সময় তিনি বহু ভাষণ প্রদান করেন। তখনো (কারবালার ঘটনার সময়) লোকদের মধ্যে হযরত আলী (আঃ)-এর ভাষণ প্রবাদ বাক্যের মতো প্রচলিত ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন,মনে হচ্ছিলো যেন হযরত যায়নাব (আঃ)-এর কণ্ঠ থেকে হযরত আলী (আঃ)-এর ভাষণ বেরিয়ে আসছে। এ সময় হযরত যায়নাব (আঃ) কোনো দীর্ঘ ভাষণ দেন নি (মাত্র দশ-বারো বাক্যে তিনি তার ভাষণ শেষ করেন)। বর্ণনাকারী বলেনঃ‘‘ দেখলাম যে,লোকেরা সকলেই তাদের আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে কামড়াচ্ছিলো।’’
এই হচ্ছে নারীর এক ধরনের ভূমিকা,যে ধরনের ভূমিকা ইসলাম তার কাছ থেকে আশা করে। লজ্জাশীলতা,সতীত্ব ,পবিত্রতা ও নারী-পুরুষের মধ্যকার অলঙ্ঘনীয় সীমারেখার সংরক্ষণ সহকারে নারী ব্যক্তিত্বই ইসলামের কাম্য । কারবালার ইতিহাস এ কারণে নারী-পুরুষের ইতিহাস যে,এ ইতিহাসের সৃষ্টিতে পুরুষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তেমনি নারীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে পুরুষের ভূমিকা পুরুষের অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয় এবং নারীর ভূমিকা নারীর অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয়। এভাবে এ ইতিহাস নারী ও পুরুষ উভয়ের হাতে গড়ে ওঠে।
মুবাল্লিগের শর্তাবলী এবং ইমাম (আঃ) এর আহলে বাইতের বন্দীকালীন তাবলীগের প্রভাব
ইতিপূর্বের আলোচনায় একটি বার্তার সফলতার জন্য চারটি শর্তের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রথম শর্তত্রয় অর্থাৎ বার্তার শক্তিমান তথা সত্যনির্ভর হওয়া,বার্তাবাহক কর্তৃক সঠিক Method বা কৌশলের প্রয়োগ এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্য উভয় উপকরণাদি ও মাধ্যমসমূহ বিধিসম্মতভাবে ব্যবহার করা-এগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বাকী আছে কেবল চতুর্থ শর্ত । আর সেটা হলো বার্তা বাহক অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার্তা পৌঁছাবে তার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব । তদ্রুপ,হোসাইনী আন্দোলনে তাবলীগের উপাদান সম্পর্কে এবং ইমামের আহল পরিবারের বন্দীকালীন সময়ে কারবালা থেকে কুফা,কুফা থেকে শাম এবং মুক্তি লাভের পরে শাম থেকে মদীনা এবং তৎপরবর্তী কালে তাদের তাবলীগি প্রভাব নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে।এ দু ’ টি বিষয় একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
একজন মুবাল্লিগ এবং বার্তা পৌছানো ব্যক্তির শর্তাবলীর বিষয় এমন একটি বিষয় যা কেন আমাদের সমাজে হালকাভাবে নেয়া হয় এর সঠিক কারণ আমার (ওস্তাদ মুতাহহারী) জানা নেই। কোনো কোনো বিষয়ের মূল্যমান সমাজে ঠিকই বজায় রয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে অন্য বিষয়গুলোর মূল্যমান সমাজ থেকে হারিয়ে যায়। একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য । আমাদের মধ্যে একটি ধর্মীয় সামাজিক মর্যাদা হলো ইফতা ( ফতোয়া প্রদান) এবং মারজায়ে তাকলীদ এর পদটি । এটি একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক পদ। সৌভাগ্যের কথা হলো যে আমাদের সমাজ এপদটির মর্যাদাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে আসছে। ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে যার সামান্যতম পরিচিতি রয়েছে সে যখনই শোনে‘‘ মারজায়ে তাকলীদ’’ -তৎক্ষণাৎ তার মনে জেগে ওঠে এমন একজন ব্যক্তির ধারণা যিনি অন্ততপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে হাঁড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন,কোরআন,হাদীস,ফেকাহ আর তফসীর নিয়ে যার দিন রাত একাকার হয়ে গেছে,বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন,বছরের পর বছর নিজেও শিক্ষকতা করেছেন,একাধিক বই রচনা করেছেন ইত্যাদি। এটা সঠিক এবং এটাই হওয়া উচিত। আল্লাহ যেন সেদিন না আনেন যেদিন এই পদ মানুষের মন থেকে মর্যাদা হারায়। যেমনটা তাবলীগ আর মুবাল্লিগের বেলায় ঘটেছে।
ইসলামের অতীত ইতিহাসে ঘটনা এমনটি ছিল না। আপনি যদি রেজাল শাস্ত্রের বই খুলেন তাহলে দেখতে পাবেন,বহু সংখ্যক ওলামা‘‘ ওয়ায়েজ’’ কিম্বা‘‘ খতীব’’ নামে প্রসিদ্ধ । যেমন খতীব রাযী,খতীব তাবরীযী,খতীব বাগদাদী,খতীব দামেশকী প্রমুখ।‘‘ খতীব’’ -তাদের নামের কোনো অংশ ছিল না। তাহলে এরা কোন ধরণের ব্যক্তি ছিলেন? এরা কি শুধু একজন শোক মজলিসের মার্সিয়া পরিবেশনকারীর মানের ছিলেন যে আমরা আজ আমাদের সমাজে তাদেরকে চিনি? এরা যারা খতীব হিসাবে প্রসিদ্ধ, এদের প্রত্যেকেই ছিলেন এককজন জ্ঞানের সাগর। যেমন ধরুন এই যে খতীব রাযীর কথা বলা হলো তিনি হলেন ফখরুদ্দীন রাযী। ইমাম ফাখর নামে বিখ্যাত। তার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে একটি হলো‘‘ তাফসীরুল কাবীর’’ ত্রিশ খণ্ড বিশিষ্ট । অনেক বড় একটি গ্রন্থ এবং অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ মানুষটি চিকিৎসা,জ্যোতিষ,দর্শন,যুক্তিবিদ্যা,হাদীস,ফেকাহ,ওয়াজ এবং খোতবা দানে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইবনে সীনার ইশারাত গ্রন্থেরও তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং তার ত্রুটিগুলোকেও সনাক্ত করেছেন। আর কেবলমাত্র খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীই সক্ষম হয়েছিলেন তার সনাক্ত করা ইবনে সীনার ত্রুটিগুলোর অপনোদন করতে। এই ব্যক্তিটি হলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন সুদক্ষ ওয়ায়েজ এবং খতীব।
আবার খতীব বাগদাদীর যে গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ রয়েছে সেটা হলো‘‘ তারীখ-ই বাগদাদ’’ । এটি ইসলামের ইতিহাসের একটি ডকুমেন্টারী গ্রন্থও বটে। আর যাকে খতীব তাবরীযী আখ্যায়িত করা হয় তিনি হলেন আরবী সাহিত্য জগতের মাআ’ নি,বাইয়্যান ও বাদি’ শাস্ত্রের বিখ্যাত‘‘ মুতাওওয়াল’’ এর রচয়িতা। এছাড়া আরো যেমন মরহুম মাজলিসী (রহঃ),যিনি শিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম একজন পুরোধা,যিনি একাধারে একজন ওয়ায়েজ এবং খতীবও ছিলেন।
অতীতে ইসলামী পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে খতীব,মুবাল্লিগ তথা ওয়ায়েজ এর পদবীটা সে সকল ব্যক্তির পদবী ছিল যারা মারজায়ে তাকলীদের সমকক্ষ ছিলেন। যেমনভাবে আজ যদি কেউ দাবী করে যে আমি রেসালা (ফতোয়ার বই) লিখেছি এবং আমি একজন মারজায়ে তাকলীদ,অসম্ভব যে আপনি তাকে মেনে নিবেন বরং তাকে প্রশ্ন করবেন,জনাব! আপনি কোথায় কোন মুজতাহীদের কাছে পড়াশুনা করেছেন? হয়তো তার বয়সও এখনো চল্লিশের বেশী নয়;অতীতে মুবাল্লিগদের ব্যাপারেও এধরনের সুক্ষ্ণ যাচাই বাছাই করা হতো। বয়স যে চল্লিশ হলো,দাবী করে বসলো যে আমি এখন মারজায়ে তাকলীদ। সে আর জানে না যে,না-পড়াশুনা করা অতীব জরুরী। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া দরকার কারো এ স্তরে পৌছতে হলে যে তাকে মুজতাহীদ,ফকীহ,মুফতী বলা যাবে এবং ইসলামের শারয়ী বিধি বিধান বের করতে সক্ষম হবে।
যেমন যদি বলা হয় মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দীর কথা। তাহলে আপনি মোটামুটি জানেন যে এ মানুষটি কয়েক বছর পরিশ্রম চালিয়েছেন,প্রায় ত্রিশ বছর বয়স অবধি তিনি ইস্ফাহানে ছিলেন। এ শহরে তিনি বড় বড় ওস্তাদবৃন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। ফেকাহ,উসূল,দর্শন,যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিকে রপ্ত করেছেন। যদিও তিনি নিজেই ছিলেন ইস্পাহানের একজন মুজতাহীদ এবং গবেষক পণ্ডিত। এরপর নাজাফে গমন করেন এবং সেখানে মরহুম আয়াতুল্লাহ অখন্দ খোরাসানীর ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন এবং বছরের পর বছর ধরে তিনি ছিলেন তার উত্তম শিষ্যদের অন্যতম। মরহুম আগা সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের কাযভীনি বলেন,আমরা মরহুম অখন্দ খোরাসানীর ক্লাসে অংশগ্রহণ করতাম। (অখন্দ খোরাসানী অধ্যাপনায় মুসলিম বিশ্বে অতুলনীয় একজন শিক্ষক ছিলেন। উসূল শাস্ত্রে তার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসাধারণ। পাশাপাশি অধ্যাপনা পেশায়ও তিনি ছিলেন নজিরবিহীন। তার ক্লাসে ছয় হাজার দুইশ ছাত্র অংশগ্রহণ করতো। যাদের মধ্যে অন্তত পাঁচশ ছিলেন মুজতাহীদ। কথিত আছে যে তিনি খুব তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং মাইক ছাড়াই তার কথা মসজিদের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়তো। কোনো ছাত্র যদি কিছু বলতে চাইতো তাহলে উঠে দাড়াতে হতো তাহলেই কেবল তার কথাকে ওস্তাদের কাছে পৌছাতে সক্ষম হতো।) এই ক্লাসে একবার মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দী (তখন তিনি যুবক ছিলেন) উঠে দাঁড়ালেন ওস্তাদের বক্তৃতায় একটি আপত্তি উপস্থাপন করার জন্যে । তিনিও সুভাষী ছিলেন। সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তার আপত্তি পেশ করলেন। মরহুম অখন্দ খোরাসানী বললেন,আরেক বার বলো। তিনি আরো একবার বললেন। অখন্দ অনুধাবন করলেন যে সে সঠিক বলছে। তার আপত্তি সঠিক। তিনি বললেন,আল-হামদুলিল্লাহ। আমি এখনো মরিনি তার আগেই আমার শিষ্যের নিকট থেকে শিখলাম। এরপর আরো কয়েকটি বছর নাজাফে কাটানোর পরে তবে আয়াতুল্লাহ বুরজার্দী ফিরে আসনে ইরানে। এসময়েও কি মারজায়ে তাকলীদ হননি। না-আরো ত্রিশ বছর একটানা গবেষণা চালিয়ে যান।
আমি (ওস্তাদ মুতাহহারী) নিজের একটি ঘটনা উল্লেখ করি। একবার শাবান মাসে আমি গিয়েছিলাম বুরুজার্দ শহরে। সেখানে আমি মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দীর খেদমতে উপস্থিত হই। তারিখটা ছিল 15 শাবান। তিনি রীতি মোতাবেক যে ক্লাস নিতেন সেটা আপাতত দূরে রেখে ঘোষণা দিলেন যে এই পনের দিন আমি ছোট একটি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার মনে পড়ে তিনি এই কথা বলে‘‘ খৃষ্টবাদ’’ সংক্রান্ত একটি আলোচনার অবতারণা করেন। তিনি বললেন,আমি এ বিষয়টি চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে যখন ইস্পাহানে ছিলাম তখন স্টাডি করেছিলাম। কিছু কিছু নোটও করা ছিল। কিন্তু তারপরে আর এ বিষয়ে স্টাডি করা হয়নি। এখন এই এতগুলো বছর পরে আরেক বার বিষয়টা নিয়ে অধ্যয়ন করতে চাই। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন,আমি আমার নোট গুলো খুলে দেখতে চাই না। বরং নতুন করে অধ্যয়ন করতে চাই। তারপর ঐ নোটগুলো খুলে দেখবো যে সে সময়ের সাথে কোনো পার্থক্য হয়েছে কিনা? এরপর দশ পনের দিন আলোচনা চালানোর পর তিনি সেই নোটগুলো নিয়ে এলেন। যখন সেগুলো পড়লেন,দেখলেন যে এখন যা কিছু তার মস্তিস্কে এসেছে,চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর আগেও ঠিক সেটাই এসেছিল। পার্থক্য শুধু এটুকু যে এখনকার মস্তিস্ক অনেক বেশী পরিপক্ক এবং বিকশিত আর তখনকার মস্তিস্ক ছিল নিয়ম ও সূত্রে বেশী আবদ্ধ । এখন ইসলামের মূল পাঠে আরো বেশী দক্ষ ও অভিজ্ঞ । তিনি বললেন যে কোনো পার্থক্য হয়নি। শুধু এখন আমার মস্তিস্ক আরো পক্কতা লাভ করেছে। এ হলো একজন মারজায়ে তাকলীদের মর্যাদা। এরূপই হওয়া দরকার। আমার (ওস্তাদ মুতাহহারী) ভয় হয়,আমাদের সমাজ এটা ভুলে না যায়। ফলে জনগণ সে সব লোককে গ্রহণ করে নেয় যারা যোগ্য নয়। তবে,এমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং অক্ষুণ্ণ থাকাই অত্যাবশ্যক।
যদি বলি যে,ইসলামের তাবলীগের মর্যাদা,জনসাধারণের কাছে ইসলামের বার্তা পৌছে দেয়া এবং ইসলামকে একটি ধর্মাদর্শ হিসাবে পরিচিত করানো মারজায়ে তাকলীদের মর্যাদার চেয়ে কম কিছু নয়,তাহলে অবাক হবেন না। বরং এটাও ঐ উচ্চতার একটি মর্যাদা। অবশ্য মারজায়ে তাকলীদের জন্য কি কি জিনিস দরকার হয় যেগুলো মুবাল্লিগের জন্য আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আমাদের সমাজ এই বিষয়ে এসেই সবকিছু ভুলে যায়। মুবাল্লিগ তৈরী হয় কোত্থেকে? কারো কণ্ঠ যদি শ্রুতিমধুর হয় এবং নিরেট কবিতা বা গযল বলতে পারে আস্তে আস্তে দাড়িয়ে যায় মেম্বারের পাশে। তারপর দেখবেন চাদরের মতো একটা কাপড় মাথায় চড়িয়ে বসে যায় মেম্বারের প্রথম সিড়িতে। এভাবে কিছুদিন চালিয়ে যায়। তারপর,জুদি,জাওহারী,জামেউল তাফসীল ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে কিছু কেসসা-কাহিনী বর্ণনা করে। অর্থাৎ তথাকথিত‘‘ সাদরুল ওয়ায়েজীন’’ থেকে বর্ণনা শুরু করে। যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন,এগুলো কোথায় পেয়েছেন? উত্তর দেবে,সাদরুল ওয়ায়েজীন বা লিসানুল ওয়ায়েজীন থেকে। একথা শুনলে আপনার মনে হবে হয়তো কোনো বই কিতাবের নাম। কিন্তু আসলে সাদরুল ওয়ায়েজীন বা লিসানুল ওয়ায়েজীন এর অর্থ হলো ওয়ায়েজকারীদের মুখে শোনা। কয়েকটা এর মুখ থেকে,কয়েকটা আরেকজনের মুখ থেকে শুনে শুনে শেখা। আদৌ সেগুলো সঠিক নাকি মিথ্যা সে খবর নেই। ক্রমে ক্রমে কিছু ভক্ত শ্রোতাও যোগাড় করে ফেলে। তখন মেম্বারের নীচের সিড়ি থেকেও উঠে আসে খানিকটা ওপরের দিকে তারপর একসময় মেম্বারের মূল আসনে বসে পড়ে। আর জনসাধারণ সবাইকে জমা করে ফেলে। তদ্রুপ,মজিলস আয়াজন কারীরাও অধিকাংশই কেবল একটি বিষয়ে নজর রাখে আর তাহলো বেশী বেশী লোক টেনে আনা। যেন কে কত বেশী লোক টানতে পারে তার প্রতিযোগিতা! এটা আর বিবেচনায় থাকে না যে এই লোক সমাগম করা হয় হিসাবী কথাবার্তার জন্য । কিন্তু এখানে লোকজন জমা হওয়ার পর কি কথা বলা হয়? এটা ইসলামের প্রতি খেয়ানত। একারণে ইসলামের প্রতি খেয়ানত যে একটি উষ্ণ কণ্ঠ থেকেই সব কথার শুরূ । এটা একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধিক আমাদের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সন্দেহ বিতর্কের যুগে এসে যখন ইসলামের শত্রুরা চারদিকে ফোঁস ফোঁস করছে,এমন কোনো দিন নেই যে পত্র পত্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু লেখা হয় না। কিম্বা রেডিও টেলিভিশনে কিছু না কিছু প্রচারিত হয় না। কেন আজ‘‘ মোহরানা’’ শব্দকে কেন্দ্র করে ঝগড়াটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে?! (ইরানের শাহরে আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এহেন পরিস্থিতিতে তোমাকে তোমার কথা স্পষ্ট জানতে হবে, যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করাতে হবে। যদি আগেকার যুগের মুবাল্লিগরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল তাহলে আমাদের যুগে এসে তা দশ গুণ,শতগুণে কঠিনতর হয়েছে।
একজন মুবাল্লিগের জন্য প্রথম শর্ত হলো খোদ ধর্মাদর্শকে চেনা,বার্তার স্বরূপকে জানা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার্তাকে সমাজে পৌছাতে চায় তার নিজেরই আগে উক্ত বার্তার সাথে পরিচিত হতে হবে। অনুধাবন করতে হবে যে এই ধর্মাদর্শের উদ্দেশ্য কি? এর ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ কি? এর পথ কোনটি এবং কোথায় গিয়ে পৌছায়? এই ধর্মাদর্শের নৈতিকতা,অর্থনীতি ও রাজনীতি কি? এর শিক্ষানীতি কি? এর তৌহীদ ও কিয়ামত কি? এর বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুন কি? এটা কি কখনো সম্ভব যে কেউ একটি বার্তাকে না বুঝে এবং অনুধাবন না করে তা জনগণের কাছে পৌছাতে পারে? এর উদাহরণ এমন হবে যে একজন মারজায়ে তাকলীদ হবে কিন্তু ফেকাহ পড়েনি। এটা কিভাবে হতে পারে যে একজন মারজায়ে তাকলীদ হবে এবং ফেকাহর ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করবে। কিন্তু আদৌ ফেকাহ পড়েনি?! অথবা এর দৃষ্টান্ত এমন যে একজন চিকিৎসক হবে কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রই পড়েনি। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে একজন মুবাল্লিগের জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত থাকতে হবে এবং একটি ধর্মাদর্শ হিসাবে ইসলামের প্রতি কত গভীর পরিচিতি থাকতে হবে।
ইসলাম নিজে একটি ধর্মাদর্শ,একটি দেহ,সুসমন্বিত একটি সমষ্টি । অর্থাৎ পৃথক পৃথক পরিচিতিও কাজে আসবে না। সবকিছু কে ঐ যে দেহে সন্নিবেশিত রয়েছে সেটাকে সামষ্টিকভাবে চিনতে হবে। ইসলামের বিষয়াদির ব্যাপারে আমাদেরা মূল্যায়ন সঠিক থাকতে হবে। একটি দেহের জন্যে পৃথকভাবে একটি অঙ্গের মূল্যায়ন মূল্যহীন। মানুষের দেহ একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। যদিও এগুলো সবগুলোই অপরিহার্য কিন্তু মূল্যমানের দিক থেকে এর সব অঙ্গই কি একসমান? যদি একটি অঙ্গকে আরেকটির জন্য উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কোন অঙ্গকে কার জন্যে উৎসর্গ করবো? প্রয়োজনে হৃৎপিণ্ডকে হাতের জন্যে নাকি হাতকে হৃৎপিণ্ডের জন্য উৎসর্গ করবো? বলা বাহুল্য যে হাতকে হৃৎপিণ্ডের জন্যে করতে হবে। কারণ,মানুষ হাত ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। ইসলামও এরূপ। অবশ্য এ বিষয়ে দীর্ঘ এক আলোচনা রয়েছে‘‘ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ’’ আর‘‘ নিছক গুরুত্বপূর্ণ’’ শিরোনামে।
বার্তা বহনকারীর জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রথমতঃ তাবলীগের উপকরণাদি ব্যবহার করার দক্ষতা এবং দ্বিতীয়তঃ সেগুলোকে চিহ্নিত করা। অর্থাৎ তাকে জানতে হবে যে কোন উপকরণকে কাজে লাগাবে কোনটিকে ব্যবহার করবে না। বরং সে নিজে প্রাকৃতিক উপকরণাদির দিক থেকে কোনটির অধিকারী থাকবে আর কোনটির থাকবে না।
আসলে খোতবা প্রদান একটি পেশাদারী কাজ। এ পেশার ওপর পণ্ডিতরা স্বতন্ত্র বই রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হলেন এরিষ্টটল। মুসলমানরা যখন এরিষ্টটলের রচনাবলী অনুবাদ করে তখন এ অংশটি যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত করে। পরবর্তিতে এ ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। ইবনে সীনা‘‘ খেতাবাহ’ তথা বক্তৃতানীতি শীর্ষক প্রায় পাঁচশ’ পৃষ্ঠার একটি বই রচনা করেন। সেখানে তিনি মুবাল্লিগের শর্তাবলী সম্পর্কে বলেনঃ নিশ্চয় খতীব তথা বক্তার প্রাকৃতিক কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। যেমন,বাগ্মীতা ও কথা বলার ক্ষমতা। এটা নিজেই একটি খোদাপ্রদত্ত বড় গুণ। তাবলীগের জন্য এই প্রাকৃতিক শৈল্পিক গুণটি অতীব প্রয়োজন। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) اَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ(
অর্থঃ করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।( সূরা রহমান , আয়াত নং 1 - 4 )
মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) এর কাহিণীতে রয়েছে যে দশবছর পর যখন মিশরে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে সস্ত্রীক রওনা হলেন,বৃষ্টিস্নাত এক অন্ধকার রাত। তার অন্তসত্তা স্ত্রী সন্তান প্রসবের বেদনায় কাতর অবস্থা। ঠাণ্ডা বাতাস। স্ত্রীকে গরম করতে হবে। কিন্তু গরম করার কোনো উপকরণ তার সাথে নেই। হঠাৎ,দূরের মরুতে আলো দেখতে পান (তুর বা সীনা পর্বতে)। তিনি ভাবলেন আগুন। এগিয়ে যান। বুঝা গেল যে আগুন নয়। ঘটনা অন্য কিছু । সেখানেই মুসা (আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আওয়াজ আসলো যে এখন থেকে তুমি আমার রাসূল। অর্থাৎ আল্লাহর মুবাল্লিগ। আমার বার্তাকে ফেরাউন ও তার অনুচরদের কাছে পৌছাতে হবে। মূসা জানেন যে একজন মুবাল্লিগের শর্ত ও যোগ্যতার প্রশ্ন রয়েছে নিজের নবুওয়াতকে যথেষ্ট মনে করেন না। তার কিছু আবেদন রয়েছেঃ
) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي(
অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমার বক্ষকে প্রসারিত করো।( সূরা তা হা , আয়াত নং 25 )
অর্থাৎ আমি যেন সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারি,তড়িঘড়ি ক্ষেপে না যাই। আমাকে সাগরের মতো উদারতা দান করো। কেননা,তাবলীগের কাজে সাগরের মতো বক্ষ দরকার হয়।
) وَ يَسِّرْ لِي اَمْرِي(
অর্থাৎ,আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও। (লক্ষ করুন যে তাবলীগের কাজকে আমরা কতটা হালকা গণ্য করি আর মূসা ইবনে ইমরান কতোটা ভারী মনে করেন)। এই বক্তব্যের সমর্থনকারী আরেকটি বক্তব্য পাওয়া যায় যা মহানবী (সাঃ) এর ব্যাপারে এসেছ। পবিত্র কোরআন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে বলেঃ
) انَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً(
অর্থাৎ অচিরেই আমরা আপনার ওপর ভারী বার্তা আরোপ করবো।( সূরা মুয্যাম্মিল , আয়াত নং 5 )
তাহলে,দেখা যাচ্ছে যে এটা এমন এক ভারী জিনিস যা নবীদের কাঁধেও ভারী হয়ে যেত। নবী রাসুল সকলের জন্যে তা ভারী। আর আমরা কি মূল্যায়ন করছি?!
হযরত মূসা (আঃ) তার আবেদন অব্যাহত রেখে বললেন,
) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي وَ يَفْقَهُوا قَوْلِي(
অর্থাৎ,আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।( তা হাঃ 27 ) যাতে আমি সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারি এবং যে সারসত্যকে তুমি আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করো এবং আমি তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলি,তারা সেটা যেন উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়। আমার ও জনগণের মাঝে এমন এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দাও যেন বিষয়বস্তুসমূহকে তুমি যেমনটা চাও ঠিক তদ্রুপভাবে আমার থেকে গ্রহণ করতে পারে। এমন না হয় যে আমি এক রকম বলবো আর তারা আরেক রকম মনে করবে। বয়ান তথা বর্ণনা করার পারঙ্গমতা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু ,প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপুষ্ট করতে হবে।
এতদসত্ত্বেও সৌভাগ্যে রকথা হলো যে শিয়া বিশ্বে ইমাম হোসাইন (আঃ) এর কল্যাণে বয়ান ও বক্তৃতা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ও অনেক শক্তিমান ও সম্মানীয় বক্তার আবির্ভাব ঘটেছে। এখনো অনেকে রয়েছেন।
হযরত মূসা (আঃ) আরো আবেদন করেনঃ
) وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي(
অর্থাৎ আর আমার পরিবারবর্গের মধ্যে থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন,আমার ভাই হারুণকে।( তা হাঃ 29 - 30 ) মূসার (আঃ) মনে হচ্ছে তিনি একা তার দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবেন না। এ কাজে তার একজন সহকর্মী দরকার। অথচ আমাদের এখনো এই অনুভূতি জন্মে না। এখনো আমরা একাই যথেষ্ট মনে করি। সহযোগী আবার কি? আমাকে একা একাই কাজ করতে হবে।
হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় ভাই হারূণকে তার তাবলীগ ও হেদায়েতের কাজে সহযোগী হিসাবে চেয়ে নিলেনঃ
) کيْ نُسَبِّحَكَ کَثِيراً وَ نَذْآُرَكَ کثِيراً(
যাতে আমরা বেশী করে তোমরা পবিত্রতা ও মহীমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশী পরিমাণে তোমাকে স্মরণ করতে পারি।( তা হাঃ 32 - 34 )
অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই শুধু তোমার তসবীহ কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দুনিয়ায় সত্যপূজারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া। পবিত্র কোরআন হুবহু এই কথাগুলোই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ব্যাপারেও উল্লেখ করেছে। তবে হযরত মূসার বেলায় সবই ছিল প্রার্থনার আদলে। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বেলায় এ সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে সম্পন্ন ও বাস্তবায়িত বিষয়ের আদলে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِآْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ اِلَي رَبِّكَ فَارْغَبْ(
অর্থঃ আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা,যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। কাজেই যখন অবসর পান (তখন একটি কঠিনতর কাজের জন্য ) পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।( ইনশিরাহ 2 - 8 )
‘‘ এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন’’ -এ আয়াতটিকে শিয়া তফসীরে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে,আমি এই বোঝাকে আলী (আঃ) এর মাধ্যমে আপনার জন্য হালকা করেছি,আলীকে আপনার জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করেছি। শিয়াদের অধিকারও আছে একথা বলার এবং ঠিকই বলে। অর্থাৎ যুক্তির নির্দেশ এটাই। এখানে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই বিখ্যাত হাদীস যা শিয়া-সুন্নী উভয় সূত্রে সমানভাবে গ্রহণীয়,তার তাৎপর্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ
اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
অর্থাৎ ( হে আলী)! আমার কাছে তোমার স্থান মূসার কাছে হারুণের স্থানের ন্যায়,শুধু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।( ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ , খণ্ডঃ 1 , পৃষ্ঠাঃ 56 , যাখায়িরুল উকবা , পৃষ্ঠাঃ 63 , সাওয়ায়িকুল মুহরিকা , পৃষ্ঠাঃ 119 , মুরুজুয যিহাব , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 425 , হিল্লিয়াতুল আবরার , খণ্ডঃ 1 , পৃষ্ঠাঃ 589 , মুসনাদ - ই ইমাম রেযা , খণ্ডঃ 1 , পৃষ্ঠাঃ 149 , মানাকিব - ই ইবনে মাগাযেলী , পৃষ্ঠাঃ 27 - 31 , শারহে নাহজুল বালাগা - ইবনে আবিল হাদীদ , খণ্ডঃ 3 , পৃষ্ঠাঃ 258 , ইহতিজাজ - তাবারসী , খণ্ডঃ 1 , পৃষ্ঠাঃ 118 )
উপরোক্ত শেষ আয়াতটির সাথে এই হাদীসটির সমন্বয় করে ফলাফল দাঁড়ায় এরূপ যে,
[فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ কাজেই যখন অবসর পান (তখন একটি কঠিনতর কাজের জন্য ) পরিশ্রম করুন] এখানে যদিانْصَبْ শব্দটির অর্থ نَصِبَ শব্দমূল থেকে গ্রহণ না করে বরংنَصَبَ শব্দমূল থেকে গ্রহণ করি তাহলে অর্থ হবে যখন আপনার অবসর হবে তখন আলী (আঃ) কে খেলাফত পদে নিয়োগ দান করুন। এটাও শতভাগ কোরআনের আয়াতসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথা।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী তাবলীগ এবং জনগণকে হেদায়েতের কাজ খুবই কঠিন এবং ভারী একটি কাজ। অথচ আমাদের সমাজে একাজকে এতই তুচ্ছ গণ্য করা হচ্ছে যে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে,যদি কেউ একটু বেশী জ্ঞান রাখেন এবং বেশী মর্যাদার অধিকারী হন,তাহলে তার মেম্বারে আরোহণ করতে শরম হয়। আর লোকেরা বলে বেড়ায়,উনি তো অনেক উচু মানুষ। মেম্বারে বসে তাবলীগ করা ওনার মানায় না। এ দোষ সমাজের।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে মুবাল্লিগ ছিলেন। ওয়ায়েজ ছিলেন। তিনি মেম্বারেও উঠতেন। প্রথমে তো মেম্বার ছিল না। একটি পিলার ছিল যার গায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলান দিয়ে দাড়াতেন এবং মানুষের জন্য নসিহত করতেন। তারপর তিনি নির্দেশ দেন একটি মেম্বার তৈরী করার জন্য । তখন থেকে মেম্বারে বসে খোতবা দিতেন।
নাহজুল বালাগায় হযরত আলী (আঃ) থেকে যেসব খোতবা বর্ণনা করা হয়েছে এর অধিকাংশই তার মেম্বারের খোতবা ছিল। যদিও নাহজুল বালাগায় হযরত আলী (আঃ) এর খোতবাসমূহের একটি অংশ মাত্রই উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই হযরত আলী (আঃ)ও মেম্বারে উঠতেন। এ সব কিছুই ইসলামে তাবলীগের মর্যাদাকে তুলে ধরে। কিন্তু আমাদের মাঝে সেই মর্যাদা হারিয়ে গেছে। ফলে,ইসলামের বার্তা এখন আর পৌছে না।
হযরত যায়নাবের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ পায় তার তাবলীগি ভূমিকায়। একবার লক্ষ্য করুন যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) এর পরিবারবর্গ কি নিপূণভাবে তাবলীগের কাজ করেছেন। এখানে দুই তিনটি বিষয় রয়েছে যেগুলো উপলদ্ধি না করা পর্যন্ত আহলে বাইতের তাবলীগের মূল্যায়ন করা যাবে না এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের এ তাবলীগি সফরের মূল্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। ইমাম হোসাইন (আঃ) এর কাজ ছিল পরিকল্পনা মাফিক। অর্থাৎ তিনি এই সফরটিকে শত্রুর হাত দিয়ে সংঘটিত করালেন। শত্রুই এই সফরটাকে অনুষ্ঠিত করে। শত্রু তার নিজের ভাবনায় বন্দীদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বটে,কিন্তু আসলে সে মুবাল্লিগ প্রেরণ করছে।
একটি কথা বলে রাখি। সব সময় মনুষ্য সমাজে যত বড়ই এবং যতই শক্তিধর স্বৈরাচার থাকুক না কেন,অবশেষে তার একটি চিন্তা ও দর্শনগত সমর্থনের দরকার হয়। অর্থাৎ একটি বিশ্বাসগত আদর্শ দরকার যার ওপর নির্ভর করে নিজের অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির সূত্র বের করতে পারে। মানুষের একটা না একটা চিন্তার তো দরকার। যদি কোনো সমাজ তার নিজের ওপরে ক্ষমতাসীন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে চিন্তা করে তাহলে ঐ শাসন টিকে থাকা অসম্ভব। আর একারণেই প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা দর্শনের সমর্থনের প্রতি নির্ভরতা রয়েছে যেখান থেকে সে তার চিন্তা ও বিশ্বাসগত খোরাক যোগান লাভ করবে। সে চায় তার শাসন ব্যবস্থা একটি দর্শন হিসাবে বলবৎ থাকুক। একটি ইজম বা মতবাদ হিসাবে টিকে থাকুক। ইয়াযিদী জান্তাও একটি চিন্তা ও বিশ্বাসগত সমর্থন ছাড়া কিম্বা অন্ততপক্ষে জনগণের বিদ্যমান বিশ্বাসগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারার মতো একটা অবলম্বন ছাড়া তাদের কাজকে এগিয়ে নিতে পারতো না।
এটা ভাববেন না যে তারা এতোটা আহম্মক ছিল যে বলবে,মস্তকগুলো সব বর্শার মাথায় তোলো,মানুষ কী ভাবে সেটা গোল্লায় যাক। না-বরং তারা সবসময় মানুষের চিন্তাকে ধোকা দিতে এবং এক জাতীয় চিন্তা ও ভাবনাকে তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। যাতে তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় যে বর্তমান অবস্থাটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। এরকমই হওয়া দরকার। অবশ্য এক দল ধর্মীয় লোকের মধ্যে ঐ চিন্তা,রঙ এবং ধর্মীয় চেহারা থাকতে হবে। কেন তারা একজন কাজী অর্থাৎ শারীহ’ র সাহায্য নিয়েছে? যাতে মানুষের চিন্তায় রং ধরিয়ে দিতে পারে এবং দিতেও পেরেছে। কারবালায় আশুরার বিকাল অবধি এই পরিকল্পনা সফল ছিল। ইমাম বাকের (আঃ) বলেন,ত্রিশ হাজার লোক কারবালায় সমবেত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সন্তানকে হত্যা করার জন্য ;
وَ کُلٌّ يَتَقَرَّبُونَ اِلَي اللهِ بِدَمِهِ
অর্থাৎ,তারা সকলেই এসেছিল ইমাম হোসাইন (আঃ) কে হত্যা করে বেহেশতে যাওয়ার আশায়।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 44 , পৃষ্ঠাঃ 298 ) অবশ্য নেতাবর্গের ক্ষেত্রে তো কবি ফারাযদাকের ভাষায় বলতে হয়,উৎকোচ দ্বারা তাদের তল্পি ভরে গিয়েছিল। কিন্তু আম জনতার তো এসব কথা তাদের মাথায় খেলতো না। তাই আম জনতার চিন্তাকে প্রতারিত করতো। আর এই কূটনীতি বিশেষ করে ইবনে যিয়াদের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইয়াযিদ মদ পানের কারণে তার লাগাম ছিড়ে যেত এবং তার ভেতরের কথা প্রকাশ করে ফেলেতা। কথায় বলে‘‘ মাতলামি তো সত্যবাদী’’ অর্থাৎ,মাতাল অবস্থায় সে তার সত্য কথা বলে দিত যে আমি কোনো কিছুই মানি না। এভাবে মাতলামির মধ্যে সে নিজের ভরাডুবি নিজেই ডেকে আনতো। নয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় সেও এই কূটনীতি খাটাতো।
ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইন (আঃ) এর শাহাদাতের পরে ঘটনার বিকৃতি প্রদানের জন্য যখন জনগণকে কুফার বড় মসজিদে সমবেত করে তখন এমন ধর্মীয় ও দীনদারের বেশ সে ধারণ করে যে বলেঃ
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَظْهَرَ الْحَقَّ وَ اَهْلَهُ، وَ نَصَرَ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اَشْيَاعَهُ، وَ قَتَلَ الْكَذَّابَ بْنَ الْكَذَّابِ
অর্থাৎ,আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই যে তিনি সত্য ও তার অনুসারীদেরকে প্রকাশ করে দিয়েছেন আর এক মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীর পুত্রকে নির্মূল করেছেন।( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ 45 , পৃষ্ঠাঃ 119 , মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 52 , মাকতালু মুকাররাম , পৃষ্ঠাঃ 426 , ইরশাদ - মুফিদ , পৃষ্ঠাঃ 244 , কামেল ফিত তারিখ , খণ্ডঃ 4 , পৃষ্ঠাঃ 82 , আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 69 , কাশফুল গুম্মাহ , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 67 )
এরপর সে‘ এলাহী শোকর’ বলার জন্য জনগণকে আহবান করে এবং হয়তো শত শত লোক‘ এলাহী শোকর’ বলে চিৎকারও করেছিল। যদি একজন অন্ধ তবে আলোকিত অন্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত না থাকতো তাহলে পুরো জনতাকেই সেদিন ধোঁকা দিয়েই ফেলেছিল।
এক ব্যক্তি ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আফীফ নাম্মী। আল্লাহর রহমত তার উপরে বর্ষিত হোক। কখনো কখনো মানুষ এমন মুহুর্তে জীবনবাজি রাখে যার এক দুনিয়া মূল্য হয়। এই মানুষটির দুচোখ অন্ধ ছিল। তার এক চোখ জামাল যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আঃ) এর পক্ষে যুদ্ধ করার সময় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আরেকটি চোখ সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আঃ) এর পক্ষে যুদ্ধ করার সময় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্ধ ছিল বলে তার দ্বারা আর কোনো কাজও সম্ভব হতো না। ফলে,আর কোনো জিহাদেও অংশগ্রহণ করতো না। অধিকাংশ সময়ই ইবাদত করে কাটাতো। সেদিনেও সে কুফার মসজিদে ছিল। সে যখন ইবনে যিয়াদের এই কথা শুনলো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং বললো,মিথ্যাবাদী হলে তুমি আর তোমার বাবা। এভাবে সে এমন এক বক্তৃতা প্রদান করা শুরু করলো যে সেখানেই অন্যরা তার ওপরে ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাকে আটক করলো। পরে তাকে হত্যাও করেছিল। তবে,সে এই পর্দাকে ছিড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।
ইবনে যিয়াদ আসলেই ঐ দুই অর্থেই জারজ ছিল। এক হলো জারজ সন্তান আরেকটি হলো শয়তান অর্থে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসব সমাজে জনগণ ধর্মমনা হয় সেখানে যখন স্বৈরাচারীরা নিজেদেরকে ব্যাখ্যা করতে চায় তখন‘ জাবরিয়া’ মতবাদ পন্থী হয়ে যায়। তখন সব কিছুকেই আল্লাহর কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আল্লাহর হাতেই এরূপ ঘটেছে। যদি এর মধ্যে মঙ্গল না থাকতো তাহলে তো এরূপ হতো না। আল্লাহ নিজেই এরূপ ঘটতে দিতেন না। মোটকথা,যা কিছু হবার সেটাই ঘটে আর যা কিছু হবার না তা ঘটে না। এ হলো একটা সূত্র ,জাবরিয়া মতবাদের কথা। ইবনে যিয়াদও এই সূত্র কাজে লাগায়। একারণে যখন হযরত যয়নাবের মুখোমুখি হয় অমনি আল্লাহর বিষয়টি মাঝখানে টেনে আনে এবং বলে :
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَحَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ وَ اَآْذَبَ اُحْدُوثَتَكُمْ
এসব কথার অনেক মানে রয়েছে। সে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ,আল্লাহই তোমাদেরকে হত্যা করেছে। এসব আল্লাহরই ইচ্ছা। তোমরা আজব এক ফেতনা সৃষ্টি করেছিলে মুসলমানদের জন্য । তাই আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি তোমাদেরকে হত্যা করেছে এবং তোমাদেরকে অপদস্থ করেছে। এখানে তার চিন্তায় অপদস্থ ও পর্যদস্ত কাকে বলে? তার প্রচারে যে ব্যক্তি বাহ্য রণাঙ্গণে পরাজিত হলো,বুঝি পর্যদস্ত হয়ে গেল এবং সব কিছু শেষ হয়ে গেল। কেননা,সে যদি সত্যের উপরে থাকতো তাহলে তো যুদ্ধে বিজয়ী হতো।
وَ اَکذَبَ اُحْدُوثَتَكُمْ
অর্থাৎ তোমাদের পরাজয়ই প্রমাণ করে যে তোমাদের কথা মিথ্যা।
কিন্তু হযরত যয়নাব কি বললেন?
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَکْرَمَنَا بِه نَبِيَّهُ
অর্থাৎ,আল্লাহকে প্রশংসা জানাই যে তিনি স্বীয় নবীকে দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তো নবীর পরিবার।
انَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَ يَكْذَبُ الْفَاجِرُ وَ هُوَ غَيْرُنَا وَ الْحَمْدُ لله
যারা যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হয় তারা লাঞ্ছিত হয় না। লাঞ্ছনার মাপকাঠি অন্য কিছু । সত্যকামিতা আর সত্যানুসরণই হলো সেই মাপকাঠি । যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় সে লাঞ্ছিত হয়নি। বরং সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত যে অন্যায় আর অত্যাচার করে এবং সত্য থেকে বঞ্চিত হয়। এমন কোনো কথা নেই যে,কেউ যদি নিহত হয় তাহলে তার কথা মিথ্যা ছিল। এখানে সত্য এবং মিথ্যাই হলো মাপকাঠি ,স্বয়ং মানুষ ও তার আদর্শ ও আমলই হলো মাপকাঠি । ইমাম হোসাইন (আঃ) নিহত হলেও সত্য বলেছেন,আর বেঁচে থাকলেও সত্য বলেছেন। পক্ষান্তরে,তুমি বেঁচে থাকলেও মিথ্যাবাদী আর নিহত হলেও মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি এমন কঠিন আক্রমণ করলেন যে ইবনে যিয়াদের কলিজা উগরে আসার উপক্রম হলো। বললেনঃ
يَابْنَ مَرْجَانَه!
হে মারজানা’ র পুত্র! মারজানা ছিল ইবনে যিয়াদের মায়ের নাম। সে পছন্দ করতো না যে কেউ তার মায়ের নাম উচ্চারণ করুক। কেননা,তার মা ছিল অসতী। হযরত যয়নাব বললেন,হে ঐ অসতী নারীর পুত্র ,লাঞ্ছনা তো মারজানা’ র পুত্রেরই।
এখানে এসেই ইবনে যিয়াদ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো এবং ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে নির্দেশ দিল,জল্লাদ কোথায়? এই মহিলার গর্দান দাও। ঘটনাক্রমে ঐ সভার এক কোণে উপস্থিত ছিল জনৈক ব্যক্তি যে ছিল খারিজী দল এবং আমিরুল মুমীনীন (আঃ) এর শত্রু। অপরদিকে তেমনি ইবনে যিয়াদ চক্রের সাথেও তার বনাবনি ছিল না। একারণে,ইবনে যিয়াদ যখন নির্দেশ দিল জল্লাদ মীর গযবকে উপস্থিত হতে,তখন খারিজী লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং বলতে গেলে তার আরববাদী অনুভূতিকে কাজে লাগালো। সে দাড়িয়ে বললো,হে আমীর! একবারও ভেবে দেখেছেন যে একজন নারীর সাথে কথা বলছেন,যে নারী একাধিক শোকে শোকাহত। যার ভাইয়েরা নিহত হয়েছে, প্রিয়জনদেরকে হারিয়েছে।
وَ عَرَضَ عَلَيْهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ
অর্থাৎ,তার সামনে আলী ইবনুল হোসাইন কে উপস্থাপন করা হলো। সাথে সাথে ফেরাউনের ন্যায়া হুঙ্কার ছেড়ে বললো : ؟ مَنْ اَنْتَ অর্থাৎ,কে তুমি? (এখানেও তার স্বৈরাচারী প্রবৃত্তি লক্ষণীয়) ইমাম উত্তর দিলেনঃ
اَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
অর্থাৎ,আমি হোসাইনের পুত্র আলী।
ইবনে যিয়াদ বললোঃ
اَلَيْسَ قَدْ قَتَلَ اللهُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ
অর্থাৎ,কেন, আল্লাহ কি আলী ইবনে হোসাইনকে হত্যা করেননি? (লক্ষণীয় যে এখন সব কাজ আল্লাহর বলে চালিয়ে দিতে হবে যাতে বুঝা যায় যে ওরা সবাই হচ্ছে হকের ওপর রয়েছে) ইমাম বললেন,আমার একটি ভাই ছিল আলী নামের। লোকেরা কারবালায় তাকে হত্যা করেছে। ইবনে যিয়াদ বললো,না। আল্লাহই তাকে হত্যা করেছেন। ইমাম বললেন,অবশ্য সকল মানুষের রূহ কবজ করেন আল্লাহ। কিন্তু তাকে হত্যা করেছে লোকজনে। তারপর সে বললো,শুধু‘‘ আলী’’ আর‘‘ আলী’’ । আর কোনো নাম কি ছিল না যে তোমার বাবা তার সব ছেলেদের নাম রেখেছে আলী,তোমারও নাম রেখেছে আলী? ইমাম বললেন,আমার বাবা তার পিতাকে অত্যাধিক ভালবাসতেন। একারণে তিনি তার সন্তানদেরকে পিতার নামেই নাম রাখতে পছন্দ করতেন। (অর্থাৎ,হে ইবনে যিয়াদ,তোমার পিতাকে নিয়ে গর্বের তো কিছু নেই। বরং কেবলই অপমান )
ইবনে যিয়াদের আশা ছিল আলী ইবনুল হোসাইন যেন কোনো কথাই না বলেন। তার দৃষ্টিকোণ থেকে একজন বন্দীর কথা বলার অধিকার নেই। যখন তাকে বলা হবে যে এটা আল্লাহরই কাজ তখন সে শুধু বলে যাবে জি,হ্যাঁ । আল্লাহরই কাজ। এটাই তকদীর ছিল। এর ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। আসলে ভুল হয়ে গেছে---ইত্যাদি। কিন্তু যখন দেখলো যে আলী ইবনুল হোসাইন একজন বন্দী হয়ে এ ধরনের কথা বলছেন তখন বলে উঠলোঃ
وَ لَكَ جُرْأَةٌ لِجَوَابِي
অর্থাৎ,এখনো তোমার সাহস হচ্ছে আমার উত্তর করার। কোথায় আছে জল্লাদ। এসো-এর গর্দান দাও।( আল কামিল ফিত তারীখ , খণ্ডঃ 4 , পৃষ্ঠাঃ 81 ও 82 , আল লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ 67 - 68 , এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ 247 , মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 42 , কাশফুল গুম্মাহ , খণ্ডঃ 2 , পৃষ্ঠাঃ 66 )
ইতিহাসে লেখা রয়েছে যে,ইবনে যিয়াদ যেই গর্দান দেবার জন্য জল্লাদকে হুকুম দিল,সাথে সাথে হযরত যয়নাব উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী ইবনুল হুসাইনকে দু’ বাহ মাঝে আঁকড়ে ধরে বললেন,আল্লাহর শপথ! তোমরা এর গর্দান দিতে পারবে না যতক্ষণ না আগে যয়নাবের গর্দান দিবে। বর্ণিত রয়েছে যে ইবনে যিয়াদ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো এই দু’ জনের দিকে। তারপর বললো,আল্লাহর কসম! দেখতে পাচ্ছি যদি এখন এই যুবককে হত্যা করতে চাই তাহলে প্রথমে এই মহিলাকে হত্যা করতে হয়। অগত্যা প্রথ থেমে গেল।
এটা ছিল আহলে বাইত-এর একটি বৈশিষ্ট্য । তারা‘ জাবরিয়া’ মতবাদের বিরুদ্ধে ও লড়াই করেছেন। যারা বলে যে দুনিয়ায় জাবর তথা বাধ্যবাধকতাই রয়েছে এবং এটাই ন্যায়নিষ্ঠ । অর্থাৎ মানুষের এই জগতে পরিবর্তন ও রদবদলের জন্য কোনো কর্তব্য নেই। যা কিছু রয়েছে সেটাই থাকার আর যা কিছু নেই সেটা না থাকার। অতএব,মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। তারা এরূপ বাধ্যবাধকতা বাদের প্রচলন রুখে দাঁড়ান। (সমাপ্ত )
সূচীপত্র
ভূমিকা. 4
হোসাইনী আন্দোলনে অন্যতম উপাদান “তাবলীগ” 7
বার্তা পৌঁছানোর উপকরণাদি ও মাধ্যমসমূহ 25
তাবলীগ (বা প্রচার) পদ্ধতি প্রসঙ্গে. 46
হোসাইনী আন্দোলনের প্রচার পদ্ধতিসমূহ 71
হোসাইনী আন্দোলনের প্রচারে আহলে বাইতের নারীদের ভূমিকা. 95
মুবাল্লিগের শর্তাবলী এবং ইমাম (আঃ) এর আহলে বাইতের বন্দীকালীন তাবলীগের প্রভাব 120