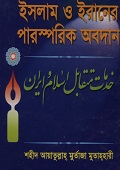ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান
শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী
অনুবাদ: এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর
ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান
মূল : শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী
অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর
সম্পাদনা : অধ্যাপক সিরাজুল হক
প্রকাশকাল :
নভেম্বর ,2003
রমজান ,1424
কার্তিক ,1410
প্রকাশনায় :
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ী নং 54 ,সড়ক নং 8/এ ,
ধানমন্ডি আ/এ ,ঢাকা-1205
বাংলাদেশ।
Islam O Iraner Parashparik Abodan,Translated by: A.K.M. Anwarul Kabir,Edited by: Prof. Shirazul Haque. Published by: Cultural Center of the Islamic Republic of Iran,Dhaka,Bangladesh. Published on: November,2003,Ramadan,1424,Kartik,1410.
শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী
অধ্যাপক শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী 1338 হিজরীর 12 জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক 1920 খ্রিষ্টাব্দের 20 ফেব্রুয়ারী ইরানের ধর্মীয় নগরী মাশহাদের 75 কিলোমিটার দূরে ‘ ফারীমান ’ নামক গ্রামে (বর্তমানে থানা) এক ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে স্থানীয় মক্তবে লেখাপড়ার পর 12 বছর বয়সে মাশহাদের দীনী শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেন।
মুতাহ্হারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইরানের ধর্মীয় নগরী কোমে গমন করেন। কোমে শহীদ মুতাহ্হারীর শিক্ষাজীবন দীর্ঘ 15 বছর স্থায়ী ছিল। এ সময়ের মধ্যে তিনি মরহুম আয়াতুল্লাহ্-উল-উজমা বুরুজেরদীর নিকট ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহ্ ,হযরত ইমাম খোমেইনীর নিকট দীর্ঘ 12 বছর মোল্লা সাদরার দর্শন ,আধ্যাত্মিকতা ,ন্যায়শাস্ত্র এবং মরহুম আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈর নিকট দর্শনশাস্ত্র ,ইবনে সীনার আশ-শিফা ,ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন।
1952 সালের দিকে তিনি কোমের দীনী মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিসেবে গণ্য হলেন। এরপর তিনি তেহরানে চলে আসেন এবং ‘ মারভী ’ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ,লেখালেখি ও বক্তৃতা প্রদানে আত্মনিয়োগ করেন। 1955 সালে শহীদ মুতাহ্হারীর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ইসলামী ছাত্র সমিতির প্রথম তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে অধ্যাপনা শুরু করেন।
1962 সাল থেকেই ইমাম খোমেইনীর উদ্যোগে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। তখন শহীদ মুতাহ্হারী অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ইমামের পাশে ছিলেন। তেহরানে 15 খোরদাদের গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করা এবং ইমামের সাথে এ আন্দোলনের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের অবদানই অগ্রগণ্য ছিল। 1963 সালের 15 খোরদাদ শাহের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানের পর রাত 1টায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তবে 43 দিন পর মফস্বল শহরের আলেমরা তেহরানে এসে পৌঁছার কারণে এবং জনমতের প্রবল চাপে অন্যান্য আলেমের সাথে শাহের জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।
শহীদ মুতাহ্হারী একটি ব্যাপক ইসলামী উত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি 1967 সালে কয়েকজন বন্ধুসহ ‘ হোসাইনিয়া এরশাদ ’ প্রতিষ্ঠা করেন।
1969 সালে জনগণের প্রতি আল্লামা তাবাতাবাঈ ও আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ আবুল ফজল মুজতাহিদ জানজানীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থসংগ্রহ ও হোসাইনিয়া এরশাদে বক্তৃতা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি 1970 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত ‘ মসজিদ আল-জাভাদ ’ -এর তাবলিগী কার্যক্রম দেখাশুনা করেন। তখন তিনিই এ মসজিদের প্রধান বক্তার ভূমিকা পালন করেন। পরে শাহী সরকারের পক্ষ থেকে ঐ মসজিদটি ও পরবর্তীতে ‘ হোসাইনিয়া এরশাদ ’ সীল করে দেয়া হয়। মুতাহ্হারী পুনরায় গ্রেফতার হন।
1974 সালের দিকে মসজিদে বক্তৃতা করার ব্যাপারে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এ নিষেধাজ্ঞা 1979 ইসলামী বিপ্লব বিজয় লাভ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। শহীদ মুতাহ্হারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত ছিল শিক্ষকতা ,বক্তৃতা ও লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে উপস্থাপন। 1972 থেকে 1979 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপের অভ্যুদয় ,বিশেষত বামপন্থী মুসলিম গ্রুপগুলোর আত্মপ্রকাশের সময়ে শহীদ মুতাহ্হারী শক্ত হাতে কলম ধরেন এবং সব রকমের বিভ্রান্তি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। এ সময়ে তিনি আরো কয়েকজন ধর্মীয় নেতার সাথে মিলে ‘ জামেয়ে রুহানিয়াতে মোবারেযে তেহরান ’ নামে সংগ্রামী আলেমদের একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তেহরানের অনুকরণে অন্যান্য শহরেও আলেমরা ঐক্যবদ্ধ হবেন। ইমাম খোমেইনী ইরান থেকে নির্বাসিত হওয়ার পরও ওস্তাদ মুতাহ্হারী পত্রযোগাযোগ ও অন্যান্য মাধ্যমে ইমামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।
ইমাম খোমেইনী প্যারিসে অবস্থানকালে ওস্তাদ মুতাহ্হারী একবার প্যারিস সফর করেন এবং ইমামের সাথে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এ সফরে ইমাম খোমেইনী তাঁকে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেন। ইমাম খোমেইনীর ইরান প্রত্যাবর্তনের সময়ে ইমামের অভ্যর্থনা কমিটির প্রধানের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। তখন থেকে বিপ্লব চূড়ান্ত বিজয় লাভের ও তারপরও সব সময় ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতার বিশ্বস্ত ও একান্ত সহচর ও উপদেষ্টারূপে দায়িত্ব পালন করেন।
ইরানে ইসলামী বিল্পবের অব্যবহিত পরে অধ্যাপক ড. মুর্তাজা মুতাহ্হারী বিপ্লবী পরিষদের বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে 1979 সালের 2 মে মঙ্গলবার ‘ ফোরকান ’ নামের একটি কুখ্যাত সংগঠনের আততায়ীদের গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এভাবেই এ ক্ষণজন্মা প্রতিভা চিরবিদায় গ্রহণ করেন। কৃতি ছাত্রের শাহাদাতে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) বলেছিলেন: ‘ আমি আমার একজন প্রিয় সন্তানকে হারিয়েছে ,আমি তার জন্য শোক প্রকাশ করছি ;সে ছিল আমার সারা জীবনের ফসল। আমি আমার প্রিয় সন্তানকে হারালেও আমি গর্বিত যে ,ইসলাম এ ধরনের উৎসর্গকারী সন্তান জন্ম দিয়েছে। দুশমনদের জানা উচিত ,ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যক্তিদের দেহ অবসানের সাথে সাথেই মৃত্যু হয় না।
লেখকের কথা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আমরা ইরানের আটানব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। একদিকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি যেমন আমাদের গভীর ঈমান রয়েছে তেমনি নিজেদের দেশ হিসেবে ইরানের প্রতি রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসা। তাই আমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য আমরা দায়িত্ববোধ করি। এ দু ’ টি বিষয় ও এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে তিনটি প্রশ্নে উত্থাপন করা যায় :
1. আমাদের মধ্যে যেমন ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা রয়েছে তেমনি রয়েছে জাতীয় অনুভূতি ও চেতনা। আমরা কি এ দু ’ ধরনের অনুভূতি ও চেতনাকে বিপরীতমুখী মনে করব নাকি বলব আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির সঙ্গে জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির কোন বৈপরীত্য ও সংঘাত নেই ?
2. চৌদ্দশ ’ বছর পূর্বে যখন ইসলাম আমাদের এ দেশে আসে তখন তা কিরূপ পরিবর্তন সাধন করে ? এ পরিবর্তনের ধারা কোন্ দিকে ছিল ? ইসলাম ইরান হতে কি গ্রহণ করেছে ও ইরানকে কি দিয়েছে ? ইরানে ইসলামের আগমন অনুগ্রহ ছিল নাকি বিপর্যয় ?
3. বিশ্বের অনেক জাতিই ইসলামকে গ্রহণ করেছিল ও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তারা ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিল এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ‘ ইসলামী সভ্যতা ’ নামে এক বৃহৎ ও আড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এ সভ্যতার সৃষ্টিতে ইরানীদের অবদান কতটুকু ? এ ক্ষেত্রে ইরানীদের অবস্থান কোন্ পর্যায়ে ? তারা কি এ ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল ? ইসলামের প্রতি তাদের এ অবদান ও ভূমিকার পেছনে কোন্ উদ্দীপনা কাজ করেছিল ?
আমার মতে ইরান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রশ্ন তিনটিই প্রধান।
এ গ্রন্থটি তিনটি বিষয় ও আলোচনাকে ধারণ করেছে :
ক. ইসলাম ও জাতীয়তা।
খ. ইরানে ইসলামের অবদান।
গ. ইসলামে ইরানের অবদান।
এ তিনটি আলোচনা পূর্বোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দান করবে।
এ গ্রন্থে উপস্থাপিত আলোচনাটি তিন বছর পূর্বে আমার দেয়া বক্তব্যের পরিবর্ধন এবং পূর্ণাঙ্গরূপ।
আলোচনার প্রথমাংশ 1388 হিজরীর মুহররম মাসে দেয়া আমার বক্তব্যের পরিবর্ধিত পূর্ণরূপ।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলোচনাটিও একই বছর সফর মাসে আমার উপস্থাপিত ‘ ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান ’ শীর্ষক আলোচনার পূর্ণরূপ।
আমার তেহরান অবস্থানকালীন দীর্ঘ সময়ে যত বক্তব্য দিয়েছি তার কোনটিই এ বিষয়ক আলোচনার ন্যায় এত অধিক আলোড়ন ও সাড়া জাগায়নি। বিশেষত সফর মাসে আমি ‘ ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান ’ শিরোনামে যে ছয়টি বক্তব্য রাখি তেহরান ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীরা সেটিকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানায় ও প্রচুর সংখ্যক ক্যাসেট কপি হিসেবে নিয়ে যায়। বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিষয়টিতে অধিকতর আগ্রহ ব্যক্ত করে। তাদের এ আগ্রহ আমার ঐ বক্তব্যের বিশিষ্টতার কারণে নয় ;বরং ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের আলোচনার বিশিষ্টতার কারণেই ছিল।
যদিও এ বিষয়টি যথার্থ ও স্পষ্ট পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের বিশেষত যুবকদের জন্য উপস্থাপন অপরিহার্য তদুপরি আমার জানা মতে দুঃখজনকভাবে এখন পর্যন্ত এরূপ কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাই আলোচ্য গ্রন্থ এ সম্পর্কিত আলোচনার প্রথম গ্রন্থ। এ বিষয়ে গবেষণার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। যদি ইসলাম ও ইরানের অভিন্ন বিষয়সমূহে পর্যাপ্ত গবেষণা করা হয় তবে তা কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ হবে। আমি আশা করি অত্র গ্রন্থটি উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে গবেষণায় অধিকতর উৎসাহিত করবে ও তাঁদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।
সাধারণত ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি কলম চালিয়েছেন হয় তাঁরা এ বিষয়ে তেমন জানতেন না ,নতুবা গবেষণার স্বার্থে নয় ;বরং নিজস্ব বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা তা করেছেন। ফলে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। আমরা ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে যতই অধ্যয়ন করেছি এ বিষয়টি আমাদের নিকট ততই স্পষ্ট হয়েছে যে ,আলোচনাটি ইরান ও ইসলাম উভয়ের জন্যই গর্বের বিষয়। একদিকে ইসলাম এর সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর দ্বারা সংস্কৃতিবান ,বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও সভ্যতার অধিকারী এক জাতিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার গর্বে গৌরবান্বিত হয়েছে ;অপরদিকে সত্যাকাঙ্ক্ষী ,কুসংস্কারমুক্ত ও সংস্কৃতিপ্রেমী এ জাতি অন্যদের থেকে ইসলামের প্রতি অধিকতর অবনত ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিবেদিত ভূমিকা রাখার গৌরব লাভ করেছে।
ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে অন্য যে বিষয়টি আমাকে হতবাক করেছে তা হলো এ সম্পর্কে বাস্তবের বিপরীত বিকৃত উপস্থাপনার পরিমাণ ধারণাতীত।
ইসলামী দেশ ইরানে বিভিন্ন সময় বেশ কিছু ধারার সৃষ্টি হয়েছিল যাকে কোন কোন প্রাচ্যবিদ ও তাঁদের অনুসারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ইরানী মানসিকতার প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহ বলে অভিহিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন শুয়ূবী বা আরববিরোধী আন্দোলন ,ফার্সী ভাষার জাগরণ ,তাসাউফ ও শিয়া প্রবণতা। আবার কোন কোন ব্যক্তিত্ব ইসলাম বিরোধিতার প্রতীক বলে আখ্যায়িত হয়েছেন ,যেমন বিপ্লবী কাব্য রচয়িতা কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী এবং ‘ শেখ ইশরাক ’ নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ দার্শনিক শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী।
অত্র গ্রন্থের আলোচনাসমূহ এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ব্যক্তিগতভাবে ফেরদৌসী ও শেখ ইশরাকের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাকর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম ,কিন্তু এ গ্রন্থে তা সম্ভব হয়নি। কারণ এজন্য পর্যাপ্ত সময় ও বিশেষ পরিকল্পনা প্রয়োজন। ফার্সী ভাষার জাগরণ ও শিয়া প্রবণতা নিয়ে এ গ্রন্থের প্রথমাংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বিষয়সমূহ ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিষয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনা এখানে লক্ষ্য করবেন।
এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর কোন নিরপেক্ষ গবেষক এ বিষয়ে অভিমত ও পরামর্শ দিলে ইনশাল্লাহ্ আমি তা সাদরে গ্রহণ করব।
মুর্তাজা মুতাহ্হারী
ফার্সী 1349 সাল
(খ্রিষ্টীয় 1970 সাল)
প্রথম ভাগ
ইরানী জাতির দৃষ্টিতে ইসলাম
আমরা এবং ইসলাম
ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা ইরানীরা কয়েক সহস্রাব্দ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ আবার কখনও শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছি। এ সম্পর্কের কারণে তাদের অনেক চিন্তা ও বিশ্বাস যেমন আমাদের মধ্যে এসেছে তেমনি আমাদের অনেক চিন্তা ও বিশ্বাসও তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে। যখনই অন্য জাতি ও গোষ্ঠীর জাতিসত্তা ও প্রভুত্বের কথা এসেছে আমরা তাদের মাঝে বিলুপ্ত হইনি ;বরং অন্য জাতিসত্তাকে প্রতিরোধ করেছি। তবে আমরা নিজ জাতিসত্তাকে ভালবাসার কারণে এটি করলেও এর মধ্যে কোন গোঁড়ামি বা অন্ধ বিশ্বাস ছিল না। কারণ মনের কোন অন্ধত্বই আমাদের সত্য হতে দূরে রাখতে এবং সত্যের বিরোধী ও শত্রু করতে পারেনি।
হাখামানেশী রাজত্বের সময় যখন ইরান বর্তমান সীমার বাইরেও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশসহ একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন হতে বর্তমানে দু ’ হাজার পাঁচশ ’ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পঁচিশ শতাব্দীর মধ্যে চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আমরা ইসলামের ছায়ায় বাস করছি এবং এ ধর্ম আমাদের জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এ দীনের রীতি ও শিক্ষাতেই আমরা আমাদের শিশুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছি ,আমাদের জীবন পরিচালিত করেছি ,এক আল্লাহর ইবাদাত করেছি ,এ দীনের রীতিতেই আমাদের মৃতদের কবরস্থ করেছি। আমাদের ইতিহাস ,রাজনীতি ,বিচার ব্যবস্থা ,আইন ,সংস্কৃতি ,সভ্যতা ,সামাজিক আচার-এক কথায় সকল কিছু ইসলামের সঙ্গে মিশে গেছে। সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করেছেন ,ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শতাব্দীকাল ধরে আমরা অসাধারণ ও মহা মূল্যবান অবদান রেখেছি যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না ,এমনকি অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে দীনের প্রচার-প্রসার এবং উন্নয়নে আরবদের চেয়েও অধিক অবদান রেখেছি। কোন জাতিই আমাদের মত এ দীনের প্রচার-প্রসার ও বিস্তৃতিতে ভূমিকা রাখতে পারেনি।
এ জন্যই ইসলাম ও ইরানের সম্পর্ককে বিভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনার অধিকার আমরা রাখি। ইসলামী জ্ঞানের প্রসারে আমাদের ভূমিকা এবং আমাদের আত্মিক ও বস্তুগত উন্নয়নে ইসলামের অবদান পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থরূপে ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহ স্পষ্ট করে তুলে ধরতেই আমাদের এ আলোচনা।
বর্তমান সময়ে জাতি আরাধনা
বর্তমান শতাব্দীর বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো জাতীয়তা। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক জাতিগোষ্ঠীই ,এমনকি মুসলমানদের মধ্যে ইরানী ও অ-ইরানী সকলেই এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের অনেকে এ আলোচনায় এতটা ডুবে গিয়েছেন ,যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।
বাস্তবতা হলো বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বিরাট সমস্যা। জাতীয়তাবাদের ধারণা ইসলামী মৌল প্রশিক্ষণের নীতির বিরোধী ও এ চিন্তাধারা মুসলিম ঐক্যের পথে বড় প্রতিবন্ধক।
আমরা জানি ইসলামী সমাজ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত এবং অতীতে ইসলাম বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামী সমাজের ছায়ায় একত্রিত করেছে। এ একতা এখনও বাস্তবে বিদ্যমান। এটি বাস্তব সত্য ,এখনও সত্তর কোটি1 মানুষের বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠী এক চিন্তা ,মূল্যবোধ ,অনুভূতি এবং সহাবস্থানের ধারণায় বিশ্বাসী। তাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা তাদের নিজস্ব নয় ;বরং তা সরকারসমূহ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে এবং সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে যার কারণ আমেরিকা ও ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ। তদুপরি এ সকল কারণ মানুষের অন্তরের এ ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারেনি। ইকবাল লাহোরীর ভাষায় :
“ সত্যের প্রমাণ মোদের নিকট রয়েছে একটিই ,
তাঁবুগুলো বিচ্ছিন্ন মোদের ,হৃদয় তো একটিই।
অধিবাসী মোরা কেউ হিজায ,চীন ,ইরান ও ভারতের ,
সকলে মোরা যেন শিশির একই প্রভাতের। ”
এই একক জনগোষ্ঠী হতেই প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে পনেরো লক্ষ মানুষের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।
জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদ এমন এক চিন্তা যা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে একে অপরের বিপরীতে দাঁড় করায়। গত শতাব্দী2 হতে ইউরোপে এ চিন্তার ঢেউ উচ্চকিত হয়েছে । হয়তো বা সেখানে এটি স্বাভাবিক। কারণ ইউরোপে এমন কোন মতবাদ ছিল না যা সেখানকার বিভিন্ন জাতিকে উচ্চতর পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদীদের মাধ্যমে এ ঢেউয়ের ধাক্কা প্রাচ্যের জাতিগুলোর মধ্যেও লাগে। সাম্রাজ্যবাদ ‘ বিভেদের জন্ম দাও ও শাসন কর ’ নীতি প্রয়োগ শুরু করে। এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম পথ হিসেবে ইসলামী জাতি-গোষ্ঠীসমূহকে নিজ নিজ বর্ণ ও জাতিসত্তার প্রতি মনোনিবেশের দিকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা নেয় এবং এক কাল্পনিক আত্মগর্বে নিমজ্জিত হতে উদ্বুদ্ধ করে ,যেমন ভারতীয়কে বলে ,তোমার অতীত এরূপ গৌরবময় ,তুর্কীকে বলে ,প্যানতুর্কী ইজম ধারণায় নব্য তুর্কী আন্দোলন শুরু কর ,আরবকে বলে ,তাদের মধ্যে পূর্ব হতেই গোত্রবাদের ধারণাসহ আরব জাতিত্বের ধারণা প্রকট ছিল-আরবী ভাষার ওপর ভিত্তি করে প্যান আরব ইজম আন্দোলনের সূচনা কর। ইরানীকে বলে ,তুমি আর্য জাতিভুক্ত এবং সেমিটিক জাতিভুক্ত আরব হতে ভিন্ন ,তোমার চিন্তা-ধারণা সবই ভিন্ন।
জাতীয়তাবাদী ধারণা জাতীয় চিন্তা ও অনুভূতির জাগরণের মাধ্যমে হয়তো অনেক জাতিরই স্বাধীন অস্তিত্বের বিষয়ে ইতিবাচক ও কল্যাণকর কিছু প্রভাব রাখতে পারে ,কিন্তু ইসলামী জাতিগুলোর মধ্যে এর কল্যাণকর কোন প্রভাব তো পড়েইনি ;বরং অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দেখা দেয়। ইসলামী জাতিসমূহ শতাব্দীকাল পূর্বে ঐক্যের আরো উচ্চতর পর্যায় অতিক্রম করেছিল। কারণ ইসলাম শতাব্দীকাল পূর্বে একক চিন্তা ,বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে অনন্য ঐক্য সৃষ্টি করেছিল ,এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও ইসলাম প্রমাণ করেছে এ ঐক্যের ভিত্তি উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর!
বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলনের মাধ্যমে উপনিবেশবাদীদের প্রভাব হতে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে তার পেছনে জাতিগত কারণ অপেক্ষা ইসলামী কারণই মুখ্য ও অধিকতর ফলপ্রসূ ছিল। উদাহরণস্বরূপ আলজিরিয়া ,ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের কথা বলতে পারি।
হ্যাঁ ,এ জাতিসমূহ শতাব্দীকাল হতে প্রমাণ দিয়েছে এক চিন্তা ,বিশ্বাস ও মতাদর্শের ভিত্তি এমন এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে যা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের থাবা হতে মুক্ত করতে সক্ষম। তাই এরূপ জাতি-গোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদের মত চিন্তার দিকে পরিচালিত করা প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।
সুতরাং বর্ণ ও জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হলো ইউরোপ এবং এ চিন্তাধারা ইসলামী বিশ্বের জন্য অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আসাদাবাদীর (আফগানী) নিজ জাতিসত্তা গোপন করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে ,তিনি চান নি তাঁকে বিশেষ কোন জাতিভুক্ত বলে পরিচিত করানো হোক যা উপনিবেশবাদীদের হাতে একটি হাতিয়ার হতে পারে এবং অন্য জাতিভুক্তদের তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে।
আমরা যেহেতু এক ধর্ম ,একই মতাদর্শ ও পথের ওপর রয়েছি যার নাম ইসলাম এবং যার মধ্যে জাতিগত ধারণার উপাদান নেই সেহেতু এ মতাদর্শের বিপরীতে বর্ণ ও জাতিগত যে কোন ধারণার বিরুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা অবহিত ,সম্প্রতি অনেক ব্যক্তিই ইরানী জাতিসত্তা সংরক্ষণের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছে এবং আরব ও আরবী ভাষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ইসলামের পবিত্র অনুভূতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছে।3
ইরানে ইসলামের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের নমুনা আমরা বই-পুস্তক ,দৈনিক ,সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে লক্ষ্য করছি। এটি আকস্মিক কোন বিষয় নয় ;বরং একটি পরিকল্পিত নকশা ও লক্ষ্যের ফলশ্রুতি।
বর্তমানে যারথুষ্ট্র ( Zoroastrian)ধর্মের প্রচারণা বেড়ে গিয়েছে এবং এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। সকলেই জানেন আজকের ইরানীরা কখনই যারথুষ্ট্র ধর্মে ফিরে যাবে না এবং যারথুস্ট্র ধর্মের শিক্ষাও ইসলামের স্থান দখল করতে পারবে না। যে সকল ব্যক্তি মাযদাকী , মনী এবং যারথুষ্ট্র ধর্মের ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত তাদের সকলেই আজ জাতীয় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিহিত এবং ইসলামী শিক্ষা হতে বিচ্যুত চরিত্র বৈ তাদের ভিন্ন কোন চরিত্র ছিল না। এখানে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই হোক বা আরব জাতির বাহানা এনেই হোক কার্যক্রম চালিয়ে ইরানীদের মন হতে ইসলামের প্রসিদ্ধ বীরদের স্মৃতি মুছে দিতে পারবে না। কখনই আল মুকান্না , মিনবাদ , ববাকে খুররামদীন এবং মজিয়ররা ইরানীদের অন্তরে আলী ইবনে আবি তালিব , হুসাইন ইবনে আলী , এমনকি সালমান ফারসীর স্থান অধিকারে সক্ষম নয়। সকলেই তা জানে।
যদিও এর মাধ্যমে হয়তো অপরিপক্ব ও বুদ্ধিহীন যুবকদের মধ্যে দেশ ,জাতি ও রাষ্ট্রীয় চেতনা ও অনুভূতি জাগরিত করা এবং তাদের সঙ্গে ইসলামের ব্যবধান ও সম্পর্কচ্ছেদ সৃষ্টি সম্ভব। অর্থাৎ যদিও ইসলামী অনুভূতির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে অন্য ধর্মানুভূতি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় ,কিন্তু ইসলামী অনুভূতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তার বিপরীত অনুভূতি সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা করা সম্ভব। এজন্যই লক্ষ্য করি ধর্ম ও আল্লাহ্বিরোধী ব্যক্তিরা বুদ্ধিহীন মগজ হতে উৎসারিত অর্থহীন লেখাগুলোতে যারথুষ্ট্র এবং ইসলাম পূর্ববর্তী ইরানের অবস্থাকে সমর্থন করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য আমাদের নিকট স্পষ্ট।
আমরা আমাদের এ আলোচনায় ঐ যুক্তি এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করব যে যুক্তি ও দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যক্তিরা বিষয়টিকে দেখে। আর তা হলো জাতীয়তা ,জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদ। হ্যাঁ ,এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আলোচনা রাখব। যদিও আমরা ইকবাল লাহোরীর এ কথা ভুলে যাই নি- ‘ জাতিভক্তি ও আরাধনা এক প্রকার অসভ্যতা ’ । এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি রয়েছে যে ,জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির ইতিবাচকতা ততক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে যতক্ষণ এর মাধ্যমে স্বদেশের মানুষের সেবা করা যায। কিন্তু কখনও কখনও অনুভূতি ও চেতনা নেতিবাচকতার জন্ম দেয় ,বৈষম্যের সৃষ্টি করে ,ভাল-মন্দ বিচারে অন্ধত্ব ও পক্ষপাতিত্ব এবং নৈতিকতা ও মানবিকতাবিরোধী চেতনার উৎপত্তি ঘটায়।
আমরা জানি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় চেতনার যুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর যুক্তি আমাদের নিকট রয়েছে যেখানে জ্ঞান ,দর্শন ও ধর্ম আবেগ-অনুভূতির ঊর্ধে অবস্থান করছে। জাতীয় অনুভূতির চেতনা সকল স্থানে গ্রহণীয় হলেও জ্ঞান ,দর্শন ও ধর্মের অনুসন্ধানে গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞান ,দর্শন ও ধর্মীয় কোন বিষয়ে তা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় হলেই গ্রহণযোগ্য হবে এমনটি নয়। তেমনিভাবে চিন্তাগত কোন বিষয় বিদেশী ও বিজাতীয় হলেই তা বর্জনীয় এমনও নয়। এ কথা সত্য যে ,জ্ঞান ,ধর্ম ও দর্শনের কোন রাষ্ট্র নেই । কারণ এগুলো সর্বজনীন। তাই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ,বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদেরও কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র নেই ,তাঁরাও বিশ্বজনীন। তাঁরা সমগ্র বিশ্বের ,সকল রাষ্ট্রই তাঁদের রাষ্ট্র এবং সকল মানুষই তাঁদের স্বদেশী।
যদিও বিষয়গুলো আমরা জানি তদুপরি এখানে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতর এ যুক্তিকে আমরা আপাতত দূরে রাখছি এবং অপূর্ণাঙ্গ মানুষদের উপযোগী অনুভূতি ও আবেগকেন্দ্রিক যুক্তির ওপর নির্ভর করেই এ আলোচনা শুরু করছি।
আমরা দেখতে চাই জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির দৃষ্টিতে যদি ইসলামকে যাচাই করি তা কি বিজাতীয় বলে পরিগণিত হবে ? আমরা দেখতে চাই জাতীয়তার মানদণ্ডে ইসলাম ইরানী জাতীয়তা ও ইরানী জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্তর্ভুক্ত নাকি এর বহির্ভূত।
এ লক্ষ্যে আমাদের আলোচনাকে দু ’ টি অংশে ভাগ করব। প্রথমত আমরা জাতীয়তার মানদণ্ড অর্থাৎ কোন বস্তুকে জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত বলার মানদণ্ড কি তা দেখব। দ্বিতীয়ত দেখব এ মানদণ্ডের আলোকে ইসলাম ইরানী জাতীয়তার অভ্যন্তরের বিষয় নাকি বিজাতীয় ? বাস্তবে আমাদের আলোচনায় দু ’ টি প্রতিজ্ঞা রয়েছে। প্রথম অংশ বৃহত্তর প্রতিজ্ঞা ( major premise) এবং দ্বিতীয় অংশ ক্ষুদ্রতর প্রতিজ্ঞা ( minor premise) ।
প্রসঙ্গত ইসলাম ও যারথুষ্ট্র প্রবণতার (যারথুষ্ট্র ধর্ম প্রবণতা) মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা রাখব এবং তাতে প্রমাণিত হবে জাতীয়তার মানদণ্ডে ইসলাম ইরানী জাতিসত্তার অধিকতর নিকটবর্তী নাকি যারথুষ্ট্র প্রবণতা ?
‘ মিল্লাত ’ ( জাতি) শব্দের অর্থ
‘ মিল্লাত ’ (ملّة ) একটি আরবী শব্দ যার অর্থ পথ ও পদ্ধতি। পবিত্র কোরআনেও শব্দটি এ অর্থে এসেছে।4 এ শব্দটি কোরআনের 15টি আয়াতে 15 বার এসেছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানে ফার্সী পরিভাষায় তা ভিন্ন অর্থে প্রচলিত হয়েছে।
কোরআনের পরিভাষায় ‘ মিল্লাত ’ অর্থ ঐশী বার্তাবাহক নবীদের পক্ষ হতে যে পথ মানুষের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে:ملّة أبيكم إبراهيم ‘ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের পথ ’ 5 অথবাملّة إبراهيم حنيفا ‘ ইবরাহীমের পথ যা সত্য ও বিশুদ্ধ ’ ।6
রাগিব ইসফাহানী তাঁর ‘ মুফরাদাতুল কোরআন ’ গ্রন্থে বলেছেন , “ মিল্লাত ও ইসলাম একই মূল হতে এসেছে যার অর্থ ‘ লিখিয়ে দেয়া ’ । যেমন বলা হয়েছে:فليملل وليّه بالعدل ‘ তখন তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখিয়ে দেবেন। ’ 7 তিনি বলেছেন ,আল্লাহর পথকে ‘ মিল্লাত ’ বলা হয়েছে এ জন্য যে ,এ পথ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত হয়েছে।
সুতরাং কোরআনের দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে যে চিন্তা ,জ্ঞান ও জীবন পদ্ধতি অনুসারে মানুষকে চলতে হবে তাকেই ‘ মিল্লাত ’ বলা হয়। সুতরাং ‘ মিল্লাত ’ ও ‘ দীন ’ সমার্থক ,তবে পার্থক্য এটুকু ,একই বস্তুকে এক দৃষ্টিতে ‘ মিল্লাত ’ এবং অন্য দৃষ্টিতে ‘ দীন ’ বলে অভিহিত করা হয়। এ দৃষ্টিতে ‘ মিল্লাত ’ বলা হয় যে ,তা আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর নবীর প্রতি নির্দেশিত হয়েছে-যা মানুষের নিকট তিনি পৌঁছে দেবেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই নেতৃত্ব দান করবেন।
ধর্মীয় পরিভাষাবিদরা বলেন ‘ দীন ’ ও ‘ মিল্লাত ’ শব্দের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো ‘ দীন ’ শব্দটিকে আল্লাহর সঙ্গে যেমন সংযুক্ত করা যায় ,উদাহরণস্বরূপ বলা যায়دين الله আল্লাহর দীন তেমনি দীনের অনুসারীদের নামের সঙ্গেও সংযুক্ত করা যায় ,যেমনدين زيد أو دين عمرو যায়েদ বা আমরের দীন। কিন্তু ‘ মিল্লাত ’ শব্দটি আল্লাহ্ বা অনুসারীদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় না। তাই ‘ আল্লাহর মিল্লাত ’ বা ‘ যায়েদের মিল্লাত ’ বলা ভুল হবে ;বরং ‘ মিল্লাত ’ শব্দটি কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর পথে নেতৃত্ব দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের সঙ্গেই সংযুক্ত হয় ,যেমন বলা হয়েছে ‘ মিল্লাতে ইবরাহীম ’ বা ‘ মিল্লাতে মুহাম্মদ ’ (সা.)। যেন ‘ মিল্লাত ’ শব্দের সঙ্গে নেতৃত্ব শব্দটিও জড়িয়ে রয়েছে।
এ দৃষ্টিকোণ হতে ‘ মিল্লাত ’ শব্দটিকেمكتب (মাকতাব) বা মতবাদের নিকটবর্তী বলা যায়। কেননা সাধারণত মতবাদ কোন প্রবক্তা বা নেতার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। যদি ‘ মিল্লাত ’ শব্দের সঙ্গে ‘ মাকতাব ’ শব্দের নির্দেশিত হওয়ার সাদৃশ্যের বিষয়টি লক্ষ্য রাখি তাহলে বিষয়টি আমাদের জন্য অধিকতর স্পষ্ট হবে।
বর্তমানে ফার্সী পরিভাষায় ‘ মিল্লাত ’
বর্তমানে ফার্সী পরিভাষায় ‘ মিল্লাত ’ শব্দটি তার মূল অর্থ হতে ভিন্ন অর্থে প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে ‘ মিল্লাত ’ শব্দটি একটি একক সমাজের প্রতি আরোপিত হয় যা অভিন্ন ইতিহাস ,আইন ,রাষ্ট্রব্যবস্থা ,মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক। আমরা এখন জার্মান ,বৃটেন বা ফ্রান্সের সকল অধিবাসীকে জার্মানী ,ব্রিটিশ বা ফরাসী জাতি না বলে তাদের দু ’ ভাগে ভাগ করি। একদিকে শাসক অন্য দিকে সাধারণ নাগরিক। আমরা শাসকবর্গকে সরকার এবং সাধারণ নাগরিকদের মিল্লাত বা জাতি হিসেবে অভিহিত করি। এ ফার্সী পরিভাষাটি একটি নতুন ও উদ্ভাবিত পরিভাষা এবং প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভুল পরিভাষা। কারণ শত বা সহস্র বছর পূর্বে শব্দটি ফার্সী ভাষায় এরূপ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হতো না। আমার মনে হয় ইরানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তীতে শব্দটির এ অর্থে ব্যবহার শুরু হয়। সম্ভবত এ ভুলের সৃষ্টি এভাবে হয়েছে ,শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং পরে সংযুক্ত শব্দটি বাদ পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইবরাইীমের পথের (মিল্লাতের) অনুসারী ,ঈসার পথের অনুসারী ,মুহাম্মদ (সা.)-এর পথের অনুসারী ইত্যাদি। পরে অনুসারী শব্দটি বাদ পড়ে যায় এবং বলা শুরু হয় ইবরাহীমের মিল্লাত ,ঈসার মিল্লাত ,মুহাম্মদের মিল্লাত ইত্যাদি। আরো পরে ‘ মিল্লাত ’ শব্দটি বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন পরিভাষায় পরিণত হয় ,যেমন মিল্লাতে ইরান ,মিল্লাতে তুর্ক ,মিল্লাতে আরব ,মিল্লাতে ইংরেজ ইত্যাদি।
আরবরা জাতি অর্থে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তারা ‘ কাওম ’ (قوم ) বা ‘ শাআব ’ (شعب ) জাতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করে। যেমন বলেالشّعب العربي বাالشّعب الإيراني বাالشّعب المصري ইত্যাদি।
আমরা আমাদের এ আলোচনায় ‘ মিল্লাত ’ ও ‘ মিল্লিয়াত ’ জাতি ও জাতীয়তা অর্থেই ব্যবহার করছি প্রচলিত ফার্সী পরিভাষা হিসেবে ,তা সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কি হচ্ছে না তার পর্যালোচনায় না গিয়েই।
সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে জাতীয়তা
এখন আমরা পারিভাষিক আলোচনার পর্ব শেষ করে সামাজিক আলোচনায় প্রবেশ করছি। সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক হলো পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ,সন্তান-সন্ততি ,কখনও কখনও সন্তানদের স্বামী ,স্ত্রী ও সন্তানদেরসহ যে যৌথ জীবন গড়ে ওঠে তাকে পারিবারিক জীবন বলা হয়। পারিবারিক জীবনের ঐতিহ্য অত্যন্ত পুরাতন। যখন হতে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে তখন হতেই পারিবারিক জীবন চলে এসেছে। অনেকের ধারণা ,মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য কোন প্রাণী ছিল। বলা হয়ে থাকে সে পর্যায়েও মোটামুটিভাবে পারিবারিক জীবন ছিল।
পরিবার হতে বৃহত্তর সমাজিক একক হলো গোত্র বা বংশ। গোত্রীয় জীবন হলো যে সকল পরিবারের পিতৃপুরুষ এক ব্যক্তি। গোত্রীয় জীবন ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের পূর্ণাঙ্গতর রূপ।
বলা হয়ে থাকে মানবের পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পদ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামষ্টিক মালিকানা ছিল ,পরবর্তীতে তা ব্যক্তি মালিকানায় পর্যবসিত হয়।
গোত্র অপেক্ষা বৃহত্তর যে সামাজিক একক পূর্ণতররূপে আবির্ভূত হয় এবং এক জনসমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করে-যাদের ওপর একই আইন ও একক সরকারের নেতৃত্ব কার্যকর তাকে ফার্সী ভাষাভাষীরা ‘ মিল্লাত ’ বা জাতি বলে থাকে। একটি জাতি একটি মূল ,রক্ত ,বংশ ও গোত্র হতে যেমন উৎপত্তি লাভ করতে পারে তেমনি এরূপ ঐক্য নাও থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে ,তাদের মাঝে ঐতিহ্যগতভাবে গোত্রীয় জীবনই হয়তো ছিল না বা থাকলেও সীমিত পর্যায়ে কোন গোষ্ঠীতেই ছিল।
‘ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলনীতি ’ 8 নামক গ্রন্থের 1ম খণ্ডের 327 পৃষ্ঠায় এসেছে :
‘ বিংশ শতাব্দীতে ‘ জাতি ’ ও ‘ জনতা ’ র মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাতে বোঝা যায় অধিকংশ ক্ষেত্রে সামাজিক কোন দলকে বুঝাতে জনতা বলা হয়ে থাকে ;কিন্তু জাতি বলতে কোন ভূখণ্ড বা রাষ্ট্রে বসবাসরত জনসমষ্টি যারা একই রাজনৈতিক ও আইনগত বিধানের আওতায় রয়েছে তাদের বুঝায়। একই ভূখণ্ডে অবস্থানের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। ঐতিহাসিক ,ভাষাগত ,ধর্মীয় ,অর্থনৈতিক ,সামাজিক মূল্যবোধ বা সামষ্টিক জীবনের অভিন্ন লক্ষ্যের কারণে এটি হতে পারে। ‘ জনতা ’ শব্দটি সাধারণত সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় এবং ‘ জাতি ’ শব্দটি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। তবে এ শব্দটি মার্কসবাদে এবং উদারনীতিবাদে9 ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তা ও লেখক কোন্ মতাদর্শে বিশ্বাসী তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ’
বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। যে বিষয়টি তাদের এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করেছে তা হলো সামষ্টিক জীবন এবং অভিন্ন আইন ও সরকার। যেহেতু একক সরকার তাদের ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু এর ওপর ভিত্তি করেই তারা এক জাতি ;এক রক্ত ,বর্ণ ও ভাষার কারণে নয়। এ সকল জাতির অনেকেরই দীর্ঘ ঐতিহাসিক কোন নজীরও নেই ;বরং সামাজিক কোন ঘটনা প্রবাহের ফলে সৃষ্ট হয়েছে ,যেমন মধ্যপ্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্রই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানী খেলাফতের পতনের কারণে সৃষ্ট হয়েছে।
বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা এক রক্ত ও বর্ণ হতে সৃষ্ট এবং অন্য জাতি হতে স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইরানীরা দীর্ঘ ইতিহাসের অধিকারী এবং শাসন ব্যবস্থা ও আইনের দৃষ্টিতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে ,কিন্তু নৃতাত্ত্বিকভাবে কি আমরা প্রতিবেশী জাতিসমূহ হতে স্বতন্ত্র ? আমরা আর্য বংশোদ্ভূত এবং আরবরা সেমিটিক বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে এখনও কি পৃথক যখন শত সহস্র মিশ্রণের ফলে ঐ নৃতাত্ত্বিক ভিত্তির কোন প্রভাবই এখন অবশিষ্ট নেই ?
বাস্তব হলো রক্ত ও বর্ণ পৃথক হওয়ার দাবিটি একটি অলীক দাবি। নৃতাত্ত্বিকভাবে কেউ আর্য সেমিটিক বা অন্য কিছু হওয়ার বিষয়টি পূর্বে ছিল ,কিন্তু পরবর্তীতে এত বেশি মিশ্রণ ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ,ঐ সকল বর্ণের স্বাধীন কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই।
বর্তমান সময়ে ইরানী ও ফার্সী ভাষী অনেক ব্যক্তিই যাঁরা ইরানী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন হয়তো তুর্কী ,মোগল বা আরব বংশোদ্ভূত তেমনি আরবদের মধ্যেও আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষাবলম্বনকারী অনেক ব্যক্তি হয়তো ইরানী ,তুর্কী বা মোগল বংশোদ্ভূত। আপনি যদি এখন মক্কা ও মদীনায় ভ্রমণ করেন তাহলে লক্ষ্য করবেন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হয় ভারতীয় ,ইরানী ,বালখী ,বুখারী বা অন্য কোন অঞ্চলের আদি অধিবাসী। হয়তো কুরুশ বা দারভীশ বংশের (ইরানের দুই প্রসিদ্ধ বংশ) কোন ব্যক্তি আরব ভাষার কোন দেশে বাস করে এবং আরব জাতীয়তার প্রতি গোঁড়ামি পোষণ করে। বিপরীত দিকে হয়তো আবু সুফিয়ানের অনেক বংশধর বর্তমানে ইরানী জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি পোষণ করে। কয়েক বছর পূর্বে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন যে ,ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া একজন ইরানী বংশোদ্ভূত। যদি তা-ই হয় তবে তার বংশধররা তো এখানে থাকতেই পারে।
সুতরাং বর্তমানে জাতি বলতে যা বুঝায় তাতে আমরা এমন এক জনসমষ্টি যারা এক ভূখণ্ডে ,এক পতাকার নীচে ,অভিন্ন সংবিধান ও সরকারের অধীনে বসবাস করছি। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ ইরানী ,গ্রীক ,আরব না মোগল ছিল তা আমরা জানি না।
যদি আমরা ইরানীরা জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কাউকে আর্য কিনা বিচার করতে যাই তবে এ জাতির অধিকাংশ লোককে অ-ইরানী বলতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের আর গর্ব থাকবে না অর্থাৎ এ কর্মের মাধ্যমে আমরা ইরানী জাতীয়তাবাদের ওপর সর্বোচ্চ আঘাতটি হানব। বর্তমানে ইরানে অনেক গোত্র ও সম্প্রদায় রয়েছে যাদের ভাষা ফার্সী নয় এবং তারা আর্য বংশোদ্ভূতও নয়। তাই বর্তমান সময়ে জাতি ,রক্ত ও বর্ণের স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিছক বুলি ছাড়া কিছুই নয়।
জাতীয়তার গোঁড়ামি
সমাজের যে কোন একক তা পরিবার ,গোত্র ,সম্প্রদায় বা জাতি যা-ই হোক না কেন ,তার সঙ্গে এক প্রকার আবেগ ও গোঁড়ামি জড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নিজ পরিবার ,গোত্র ও জাতির প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। পক্ষপাতিত্বের এ অনুভূতি কখনও কখনও কোন বৃহত্তর এককেও (বৃহত্তর অঞ্চল নিয়েও) দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এশিয়ানদের মোকাবিলায় ইউরোপীয়রা এক ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক আবেগ প্রদর্শন করতে পারে যেমনিভাবে পারে এশিয়ানরাও। একই বর্ণের ও জাতির মানুষরাও পরস্পরের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে।
জাতীয়তার বিষয়টিও স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বের অন্তর্ভুক্ত তবে তা ব্যক্তি ও গোত্রের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে।
জাতীয়তার মধ্যে স্বার্থপরতার সাথে স্বাভাবিকভাবেই পক্ষপাতিত্ব ,গোঁড়ামি ,জাতীয় মানদণ্ডে স্বজাতির ত্রুটির প্রতি নির্লিপ্ততা ,স্বজাতির ভাল দিকগুলোকে বড় করে দেখা ,অহংকার ও গর্বের মত বিষয়গুলো চলে আসে।
জাতীয়তাবাদ
স্বজাতির প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাকে ইংরেজি ভাষায় ‘ ন্যাশনালিজম ’ বলে অভিহিত করা হয় যা ফার্সী ভাষার পণ্ডিতরা ‘ মিল্লাত পারাস্তি ’ অনুবাদ করেছেন।
জাতীয়তবাদ জাতীয় আবেগ ও অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ;কোন যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে নয় যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করা যায় না যদি তার মধ্যে শুধু ইতিবাচক দিকগুলোই থাকে। যেমন পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা ,স্বজাতির লোকদের অধিকতর কল্যাণ সাধন প্রভৃতি দিকগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যুক্তিহীন নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতেও নিন্দনীয় নয় ;বরং ইসলাম প্রতিবেশী ,আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের প্রতি অধিকতর অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করেছে।
জাতীয়তাবাদ তখনই নিন্দনীয় যখন তা নেতিবাচকতা লাভ করে অর্থাৎ যখন বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি শত্রু করে তোলে এবং অন্যের ন্যায্য অধিকারের প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করে।
জাতীয়তাবাদের বিপরীত হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ যা বৈশ্বিক মানদণ্ডে জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করে। ইসলাম জাতীয়তাবাদী অনুভূতির সকল দিককেই নিন্দা করে না ;বরং শুধু নেতিবাচক দিকগুলোকে নিন্দা করে ,ইতিবাচক দিকগুলোকে নয়।
জাতীয়তার মানদণ্ড
বাহ্যিকভাবে মনে হয় জাতীয়তাবাদী চেতনা হলো একটি ভূখণ্ডের মানুষের সৃষ্টি ও চিন্তার ফল যা ঐ ভূখণ্ডের সম্পদ এবং যা কিছু জনসাধারণের দৃষ্টিতে জাতীয় বলে পরিগণিত তা গ্রহণ ,সে সাথে ঐ ভূখণ্ডের বাহির্ভূত সকল কিছুই বিদেশী ও বিজাতীয় বলে পরিত্যাগ। এ মানদণ্ডই জাতীয়তা যাচাইয়ের ভিত্তি বলে অনেকে মনে করেন।
কিন্তু এ মানদণ্ড সঠিক নয়। কারণ অসংখ্য লোক নিয়ে জাতি গঠিত হয়। তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি সৃজনশীল কিছু করলেই অন্যরা তা গ্রহণ করবে তা সম্ভব নয় ;বরং সাধারণের পছন্দ ভিন্ন কিছু হতে পারে। তাই এমন বিষয় জাতীয় বলে পরিগণিত হতে পারে না।
উদাহরণস্বরূপ কোন জাতি হয়তো কোন বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাকে নিজেদের জন্য মনোনীত করেছে ,কিন্তু ঐ জাতিরই কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নতুন কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করতে পারে যা তারা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত এ ব্যবস্থাকে ঐ জাতির এক ব্যক্তির উদ্ভাবিত চিন্তার ও সৃজনশীলতার প্রমাণ হওয়ায় তাকে জাতীয় বলে অভিহিত করা যায় না ,অথচ ঐ রাষ্ট্রের বহির্সীমার কোন ব্যক্তি কোন সামাজিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার পর যদি ঐ জাতি তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে তবে এ ব্যবস্থাকে অন্য দেশ হতে এসেছে এ অজুহাতে বিজাতীয় বলে অভিহিত করা যায় না কিংবা যে ব্যক্তি এ ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে তাকেও জাতীয় মৌলনীতি পরিপন্থী কাজ করেছে বলে অভিযুক্ত করা যায় না। এ কর্মের ফলে ঐ জাতি অন্য জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় না বা তারা তাদের পথ ও জাতিসত্তাকে পরিবর্তন করেছে বলা যায় না।
অবশ্য কখনও কখনও এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বাইরে থেকে এলে সেটি বিজাতীয় এবং জাতীয় নীতির পরিপন্থী বলে পরিগণিত হবে। এরূপ বিষয়ের গ্রহণও তাই জাতিসত্তা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বলে ধরা হবে । যেমন এমন কোন বিষয় যা এক জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও রং ধারণ করেছে এবং তাদের জাতীয় প্রতীক ও স্লোগান বলে গণ্য হয় ,যদি অন্য কোন জাতি সে রং ও স্লোগান ধারণ করে তবে জাতিসত্তার নীতি বহির্ভূত কাজ হবে। তাই জার্মানীর নাজী বা যায়নবাদী ইহুদীদের যে বিশেষ প্রতীক ও রং রয়েছে তা যদি অন্য কোন জাতি গ্রহণ করে তবে তারা স্বজাতির বিরুদ্ধে জাতীয়তা বিরোধী কাজ করেছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি ঐ রংয়ের কোন বিশেষত্ব না থাকে ও কোন বিশেষ জাতির প্রতীক না হয় ;বরং সকল জাতির জন্য সাধারণ হয়ে থাকে অর্থাৎ এর স্লোগানগুলো যদি সর্বজনীন ও মানবিক হয় তবে যে কেউ তা গ্রহণ করুক না কেন তা বিজাতীয় ও জাতিসত্তা পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে না। ধর্মীয় ছাত্রদের ভাষায়
لا بشرط يجتمع مع ألف شرط শর্তহীন বিষয় সহস্র শর্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে অর্থাৎ রংহীন প্রকৃতির বস্তু যে কোন রংই গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু রঙ্গীন বস্তু অন্য কোন রূপের সঙ্গে মিলে না।
এ কারণেই জ্ঞানগত বিষয়সমূহ সমগ্র বিশ্বের সম্পদ বলে পরিগণিত। পীথাগোরাসের চার্ট বা আইনস্টাইনের সূত্র কোন জাতির সম্পদ নয় এবং কোন জাতিসত্তার সঙ্গেই এর বৈপরীত্য নেই। কারণ এটি একটি রংহীন বাস্তবতা যা বিশেষ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়। এজন্যই নবী ,দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও সকল জাতির সম্পদ এবং তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাস কোন বিশেষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়।
সূর্য বিশেষ কোন জাতির জন্য নয় বলে কোন জাতিই সূর্যকে বিজাতীয় ভাবে না। সূর্য সমগ্র বিশ্বের জন্য ,কোন বিশেষ ভূমির জন্য নির্দিষ্ট নয়। যদি কোন স্থান সূর্যতাপ স্বল্প পরিমাণে পেয়ে থাকে তবে সেটি তার অবস্থানের কারণে ,সূর্যের কারণে নয়। সূর্য নিজেকে কোন বিশেষ ভূমিতে সীমাবদ্ধ রাখেনি।
সুতরাং আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো যে ,কোন বিষয় এক জাতি হতে উদ্ভূত হলেই তা তাদের নিজস্ব হয়ে যায় না যেমনি তার সীমাবহির্ভূত অঞ্চল হতে কিছু প্রবেশ করলেই বিজাতীয় বলা যায় না। অর্থাৎ জাতীয় ও বিজাতীয় হওয়ার মানদণ্ড এটি নয়। অভিন্ন দীর্ঘ ইতিহাসের অধিকারী হওয়াও জাতীয়তার মানদণ্ড নয়। যেমন আমাদের ইরানে অন্যান্য অনেক দেশের মতই আড়াই হাজার বছর ধরে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কার্যকর ছিল যা অর্ধ শতাব্দী কালের কিছু বেশি সময় হলো সাংবিধানিক সরকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা নিজেরা উদ্ভাবন করি নি ;বরং অন্যরা তা উদ্ভাবন করেছে ও আমরা তা গ্রহণ করেছি ও এটি অর্জনের জন্য অনেক আত্মবিসর্জনও দিয়েছি। অবশ্য এ জাতিরই অনেক ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য আশ্চর্যজনক প্রতিরোধ করেছে ,অস্ত্রধারণ করেছে ,নিজের রক্ত ঝরিয়েছে যদিও তারা ছিল সংখ্যালঘু। অপরদিকে ইরান জাতির অধিকাংশ মানুষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। অবশেষে সংখ্যালঘু বিরোধীরা সংখ্যাগুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এখন কি আমরা শাসনন্ত্রিক ব্যবস্থাকে জাতীয় সরকার বলে মেনে নেব না ? নাকি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব স্বৈরতান্ত্রিক ছিল বিধায় এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক যেহেতু আমরা নই ;বরং অন্য জাতির নিকট হতে গ্রহণ করেছি এ অজুহাতে দাবি তুলব আমাদের জাতীয় সরকার হলো স্বৈরতান্ত্রিক (তাই উচিত হলো একে গ্রহণ করা) এবং শাসনতান্ত্রিক সরকার বিজাতীয় সরকার (তাই উচিত তা বর্জন করা)।
বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্র আমরা প্রস্তুত করিনি বা এটি প্রস্তুতেও আমরা ভূমিকা রাখিনি এবং এই ঘোষণাপত্রে যা এসেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তা উল্লিখিত হয় নি ,কিন্তু অন্যান্য জাতির মতই আমরা এ ঘোষণাপত্রকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছি। এখন ইরানী জাতীয়তার ধারণায় এ ঘোষণাপত্রকে কি বলে উল্লেখ করব ? যে সকল রাষ্ট্র এ ঘোষণাপত্র প্রস্তুতে অংশ নেয় নি ,যেহেতু ঘোষণাপত্রটি তাদের রাষ্ট্রসীমার বহির্ভূত সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যই বা কি হবে ? তাদের জাতীয় চেতনা কি এ ঘোষণাপত্র তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ও তাদের ভূখণ্ডের বাইরে থেকে আগমনের অজুহাতে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে বলে ? তারা কি একে বিজাতীয় মনে করে ? নাকি যেহেতু এ ঘোষণাপত্র কোন বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্য নেয় নি এবং জাতি একে গ্রহণ করেছে এ দু ’ যুক্তিতে আমরাও একে জাতীয় ও নিজস্ব বলে মনে করব ?
এর বিপরীতে সম্ভাবনা রয়েছে এমন কিছু প্রচলিত মত ও পথ থাকতে পারে যা কোন জাতি হতে উদ্ভূত ,কিন্তু ঐ জাতির জাতীয় বিষয় বলে পরিগণিত হয় না। যেহেতু বিষয়টিতে অন্য জাতির রং রয়েছে অথবা নিজ ভূখণ্ড হতে উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও জাতি তা গ্রহণ করে নি সেহেতু তা জাতীয় বলে গৃহীত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ মনী ও মাজদাকী ধর্ম বিশ্বাস ইরানী জাতির মধ্যে আবির্ভূত হলেও জাতির পক্ষ হতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি। তাই এ দু ’ ধর্মমতের কোনটিকেই ইরানের জাতীয় বিষয় বলা যায় না।
যদি এরূপ উদ্ভাবক ও তাদের গুটি কয়েক অনুসারীদের কর্মকে ‘ জাতীয় ’ বলে অভিহিত করি তবে অধিকাংশ মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে উপেক্ষা করা হবে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল জাতীয় অনুভূতি ও আবেগের চেতনার দৃষ্টিতে যা কিছুই ঐ দেশে উদ্ভাবিত হয় তা-ই জাতীয় হতে পারে না। আবার যা কিছুই দেশের সীমার বাইরে থেকে আসে বিজাতীয় বলে পরিগণিত হয় না ;বরং মানদণ্ড হলো প্রথমে জানতে হবে ঐ বিষয়টি কোন জাতির বিশেষ রং ধারণ করেছে কি ? নাকি তা রংহীন সর্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন ? দ্বিতীয়ত ঐ জাতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তা গ্রহণ করেছে নাকি চাপে বাধ্য হয়ে ?
যদি দু ’ টি শর্তই পূরণ হয় তবে ঐ বিষয়টি নিজস্ব ও জাতীয় বলে গণ্য হবে আর যদি এ দু ’ শর্ত সমন্বিত না হয় অর্থাৎ যে কোন একটি উপস্থিত থাকে অথবা কোনটিই উপস্থিত না থাকে তবে তা বিজাতীয় বলে গণ্য হবে। যা হোক কোন বিষয় কোন জাতির মধ্যে উদ্ভাবিত হলেই তা যেমন স্বীয় সম্পদ হতে পারে না। আবার একই কারণে তা বিজাতীয়ও হতে পারে না।
এখন আমরা এ আলোচনায় প্রবেশ করব ,ইসলাম কি ইরানে এ দু ’ শর্ত পূরণ করেছে ? অর্থাৎ প্রথমত ইসলাম কি বিশেষ জাতির রং (বৈশিষ্ট্য) ধারণ করেছে যেমন আরব জাতীয়তার রং নাকি এমন এক দীন যা সাধারণ ও বিশ্বজনীন হওয়ার কারণে রংহীন ? দ্বিতীয়ত ইরান জাতি কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে নাকি বাধ্য হয়ে ?
‘ জাতি ’ ও ‘ জাতীয়তা ’ নিয়ে যে আলোচনা রেখেছি তা ধর্মীয় ছাত্রদের ভাষায় আলোচনার বৃহত্তর প্রতিজ্ঞা এবং বর্তমান বিষয়টি আলোচনার ক্ষুদ্রতর প্রতিজ্ঞা।
ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ
এ বিষয় সুনিশ্চিত ,ইসলাম ধর্মে বর্তমানে প্রচলিত জাতীয়তার কোন মূল্য নেই ;বরং ইসলাম সকল জাতি ,গোত্র ও বর্ণকে সমদৃষ্টিতে দেখে। আবির্ভাবের প্রথমেও এ ধর্মের দাওয়াত বিশেষ জাতির প্রতি ছিল না। তাই প্রথম থেকেই এ ধর্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্ন উপায়ে গোত্রীয় ও জাতীয় গর্ব ও অহংকারের ভিত্তিকে উপড়ে ফেলার।
এখানে দু ’ টি অংশে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমাংশে ইসলামের ঊষালগ্ন হতেই যে ইসলাম বিশ্বজনীন দাওয়াত পেশ করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং দ্বিতীয়াংশে ইসলামের মানদণ্ড যে জাতি ,গোত্র বা বর্ণভিত্তিক নয় ,বরং বিশ্বজনীন সেটি প্রমাণ করা হবে।
ইসলামের বিশ্বজনীন আহ্বান
কোন কোন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের দাবি ইসলামের নবী (সা.) প্রথম দিকে চেয়েছিলেন শুধু কুরাইশদের হেদায়েত করতে ,কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের প্রসারের গতি লক্ষ্য করে আরব ও অনারব সকলের নিকট এ ধর্মের দাওয়াত উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।
এ মন্তব্য কাপুরুষতামূলক অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। আর এ কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিও নেই এবং কোরআনের প্রথম দিকের আয়াত যা নবীর ওপর অবতীর্ণ হয় তাও এ কথাকে অসত্য প্রমাণ করে। কোরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে ,অথচ সর্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন। তন্মধ্যে কোরআনের ক্ষুদ্র সূরাগুলোর অন্যতম সূরা আত-তাকভীরের কথা উল্লেখ করতে পারি। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ও নবুওয়াতের প্রারম্ভিক একটি সূরা-যার একটি আয়াতে বলা হয়েছে
) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (
‘ এটি বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়। ’ 10
সূরা সাবার 28 নং আয়াতে বলা হয়েছে:
) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (
‘ আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ;কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। ’
সূরা আম্বিয়ার 105 নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ,
) و لقد كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون (
‘ আমরা উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি ,আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। ’
সূরা আ ’ রাফের 158 নং আয়াতে বলা হয়েছে :
) يا أيّها النّاس إنّي رسول الله إليكم جميعا (
‘ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল। ’
কোরাআনের কোন স্থানেইيا أيّها العرب ‘ হে আরব জাতি ’ বাيا أيّها القريشيّون ‘ হে কুরাইশ সম্প্রদায় ’ বলে উল্লিখিত হয়নি। কোরআনে কখনও কখনওيا أيّها الذين آمنوا এসেছে সে সকল মুমিনের প্রতি লক্ষ্য করে যাঁরা নবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বা হবেন। এ ক্ষেত্রেও মুমিন ব্যক্তি যে কোন জাতি ,গোত্র বা বর্ণের হতে পারেন ,বিশেষ কোন জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানগুলোতে সাধারণভাবেيا أيّها النّاس ‘ হে মানবমণ্ডলী ’ বলা হয়েছে।
ইসলামী শিক্ষার সর্বজনীনতা এবং এ দীনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আরেক ভাবেও প্রমাণ করা যায়। তা হলো কোরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যাতে ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আরবদের এক প্রকার তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং তাদের অমনোযোগের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ঐ আয়াতগুলোর ভাবার্থ এরূপ যে ,ইসলামের তোমাদের প্রতি কোন প্রয়োজন নেই ,তাই যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবে পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি রয়েছে যারা মন হতে ইসলামকে গ্রহণ করবে ,এমনকি এরূপ আয়াতসমূহ হতে এও বোঝা যায় ,কোরআন ঐ জাতিসমূহের হৃদয়কে ইসলামের জন্য অধিকতর উপযোগী ও প্রস্তুত বলে মনে করে। এ আয়াতগুলো যাথার্থভাবে ইসলামের বিশ্বজনীনতাকে তুলে ধরে। যেমন সূরা আনআমের 89 নং আয়াতে বলা হয়েছে :
) فإن يكفربِها هؤلاء فقد وكّلنا بِها قوماً ليسوا بِها بكافرين (
‘ যদি তারা (আরবরা) কোরআনকে অস্বীকার করে তবে অবশ্যই আমরা অন্য জাতিকে তাদের স্থালাভিষিক্ত করব যারা একে অস্বীকার করবে না অর্থাৎ এর প্রতি ঈমান আনবে ও এর মর্যাদা রক্ষা করবে। ’
সূরা নিসায় বলা হয়েছে :
) إن يشأ يذهِبكم أيّها النّاس و يأت بآخرين و كان الله على ذلك قديرا (
‘ হে মানবকুল! মহান আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের সরিয়ে অন্য কাউকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। বস্তুত আল্লাহর সে ক্ষমতা রয়েছে। ’ 11
আবার সূরা মুহাম্মদে এসেছে :
) و إن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثُمّ لا يكونوا أمثالكم (
‘ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (কোরআন হতে) তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। ’ 12
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাকির (আ.) বলেন , ‘ অন্য জাতি বলতে মাওয়ালীদের (ইরানীদের) কথা বলা হয়েছে। ’
অনুরূপ ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন ,কোরআন থেকে আরবদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এ আয়াত সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তদস্থলে মাওয়ালী অর্থাৎ ইরানীদের প্রতিস্থাপিত করেছেন যারা মন-প্রাণ দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করেছে।13
অবশ্য এখানে আমাদের লক্ষ্য এটি নয় যে ,প্রমাণ করব অন্য জতিটি ইরানীই ছিল বা অন্য কেউ ;বরং এখানে আমরা যেটি বলতে চাই তা হলো ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে আরব-অনারব ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। এ জন্যই আরবরা ইসলামের প্রতি অমনোযোগিতার কারণে পুনঃপুন তিরস্কৃত হয়েছে। ইসলাম আরবদের বুঝাতে চায় তারা ঈমান আনুক বা না আনুক এ দীন অগ্রগতি লাভ করবেই। কারণ ইসলাম এমন দীন নয় যা বিশেষ কোন জাতির জন্য আবির্ভূত হয়েছে।
এখানে অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি ,তা হলো: কোন ধর্মমত ,পথ ও চিন্তা-বিশ্বাস দেশ ,জাতি ও রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া শুধু ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় ;বরং সকল বৃহৎ ধর্ম ও মতের ক্ষেত্রে এটি সত্য। বৃহৎ অনেক ধর্ম ও মতবাদই তার উৎসভূমিতে হয়তো অভিনন্দিত হয়নি ,কিন্তু তার উৎসস্থলের বাইরের দেশ ও জাতির নিকট গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হযরত ঈসা (আ.) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেছেন ,কিন্তু ফিলিস্তিনসহ প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা অধিক। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ,অথচ তারা ভূখণ্ড ও মহাদেশ হিসেবেও হযরত ঈসার জন্মভূমি হতে বিচ্ছিন্ন। এর বিপরীতে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং ইহুদী। খ্রিষ্টানরা থাকলেও খুবই কম। প্রশ্ন হলো আমেরিকা ,ইউরোপের অধিবাসীরা কি খ্রিষ্ট ধর্মকে বিজাতীয় মনে করে ? আমি জানি না ,যে ইউরোপীয়রা অনৈক্যের স্রষ্টা তারা এই জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হিসেবে নিজেদের বিষয়ে কেন এরূপ চিন্তা করে না ,অথচ তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে এ মতবাদ প্রচার করে।
যদি ইসলাম ইরানীদের জন্য বিজাতীয় হয় তবে খ্রিষ্টধর্ম ইউরোপ-আমেরিকার জন্য বিজাতীয় পরিগণিত হবে না কেন ?
কারণটি পরিষ্কার। তারা জানে ও অনুভব করেছে প্রাচ্যের দেশগুলোতে শুধু ইসলাম জীবনের এক স্বাধীন দর্শনে বিশ্বাসী যা এর অনুসারীদের স্বাধীনচেতা হিসেবে গড়ে তোলে। যদি এ ইসলাম না থাকে তবে অন্য কোন কিছুই কাল ও লাল সাম্রাজ্যবাদের চিন্তাকে প্রতিরোধে সক্ষম নয়।
গৌতম বুদ্ধ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও ভারতের বাইরে চীনের শত কোটি লোক এ ধর্ম গ্রহণ করেছে।
যারথুষ্ট্র ধর্ম যদিও ইরানের বাইরে তেমন প্রসার লাভ করেনি ,তদুপরি এর জন্ম স্থল আজারবাইজানে বিস্তৃতি না ঘটে বালখে বিস্তার লাভ করে।
তদ্রূপ মক্কাও রাসূলুল্লাহর জন্মস্থল হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে এর অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে নি ;বরং শত ক্রোশ দূরের মদীনার অধিবাসীরা ইসলামকে আলিঙ্গন করেছিল। ধর্মের কথা বাদ দিলেও বিভিন্ন মতাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে পর্যালোচনা করলেও তাই দেখা যায়। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী মতবাদ হলো কমিউনিজম। কমিউনিজম কার মাথা হতে ,কোথায় উৎপত্তি লাভ করেছে আর কোন্ জাতি তা গ্রহণ করেছে। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এ দু ’ জার্মান বংশোদ্ভূত বর্তমান কমিউনিজমের স্রষ্টা। কার্ল মার্কস তাঁর শেষ জীবনে ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল বৃটেনের অধিবাসীরা অন্যদের হতে পূর্বে কমিউনিজম গ্রহণ করবে। কিন্তু জার্মান বা ইংরেজরা তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেনি ;বরং রাশিয়ার জনগণ তা গ্রহণ করে। কার্ল মার্কস ভাবতে পারেননি ,তাঁর মতবাদ জার্মান বা ইংরেজরা গ্রহণ করবে না ;বরং চীন ও সোভিয়েতরা গ্রহণ করবে।
এই কট্টর জাতীয়তাবাদীদের প্রশ্ন করতে চাই কেন সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের জনগণ দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা তাদের দেশের বাইরে থেকে এসেছে তাকে বিজাতীয় বলে প্রত্যাখ্যান করছে না ? যদি তাদের এ প্রশ্ন করেন তাহলে হেসে বলবে :
‘ আমি মানব সন্তান ,আমায় শয়তান ভেব না
আমার জন্য কখনও তুমি ‘ লা হাওলা ’ পড় না। ’
কোন কোন মতবাদ ও মতাদর্শ তার উৎপত্তি স্থলের বহির্সীমায় অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার বিষয়টি নতুন নয়। ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথমেই এ বিষয়টিকে তার দৃষ্টিতে রেখেছিল।
আরব জাতির অনেকেই কোরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেও ইসলাম অন্যান্য জাতির মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করবে এ বিষয়টি ইসলাম পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী কুরেছিল।14
ইসলামের মানদণ্ড
ইসলাম যে সময় আবির্ভূত হয় সে সময় আরব জাতির মাঝে বংশ. গোত্র ও জাতিভক্তি চরম পর্যায়ে ছিল। তখন আরবদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদ তেমন প্রসার লাভ করে নি ,কারণ আরবরা অন্যান্য জাতির মোকাবিলায় তখনও একক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই আরবদের গোঁড়ামি গোত্রবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা নিজ গোত্র নিয়েই গর্ব করত। কিন্তু ইসলাম তাদের এ গোত্রভক্তির প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় নি ;বরং এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং কোরআন স্পষ্ট বলেছে ,
) يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم (
‘ হে মানব জাতি! আমরা এক পুরুষ ও নারী হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্তি করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও (পরস্পরকে চিনতে পার) ,নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন । ’ 15
এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত ,রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস এবং বিভিন্ন আনারব গোত্র ও জাতির সঙ্গে তাঁর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে।
পরবর্তীতে উমাইয়্যা বংশের ক্ষমতায় আরোহণ এবং তাদের ইসলামবিরোধী নীতির কারণে একদল আরব আরব জাতীয়তার বিষয়টিকে ব্যবহার করে জাতি ও বংশগত গোঁড়ামির অগ্নি প্রজ্বলিত করে। অনারব অন্যান্য জাতি বিশেষত ইরানীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ও পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহকে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদেরকে সমতাকামী ও সাম্যের পক্ষ শক্তি বলে প্রচার করে। তারা আয়াতে ব্যবহৃতشعوبا শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদেরشعوبي বলত। কোন কোন মুফাসসিরের মত এবং ইমাম সাদিক (আ.)-এর হাদীস হতে বোঝা যায় আরবী ‘ কাবায়িল ’ শব্দ এমন একটি একক যা ঐ গোত্রসমূহের জন্য ব্যবহৃত হয় যারা বংশগতভাবে একত্রে বসবাস করে এবংشعوب গোত্র হতে বৃহত্তর একক যারা জাতি হিসেবে একত্রে বসবাস করে। সুতরাং শুয়ুবীরা নিজেদের এ নামে সম্বোধিত করার কারণ স্পষ্টত বোঝা যায় তাদের আন্দোলন আরব জাতীয়তার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ইসলামের মৌলনীতিনির্ভর একটি আন্দোলন ছিল। অন্তত বলা যায় ,এ আন্দোলনের ভিত্তি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও এ আন্দোলনের কিছু সংখ্যক লোক এর গতিকে ইসলাম বিরোধিতার দিকে টানার চেষ্টা করে থাকে তদুপরি পুরো আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী বলা যায় না।16 সকল ঐতিহাসিকই রাসূল (সা.)-এর নিকট হতে এ বাক্যটি পুনঃপুন বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ,
أيّها النّاس كلّكم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربيّ على عجميّ إلّا بالتّقوى
‘ হে মানবকূল! তোমরা সকলেই আদমের সন্তান ,আদম মাটি হতে সৃষ্ট হয়েছে। আরব অনারবের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না একমাত্র তাকওয়া ব্যতীত। ’ 17
মহানবী (সা.) তাঁর এক হাদীসে স্বজাতির পূর্ববর্তীদের নিয়ে গর্ব করার বিষয়টিকে দুর্গন্ধময় বলে অভিহিত করেছেন এবং যে সকল ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তাদেরجُعل অর্থাৎ তেলাপোকার (আরশোলা) সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাদীসটি এরূপ :
ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنّما هم فحم من فحم جهنّم أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان الّتي تدفع بأنفها النّتن
‘ যারা নিজ জাতীয়তা নিয়ে গর্ব করে ,তারা জেনে রাখুক এই গর্ব জাহান্নামের ইন্ধন বৈ কিছু নয় ,(যদি তারা এ কর্ম পরিত্যাগ না করে) আল্লাহর নিকট নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ বহনকারী তেলাপোকা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে। ’ 18
রাসূল (সা.) আবুযার গিফারী ,মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী এবং আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে যেভাবে গ্রহণ করতেন ঠিক তেমনিভাবে সালমান ফরসী ও বেলাল হাবাশীকে গ্রহণ করতেন। কারণ সালমান ফারসী (ইরানী) অন্যদের হতে এতটা অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন ,নবী (সা.)-এর ‘ আহলে বাইত ’ 19 বলে তাঁর নিকট হতে উপাধি লাভ করেছিলেন:سلمان منّا أهل البيت
রাসূল সব সময় লক্ষ্য রাখতেন অন্যদের মধ্যে জাতিভক্তির যে বাড়াবাড়ি রয়েছে তা যেন মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। উহুদের যুদ্ধে একজন ইরানী মুসলিম যুবক শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা আঘাত করে বলল ,خذها و أنا الغلام الفارسيّ ‘ এই তরবারীর আঘাত গ্রহণ কর আমার মত এক ইরানী যুবকের নিকট হতে। ’ নবী (সা.) এ বিষয়টি জাতিগত গোঁড়ামির সৃষ্টি করতে পারে বলে তৎক্ষণাৎ যুবককে বললেন , ‘ কেন তুমি বললে না ,এক আনসার যুবক হতে ? ’ 20 অর্থাৎ ইসলাম যে বিষয়টিকে গর্বের উপকরণ মনে করে তা না করে কেন জাতীয় ও গোত্রীয় বিষয়কে টেনে আনলে ?
নবী (সা.) অন্য এক স্থানে বলেছেন ,
ألا إنّ العربيّة ليست بأب والد و لكنّها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ به حسبه
‘ আরবীয়তা কারো পিতৃত্ব নয় ;বরং একটি ভাষা। তাই যার আমল ও কর্ম অপূর্ণ ,পিতৃত্ব ও বংশীয় পরিচয় তাকে কোথাও পৌঁছাবে না। ’ 21
রাওজায়ে কাফীতে উল্লিখিত হয়েছে: ‘ একদিন সালমান ফারসী মদীনার মসজিদে বসেছিলেন। রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বংশ ও গোত্রীয় পরিচয় নিয়ে সকলে আলোচনা করছিলেন। সকলেই নিজ গোত্র ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলছিলেন ও এর মাধ্যমে নিজেকে সম্মানিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হযরত সালমানের পালা আসলে তাঁকে সকলে নিজ বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলতে বললেন। ইসলামের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত এ মনীষী তখন নিজ গোত্র ,বংশ ও জাতীয় পরিচিতির কোন গর্ব না করে বললেন:
أنا سلمان بن عبد الله “ আমি সালমান ,আল্লাহর এক বান্দার সন্তান ” ,كنت ضالّا فهداني الله عزّ وجلّ بمحمّد “ আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম ,আল্লাহ্ আমাকে মুহাম্মদের মাধ্যমে হেদায়েত করেছেন। ”
كنت عائلا فأغناني الله بمحمد “ আমি দরিদ্র ছিলাম ,তিনি মুহাম্মদের মাধ্যমে আমাকে ধনী করেছেন। ” كنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد “ আমি দাস ছিলাম ,মুহাম্মদের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছেন। এটিই আমার বংশ পরিচয় ” । ’
এমন সময় রাসূল (সা.) সেখানে প্রবেশ করলে হযরত সালমান তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল সমবেত লোকদের (যাদের অধিকাংশই কুরাইশ ছিলেন) উদ্দেশে বললেন ,
يا معشر قريش إنّ حسب الرّجل دينه و مروئته خلقه و أصله عقله
“ হে কুরাইশ! ব্যক্তির গর্ব হলো তার ধর্ম (তার রক্ত ও বংশ নয়) ,তার পৌরুষত্ব হলো তার চরিত্র ও সুন্দর স্বভাব ,তার ভিত্তি হলো তার আক্ল (বুদ্ধিবৃত্তি) ও চিন্তাশক্তি। ” 22
মানুষের মূল তার বংশের ভিত্তিতে নয় ;বরং বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির ভিত্তিতে। ‘ পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত অস্থিমাংস নিয়ে গর্ব করা অপেক্ষা দীন ,চরিত্র ,আক্ল ও অনুধাবন ক্ষমতা নিয়ে গর্ব কর ’ চিন্তা করুন এ হতে উত্তম ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত কথা কি হতে পারে ?
জাতি ও বংশগৌরবের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর উপর্যুপরি তাগিদ মুসলমানদের মনে বিশেষত অনারব মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। এ কারণেই আরব-অনারব সকল মুসলমানই ইসলামকে তাদের স্বকীয় ও নিজস্ব বলে মনে করত। এ জন্যই উমাইয়্যা শাসকদের জাতিগত গোঁড়ামি অনারব মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে পারে নি । তারা জানত খলীফাদের এ সকল কর্মের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এ সকল খলীফার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ছিল-কেন ইসলামী বিধান অনুযায়ী কাজ করা হয় না।
ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ
আমাদের এতক্ষণের আলোচনা হতে কোন বিষয় জাতীয় বা বিজাতীয় হওয়ার মানদণ্ড কি তা স্পষ্ট হলো । আমরা আরো জানলাম রংহীন ,সর্বজনীন ,মানবিক হওয়া এবং বিজাতীয় বা বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার শর্তটি ইসলামের মধ্যে পূর্ণরূপে রয়েছে।
ইসলামের মানদণ্ড যে সার্বিক ,সর্বজনীন ও মানবিক ,বর্ণ ও জাতিগত নয় তাও স্পষ্ট হলো। ইসলাম কখনই কোন বিশেষ জাতি ,গোত্র ও বর্ণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি ;বরং এরূপ সংকীর্ণ গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।
এখন আমরা দেখব ইসলাম দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ করে কি না ? অর্থাৎ ইরান জাতীয়ভাবে ইসলামকে গ্রহণ করেছে কি না ? অন্য ভাবে বললে ইসলাম তার বিষয়বস্তুর উচ্চমান ,মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার কারণে ইরানীদের নিকট গৃহীত হয়েছে ,নাকি এ জাতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ফলে তা মেনে নিতে হয়েছে- যেমনটি অনেকে মনে করেন। অবশ্য আমাদের এ কথার উদ্দেশ্য এটি নয় যে ,আমরা বলতে চাই সকল জাতিরই ইসলাম গ্রহণের পেছনে একমাত্র কারণ এর শিক্ষার সর্বজনীনতা ও সাম্যের ধারণা ;বরং অন্যান্য জাতিসমূহের ইসলাম গ্রহণের পেছনে চিন্তা ও বিশ্বাসগত কারণও যেমন ছিল তেমনি রাজনৈতিক ,সামাজিক ও আচরণগত কারণও ছিল। ইসলামী শিক্ষা একদিকে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক ,অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতিগত ও সহজাত। ইসলামের বিশেষ এক আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে যে কারণে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে নিজ প্রভাবে টেনেছে। সর্বজনীনতা এর বিভিন্ন দিকগুলোর একটি যা তাকে এ আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়েছে । আমরা এখানে আপাতত অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব না। জাতীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে শুধু এ একটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনা রাখব।
প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী হলো ইরানীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। শতাব্দী কাল হতে লক্ষ কোটি ইরানী এ দীনের অনুসারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এ দীনের ওপর জীবন পরিচালনার পর এর সাক্ষ্যের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে।
ইসলামী বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত সৌদি আরব ব্যতীত অন্য কোন দেশের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার ইরান হতে অধিক নেই ,এমনকি যে মিশর নিজেকে ইসলামের কেন্দ্র বলে দাবি করে সেখানেও শতকরা হারে ইরান অপেক্ষা মুসলমান অধিক নয়। তদুপরি উত্তম হলো এ ইরানীদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি বাধ্যবাধকতার কারণে নাকি আন্তরিকতার কারণে ঘটেছে তা পর্যালোচনা করা।
সৌভাগ্যবশত সাম্রাজ্যবাদীদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও ইরান ও ইসলামের ইতিহাস স্পষ্ট। এ বিষয়ে আমরা পাঠকদের সত্যের নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে ইরানের ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলাব ও এ দেশে ইসলামের প্রবেশের সময় হতে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করব।
ইরানীদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা
ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁর হিজরতের কয়েক বছর পর হতে বিভিন্ন দেশের শাসকদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ শুরু করেন এবং তাতে নিজ নবুওয়াতের ঘোষণা ও ইসলামের দাওয়াত লিখে পাঠান। তন্মধ্যে ইরান সম্রাট খসরু পারভেজের উদ্দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠান এবং আমরা অবহিত ,একমাত্র তিনিই রাসূলুল্লাহর পত্রটির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে তা ছিঁড়ে ফেলেন। এটি তৎকালীন পারস্য রাজসভায় অনাচার ও বিশৃঙ্খলার একটি প্রমাণ। অন্য কোন সম্রাট ও শাসক এরূপ কাজ করেননি ;বরং তাঁদের অনেকেই সম্মানের সঙ্গে পত্রের জবাব দান করেন এবং উপঢৌকনও প্রেরণ করেন।
খসরু তার অনুগত ইয়েমেনের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন নবুওয়াতের দাবিকারী এ ব্যক্তি যে তার নামের পূর্বে নিজ নাম লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছে দ্রুততর সময়ে যেন তার নিকট হাজির করা হয়। কিন্তুيريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم و الله متمّ نوره “ যদিও তারা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে ,তদুপরি আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেন । ” তাই খসরুর প্রতিনিধিরা মদীনায় না পৌঁছতেই খসরু তার পুত্রের হাতে নিহত হন এবং রাসূল (সা.) তার প্রতিনিধিদের সম্রাট নিহত হওয়ার খবর দিলে তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু তাঁরা ইয়েমেনে ফিরে এসে জানতে পারেন রাসূল সত্যই বলেছেন। ইয়েমেনের শাসনকর্তাসহ অনেকেই এ ঘটনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়েমেনের অধিবাসী অনেক ইরানীও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিহাস গ্রন্থসমূহ হতে জানা যায় ,সে সময় ইয়েমেনের শাসনভার শত ভাগ ইরানীদের হাতে ছিল এবং প্রচুর ইরানী সেখানে বসবাস করত।
মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচারের প্রভাবে বাহরাইনের অধিবাসী মাজুসী ও অ-মাজুসী ইরানীদের অনেকেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল ,এমনকি বাহরাইনের ইরানী শাসনকর্তাও ইসলাম গ্রহণ করে। মোট কথা ইয়েমেন ও বাহরাইনের অধিবাসী ইরানীরাই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ইরানী।
অবশ্য প্রথম যে ইরানী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন সম্ভবত তিনি হলেন সালমান ফারসী। এই স্বনামধন্য সাহাবীর মর্যাদা এতটা উচ্চে উঠেছিল যে ,রাসূল (সা.) বলেন ,سلمان منّا أهل البيت “ সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ” সালমান শুধু শিয়াদের মধ্যে নন ,এমনকি সুন্নীদের নিকটও প্রথম সারির সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা মদীনায় যিয়ারতে গিয়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন মসজিদে নববীর দেয়াল ঘিরে বিশিষ্ট সাহাবী ও মাজহাবের ইমামদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখানে বিশিষ্ট সাহাবীদের নামের মধ্যে সালমান ফারসীর নামও রয়েছে।
মহানবীর জীবদ্দশায় যে স্বল্প সংখ্যক ইরানী ইসলাম গ্রহণ করে এটি অন্য ইরানীদের জন্য সত্যকে জানার যথেষ্ট সুযোগ এনে দেয় ।
স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি ইরানীদের ইসলাম পরিচিতির পরিবেশ সৃষ্টি করে ও ইরানে ইসলামের বাণী পৌঁছায়। বিশেষত ইরানের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় পরিবেশ তখন এমন অবস্থায় ছিল ,সাধারণ মানুষ নতুন বাণী শোনার জন্য তৃষ্ণার্ত এবং প্রকৃতপক্ষে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। তাই এরূপ নতুন কোন বাণী মানুষের মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ত এবং প্রকৃতভাবেই তারা প্রশ্ন করত এ নতুন ধর্মের ভিত্তি কি ? এর মূল ও শাখাসমূহ-ই বা কি ?
এ পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর ও উমরের খেলাফত শুরু হয়। হযরত আবু বকরের খেলাফতের শেষ দিকে এবং হযরত উমরের খেলাফতকালে মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে সমগ্র ইরানী ভূখণ্ড মুসলমানদের পদানত হয়। এ ভূখণ্ডের লক্ষ লক্ষ ইরানী মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।
আমরা এখানে ইসলামের সেবায় ইরানীদের অবদানের বিষয়ে আজিজুল্লাহ্ আওরাদী (ইরানের ওপর ইসলামের সামরিক বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত) ‘ ইসলামে ইরানীদের অবদান কখন হতে শুরু হয়েছে ’ শিরোনামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা হুবহু তুলে ধরছি:
‘ ইসলামে ইরানীদের অবদান কখন হতে শুরু হয়েছে ? পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি ইরানীদের আগ্রহ ইসলামের আবির্ভাবের সময় হতেই শুরু হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র শরীয়ত ইরানে আসার পূর্বেই ইয়েমেন অধিবাসী ইরানীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সাগ্রহে কোরআনের বিধি পালন শুরু করেছিল ,এমনকি তারা চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামী শরীয়তের প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত এবং ইসলামের পথে নবী (সা.)-এর বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রামেও ব্যাপৃত হয়েছিল।
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইরানীদের অবদানের বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে এবং ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য অনুযায়ী গবেষণাকর্মও চালাতে পারেন। পূর্ব ও পশ্চিমে ইসলামের বিজয় ইতিহাসের পেছনে ইরানের একদল আত্মত্যাগী মুজাহিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য যাঁরা একনিষ্ঠভাবে ইসলামের পথে আত্মোৎসর্গ করে ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির মোকাবিলা ও দমন করেছেন।
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার23 বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত উপমহাদেশ ,পাকিস্তান ,চীন ,মালয়েশিয়া ,ইন্দোনেশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহের মুসলমানরা ইরানী মুসলমানদের নিকট ঋণী এ জন্য যে ,তারা সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সাথে এ অঞ্চলের মানুষদেরকে পবিত্র ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করান।
ইরানীরা উত্তর আফ্রিকা ,ইউরোপ মহাদেশ ,এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিমের দেশগুলোতেও ইসলামের প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছে। বিশেষত খোরাসানসহ পূর্ব ইরানের বাসিন্দারা উমাইয়্যা খেলাফতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তাতে মুসলমানদের ওপর ইসলামের নামে শোষণকারী উমাইয়্যা শাসকদের পতন ঘটে এবং আব্বাসীয়রা খেলাফত লাভ করে। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ও অন্যান্য সকল কর্ম ইরানীদের হাতে ন্যস্ত হয় । বিশেষত খোরাসানীরা পূর্ব ও পশ্চিমের দেশসমূহে আব্বাসীয়দের পক্ষ হতে সকল রাজনৈতিক পদ লাভ করে। খলীফা মামুনের সময় তিনি যখন ইরাকে (বাগদাদে) যান তখন খোরাসানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে অবস্থান নেন। মামুন তাঁর নিজ বংশের অনেক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ ইরানীদের হাতে সোপর্দের সিদ্ধান্ত নেন। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তিনি কিছু বিশিষ্ট ইরানী ব্যক্তিকে মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন যাতে করে তাঁর বিরোধীদের আক্রমণ হতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারেন। বিশেষত আন্দালুসে (স্পেন) তখনও উমাইয়্যা শাসন বলবৎ ছিল ও তাদের আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল বিধায় মামুন এই প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ নেন।
ইরানী মুহাজিরগণ যাদের অধিকাংশই নিশাবুর ,হেরাত ,বালখ ,বুখারা ও ফারগানার অধিবাসী ছিল তাদের অবদান ও ভূমিকা নিয়ে কয়েক খণ্ডের আলাদা বই রচনা সম্ভব। উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী ইরানীদের অবদান ইতিহাস ,সাহিত্য ও হাদীস গবেষণার গ্রন্থসমূহে
বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
আমরা ইরানীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে দু ’ টি পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা আকারে পেশ করছি। প্রথম পর্যায়ে ইরানে ইসলামের প্রবেশের পূর্ব ইতিহাস নিয়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের পর ইরানীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা রাখব।
ইয়েমেনের ইরানীরা
রাসূল (সা.)-এর জন্মের সময় ইয়েমেন ,এডেন ,হাজরা মাউত এবং লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু ইরানীর বসবাস ছিল এবং ইয়েমেনের শাসনভারও ইরানীদের হাতে ছিল। এ বিষয়টি পর্যালোচনার পূর্বে ইরানীদের ইয়েমেনে হিজরতের কারণের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি যাতে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়।
অনুশীরওয়ানের রাজত্বকালে ইথিওপিয়ার (হাবশা) রাজা সমুদ্র পথে ইয়েমেনে আক্রমণ করে এলাকাটি দখল করেন। ইয়েমেনের রাজা সাইফ ইবনে ফি ইয়াযান অনুশীরওয়ানের কাছে হাবাশীদের কবল থেকে ইয়েমেন উদ্ধারের জন্য সাহায্যে চান। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন সাইফ সাত বছর তিসফুনে (মাদায়েন) অপেক্ষার পর অনুশীরওয়ান তাঁকে দরবারে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি দেন । সাইফ অনুশীরওয়ান-এর নিকট হাবাশীদের হাত হতে রাজ্য উদ্ধারের লক্ষ্যে সাহায্য চান ।
অনুশীরওয়ান বলেন , “ আমার ধর্মে নিজ সেনাদলকে প্রতারণা এবং ভিন্ন ধর্মীদের সাহয্যের অনুমতি নেই। ” অতঃপর তিনি রাজকীয় পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন তাঁর জেলখানার মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েদীদের সাইফের সঙ্গে প্রেরণ করবেন যাতে তিনি রাজ্য উদ্ধার করতে পারেন।
সাইফের সঙ্গে প্রেরিত যোদ্ধারা সংখ্যায় ছিল এক হাজারের মত। এই স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধা ত্রিশ হাজার সোনদলের হাবাশী বাহিনীকে পরাস্ত ও তাদের সকলকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। ইরানীদের এ সেনাদলের প্রধানের ডাক নাম ছিল ওয়াহরায। হাবাশীদের পতন ও সাইফ ইবনে ইয়াযানের মৃত্যুর পর ওয়াহরায যাঁর ভাল নাম ছিল খারযাদ তিনি ইয়েমেনের শাসনকর্তা হন ও ইরানী সম্রাটের আনুগত্য ঘোষণা করেন।
ইয়েমেনের ইরানী শাসক বজান ও তাঁর অনুগত ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ
যখন মহানবী (সা.) ইসলাম ধর্মের দাওয়াত শুরু করেন তখন ইয়েমেনে ইরানী শাসক হিসেবে বজান ইবনে সাসান রাজত্ব করছিলেন। তাঁর সময়েই কুরাইশ ও অন্যান্য আরব মুশরিকদের সঙ্গে রাসূলের যুদ্ধ শুরু হয়। বজান খসরু পারভেজের পক্ষ হতে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল হিজায ও তাহামার ওপর নজর রাখা। তাই তিনি রাসূলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খসরুকে নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করতেন।
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ষষ্ঠ হিজরীতে খসরু পারভেজকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি এ আহ্বানে অসন্তুষ্ট হয়ে নবীর পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন ও বজানকে নির্দেশ দেন রাসূলকে বন্দী করে তাঁর নিকট উপস্থিত করার। বজান ববাভেই ও খসরু নামের দু ’ ব্যক্তিকে রাসূলের নিকট এ নির্দেশপত্রসহ প্রেরণ করেন। এটিই ছিল ইরানীদের সঙ্গে রাসূলের প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ।
ইরানী দূতের এরূপ নির্দেশ সম্বলিত পত্রসহ আগমনের সংবাদে মক্কার কুরাইশরা অত্যন্ত খুশী হয় ও বলতে থাকে ,এবার মুহাম্মদের আর রক্ষা নেই। কারণ পারস্য সম্রাট খসরু তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন ও তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছেন। বজানের প্রেরিত দূতরা নবীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন , ‘ আগামীকাল আমি জবাব দেব। ’ পরবর্তী দিন তাঁরা নবীর নিকট জবাবের জন্য আসলে তিনি বললেন , ‘ খসরুর পুত্র শিরাভেই গতরাতে পিতাকে পেট ফেঁড়ে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন তোমাদের সম্রাট নিহত হয়েছেন এবং শীঘ্রই তোমাদের রাজ্য মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। তোমরা ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে বজানকে বল ইসলাম গ্রহণ করতে। যদি সে মুসলমান হয় তাহলে ইয়েমেন পূর্বের মতই তার শাসনাধীন থাকবে। ’ মহানবী (সা.) এ দু ’ ব্যক্তির হাতে কিছু উপঢৌকনও প্রেরণ করলেন। তাঁরা ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে সমগ্র ঘটনা খুলে বললেন। বজান বললেন , ‘ আমরা কয়েক দিন অপেক্ষা করব। যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয় তবে তিনি সত্যই আল্লাহর নবী ও তাঁর পক্ষ হতেই কথা বলেন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নেব। ’ কয়েকদিন পর তিসফুন হতে বার্তাবাহক শিরাভেইয়ের পত্র নিয়ে বজানের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন। সেখানে শিরাভেই তাঁর পিতার হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসীদের তাঁর নেতৃত্বের দিকে আহ্বান করার ও হেজাযে নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়ার। সেই সাথে তাঁর অসন্তুষ্টি ঘটতে পারে এমন কাজ হতে বিরত থাকারও তিনি নির্দেশ দেন। এর পরপরই বজান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ‘ আবনা ’ ও ‘ আহরার ’ নামক ইরানীদের দু ’ টি গোষ্ঠীও তাঁর সঙ্গে ঈমান আনে। এরাই পবিত্র ইসলামী শরীয়ত গ্রহণকারী প্রথম ইরানী মুসলমান।
রাসূল বজানকে পূর্বের ন্যায় ইয়েমেনের শাসক হিসেবে বহাল রাখেন এবং এ দিন হতে তাঁর পক্ষ হতে ইয়েমেনের শাসনকার্য পরিচালনা ও জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। তিনি বিরোধীদের দমন ও ইসলামের প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল তাঁরই পুত্র শাহর ইবনে বজানকে শাসক নিয়োগ করলে তিনিও পিতার ন্যায় ইসলামের প্রচার ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।
আসওয়াদ উনসীর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়া ও তার রিরুদ্ধে ইরানীদের অভিযান
মহানবী (সা.) বিদায় হজ্ব হতে ফিরে আসার কয়েক দিন পরই অত্যধিক ক্লান্তির কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আসওয়াদ উনসী নবীর অসুস্থতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভাবল নবী আর আরোগ্য লাভ করবেন না। তাই সে নবুওয়াতের দাবি করে কিছু লোককে নিজের চারপাশে সমবেত করল। ইয়েমেনী আরবদের এক বড় অংশ তার অনুসারীতে পরিণত হলো।
আসওয়াদ উনসী ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুরতাদ।24 উনসী তার অনুসারী আরব গোত্রদের নিয়ে সানআয় আক্রমণ করে। সানআয় তখন শাহর ইবনে বজান রাসূলের পক্ষ হতে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। তিনি ইসলামের শত্রু ও মিথ্যা দাবিদার আসওয়াদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তাঁর ও আসওয়াদ কায্যাবের সাতশ ’ সৈন্যের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে শাহর ইবনে বজান নিহত হন। তিনি ইসলামের পথে নিহত প্রথম ইরানী শহীদ। আসওয়াদ উনসী শাহর ইবনে বজানকে হত্যার পর তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করে। সে এহসা ,বাহরাইন ,নাজদ ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলসহ ইয়েমেন হতে হাজরা মাউত পর্যন্ত অঞ্চল দখল করে ও সকল ইয়েমেনী গোত্রকে তার আনুগত্য পালনে বাধ্য করে। শুধু কয়েকজন আরব তার নিকট হতে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।
শাহর ইবনে বজানের মৃত্যুর পর ফিরুজ ও দদাভেই ইরানীদের নেতৃত্ব দান শুরু করে। তাঁরা বজান ও শাহর ইবনে বজানের ন্যায় ইসলামের পথে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ইতিমধ্যে রাসূল ও মদীনার মুসলমানগণ জানতে পারেন ইরানীরা ও কিছু আরব ব্যতীত ইয়েমেনের সকল লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আসওয়াদ কায্যাবের অনুসারী হয়েছে।
ইয়েমেনের ইরানীদের উদ্দেশে রাসূলের পত্র
জাশীশ দাইলামী ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী এক ইরানী মুসলমান। তিনি বলেন , ‘ নবী (সা.) আমাদের আসওয়াদ কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্র দদাভেই ,ফিরুয ও জাশীশের নামে প্রেরিত হয়। সেখানে রাসূল তাঁদের গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ দেন ও সকল মুসলমানের নিকট এ বার্তা পৌঁছাতে বলেন। ফিরুয ,দদাভেই ও জাশীশ দাইলামী এ বার্তা সকল ইরানীর নিকট পৌঁছান।
দাইলামী বলেন , “ আমরা জনসাধারণকে আসওয়াদ উনসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পত্র ও বার্তা প্রেরণ শুরু করি। এ সময় আসওয়াদ এ তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারে ও ইরানীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা প্রেরণ করে বলে ,যদি তার সঙ্গে ইরানীরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা তার উত্তরে বলি: আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তদুপরি সে আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি এবং সর্বক্ষণ আমাদের আক্রমণের আশংকায় থাকত। ”
এমতাবস্থায় আমের ইবনে শাহর ,যিজুদ এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছল। এতে আসওয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা দানের আশ্বাস দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি রাসূল (সা.) বিভিন্ন গোত্রের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ করে দদাভেই ,ফিরুয ও দাইলামীকে আসওয়াদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে আমরা জনসাধারণের মধ্যে সমর্থন লাভ করি।
আসওয়াদ উনসীকে হত্যার জন্য ইরানীদের পরিকল্পনা
আসওয়াদ উনসী ইরানীদের ষড়যন্ত্রের ভয় করছিল ও এ ষড়যন্ত্রের পরিণাম অত্যন্ত উত্তেজনাকর অবস্থায় পৌঁছতে পারে তা বুঝতে পারছিল। এ সম্পর্কে দাইলামী বলেন , ‘ শাহর ইবনে বজানের স্ত্রী অযাদ আসওয়াদের অধীনে থেকে আমাদের ভালভাবেই সহযোগিতা করে আসছিলেন এবং তাঁর সাহায্যেই আমরা জয় লাভ করি ও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাই। আমরা অযাদকে বলি: “ আসওয়াদ তোমার স্বামীসহ অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেছে ,তাদের কেউই তার তরবারী হতে রক্ষা পায়নি ” । সে তাদের নারীদেরও দাসীতে পরিণত করেছে। অযাদ আত্মসম্মানবোধসম্পন্না সাহসী নারী ছিলেন। তিনি বললেন: “ আল্লাহর শপথ ,আসওয়াদের মত অন্য কোন শত্রু আমার নেই। সে আল্লাহর কোন অধিকারই রক্ষা করে না। ”
অযাদ বলেন: “ তোমরা তোমাদের লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তসমূহ আমাকে জানাও। আমিও
গৃহাভ্যন্তরের তথ্য তোমাদের জানাব। ” দাইলামী বর্ণনা করেছেন , “ অযাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে আমাদের মধ্যকার সংলাপের বিষয়বস্তু ফিরুয ও দদাভেইকে জানালাম। সে মুহূর্তে এক ব্যক্তি গৃহাভ্যন্তর হতে আমাদের অন্যতম সহযোগী কাইস ইবনে আবদে ইয়াগুছকে আসওয়াদের কক্ষে আহ্বান করল। কাইস কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেও আসওয়াদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ”
তবে কাইস ও আসওয়াদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় এবং কাইস সেখান হতে ফিরে ফিরুয ,দদাভেই ও দাইলামীর নিকট এসে বলে , “ এখন আসওয়াদ কায্যাব এখানে আসবে ,তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। ” কাইস গৃহ হতে বেরিয়ে যাবার পরপরই আসওয়াদ তার সঙ্গীঁসাথীদের নিয়ে আমাদের নিকট আসল। গৃহের নিকট দু ’ শ ’ উট ও গরু ছিল। আসওয়াদ সবগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। অতঃপর চীৎকার করে বলল , “ হে ফিরুয! এ কথা কি সত্য ,তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ও আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করছ ? ” এ কথা বলেই আসওয়াদ তার হাতের অস্ত্র ফিরুযের প্রতি ছুঁড়ে মেরে বলল , “ তোমাকে এই পশুদের মত হত্যা করব। ” ফিরুয বললেন , “ আপনি যা চিন্তা করেছেন তেমনটি নয়। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন সংঘর্ষ নেই ,তাই আপনাকে হত্যার কোন পরিকল্পনাও নেই। কারণ আপনি ইরানীদের জামাতা। আপনার স্ত্রী অযদের সম্মানে আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। তা ছাড়া আপনি নবী হিসেবে দুনিয়া ও আখেরাতের দায়িত্বশীল। ”
আসওয়াদ বলল , “ তোমাকে কসম করে বলতে হবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ও আমার প্রতি প্রতিশ্রুতি পরায়ণ থাকবে। ” ফিরুয তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গৃহের বাইরে আসল। আসওয়াদ কিছু দূরে অগ্রসর হতেই এক ব্যক্তিকে তার সম্পর্কে মন্দ বলতে শুনল। সে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল , “ আগামীকাল ফিরুয ও তার বন্ধুদের হত্যা করব। ” আসওয়াদ পাশ্চাতে তাকিয়ে দেখল ফিরুযও এ কথা শুনে ফেলেছেন।
দাইলামী বলেন , “ ফিরুয আসওয়াদের নিকট হতে ফিরে এসে তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের বলল। আমরা কাইসকে এ আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠালাম। অতঃপর আমরা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম আসওয়াদের স্ত্রী অযাদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করে আমাদের সিদ্ধান্ত তাঁকে জানিয়ে তাঁর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ” দাইলামী বলেন , “ আমি অযাদের নিকট গমন করি এবং তাঁকে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করি। ”
অযাদ বলেন: “ আসওয়াদ নিজের বিষয়ে অত্যন্ত ভীত ও নিজ জীবনের ব্যাপারে কোন আস্থা রাখে না। যখন গৃহে প্রবেশ করে সমগ্র প্রাসাদ ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোতে পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করে যাতে যে কোন ব্যক্তির চলাচলের ওপর নজর রাখতে পারে। তাই সাধারণ কোন লোকের পক্ষে এ প্রাসাদে প্রবেশ অসম্ভব। একমাত্র আসওয়াদের শয়ন কক্ষে কোন প্রহরী নেই। সুতরাং তার শয়নকক্ষেই তোমরা তাকে হত্যা করতে পার। এ কক্ষে একটি তরবারী ও লণ্ঠন ব্যতীত কিছু নেই। ”
দাইলামী বলেন , ‘ আমি প্রাসাদ হতে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অযাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। এমন সময় আসওয়াদ নিজ কক্ষ হতে বের হয়ে আমাকে দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। রাগে তার চক্ষু রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। সে রাগতস্বরে বলল: কোথা হতে এসেছ ,কে তোমাকে এখানে প্রবেশের অধিকার দিল। অতঃপর সে আমার মাথা এমনভাবে চেপে ধরল যে ,আমার প্রাণ বেরিয়ে আসছিল। এ অবস্থা দেখে অযাদ চীৎকার করে বলল: আসওয়াদ ওকে ছেড়ে দাও। যদি অযাদের চীৎকার তার কানে না পৌঁছত তবে সে আমাকে হত্যাই করে ফেলত। ’
অযাদ আসওয়াদকে বললেন: সে আমার চাচাত ভাই ,আমাকে দেখতে এসেছে। তাকে ছেড়ে দাও। আসওয়াদ এ কথা শুনে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি প্রাসাদ হতে বেরিয়ে এলাম ও বন্ধুদের নিকট ঘটনা খুলে বললাম। যখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় রত ছিলাম ঠিক তখনই অযদের পক্ষ হতে এক বার্তাবাহক এসে বলল: তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার সুবর্ণ সুযোগ এখনই ,যে পরিকল্পনা নিয়েছ তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নাও।
আমরা ফিরুযকে বললাম: তুমি দ্রুত অযাদের নিকট যাও। ফিরুয অযাদের নিকট গেলে অযাদ পূর্ণ পরিকল্পনা ফিরুযের নিকট বর্ণনা করেন। ফিরুয বর্ণনা করেছেন , ‘ আমরা প্রাসাদের বাহির হতে আসওয়াদের শয়নকক্ষ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে একটা পথ তৈরি করি ও গর্তের মুখে কয়েক জনকে মোতায়েন করি যাতে তারা প্রয়োজনে এ পথে প্রবেশ করে আসওয়াদকে হত্যায় সহযোগিতা করতে পারে। ’ অতঃপর ফিরুয ঐ কক্ষে অযদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এমন ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ফিরুয ও অযাদের সংলাপের মাঝেই আসওয়াদ কক্ষে প্রবেশ করল। ফিরুযকে দেখা মাত্রই সে প্রচণ্ডভাবে রেগে গেল। অযাদ আসওয়াদকে রাগান্বিত হতে দেখে বলল , ‘ সে আমার নিকটাত্মীয় ,আমাকে দেখতে এসেছে। ’ আসওয়াদ ক্ষুব্ধভাবে ফিরুযকে কক্ষ হতে বের করে প্রাসাদের বাইরে টেনে নিয়ে গেল।
রাত্রিতে ফিরুয ,দদাভেই ও দাইলামী ভূগর্ভস্থ পথে আসওয়াদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। আসওয়াদকে হত্যার প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর তাঁরা বন্ধু ও সমচিন্তার ব্যক্তিদের নিকট তা প্রকাশ করেন। দু ’ টি আরব গোত্র হুমাইর ও হামাদানীদের ঘটনাটি জানানো হলো।
দাইলামী বলেন , ‘ আমরা রাত্রিতে কাজ শুরু করলাম। আসওয়াদের পাশের কক্ষে ভূগর্ভস্থ গোপন পথে পৌঁছলাম । কক্ষটিতে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তার মৃদু আলোতে কক্ষটি আলোকিত হচ্ছিল। ফিরুযের ওপর আমাদের আস্থা ছিল। কারণ তিনি ছিলেন শক্তিশালী ও সাহসী এক পুরুষ। আমরা ফিরুযকে কক্ষের বাইরে লক্ষ্য করতে বললাম। সে সন্তর্পণে আসওয়াদের কক্ষে প্রবেশ করতেই তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি নিশ্চিত হলেন ,আসওয়াদ গভীর ঘুমে রয়েছে। তার স্ত্রী অযাদ কক্ষের এক কোণে বসেছিলেন। ফিরুয আসওয়াদের নিকটবর্তী হতেই সে ঘুম হতে হতচকিয়ে উঠল ও ফিরুযের উদ্দেশ্যে বলল: “ এখানে কি করতে এসেছ ? আমার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন ? ”
ফিরুয বুঝতে পারল তখন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে নির্ঘাত প্রহরীদের হাতে নিহত হবে এবং অযদও প্রাণ হারাবে। তাই অকস্মাৎ আসওয়াদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা চেপে ধরলেন। ক্ষিপ্ত পুরুষ উটের ন্যায় হামলা চালিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করলেন। যখন তিনি কক্ষ হতে বেরিয়ে আসবেন তখন অযাদ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন: “ তুমি কি নিশ্চিত যে ,সে মারা গেছে ? ” ফিরুয বললেন: হ্যাঁ। সে মারা গেছে ,তুমিও তার হাত হতে মুক্তি পেলে। এ বলে তিনি ঐ কক্ষ হতে বেরিয়ে আমাদের নিকট এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। আমরা তার সঙ্গে আসওয়াদের কক্ষে প্রবেশ করলাম। সে তখনও গরুর মত গোঁ গোঁ করছিল। আমরা বড় একটি ছুরি দিয়ে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তার অপবিত্র উপস্থিতি হতে ইয়েমেনকে রক্ষা করলাম।
এ মুহূর্তে আসওয়াদের কক্ষের বাইরে অস্থিরতা ও শোরগোলের সৃষ্টি হলো। প্রহরীরা চারদিক হতে তার কক্ষের বাইরে ভীড় জমালো ও চীৎকার করে কি হয়েছে জানতে চাইলো। অযাদ বললেন , ‘ নতুন কোন বিষয় নয়। নবীর ওপর এখন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। ওহীর কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তখন প্রহরীরা কক্ষের নিকট হতে চলে গেল এবং আমরাও বিপদ হতে রক্ষা পেলাম।
প্রহরীরা চলে গেলে কক্ষে আবার নীরবতা নেমে এল। আমরা চারজন (ফিরুয ,দদাভেই ,জশীশ দাইলামী ও কাইস) এ ঘটনা কিভাবে সকলকে জানান যায় সে চিন্তায় মশগুল হলাম। সিদ্ধান্ত হলো বেরিয়ে গিয়ে চীৎকার করে সকলকে জানাব ,আমরা আসওয়াদকে হত্যা করেছি। ফজরের সময় চীৎকার করে আমরা বিষয়টি ঘোষণা করলাম। সকল কাফের ও মুসলমান এ বড় ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল। দাইলামী বলেন , ‘ অতঃপর আযান দেয়া শুরু করলাম। উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলাম: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। বললাম: আইয়াহ্লাহ্ অর্থাৎ আসওয়াদ কায্যাব মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করত। এ কথা বলে আমরা তার মাথা সবার সামনে ছুঁড়ে ফেললাম। যখন তার প্রাসাদের প্রহরীরা তার নিহত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারল তখন তারা প্রাসাদ লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক মুহূর্তে প্রাসাদের সব কিছু লুটপাট হয়ে গেল। এভাবেই অসংখ্য মানুষের হত্যাকারী এক মিথ্যুকের পতন ও ধ্বংস হলো।
অতঃপর সানআবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলাম ,আসওয়াদ উনসীর কোন অনুসারীকে পেলে যেন বন্দী করে। এর ফলে আসওয়াদের বেশ কিছু সঙ্গী-সাথী বন্দী হলো। আসওয়াদের অনুসারীরা যখন দেখল তাদের সত্তর জন নিখোঁজ হয়েছে তারা আমাদের নিকট পত্র পাঠাল । আমরাও তার জবাব জানিয়ে দিলাম: “ তোমরা আমাদের যা কিছু হস্তগত করেছ তা ফেরত দিলে আমরাও তাদের ছেড়ে দেব। ”
এ প্রস্তাব কার্যকর হলেও আসওয়াদের অনুসারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারল না এবং নতুন কোন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। আমরাও সম্পূর্ণরূপে তাদের অকল্যাণ হতে মুক্তি পেলাম। আসওয়াদের নিহত হওয়ার ঘটনা মদীনাতেও দ্রুত পৌঁছল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন , ‘ যে রাত্রে আসওয়াদ কায্যাব নিহত হয় রাসূল (সা.) ওহীর মাধ্যমে তা জানতে পারেন এবং বলেন: “ উনসী একটি বরকতময় পরিবারের হাতে নিহত হয়েছে। সকলে জানতে চাইল: সে কে ? নবী বললেন: ফিরুয। ”
ইয়েমেন ও পাশ্ববর্তী এলাকায় আসওয়াদের শাসনকাল তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। ফিরুয বর্ণনা করেছেন , ‘ আসওয়াদকে হত্যার কারণে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং তার উত্থানের পূর্বে ইয়েমেনে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল তা ফিরে আসে। মাআয ইবনে জাবাল ইতোপূর্বে রাসূলের পক্ষ হতে ইয়েমেনে জামায়াতের নামাজের ইমাম ছিলেন এবং উনসীর শাসনামলে গৃহবন্দী ছিলেন। তাঁকে ইমামতির জন্য নতুন করে আহ্বান করা হলো । শুধু আসওয়াদের কিছু অনুচর যারা ইয়েমেনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের আক্রমণের ক্ষীণ আশংকা ছাড়া অন্য কোন ভয় আমাদের ছিল না। কিন্তু এরূপ শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রাসূলের মৃত্যু সংবাদ ইয়েমেনে এসে পৌঁছলে পুনরায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।
ইয়েমেনী আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইরানীদের সংগ্রাম
কাইস ইবনে আবদ ইয়াগুস ফিরুয ও অন্যান্য ইরানীদের সঙ্গে আসওয়াদের বিরুদ্ধে কাজ করলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে যায় ও ফিরুযের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সে প্রথমত ফিরুযকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এ কারণে যে ,আসওয়াদকে হত্যার কারণে ইয়েমেনের মানুষের নিকট ফিরুয জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ও তারা তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিত।
কাইস তার শয়তানী চক্রান্তের মাধ্যমে ফিরুযকে অসহায় ও দিশেহারা করে ফেলে। ইয়েমেনের অবস্থা পুনরায় অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে বিশেষত ইরানী মুসলমানদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। তারা ইয়েমেনের মুসলমানদের প্রকৃত নেতা ,সংরক্ষক ও কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাইস তিন ব্যক্তির (যাদের তিনজনই ইরানী) ব্যাপারে ভীত ছিল। তাঁরা হলেন ফিরুয ,দদাভেই ও জাশীশ দাইলামী। যখন কাইস ইবনে আবদ ইয়াগুসের ধর্মত্যাগের কথা মদীনায় পৌঁছল তখন নতুন খেলাফতে অধিষ্ঠিত খলীফা আবু বকর কয়েক ব্যক্তির নামে পত্র লিখে ফিরুয ও ইরানী মুসলমানগণ যাঁরা আসওয়াদ কায্যাবকে হত্যা করেছেন তাদেরকে কাইসের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।
কাইস এ কথা শোনার পর যুল কালাকে পত্র লিখে যেন সে তার সঙ্গীদের নিয়ে ইরানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইয়েমেন হতে বিতাড়িত করে। কিন্তু যুলকালা তার নির্দেশের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কাইস যখন দেখল কেউ তাকে সহযোগিতা করছে না তখন সিদ্ধান্ত নিল প্রতারণা ,ষড়যন্ত্র যে কোন ভাবেই হোক না কেন ফিরুয ,দদাভেই ও দাইলামীকে হত্যা করে ইরানীদের পরাস্ত করার। কাইস ফিরুয ও ইরানীদের কঠিন শত্রু আসওয়াদ কায্যাবের যে সকল সঙ্গী পাহাড় ও মরুভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আহ্বান জানাল এবং ফিরুয ও ইরানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সাহায্য চাইল। এ আহ্বানের পর আসওয়াদ উনসীর সহযোগীরা সানআয় সমবেত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। সানআর অধিবাসীরা কাইস ইবনে আবদে ইয়াগুসের পৃষ্ঠপোষকতা ও গোপন তৎপরতায় এ ঘটনা ঘটেছে জানতে পারল। কিন্তু কাইস ফিরুয ও দদাভেইয়ের নিকট বিপরীত চিত্র তুলে ধরে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল ও পরদিন তাঁদের নিজগৃহে আহারের আমন্ত্রণ জানাল। তাঁরাও কাইসের কথায় বিশ্বাস করে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।
পরদিন প্রথমে দদাভেই কাইসের গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ওঁত পেতে থাকা ব্যক্তিদের হাতে নিহত হলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরুয গৃহদ্বারে পৌঁছামাত্র গৃহের ছাদে দু ’ মহিলাকে বলতে শুনলো: “ এই লোকটিও এখন নিহত হবে যেমনভাবে দদাভেই নিহত হয়েছে। ”
ফিরুয এ কথা শোনামাত্রই বিপরীত দিকে ফিরে দৌড় দিলেন। কাইসের সঙ্গীরা তাঁকে দেখে ধওয়া করল ,কিন্তু ধরতে সক্ষম হলো না।
ফিরুয ঐ এলাকা হতে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জাশীশ দাইলামীকে কাইসের গৃহের দিকে রওয়ানা হতে দেখে তাঁকে এ সম্পর্কে জানাল। পরে তাঁরা দু ’ জন খাউলান পর্বতের দিকে যাত্রা করে ফিরুযের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছলেন। ফিরুয সানআ হতে চলে যাওয়ার পর আসওয়াদ উনসীর অনুসারীরা তাদের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে দিল। ফিরুয খাউলান পর্বতে আশ্রয় নেয়ার পর কিছু সংখ্যক আরব ও ইরানী তাঁর চারপাশে ভীড় জমাল। ফিরুয ইয়েমেনের অবস্থা জানিয়ে মদীনায় খবর পাঠালেন।
অধিকাংশ আরব গোত্রপ্রধান ফিরুযের প্রতি সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নিল। কাইস সকল ইরানীকে যত দ্রুত সম্ভব ইয়েমেন হতে ইরানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। ফিরুয ও দদাভেইয়ের পরিবারবর্গকেও ইয়েমেন ত্যাগ করতে বাধ্য করল।
ফিরুয এ ঘটনা শোনার পর কাইস ইবনে আবদে ইয়াগুসের সঙ্গে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কয়েকজন আরব গোত্রপতির নিকট মুরতাদদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখলেন। তখন আকিল গোত্রের লোকেরা ফিরুয ও ইরানীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসল। তারা কাইসের অশ্ববাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে একদল ইরানীকে তাদের হাত হতে মুক্ত করে।
আক গোত্রের লোকেরাও ফিরুযের সাহায্যে এগিয়ে এসে আরব মুরতাদদের হাত হতে অপর এক দল বন্দী ইরানীকে মুক্ত করে। আকিল ও আক গোত্রের লোকরা সম্মিলিতভাবে কাইসের নেতৃত্বাধীন ধর্মত্যাগীদের ওপর হামলা শুরু করল। ফলে কাইস ইবনে ইয়াগুস পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। সে সাথে আসওয়াদ উনসীর অনুচররাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।
অবশেষে মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়্যার হাতে সে বন্দী হয়। অতঃপর বন্দী অবস্থায় তাকে মদীনায় প্রেরণ করা হয়। খলীফা আবু বকর তাকে দদাভেইকে হত্যার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে , “ আমি তাকে হত্যা করিনি। তাকে গোপনে হত্যা করা হয়েছে। তার হত্যাকারী কে তা অস্পষ্ট। ” খলীফা আবু বকর তার কথাকে মেনে নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। সম্ভবত ইসলামী আইনের এটি সর্বপ্রথম লঙ্ঘন ও পদদলন যেখানে জাতিগত গোঁড়ামি ও অন্ধত্বের ভিত্তিতে অনারবদের ওপর আরবদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল ,যদিও সকলেই জানত কাইস মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল ও ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করত এবং বিপরীত দিকে দদাভেই একজন ইরানী মুসলমান হিসেবে ইসলামের পথে নিহত হয়েছিলেন।
মুসলমানদের হাতে ইরানীদের পতন
ইরানের শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ ও মুসলমানদের হাতে সাসানী সাম্রাজ্যের পতন ইরানীদের চোখে ইসলামের মহত্ত্ব ও বিরাটত্বের প্রকৃত রূপ প্রস্ফুটিত করে তোলে।
সাসানী শাসকবাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধের সময় ইরানের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও চরম গোলযোগ সত্ত্বেও সামরিক দিক হতে ইরান খুবই শক্তিশালী ছিল। সামরিক দিক দিয়ে সে সময় মুসলমানরা ইরানের প্রতিপক্ষ বলেই ধর্তব্য ছিল না। তখন দু ’ পরাশক্তি পৃথিবীতে রাজত্ব করত: পারস্য ও রোম। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো তাদের অধীন অথবা করদরাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতো। সে সময়কার ইরান সৈন্য ,যুদ্ধাস্ত্র ,জনসংখ্যা ,খাদ্য সম্পদ ,সাজ-সরঞ্জাম ও বৈষয়িক সকল দিক হতেই মুসলমানদের থেকে অনেক উন্নত অবস্থানে ছিল। এমনকি মুসলমানরা ইরান ও রোমীয়দের উন্নত যুদ্ধ কৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আরবরা গোত্রযুদ্ধ হতে ব্যাপকতর ,সর্বব্যাপী যুদ্ধে পারদর্শী ছিল না। এ কারণেই তখন কেউই আরব মুসলমানদের হাতে ইরানের পরাজয়ের চিন্তাও করেনি।
এখানে হয়তো কেউ বলতে পারেন মুসলমানদের জয়ের পিছনে তাদের ঈমানী চেতনা ,রিসালতের প্রতি বিশ্বাস ,উজ্জ্বল লক্ষ্যমাত্রা ,জয়ের প্রতি অবিচল আস্থা ,সর্বোপরি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি দৃঢ় ঈমানই মূল ছিল।
অবশ্যই এ বিষয়গুলো মুসলমানদের জয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই। তাদের আত্মত্যাগ ,আত্মবিসর্জনের যে সকল নমুনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের জিহাদকালীন বক্তব্যসমূহে ফুটে উঠেছে। এগুলো তাদের আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি দৃঢ ঈমান ,রাসূল (সা.)-এর রেসালতের প্রতি তাদের আস্থা ,সে সাথে নিজ ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর বহন করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা যাবে না- এ বিশ্বাস তাদের অন্য জাতিসমূহকে সব ধরনের খোদা ভিন্ন অন্য সত্তার উপাসনা হতে মুক্তি দিতে অনুপ্রাণিত করত। তারা একত্ববাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে নিজ দায়িত্ব মনে করত। তারা চাইত অসহায় ও নির্যাতিতকে অত্যাচারীদের হাত হতে মুক্তি দিতে।
বিভিন্ন বক্তব্যে যখন নিজ লক্ষ্য সম্পর্কে তারা বলত তাতে এটি স্পষ্ট হতো যে ,পূর্ণ সচেতনতা সহকারেই তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রকৃতই একটি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। স্বয়ং হযরত আলী (আ.) তাদের এভাবে বর্ণনা করেছেন ,و حملوا بصائرهم على أسيافهم “ এবং তারা তাদের তরবারীগুলোতে তাদের অন্তর্দৃষ্টিসমূহকে বহন করত। ” 25 কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বেতনভোগীরা কাপুরুষোচিতভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোকে আলেকজান্ডার ও মোগলদের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করে থাকে।
মুসলমানদের ঈমানী চেতনা ও আত্মিক শক্তির বিষয়ে কথাগুলো পুরোপুরি ঠিক ,কিন্তু এরূপ মহাবিজয় হস্তগত করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। কারণ স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সাসানী শাসকবর্গের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত রাজত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চি হ্ন করা (বিশেষত যে অবস্থার কথা আমরা উল্লেখ করেছি) এতদসত্ত্বেও অসম্ভব বলে পরিগণিত।26
তৎকালীন ইরানের লোক সংখ্য চৌদ্দ কোটি ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে27 এবং তাদের একটি বড় অংশ সৈনিক ছিল। আপরদিকে ইরান ও রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ষাট হাজারের অধিক ছিল না। যদি ইরানীরা পশ্চাদাপসরণ না করত তবে এ সংখ্যা ইরানের মানুষের মাঝে হারিয়ে যেত ,অথচ এ অল্প সংখ্যক সৈনিকের হাতেই সাসানী রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই ইরানীদের পরাজয়ের পেছনে অন্য কারণও খুঁজতে হবে।
গণ অসন্তোষ
প্রকৃতপক্ষে ইরানে সাসানী শাসকদের পরাজয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শাসন কর্তৃপক্ষের অনৈতিক পথ ও জোর-জবরদস্তিমূলক আচরণের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল ঐতিহাসিক এটি স্বীকার করেছেন ,তৎকালীন সামাজিক ,রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এতটা অধঃপতিত ছিল যে ,প্রায় সকলেই শাসকবর্গের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই অসন্তোষ খসরু পারভেজের পরবর্তী কয়েক বছরের ফলশ্রুতি নয় । কারণ জনগণ যদি কোন শাসন পদ্ধতি ও ধর্মের অনুগত ও আশান্বিত থাকে তাহলে একজন শাসকের প্রতি সাময়িক অসন্তুষ্টির কারণে তারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে পারে না। এর বিপরীতে যদি জাতীয় চেতনা জাগ্রত থাকে তবে বাহ্যিক পরিস্থিতি মন্দ ও প্রতিকূল হলেও জনসাধারণ অভ্যন্তরীণ বিভেদ ভুলে নিজেদের সমন্বিত করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর রয়েছে।
সাধারণত বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূরীভূত হয়ে অধিকতর ঐক্য স্থাপিত হয়। তবে এ শর্তে ,ঐ জনগণের মধ্যে সে দেশের সরকার ও ধর্মের অভ্যন্তর হতে উৎসারিত এক জীবন্ত মানসিকতা থাকতে হবে।
বর্তমান সময়েও লক্ষ্য করলে দেখি আরবদের মাঝে যথেষ্ট অনৈক্য ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও (তদুপরি রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের তৎপরতা) সাধারণ শত্রু ইসরাইলের উপস্থিতির কারণে তারা তাদের শক্তিকে সমন্বিত করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এটি তাদের মধ্যে এক জীবন্ত চেতনার উপস্থিতির প্রমাণ।
তৎকালীন ইরানী সমাজে আশ্চর্যজনক শ্রেণীবিভক্তি ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সকল মন্দ প্রভাব সেখানে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর যারথুষ্ট্রিয়ানদের জন্য স্বতন্ত্র অগ্নিমন্দির ছিল। এখন চিন্তা করুন যদি মুসলমানদের ধনী ও দরিদ্রদের জন্য স্বতন্ত্র মসজিদ হতো তাহলে মানুষের মধ্যে কিরূপ ধারণার জন্ম নিত। তৎকালীন শ্রেণীবিভক্তির বাড়াবাড়ি এতটা বেশি ছিল যে ,এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার রাখত না। ধর্মীয় আইন শ্রমিক ও জুতা মেরামতকারীর (মুচি) সন্তানকে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দিত না। একমাত্র ধর্মীয় গুরু ও রাজসভার সদস্যদের পুত্ররাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত।
যারথুষ্ট্র ধর্ম বাস্তবে যা-ই হয়ে থাক সেসময়ে ধর্মীয় গুরুদের হাতে এতটা বিচ্যুত ও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ,বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ইরানী জাতি অন্তর থেকে এ বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা যদি ইসলাম এ সময় ইরানে না আসত খ্রিষ্টধর্ম ইরানকে দখল করে ফেলত ও যারথুষ্ট্র ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ইরানের সকল চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তি তখন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা যারথুষ্ট্র ছিলেন না এবং ইরানের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সকল কেন্দ্রও তখন খ্রিষ্টানদের হাতে ছিল। যারথুষ্ট্রগণ ভ্রান্তি ও কুসংস্কারপূর্ণ রীতি বিশ্বাস এবং নিরস ধর্মীয় গোঁড়ামির অহংকারে এতটা নিমজ্জিত ছিল যে ,ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। বাস্তবে ইরানে ইসলামের প্রবেশের ফলে যারথুষ্ট্র মতবাদ নয় ;বরং খ্রিষ্টধর্ম সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ সবচেয়ে উপযোগী ভূমিটি তাদের হাতছাড়া হয়েছিল। ইরানের জনসাধারণ ক্ষমতাশীল শাসকবর্গ ,ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও পুরোহিতদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যে কারণে সাধারণ সৈনিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন উৎসাহবোধ করত না ;বরং কখনও কখনও তারা মুসলমানদের সহযোগিতাও করেছে।28
এডওয়ার্ড ব্রাউন তাঁর ‘ তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ’ গ্রন্থের 299 পৃষ্ঠায় বলেছেন ,
‘ ইসলাম ইরানীদের ওপর আরোপিত হয়েছে , নাকি তারা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছে এ সম্পর্কে আলীগড় প্রকৌশল ইসলামী প্রশিক্ষণ বিষয়ক ইনস্টিটিউটের প্রফেসর আর্নল্ড তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে উত্তমরূপে আলোচনা করেছেন। আর্নল্ড যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের অসহনশীলতার উল্লেখ করে বলেছেন: “ পুরোহিতগণ অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের প্রতিই শুধু নয় ; বরং তাঁদের মতাদর্শের বিরোধী আর্য , মনু , মাযদাকী , খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ( Gnostic)সকলের প্রতিই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। এ কারণে তাঁরা অনেকেরই অসন্তোষের কারণ হয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের অত্যাচারী আচরণের কারণে ইরানী জনসাধারণের অনেকের অন্তরেই যারথুষ্ট্র ধর্ম ও এর পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক সম্রাটদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল এবং আরবদের বিজয় অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে ইরানীদের মুক্তির সন্ধিক্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছিল। ”
এডওয়ার্ড ব্রাউন আরও বলেছেন ,
‘ সুনিশ্চিত বলা যায় অধিকাংশ মানুষ যারা ধর্ম পরিবর্তন করেছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে
সন্তুষ্ট চিত্তেই তা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ,কাদেসীয়ায় ইরানীদের পরাজয়ের পর কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী স্থানের দাইলামী বংশের চার হাজার সৈন্য পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে ইসলাম গ্রহণ করে আরবদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা জালুলা দখলে আরব মুসলমানদের সাহায্য করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাসের লক্ষ্যে কুফায় হিজরত করে। অন্যান্য ইরানীও দলে দলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ইসলামে প্রবেশ করে। ’
ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন ইরানী শাসক ,আইন ও ধর্মীয় পরিবেশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সমগ্র ইরানী জাতিকে নতুন এক শাসন ব্যবস্থা ও ধর্ম গ্রহণের উপযোগী করে তুলেছিল। এ কারণেই মুসলমানদের হাতে ইরান বিজিত হওয়ার পর ইরানী জনসাধারণ কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া তো প্রদর্শন করেইনি ;বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামের অগ্রগতির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল।
ডক্টর সাহেবুয যামানী তাঁর ‘ দীবাচেই বার রাহবারী ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,
“ ইরানের সাধারণ মানুষ ইসলামের আকর্ষণীয় শ্রেণীবিদ্বেষহীন বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের প্রতি বিপরীত কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি এ জন্য যে ,এ মতাদর্শে তাদের শতাব্দী কালের আকাক্সিক্ষত বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল যা পাওয়ার জন্য তারা রক্ত ,অশ্রু ,জীবন সব কিছুই বিনিময়ে প্রস্তুত ছিল এবং দীর্ঘকাল তার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল...। ”
ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রথম ইরানী প্রজন্ম নতুন এ ধর্মের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক চাকচিক্যময় স্লোগানের আবর্তে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার কোন নমুনা তো দেখেইনি ;বরং এর বাণীসমূহের প্রতিফলন তারা প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিল। ইসলামের নবী (সা.) বিভিন্ন সময় যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন , “ আমি তোমাদের মতই মানুষ ,কালো হাবাশী দাস এবং সম্ভ্রান্ত কুরাইশের মধ্যে খোদাভীতির মানদণ্ড বহির্ভূত কোন পার্থক্য নেই ” - তেমনি বাস্তবেও তার নমুনা তিনি দেখিয়েছেন। ইরানীরা স্বপ্নে ও কল্পকাহিনীতেও যা ভাবেনি ও অন্তরে যার আকাঙ্ক্ষাই শুধু করেছিল বাস্তবে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে বিশেষত আলী (আ.)-এর মধ্যে তা হতেও আশ্চর্যজনক কিছু লক্ষ্য করেছিল।... বিলুপ্ত সাসানী ও নবীন ইসলামী সভ্যতার বিশ্বদৃষ্টিগত পার্থক্যের এক সংবেদনশীল চিত্র আমরা লক্ষ্য করি আমিরুল মুমিনীন আলীর সিরিয়া অভিযানের সময় যখন তিনি ফোরাত উপকূলের ‘ আনবার ’ শহরের মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদের উদ্দেশ বক্তব্য রাখেন। হযরত আলীর অলংকারপূর্ণ ও উদ্দীপনাময় বক্তব্যসমূহের অন্যতম এটি। সেখানে তিনি পারস্পরিক আচরণের (বিশেষত সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকের আচরণের) যে নমুনা পেশ করেন ,তাতে এ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বের ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য এক আদর্শ রেখে যান...। ইরাকী সেনাদল সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। ফোরাত উপকূলের সুন্দর এ শহরের কৃষকরা আমীরুল মুমিনীনের শুভাগমনকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে তাদের প্রাচীন রীতি (সাসানী আমলের) অনুযায়ী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেনাদল আনবারে পৌঁছলে তারা হর্ষধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ শুরু করল। (তারা সেনাদলের প্রতি উল্লাস ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসল ,কিন্তু হযরত আলীকে অন্যদের হতে পার্থক্য করে চিনতে পারল না।) হযরত আলী শাসকদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপনের এ রীতিকে বিনয়ের সঙ্গে সমালোচনা করে বললেন ,... “ মহান আল্লাহ্ এরূপ আচরণে সন্তুষ্ট নন। মুমিনদের নেতা হিসেবেও এটি আমার নিকট অপছন্দনীয়। স্বাধীনচেতা মানুষরা কখনও নিজেদের এরূপ ছোট ও অপমানিত করে না... চিন্তা করে দেখ বুদ্ধিমানরা নিজেদের কষ্টের বিনিময়ে কখনও কি আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করতে চায় ? ” 29
ডক্টর সাহেবুয যামানী আরো বলেছেন ,
“ ইসলাম নেতৃত্বের দর্শনের মধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন বিষয় সংযুক্ত করেছিল। ইসলাম রাখালকে মেষপালের সংরক্ষণকারী বলে মনে করে। নেকড়ে রূপ রাখালের রক্ত পিপাসা মিটানোর জন্য মেষপাল নয়। তাই ইসলাম বঞ্চিত ও নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তির উদ্দীপনা দিয়েছিল। ”
‘ নেতার জন্য মানুষ ,নাকি মানুষের জন্য নেতা ? ’ প্রাচীন বিশ্ব ও সাসানী আমলের প্রচলিত রাজনীতির বিপক্ষে ইসলাম এ নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। ইরান (পারস্য) ও রোম সাম্র্যজ্যের মধ্যে সাতশ ’ বছরে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে সাধারণ মানুষের নিকট এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। কারণ স্বেচ্ছাচারী এ দু ’ সাম্রাজ্যের রাজনীতি ছিল অভিন্ন। জনসাধারণ নেতার জন্য এবং সাধারণ শ্রেণী অভিজাতের জন্য-এই ছিল নীতি...। (এর বিপরীতে) কুফায় আলী (আ.)-এর সাধারণ গৃহের সভাকক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ও ইরানীদের সার্বক্ষণিক যাতায়াত ছিল। তারা শুধু শুনে নয় ,নিকট হতে আলীর সাদাসিধে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিল। তাই ইরানের নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষের এরূপ আহ্বানে সাড়া দেয়া আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়।
মন্থর ও পর্যায়ক্রমিক অনুপ্রবেশ
যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ইরানীদের ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ,সে সাথে পুরাতন ধর্মের রীতি ও আচার-প্রথা বিলীন হচ্ছিল। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলো ফার্সী সাহিত্য। সময়ের পরিক্রমায় ফার্সী সাহিত্যে ইসলাম ,কোরআন ও হাদীসের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর সাহিত্যিক ,কবি ও লেখকদের অপেক্ষা ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরী শতাব্দীর ইরানী লেখক-কবিদের লেখায় ইসলামের প্রভাব অধিকতর লক্ষণীয়। ফেরদৌসী ও রুদাকীর লেখার সঙ্গে মৌলাভী (জালালুদ্দীন রুমী) ,সা ’ দী ,নেযামী ,হাফিয ও জামীর লেখা তুলনা করলে এটি স্পষ্ট হয়।
মরহুম বদিউজ্জামান ফুরুযন ফার তাঁর ‘ আহাদীসে মাসনাভী ’ গ্রন্থে ফার্সী কবিতায় হাদীসসমূহের ভাবার্থের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রুদাকীর কবিতার উল্লেখ করে বলেন ,
“ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন ইসলামী সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন ইসলাম ধর্ম ইরানের অন্য সকল ধর্মের ওপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। যারথুষ্ট্র ধর্ম ইরানের সকল শহরেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে অবধারিত পরাজয় বরণ করল। ইরানী সংস্কৃতি ইসলামের রঙে দীপ্তিমান হলো। শিক্ষাব্যবস্থা আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলশ্রুতিতে লেখক ও কবিদের লেখায় আরবী শব্দ ও ভাবার্থের প্রচলন বৃদ্ধি পেল। ইসলাম-পূর্ব যুগে গল্প ও কবিতায় এরূপ শব্দ ও প্রবাদের প্রচলন খুবই কম ছিল । এমনকি সাসানী ও গজনভী শাসনামলের প্রথমে দাকীকী ,ফেরদৌসী ও অন্যান্য কবিদের লেখায়ও যারথুষ্ট্র ,আভেস্তা ,বুজার জামহার ও তাঁর প্রজ্ঞার কথা উল্লিখিত হয়েছে যা চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগের উনসুরী ,ফারখী ,মনুচেহরী প্রভৃতি কবির লেখায় আসেনি। ”
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইরানীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলামী নৈতিকতা ,আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার গ্রহণযোগ্যতা ইরানীদের মাঝে তত প্রসার লাভ করেছে।
তাহেরীয়ান ,আলেবুইয়া এবং অন্যান্যরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও কখনও চিন্তা করেননি ‘ আভেস্তা ’ 30 কে নতুনভাবে ইরানে জীবিত করবেন এবং তাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন ;বরং তাঁরা এর বিপরীতে ইসলামের সত্যকে প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করেছেন।
মুসলমানদের হাতে ইরান বিজিত হওয়ার একশ ’ বছর পর ইরানীরা একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী তৈরিতে সক্ষম হয়। শক্তির অপপ্রয়োগ এবং ইসলামের শিক্ষা হতে বিচ্যুত হওয়ার কারণে উমাইয়্যা শাসকবর্গের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাই কিছু গোঁড়া আরব ব্যতীত তাদেরকে কেউই পছন্দ করত না। ইরানীরা তাদের সেনা সাহায্য ও নেতৃত্বে উমাইয়্যাদের নিকট থেকে ক্ষমতা আব্বাসীয়দের হাতে অর্পণে সক্ষম হয়। সে সময় ইরানীরা চাইলে অবশ্যই এক স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তাদের পুরাতন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারত। কারণ পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু সে সময় তারা খেলাফতের বাইরে স্বাধীন শাসন কর্তৃপক্ষের যেমন চিন্তা করত না তেমনি নতুন ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে পুরাতন ধর্মে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাও কখনও পোষণ করত না। কারণ তখনও তারা চিন্তা করত শাসন ক্ষমতা এক পরিবার হতে অপর এক অভিজাত পরিবারে31 স্থানান্তরের মাধ্যমে কোরআন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপনের তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।
কিন্তু বনি আব্বাসের শাসনামলেও আব্বাসীয়দের ভূমিকায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আব্বাসীয় খলীফা হারুনের মৃত্যুর পর হারুনের দু ’ পুত্র মামুন ও আমিনের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে পারস্য সেনাদল তাহের ইবনে হুসাইনের নেতৃত্বে মামুনের পক্ষে আলী ইবনে ঈসার নেতৃত্বের আরব সেনাদলের (আমিনের পক্ষের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাহের ইবনে হুসাইনের জয় প্রমাণ করে ইরানীদের সামরিক শক্তি কতটা দৃঢ় ছিল! তদুপরি ইরানীরা সে সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ইসলামকে প্রত্যাখ্যানের কোন চিন্তা করেনি। ইরানীরা তখনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাসন ক্ষমতার চিন্তা করেছে যখন তারা শত ভাগ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় আরবদের ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছে।
তাই এমনকি যখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে তখনও ইসলাম ধর্মের প্রতি পূর্ণ নিবেদিত ভূমিকা রেখেছে। অধিকাংশ ইরানী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইরানীরা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিক হতে স্বতন্ত্র শাসন ক্ষমতা লাভ করতে শুরু করে। এ সময় পর্যন্ত বেশির ভাগ ইরানী তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম যথা যারথুষ্ট্র ,খ্রিষ্টধর্ম ,সাবেয়ী বা বৌদ্ধ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে যে সকল পর্যটক ইরান সফর করেছেন তাঁদের সফর নামায় উল্লিখিত হয়েছে সে সময় প্রচুর পরিমাণ অগ্নিমন্দির ও গীর্জা দৃষ্টিগোচর হতো। পরবর্তীতে এগুলোর সংখ্যা কমে যায় এবং মসজিদ স্থাপিত হয়।
মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকেই বেশ কিছু ইরানী পরিবারের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের কেউ কেউ চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী হিসেবেই ছিল এবং মুসলিম সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করত। পরবর্তীতে তারা যারথুষ্ট্র ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। বলা হয়ে থাকে ,সাসানী বংশধারার সামান (বালখের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব) যিনি সামানী শাসকবর্গের পূর্বপুরুষ তিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে ,কাবুস শাসকবর্গের পূর্বপুরুষ তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে এবং প্রসিদ্ধ ও দক্ষ কবি মেহইয়র দাইলামী চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইরানের উত্তরাংশ ও তাবারিস্তানের অধিবাসীরা তৃতীয় হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের সঙ্গে পরিচিত ছিল না ও মুসলিম খলীফাদের বিরোধিতা করত। ইরানের কেরমানের অধিবাসীরা উমাইয়্যা শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিল।
‘ আল মাসালিক ওয়াল মামালিক ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন ,ইসতাখরীর যুগে ইরানের অধিকাংশ মানুষ যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিল। বিশিষ্ট মুসলিম ভূগোলবিদ ও ‘ আহসানু তাকাসীম ’ গ্রন্থের লেখক মাকদেসী তাঁর গ্রন্থের 39 ,420 ও 429 পৃষ্ঠায় ইরান ভ্রমণের বর্ণনায় তৎকালীন সময়ের ইরানী যারথুষ্ট্রদের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন ,যারথুষ্ট্রগণ যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল ও মুসলমানদের নিকট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হতে অধিকতর সম্মানিত ছিল। তাঁর বর্ণনা মতে তৎকালীন সময়ে যারথুষ্ট্রদের উৎসবগুলোতে বাজারসমূহ বিভিন্ন রঙে সজ্জিত করা হতো ,নববর্ষ ও শরৎকালীন ফসলী উৎসবে শহরের লোকজন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত।
মাকদেসী তাঁর ‘ আহসানুত তাকাসীম ’ -এর 323 পৃষ্ঠায় ইরানের খোরাসানীদের ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন ,খোরাসানে প্রচুর ইহুদী ছিল ,কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান ও মাজুসীও বসবাস করত। মুসলিম ঐতিহাসিক মাসউদী (মৃত্যু চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধে) যদিও তিনি ইরানী ছিলেন না ,কিন্তু ইরানী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর ইরান সফরের ঘটনা ‘ আত তানবীহ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের 91 ও 92 পৃষ্ঠায় তিনি ইসতাখরের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট সাসানী আমলের ‘ ইতিহাস সমগ্র ’ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ গ্রন্থ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানকার কিছু যারথুষ্ট্র পুরোহিতের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে বিশিষ্ট যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের বিশেষ অবস্থান ছিল। মাসউদী তাঁর ‘ মুরুজুয যাহাব ’ গ্রন্থের 382 পৃষ্ঠায় ‘ ফি যিকরিল আখবার আজ বুয়ুতিন নিরান ওয়া গাইরাহা ’ শিরোনামের আলোচনায় যারথুষ্ট্রদের অগ্নিমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। তিনি ‘ দরাব জারদের ’ অগ্নিমন্দিরের বিষয়ে বলেছেন ,332 হিজরীতেও এ অগ্নিমন্দিরে মাজুসিগণ উপাসনার জন্য দলে দলে আসত। অন্য কোন অগ্নিমন্দিরের অগ্নির এত সম্মান ছিল না।
উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করে ইরানীরা পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে। বিশেষত ইরানীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান লাভের পরই ইসলাম যারথুষ্ট্র ধর্মের ওপর পূর্ণ বিজয় অর্জন করে। আশ্চর্যজনক যে ,ইরানের যারথুষ্ট্ররা ইরানীদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভের সময়কাল অপেক্ষা আরব শাসনামলে অধিকতর সম্মানিত ও স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে পারত। ইরানীরা যত বেশি ইসলাম গ্রহণ করেছিল যারথুষ্ট্রগণ তত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছিল ও তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ছিল। আরবদের অপেক্ষা ইরানী মুসলমানরা যারথুষ্ট্র মতবাদের প্রতি অধিকতর অসহিষ্ণু ছিল। ইরানী নও মুসলিমদের এই অসহিষ্ণুতার কারণেই যারথুষ্ট্রদের অনেকেই ভারতে চলে যায়। তারাই ভারতের সংখ্যালঘু পারসিক।
মিস্টার ফ্রয় তাঁর ‘ মিরাসে বসতনীয়ে ইরান ’ 32 গ্রন্থের 396 পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করছি না । তিনি বলেছেন ,
‘ বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক সূত্র হতে জানা যায় পারস্যের ইসতাখরে যারথুষ্ট্রদের সর্ববৃহৎ দু ’ টি কেন্দ্রের একটি (অপরটি আজারবাইজানের ‘ শীজে ’ ছিল) মুসলিম শাসনামলেও পূর্বের মত জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় ছিল। দিন দিন যারথুষ্ট্রদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় অগ্নিমন্দিরগুলোর জৌলুস কমতে শুরু করল। এতদসত্ত্বেও এক হাজার খ্রিষ্টাব্দ (400 হিজরী শতাব্দী) পর্যন্ত পারস্যের অধিবাসীরা যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রতি অনুগত ছিল। একাদশ খ্রিষ্ট শতকে সালজুকীদের রাজ্য বিস্তারের সময় পর্যন্ত পারস্যের বিরাট অংশ যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিল।
এ শতাব্দীতে ইরানের কযেরুন শহরে মুসলমান ও যারথুষ্ট্রদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় । বিশিষ্ট সুফী আবু ইসাহাক ইবরাহীম ইবনে শাহরিয়ার কযেরুনীর (মৃত্যু 1034 খ্রিষ্টাব্দ) সময়কালে এ ঘটনা ঘটে। যারথুষ্ট্রদের অনেকেই এ সুফী সাধকের দিক-নির্দেশনায় ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ‘ মু ’ জামুল বুলদান ’ ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ হতে জানা যায় পারস্যে তখনও যারথুষ্ট্ররা শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলে বুইয়াদের সময় কযেরুনের শাসক ছিলেন খুরশীদ নামক এক যারথুষ্ট্র ব্যক্তি। পারস্যের সিরাজের শাসনকর্তা বুয়াইহী সিরাজের দরবারে তাঁর বিশেষ অবস্থান ছিল। বুয়াইহী সিরাজ খুরশীদের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠান আবু ইসহাককে যেন তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। কেন সে মুসলমান করার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে তার জবাবদিহিতার জন্য তিনি এ নির্দেশ দেন। মুসলমান ও যারথুষ্ট্র উভয়েই ইরানী বংশোদ্ভূত ছিল। তাদের মধ্যে খ্রিষ্টান ও ইহুদীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। ’
তিনি 399 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ,
“ ইসলামী চিন্তা দিন দিন যত প্রসার লাভ করতে লাগল সুফী ও শিয়া মতাদর্শ তত দীপ্তি অর্জন করল। ফলে সংকীর্ণ ও অনুন্নত যারথুষ্ট্র চিন্তাধারা ইরানীদের মাঝ হতে হারিয়ে যেতে লাগল। ইরানের দাইলামী শাসকরা শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করলে ইরানের পশ্চিম অংশ ইরানীদের হস্তগত হয়। 334 হিজরীতে বাগদাদ ইরানীদের পদানত হয়। তখনই যারথুষ্ট্র ধর্ম বিলুপ্তির পথে পা দেয়। আলেবুইয়া রাষ্ট্রীয় নীতিতে ইসলাম ও আরবী ভাষাকে মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণ এ দু ’ টি বিষয় আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছিল এবং যারথুষ্ট্র ধর্ম নিজস্ব গণ্ডীতে সীমিত হয়ে পড়েছিল। আলেবুইয়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহনশীল অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে সুন্নী মতাবলম্বী খলীফা বিভিন্ন প্রদেশে সুন্নী শাসকবর্গকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আলেবুইয়া বিশেষভাবে হযরত আলীর পরিবারের প্রতি দুর্বল ছিলেন ও এই ধারার আরবীয় সংস্কৃতির প্রচলনে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যতম আলেবুইয়া শাসক আজদুদ্দৌলা 344 হিজরীতে (955 খ্রিষ্টাব্দে) জামশীদের সিংহাসনে উৎকীর্ণ ফার্সী বাক্যগুলোকে আরবীতে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। ’
কি কারণে আরবদের শাসনকাল শেষ হওয়ার পরও ইরানের মানুষ ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছিল ? ইসলামের আকর্ষণ ও ইরানীদের মানসিকতার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ভিন্ন অন্য কিছু এর কারণ হতে পারে কি ?
ইরানের স্বাধীন শাসকবর্গ যাঁরা রাজনৈতিকভাবে আরবদেরকে শত্রু ও প্রতিপক্ষ মনে করতেন তাঁরা বরং ইসলামের প্রচার ,প্রসার ও দীনী আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবদের হতে অধিক নিবেদিত ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁরা আলেমদের অধিকতর সহযোগিতা করতেন।
গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে ইরানীরা ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানের বিষয়ে যে অবদান রেখেছে ইসলামের দৃষ্টিতে তা নজীর বিহীন। এমনকি ব্রিটিশ সার্জন ম্যালকম যিনি প্রথম দু ’ শতাব্দীকে ‘ নীরব দু ’ শতাব্দী ’ বলেছেন তাঁর দৃষ্টিতেও অন্য কোন জাতি ইরানীদের ন্যায় এত উদ্দীপনা ও ভালবাসা নিয়ে ইসলামের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখেনি। ইসলামের আগমনের পূর্বেও ইরানীরা কোন সময়ে এত নিবেদিত ভূমিকা রাখেনি।
ইরানীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর তাদের প্রাচীন ধর্ম ও আচার ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারত ,কিন্তু তারা তা করেনি ;বরং তা প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের দিকে অধিকতর নিবেদিত হয়েছে। কেন ? কারণ ইসলামকে তারা তাদের চিন্তা ও প্রকৃতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হিসেবে পেয়েছে। তাই কখনই যে ধর্ম ও আচার তাদের দীর্ঘ দিনের আত্মিক কষ্টের কারণ ছিল তা পুনরুজ্জীবিত করার কল্পনাও করত না। চৌদ্দ শতাব্দীর ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। এখন যদি মাঝে মাঝে কিছু হাতে গোনা আত্মপরিচয়হীন ব্যক্তি প্রাচীন আচার ও ধর্মরীতি পুনরুজ্জীবনের কথা বলে তা ইরানী জাতির কথা বলে ধরা যায় না।
পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ,ইরানীরা বারবার প্রমাণ করেছে ইসলাম তাদের প্রকৃতির সাথে আরবদের হতে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। এর প্রমাণ হলো গত চৌদ্দ শতাব্দীব্যাপী ইসলামের জন্য তাদের নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকা। এই অবদান গভীর ঈমান ও ইসলাম প্রসূত ছিল । মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহযোগিতায় আমরা পরবর্তী আলোচনাতে ইরানীদের কিছু মূল্যবান অবদানের উল্লেখ করব। এতে প্রমাণিত হবে ইরানী মুসলমানগণ অন্তরের অন্তস্তল হতে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল এবং এ ধর্মের বিধানকে তারা চিন্তা ও বিবেকের প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। এ সত্য আমাদের রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি বলেছিলেন , ‘ আল্লাহর শপথ ,আমি এমন দিন দেখতে পাচ্ছি সে দিন এই ইরানীরা ,যাদের সঙ্গে তোমরা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছ তারা তোমাদের মুসলমান বানানোর জন্য যুদ্ধ করবে। ’
ইরানে দু ’ টি ধারার উপস্থিতির ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে অনেকে ভুল অথবা বাড়াবড়ি করেছেন এবং এ দু ’ ধারাকে ইসলামের বিরুদ্ধে বা অন্তত আরবদের বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে দেখেছে। প্রথমত ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবন। দ্বিতীয়ত শিয়া মাযহাব। তাই এ দু ’ টি বিষয় যার একটি আমাদের জাতীয় ভাষা অন্যটি রাষ্ট্রীয় মাযহাব-এ সম্পর্কে বিশেষ গবেষণামূলক আলোচনা রাখা প্রয়োজন মনে করছি।
ফার্সী ভাষা
ইসলাম ধর্ম ইরানীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে- এর যুক্তি হিসেবে অনেকেই বলে থাকেন ,ইরানীরা তাদের ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করেছে ,আরবী ভাষার মাঝে একে বিলুপ্ত হতে দেয়নি।
আশ্চর্যজনক এ যুক্তি! তবে কি ইসলাম গ্রহণের অপরিহার্যতা হলো বিশেষ ভাষার ব্যক্তিরা তাদের স্বভাষা ত্যাগ করে আরবী ভাষায় কথা বলা শুরু করবে! আপনারা কোরআন ,হাদীস বা ইসলামী বিধানের কোথায় এরূপ বিষয় পেয়েছেন ?
ইসলাম ধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম যেখানে ভাষা মৌল বিষয় নয়। তাই ইরানীরা কখনও
চিন্তা করে নি ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবন ইসলামের মৌলনীতির পরিপন্থী।
যদি ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবন ইসলামের বিরোধিতার জন্য হতো তবে কেন ইরানিগণ আরবী ভাষার শব্দ গঠন (صرف ) ,বাক্য গঠন (نحو ) ,ব্যাকরণগত বিধি এবং অলংকারশাস্ত্র প্রণয়ন ও ভাষার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধিতে এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে ? আরবগণ কখনই আরবী ভাষায় ইরানীদের ন্যায় অবদান রাখে নি। যদি আরবী ভাষা ও ইসলামের বিরোধিতার লক্ষ্যেই ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়ে থাকে তবে ইরানীরা এত আরবী অভিধান রচনা ,আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্র চর্চা না করে ফার্সী অভিধান রচনা ও ফার্সী ব্যাকরণ বিধি প্রণয়নে মনোনিবেশ করত। তা না করলেও অন্তত আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে ভূমিকা রাখা হতে বিরত থাকত। তাই ইরানীদের ফার্সী ভাষার প্রতি আগ্রহ ইসলাম ও আরবী ভাষার প্রতি বিদ্বেষের কারণে ছিল না এবং আরবীকে তারা বিজাতীয় ভাষা হিসেবেও মনে করত না। তারা আরবীকে ইসলামের ভাষা হিসেবে জানত ,আরবদের ভাষা হিসেবে নয়। যেহেতু ইসলাম সকল মুসলমানের ,তাই আরবী ভাষাকেও তারা সকল মুসলমানের ভাষা মনে করত।
মূল কথা হলো যদি ফার্সী ,তুর্কী ,ইংরেজি ,ফরাসী ,জার্মানী ও অন্যান্য ভাষা কোন জাতি বা গোত্রের হয়ে থাকে তবে আরবী ভাষা শুধু একটি মাত্র গ্রন্থের ভাষা। ফার্সী ভাষা একটি জাতির সম্পদ ;অসংখ্য মানুষ এ ভাষার জীবন ও টিকে থাকার পেছনে ভূমিকা রেখেছে। যদি তারা এ ভূমিকা না রাখত ,তা হলেও এ ভাষা পৃথিবীতে থাকত। ফার্সী ভাষা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থের ভাষাই শুধু নয় ,শুধু ফেরদৌসী ,রুদাকী ,নেজামী ,সা ’ দী ,মৌলাভী রুমী ,হাফিযের ভাষা নয় ;বরং সকলের ভাষা ,কিন্তু আরবী কেবল একটি গ্রন্থের ভাষা। আর তা হলো কোরআন। কোরআন এ ভাষার জীবনদাতা ,সংরক্ষক ও অমরত্বদানকারী। এ ভাষার যত কীর্তি ও ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছে তা কোরআনের আলোক রশ্মির বিকিরণ হতেই এবং এ গ্রন্থের কারণেই। এ ভাষার যত বিধিবিধান তৈরি হয়েছে তাও এ গ্রন্থের কারণেই ।
যে কেউ এ ভাষায় অবদান রেখেছেন ,গ্রন্থ রচনা করেছেন কোরআনের স্বার্থেই তা করেছেন। দর্শন ,এরফান ,ইতিহাস ,চিকিৎসা ,গণিতশাস্ত্র ,আইনশাস্ত্র ও অন্য যে সকল গ্রন্থ এ ভাষায় অনূদিত হয়েছে তা কোরআনের সেবার মানসিকতাতেই হয়েছে। তাই সত্য হলো আরবী ভাষা কোন জাতির নয় ;বরং একটি গ্রন্থের ভাষা।
যদি বিশেষ ব্যক্তিগণ এ ভাষাকে তাঁদের মাতৃভাষা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দিতেন তা এ জন্য যে ,তাঁরা এ ভাষাকে বিশেষ কোন জাতির বলে মনে করতেন না ;বরং তাঁদের ধর্মের ভাষা বলে মনে করতেন। তাই এ ভাষাকে অগ্রাধিকার দানকে নিজ জাতি ও জাতীয়তার প্রতি অসম্মান বলে মনে করতেন না। অনারবরা আরবীকে তাদের ধর্মীয় ভাষা এবং মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে জানত।
মাওলানা রুমী তাঁর ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ কয়েকটি কবিতা আরবীতে লিখেছেন। যেমন :
أقتلوني أقتلوني يا ثقات |
إنّ في قتلي حيوة في حيوة ا |
“ আমাকে হত্যা কর ,হত্যা কর হে বিশ্বাসিগণ!
আমাকে হত্যার মাঝেই জীবনের জীবন। ”
অতঃপর ফার্সী কবিতায় বলছেন ,
‘ ফার্সী বল ,যদিও আরবী আরো মধুর ,
শত ভাষা হতে অধিক ভালবাসার। ’
মাওলানা তাঁর এ কবিতায় তাঁর মাতৃভাষা ফার্সীর ওপর আরবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ আরবী ইসলাম ও কোরআনের ভাষা। সা ’ দী তাঁর ‘ গুলিস্তান ’ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তুর্কিস্তানের কাশগর নামক স্থানের এক যুবকের সঙ্গে কথোপকথনের কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ গল্পে যুবকটি ‘ যামাখশারী ’ রচিত আরবী ব্যাকরণ পড়ত। তার ভাষায় হাফিয বলছেন ,ফার্সী সাধারণ মানুষের ভাষা ,কিন্তু আরবী জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাষা। হাফিয তাঁর এক প্রসিদ্ধ গীতি কবিতায় বলেছেন ,
‘ যেহেতু বন্ধুর নিকট শৈল্পিকতা অশোভনীয়
তাই রয়েছে নিশ্চুপ ,যদিও মুখ আরবীতে পূর্ণ। ’
মরহুম কাযভীনী তাঁর ‘ বিসত মাকালেহ্ ’ 33 গ্রন্থে বলেছেন , ‘ নির্বুদ্ধিতার জালে (সাম্রাজ্যবাদীদের নীলনকশায়) বন্দী এক মাকড়সা সব সময় হাফিযের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ তিনি আরবী ভাষাকে শিল্প মনে করেছেন। ’
ইসলাম বিশেষ কোন জাতি বা দলের প্রতি এ উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দেয় না যে ,তারা আরবীকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে মাতৃভাষাকে বর্জন করবে।
মাসউদী তাঁর ‘ আত তানবীহ্ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন , ‘ যায়েদ ইবনে সাবিত রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে ফার্সী ,রোমীয় ,কিবতী ও হাবাশী ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তিনি রাসূলের অনুবাদকের ভূমিকা পালন করতেন। ’ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ,আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) কখনও কখনও ফার্সী ভাষায় কথা বলেছেন।
সার্বিকভাবে যে ধর্ম ও আইন সকল মানুষের জন্য তা বিশেষ কোন ভাষার ওপর নির্ভর করতে পারে না। তাই যে কোন জাতি কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাদের ভাষা ও বর্ণের মাধ্যমে-যা তাদের চিন্তা ,রুচি ও চেতনার প্রকাশস্থল-ঐ ধর্ম ও আইনের অনুসরণ করতে পারে।
সুতরাং ইসলাম গ্রহণের পরও যদি ইরানীরা ফার্সী ভাষায় কথা বলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এ দু ’ টি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত নয়। তাই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের একে ইরানীদের ইসলাম অপছন্দ করার যুক্তি হিসেবে মনে করার কোন অবকাশ নেই।
বস্তুত ভাষার বৈচিত্র্য ইসলাম গ্রহণের প্রতিবন্ধক তো নয়ই ;বরং তা এ ধর্মের অগ্রগতির উপকরণ। কারণ প্রতিটি ভাষা তার নিজস্ব বৈচিত্র্য ,সৌন্দর্য ও যোগ্যতা নিয়ে পৃথকভাবে ইসলামের পেছনে অবদান রাখার সুযোগ পায়। ইসলামের এটি সফলতা যে ,বিভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করেছে এবং নিজ ভাষা ,সংস্কৃতি ও রুচি অনুযায়ী এর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।
যদি ফার্সী ভাষা বিলুপ্ত হতো তবে আমরা আজ ইসলামের অনেক মহামূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম ,যেমন মাসনাভী ,গুলিস্তান ,দিওয়ানে হাফিয ও নিজামী এবং এরূপ শত সহস্র স্মরণীয় নিদর্শন যার সর্বত্র ইসলাম ও কোরআনের জ্ঞান তরঙ্গায়িত তা আমরা পেতাম না এবং ইসলামের সঙ্গে ফার্সী ভাষার চিরন্তন এক বন্ধনও রচিত হতো না।
কত ভাল হতো যদি মুসলমানদের মধ্যে ফার্সীর ন্যায় আরো কয়েকটি ভাষা নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের জন্য অবদান রাখত!
(তা ছাড়া দেখতে হবে) ফার্সী ভাষা কি কারণে কাদের দ্বারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ? প্রকৃতপক্ষে ইরানীরা কি ফার্সী ভাষাকে জীবন্ত করেছে নাকি অ-ইরানীরা এ ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রেখেছে ? এর পেছনে উদ্দীপক কি ছিল ? ইরানী জাতীয় চেতনা নাকি এ চেতনার সাথে সম্পর্কহীন রাজনৈতিক কোন কারণ ?
ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে ,আরব জাতির আব্বাসীয় খলীফারা ইরানীদের চেয়ে অধিক ফার্সীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এর পেছনে তাঁদের লক্ষ্য ছিল বনি উমাইয়্যার আরব জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার বিরুদ্ধে অনারবীয় রাজনৈতিক চিন্তার জাগরণ সৃষ্টি ,এ জন্যই আরব জাতীয়তাবাদীরা বনি উমাইয়্যাদের প্রশংসা ও বনি আব্বাসের কম-বেশি সমালোচনা করে থাকে।
বনি আব্বাস বনি উমাইয়্যার সঙ্গে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তাদের আরব জাতীয়তাবাদ এবং আরব ও অনারবের মধ্যে পার্থক্যের নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ লক্ষ্যে তারা অনারব জাতিগুলোর স্বকীয় উপাদানসমূহের গুরুত্ব আরোপ করত এবং প্রচেষ্টা চালাত যাতে করে তারা আরবদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়।
বনি আব্বাসের অন্যতম ভিত্তিদাতা ইবরাহীম ইমাম আবু মুসলিম খোরাসানীকে পত্র লিখে নির্দেশ দেন , “ এমন কাজ কর যাতে কোন ইরানীই আরবী ভাষায় কথা না বলে ,যদি কাউকে আরবীতে কথা বলতে দেখ তবে তাকে শাস্তি দাও। ”
মি. ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের 387 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ,
“ আমার বিশ্বাস স্বয়ং আরবগণ প্রাচ্যে ফার্সী ভাষার প্রসারে সাহায্য করে। এ বিষয়টি এ অঞ্চলের সুগদী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বিলুপ্তি ঘটায়। ”
‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে :
“ একশ ’ সত্তর হিজরীতে মামুন খোরাসানে এলে ঐ এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই প্রশংসা ও সেবার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। আবুল আব্বাস মুরুজী যিনি আরবী ও দারী (ফার্সী ভাষার একটি রূপ) উভয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষার মিশ্রণে একটি প্রশংসা-কবিতা ও বক্তব্য রাখেন যা মামুনের বেশ পছন্দ হয়। তিনি খুশী হয়ে তাঁকে এক হাজার দিনার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন এবং তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের সম্মান লাভ করেন। এরপর হতে ফার্সী ভাষীরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে ;পূর্বে এরূপ বিন্যাস প্রত্যাখ্যাত হলেও এ সময় হতে প্রচলন লাভ করে।
অন্যদিকে আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করি অনেক ইরানী মুসলমানই ফার্সীর প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করতেন না ,যেমন তাহেরীয়ান ,দাইয়ালামা ও সামানিগণ নিখাঁদ ইরানী হওয়া সত্ত্বেও ফার্সী ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের কোন প্রচেষ্টা নেননি ,অথচ অ-ইরানী গজনভী শাসকগণ ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।
মি. ফ্রয় তাঁর ‘ প্রাচীন ইরানী সভ্যতার উত্তরাধিকার ’ নামক গ্রন্থের 403 পৃষ্ঠায় বলেছেন ,
“ আমরা জানি তাহেরীয়ান তাঁর দরবারে আরবী ভাষা প্রচলনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পরবর্তীরা বিশেষ আরবীর প্রচলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ”
পূর্বে দাইলামীদের আরবী ভাষার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে এই প্রাচ্যবিদের উদ্ধৃতি আমরা উল্লেখ করেছি।
ইরানের অন্যতম রাজকীয় শাসকগোষ্ঠী সামানিগণ প্রসিদ্ধ সামানী সাম্রাজ্যের সেনাপতি বাহরাম চুবিনের বংশধর ছিলেন। এ বংশের শাসকরা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ছিলেন এবং ইসলাম ও ইসলামী বিধিবিধানের প্রতি আসক্ত ছিলেন।
‘ আহদীসে মাসনাভী ’ গ্রন্থের ভূমিকায় ইসলামী বিশ্বের সাহিত্য ও জ্ঞানের সকল পরিমণ্ডলে নবী (সা.)-এর হাদীসের অনুপ্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে আনাসাবে সামআনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে :
“ অধিকাংশ রাজকীয় ব্যক্তিত্ব যাঁরা লেখক ও কবিদের উৎসাহিত করতেন তাঁরা নিজেরা হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। যেমন সামানী শাসক আমীর আহমাদ ইবনে আসাদ ইবনে সামান (মৃত্যু 250 হিজরী) ও তাঁর কয়েক পুত্র আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে আহমদ (মৃত্যু 295 হিজরী) ,আবুল হাসান নাছর ইবনে আহমাদ (মৃত্যু 279 হিজরী) এবং আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে অহমাদ (মৃত্যু 301 হিজরী) হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। সামানী রাজসভার উজীর আবুল ফাজল মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ বালআমী (মৃত্যু 319 হিজরী)ও হাদীস বর্ণনা করতেন। সামানী রাজসভার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমির ইবরাহীম ইবনে আবি ইমরান সিমজুর ও তাঁর পুত্র আবুল হাসান নাসেরুদ্দৌলা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হাদীসের রাবী ছিলেন। খোরাসানের আমীর আবু আলী মুজাফ্ফর ইবনে আবুল হাসান (নিহত 388 হিজরীর রজব মাস)ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। মুসতাদরাক গ্রন্থের লেখক আবু আবদুল্লাহ্ হাকিম ইবনুল বাই (মৃত্যু 405 হিজরী) তাঁর নিকট হতে হাদীস শুনতেন।
সামানী শাসকরা ইরানী বংশাদ্ভূত হলেও কখনও তাঁদের রাজদরবারে ফার্সীর প্রচলন ছিল না এবং তাঁরা একে উৎসাহিত করতেন না। তাঁদের মন্ত্রী ও সভাসদরাও ফার্সীর প্রতি কোন আগ্রহ দেখাতেন না। দাইলামী ইরানী শিয়ারাও এরূপ ছিল।
এর বিপরীতে তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনভী গোঁড়া সুন্নী শাসকদের দরবারে ফার্সী ভাষার চর্চা হতো। এ সব উদাহরণ প্রমাণ করে জাতিগত গোঁড়ামি নয় ;বরং অন্য কোন উপাদান ও কারণ ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।
সাফারিগণ ফার্সীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এর কারণ আরবী ভাষার প্রতি বিদ্বেষ ,নাকি ফার্সীর গোঁড়ামি-এ সম্পর্কে মিস্টার ফ্রয় বলেন ,
“ সাফারী বংশের শাসকদের রাজসভার কবিরা আধুনিক ফার্সীর প্রচলন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। কারণ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব আরবী জানতেন না। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি চাইতেন কবিতা এমন ভাষায় পড়া হোক যা তিনি বুঝতে পারেন। ”
সুতরাং সাফারীদের ফার্সীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কারণ তাদের অজ্ঞতা। মিস্টার ফ্রয় সামানীদের শাসনামলে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত ভাষা প্রচলনের আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন , “ আরবী মিশ্রিত আধুনিক ফার্সী সাহিত্য ইসলাম বা আরবীর প্রতি বিদ্বেষ থেকে সৃষ্টি হয় নি। যে সব কবিতায় যারথুষ্ট্রীয় বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা মানুষের যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কারণে নয় ;বরং প্রচলিত সাহিত্যের ধারার কারণে ঘটেছিল । সেসময়ে অতীত নিয়ে আক্ষেপ করার বেশ প্রচলন ছিল। বিশেষত সংবেদনশীল কবিদের মধ্যে অতীতের অনুতাপ অধিকতর লক্ষণীয় ছিল ,কিন্তু অতীতে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ তাঁদের ছিল না। এই নতুন ধারার ফার্সী ,আরবীর পাশাপাশি অন্যতম ইসলামী ভাষায় পরিণত হয়েছিল। সন্দেহ নেই তখন ইসলাম আরবীর ওপর নির্ভরতা হতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। কারণ ইসলাম অসংখ্য জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ায় সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতা লাভ করেছিল এবং ইরান ইসলামী সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। ”
মিস্টার ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের 400 পৃষ্ঠায় ফার্সী ভাষায় আরবী শব্দ ও পরিভাষার অনুপ্রবেশ ও এর প্রভাব নিয়ে ‘ ইরানে নতুন জীবনের শুরু ’ শিরোনামে যে আলোচনা করেছেন সেখানে বলেছেন , “ কোন কোন সংস্কৃতিতে ভাষা সমাজ ও ধর্ম অপেক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণে অধিক ভূমিকা রাখে। এ কথাটি ইরানী সংস্কৃতির জন্য খুবই সত্য। কারণ সাসানী আমলের প্রাচীন ফার্সীর সঙ্গে ইসলামী আমলের আধুনিক ফার্সীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি এ দু ’ য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো আধুনিক ফার্সীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবী শব্দ ও পরিভাষার প্রবেশ যা একে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিশ্বজনীনতা দান করেছে যা প্রাচীন পাহলভী ফার্সীতে ছিল না। বাস্তবিকই আরবী ভাষা নতুন ফার্সী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে গতিশীল সাহিত্য (বিশেষত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে) রচনার পটতূমি প্রস্তুত করেছিল। মধ্যযুগের শেষ দিকে ফার্সী কবিতা সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আধুনিক ফার্সী ভিন্ন এক পথ ধরেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন আরবী ভাষায় দক্ষ একদল ইরানী মুসলমান। তাঁদের যেমন আরবী সাহিত্যে দক্ষতা ছিল তেমনি তাঁদের মাতৃভাষার প্রতিও ছিল তীব্র অনুরাগ। আধুনিক ফার্সী ভাষা আরবী বর্ণমালায় লেখা হতো এবং তা খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পূর্ব ইরানে উদ্ভাসিত ও সামানী রাজত্বের রাজধানী বোখারায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।
মি. ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের 402 পৃষ্ঠায় ফার্সী কবিতায় আরবী ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন ,
“ এ ধরনের কবিতা গঠনে প্রাচীন ফার্সী পদ্ধতির সঙ্গে আরবী কর্তৃবাচক শব্দের মিশ্রণের আশ্রয় নেয়া হয় এবং বিভিন্ন মাত্রা ও ছন্দের কবিতা তৈরি করা হয়। এ ধরনের পদ্ধতির সবচেয়ে প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট নমুনা হলো কবি ফেরদৌসীর ‘ শাহনামা ’ যা এরূপ সমধর্মী ছন্দে রচিত হয়েছিল। ”
শিয়া মাযহাব
প্রথম যখন ইরানীরা ইসলাম গ্রহণ করে তখন হতেই তারা নবী (সা.)-এর পরিবার ও বংশের প্রতি বিশেষ ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করেছে।
কোন কোন প্রাচ্যবিদ তাদের এ ভক্তি-ভালবাসাকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে বলে মনে করেন নি ;বরং একে ইসলাম অথবা আরব জাতীয়তার বিরুদ্ধে নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম ও রীতিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন এবং একে ইরানীদের কৌশল ও প্রতিক্রিয়ার ফল বলে মনে করেছেন।
প্রাচ্যবিদদের এ বক্তব্য দু ’ শ্রেণীর মানুষের জন্য বাহানা উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে :
প্রথম শ্রেণী হলো গোঁড়া সুন্নীরা যারা এর মাধ্যমে শিয়াদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একদল কৃত্রিম মুসলমান বলে প্রচারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে শিয়াদের ওপর হামলা করেছে। যেমন মিশরীয় লেখক আহমাদ আমিন তাঁর ‘ ফাজরে ইসলাম ’ গ্রন্থে এরূপ করেছেন। বিশিষ্ট শিয়া আলেম মুহাম্মদ হুসাইন কাশেফুল গেতা এ মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে ‘ আসলুশ্ শিয়া ওয়া উসূলুহা ’ নামক এক যুক্তিনির্ভর ও বলিষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছেন।
দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তথাকথিত ইরানী জাতীয়তাবাদীরা। প্রথম দলের বিপরীতে এরা ইরানীদের এ জন্য প্রশংসা করে থাকে যে ,তারা শিয়া মতাদর্শের আবরণে তাদের প্রাচীন ধর্মকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে। যেমন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা হতে প্রকাশিত ডক্টর পারভেজ সানেয়ী রচিত ‘ কানুন ওয়া শাখসিয়াত ’ গ্রন্থের 157 পৃষ্ঠায় আমাদের স্কুলগুলোর ইতিহাস গ্রন্থসমূহ অগভীর চিন্তাপ্রসূত ও বেশ শুষ্ক হয়ে পড়ার সমালোচনা করে একে সজীব ও বিশ্লোষণধর্মী গভীরতা দানের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে :
“ যেমন ইসলামে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে ইতিহাসে আমাদের শিখানো হয়েছে ইরানীরা হযরত আলী (আ.)-এর পন্থাবলম্বন করেছে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যকার বিভেদের সূত্র ধরে। আর তা হলো আমরা হযরত আলীকে প্রথম খলীফা মনে করি। আর সুন্নীরা তাঁকে চতুর্থ খলীফা বলে বিশ্বাস করে। শিয়া-সুন্নী পার্থক্যের বিষয়ের মূলকে বিশ্লেষণ না করে এভাবে উপস্থাপন করে অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রধান্য দান করা হয়েছে ,অথচ পার্থ্যক্যের এ ভিত্তি অযৌক্তিক বলে মনে হয়। স্কুল ত্যাগের অনেক বছর পর আমি নিজে অধ্যয়ন করে বুঝতে পারলাম শিয়া মাযহাব ইরানীদের আবিষ্কার। ইরানীরা তাদের স্বাধীনতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এর জন্ম দেয়। যেহেতু ইমাম হুসাইন (আ.) ইরানের সর্বশেষ বাদশার কন্যাকে বিয়ে করেন সেহেতু তাঁর সন্তানরা বংশ পরম্পরায় শাহজাদা হিসেবে ইরানী শাসনেরই গৌরবময় ধারাবাহিকতা। ইমাম হুসাইনের সন্তানদের যে ‘ সাইয়্যেদ ’ 34 বলা হয় তা ফার্সী ভাষার ‘ শাহজাদা ’ শব্দের সমার্থক।
ইরানীদের এ আবিষ্কার তাদের জাতীয়তাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ছিল। ইরানের প্রাচীন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানই শিয়া মাযহাবে অনুপ্রবেশ করেছে। শিয়া মাযহাবের সঙ্গে প্রাচীন ইরানী ধর্মীয় ঐতিহ্যের তুলনার মাধ্যমে আমরা এটি বুঝতে পারব। অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব প্রাচীন ইরানী ধর্ম (যারথুষ্ট্রবাদ) কিভাবে শিয়া মাযহাবের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। ”
প্রায় একশ ’ বছর পূর্বে কান্ট গোবিনু ‘ মধ্য এশিয়ার ধর্ম ও দর্শন ’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি নবী (সা.)-এর আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের নিস্পাপ হওয়ার বিশ্বাসকে সামানী সম্রাটদের ঐশী হওয়ার বিশ্বাস হতে উৎসারিত বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম হুসাইনের সঙ্গে ইরানী শাহজাদী শাহের বানুর বিবাহের কারণে তাঁর বংশধারা এ পবিত্রতা লাভ করেছে বলে প্রচার করেছেন।
এডওয়ার্ড ব্রাউনও গোবিনুর এ মতকে সমর্থন করে বলেছেন ,
“ আমি বিশ্বাস করি গোবিনু সঠিক বলেছেন। যেহেতু ইরানীরা রাজকীয় ক্ষমতা স্রষ্টার ঐশী দান ও অধিকার বলে মনে করত যা সাসানীদের হাতে তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন ,এ বিশ্বাস পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইরানের ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। বিশেষত শিয়া মাযহাবের প্রতি ইরানীদের ঝুঁকে পড়ার পেছনে এ বিশ্বাসের প্রভাব খুবই বেশি ছিল। রাসূলের ঐশী স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নির্বাচিত হওয়াটাই গণতান্ত্রিক আরবদের নিকট স্বাভাবিক ছিল। এর বিপরীতে শিয়াদের নিকট এটি অস্বাভাবিক ও নিদারুণ বিরক্তির কারণ ছিল। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর কর্তৃক ইরান সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণে শিয়াদের নিকট অপছন্দীয় ছিলেন। তাঁর প্রতি ইরানীদের অসন্তুষ্টিই যে একটি মাযহাবরূপে আবির্ভূত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইরানীদের বিশ্বাস নবীর কন্যা হযরত ফাতিমার কনিষ্ট সন্তান হুসাইন ইবনে আলী সর্বশেষ সাসানী শাসক ইয়ায্দ গারদের কন্যাকে বিয়ে করেন। তাই শিয়াদের বড় দু ’ টি দলই (বার ইমামী ও ইসমাঈলী) শুধু নবুওয়াতের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারীই নয় ,সে সাথে রাজকীয় মর্যাদারও প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ এতে দু ’ বংশধারার সমন্বয় ঘটেছে: নবুওয়াত ও সাসানী অভিজাত। ”
কিছু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ এবং ইরানীও এ ধরনের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং শিয়া মাযহাবের উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। এটা স্পষ্ট যে ,এ বিষয়ে আলোচনার জন্য পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। তবে আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বিষয় তুলে ধরছি।
ইমাম হুসাইনের সঙ্গে ইয়ায্দ গারদের কন্যার বিবাহের ঘটনা এবং এ দম্পতি হতে ইমাম সাজ্জাদের (জয়নুল আবেদীনের) জন্মের মাধ্যমে আহলে বাইতের ইমামদের ধারার উৎপত্তি তথা নবুওয়াতের পরিবারের সঙ্গে সাসানী রাজবংশের আত্মীয়তার বানোয়াট ঘটনা স্বার্থন্বেষী কিছু ব্যক্তির হাতে এমন এক হাতিয়ার তুলে দিয়েছে যা ইমামদের প্রতি শিয়াদের বিশ্বাসকে সাসানী সম্রাট ‘ ফাররাহে ইয়াযাদীর ’ প্রতি বিশ্বাসের ফলশ্রুতি বানিয়ে ছেড়েছে। কারণ সাসানী সম্রাটগণ নিজেদেরকে স্বর্গীয় বংশধারার এবং মানুষের ঊর্ধ্বে প্রায় খোদায়ী মর্যাদার সমতুল্য মনে করত। যারথুষ্ট্র ধর্মও তাদের এ চিন্তাকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করত।
জানা গেছে ,সাসানী শাসক আরদ্শিরের পুত্র শাপুরের আমলের পাহলভী ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি হাজীআবাদে পাওয়া গিয়েছে যাতে লেখা রয়েছে :
“‘ ইরান ও অ-ইরানের সম্রাট শাপুর মিনুসেরেশত ‘ ইয়ায্দানের ’ পক্ষ হতে মনোনীত ,তাঁর স্বর্গীয় পুত্র মাসদার উপাসক আরদ্শির মিনুসেরেশত ‘ ইয়ায্দানের ’ পক্ষ হতে মনোনীত ,তাঁর স্বর্গীয় প্রপৌত্র ববাকও ‘ ইয়ায্দানের ’ পক্ষ হতে মনোনীত। ” 35
যেহেতু সাসানী সম্রাটগণ নিজেদের স্বর্গীয় অবস্থান ও মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পবিত্র ইমামগণের বংশধারাও তাঁদের সঙ্গে মিশে যায় সেহেতু তাঁরা ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই ইরানী বংশোদ্ভূত হিসেবে স্বর্গীয় হতে বাধ্য। এ দু ’ প্রতিজ্ঞা পাশাপাশি রাখলে সহজেই বোঝা যায় ,পবিত্র ইমামদের নেতৃত্বের বিষয়ে বিশ্বাস ইরানীদের প্রাচীন বিশ্বাসেরই ধারাবাহিকতা।
আমরা এখানে সংক্ষেপে এ দাবির অসাড়তা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করব। প্রথমে বলে রাখি এখানে দু ’ টি বিষয় রয়েছে যে দু ’ টিকে পার্থক্য করা উচিত। প্রথমত এটি প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক। কোন জাতি যদি পূর্বে বিশেষ কোন চিন্তাধারা ও ধর্মের অনুসরণ করে পরে তা পরিবর্তন করে তবে তাদের অজান্তেই পূর্ববর্তী আকীদা-বিশ্বাসের কিছু বিষয় চলে আসে। হয়তো নতুন গৃহীত ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা রয়েছে এবং আন্তরিকভাবেই তা গ্রহণ করেছে ,পূর্ববর্তী বিশ্বাসের প্রতি তার কোন গোঁড়ামি ও এর ধারবাহিকতার চিন্তাও সে করে না ,কিন্তু তদুপরি তার চিন্তাশক্তি হতে প্রাচীন বিশ্বাসের কিছু বিষয় মুছে যায়নি এবং অসচেতনভাবেই সেগুলোকে সে নতুন ধর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে।
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ,যে সকল জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কেউ পূর্বে মূর্তিপূজক ,কেউ দ্বিত্ববাদী ,কেউ খ্রিষ্টান ,ইহুদী বা মাজুসী ছিল। তাই সম্ভাবনা রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তদপূর্ববর্তী চিন্তা ও বিশ্বাসসমূহ ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের মধ্যে বর্তমান থাকার।
নিশ্চিত বলা যায় ইরানিগণও কোন কোন বিশ্বাসকে ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের অজান্তেই সংরক্ষণ করেছে। দুঃখজনকভাবে কিছু সংখ্যক ইরানীর মধ্যে পূর্ববর্তী সময়ের কুসংস্কার এখনও বর্তমান রয়েছে ,যেমন বছরের শেষ বুধবার আগুনের ওপর দিয়ে লাফ দেয়া অথবা আগুনের দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করা ইত্যাদি। এটি আমাদের দীনী দায়িত্ব ,নিখাঁদ ইসলামের মূল মানদণ্ডের ভিত্তিতে জাহেলী যুগের সকল চিন্তাধারাকে দূর করার।
নবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের ইমামত (নেতৃত্ব) ও বেলায়েতের (অভিভাবকত্ব) বিষয়টি যদি আমরা অধ্যয়ন করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই কোরআন ও রাসূলুল্লাহর অকাট্য সুন্নাতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তবেই আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীর ইসলাম আনয়নের পূর্বেও ইসলামে এ বিষয়টি ছিল কি না ?
পবিত্র কোরআন ও রাসূলুল্লাহর অকাট্য সুন্নাহ্ হতে হয় স্পষ্ট যে ,প্রথমত কোরআন কোন কোন সত্যপন্থী সৎ কর্মশীল বান্দাকে ঐশীভাবে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করেছেন। দ্বিতীয়ত কোরআন কোথাও কোথাও সুস্পষ্টভাবে আবার কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতে ইমামত ও বেলায়েতের বিষয় দু ’ টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে সাথে রাসূলও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের এরূপ মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন।
আরব মুসলমানগণ অন্যান্য জাতির ওপর শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার অনেক পূর্বেই ইসলামে এ বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন কোরআনের সূরা আলে ইমরানের 33-34 নং আয়াতে এসেছে:
) إنّ الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين ذرّيّة بعضها من بعض و الله سميع العليم (
“ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম ,নূহ ,ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন। যাঁরা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। ” (তাই তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর হতেও নির্বাচন করবেন। এটিই স্বাভাবিক ,নয় কি ? কারণ তিনি পূর্ববর্তীদের হতে শ্রেষ্ঠ)।
সুতরাং শিয়া মাযহাবের মূল ভিত্তি কোরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকলেও যেহেতু আমাদের মূল আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় সেহেতু এতে প্রবেশ করতে চাই না। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো শিয়া মাযহাবের সঙ্গে ইরানীদের সম্পর্ক। কোন কোন প্রাচ্যবিদ ও তাদের এ দেশীয় অনুচররা শিয়া মাযহাব ইরানীরা উদ্ভাবন করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যাতে করে এ মাযহাবের ছত্রছায়ার তার প্রাচীন আচার ও ধর্মনীতিকে সংরক্ষণ করা যায় বলে যে দাবি করেছেন এখানে আমরা তার জবাব দেব।
আরেক দল প্রাচ্যবিদ যাঁরা বলেন ইরানীরা শিয়া মাযহাব তৈরি করেনি ;বরং সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত হওয়ার ফলশ্রুতিতে প্রতিরোধ হিসেবে এ মতাদর্শ গ্রহণ করেছে যাতে করে প্রাচীন বিশ্বাসকে এর ছায়ায় টিকিয়ে রাখা যায়-এ দৃষ্টিকোণ হতেও আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।
এ বিষয় দু ’ টি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার ওপর নির্ভরশীল যেখানে আমরা ইরানীদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জবরদস্তিমূলক নাকি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তা বিশ্লেষণ করেছি। যদি এটি সত্য হতো ,ইরানীরা বাধ্য হয়ে পূর্ববর্তী ধর্ম পরিত্যাগ করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করেছে তবে এরূপ ধারণা স্বাভাবিক ছিল যে ,তারা পূর্ববর্তী বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য এরূপ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়েছে আরব মুসলমানগণ কখনই ইরানীদের পূর্ববর্তী ধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করেনি ;বরং অনুমতি দিয়েছিল তাদের অগ্নিমন্দিরগুলো সংরক্ষণের ;এ জন্য যে ,আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,সাবেয়ী ,মাজুসী) জিম্মি হিসেবে মুসলমানদের অধীনে থাকায় আরবগণ তাদের উপাসনালয়ের সংরক্ষণকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করত। তা ছাড়াও ইরানে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক আরবের পক্ষে সম্ভব ছিল না কয়েক মিলিয়ন মানুষকে তাদের দীন পরিত্যাগে বাধ্য করা। কারণ সংখ্যায় যেমন তারা স্বল্প ছিল তেমনি যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য দিক হতেও তারা ইরানীদের থেকে দুর্বল ছিল (আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি 170 হিজরীতে আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে মুসলিম সেনা বাহিনীর বৃহদাংশ ইরানীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল)। তাই আরবদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তাদের পূর্ববর্তী দীন পরিত্যাগে বাধ্য করা। তাহলে ইরানীদের কি প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী ধর্মকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করার বা শিয়া মাযহাবের আশ্রয় নেয়ার ?
তদুপরি আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ মন্থর প্রক্রিয়ায় হয়েছিল। ইরানীদের অন্তরে পবিত্র ইসলামের গভীর প্রভাব এবং যারথুষ্ট্র ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় ইরানীদের স্বাধীনতা অর্জনের পর ঘটেছিল। তাই এ অনর্থক কথার কোন মূল্য নেই।
স্বয়ং এডয়ার্ড ব্রাউন তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন ,ইরানীরা ইসলাম ধর্মকে সাগ্রহে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে। যেমন তাঁর ‘ সাহিত্যের ইতিহাস ’ গ্রন্থের 297 পৃষ্ঠায় বলেছেন ,
“ যারথুষ্ট্র ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয়ের বিষয়ে গবেষণা চালানো সাসানীদের ভূখণ্ডের ওপর আরবদের বিজয় নিয়ে গবেষণা অপেক্ষা কঠিন। অনেকে ভেবে থাকেন মুসলিম যোদ্ধারা তাদের বিজিত ভূমিগুলোর অধিবাসীদের কোরআন ও তরবারীর মাঝে যে কোন একটি বেছে নেয়ার নির্দেশ দিত। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ ইহুদী ,গোবার36 ও তারসাগণ37 স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করত। তারা শুধু জিজিয়া দিতে বাধ্য ছিল। এটি করা ন্যায়সঙ্গতই ছিল। কারণ অমুসলিমগণ মুসলমানদের ন্যায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ,যাকাত ও খুম্স দেয়া হতে মুক্ত ছিল। ”
একই গ্রন্থের 306 ও 307 পৃষ্ঠায় যারথুষ্ট্র ধর্মের বিলুপ্তির পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছেন ,
“ প্রথম দিকে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত কম ছিল। কারণ ইসলামের বিজয়ের পর সাড়ে তিনশ ’ বছর পর্যন্ত ইরানীরা বিজয়ী শাসকদের মহানুভবতা ও সহনশীলতার অনুগ্রহ লাভ করেছিল যা এ সত্যকে প্রমাণ করে যে ,ইরানিগণ শান্ত পরিবেশে পর্যায়ক্রমে তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করেছে। ”
এডওয়ার্ড ব্রাউন হল্যান্ডের প্রাচ্যবিদ দুজীর ‘ ইসলাম ’ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন :
“ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জাতি ধর্মান্তরিত হয় তা হলো ইরানী। কারণ আরব নয় ,ইরানীরাই ইসলামকে দৃঢ় ও মুজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে ,তাদের মধ্য হতেই আকর্ষণীয় এক মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। ”
ইরানীরা ইসলামের প্রতি যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা এতটা ভালবাসায় পূর্ণ ছিল যে ,এটি বলার কোন সুযোগ নেই ,তারা শিয়া মাযহাবের আবরণে তাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তা করেছে।
আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ইরানীদের পরাজয়ের অন্যতম বড় কারণ ছিল শাসক ও প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি ও অনাস্থা। সাধারণ মানুষ তাদের শাসনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ,তারা শান্তির আশ্রয় খুঁজছিল এবং সত্য ও ন্যায়ের ধ্বনি শ্রবণের অপেক্ষায় ছিল। ইতোপূর্বে মাযদাকী ধর্মের প্রতি তাদের ঝুঁকে পড়ার কারণও এটিই ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ,বিচ্যুত ও অনাচারক্লিষ্ট যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রতি তারা এতটা অসন্তষ্ট ছিল যে ,যদি ইরানে ইসলাম না আসত তবে খ্রিষ্টধর্ম ইরান দখল করত।
দুজির উদ্ধৃতি দিয়ে ব্রাউন আরো বলেছেন ,
“ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে (600-640 খ্রিষ্টাব্দ) পূর্ব রোম ও পারস্যে রাজকীয় শাসক স্বাভাবিক গতিতে চলছিল। এ দু ’ সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো দখলের লক্ষ্যে সব সময় যুদ্ধরত থাকত। বাহ্যিকভাবে এ দু ’ সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ঘটেছিল। তাদের রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর ও মুনাফা আহরিত হতো ,দু ’ সাম্রাজ্যের রাজধানীর জাঁকজমক ও সৌন্দর্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। স্বৈরাচার উভয় সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডকে ন্যুব্জ করে ফেলেছিল। এতদু ’ ভয়ের ইতিহাসই মানব শোষণের মর্মান্তিকতায় পূর্ণ। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ ও দ্বৈততার ফলশ্রুতিতে এ জুলুম তুঙ্গে উঠেছিল। এমন সময় আকস্মিকভাবে মরুভূমির মধ্য হতে এক অপরিচিত জাতি বিশ্বের বুকে জাগরিত হলো। ঐ সময় পর্যন্ত যে জাতি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধে রত ছিল প্রথম বারের মত পরস্পর একত্র হয়ে অভিন্ন এক জাতির আকারে আবির্ভূত হলো।
স্বাধীনতা পিয়াসী এ জাতিটি সাধারণ পোশাক পরিধান করত , সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করত , খোলা মনের , অতিথিবৎসল , ফুর্তিবাজ ও রসিক , অথচ আত্মগর্বী ও রগচটা প্রকৃতির এবং যখন তার ক্রোধ বৃদ্ধি পায় তখন চরম অত্যাচারী ও শান্তি বিরোধীতে পরিণত হয়। এরূপ একটি জাতিই কিছু দিনের মধ্যে প্রাচীন ও ক্ষমতাধর কিন্তু অন্তঃক্ষয়প্রাপ্ত ইরানকে পদানত করে , কনস্টানটাইনের ( constantine)উত্তরাধিকারীদের ( রোমীয়দের ) হতে সবচেয়ে সুন্দর প্রদেশ
হস্তগত করে। স্পেন দখল করে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশ ,যেমন নতুন প্রতিষ্ঠিত জার্মানদের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করল ,পূর্ব দিকেও হিমালয় পর্বত পর্যন্ত অঞ্চল তাদের পদানত হলো। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যজয়ী জাতির সঙ্গে এদের কোন সাদৃশ্য ছিল না। কারণ তারা নতুন ধর্ম সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং অন্যান্য জাতিকে তা গ্রহণের আহ্বান জানাত। ইরানের প্রচলিত দ্বিত্ববাদ ও পতনশীল খ্রিষ্ট মতবাদের বিপরীতে এরা নিখাঁদ একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানাত। বর্তমান সময়েও ইসলাম পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধর্ম যার অসংখ্য অনুসারী রয়েছে ;পৃথিবীর এক দশমাংশ মানুষ এ ধর্মের অনুসারী। ”
এডওয়ার্ড ব্রাউন তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থের 155 পৃষ্ঠায় পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ‘ আভেস্তা ’ সম্পর্কে বলেছেন , ‘ আভেস্তা যারথুষ্ট্রের (যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তা) ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রাচীন ধর্মের বিধিবিধান সম্বলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যদিও বর্তমানে এ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ইরানে দশ হাজার এবং ভারতবর্ষে নব্বই হাজারের অধিক নয়। কিন্তু এ ধর্ম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল ও গভীর প্রভাব রেখেছে। আভেস্তাকে কোন আনন্দদায়ক গ্রন্থ বলা যায় না এবং এর বিভিন্ন অংশ সন্দেহযুক্ত বিবরণে পূর্ণ তদুপরি হয়তো গভীর অধ্যয়নে এর মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করা যাবে। কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় ,এ গ্রন্থ অত্যন্ত সাবলীল ও যত অধিক অধ্যয়ন করা যায় এর গূঢ় অর্থও তত অনুধাবন করা যায় ,ততই এর মর্যাদা স্পষ্ট হয়। এর বিপরীতে আভেস্তা দ্রুত অনুধাবনযোগ্য নয় ;বরং এর অধ্যয়ন ক্লান্তিকর ,তবে যদি কেউ ভাষাবিদ হিসেবে পৌরাণিক বিষয়াবলী অধ্যয়ন করতে চান তাঁর কথা ভিন্ন। ”
এডওয়ার্ড ব্রাউন যা বলেছেন সকল ইরানীও তা বলেন এবং এটিই সত্য ,ইরানিগণ শতাব্দী ক্রমে দলে দলে আভেস্তাকে পরিত্যাগ করে কোরআনকে ধারণ করেছে। আভেস্তা থেকে কোরআনের দিকে ঝুঁকে পড়া ইরানীদের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাধারণ ছিল। তাই প্রাক্তন সম্রাটদের রীতিনীতি ও আভেস্তার শিক্ষাকে সংরক্ষণের জন্য নিজেদের শিয়া মাযহাবের আড়ালে লুকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না।
দ্বিতীয়ত সাসানী সম্রাট ইয়ায্দ গারদ রাজধানীতে প্রতিরোধে সক্ষম নয় বুঝতে পেরে তাঁর পরিবার ও সভাসদদের নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশ ও শহর হতে অন্য শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন (যদিও তাঁর রাজধানীতে ও প্রাসাদে সহস্র প্রহরী ,শিকারী কুকুর ,সহস্র গায়ক ,পাচক ,খেদমতগার ,দাস-দাসী ছিল তবুও সেখানে নিরাপত্তা বোধ করেননি)। অবশ্যই রাজধানী ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা চাইলে আক্রমণকারী আরব মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু এর বিপরীতে তারা সম্রাটকে সহযোগিতা ও আশ্রয় দেয়নি। ফলে তিনি খোরাসানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেখানেও তাঁকে কেউ সহায়তা না করায় একটি ঘানি কলে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ইরানীরাই (সীমান্ত রক্ষীরা) তাঁকে হত্যা করে।
কিরূপে সম্ভব ,যে ইরানীরা ইয়ায্দ গারদকে আশ্রয় দেয়নি ,তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে নবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতকে তাদের মনের মণিকোঠায় আশ্রয় দেবে ? কিরূপে সম্ভব এ কারণে নবীর বংশধরদের জন্য নিজেদের উৎসর্গের প্রস্তুতি নেবে ?
তৃতীয়ত যদি ধরেও নেই ইরানীরা প্রথম হিজরী শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল তাই শিয়া বিশ্বাসের অন্তরালে নিজ বিশ্বাসকে গোপন করেছিল । তবে কেন তারা দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ করে নি ? বরং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে নিজেদের ইসলামের মধ্যে অধিকতর নিমজ্জিত করেছে এবং পূর্ববর্তী ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।
চতুর্থত ইরানের প্রতিটি মুসলমান জানে শাহর বানু (ইমাম সাজ্জাদের মাতা)-এর মর্যাদা কোন ক্রমেই অন্যান্য ইমামদের মাতাদের চেয়ে যাঁরা কেউ আরব ,কেউ আফ্রিকান ছিলেন ,অধিক নয়। কোন্ ইরানী ও অ-ইরানী শিয়া ইমাম সাজ্জাদের মাতার প্রতি অন্য ইমামদের মাতাদের চেয়ে অধিকতর সম্মান দেখায় ? ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর মাতা হযরত নারজেস খাতুন যিনি একজন রোমীয় দাসী ছিলেন তাঁর মর্যাদা শিয়াদের নিকট শাহর বানু অপেক্ষা অনেক বেশি।
পঞ্চমত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে ইমাম হুসাইনের সঙ্গে শাহর বানুর বিবাহ এবং ইরানী শাহজাদা হিসেবে ইমাম সাজ্জাদের জন্মের ঘটনা অপ্রমাণিত। আহলে বাইতের ইমামদের সঙ্গে সাসানী রাজবংশের সম্পর্কের ঘটনাটি নিম্নোক্ত কাহিনীর মতো: “ এক ব্যক্তি বলল , ‘ ইমাম পুত্র ইয়াকুবকে মসজিদের মিনারের ওপর নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে। ’ অন্য একজন বলল , ‘ না ,না। ইমামপুত্র নয় ,নবীর পুত্র ,ইয়াকুব নয় ,ইউসুফ ছিলেন ,মিনারের ওপর নয় কেনানের গর্তে। ” মূল কথা ঘটনাটিই মিথ্যা। আসলে ইউসুফকে কোন নেকড়েই খায়নি।
এখানে প্রকৃতপক্ষে ইয়ায্দ গারদের শাহর বানু অথবা ভিন্ন নামে কোন কন্যা ছিল কিনা বা ইমাম হুসাইনের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমেই তিনি ইমাম সাজ্জাদের মাতৃত্ব অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন কিনা সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঐতিহাসিক দলিলের ভিত্তিতে সন্দেহযুক্ত একটি বিষয়। বলা হয়ে থাকে ,সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে একমাত্র ইয়াকুবী এ সম্পর্কে একটি বাক্য বলেছেন। আর তা হলো: আলী ইবনুল হুসাইনের মাতার নাম ছিল হাররার যিনি ইয়ায্দ গারদের কন্যা এবং ইমাম হুসাইন তাঁর নাম পরিবর্তিত করে গাযালাহ্ রাখেন।
স্বয়ং এডওয়ার্ড ব্রাউন এ ঘটনাকে বানোয়াট বলে মনে করেন। ক্রিস্টেন সেনও বিষয়টি অপ্রমাণিত মনে করেন। সাঈদ নাফিসী তাঁর ‘ ইরানের সামাজিক ইতিহাস ’ গ্রন্থে একে কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু মনে করেন নি। এখন যদি ধরে নিই ইরানীরাই এ কাহিনী তৈরি করেছে তবে অবশ্যই তা দু ’ শ বছর পর তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ ইরানীদের স্বাধীন শাসন কর্তৃত্ব লাভের সময়কালে এবং শিয়া মাযহাবের উৎপত্তিরও দু ’ শ ’ বছর পর।
এখন আমরা কি করে বলতে পারি আহলে বাইতের ইমামগণ শাহজাদা হওয়ার কারণেই ইরানীরা শিয়া মাযহাবের প্রতি ঝুঁকেছিল ?
ইয়ায্দ গারদের কন্যার সঙ্গে ইমাম হুসাইনের বিবাহের ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত না হলেও কিছু কিছু হাদীসে এ ঘটনাকে সত্য বলা হয়েছে। তন্মধ্য ‘ উসূলে কাফী ’ র এ হাদীসটি যেখানে বলা হয়েছে: “ খলীফা উমরের শাসনামলে ইয়ায্দ গারদের কন্যাকে মদীনায় আনা হলে খলীফা উমর হযরত আলী (আ.)-এর পরামর্শে তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং যে কোন যুবককে বেছে নেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি ইমাম হুসাইনকে বেছে নেন। ”
কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এ হাদীসের বক্তব্যের সাদৃশ্য নেই এবং এর সনদে এমন দু ’ জন রাবী রয়েছে যারা নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের একজন ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আহ্মারীকে রেজালশাস্ত্রবিদগণ ধর্মীয় বিষয়ে অভিযুক্ত মনে করেন ও তার হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। অপরজন হলেন আম্মার ইবনে শিমার যাকে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ মিথ্যুক ও হাদীস জালকারী বলেছেন।
আমার জানা নেই এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসও অনুরূপ কি না ? তবে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের যথার্থ পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।
ষষ্ঠত যদি সাসানী বংশধারার সঙ্গে রক্ত সম্পর্কের কারণেই ইরানীরা আহলে বাইতের ইমামদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে তবে উমাইয়্যা বংশীয়দের প্রতিও তাদের সম্মান দেখান উচিত। কারণ এমনকি যে সকল ঐতিহাসিক ইয়ায্দ গারদের কন্যা শাহর বানুর সঙ্গে ইমাম হুসাইনের বিবাহকে অস্বীকার করেন তাঁরাও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন ,উমাইয়্যা শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সময় সংঘটিত এক যুদ্ধে ইয়ায্দ গারদের এক নাতনী শাহ আফরিদ কুতাইবা ইবনে মুসলিমের হাতে বন্দী হন। তখন ওয়ালিদ তাঁকে বিবাহ করে এবং উমাইয়্যা খলীফা ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের জন্ম হয়। এই উমাইয়্যা খলীফাকে ‘ অপূর্ণ ইয়াযীদ ’ বলা হয়ে থাকে। উমাইয়্যা শাসকরাও এ ক্ষেত্রে ইরানী শাহজাদা হওয়ার কারণে ইরানীদের উচিত উমাইয়্যা শাসকদেরও সম্মান করা।
তবে কেন ইরানীরা ইয়ায্দ গারদের জামাতা হিসেবে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ও ইরানী শাহজাদা হিসেবে ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালিদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে না ,অথচ তারা ইয়ায্দ গারদের ষষ্ঠ বংশধর (যদি ধরেও নিই তা সত্য) ইমাম রেযার প্রতি কেন এত অধিক ভালবাসা প্রদর্শন করে ?
ইরানীদের জাতীয় অনুভূতি যদি এতটা তীব্রই হয়ে থাকে তবে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের প্রতি ইরানীদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কারণ বলতে গেলে সে অর্ধেক ইরানী ছিল। কারণ তার মাতা মারজানা ইরানের সিরাজের মেয়ে এবং তার পিতা যিয়াদ ফার্স প্রদেশের শাসনকর্তা থাকাকালে তাকে বিয়ে করে।
ইরানীরা যদি জাতীয় অনুভূতির কারণে সাসানীদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কের যুক্তিতে নবী (সা.)-এর আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের প্রতি এতটা সম্মান দেখিয়ে থাকে তবে ইরানী মারজানা ও তার পুত্রের প্রতি তারা কেন এত অসন্তুষ্ট ও তাকে অভিশপ্ত মনে করে (ইমাম হুসাইনকে হত্যার নির্দেশ দেয়ায়) ?
সপ্তমত ইরানীদের শিয়া হওয়ার যুক্তি হিসেবে এ কথা তখনই সত্য হতো যদি শিয়া মাযহাব ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত অথবা অন্ততপক্ষে প্রথম পর্যায় ও সময়ের শিয়াগণ যদি ইরানী হতো অথবা এমন হতো যে ,প্রথম সময়ের অধিকাংশ ইরানী শিয়া মাযহাব গ্রহণ করেছে। অথচ সালমান ফারসী ব্যতীত প্রথম পর্যায় ও সময়ের অন্য কোন শিয়া ইরানী ছিল না এবং প্রথম সময়ের অধিকাংশ ইরানীও শিয়া ছিল না ;বরং এর বিপরীতে প্রথম সময়ের অধিকাংশ ইরানী আলেম ও মুসলমান যাঁরা তাফসীর ,হাদীস ,কালামশাস্ত্র অথবা আরবী সাহিত্যে ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা সকলেই সুন্নী ছিলেন ও শিয়া মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতেন। ইরানীদের মধ্যে এ অবস্থা সাফাভী শাসনামল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সাফাভী শাসনামল পর্যন্ত ইরানের অধিকাংশ প্রদেশে সুন্নী ছিল ,এমনকি উমাইয়্যা শাসনামলে ইরানের সকল স্থানে মসজিদের মিম্বারে হযরত আলী (আ.)-এর প্রতি লানত (অভিশাপ) পড়া হতো। ইরানীরা উমাইয়্যাদের অপপ্রচারে প্রচণ্ড রকম প্রভাবিত ছিল এবং অজ্ঞাতবশত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত। এমনকি বলা হয়ে থাকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর ইরানের সকল স্থানে প্রতিবাদ হয়।
সাফাভী শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ বড় মুফাসসির ,ফকীহ্ ,মুহাদ্দিস ,কালামশাস্ত্রবিদ ,দার্শনিক ,আরবী ভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রবিদ ইরানী ছিলেন ,এমনকি আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় ফকীহ্ আবু হানিফা যাঁকে ‘ ইমামে আযম ’ বলা হয় তিনিও একজন ইরানী। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী যিনি আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ও প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ প্রণেতা তিনিও একজন ইরানী। বিশিষ্ট ব্যাকরণ ও আরবী ভাষাশাস্ত্রবিদ সিবাভেই ,অভিধান রচয়িতা জওহারী ও ফিরুযাবাদী ,মুফাসসির যামাখশারী এবং কালামশাস্ত্রবিদ আবু উবাইদা এবং ওয়াসিল ইবনে আতাও ইরানী ছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় সাফাভী আমলের পূর্বে প্রায় সকল ইরানী আলেম ও অধিকাংশ জনগণ সুন্নী ছিল।
জাতিগত গোঁড়ামির ওপর ইসলামের বিজয়
আশ্চর্যের বিষয় হলো ইসলামী জাতিসমূহ পূর্বে দৃশ্যত এমন সব আলেমের ফতোয়ার অনুসরণ করত যারা জাতিগতভাবে তাদের হতে ভিন্ন ছিল। যেমন মিশরের অধিবাসীরা ইরানী আলেম লাইস ইবনে সা ’ দের অনুসারী ছিল ,তার বিপরীতে সেসময় ইরানীরা আরব বংশোদ্ভূত শাফেয়ীর অনুসারী ছিল। ইরানের প্রসিদ্ধ কিছু আলেম ,যেমন ইমাম গাযযালী ,তুসী এবং ইমাদুল হারামাইন জুয়াইনী শাফেয়ীর ভক্ত এবং ইরানী জাতিভুক্ত আবু হানিফার চরম সমালোচক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইরানের জনসাধারণ যখন শিয়া মাযহাব গ্রহণ করে তখন হতে আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ যাঁরা কুরাইশ ও হাশেমী বংশোদ্ভূত তাঁদের অনুসরণ শুরু করে।
ফিকাহ্শাস্ত্রের ‘ নিকাহ্ অধ্যায়ে ’ ‘ কুফু ’ বা ‘ কুফুওয়াত ’ (সমকক্ষতা) অর্থাৎ সকল জাতি বিবাহের ক্ষেত্রে সমমর্যাদার কিনা এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইরানী আবু হানিফার ফতোয়ার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে (ভিন্নতার কারণে)। আবু হানিফা গোঁড়া আরবদের ন্যায় বলেছেন , ‘ অনারবরা আরবদের সমকক্ষ নয় ;তাই অনারব আরব নারী বিয়ে করতে পারবে না। ’ কিন্তু আরব ফকীহ্ মালিক ইবনে আনাস ও অন্যরা বলেছেন ,এ ক্ষেত্রে আরব-অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুফিয়ান সাওরী আরব ফকীহ্ হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন ,এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। আরবীয় শিয়া ফকীহ্ আল্লামাহ্ হিল্লীও তাই বলেছেন। তিনি তাঁর ‘ তাযকিরাতুল ফোকাহা ’ গ্রন্থে আবু হানিফার ফতোয়া উল্লেখ করে বলেছেন , ‘ আবু হানিফার বক্তব্য সঠিক নয়। ইসলামে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ও হাবাশী কৃতদাসী সমান মর্যাদার। ’ তিনি আরো বলেছেন , ‘ এ বক্তব্যের সপক্ষে দলিল হলো নবী (সা.) তাঁর চাচাতো বোনকে কৃষ্ণবর্ণের মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দীর সঙ্গে বিবাহ দেন। কেউ কেউ তাঁর এ কর্মের প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন:لتتّضع المناكح সকলকে সমকক্ষ করার উদ্দেশ্যেই আমি এটি করেছি। ’
আবু হানিফার এ ফতোয়া আশ্চর্যজনক তা আহলে সুন্নাতের অনেকেই স্বীকার করেছেন। তবে এতে প্রমাণিত হয় সে সময়ে মুসলমান আলেমদের মধ্যে জাতিগত কোন গোঁড়ামি ছিল না।
ফিকাহর গ্রন্থসমূহে এমন কিছু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যাতে একদিকে অনারবদের প্রতি আরবদের তীব্র অনীহা ,অন্য দিকে এরূপ গোঁড়ামির ওপর ইসলামের আশ্চর্যজনক বিজয় ফুটে উঠেছে।
কথিত আছে ,সালমান ফার্সী খলীফা হযরত উমরের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে যদিও তিনি (খলীফা) এরূপ (জাতিগত) গোঁড়ামি হতে পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না তদুপরি ইসলামের নির্দেশের কারণে তা গ্রহণ করেন। খলীফার পুত্র আবদুল্লাহ্ এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে আমর ইবনে আসের শরণাপন্ন হলে আমর ইবনে আস বললেন ,এ কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ’ আমর একদিন সালমান ফারসীর মুখোমুখি হলে তাঁকে বললেন , ‘ তোমার প্রতি অভিনন্দন ,শুনলাম খলীফার জামাতা হওয়ার সম্মান লাভ করছ ? ’ সালমান বললেন , ‘ এ কাজ যদি আমার সম্মান বলে পরিগণিত হয় তবে আমি এ কাজ হতে বিরত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। ’
ইরানীদের শিয়া প্রবণতা
অধিকাংশ ইরানী সাফাভী শাসনামলের পরবর্তী সময়ে শিয়া হয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ,অন্য সকল স্থান অপেক্ষা ইরানে শিয়া মাযহাবের উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছিল। শিয়া মাযহাব যেরূপ মন্থর গতিতে ইরানে প্রবেশ করেছে এবং গভীরে প্রবেশ করেছে তা অন্য কোথাও হয় নি। সময়ের আবর্তনে ইরানীদের শিয়া মাযহাব গ্রহণের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত হয়েছে। যদি ইরানীদের হৃদয়ে শিয়া প্রবণতার বীজ রোপিত না হতো তাহলে সাফাভিগণ শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের শিয়া ও আহলে বাইতের অনুসারী করতে পারত না।
বাস্তবতা হলো ইরানীদের শিয়া ও মুসলমান হওয়ার কারণ একই। ইরানীরা ইসলামকে তাদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পেয়েছে এবং ইসলাম তাদের হারানো বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। ইরানীরা প্রকৃতিগতভাবে যেমন সচেতন তেমনি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক হতেও উজ্জ্বল অতীতের অধিকারী ছিল। তাই অন্যান্য জাতি হতে ইসলামের প্রতি অধিকতর সেবা দান করতে পেরেছে। ইরানের জনসাধারণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রাণকে অধিক অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণেই রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রতি তাদের ভালবাসা অন্যদের হতে বেশি ছিল এবং শিয়া মাযহাব তাদের মাঝে অন্যদের অপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করেছিল। ইরানীরা ইসলামের প্রাণকে নবীর আহলে বাইতের নিকট হতে পেয়েছিল এবং তাদের আত্মিক প্রশ্নাবলীর উত্তর কেবল তাঁরাই দান করতে পেরেছিলেন বলে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।
যে বিষয়টি ইরানীদের ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হলো ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচার। শতাব্দীকাল হতে ইরান এর অভাব অনুভব করছিল এবং এর জন্য আকাক্সিক্ষত ছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল মুসলমানদের যে অংশটি ইসলামের সাম্য ও ন্যায়ের প্রতি সবচেয়ে নিবেদিত এবং জাতি ,বংশের ঊর্ধ্বে উঠে এর প্রয়োগে সবচেয়ে তৎপর তাঁরা হলেন নবীর পবিত্র আহলে বাইত । নবীর আহলে বাইত অনারবদের নিকট ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক ও আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।
আমরা যখন কোন কোন খলীফার কর্মকাণ্ডে আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে আরব-অনারবদের মধ্যে পার্থক্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করি তখন দেখি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ইসলামের সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে এ বৈষম্যের বিরোধিতায় নেমেছেন। এটি এ সত্যকেই প্রমাণ করে।
বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের নবম খণ্ডের 124 পৃষ্ঠায় ‘ আল কাফী ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে :
‘ একদিন একদল মাওয়ালী (অনারব মুক্ত দাস শ্রেণী) হযরত আলী (আ.)-এর নিকট এসে আরবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল: “ রাসূল (সা.) বায়তুল মাল বণ্টন ও বিবাহের ক্ষেত্রে কখনই আরব ও অনারবের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তিনি তাদের মধ্যে সমানভাবে বায়তুল মাল বণ্টন করতেন এবং অনারব সালমান ,বেলাল ও সাহিবকে আরব নারীদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন ,অথচ এখন আরবরা তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য করছে। হযরত আলী আরবদের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে কথা বললেন ,কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। তিনি তখন চীৎকার করে বললেন: অসম্ভব ,অসম্ভব। অতঃপর তিনি তাদের নিকট হতে অসন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে এসে মাওয়ালীদের জানালেন: অত্যন্ত দুঃখজনক ,এরা তোমাদের সঙ্গে সাম্যের নীতি গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। তারা একজন মুসলমান হিসেবে তোমাদের সম অধিকার দানে আগ্রহী নয়। আমি তোমাদের পরামর্শ দেব ব্যবসার পথ ধরার। আশা করি আল্লাহ্ তোমাদের ওপর বরকত অবতীর্ণ করবেন। ”
মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইরাকের প্রদেশিক শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে আবিহ্-এর নিকট লিখিত পত্রে বলেন , ‘ ইরানী মুসলমানদের হতে সাবধান থাক। কখনই তাদের আরবদের সম মর্যাদা দান কর না। আরবদের তাদের নারী গ্রহণের অধিকার থাকলেও তাদের আরব নারী গ্রহণের অধিকার নেই। আরবরা তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেও তারা আরবদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। যতদূর সম্ভব তাদের কম মজুরী ও নিম্নমানের কাজ দাও। আরবদের উপস্থিতিতে তাদের জামায়াতের ইমাম হতে দিও না। জামায়াতের প্রথম সারিতে যেন তারা না দাঁড়ায়। তাদেরকে বিচারক ও সীমান্ত প্রহরী হিসেবে নিয়োগ দান কর না। ”
কিন্তু এর বিপরীতে হযরত আলীর নিকট একজন আরব ও একজন ইরানী মহিলা বিচার নিয়ে আসলে তিনি তাদের মধ্যে সমভাবে বিচার করেন। এতে আরব মহিলা ক্ষিপ্ত হলে হযরত আলী মাটি হতে দু ’ মুঠো মাটি উঠিয়ে কিছুক্ষণ এর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন , ‘ যতই চিন্তা করি তবু এ দু ’ মুঠো মাটির মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। ’
হযরত আলী তাঁর এ তুলনামূলক কর্মের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রসিদ্ধ এ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন :
كلّهم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربيّ على عجميّ إلّا بالتّقوى
“ সকলেই আদম হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট হয়েছেন। আরবদের অনারবদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই ,কারণ শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড তাকওয়া ও খোদাভীতি। ” জাতি ,বংশ ,রক্ত সম্পর্ক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যায় না। যখন সকলেই আদমের বংশের ,আর তিনি মাটি হতে সৃষ্ট হয়েছিলেন তখন রক্ত ,বর্ণ ও বংশ গৌরবের কোন স্থান নেই।
‘ সাফিনাতুল বিহার ’ -এর 2য় খণ্ডের 692 পৃষ্ঠায় ‘ ওয়ালী ’ ধাতুর অধ্যায়ে বলা হয়েছে :
“ একদিন হযরত আলী (আ.) মিম্বারে জুমআর নামাজের খুতবা দিচ্ছিলেন। আরবের প্রসিদ্ধ নেতা আশআস ইবনে কাইস কিন্দী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল: হে মুমিনদের নেতা! এই রক্তিম বর্ণের লোকেরা (ইরানীরা) আপনার সম্মুখে আমাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ,অথচ আপনি কিছু করছেন না। এ কথা বলে রাগত স্বরে বলল: আজকে আমি দেখাব আরবরা কি করতে পারে। হযরত আলী এ কথা শুনে বললেন , ‘ এই স্ফীত উদররা দিনের বেলা যখন নরম বিছানায় ঘুমায় তখন ইরানী ও মাওয়ালীরা আল্লাহর জন্য প্রখর রৌদ্রের নীচে কাজ করে। অথচ এই আরামপ্রিয়রা চায় আমি এই পরিশ্রমী লোকদের বিতাড়িত করে জালিমের অন্তুর্ভুক্ত হই। সেই আল্লাহর শপথ ,যিনি বীজ অঙ্কুরিত ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ,আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি: প্রথম যুগে তোমরা ইসলামের জন্য ইরানীদের ওপর অস্ত্র চালাবে এবং পরবর্তী যুগে ইরানীরা তোমাদের ওপর ইসলামের স্বার্থে তরবারী চালাবে। ”
‘ সাফিনাতুল বিহার ’ -এর 2য় খণ্ডের 693 পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে :
“ মুগীরা ইবনে শোবা প্রায়শঃই হযরত আলী ও হযরত উমরের মধ্যে তুলনা করে বলতেন: আলী অনারব মাওয়ালীদের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর বিপরীতে খলীফা উমর তাদের অপছন্দ করতেন। ”
এক ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল , “ মানুষ বলাবলি করে ,কেউ খাঁটি আরব ও খাঁটি দাস না হলে নিম্নশ্রেণীর। ”
সে বলল , ‘ যার পিতা-মাতা উভয়েই দাস ছিল। ’
ইমাম বললেন , ‘ খাঁটি দাসের শ্রেষ্ঠত্ব কি জন্য ? ’
সে বলল , ‘ নবী (সা.) যেহেতু বলেছেন প্রত্যেক জাতির দাসরা তাদের জাতিরই অন্তুর্ভুক্ত সেহেতু আরবদের খাঁটি দাস আরবদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে যে খাঁটি আরব অথবা আরবদের অধীনস্থ খাঁটি দাস। ’
ইমাম বললেন , ‘ তুমি শোন নি রাসূল (সা.) বলেছেন আমি তাদের অভিভাবক যাদের কোন অভিভাবক নেই। আমি আরব-অনারব সকলের অভিভাবক। নবী যাদের অভিভাবক তারা কি নবীর জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় ? ’
ইমাম আরো বললেন , ‘ এ দু ’ য়ের মধ্যে কে উত্তম ? যে নবীর সঙ্গে সংযুক্ত নাকি যে মূর্খ ও অত্যাচারী এক আরবের সঙ্গে সংযুক্ত যার মূত্রত্যাগের সভ্যতাটুকুও জানা নেই ? ’
অতঃপর বললেন , ‘ যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ঐ ব্যক্তি হতে উত্তম যে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই আরবরা ভয়ে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে ,অপর দিকে ইরানীরা নিজ ইচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামে প্রবেশ করেছে ? ’ 38
এ ধরনের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিকভাবে আরব ও অনারবদের মধ্যে পার্থক্য করা হতো এবং নবীর আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ অহরহ এরূপ রাজনীতির বিরোধিতা করতেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এ কারণেই ইরানীরা একদিকে ইসলামের প্রকৃত প্রাণ ও বাস্তবতার প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রেখেছিল এবং অন্য দিকে অন্যান্য জাতি হতে অধিকতর বৈষম্যের শিকার হওয়ায় নবীর আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করেছিল।
পৃষ্ঠপোষকতার নামে অমার্যাদা
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু লোক ইরানী জাতীয়তা সংরক্ষণের নামে ইরান জাতির প্রতি সর্বাধিক অমর্যাদা করছেন।
কখনও তাঁরা বলেন , “ ইরান জাতি সর্বাত্মকভাবে চেয়েছিল তাদের প্রাচীন ধর্মকে সংরক্ষণ করতে। কিন্তু সকল প্রকার ইতিবাচক ক্ষমতা ও মর্যাদা এবং বিশাল ভূমি ও চৌদ্দ কোটি মানব শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা পঞ্চাশ বা ষাট হাজার আরবের নিকট পরাস্ত হয়েছিল। ”
যদি এ কথা সত্য হয়ে থাকে তবে এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে ?
কখনও তাঁরা বলেন , ‘ ইরানীরা ভয়ে তাদের ধর্মীয় রীতি ও আচার পরিত্যাগে বাধ্য হয়। ’ যদি এমনটিই হয় তবে ইরানীরা জাতিসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। যে জাতি বিজেতা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্তরিক বিশ্বাসকেও সংরক্ষণে সক্ষম নয় সে জাতি মানবীয় গুণশূন্য।
কখনও তাঁরা বলেন , “ ইরানী জাতি চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আরবদের জোয়ালের নীচে আছে যদিও আরবদের সামরিক কর্তৃত্ব একশ ’ বছরের বেশি স্থায়ী ছিল না। কিন্তু চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে ইরানীদের যে মেরুদণ্ড ভেঙ্গেছিল তা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ”
কিরূপ উত্তম এ দুর্বলতা ও অক্ষমতা! যখন আফ্রিকার অর্ধবর্বর অনেক জাতি কয়েক শতাব্দীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের শেকলগুলো একের পর এক ছিন্ন করে নিজেদের মুক্ত করছে তখন দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এক জাতি মরুভূমির কিছু গোত্রের হাতে পরাস্ত হওয়ার কিছু দিন পরই স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও চৌদ্দশ ’ বছর ধরে সেই শেকলের বন্ধনে আড়ষ্ট। এমনকি শতাব্দীকাল পূর্বের বিজেতার ভাষা ,আচার ও ধর্মীয় রীতি তাদের নিকট অপছন্দীয় হওয়ার পরেও প্রতিদিন তাদের সামাজিক ,ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের গভীর হতে গভীরে প্রবেশ করছে। কি আশ্চর্য!
কখনও তাঁরা বলেন , “ ইরানীরা তাদের প্রাচীন ধর্ম ও আচার-বিশ্বাসকে সংরক্ষণের লক্ষ্যেই শিয়া মতবাদের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে বাহ্যিকভাবে মুনাফিকের ন্যায় ইসলামকে মেনে চলছিল। তাদের মুসলমান হওয়ার দাবি ও ইসলামের জন্য তাদের সকল অবদান মিথ্যা ভান ছিল। তারা চৌদ্দ শতাব্দী ধরে মিথ্যা বলছে ,মিথ্যা লিখছে ও কৃত্রিম আচরণ করেছে। ” কি চমৎকার কাপুরুষ ও অমর্যাদাশীল এ জাতি!
কেউ কেউ আবার বলে থাকেন , “ এত সব আত্মত্যাগ ও ঝোঁকের মূলে ইসলামের সত্যকে অনুধাবন এবং শিয়া মাযহাবের সঙ্গে ইরানীদের আত্মিক মিলের বিষয়টি ছিল না ;বরং একটি বিবাহের রহস্য কার্যকর ছিল এবং এ জাতি একটি বিবাহের কারণেই তাদের জীবন পদ্ধতিকে পরিবর্তন করেছিল । ” কিরূপ অন্তঃসারশূন্য এ জাতি!
আবার অনেকে বলেন , “ ইরানীরা প্রথমে চেয়েছিল তাদের ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার সংরক্ষণে অংশ নিতে ,কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেয় বিষয়টিকে তলিয়ে দেখায়। ” কি ভীতু ও কাপুরুষ এ জাতি!
এই সকল ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে বোঝা যায় ,জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো ইরানী। কারণ ইরানীরা ভয়ে নিজস্ব প্রচীন লিখন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আরবী লিখন পদ্ধতি গ্রহণ করে ,ফার্সী ভাষার ওপর আরবী ভাষাকে প্রধান্য দেয়া শুরু করে ,আরবদের ভয়ে আরবী ভাষার ব্যাকরণবিধি তৈরি করে ও আরবী ভাষায় বই লেখা শুরু করে।
আরব শাসকরা চলে যাওয়ার পরও তাদের এ ভীতি থেকে যায় এবং তারা তাদের সন্তানদের আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়। তাদের সাহিত্যে আরবী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং ইসলামকে গ্রহণ করে প্রাচীন ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা তাদের প্রিয় ধর্মকে (তাদের ভাষায়) রক্ষার কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেনি।
মোট কথা ,এই সকল বিশ্লেষকের মত গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে ইরানে সংঘটিত ঘটনাসমূহে এ জাতির অক্ষমতা ,দ্বিমুখিতা ,কাপুরুষতা ,অমর্যাদা ,মূল্যহীনতা ও নীচতাকেই প্রমাণ করে। সে সাথে স্পষ্ট করে যে ,এ জাতির মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষমতা ,ঈমান ,সত্যাকাঙ্ক্ষা ও সত্য নিরূপণ ক্ষমতা অনুপস্থিত। এই সকল মূর্খ লেখক ও বিশ্লেষকের এ সব মন্তব্য সত্যপরায়ণ ও সম্ভ্রান্ত ইরানী জাতির প্রতি অসম্মান ছাড়া কিছুই নয়।
প্রিয় পাঠকবৃন্দ ,এ গ্রন্থ প্রমাণ করবে এ সকল কিছুই ইরান ও ইরানী জাতির প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এ জাতি যা করেছে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন মনোনয়নের মাধ্যমে করেছে। ইরানীরা যোগ্য ,অক্ষম নয় ;সত্যপরায়ণ ,মিথ্যাবাদী নয় ;মুমিন ,মুনাফিক নয় ;সাহসী ,ভীতু ও কাপুরুষ নয় ;সত্যাকাঙ্ক্ষী ,মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকারী নয় ;মূল ও শেকড়ের অধিকারী ,মূলহীন নয়। ইরানীরা ভবিষ্যতেও তার মৌলিকত্ব সংরক্ষণ করবে এবং ইসলামের সঙ্গে তার চিরন্তন বন্ধনকে দৃঢ় ও মজবুত করবে।
দ্বিতীয় ভাগ
ইরানে ইসলামের অবদান
অনুগ্রহ নাকি বিপর্যয়
আমাদের এ পর্যায়ের ও পরবর্তী অংশের আলোচনা ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান। অর্থাৎ ইসলাম ইরান ও ইরানী জাতির ওপর কি অবদান রেখেছে এবং ইরান ও ইরানী জাতি ইসলামের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে। অন্যভাবে বলা যায় ,ইসলাম ইরানকে কি দিয়েছে এবং ইসলাম ইরান হতে কিভাবে লাভবান হয়েছে।
একটি ধর্ম কোন জাতিতে কিরূপ অবদান রাখতে পারে ? অবশ্যই এ অবদান বা ভূমিকা সাময়িক ও তাৎক্ষণিক কোন বিষয় নয় ,যেমন কোন যুদ্ধে সামরিকভাবে তাদের সহযোগিতা করা অথবা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দান করা বা শিল্প কারখানা স্থাপন করে সহযোগিতা করা ;বরং এ অবদান এ বিষয়সমূহ হতে অনেক মৌল এবং তা হলো তাদের চিন্তা-চেতনায় ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর পরিবর্তন আনয়ন ,তাদের নৈতিক ও প্রশিক্ষণগত উন্নয়ন সাধন ,আবদ্ধ ও সংকীর্ণ প্রাচীন রীতির পরিবর্তন করে জীবন্ত ও গতিশীল জীবন পদ্ধতির প্রবর্তন ,নববিশ্বাস ,আদর্শ ও উন্নত চেতনার জন্মদান ,নব উদ্যোগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে সত্যজ্ঞান ও কল্যাণকর সৎ কর্মের প্রতি নির্দেশনা দান এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি। যদি এমন হয় তবেই তাদের অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হবে ,মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হবে ,তাদের বিজ্ঞান ,দর্শন ,শিল্প ,স্থাপত্য ,সাহিত্যসহ জ্ঞানের সকল দিকের বিকাশ সাধিত হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে ঐ জাতি ও সভ্যতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।
অন্যদিকে কোন ধর্মের প্রতি এক জাতির অবদানের অর্থ হলো ঐ ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং তার সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে সে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে ও এজন্য আত্মনিয়োগ করবে। ঐ ধর্মের ভাষার গাঁথুনিকে মজবুত করবে ,অন্যান্য জাতিকে ঐ ধর্মের সঙ্গে পরিচিত করাবে ,নিজ জীবন ও সম্পদ দিয়ে একে রক্ষা করবে ,এর পথে জীবন উৎসর্গ করবে এবং এর সকল ক্ষেত্রে ঐকান্তিকতা ,নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করবে।
আমাদের এ পর্যায়ে আলোচনার প্রথমাংশ নিয়ে অর্থাৎ ইসলাম ইরানে কি অবদান রেখেছে। ইরান ও ইরানী জাতি ইসলামে কি ভূমিকা পালন করেছে আমরা তা এ গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে আলোচনা করব।
পূর্বে আমরা যে মানদণ্ড দিয়েছি তার ভিত্তিতে দেখব ইসলাম ইরানে কোন অবদান রেখেছে কি না ? ইসলাম কি ইরানকে স্বাধীন করে এর হৃদয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে ? ইসলাম কি ইরানের ইতিহাসকে উন্নত ইতিহাসের দিকে পরিচালিত করেছে ? ইসলামের কারণেই কি ইরানের মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা পরিস্ফুটিত হয়েছে নাকি ইসলাম ইরানকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে নিয়ে গেছে ? তাদের প্রতিভার বিকাশকে স্তিমিত করে দিয়েছে ? ইরানের ইতিহাসকে কি বিপথে পরিচালিত করেছে ? ইরানের সভ্যতাকে কি নষ্ট ও ধ্বংস করেছে ? ইসলামের কারণেই কি ইরান জ্ঞান ,দর্শন ,ইরফান (আধ্যাত্মিকতা) ,শিল্প ,স্থাপত্যকলা ও নৈতিকতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে ও বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে নাকি ইসলাম এরূপ বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীদের আবির্ভাবের পথকে রুদ্ধ করেছে ? যদি ইরানের ভূমিতে এরূপ মনীষীদের আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং তা ইসলামের কারণে নয় বা ইসলাম সে পরিবেশ সৃষ্টি করে নি ;বরং ইরানীরা তাদের প্রকৃতিগত মেধা ও যোগ্যতা এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই ইবনে সিনা ,আল বিরুনী (আবু রাইহান) ,খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী এবং আল রাযীর মত প্রতিভার জন্ম দিতে পেরেছিল ;তাহলে এ প্রশ্নটি আসে যে ,ইসলাম ইরানের জন্য অনুগ্রহ ছিল নাকি তা বিপর্যয় ডেকে এনেছিল ?
নিঃসন্দেহে ইসলামের আবির্ভাব ও রাষ্ট্র গঠনের পর বিভিন্ন জাতি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ায় বিশাল মর্যাদাশীল ,বিরল ও ব্যাপক এক সভ্যতার জন্ম হয়। ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা যাকে ‘ ইসলামী সভ্যতা ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই সভ্যতায় এশিয়া ,আফ্রিকা ,এমনকি ইউরোপও অংশগ্রহণ করেছে। ইরানীরাও এ সভ্যতায় অংশগ্রহণকারী একটি জাতি এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এ সভ্যতায় ইরানীদের অংশগ্রহণ সর্ববৃহৎ।
এর বাস্তবতা কি ? ‘ ইসলামী সভ্যতা ’ নাম হতে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় প্রকৃতই কি তাই ? অর্থাৎ বাস্তবে ইসলামই কি এ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিবেশ সৃষ্টিকারী ও প্রকৃত উদ্দীপক ? এ সভ্যতার প্রাণ সঞ্চারক ও পরিচালনাকারী শক্তি কি ইসলাম ? নাকি অন্য কোন কারণ ও উদ্দীপক এর পেছনে ভূমিকা রেখেছে এবং প্রত্যেক জাতিই নিজস্ব উদ্দীপকের তাড়নায় এ সভ্যতায় ভূমিকা রেখেছে ? যেমন ইরানী জাতি তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উদ্দীপনায়ই এতে অবদান রেখেছে।
এ বিষয়ে ধর্মীয় ,সামাজিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন সময়ের ইরানের চিন্তাগত ,ধর্মীয় ,সামাজিক ,রাজনৈতিক ,পারিবারিক ও নৈতিক অবস্থার একটি পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে ইসলাম তার আগমনের পর এ বিষয়গুলোতে কি পরিবর্তন সাধন করেছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।
সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের ইতিহাস এবং এর আবির্ভাবের সমকালীন ইরানের ইতিহাস স্পষ্ট। তাই সহজেই আমরা প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে পারি। বিশেষত বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইউরোপীয়রা বিষয়টি উপস্থাপন করে। পূর্বে ইরানীরা অন্যান্যের মতই এ বিষয়ে তেমন চিন্তা করত না। কিন্তু অধুনা এরূপ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়ে থাকে। তবে দুঃখজনকভাবে এখনও আমাদের দেশে অন্যদের অনুসরণের নীতি অব্যাহত রয়েছে ;সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজে ‘ গবেষণা ’ ও ‘ পর্যালোচনা ’ র ধারা এখনও চালু হয় নি। একদল লোক তোতা পাখির ন্যায় অন্যদের অনুকরণে ইরানে ইসলামের আগমনকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেন। অন্যদলও অন্যদের অনুকরণে তাদের বিপরীতে অবস্থান নেন ও বলেন ,ইসলাম ইরানের জন্য এক বিপর্যয় ছিল। বর্তমানে এমন দিন নেই যে দিন বই-পুস্তক ,পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে কিছু লিখছে না বা রেডিও ,টিভি কিছু বলছে না। এ সবের ঊর্ধ্বে স্কুল-কলেজের বইগুলোও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তাধারার প্রচারের পথ হতে বিরত থাকছে না।
আমাদের ইচ্ছা সকল প্রকার গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে এ বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা রাখব। আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একদল ইউরোপীয় গবেষক এবং কিছু সংখ্যক ইরানী বিশেষজ্ঞও এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রায়শই তাঁদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করব।
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মত
এ বিষয়ে বিভিন্ন মত হতে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি এখানে আমরা উল্লেখ করছি।
ড. মুঈন তাঁর ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ 39 গ্রন্থে জনাব তাকী যাদের ‘ অতীত ইরানের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন ’ সম্পর্কিত বক্তব্য হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ,
“ ইসলাম... এক নতুন ধর্ম এবং এক সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় বিধান ও ন্যায়ের ভিত্তিসহ আগমন করেছিল ,ইরানে ইসলামের প্রসার নব প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিল এবং শক্তিশালী ঈমানের ভিত্তি দান করেছিল। যে দু ’ টি ইতিবাচক প্রভাব এর আগমনের মাধ্যমে এ ভূখণ্ডে ঘটেছিল তার প্রথমটি হলো ইসলাম সমৃদ্ধ ও ব্যাপক এক ভাষা আরবীকে সঙ্গে করে এনেছিল... এ ভাষা ইরানে এসে আকর্ষণীয় ,মনোমুগ্ধকর ও নমনীয় আর্য ভাষার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশ্রিত হতে থাকে ও ইরানী ঐতিহ্যে মিশে যায় এবং একে পূর্ণতা দান করে। চতুর্থ ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও ভাষাবিদের বদৌলতে নব অলংকারপ্রাপ্ত আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল যা সকল ধরনের বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এরূপ প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন সা ’ দী ,হাফিয ,নাসির খসরু এবং তাঁদের মত উজ্জ্বল কিছু প্রতিভা।... দ্বিতীয় বিষয়টি হলো (ইসলামের সঙ্গে) জ্ঞান ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ এক নতুন ধারার আগমন ঘটে যা গ্রীক ,সুরিয়ানী ,হিন্দী (সংস্কৃত) ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদের মাধ্যমে (দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত) শুরু হয় এবং ইসলামী খেলাফতশাসিত অংশে বিশেষত ইসলামী প্রাচ্যে ইরানীদের ও আরবী ভাষাজ্ঞানসম্পন্নদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।
...গ্রীক শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবারিত সমুদ্রের খুব কম অংশই যা দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অননূদিত ছিল এর অধিকাংশই মুসলমানগণ অনুবাদ করেছিল... গ্রীক জ্ঞান ,বিজ্ঞান ও দর্শনের আরবী অনুবাদ এত অধিক পরিমাণে ইসলামী বিশ্বে বিশেষত ইরানে প্রচলন লাভ করে যে ,ইবনে সিনা ,ফারাবী ,আলবিরুনী ,মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযীদের মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা দশ হাজারের অধিক পুস্তক রচনা করেন যার নিরানব্বই ভাগ আরবী ভাষায় রচিত হয়। দ্বিতীয় হতে সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা গ্রীক ও রোম সভ্যতার পর সবচেয়ে বড় সভ্যতা হিসেবে আবির্ভূত হয় ...। ”
তাকী যাদেহ্ তাঁর এ বক্তব্যে শুধু এতটুকু বলেছেন ,ইসলাম ইরানে নব প্রাণের সঞ্চার করেছিল ,কিন্তু ইসলাম ইরান হতে কি নিয়েছে বা ইরানকে কি দিয়েছে যার ফলে ইরান নতুন প্রাণ লাভ করেছিল তা আলোচনা করেন নি। আমরা এ গ্রন্থে এ বিষয়টি ইনশাআল্লাহ্ স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। তাকীযাদেহ্ এ বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন , ‘ ইসলাম সুশৃঙ্খল এক বিধান ও ন্যায়ের ভিত্তি নিয়ে এসেছিল ’ । কিন্তু এ বিষয়টি ইসলামের অসংখ্য অবদানের একটি মাত্র। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ,ইসলামই সা ’ দী ,হাফিয ও নাসির খসরুদের সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং চিকিৎসা ,দর্শন ও অংকশাস্ত্রে ইবনে সিনা ,রাযী ,ফারাবী ও বিরুনীদের সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটনের সুযোগ করে দিয়েছিল।
জয়নুল আবেদীন রাহনামা ‘ তরজমা ওয়া তাফসীরে কোরআন ’ গ্রন্থের ভূমিকায় (75 পৃষ্ঠায়) বলেছেন , “ আরব ভূমিতে ইসলামের আগমন মানব ইতিহাসের বৃহৎ বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহের একটি... সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে এ বিপ্লব শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তা পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সভ্যতার ধারক দেশগুলোর মানুষ ও সমাজের মাঝে যে গভীর ও বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে তা তাদের অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন জীবন সম্পৃক্ততা হতে মুক্তি দেয় এবং স্থায়ী ও দৃঢ়তর এক নব সম্পৃক্ততা তাদের হৃদয়ে ও চিন্তায় সৃষ্টি করে যা মানবতার নব জীবনের ইতিহাসে এক আশ্চর্যজনক রহস্য। এই বিপ্লব নব সভ্যতার জন্মদানের মাধ্যমে তৃণলতা ও পানিশূন্য মৃত আরব মরুভূমির কিছু অপরিচিত ও শব্দহীন মরুচারীর মধ্য হতে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের সহস্র ব্যক্তির সরব পদচারণার সৃষ্টিই করে নি ;বরং তাদের জন্য এক নব দর্শন নিয়ে এসেছিল।
যদিও এ সভ্যতার কিছু মূল পার্শ্ববর্তী রোম ও পারস্য এ দু ’ বৃহৎ সভ্যতার পানিতে পুষ্ট হয়েছিল তদুপরি তাদের জন্যও এটি নব অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিগণিত ছিল। তাকওয়া ও ন্যায়ের ভিত্তিতে যে ঐশী ও দার্শনিক শিক্ষা এ সভ্যতা দান করেছিল তা চিন্তাশীল ,অনুসন্ধানী ও তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে শীতল ও সুপেয় পানি ঢেলে দিয়েছিল ,তাদের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার করেছিল। এ চিন্তা প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতা এ দু ’ বৃহৎ সাম্রাজ্যের নির্যাতিত সাধারণ মানুষ যাদের জন্য স্রষ্টার ভিন্ন সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের শুধু আশ্বাসই দেয়নি যে ,নাঙ্গাপদরা আবৃতপদদের ওপর বা অস্ত্রধারীদের ওপর অস্ত্রহীনরা বিজয়ী হবে ;বরং সেই সাথে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক চিন্তা-যা জালেমদের ওপর মজলুমদের চিরস্থায়ী বিজয়ের বার্তা বহন করে এনেছিল। এই চিন্তা ও অনুভূতি এই রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ মানুষের মাঝে এতটা তীব্র হয়ে ওঠে যে ,তারা তাদের শাসকবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে ইসলামের ধ্বজাধারীর পাশে দাঁড়িয়ে সমস্বরে ফরিয়াদ জানাতে লাগল। সে সময় হতে চৌদ্দশ ’ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এ চিন্তার নৈতিক প্রভাব এ ধর্মে বিশ্বাসী জাতিসমূহের মধ্যে পূর্বের মতই বিদ্যমান রয়েছে ,অথচ আরব বিজেতাদের বিজয়ের কোন ক্ষুদ্র চিহ্নও এ জাতিগুলোর মধ্যে এখন অবশিষ্ট নেই। ”
(বিশিষ্ট চিন্তাবিদ) রাহনামার মতে ইসলাম অর্থহীন বিষয়াবলীর সম্পৃক্ততা হতে জীবনকে মুক্ত করে দৃঢ় অর্থপূর্ণ জীবন সম্পৃক্ততার সৃষ্টি করে এবং নব চিন্তা ও দর্শন উপস্থাপন করে। তাই ইসলামের বিজয় কোন জাতির ওপর নব চিন্তা ও বিশ্বাসের বিজয় ,অন্যায় ও অবিচারের ওপর ন্যায় আকাঙ্ক্ষা ও সত্যপরায়ণতার বিজয়। ইসলামের বিজয়ের পশ্চাতে মূলত আরবরা নয় ;বরং বিজিত অঞ্চলের বঞ্চিত-নির্যাতিত ,সত্য ও ন্যায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত সাধারণ মানুষের জাগরণ মূল ভূমিকা পালন করেছিল। তারা এক ঐশী চিন্তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অত্যাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সার্বিক বিদ্রোহ করেছিল।
ড. আবদুল হুসাইন যেররিন কুব তাঁর ‘ কর-নমেয়ে ইসলাম ’ গ্রন্থের 13 পৃষ্ঠায় ইসলামের আড়ম্বরপূর্ণ ও মর্যাদাবান সভ্যতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন , “ যে বিষয়টি মুসলমানদের জ্ঞানগত ও বৈষয়িক উন্নয়নকে সম্ভব করে তুলেছিল তা হলো ইসলামের বাস্তবতা। ইসলাম জ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যে জীবনসঞ্চারী উদ্দীপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। প্রাচীন পৃথিবীর গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে এর প্রসারে পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতার জন্ম দেয় ও এর পথকে সুগম করে। যখন খ্রিষ্টধর্ম ও তাদের যাজকগণ মানুষকে জ্ঞান বর্জন করে উপাসনালয়ে নিজেদের সীমিত করার উপদেশ দিচ্ছিল তখন ইসলাম জ্ঞান ও শিল্পের পূর্ণতা ও উন্নয়নের পথকে সহজীকরণের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল।
ইসলাম যখন জ্ঞানের প্রসারের এই ময়দানে প্রবেশ করে তখন ভারসাম্য ও সহনশীলতার পথ অস্তগামী ছিল। সে সময়ের দুই পরাশক্তির (বাইজান্টাইন ও ইরান) একটি বাইজান্টাইনীরা খ্রিষ্টধর্মের গোড়ামিতে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং প্রতিদিনই তারা জ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলেছিল। জাস্টিনিয়ান দর্শনের চর্চাকে নিষিদ্ধ করে রোমীয়দের সঙ্গে সভ্যতা ও জ্ঞানের সম্পর্কের আশু বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। তৎকালীন ইরানেও অপসৃয়মান সাসানী শাসক খসরু অনুশিরওয়ানদের জ্ঞান ও চিন্তার প্রতি যে অনীহা ছিল তা এ ভূখণ্ডে সকল প্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের পথকে অসম্ভব করে তুলেছিল।
বারজুইয়া তাবিব তাঁর ‘ কালিলা ও দিমনা ’ গ্রন্থের ভূমিকায় তৎকালীন শাসকদের চিন্তাগত গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার প্রতি ইশারা করেছেন। এরূপ জাতিগত গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সমাজে ইসলাম নতুন জীবন ফুঁকে দিয়েছিল। ইসলাম এক ইসলামী রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) গঠনের মাধ্যমে-যার প্রাণকেন্দ্র ইরাক বা সিরিয়া নয় ,ছিল কোরআন-বর্ণ ও জাতিগত গোঁড়ামিকে বিশ্ব মাতৃভূমির ধারণার মধ্যে নিশ্চি হ্ন করে এর সমাধান দেয়। খ্রিষ্টান ও মাজুসীদের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিপরীতে ইসলাম জ্ঞান ও জীবনের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ এবং আহলে কিতাবদের সঙ্গে সহনশীলতা ও সম্মানজনক সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। ইসলামের বিজয়ের ফলশ্রুতিতে এ বিস্ময়কর বৃক্ষের-যা না পূর্বের না পশ্চিমের কারণে-সৃষ্টি হয়েছিল। ”
ড. যেররিন কুবের দৃষ্টিতে ইসলাম এমন এক পৃথিবীতে পা রেখেছিল যা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সে পরিস্থিতিতে ইসলাম জ্ঞানার্জন ,ধর্মীয় ও জাতিগত গোঁড়ামি পরিত্যাগ ,আহলে কিতাবগণের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতি নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোরআনের ভাষায় যে শৃঙ্খল তৎকালীন বিশ্ববাসীদের হাত ,পা ও চোখ বেঁধে রেখেছিল তা ছিন্ন করেছিল এবং এক নতুন ও ব্যাপক সভ্যতার জন্ম ও উত্তরণের পথকে সুগম করেছিল।
জার্মান অধ্যাপক আর্নেস্ট কুনেল যিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ ইসলামী শিল্পকলা ’ অনুষদে 1935-1964 সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন তাঁর ‘ ইসলামী শিল্পকলা ’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন , “ অভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব ইসলামী বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসমূহে খ্রিষ্টীয় বিশ্বে তাদের (খ্রিষ্টধর্মের) অভিন্ন বিশ্বাসের প্রভাব হতে অধিক। অভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই অতীতে ভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতিসমূহকে এক সূত্রে গেঁথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। শুধু নৈতিকতার ক্ষেত্রে নয় ,এমনকি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকেও আশ্চর্যজনকভাবে এ লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। এই ঐক্য সৃষ্টির পশ্চাতে যার ভূমিকা সর্বাধিক ছিল তা হলো কোরআন-যা তাদের জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। কোরআন তার অবতীর্ণ হবার ভাষায় প্রচারিত হওয়ায় আরবী লিখন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে সম্পর্কিত করে এবং সকল শিল্পের সৃষ্টিতে মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত শিল্পকলার মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তা এ ক্ষেত্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহ সৃজনশীলতার প্রয়োজনে বিশেষ স্থাপত্য গঠনে তৈরি হলেও বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনে ব্যবহৃত নকশাই গৃহীত হতো।40
তিনি আরো বলেছেন , ‘ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য তা হলো মধ্যযুগের কঠোর রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও ইসলামী বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যা তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনই শুধু নয় ,সে সাথে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও বিনিময় প্রক্রিয়াকেও সহজ ও ত্বরান্বিত করেছিল। আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী হতে বোঝা যায় ,এক অঞ্চল ও রাষ্ট্রের মানুষ অপর অঞ্চল ও রাষ্ট্রের মানুষের অবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও শিল্পের দ্রুত স্থানান্তরের বিষয়ে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পাশ্চাত্য বিশ্বদৃষ্টির শিক্ষার্থীদের জানতে হবে ইসলামী বিশ্বে বিশেষ এক পরিবেশ ক্রিয়াশীল ছিল যা যে কোন সৃজনশীল সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করত। ” 41
এই গবেষক যা বলেছেন তা শুধু ইরানেই নয় ;বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এরূপ ছিল এবং ইরান এর চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল না। এই বিশেষজ্ঞের বক্তব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টি হলো তিনি বলেছেন ,মুসলমান জাতি-বর্ণের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পরস্পর সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ ইসলামই প্রথমবারের মত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণেই এরূপ ব্যাপক ও আড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এরূপ ইতিবাচক মতসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।
এ ধরনের ইতিবাচক মতামতের বিপরীতে নেতিবাচক কিছু মতও বিদ্যমান রয়েছে যা পর্যালোচনার দাবি রাখে। এ ধরনের মতানুযায়ী আরবদের ইরান আক্রমণ ও বিজয় ইরানীদের জন্য বিপর্যয় ছিল। এ বিপর্যয় মোগল বা আলেকজান্ডারের আক্রমণের ন্যায় মারাত্মক ছিল। বিশেষত মোগলদের আক্রমণ যেমন করে এক প্রতিষ্ঠিত ও বিন্যাসিত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল ,আরবদের আক্রমণও তেমনি প্রাচীন এক সভ্যতাকে চুরমার করে দিয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর তৃতীয় ,চতুর্থ ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে ইরানীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সেবায় যে আত্মনিয়োগ করেন তা তাদের প্রাচীন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণেই ;এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের ইসলাম-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ারই দৃষ্টান্ত। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যা করেছে তা হলো দু ’ শতাব্দী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। দু ’ শতাব্দী পর যখন ইরান আরবদের প্রভাবমুক্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে তখন তারা পূর্ব বৈশিষ্ট্য ফিরে পায় এবং ঐতিহ্যবাহী সে পথে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। এভাবেই ইরানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে।
অবশ্য কোন ইরানী বা অ-ইরানী গবেষকদের এরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায় না। শুধু যে সকল ব্যক্তির কথায় বিশেষ এক ধরনের প্রচারণার রং ও গন্ধ রয়েছে তাদেরই এরূপ বলতে শোনা যায়। সম্প্রতি এরূপ মন্তব্য উস্কানিমূলক সাহিত্যিক রং দিয়ে অধিক হারে প্রচার করা হচ্ছে।
ফারিদুন অদামিয়ত তাঁর ‘ আমির কবির ও ইরান ’ শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন , “ ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির কেন্দ্র হিসেবে আরব ভূখণ্ডের মত একটি প্রাথমিক সমাজ অপরিহার্য ছিল এবং এ কারণেই ইসলাম সেখানে আবির্ভূত হয়। এ ধর্ম আরব উপদ্বীপের পূর্ববর্তী ধর্ম ও বিধানের মিশ্রণ হিসেবে দ্বিমুখী ও স্থিতিস্থাপক শিক্ষা সম্বলিত ছিল। তাই যখন এ ধর্ম ইরানে প্রবেশ করে তখন এ দেশের সামাজিক গতিকে আকস্মিক বিচ্যুতির পথে পরিচালিত করে। এটি আরব ভূখণ্ডের মত প্রাথমিক সমাজে যতটা কল্যাণ বয়ে এনেছিল ইরানের জন্য ঠিক ততটা অকল্যাণ ও ধ্বংস ডেকে এনেছিল। ইরানীরা তাদের সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল । তাই তাদের আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সময় দীর্ঘায়িত হয় নি। তারা সকল দিক হতে বিরোধিতার ঐকতান বাজাতে শুরু করল। সাধারণত কোরআনের নাসখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) আয়াতের সাহায্য নিয়ে তারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে লাগল।
...একদিকে ইসলামের কিছু নেতিবাচক শিক্ষা ,যেমন দুনিয়াকে ধ্বংসশীল ,মৃত ও মুমিনদের জন্য বন্দীশালা হিসেবে দেখা ,অন্যদিকে হিন্দু দর্শনের স্রষ্টার মধ্যে বিলুপ্তির ধারণাসমূহ প্রচারের ফলে ইরানের মানুষ দুনিয়ার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা এ হতে মুক্তির পথ খুঁজছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা ,যেমন সম্পদ পুঞ্জীভূত করা গুনাহ্ ,কারুকার্যময় শিল্পকে নিষিদ্ধ ,মানুষের রিযিক নির্ধারিত ,তার ভাগ্য অবধারিত ও নির্দিষ্ট ,তাকদীরে বিশ্বাস প্রভৃতি ধারণা এ সমাজে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে। ইসলামের বিরোধীরা প্রথম দিকে নেতিবাচকভাবে ইশরাকী (দর্শনের একটি শাখা) ও তাসাউফের (সুফী) দর্শন দ্বারা একে মোকাবিলা করতে গিয়ে তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। ভাগ্যে বিশ্বাস ইরানে ব্যাপক প্রচলন লাভ করার ফলশ্রুতিতে ইরানের বস্তুগত জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হলো। দুনিয়া বিমুখতা ,অলসতা ,ধ্বংসকামিতা ,ভিক্ষা প্রবণতা ,দরবেশী জীবন এ সবই ইরানীরা ইসলাম হতে লাভ করেছে। এ সব শিক্ষা ইরানে প্রসার লাভের মাধ্যমে সামাজিক পতনের সূচনা ও ভিত্তি রচিত হয়েছিল। ”
এ লেখক একদিকে বলেছেন ইসলামের আবির্ভাবের কেন্দ্র হিসেবে আরব ভূখণ্ডের মত প্রাথমিক একটি সমাজ অপরিহার্য ও উপযোগী ছিল। আবার অন্যদিকে বলছেন অলসতা ,ধ্বংসকামিতা ,ভিক্ষা প্রবৃত্তি ও দরবেশী জীবন ইসলামী শিক্ষার ফসল। তবে কিরূপে এ ধর্ম তার শিক্ষার মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডের মত প্রাথমিক সমাজকে ক্ষমতা ,ঐক্য ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করতে সক্ষম হলো ? দ্বিতীয়ত যদি এমনটিই হতো তাহলে ইসলামী জাতিসমূহ ইসলামের আগমণের শুরুতেই পতনের মুখোমুখি হতো। যেহেতু দুনিয়া মৃতদেহ তাই নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করে তাকদীরের ওপর ভরসা করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকত ও নিজেকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত ,কিন্তু এর বিপরীতে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইসলামের আবির্ভাবের ফলে উত্তর আফ্রিকা হতে পূর্ব এশিয়ার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ও আড়ম্বরপূর্ণ গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এক নজীরবিহীন সভ্যতার জন্মদান করেছিল। এ অবস্থা ছয় শতাব্দী অব্যাহত থাকে এবং তার পরবর্তী সময়ে এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্থবিরতা ও পতনের মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এই লেখক জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে ইসলামের নৈতিক যুদ্ধকে (যা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ ও আত্মীকরণকে অনাকাক্সিক্ষত বলে ঘোষণা করে) কর্মবিমুখতা ও উৎপাদনহীনতা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন ,অথচ ইসলাম সেবা ও জীবনের উন্নয়নের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন ,শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ ও একে উৎসাহিত করেছে । তিনি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের তাকওয়া ও যুহদের ধারণা-যা ইবাদত ও কর্মকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে-তার সঙ্গে ইসলামের তাকওয়া ও যুহদের পার্থক্য করেননি বা করতে চাননি ,অথচ ইসলামের যুহদ অর্থ দুনিয়া বিমুখতা নয় যেমনি এর তাকওয়ার অর্থও ভিন্ন-যা উন্নত চিন্তাশক্তি ও হৃদয়ের পবিত্রতায় বিশ্বাসী।
এ সবের চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো ইউরোপীয়দের অনুকরণে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসকে মুসলমানদের পতনের কারণ হিসেবে দেখান। তার জন্য উত্তম ছিল এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের হাতে অর্পণ করা। আমরা ‘ মানুষ ও তার গন্তব্য ’ 42 (ফার্সী ভাষায় লিখিত) নামক গ্রন্থে ইসলামী পরিভাষায় ভাগ্যের (ক্বাযা ও ক্বাদর) অর্থ এবং মুসলমানদের পতনের পেছনে এর আদৌ কোন প্রভাব ছিল কিনা সে বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি।
স্কুল-কলেজের বইগুলোতেও এ চিন্তার প্রচার কম-বেশি লক্ষণীয়।43 পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা এলেই এ চিন্তার প্রচারণা চালানো হয়েছে। আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি পুস্তক হতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করছি। ‘ ইরানের মানবিক ভূগোল ’ নামক পুস্তকে বলা হয়েছে :
“ সামানী আমলে খুজিস্তানের জানদীশাপুরে যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় তা ইরানীদের জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহের প্রমাণ। অকাট্য সত্য ,তৎকালীন সময়ে ইরানীরা অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছিল। দুঃখজনকভাবে সেগুলো ভিনদেশী শত্রুদের আক্রমণে নিশ্চি হ্ন হয়েছে। এখন শুধু তৎকালীন গ্রন্থগুলোর কিছু নাম আমাদের নিকট অবশিষ্ট আছে। ইরানের ওপর আরবদের প্রভুত্ব আমাদের জ্ঞান ও সাহিত্যের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ তারা জ্ঞান ,সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিরাট অংশ ধ্বংস করে এবং তাদের ভাষা ও লিখনরীতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ইবনে মুকাফ্ফা ,মুহাম্মদ যাকারিয়া রাযী ,আবু আলী সিনা ,আবু রাইহান বিরুনী ,আবু নাসর ফারাবীর মত বড় বড় ইরানী মনীষিগণ বাধ্য হয়ে আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর ইরানীদের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে যখন ইরান স্বাধীনতা লাভ করল তখন আধুনিক ফার্সী ভাষা সর্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করল। ফলে লেখক ,বক্তা ,কবি ,সাহিত্যিকগণ ,যেমন রুদাকী ,ফেরদৌসী ,ওমর খাইয়াম ,মাসউদ সাদ সালমান ,মৌলাভী (জালাল উদ্দীন রুমী) ,সা ’ দী ,হাফিযসহ এ দেশের শত শত প্রতিভা তাঁদের চমৎকার লেখনীর মাধ্যমে বিশ্ব-সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। ”
এ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইরান জ্ঞান ,শিল্প ও সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং আরব মুসলমানদের বিজয় ইরানীদের মানসিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। আরবগণ তাদের ভাষা ও লিপি ইরানীদের ওপর এমনভাবে চাপিয়ে দেয় যে ,আরবদের আক্রমণের চারশ ’ বছর পরের ইবনে সিনা ও গাজ্জালীরা আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনায় বাধ্য হয় অর্থাৎ ইরানীরা স্বাধীনতা লাভের দু ’ বা তিনশ ’ বছর পরও আরবদের ভয়ে আরবীতে গ্রন্থ রচনা করত। এ পুস্তকের বর্ণনানুসারে সাহিত্যিক ও কবিগণ তখনই সাহিত্য ও কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন যখন আরবদের হতে মুক্তি লাভ করেছেন এবং তাঁদের এ ফার্সী-সাহিত্য চর্চা ইসলাম ও আরবদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটেছিল। আমরা পূর্বে ইরানীদের ওপর আরবী ভাষা চাপিয়ে দেয়ার কল্পকাহিনী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফার্সী ভাষার পুনরুজ্জীবনের মিথ্যা প্রচারণার জবাব দিয়েছি। আমরা পরবর্তীতে তাদের আরেকটি মিথ্যা দাবি-আরবদের হাতে ইরানের জ্ঞানকেন্দ্রগুলোর ধ্বংস সাধন বিশেষত জানদীশাপুর মহাবিদ্যালয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।
কেউ কেউ এ থেকেও এক ধাপ এগিয়ে ইরানে ইসলামের আগমনকে দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁরা ইরানীদের সকল মন্দ চরিত্র আরবদের ইরান আক্রমণ ও ইসলামের অনুপ্রবেশের ফসল বলে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ ফার্সী 1345 সালের (খ্রিষ্ট 1967) 3 আবানে প্রকাশিত ‘ ফেরদৌসী ’ প্রত্রিকার একটি প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ প্রবন্ধের লেখক তাঁর এ প্রবন্ধে জালাল আলে আহমাদের ‘ পাশ্চাত্য প্রবণতা ’ গ্রন্থের উত্তর দিয়েছেন। আলে আহমাদ দাবি করেছেন ,বর্তমান প্রজন্মের অবক্ষয়ের মূল কারণ যান্ত্রিকতা ও পাশ্চাত্যপ্রবণতা। তিনি ‘ পাশ্চাত্যঘেষা ’ র সংজ্ঞায় বলেন ,
‘ পাশ্চাত্যঘেষা (পাশ্চাত্যসেবী) ব্যক্তি অধার্মিক। কোন কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। আবার কোন কিছুতে অবিশ্বাসীও নয়। সে এক পরিত্যক্ত মানুষ। সে স্রোতের অনুকূলে চলে। সব কিছুই তার নিকট সমান। সে তার ও তার গাধার চিন্তা করে। তার গাধা পুল পেরিয়ে গেলে পুলের আর কোন প্রয়োজন মনে করে না। তার না ঈমান আছে ,না নীতি। না আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে ,না মানবতায়। না সে সামাজিক পরিবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী ,না ধর্মহীনদের দলে রয়েছে। কখনও কখনও সে মসজিদে যায় যেমনটি সিনেমায় বা কোন দলের সভায়ও তাকে দেখা যায়। কিন্তু সকল স্থানে সে শুধুই দর্শক ,ফুটবলের দর্শকের ন্যায়। সব সময় তাকে গর্তের কিনারায় দেখা যায় ,কোন সময়েই গর্তের মাঝে পাওয়া যায় না। কখনই সে পুঁজি বিনিয়োগ করে না ,হোক সে পুঁজি বন্ধুর মৃত্যুতে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন বা যিয়ারতগাহের প্রতি দৃষ্টি দান বা কিছুক্ষণ একাকী চিন্তা করা। সে একাকিত্বকে ভয় পায়-এতে অভ্যস্ত নয় ,তাই এ থেকে দূরে থাকে। যদিও সে সকল স্থানে বর্তমান ,কিন্তু কখনই তাকে কোন বিষয়ে ফরিয়াদ জানাতে ও প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। তাকে কোন বিষয়ের কারণ জানার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করতেও দেখা যায় না। ‘ পাশ্চাত্যঘেষা ’ ব্যক্তি স্বার্থপর ও সুযোগসন্ধানী। তাই প্রতিটি শ্বাসকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে নেয় (অবশ্য দার্শনিক অর্থে নয়)। ‘ পাশ্চাত্যসেবী ’ দের কোন ব্যক্তিত্ব নেই ,এরা মূলহীন...। ’
‘ ফেরদৌসী ’ পত্রিকা আলে আহমাদকে উত্তর দিয়েছেন এভাবে :
“ তুমি যেরূপ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছ তা কি শুধুই বিগত দু ’ শ ’ বছরে এসেছে ?... না ;বরং তোমার বর্ণিত এরূপ অধার্মিক ,চাটুকার ,মিথ্যাবাদী ,ভূমিহীন ,নিঃস্ব ও চিন্তা-বিশ্বাসহীন গত তেরশ ’ বছর হলো ইরানে সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অলুক্ষণে ও কালো দিবস যে দিন মাদায়েনের প্রাসাদের প্রহরীরা আরবদের স্বাগত জানিয়ে প্রাসাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে ‘ মহাসম্মানিত বিচারক এসেছেন ’ বলে চিৎকার করেছিল সে দিন এ অবৈধ সন্তানের বীজ রোপিত হয়। যে দিন নাহাভান্দের যুদ্ধে দুর্ভাগা ইরানী সেনাপতি ফিরুযন কাপুরুষ আরবদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে পরাজিত হয় সে দিন এই অশুভ সত্তার জন্ম হয়। এখন তেরশ ’ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এরূপ ব্যক্তিদের দেখি যারা তাকিয়া (সত্যকে প্রকাশ হতে বিরত) করে ,অন্যদের ওপর বিশ্বাস করে না ,যেহেতু সন্দেহ প্রবণ ও মন্দ ধারণা পোষণকারী সেহেতু মন খুলে কথা বলে না ,তাদের কোন প্রতিবাদ ,যাচাই-বাছাই ও যুক্তির ময়দানে দেখা যায় না। ”
একই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় লেখা হয়েছে :
“ এক হাজার বছরের কিছু অধিক সময় পর আরবদের ইরান আক্রমণের ফল এ জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ভূখণ্ডের নৈতিক ,আত্মিক ও জাতিগত সকল মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমাদের যুদ্ধংদেহী ,আক্রমণাত্মক ও প্রতিদ্বন্দ্বী অনুসন্ধানের দৃঢ় মানসিকতা ভীরুতা ,কাপুরুষতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় পরিণত হয়েছে। কত জীবাণু আমাদের প্রাণের ওপর এখন হামলা চালাচ্ছে! ”
ঐ পত্রিকারই 1347 ফার্সী সালের (1369 খ্রিষ্টাব্দ) উরদিবেহেশতে প্রকাশিত 23 নং সংখ্যায় ‘ কবিতায় রূপকের ব্যবহার ’ শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়েছে , “ আমরা জানি ইরানে আরবদের হামলায় আমাদের মাতৃভূমির অধিবাসীদের চরম খেসারত দিতে হয়েছিল। আরব ও পারস্য সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইরানীদের রাজনৈতিক পরাজয় পারস্য সভ্যতার নৈতিক পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। আরবগণ ইরানী সভ্যতাকে তিরস্কার করত ও ইরানীদের ‘ মাওয়ালী ’ অর্থাৎ দাস বলে সম্বোধন করত... ইরানীদের আনন্দ উৎসবসমূহ বন্ধ হয়ে গেল। ইরানীরা মধ্যাহ্ন ও নৈশ ভোজের পর যে মদ পান করত তা শয়তানের কাজ বলে নিষিদ্ধ করা হলো। আমাদের অগ্নিমন্দিরসমূহের সকল অগ্নি নিভিয়ে ফেলা হলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইরানের জনগণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ইরান জাতি ছাইভস্মের মধ্য হতে অগ্নিপক্ষির ন্যায় জেগে উঠল এবং অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ইরানী প্রতিভাগণ ,যেমন আবু রাইহান বিরুনী ,ফেরদৌসী ,খাইয়াম ,আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফা ,রুদাকী ,দাকীকী ,যাকারিয়া রাযী ,বাইহাকীরা জাগ্রত হলেন ও দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটালেন। ”
ইংরেজ স্যার জন ম্যালকম তাঁর ‘ তারিখে ইরান ’ (ইরানের ইতিহাস) গ্রন্থে বলেছেন , ‘ রাজ্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য ইরানীদের অবিচলতা ও একগুঁয়েমী তৎপরতায় আরবীয় নবীর অনুসারিগণ এতটা ক্ষিপ্ত হলো যে ,ইরানী জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে এমন সকল চিহ্ন তারা ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিল। শহরগুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো ,অগ্নিমন্দিরগুলো ভস্মীভূত করা হলো ,উপাসনালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবকদের হত্যা করা হলো ,জ্ঞান ,বিজ্ঞান ,ইতিহাস ,ধর্ম সম্পর্কিত সকল গ্রন্থ ধ্বংস করা হল। তৎকালীন গোঁড়া আরবগণ কোরআন ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে জানত না এবং জানার চেষ্টাও করত না। পুরোহিতদের ‘ মাজুস ’ (অগ্নি উপাসক) ও ‘ জাদুকর ’ এবং তাঁদের পবিত্র গ্রন্থকে ‘ জাদুর গ্রন্থ ’ নামকরণ করা হলো । গ্রীস ও রোম সভ্যতার উদাহরণ হতে বোঝা যায় সে পারস্যের ন্যায় সভ্যতার কি পরিমাণ গ্রন্থ ছিল যা এ আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।
এ সকল তথাকথিত ঐতিহাসিকের কথায় নতুনত্বের গন্ধ পাওয়া যায় যা কোন ঐতিহাসিক দলিল ও পাণ্ডুলিপিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের ধরে নিতে হবে এ সব ইতিহাস বৈধভাবে জন্ম লাভকারী মনুষ্যরূপ কোন প্রাণীর চোখে পড়ে নি ও তাদের হাতে পৌঁছে নি। তাই তার গ্রন্থসূত্রের নামও প্রকাশিত হয় নি। বাধ্য হয়ে এমন ভাবাই স্বাভাবিক। কারণ তা না ভাবলে এই মহান লেখকদের চরম ও পরম সত্যবাদিতার পেছনে সৎ মনোভাব ছিল মনে হতে পারে এবং তাঁরা ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে এরূপ গ্রন্থ রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নি বলে সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ সকল লেখকের বর্ণনা ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিলপত্রের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ প্রথমত সকল ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যের বিপরীতে এই ব্যক্তিবর্গের মতে ইরানীরা তাদের সাম্রাজ্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অর্থাৎ আনুমানিক চৌদ্দ কোটি ইরানীর তৎকালীন সমাজ চার লক্ষ সৈনিক বিপুল সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সর্বোন্নত যুদ্ধ কৌশল নিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করেও পঁয়তাল্লিশ হাজার নাঙ্গা পায়ের আরব মুসলমানের হাতে পরাস্ত হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে নবীন ধর্ম ইসলামের আদর্শের আকর্ষণ এবং অন্যদিকে প্রাচীন ধর্ম ,পুরোহিতগণ ও শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি ইরানীদের অসন্তোষের কারণে এ পরাজয় ঘটে নি ;বরং এ ব্যক্তিদের মতে যেহেতু ইরানীরা অক্ষম এক জাতি সেহেতু মরণপণ সংগ্রামের পরও তারা ক্ষুদ্র এক দলের নিকট পরাস্ত হয়েছিল।
দ্বিতীয়ত এদের মতে ইরানের শহরগুলো আরবদের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়েছিল। প্রশ্ন হলো শহরগুলো কোথায় অবস্থিত ছিল ? সেগুলোর নাম কি ? ইতিহাসে আদৌ ধ্বংসপ্রাপ্ত এরূপ কোন শহরের নাম উল্লিখিত হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে কেন তিনি সেই ইতিহাস গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করেন নি ? সার্জন ম্যালকমের নিকট এটিই প্রশ্ন।
তৃতীয়ত এই ব্রিটিশ লেখকের মতে উপাসনালয়সমূহের পুরোহিত ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের হত্যা করা হয় এবং অগ্নিমন্দিরসমূহ ভস্মীভূত করা হয়। তাহলে মাসউদী ,মুকাদ্দাসীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতেও ইরানে অগ্নিমন্দিরসমূহ ছিল বলে যে উল্লেখ করেছেন ও পুরোহিতদের নিকট প্রাচীন গ্রন্থ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি কেন আলোচনা করেন নি ? আরব শাসকরা আহলে কিতাব হিসেবে মাজুসদের উপাসনালয় সংরক্ষণের জন্য ইসলামী বিধান মতে চুক্তিবদ্ধ হতেন ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন বলে যে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন কেন তিনি তা উপেক্ষা করেছেন ?
চতুর্থত ইরানীদের নিকট বর্তমান ধর্ম ,বিজ্ঞান ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করা হয় বলে তিনি যে উল্লেখ করেছেন তা আমরা ‘ গ্রন্থ ভস্মীভূতকরণ ’ শিরোনামে পরে আলোচনা করব।
পঞ্চমত আরবগণ পুরোহিতদের জাদুকর ও তাদের পবিত্র গ্রন্থকে যাদুর গ্রন্থ বলে অভিহিত করত বলে যে এই লেখক উল্লেখ করেছেন তা প্রথমবারের মত এমন ব্যক্তিদের নিকট হতেই শোনা যায় যাদের এরূপ কথার পেছনে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে।
এখানে ইসলাম ও ইরান সম্পর্কে উত্থাপিত বিপরীতমুখী দু ’ টি দৃষ্টিভঙ্গিই আমরা উল্লেখ করেছি। এখন আমরা কোন্ মতটিকে গ্রহণ করব ? আমরা কি এ মতকে গ্রহণ করব ,যে দাবি করেছে ইসলামের আবির্ভাবের যুগে ইরানসহ অন্যান্য অঞ্চল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল ,মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল ,শাসকবর্গ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ,সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বেড়ে গিয়েছিল ,সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট ও অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্ব এক পরিবর্তন ও বিনির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করছিল। এমন মুহূর্তেই ইসলামের আগমন ঘটে এবং এই মহান কর্ম সম্পাদন করে। ইসলাম পুরাতন জরাজীর্ণ মানদণ্ডকে পরিবর্তন করে ও সকল শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে সকলকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করে অর্ধমৃত জাতিসমূহের দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। ইরানী জাতিও তাদেরই অন্যতম যারা নতুন জীবনপ্রাপ্ত হয়েছিল।
নাকি আমরা এর বিপরীত অবস্থান নিয়ে বলব যে ,আমাদের সব কিছু ছিল ,ইসলাম এসে আমাদের নিঃস্ব করে ফেলে। পূর্বেও আমরা বলেছি সৌভাগ্যবশত ইসলামের আবির্ভাবের সমকালের ইরানের ইতিহাস স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে মোটামুটি অধ্যয়নেই তা আমাদের নিকট পরিষ্কার হবে। ইসলামপূর্ব ইরানের চিন্তা ও বিশ্বাসগত অবস্থা ,সমাজে ঐ সকল বিশ্বাসের প্রভাব ,তৎকালীন ইরানের সামাজিক ,ধর্মীয় ,পারিবারিক ,রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দান করাই এখানে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর ইতিহাস হতে ইসলামের চিন্তা-বিশ্বাস ,সামাজিক ,রাজনৈতিক ,পারিবারিক ও নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এর তুলনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। প্রথমে তৎকালীন ইরানী সমাজের চিন্তা ও বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা করব।
চিন্তা ও বিশ্বাসগত অবস্থা
এ পর্যায়ে আমদের আলোচনার বিষয়বস্তু ইসলামের আবির্ভাবের সমসাময়িক ইরানের সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস। আমরা আপাতত তৎকালীন সময়ের দার্শনিক
চিন্তা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করছি না। তাই সামানী আমলে ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের বাইরে স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক চিন্তা-বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল কি না ,থাকলে কিরূপ মতের তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। কারণ যদি তেমন কোন মতবাদ থেকেও থাকে সেরূপ দার্শনিক মত বাস্তবে সাধারণ মানুষের মানসিকতায় কোন প্রভাব রাখত না। যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব সেহেতু অবশ্যই তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে।
নিঃসন্দেহে ইসলাম ইরানকে এক নতুন ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দান করেছিল। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ইরানের মানুষ নজীরবিহীনভাবে ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের পূর্ব পুরুষের চিন্তা-বিশ্বাসকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। তবে এ গ্রহণ আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক ছিল না ;বরং মন্থর গতিতে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়েছিল এবং বিশেষত ইরানীদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভের পরবর্তী সময়ে এটি ঘটেছিল।
এ আলোচনাটি এ দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় যে ,ইসলাম বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর তা হলো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই বিজিত জাতির আত্মাকে জয় করে তাদের আত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি।
গুসতাভ লুবুন তাঁর ‘ ইসলাম ও আরব সভ্যতার ইতিহাস ’ গ্রন্থে বলেছেন , “ যে সকল জাতি ইসলামী শরীয়ত ও এর বিধানকে গ্রহণ করেছিল ,এ শরীয়ত তাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পৃথিবীতে খুব কম ধর্মই পাওয়া যায় যা তার অনুসারীদের হৃদয়ে ইসলামের ন্যায় গভীরভাবে প্রবেশের ক্ষমতা ও প্রভাব রাখতে পেরেছে ;বরং হয়তো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যাবে না যা এতটা প্রভাবশীল হতে পেরেছিল। অর্থাৎ যেমনভাবে কোরআন মূলকেন্দ্র হিসেবে সার্বিক ও নির্দিষ্ট (সাধারণ ও বিশেষ) সকল বিধানসহ মুসলমানদের সকল কর্মকাণ্ড ও আচরণে প্রকাশিত হয়েছে ,অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ তা পারেনি। ” 44
অপর যে দিক হতে এ আলোচনাটি আকর্ষণীয় তা হলো ইসলাম গ্রহণকারী জাতিসমূহের মধ্যে ইরানীরা বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেটি হলো ইরানীদের ন্যায় অন্য কোন জাতি এত সহজে তার পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করে নি এবং তাদের ন্যায় এত আন্তরিকভাবে ,ভালবেসে ও একাগ্রতার সাথে নতুন ধর্মের চিন্তা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নি। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ দুজী বলেছেন , “ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জাতিটি ধর্ম পরিবর্তন করে সেটি হলো ইরানী জাতি। কারণ আরবরা নয় ,ইরানীরাই ইসলাম ধর্মকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর স্থাপন করে। ” 45
তাই বাধ্য হয়ে তৎকালীন ইরানী সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারার একটি পর্যালোচনা আমরা করব এবং ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সঙ্গে তার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব ইসলাম চিন্তাগতভাবে ইরানকে কি দিয়েছে এবং ইরান হতে ইসলাম কি চিন্তাসমূহ গ্রহণ করেছে। তৎকালীন ইরানের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার জন্য প্রথমেই দেখব সে সময় ইরানে কি কি ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।
ধর্ম ও সম্প্রদায়
সামানী শাসনামলে বাহ্যিকভাবে একমাত্র যারথুষ্ট্র ধর্মের শাসন ছিল বলে মনে হলেও এমনটি নয়। যদিও যারথুষ্ট্র ধর্ম এ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল কিন্তু অন্যান্য ধর্মসমূহেরও সংখ্যালঘু হিসেবে পর্যাপ্ত অনুসারী ছিল। এদের কেউ কেউ যারথুষ্ট্রকে নবী জানা সত্ত্বেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত ছিল ,আবার অনেকের যারথুষ্ট্রদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না এবং যারথুষ্ট্রকে নবী হিসেবেও মানত না।
সাঈদ নাফিসী তাঁর ‘ তারিখে এজতেমায়ীয়ে ইরান ’ (ইরানের সামাজিক ইতিহাস) গ্রন্থের 2য় খণ্ডে সামানী শাসনামলের সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে ধর্মীয় বিভেদকে দেখিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন ,যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণের জোর-জবরদস্তি ও অনাচারের কারণেই বিভিন্ন দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সামাজিক অসন্তোষ বেড়ে গিয়েছিল । তিনি বলেন , “ তৎকালীন সময়ের সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তিতে যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বিশেষত ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের মধ্যে যাঁরা সামানী রাজ দরবারে উচ্চপদ দখল করেছিলেন তাঁরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন ,যেমন সম্পদের মালিকানা ,উত্তরাধিকার ,বিবাহ ইত্যাদির পরিবর্তন ,পরিবর্ধন ,রহিতকরণ ,নতুন আইন প্রবর্তন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দানের পূর্ণ অধিকার রাখতেন। সামানী সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাঁদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারও বেড়ে গিয়েছিল। ইরানের সাধারণ মানুষেরাও তাদের অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। তারা এ অশান্ত অবস্থা হতে বের হওয়ার চেষ্টায় রত ছিল। এ লক্ষ্যে তারা ‘ মাযদিস্তী যারথুষ্ট ’ ধর্ম যা রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত ছিল ও ‘ বেছদীন ’ নামে পরিচিত ছিল তা হতে মুখ ফিরিয়ে যারথুষ্ট্র ধর্মের নতুন দুই শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তাদের একটি হলো ‘ যারওয়ানীয়ান ’ যাদের বিশ্বাস ছিল আহুরামাযদা (সত্যের খোদা) ও আহ্রিমান (মন্দের খোদা) এ দু ’ জনই এদের হতে উন্নত ও প্রাচীন এক খোদা যার নাম ‘ যারওয়ান আকারনু ’ অর্থাৎ সীমাহীন সময় হতে জন্ম লাভ করেছে। অপরটি হলো ‘ কিউমারসিয়ান ’ যাদের বিশ্বাস ছিল আহ্রিমান স্বতন্ত্র কোন সত্তা ছিল না এবং যখন আহুরমাযদা তাঁর কর্মে সন্দেহ পোষণ করেন তখন তাঁর সন্দেহ হতে আহ্রিমানের জন্ম হয়। ‘ যারওয়ানিয়ান ’ ও ‘ কিউমারসিয়ান ’ এ উভয় দলেরই ‘ মাযদাইসনা যারথুষ্ট্র ’ ধর্মের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধ ছিল এবং এ বিরোধ হতে প্রচণ্ড শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। কখনও কখনও অ-পারসিকরা এ শত্রুতাকে ব্যবহার করে লাভবান হতো। এ ছাড়াও অন্য পাঁচটি ধর্ম ইরানে প্রচলিত ছিল যাদের যারথুষ্ট্র ,কিউমারসিয়ান ও যারওয়ানীয়ানদের সঙ্গে যেমন বিরোধ ছিল তেমনি তাদের নিজেদের মধ্যে তীব্র বিরোধ পরিদৃষ্ট হতো।
এদের মধ্যে প্রধান হলো ইহুদীরা যারা হাখামানেশী আমলে কুরেশের বাবেল অভিযানের সময় মুক্তি লাভ করে। তাদের একটি অংশ ইরানে আগমন করে। তাদের অধিকাংশই ইরানের পশ্চিমাংশের খুজিস্তান ও একবাতানে বসতি স্থাপন করে। সাসানী শাসনামলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ইরানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ,এমনকি ইসফাহানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইহুদী সমবেত হয়েছিল। দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটি খ্রিষ্টানদের যারা ‘ আশকান ’ শাসনামলে খ্রিষ্টান ধর্মের আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়েই এ ধর্ম গ্রহণ করে। ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের একাংশ যারা ফোরাতের পূর্ব ও পশ্চিমে বাস করত তারা নাস্তুরী খ্রিষ্টবাদকে গ্রহণ করেছিল। তারা সেখানে বিশেষ গীর্জাসমূহও তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে তারা ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও উত্তর পূর্ব ইরানের উজবেকিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ খ্রিষ্টবাদের এ ধারাকে চীন পর্যন্ত নিয়ে যায়।
তৃতীয় ধর্মীয় দলটি হলো মনী (মনাভী)। 228 খ্রিষ্টাব্দে এ ধর্মের উৎপত্তি ঘটে ও দ্রুত ইরানে বিস্তৃতি লাভ করে। এ ধর্ম সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর একটি ধর্ম। মনুগণ চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ,আত্মসংশোধন ,বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করতেন এবং আধ্যাত্মিকতা ও একান্তভাবে স্রষ্টার হয়ে যাওয়ার শিক্ষা দিতেন। ইরানের প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে এ ধর্মে সৌন্দর্যের আরাধনা (উপাসনা) ,বস্তুগত ও আত্মিক সুখের সন্ধান অধিকতর লক্ষণীয়। ইরানীরা দ্রুততার সাথে এ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল এবং যারা এ ধর্ম গ্রহণ করত তারা গভীরভাবে একে বিশ্বাস করত। সাসানী শাসকগণ তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেও এ ধর্ম হতে বিরত রাখতে পারেনি।
চতুর্থ ধর্মীয় দল হলো মাযদাকী। এ ধর্ম 497 খ্রিষ্টাব্দে ইরানে উৎপত্তি লাভ করে। তবে তাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কারণ খসরু নুশিন রাওয়ান তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করেছিল। তাদের এক স্থানে বন্দী করে সকলকে হত্যা করে। তদুপরি এ ধর্ম ইরান হতে বিলুপ্ত হয় নি ও অনেকে গোপনে এ ধর্ম পালন করত... এ ধর্ম সম্পর্কে বিরোধীদের মুখ হতে যা জানা যায় তার ওপর নির্ভর করা যায় না। তাদের বর্ণনা মতে মাযদাকীরা সম্পদ ও নারীর সামষ্টিক মালিকানায় বিশ্বাস করত ,এমনকি সম্পত্তি বন্টনে ‘ সর্ব অধিকার ’ স্বীকৃত ছিল।
পঞ্চম ধর্মটি হলো বৌদ্ধ ধর্ম। এর অনুসারীরা উত্তর-পূর্ব ইরানের জেলাগুলোতে বাস করত। একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্যদিকে চীন ছিল তাদের প্রতিবেশী। তাদের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিশেষত ‘ বালখ ’ ও ‘ বামিয়ানে ’ তাদের জাঁকজমকপূর্ণ মূর্তিমন্দির ছিল। বালখের ‘ নওবাহার ’ অবস্থিত উপাসনালয়টি যাকে ইসলামী যুগে যারথুষ্ট্রদের কেন্দ্র ও অগ্নিমন্দির মনে করা হতো মূলত সেটি ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দির ছিল। খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে যে ‘ বার্মাকী ’ বংশ ইরানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তারা নওবাহারের মূর্তিমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠী ‘ বার্মাক ’ -এর পরবর্তী বংশধর ছিল...।
মনী ও বৌদ্ধরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। যারথুষ্ট্র ,ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ভূমিকার (তারা এরূপ কোন প্রচেষ্টা চালায় নি) বিপরীতে তারা বিশ বছরের অধিক সময় স্বভূমি রক্ষার নিমিত্তে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।
অতঃপর তিনি (সাইদ নাফিসী) উল্লেখ করেছেন ,
“ সাসানী আমলে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল ইরাক ও টাইগ্রীস - ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী জেলাসমূহ। এ অঞ্চল নিয়ে সব সময় সাসানী ও রোম স াম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো। এতদঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ‘ সামী ’ (semitic)বংশোদ্ভূত ছিল। ইরানের প্রতি তারা সর্ববৃহৎ যে খেদমতটি করে তা হলো ‘ গ্রীক সভ্যতার জ্ঞানসমূহকে গ্রীক ভাষা হতে তাদের ‘ সুরিয়ানী ’ ভাষায় অনুবাদ করার মাধ্যমে গ্রীক ভাষার চিকিৎসা বিজ্ঞান , অংকশাস্ত্র , জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ সারা ইরানে ছড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় মনীষীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের ভাষা সাসানী রাজ দরবারেও প্রচলন লাভ করেছিল। ইতোপূর্বে হাখামানেশীদের যুগেও তাদের ভাষা ইরানের অফিস আদালতের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিশ্বাসের কয়েকটি ধর্ম ছিল এবং অনুসারীদের স্বতন্ত্র আচার - নীতি ছিল। তন্মধ্যে ‘ ইবনে দাইসান ’ - এর অনুসারীরা ও ‘ মারকিউন ’ - এর অনুসারীরা প্রসিদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়গণ এদের যথাক্রমে ‘ বরদেসান ’ ও ‘ মারকিউন ’ বলে থাকে। অন্য যে ধর্মটি তখন প্রচলিত ছিল তা হলো ‘ সাবেয়ী ’ । কোরআনে কোথাও কোথাও ইহুদী ও নাসারাদের নামের পাশে তাদের ‘ সাবেয়ীন ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 46
সাসানী শাসনামলে ইরানে প্রচলিত ধর্মসমূহ নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই উপরোক্ত ধর্মসমূহের উল্লেখ করেছেন। ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ গবেষক ক্রিস্টেন সেন তাঁর গবেষণানির্ভর গ্রন্থ ‘ ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ’ -এ উল্লিখিত ধর্মসমূহের পুনঃপুন উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইরানের প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রতি ইশারা করেছেন এবং এ গ্রন্থকে বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যাস করেছেন ,যেমন ‘ যারথুষ্ট্র ধর্ম-রাষ্ট্রীয় ধর্ম ’ , ‘ মনী ও তাঁর ধর্ম ’ , ‘ ইরানের ঈসায়িগণ ’ , ‘ মাযদাকী আন্দোলন ’ প্রভৃতি এবং এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কয়েকজন মধ্যপ্রাচ্যবিদ রচিত ‘ ইরানী সভ্যতা ’ যা ডক্টর ঈসা বাহনাম অনুবাদ করেছেন সেখানেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা রয়েছে। আগ্রহীরা এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন।
লক্ষণীয় বিষয় হলো সাসানী আমলে যারথুষ্ট্র ধর্ম ‘ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ’ হওয়া সত্ত্বেও (একদিকে শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ,অন্যদিকে যারথুষ্ট্র ধর্মীয় পুরোহিতদের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সংগঠনের উপস্থিতি সত্ত্বেও) তারা ইরানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়নি।
তাই শুধু খ্রিষ্টানগণ নয় ,এমনকি ইহুদী ও বৌদ্ধগণ তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিগণিত হতো। বিশেষত খ্রিষ্টান ধর্ম সে সময় দ্রুত অগ্রসরমান ছিল। আর্যদের মধ্যেও ইরানের অভ্যন্তরে মনী ,মাযদাকী ও অন্যান্য ধর্ম উৎপত্তি লাভ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এর বিপরীতে যারথুষ্ট্রদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছিল।
ইরানের সর্বকালীন ইতিহাসে ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা পর্যায়ক্রমে ইরানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং দু ’ তিন শতকের মধ্যে মনী ,মাযদাকী ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয় ,ইরানের পূর্বাঞ্চল ও আফগানিস্তান হতে বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটন করে ও যারথুষ্ট্র ,খ্রিষ্ট ও ইহুদী ধর্মকে সংখ্যালঘুর ধর্মে পরিণত করে।
সাসানী শাসকগণ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি গ্রহণ করে। সাসানী ধারার অন্যতম শাসক আরদ্শির বাবেকান ধর্মযাজক শ্রেণী হতে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। একদিকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশ্বাসগত ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজনে আরদ্শির যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রচার ,পুনরুজ্জীবন ও দৃঢ়করণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যারথুষ্ট্র ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ‘ আভেস্তা ’ র পুনর্বিন্যাস ও লিখন এবং যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। ফলে যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকগণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।
ড. মুহাম্মদ মুঈন ‘ মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ’ গ্রন্থে বলেছেন ,
‘ আশকানীদের পতনের পর আরদ্শির ববেকান (226-241 খ্রি.) সাসানী সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর আবির্ভাব ইরানের সাফল্য গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় ইরান জাতি বিশেষ দীপ্তি লাভ করে। এই সম্রাট ‘ মাযদা ইয়াসনা ’ (যারথুষ্ট্র ধর্মের বিশেষ ফির্কা) ধর্মরীতির ওপর তাঁর সাম্রাজ্য ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের ভিত রচনা করেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর পিতামহ সাসান ইসতাখারের ‘ নাহিদ ’ (শুকতারা) মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এ কারণেই আরদ্শির প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। মুদ্রার ওপর অগ্নিমন্দিরের ছাপ জাতীয় প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। তিনি শিলালিপিতে নিজেকে ‘ সেতাইয়ান্দে মাযদা ইয়াসনা ’ অর্থাৎ মাযদার প্রশংসাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ সম্রাটের সঙ্গে ধর্মজাযকদের সম্পর্ক ও ধর্মপরায়ণতার বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন বাণীর উল্লেখ করেছেন। কবি ফেরদৌসী তাঁর ‘ শাহনামা ’ কাব্যগ্রন্থে তার পুত্র শাপুর-এর প্রতি সম্রাটের উপদেশ বাণী কবিতার আকারে এনেছেন ,
“ দীন ও দৌলত পরস্পর সম্পর্কিত জেনো
এক চাদরের নীচে দু ’ সুহৃদ যেন
সিংহাসন ছাড়া হয় না বাদশাহী
দীন ছাড়া অচল শাহনশাহী। ”
দিনকারতের বর্ণনা মতে আরদ্শির বিশিষ্ট ধর্মযাজক তানসেরকে তাঁর দরবারে ডেকে
আভেস্তাকে পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশ দেন।
ড. মুঈন আরো বলেছেন ,
‘ সাসানীদের যুগে মাযদা ইয়াসনা ধর্মের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থান ছিল। যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকরা এ সময় ক্ষমতার পূর্ণতায় পৌঁছেন। কখনও কখনও ধর্মযাজক ও সম্ভ্রান্তগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতেন। ধর্মযাজকদের প্রভাব এতটা বেশি ছিল যে ,মাঝে মাঝে তাঁরা সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবনেও হস্তক্ষেপ করতেন। এমন অবস্থা ছিল ,সব বিষয়ের মীমাংসার অধিকার এ শ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছিল।
অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ ইরান বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টেন সেন হতে বর্ণনা করেছেন ,
‘ ধর্মযাজকদের প্রভাব সরকার নির্ধারিত ও ধর্মীয় বিষয় ,যেমন সাধারণ বিচার-আচার ,বিয়ে ,নবজাতককে পুণ্য ও বরকত দান করা ,পবিত্রকরণ ও কুরবানী বা ত্যাগ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ;বরং তাঁরা নির্দিষ্ট ভূমির মালিকানা ছাড়াও সদকা ,হাদীয়া ,শস্যকর ও অপরাধের জরিমানা হতে প্রচুর অর্থ পেতেন যা তাঁদের প্রভাবকে বর্ধিত করত। তদুপরি যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং বলতে গেলে তাঁরা সরকারের মধ্যে সরকার তৈরি করছিলেন । ’ 47
রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে যারথুষ্ট্র ধর্ম
সাসানীরা যেহেতু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল সেহেতু যারথুষ্ট্র ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে এবং যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করে। তারা অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সদাচারণ করত না ;বরং কখনও কখনও তারা ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করত এবং যারথুষ্ট্র ধর্মকে শক্তি প্রয়োগে তাদের ওপর চাপিয়ে দিত।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ যারথুষ্ট ধর্মযাজকগণ অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোন ধর্মকেই অনুমতি দিতেন না। তবে এই নীতি বিশেষভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে গৃহীত হয়েছিল। যারথুষ্ট্র ধর্ম প্রচার উপযোগী ধর্ম ছিল না। কারণ এর পুরোধাগণ সমগ্র মানব জাতির মুক্তির কথা বলতেন না। তাঁরা দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র কর্তৃত্বের দাবিদার ছিলেন। অন্যান্য ধর্মের অনুসারিগণের প্রজা হিসেবে কোন নিরাপত্তা ছিল না। বিশেষত যদি ঐ ধর্মের কেউ অন্য রাষ্ট্রে বিশিষ্ট কোন পদ অর্জন করে থাকে তবে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হতো। ”
সাঈদ নাফিসী উল্লেখ করেছেন ,
‘ সাসানী আমলের বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই বংশের শাসন কর্তৃত্বের পূর্বে ইরানের সকল মানুষ যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিল না। আরদ্শির বাবেকান যেহেতু পূর্বে ধর্মযাজক ছিলেন ও যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের সহযোগিতায় শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন সেহেতু চেয়েছিলেন যে কোনভাবেই হোক পূর্বপুরুষদের ধর্মকে ইরানে ছড়িয়ে দেবেন। তাই যখন পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন হতেই যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করলেন। ফলে তাঁরা সমাজের সবচেয়ে শক্তিধর শ্রেণী বলে পরিগণিত হতেন ,এমনকি কোন সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁরাই নতুন সম্রাট মনোনীত করতেন ও স্বহস্তে রাজমুকুট পরিধান করাতেন। এ কারণেই একমাত্র আরদ্শির বাবেকান তাঁর পুত্র শাপুরকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে গিয়েছিলেন। অন্য কেউ এরূপ স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর শীর্ষস্থানীয় পুরোহিতগণ যদি তাঁকে মেনে না নিতেন তবে তিনি সম্রাট বলে পরিগণিত হতেন না। এ সময়ের সকল সম্রাট শীর্ষস্থানীয় পুরোহিতদের ক্রীড়নক ছিলেন এবং যদি তাঁদের কেউ এই ধর্মযাজকদের কথা না শুনতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার মাধ্যমে পদত্যাগে বাধ্য করা হতো। যেমন দ্বিতীয় ইয়ায্দ গারদ খ্রিষ্টানদের হত্যা না করায় তাঁকে গুনাহগার ও অপরাধী ঘোষণা করা হয়। এরই আরবী প্রতিশব্দ হলো ‘ আসিম ’ যা আরব ঐতিহাসিকগণ ব্যবহার করেছেন। তিনি আট বছর পর বাধ্য হয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের মত খ্রিষ্টানদের সঙ্গে অসদাচারণ করেন। ”
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,
“ হাখামানেশী ,আশকানী ও সাসানী সকল রাজত্বকালেই আর্মেনিয়া ইরানের প্রদেশ ছিল এবং ‘ মাদ ’ বংশ সেখানে শাসনকার্য চালাত। আশকানী যুবরাজগণও দীর্ঘ সময় সেখানে শাসনকার্য চালিয়েছেন। সাসানী আমলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয় ও জোরপূর্বক যারথুষ্ট্র ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। আর্মেনিয়ার অধিবাসীরা শতাব্দীকাল ধরে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায় ও মূর্তিপূজা অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে 302 খ্রিষ্টাব্দ হতে ধীরে ধীরে সকলে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের গৃহীত খ্রিষ্ট মতবাদ ‘ আর্মেনিয়ান খ্রিষ্টবাদ ’ বলে প্রসিদ্ধ। ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার কারণেই পুরো সাসানী আমল জুড়ে আর্মেনিয়া নিয়ে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত ছিল। এরূপ ধর্মীয় বাড়াবাড়িই রোম বাইজান্টাইন শাসকদের মোকাবিলায় ইরানকে দুর্বল করে তুলেছিল। পরবর্তীতে অন্যান্য বিশেষত আরবদের জন্যও ইরান বিজয়কে সহজতর করেছিল। ”
তিনি আরো বলেছেন ,
“ প্রথম শাপুরের শাসনামলে ‘ আযকিরিতার ’ প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন এবং শাপুরের পরবর্তীতেও তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। নাকশে রাজাব ,সার মাশহাদ ও যারথুষ্ট্রদের তীর্থস্থানে বিদ্যমান তিনটি শিলালিপিতে শক্তি প্রয়োগে যারথুষ্ট্র ধর্ম প্রচারে তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ”
তিনি ‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ (ইরানী সভ্যতা)48 গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে পুরোহিতগণের শিলালিপি সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন ,
‘ 1939 সালে তাখতে জামশিদের নিকটবর্তী নাকশে রুস্তমে ‘ শিকাগো ইস্টার্ন এজেন্সী ’ যে খনন কার্য চালায় তাতে যারথুষ্ট্রদের তীর্থস্থানের পূর্বদিকে একটি দীর্ঘ শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এ শিলালিপিতে শীর্ষ ধর্মযাজক কিরিতার বর্ণনা করেছেন যে ,তিনি কিভাবে 242-293 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান ধর্মযাজকের পদ দখল করেছিলেন। অপর একটি শিলালিপিতে অন্য ধর্মের পুরোহিতদের (এ দেশে যাঁদের অবস্থান কল্যাণকর বলে পরিগণিত হতো না) কিভাবে ইরান হতে বহিষ্কার করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। যে সকল পুরোহিতকে বহিষ্কার করা হয় তাঁরা হলেন ইহুদী ,সামনা (বৌদ্ধ পুরোহিত) ,ব্রাহমা ,খ্রিষ্টান ,নাসেরী ,মুকতাকা ,মুক্তিপ্রাপ্ত (সম্ভবত ভারতীয়) এবং মনিগণ।49
অবশ্য সাসানী শাসনামলের সকল পর্যায়ে ধর্মীয় কঠোরতা একরূপ ছিল না তেমনি বিভিন্ন পর্যায়ে যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের ক্ষমতারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত। সকল শাসকই তাঁদের সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন না। যেমন প্রথম শাপুর ,প্রথম ইয়ায্দ গারদ ও খসরু আনুশিরওয়ানগণ অন্তত তাদের শাসনামলের একাংশ তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিলেন এবং অন্য ধর্মসমূহের প্রতি কিছুটা উদার আচরণ প্রদর্শন করতেন।
‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ গ্রন্থে ধর্মযাজক কিরিতার-এর শিলালিপি ও তাঁর দ্বারা আরোপিত কঠোরতার আলোচনার পর ‘ সাসানী আমলে পশ্চিম ইরানের ধর্মীয় অবস্থা ’ শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়েছে :
‘ অন্যদিকে আর্মেনীয় লেখক এলিজা ওয়ারদাপেটের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে তিনি সম্রাট শাপুরের হস্তলিপির উল্লেখ করে বলেছেন সেখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুগ ,ইহুদী ,মনী ও অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বী যারা ইরানের বিভিন্ন স্থানে বাস করে তাদের যেন স্বাধীনতা দেয়া হয় যাতে করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে। প্রথম শ্রেণীর শিলালিপিতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যাচারের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা দ্বিতীয় বাহরামের (277-293 খ্রি.) সময়কালীন ঘটনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শিলালিপি যাতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনতা দানের কথা বলা হয়েছে তা প্রথম শাপুরের (242-273 খ্রি.) সময়কালের এবং এ কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। ’ 50
ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের যেখানে ইরানের খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন:
‘ সেখানে তৎকালীন ইরানী খ্রিষ্টানদের সার্বিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন , ‘ চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর ইরানী খ্রিষ্টানদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে ‘ যাখু ’ হতে বর্ণিত হয়েছে ,সাসানী আমলের সবচেয়ে কঠিন সময়েও খ্রিষ্টধর্ম ইরানে স্বাধীন ছিল ;যদিও কখনও কখনও তারা বিভিন্ন শহর ও গ্রামে রাজকীয় কর্মচারীদের অত্যাচারের শিকার হতো। খ্রিষ্টানরা 410 ও 420 খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তৎকালীন রাজধানীতে ধর্ম সমিতি গঠন করে যাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পক্ষ হতে দু ’ জন পাদ্রী প্রতিনিধি ছিলেন যাঁদের একজন হলেন মিয়াফারেকিনের বিশপ ‘ মারুসা ’ এবং আমিদার বিশপ ‘ অকাস ’ । দ্বিতীয় শাপুরের আমলে যখন খ্রিষ্টানদের ওপর চরম নিপীড়ন চালানো হয় তখন খ্রিষ্টান পাদ্রী ইফাউত তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাতে এরূপ কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না যে ,খ্রিষ্টানরা তাদের স্বাভাবিক ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করেছিল। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ওপর সব সময় চাপ থাকলেও কখনো সাধারণ খ্রিষ্টানদের ধর্মান্তরিত করার কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয় নি। ইরান ও রোমের খ্রিষ্টানরা পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে রোম ও সিরিয় আইনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করত। বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড খুব কম ঘটত এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্মযাজকদের নৈতিক দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করত। ’ 51
সার্বিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম ইরানে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করত। যদিও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের কথা শোনা যায় তদুপরি বলা যায় তা রাজনৈতিক কারণে করা হতো। কারণ ইরানের খ্রিষ্টানগণ পারস্য ও রোম সম্রাজ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বে তাদের স্বধর্মের রোমীয়দের পক্ষাবলম্বন করত। তাদের এ ভূমিকা পারস্য সম্রাটদের ক্রোধের উদ্রেক করত।
ক্রিস্টেন সেন প্রথম ইয়ায্দ গারদ সম্পর্কে বলেন ,
“ প্রথম ইয়ায্দ গারদ রাজনৈতিক কারণেই খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তা স্পষ্ট। কারণ তিনি ইরান ও রোমের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নের যে ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করে তাতে তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত হয়। খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হলেও প্রকৃতগতভাবে তিনি সকল ধর্মের বিষয়ে সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাস করতেন।
তিনি খসরু আনুশিরওয়ান সম্পর্কে বলেছেন ,
“ খসরু যদিও মাযদাকীদের শায়েস্তা করার জন্য যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলে পুরোহিত ও সম্ভ্রান্তগণের কেউই পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা পান নি। প্রথম খসরু নিঃসন্দেহে যারথুষ্ট্র মতাবলম্বী ছিলেন ,কিন্তু অন্যান্য সাসানী শাসকদের হতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য হলো তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও স্থবিরতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি খ্রিষ্টানদের দাতব্য ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতায় কুণ্ঠিত হতেন না। ”
খ্রিষ্টধর্ম
ইরানে খ্রিষ্টধর্মের আগমন এবং কখনও কখনও চাপের মধ্যে পড়ার পরও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধ ,ইরানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া ও দিন দিন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া যে সাসানী শাসনকালের শেষ ভাগে কোন কোন সাসানী শাসক ও প্রাচীন যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীর এ ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়ও বটে। এ বিষয়টি যারথুষ্ট্র ধর্মের পুরোহিতদের প্রচণ্ড ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও এ ধর্মের নৈতিক দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে।
যদি ইসলাম ইরানে না আসত তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় খ্রিষ্টধর্ম ইরানকে দখল করে যারথুষ্ট্র ধর্মকে নিশ্চি হ্ন করত যেমনভাবে ইরানের অভ্যন্তরের মনী ও মাযদাকী ধর্মও দিন দিন যারথুষ্ট্র ধর্মের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীরা এদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করত। এ কারণেই ইরানী যারথুষ্ট্রগণ মনী ,মাযদাকী ,এমনকি খ্রিষ্টানদের মুসলমানদের চেয়ে বড় শত্রু মনে করত। মুসলিম শাসনামলেও আমরা লক্ষ্য করি যারথুষ্ট্রগণ বিশেষত তাদের ধর্মযাজকগণ মনী ও মাযদাকীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহযোগিতা করেছে। তেমনিভাবে ইরানের খ্রিষ্টানগণ যারথুষ্ট্রদের দ্বারা অত্যাচারিত এবং বিশেষভাবে দ্বিতীয় শাপুরের হাতে গণনিধনের শিকার হওয়ায় যারথুষ্ট্রদের হতে মুসলমানদের পছন্দ করেছিল ও ইরানে তাদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল।
ইরানে খ্রিষ্টানদের অগ্রগতি ও প্রভাব বলয় বৃদ্ধির বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইরানে খ্রিষ্টবাদের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে ক্রিস্টেন সেন বলেন ,
“ যখন সাসানী শাসকগণ আশকানিয়ানদের স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন খ্রিষ্টানগণ ‘ আলরেহা ’ শহরে (এশিয়া মাইনর ,বর্তমানে তুরস্কে) এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচার কেন্দ্রের অধিকারী ছিল।... পারস্য সম্রাটগণ রোমের সঙ্গে বড় কোন যুদ্ধ হলে বন্দীদের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে পুনর্বাসিত করতেন। সিরিয়ায় সেনা অভিযানের সময় সীমান্তবর্তী শহর বা জেলার সকল অধিবাসীকে সরিয়ে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসতেন। যেহেতু সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী খ্রিষ্টান ছিল সেহেতু খ্রিষ্টধর্ম ধীরে ধীরে ইরানের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।
‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ গ্রন্থে কিছু সংখ্যক মধ্যপ্রাচ্যবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ,
“ প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার অধিবাসী অরামীরা অথবা আলরেহা ও এডিস হতে আগত ধর্ম প্রচারক অথবা রোমীয় যুদ্ধ বন্দীদের মাধ্যমে ইরানে খ্রিষ্টধর্ম প্রথম প্রবেশ করে। একশ ’ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে আরবেলে কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান ছিল এবং 148-191 সালে কারকুকে খ্রিষ্টানদের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়। যদিও সে সময় খ্রিষ্টধর্ম ইরানে কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি ,কিন্তু এ ধর্ম এ দেশের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশেষত মনী ধর্মের প্রবর্তক ‘ মনী ’ এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ” একই গ্রন্থে ‘ সাসানী আমলের ইরানে খ্রিষ্টধর্ম ’ শিরোনামের আলোচনায় বলা হয়েছে :
‘ বাইজান্টাইন সম্রাট ,তাঁর সভাসদ ও রাজ্যের সকলেই খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অন্যদিকে পারস্যে যারথুষ্টদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল ও সাসানী সম্রাটগণ এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাবের প্রথম হতেই এ ধর্মের প্রতি তারা গোঁড়ামি প্রদর্শন করতেন। বিশেষত দ্বিতীয় শাপুরের সময়-যিনি রোম সম্রাট কনস্টানটাইনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন-ইরানে খ্রিষ্টানদের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে পড়ে...। প্রথম হতেই তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়। তাদেরকে কোন বিচার ব্যতিরেকে অথবা সংক্ষিপ্ত বিচারের পর হত্যা করা হতো কিংবা চরম নির্যাতন করা হতো। তৎকালীন সময়ে শহীদ অথবা নিহত খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা সেমিটিক ভাষার গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে। এ গ্রন্থ সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে ,নাম না জানা কত খ্রিষ্টান সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধের পর শহীদ হয়েছেন! তাঁদের আমরা ভুলে গিয়েছি। পরবর্তী পর্যায়ে জানা গিয়েছিল এ সকল খ্রিষ্টান বিদেশী বেঈমান নন ;বরং ইরানী খ্রিষ্টান ছিলেন যাঁরা যারথুষ্ট্র ধর্মের একান্ত অনুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতেন ,কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেশপ্রেমের বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না ,কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে তাঁরা ছিলেন দৃঢ়পদ। পরবর্তীতে শাসকবর্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ,এদেরকে নির্যাতন না করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে ,কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় নি ;বরং চল্লিশ বছরের নিপীড়ন ও নির্যাতনের পরও খ্রিষ্টধর্ম ইরানে শক্তিশালী অবস্থান লাভ করে। এদিকে ‘ হুন ’ ও ‘ হিয়াতালাহ্ ’ বংশীয়গণের ইরানের পূর্বাঞ্চল আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টানদের ওপর নিপীড়নের আপাত যবনিকাপাত ঘটে। এতে খ্রিষ্টানদের স্থায়ী সংগঠনের সৃষ্টির সুযোগ আসে... ইরানের খ্রিষ্টানগণ দ্রুত শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো যে কারণে পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইয়ায্দগারদ ও পঞ্চম বাহরামের খ্রিষ্টান নিপীড়ননীতি ফলপ্রসূ হয়নি। তিসফুন বা মাদায়েনের সুলূকিয়েহ্ এবং নাসিবীন প্রাচ্যের দীপ্তিমান ধর্মযাজকদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে পাদ্রীদের আশ্রম তৈরি হওয়ায় ধর্মীয় অনেক শিক্ষক সেখানে প্রশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পান। পাদ্রী আশ্রমগুলোতে এখনও এ রীতির প্রচলন রয়েছে। এদের প্রচার কার্যের ফলেই খ্রিষ্টধর্ম ইরানে নতুন জীবন লাভ করে।
প্রাগুক্ত প্রবন্ধের লেখক পি. জে. দুমানাশেহ সেখানে তৎকালীন খ্রিষ্টধর্মের শক্তিশালী প্রচার ব্যবস্থা ও ইরানে খ্রিষ্টধর্মের সজীব অবস্থার বর্ণনা দানের পর ইরানের পূর্বাঞ্চলে খ্রিষ্টবাদের ওপর ইসলামের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ,
“ সম্প্রতি নওলুয আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. দুয়াইলিয়ারের পরিশ্রমী গবেষণালব্ধ যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে চোখ বোলালে পরিষ্কার বোঝা যায় কিরূপে কালাদা প্রদেশের ধর্মযাজকগণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ ,তিব্বত ,কাশ্মীর ,দক্ষিণ ভারত ,মঙ্গোলিয়া ,এমনকি চীন সাগর পর্যন্ত এলাকার অধিবাসীদের অনেককেই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন! এ দীনী প্রচার শুধু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না ;বরং দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণকারী যাযাবর জাতিসমূহের মধ্যেও চলেছিল। খ্রিষ্টধর্ম এভাবেই ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও টিকে ছিল। যখন ফ্রানসিসকেন ধর্ম প্রচারকগণ বিশেষত জাঁ দোপলান করপেন ও রুবেরুক এবং বিশিষ্ট পর্যটক মার্কো পোলো এ দেশগুলোতে ভ্রমণ করেন তখন খ্রিষ্ট ধর্মের সূদৃঢ় অবস্থান লক্ষ্য করেন। তাঁরা পশ্চিমদিকে দেশ জয়ের অভিযানে প্রস্তুত মোগল গোত্রপতিদের শিবিরগুলোতে গিয়ে লক্ষ্য করেন তাঁদের মধ্যে খ্রিষ্টবাদের পক্ষাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা অসংখ্য ও সম্ভাবনা রয়েছে তারা সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করবে ,কারণ তারা বৌদ্ধ ,মনুয়ী ও ইসলামের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে মোগলদের ইসলাম গ্রহণ এতদঞ্চলে খ্রিষ্টবাদের বিরাট পরাজয় ডেকে আনে। ’ 52
খসরু পারভেজের সময়কালে খ্রিষ্টবাদ ইরানে অন্য যে কোন সময় হতে অধিক শক্তিধরে পরিণত হয়েছিল ,এমনকি সম্রাটের নিকটবর্তী অনেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা অবগত ,প্রসিদ্ধ ইরানী সেনাপতি বাহরাম চুবিনের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের কারণে খসরু পারভেজ ইরান ত্যাগ করে তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রোমের বাদশাহ্ মারকিউস-এর আশ্রয় নেন ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য মারকিউসকে কিছু ছাড় দিতেও রাজী হন। কথিত আছে খসরু রোমে অবস্থানকালে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ 581 সালে যখন খসরু রোম হতে ফিরে আসেন তখন যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ ততটা খুশী হতে পারেননি। কারণ (তাঁদের ভাষায়) এই সম্রাট খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তিহীন ও অমূলক বিশ্বাসসমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো তাঁর নিকট হেরেমের প্রিয় নারী ছিলেন শিরিন নামের এক খ্রিষ্টান নারী। ” 53
কেউ কেউ দাবি করেছেন খসরু পারভেজ যারথুষ্ট্র ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রিস্টেন সেন এ বিষয়ে বলেন ,
“ কোন কোন গবেষক উতিকিউসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে থাকেন খসরু পারভেজ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ,কিন্তু এ কথার কোন ভিত্তি নেই। বাস্তবে বিষয়টি এরূপ ,রোমের সম্রাট মারকিউস যিনি তাঁকে সিংহাসন ও রাজমুকুট পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর রোমীয় স্ত্রী (শাহযাদী) মারিয়া ও হেরেমের প্রেয়সী শিরিনের কারণে তিনি বাহ্যিকভাবে কিছু কিছু খ্রিষ্টীয় আচার পালন করতেন। তবে সম্ভাবনা রয়েছে খোদ সম্রাট খসরু খ্রিষ্টধর্মের কোন কোন কুসংস্কার লালন করতেন। ” 54
ক্রিস্টেন সেন অতঃপর খসরুর রাজ দরবারে খ্রিষ্টধর্মের দু ’ ফিরকা ইয়াকুবী ও নাসতুরীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তাঁর দরবারের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি ,যেমন মেহরান গুশনাস্প যাঁকে নাসতুরিগণ পবিত্র পানি দ্বারা গোসল দিয়ে ‘ গিওরগিম ’ নাম দেয় তাঁকেসহ খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত অন্য দরবারীদের নামের তালিকাও দিয়েছেন।
ক্রিস্টেন সেন বলেন ,
‘ মেহরন গুশনাস্প খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর নতুন এ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণের জন্য সংসার ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের শরণাপন্ন হন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর ভ্রাতাকে প্রশ্ন করেন ,তাঁর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে রাজ দরবারে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে ? তাঁর ভ্রাতা উত্তর দেয় , “ তুমি ফিরে আস ,কোন আশংকাই নেই। সম্রাট তোমার খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের কথা শুনে শুধু বলেছেন: মেহরান গুশনাস্প জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়েছে। এখন নিজের বিষয়ে চিন্তা করে দেখ। যদি ফিরে আস তবে সম্ভাবনা রয়েছে সম্রাট তোমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন। কিছুদিন পর তাঁর ভগ্নি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে মেহরন তাঁর সাক্ষাতে যায় ও পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে মাথা নীচু করেন। তাঁর ভগ্নি উচ্চাসন হতে নেমে এসে ভ্রাতার দিকে হাত প্রসারিত করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন: আনন্দিত হও এ জেনে ,আমিও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি। ”
এতক্ষণের আলোচনায় যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় তন্মধ্যে প্রথমত যারথুষ্ট্র ইরানে খ্রিষ্টধর্ম স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং এ গতি অব্যাহত থাকলে যারথুষ্ট্র ধর্মের জন্য বড় ধরনের বিপদ ছিল। দ্বিতীয়ত যারথুষ্ট্র ধর্মের বিপরীতে খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বজনীন এবং এর আহ্বানও সর্বজনীন। অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ কোন ভূখণ্ড ও সীমায় আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা সব সময় খ্রিষ্টধর্মকে ইরান ও ইরানের বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। তৃতীয়ত ইরানে ইসলামের আগমনের মাধ্যমে অবক্ষয় প্রাপ্ত যারথুষ্ট্র ধর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিবর্তে মূলত ক্রমপ্রসারমান খ্রিষ্টধর্মের ওপরই আঘাত এনেছে ও এর প্রচারের পথকে রুদ্ধ করে ময়দান হতে বিতাড়িত করেছে। যদি ইসলামের আগমন না ঘটত তবে সমগ্র প্রাচ্যে তার মূল প্রসারিত করত। ইসলামের নৈতিক প্রভাবই নিকট ও দূর প্রাচ্যে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তারের প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তাই ইরানে ইসলামের প্রভাব ও প্রসারে যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ অপেক্ষা খ্রিষ্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ অধিকতর কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ তাঁরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এ জন্যই লক্ষ্য করা যায় শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অপবিত্র প্রকৃতির খ্রিষ্টান লেখকগণ ইরান ও ইরানী জাতির নামে কিছু লিখতে গেলে ইসলামের ওপর আক্রমণ করেন এবং পোপের প্রশংসায় রত হন।
মনী ধর্ম (মনাভী)
সাসানী আমলের অন্যতম গতিশীল ও সজীব ধর্ম হলো মনী ধর্ম। মনী ধর্মের আচার-বিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে বলতে গেলে তা বেশ দীর্ঘ। মনী ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। সাধারণত বলা হয়ে থাকে মনী ধর্ম বৌদ্ধ ,খ্রিষ্ট ও যারথুষ্ট্র ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে স্বয়ং মনী উদ্ভাবিত আচার-বিশ্বাসের সমন্বয়। জনাব সাইয়্যেদ হাসান তাকীযাদেহ্ ‘ ইরান পরিচিতি সংঘ ’ -এ তাঁর উত্থাপিত গবেষণানির্ভর দু ’ টি বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ,
“ কোন কোন গবেষক মনে করেন মনী ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি হলো প্রাচীন ইরানের বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস , বিশেষত যারওয়ানী ধর্ম এবং আশকানি শাসনামলের শেষ দিকে ও সাসানী শাসনের প্রারম্ভে সৃষ্ট নব মতবাদ সমন্বিত যারথুষ্ট্র ধর্ম বিশ্বাস। কিন্তু যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সাদৃশ্য বাহ্যিক এবং এটি এ কারণে হয়েছে যে , মনী তাঁর ধর্ম বিশ্বাস প্রচারে বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় পরিভাষা ও শিক্ষাকেই ব্যবহার করতেন। তবে পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মের বিশেষ কিছু বিশ্বাস এর সঙ্গে সমন্বিত করা হয়। কারণ খতিয়ে দেখা গেছে মনী ইরান ও ভারতের অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে অধিকতর জানতেন। তবে তাঁর এই জ্ঞানের উৎস মূল ধারার খ্রিষ্টধর্ম নয় ; বরং বিশেষ ধারার খ্রিষ্টবাদ যাকে ‘ গোনুসী ’ (Gnostic)বলা হয়। এ ধারার খ্রিষ্টবাদ ‘ হেলুনিজম ’ প্রভাবিত যা গ্রীক দর্শনের প্লেটোনিক যে ধারাটি সিরিয়া ও দজলা - ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী সময়ে প্রচলন লাভ করেছিল তার সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। এ ধারাটি খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে এতদঞ্চলে প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ ধারার দু ’ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন ‘ মারকিউন ’ ও ‘ বরদিসান ’ যারা উভয়েই গোনুসী ছিলেন ও সানাভী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। 55
তাকী যাদেহ্ আরো বলেছেন , “ মনী ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত হলো যদিও মনী সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম ও ফির্কা হতে কিছু কিছু চিন্তা-বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন ,যেমন বৌদ্ধ ধর্ম হতে সামান্য ,যারথুষ্ট্র ও যারওয়ানী ধর্ম হতে আরো অধিক ,খ্রিষ্ট ধর্ম হতে বিশেষত গোনুসী (খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকদের) হতে সর্বাধিক ,তদুপরি মনী ধর্মকে এগুলোর সমন্বয় মাত্র বলা যায় না ;বরং এর মূল ভিত্তি মনীর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত ও এ ধারার উদ্গাতা স্বয়ং মনীর ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তাই যদি এ ধর্ম অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য রং ধারণ করে থাকে তা এ ধর্মকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের সুবিধার্থেই করা হয়েছিল। ” 56
যা হোক মনী ধর্মের বিষয়বস্তু কি ছিল বা স্বয়ং মনী কে ছিলেন তা আমাদের বর্তমান আলোচনার সাথে সম্পর্কশীল নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে অবশ্য আমরা তাঁর ‘ সানাভী ’ মতবাদ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং মনী ধর্মের অন্যান্য বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেব। যে বিষয়টি আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা হলো ইসলামের আবির্ভাবের মুহূর্তে এ ধর্মের কি অবস্থা ছিল ,এর অনুসারীর সংখ্যা কিরূপ ছিল ও এ ধর্ম কতটুকু আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তার করেছিল ? সে মুহূর্তে তা উত্থানের পথে ছিল নাকি পতনের পথে ?
ঐতিহাসিক সত্য হলো এ ধর্মটি বিশ্বজনীনতা দাবি করে। স্বয়ং মনী নবুওয়াতের দাবি করতেন ,নিজেকে সর্বশেষ নবী এবং তাঁর ধর্মকে সর্বশেষ ধর্ম বলে প্রচার করতেন। যারথুষ্ট্র মতবাদের বিপরীতে মনীদের মাঝে পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকজন শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা মনী ধর্মকে ইরানের সীমার বাইরে নিয়ে যেতে এবং অন্যান্য দেশের অনেক মানুষকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত চাপ ও নিপীড়ন সত্ত্বেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ ধর্ম টিকে ছিল এবং যারথুষ্ট্র অপেক্ষা মনিগণ ইসলামের বিরুদ্ধে অধিকতর দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। ইসলামী শাসনামলের কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের অস্তিত্ব ছিল। তবে ধীরে ধীরে তারা নিশ্চি হ্ন হয়ে যায়।
সাসানী আমলের প্রারম্ভে মনীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জন্ম দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিন্তু তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আরদ্শিরের সময়কাল হতে কয়েকজন সাসানী শাসককে তিনি পেয়েছিলেন। সম্ভবত আরদ্শিরের পুত্র প্রথম শাপুরের সময় তিনি নবুওয়াতের দাবি করেন। কথিত আছে শাপুর মনীর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছিলেন ও মনী ধর্মকে যারথুষ্ট্র ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দেবেন কিনা এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি অনুতপ্ত হয়ে এ চিন্তা হতে ফিরে আসেন।57 বলা হয়ে থাকে সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মনী ধর্ম টিকে ছিল। সুতরাং এ ধর্মের উৎপত্তির সময় হতে সম্পূর্ণ নিশ্চি হ্ন হওয়া পর্যন্ত এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল।
মনী ধর্ম আবির্ভাবের পর অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সম্পর্কে তাকী যাদেহ্ বলেছেন ,
“ মনীদের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ,মোগলদের উত্থানের সময়কাল পর্যন্ত এর অনুসারীরা বিদ্যমান ছিল। মনী ধর্ম আবির্ভাবের পর অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। মনীর মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ 300 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ধর্ম সিরিয়া ,মিশর ,উত্তর আফ্রিকাসহ স্পেন ও গল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ” 58
তিনি আরো বলেছেন ,
“ ইরানের মারভ ,বালখ ও তাখারিস্তানে মনী ধর্মের অসংখ্য অনুসারী ছিল। বিশিষ্ট চীনা পর্যটক হিউয়ান সাং সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনী ধর্মকে ইরানের প্রধান ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য ইরানের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে এ অবস্থা ছিল অর্থাৎ তাখারিস্তানে মনী ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল যা অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ’ 59
ক্রিস্টেন সেন তাদের সম্পর্কে বলেছেন ,
“ মনীদের ওপর যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের চাপ ও কঠোরতা সত্ত্বেও এ নতুন ধর্মটি ইরানে টিকে ছিল তবে কিছুটা অপ্রকাশ্যভাবে। সামানী শাসক নারসী ও দ্বিতীয় হারমুযদের শাসনামলে মনীদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা ‘ কিবতী মনী ’ গ্রন্থের শেষে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আরবের হীরা অঞ্চলের আরব শাসনকর্তা আমর ইবনে আদী মনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মনী ধর্মের উৎপত্তিস্থল ব্যাবিলন ও তিসফুনের প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রচুর মনী বাস করত। কিন্তু তৎকালীন শাসকদের নির্যাতনে তাদের অনেকেই পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের ইরানীদের অঞ্চলে চলে যায়। সেখানকার সাগাদ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনী বসবাস করত। এ অঞ্চলের মনীরা তাদের পশ্চিমাঞ্চলের স্বধর্মীদের হতে দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ” 60
মনী ধর্ম পরবর্তীতে টিকে থাকতে পারে নি। নিঃসন্দেহে এ পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ইসলাম। মনী ধর্ম দ্বিত্ববাদনির্ভর হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা ও মানব প্রকৃতিনির্ভর একত্ববাদী ধর্মের মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে নি। কারণ একত্ববাদী ধর্ম সহজেই প্রজ্ঞাবান ও দার্শনিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। তদুপরি মনী ধর্ম কঠিন যোগ-সাধনা নির্ভর হওয়ায় এর বাস্তব অনুশীলনও অসম্ভব। বিশেষত বিবাহ ও যৌনাচার হতে বিরত থাকা এ ধর্মের অন্যতম পবিত্র নির্দেশ হওয়ায় অনেকেই এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর বিপরীতে মানুষ ইসলামের মত এমন এক ধর্ম পায় যা আত্মিক পরিশুদ্ধির সর্বোচ্চ মর্যাদাসহ বিবাহ ,বৈধ যৌনাচার ও সন্তান জন্মদানকে অত্যন্ত পবিত্র সুন্নাহ্ মনে করে।
যদি মুসলমানরা মনী ধর্মকে যারথুষ্ট্র ,ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের ন্যায় ঐশী ধর্ম মনে করত ও আহলে কিতাব হিসেব করত তবে মনীরা ইসলামের আবির্ভাবের সময়কালে যত অধিক ছিল তাতে সম্ভাবনা ছিল যারথুষ্ট্র ,ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের ন্যায় সংখ্যালঘু হিসেবে টিকে থাকার। কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু মনীদের অধার্মিক মনে করত সেহেতু সংখ্যালঘু হিসেবেও তাদের টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।
মাযদাকী ধর্ম
অন্য যে ধর্মটি সাসানী আমলের শেষাংশে উৎপত্তি লাভ করেছিল ও যার বিপুল সংখ্যক অনুসারীও ছিল তা হলো মাযদাকী। মাযদাকী ধর্মকে মনী ধর্ম হতে উদ্ভূত মনে করা হয়। এ ধর্মের প্রবর্তক মাযদাক সাসানী শাসক আনুশিরওয়ানের পিতা কাবাদের শাসনামলে নিজেকে এ ধর্মের প্রবক্তা বলে ঘোষণা করেন। কাবাদ প্রথম দিকে মাযদার প্রতি ভালবাসা অথবা এ ধর্মে বিশ্বাসের কারণে অথবা যারথুষ্ট্র পুরোহিত ও সম্ভ্রান্তদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সমর্থন জানান। এতে মাযদাকের কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর পুত্র আনুশিরওয়ানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা আনুশিরওয়ান শাসন ক্ষমতা লাভের পর মাযদাকীদের গণহত্যার নির্দেশ দেন। মাযদাকীদের ওপর গণহত্যা পরিচালনায় এ ধর্মাবলম্বীরা আত্মগোপন করে।
মাযদাকীরা ইসলামী শাসনামলের দু ’ বা তিন শতাব্দী পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল এবং এ সময়ে ইসলাম ও খেলাফতের বিরুদ্ধে যে সকল ইরানী বিদ্রোহ করেছিল মাযদাকীরা তার নেতৃত্বে ছিল। এ কারণেই যারথুষ্ট্রগণ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে মুসলমানদের সহযোগিতা করে।
কথিত আছে মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা মূলত যারদুশ্ত নামের এক ব্যক্তি যিনি ইরানের সিরাজের ফাসার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে মনী ধর্মের একটি স্বতন্ত্র ফির্কার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন। তাঁর এ আহ্বান রোম হতে শুরু হয়। পরে তিনি ইরানে ফিরে এসে তাঁর এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। রোমে তিনি ‘ বুন্দেস ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রিস্টেন সেন উপরোক্ত বিষয়টি বর্ণনার পর উল্লেখ করেছেন ,
‘ সুতরাং মাযদাকী ধর্ম বুন্দেসের প্রচারিত ‘ সত্য দীন ’ । মনী ধর্মের এ ব্যক্তির নতুন ধর্মমত প্রচারের জন্য ইরানে আগমন হতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে ,তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। যদিও ‘ বুন্দেস ’ শব্দটি ফার্সী ভাষায় নাম হিসেবে নেই তদুপরি এটি তিনি নিজের উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলামী গ্রন্থগুলোতে দু ’ টি উৎস হতে মাযদাকী ধর্মের বিষয়ে আলেচনা এসেছে। এর একটি হলো ‘ আল ফেহেরেসত ’ যেখানে মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা মাযদাকের কিছু পূর্বের এক ব্যক্তি বলে উল্লিখিত হয়েছে ;ইসলামী গ্রন্থসমূহের অপর উৎস ‘ খুযায়ে নমাগ ’ গ্রন্থে তাঁর নামের সঙ্গে ‘ যারদুশত ’ শব্দটি জুড়ে দেয়া আছে এবং এখান হতেই যারদুশত ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে... সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় ‘ বুন্দেস ’ ও ‘ যারদুশত ’ এক ব্যক্তি ছিলেন এবং এ ধর্মের প্রবক্তার প্রকৃত নাম ‘ যারদুশত ’ যেটি যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তার সমনাম অর্থাৎ মাযদা ইয়াসনা যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তা ও নবী এবং মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা উভয়ের নামই ছিল ‘ যারদুশত ’ । সুতরাং আমাদের আলোচিত ধর্মটি মনী ধর্মেরই একটি ফির্কা যার উৎপত্তি মাযদাকের দু ’ শতাব্দী পূর্বেই রোমে ‘ বুন্দেসে ’ র হাতে ঘটেছিল এবং তিনি ইরানের ফাসার অধিবাসী খুরেগনের পুত্র ‘ যারদুশত ’ ছিলেন।... আরবী গ্রন্থসমূহ হতে জানা যায় ফাসার যারদুশতের আহ্বান শুধুই তত্ত্বগত ছিল। কিন্তু মাযদাক এ ধর্মের একজন সাধারণ প্রতিনিধি ও প্রচারক হিসেবে (তাবারীর মতে) ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় ধীরে ধীরে প্রবক্তার স্থান দখল করেন ও তাঁর জীবদ্দশায়ই এ ধর্মকে মাযদাকী বলে প্রচার চালান। ফলে পরবর্তীতে সাধারণ মানুষ ধারণা করেছে এ ধর্মের প্রকৃত উদ্গাতা ছিলেন মাযদাক। ” 61
মাযদাকী ধর্মের স্বরূপ ,ফাসায়ী যারদুশতের আবির্ভাবের কারণ ও মাযদাক সম্পর্কে প্রচুর কথা রয়েছে। মাযদাক নিঃসন্দেহে মনীর ন্যায় দ্বিত্ববাদী ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ দু ’ য়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করব। এ ধর্মের আচার-নীতি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব ও সংসার বিরাগের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন , “ ...মনী ধর্মের ন্যায় এ ফির্কারও মৌল নীতি হলো মানুষ যেন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কমায় এবং যা কিছুই এ আকর্ষণের সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করে ও দূরে থাকে। এ কারণেই পশুর মাংস ভক্ষণ মাযদাকীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং তারা বিশেষ নীতির মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করত ও কঠোর সাধনায় রত হত । ...শাহরেস্তানী বর্ণনা করেছেন মাযদাক অন্ধকার হতে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার নির্দেশ দিতেন। অবশ্য সম্ভাবনা রয়েছে আত্মহত্যা বলতে প্রবৃত্তিকে হত্যা বুঝানো হয়েছে যা আত্মার মুক্তির পথের অন্তরায় । মাযদাক মানুষকে ঈর্ষা ,প্রতিহিংসা ,দ্বন্দ্ব ও হত্যা হতে নিষেধ করতেন। তাঁর মতে যেহেতু মানুষের মধ্যে হিংসা ও দ্বন্দ্বের মূল কারণ অসাম্য সেহেতু বিশ্ব হতে অসাম্যকে বিনাশ করতে হবে। তবেই মানুষের মধ্যে হিংসা ও দ্বিমূখিতার অবসান ঘটবে। মনী ধর্মের মনোনীত প্রতিনিধিগণ বিবাহ করতে পারবেন না ,একদিনের আহার ও এক বছরের প্রয়োজনীয় পোশাকের অধিক রাখতে পারবেন না। যেহেতু মাযদাকীরাও মনীদের ন্যায় সংসার বিরাগ ও কঠোর সাধনায় বিশ্বাসী ছিল তাই ধারণা করা যায় তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের জন্যও এরূপ বিধান ছিল। তবে মাযদাকীদের নেতৃবর্গ বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষ বস্তুগত আনন্দ উপভোগ যেমন সম্পদ ,তার পছন্দনীয় নারী প্রভৃতি হতে বিরত থাকতে পারে না ;বরং তারা স্বাধীনভাবে এগুলো উপভোগ করতে প্রত্যাশী ,তাই ধর্মযাজকগণ তাঁদের বিশ্বাসকে এভাবে বর্ণনা করেন: “ খোদা জীবন যাপনের সকল উপকরণ পৃথিবীতে দিয়েছেন যাতে করে সকল মানুষ সমভাবে তা হতে ব্যবহার করতে পারে। কেউ যেন অপর হতে অধিক গ্রহণ না করে। অসাম্যের কারণেই মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা জন্ম নিয়েছে যে ,তার ভ্রাতার সম্পদ অপহরণ করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করবে। তাই কেউ অন্যের চেয়ে অধিক সম্পদ ও নারীর অধিকারী হতে পারবে না। তাই সম্পদশীলদের নিকট থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দিতে হবে যাতে করে পুনরায় পৃথিবীতে সাম্য স্থাপিত হয়। ” 62
অবশ্য স্বয়ং মাযদাক এবং এ ধর্মের উদ্ভাবনের পেছনে কি বিষয় তাঁকে উদ্দীপিত করেছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। মাযদাকের পরিচিতি বিশেষত তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার কারণে । ক্রিস্টেন সেন মাযদাকের এরূপ চিন্তার মূলে মানবপ্রেম ও নৈতিক অনুভূতি বলে মনে করেন।
মাযদাকের এরূপ চিন্তার কারণ ও উদ্দেশ্য যাই হোক যে বিষয়টি ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দাবি রাখে তা হলো তৎকালীন ইরানী সমাজ সাম্যবাদী ধারণা গ্রহণের জন্য কিরূপ উপযোগী ছিল। ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের ‘ মাযদাকী আন্দোলন ’ অধ্যায়ে তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত ইরান সমাজ কিভাবে মাযদাকী চিন্তাধারার প্রসারের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার আশ্চর্য বিবরণ দিয়েছেন। আমরা ইরানের তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এরূপ চিন্তার প্রসারের কারণ হয়েছিল।
সাঈদ নাফিসী সাসানী আমলের ইরান সমাজে বিবাহ ,তালাক ,উত্তরাধিকার ও নারীর অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন , “ বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য ও জনসমষ্টির বিশাল অংশের সম্পদের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার কারণে ইরান সমাজে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই সাসানী আমলের ইরান সমাজ ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং সাধারণ মানুষদের বিরাট অংশ বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দু ’ টি বিপ্লবী ধারার জন্ম হয়। যে দু ’ ধারারই লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে তার খোদাপ্রদত্ত অধিকার দান করা। 240 খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সাসানী শাসনামলের চৌদ্দতম বছরে সাসানী সম্রাট প্রথম শাপুরের সিংহাসনে আরোহণের দিন মনী বঞ্চিত শ্রেণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে তাঁর ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন ও ঘোষনা দেন। এর ঠিক পঞ্চাশ বছর পর ফার্সের ফাসার যারদুশত নতুন আরেকটি ধর্মের উদ্ভব ঘটান যদিও তাঁর ধর্মে সাম্যবাদের বিষয়টি কতটা উপস্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না। কারণ তিনি এ ধর্ম তেমনভাবে প্রচার করতে পারেননি। তবে এর প্রায় দু ’ শ বছর পর বমদাদের পুর মাযদাক তাঁর প্রণীত মৌলনীতিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। অবশেষে সাম্য ও মুক্তির বাণী নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটলে সমাজের অধিকারবঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার অর্জন করে ও সাসানী আমলের বৈষম্যের অবসান ঘটে। ” 63
মাযদাকী ধর্ম বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষে থাকায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করে। ক্রিস্টেন সেন বলেন ,
“ মাযদাকী ধর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন শ্রেণীর মাঝে উদ্ভব হয়ে এক রাজনৈতিক বিপ্লবী ধারার জন্ম দেয় ,কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও এ ধর্মের অনুসারী ছিল। ধীরে ধীরে মাযদাকীরা শক্তি লাভ করে ধর্মযাজক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় এবং একজন ধর্মযাজককে তাদের প্রধান মনোনীত করে। ” 64
ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে ,মাযদাক ও তাঁর অনুসারীরা কাবাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর অন্যতম পুত্র কাউসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায় ও কাবাদের ঈপ্সিত উত্তরাধিকারী পুত্র আনুশিরওয়ানকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলেই আনুশিরওয়ান তাদের সমূলে ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ শাসকশ্রেণী তাদের দীর্ঘ দিনের সফল অভিজ্ঞতাকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। তারা ধর্মযাজকদের বিভিন্ন গ্রুপকে দাওয়াত করে। অন্যান্য ধর্মযাজকদের প্রধানদের সঙ্গে মাযদাকী ধর্মীয় গুরুদেরও আহ্বান করা হয়। মাযদাকী পুরোহিতদের এক বৃহৎ অংশ সরকারীভাবে আয়োজিত এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হলেন। স্বয়ং সম্রাট কাবাদ (কাওয়ায) অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। এদিকে সম্রাটপুত্র খসরু আনুশিরওয়ান সম্রাটের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে মাযদাকী ও কাউসের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত ছিলেন যাতে করে এ অনুষ্ঠান মাযদাকীদের ওপর ভয়ঙ্কর এক হামলার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। যা হোক বিতর্ক শুরু হলে বেশ কিছু প্রশিক্ষিত ধর্মযাজক ময়দানে আসলেন...। দু ’ জন প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গুলুনাযেস ও বাযানেস যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের সঙ্গী হিসেবে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাযানেস সম্রাট কাবাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কারণ তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেশ দক্ষ ছিলেন। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই মাযদাকীরা পরাস্ত হলেন। এমতাবস্থায় মাযদাকীদের পেছনে অবস্থানকারী প্রহরীরা অস্ত্র হাতে মাযদাকীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রধান বিতর্ককারী (সম্ভবত স্বয়ং মাযদাক ছিলেন) নিহত হলেন। কতজন মাযদাকী এ আক্রমণে নিহত হন তা সঠিক জানা যায়নি। আরব ও ইরানী ঐতিহাসিকগণ যে সংখ্যাসমূহের উল্লেখ করেছেন তার কোন সঠিক ভিত্তি নেই। তবে মনে হয় মাযদাকীদের প্রধান ধর্মযাজকদের সকলেই এতে নিহত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পর মাযদাকীদের সকলকে হত্যার নির্দেশ জারী হলো। মাযদাকীরা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ও শত্রুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হলো। তাদের সম্পদ ও গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেয়া হলো... তখন হতে মাযদাকীরা গোপনে কর্মতৎপরতা চালানো শুরু করে এবং সাসানী আমলের পরবর্তীতে ইসলামের আবির্ভাবের পরও তারা অনেকবার আত্মপ্রকাশ করেছে। ” 65
বাহ্যিকভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতার মাধ্যমে মাযদাকী ধর্ম অবদমিত হয়েছিল ,কিন্তু বাস্তবে তারা ছাইচাপা আগুনের ন্যায় অপ্রকাশ্য ছিল। নিঃসন্দেহে ইসলাম আবির্ভূত না হলে মাযদাকী ধর্ম তার সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে পুনরুত্থিত হতো। কেননা যে সকল কারণে এ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল ও মানুষ এর প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে ঝুঁকে পড়ছিল সে কারণসমূহ বর্তমান ছিল। মাযদাকী ধর্ম দীনের মৌল বিশ্বাস ,বিশ্ব ,মানুষ ও সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণার বিষয়ে যারথুষ্ট্র ধর্ম হতে কোন বিষয়ে কমতি রাখত না ;বরং হয়তো কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তাই অন্যান্য ধর্ম হতে তাদের আকর্ষণ কম ছিল না। সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল যারথুষ্ট্র ধর্মের বিপরীতে। কারণ যারথুষ্ট্রগণ শক্তিমান ও ক্ষমতাশীলদের পক্ষে ছিল। আর মাযদাকীরা সাধারণ নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ছিল।
শক্তি প্রয়োগ ও দমন-নিপীড়নের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে মাযদাকী ধর্মের বিলুপ্তির মূল কারণ ছিল ইসলাম। ইসলাম একত্ববাদী ধর্ম হিসেবে খোদা ,সৃষ্টি ,মানুষ ও জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ মৌলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হয় ,মাযদাকী ধর্ম কোনক্রমেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। ইসলাম তার সামাজিক প্রশিক্ষণের ধারায় ন্যায়নীতি ,সাম্য ,মানুষ হিসেবে সকল শ্রেণী ,বর্ণ ও জাতির অভিন্নতার ধারণা উপস্থাপন করে যার মধ্যে মাযদাকীদের ন্যায় কোন বাড়াবাড়ি ছিল না। বস্তুত ইসলাম চিন্তাগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাযদাকীদের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। তাই ইরানের সাধারণ মানুষ মাযদাকী ধর্মে প্রবেশ না করে তাওহীদ ও ন্যায়নীতির প্রতি আহ্বানকারী ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফাগণ তাঁদের শাসনামলে পারস্য ও রোমের শাসকবর্গের নীতি অবলম্বন করলে ইরানে দ্বিতীয়বারের মত মাযদাকী চিন্তার প্রসারের সুযোগ আসলেও ইরানের মানুষদের সচেতনতা সে সুযোগ দেয়নি। কারণ তারা জানত খলীফাদের আচরণের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাই ইসলামকে এই খলীফাদের হাত হতে মুক্তি দিতে হবে।
তাই আমরা লক্ষ্য করি উমাইয়্যা শাসনের শেষ দিকে 129 হিজরীতে মারভের সেফিযানজ হতে কালো পোশাকধারীরা যে আন্দোলন শুরু করে তাতে তারা তাদের পতাকায় কোরআনের যে আয়াতটি খোদিত করে তা নিম্নরূপ :
) أذِنَ للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و إنَّ الله على نصرهم لقدير (
“ যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদের যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। ” 66
এ আন্দোলনের প্রথম দিন ছিল ঈদুল ফিতর। এদিন আন্দোলনের প্রধান নেতা আবু মুসলিম খোরাসানীর নির্দেশে অন্যতম নেতা সুলাইমান ইবনে কাসির ঈদের খুতবা পড়েন ও উমাইয়্যা খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তৎকালীন সময়ে ইরানীদের মধ্যে মাযদাকী ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তা প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল এটি। কিন্তু আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করি ইরানীদের ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সব সময় ইসলামের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল ;মাযদাকী বা অন্য কোন চিন্তার ওপর নয়।
মাযদাকীরাও মনুয়ীদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে ,যারথুষ্ট্রদের ন্যায় সংখ্যালঘু হিসেবেও টিকে থাকতে পারে নি। এর কারণ মনী ধর্মের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি ,মুসলমানরা মাযদাকীদের ঐশী ধর্ম বা আহলে কিতাব মনে করত না ;বরং মনীদের ন্যায় তাদেরও ধর্মহীন মনে করত। এ কারণেই তারা যারথুষ্ট্রদের ন্যায় সংখ্যালঘু হিসেবেও অবশিষ্ট থাকে নি। অবশ্য একদিকে মাযদাকীদের কঠোর নৈতিক সাধনা ও প্রচেষ্টার বাড়াবাড়ি ,অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সাম্যবাদী ধারণা এ দু ’ টি বিষয়ও তাদের নিশ্চি হ্ন হওয়ার কারণ ঘটিয়েছিল।
বৌদ্ধধর্ম
প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের হিমালয় পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারী ‘ শৈক্য ’ নামে প্রসিদ্ধ একদল মানুষের মাঝে তাদের সম্রাটের এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। ত্রিশ বছর তিনি তাদের মধ্যে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন ও তৎকালীন সময়ের সকল জ্ঞান অর্জন করেন বিশেষত হিন্দু ধর্মের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ বেদ ’ সমূহ অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তাঁর মনের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং তিনি সাত বছরের জন্য রাজকীয় সব আড়ম্বর ত্যাগ করে নির্জনে চিন্তা ও যোগ সাধনার কাজে লিপ্ত হন। তাঁর মূল ভাবনা ছিল মানব সন্তানের
দুঃখ-কষ্টের কারণ নির্ণয় ও এ হতে মুক্তিদানের মাধ্যমে তাদের সৌভাগ্য ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন দান। দীর্ঘকালের চিন্তা ,সাধনা ,একাকী জীবন যাপন ও আত্মিক অনুশীলনের পর এক তমুর (বোধি) বৃক্ষের নীচে তাঁর মনে এক নতুন চিন্তার উদ্ভব হয়। এ চিন্তা ও বিশ্বাসই মানব সন্তানের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে বলে তিনি অনুভব করেন। তখন তিনি মানব সমাজে ফিরে এসে এ শিক্ষা হতে দিক-নির্দেশনা দেয়া শুরু করেন। তিনি যা উদ্ঘাটন করেন তা প্রকৃতির এক স্বাভাবিক রীতি। আর তা হলো এ বিশ্বজগতে পুরস্কার ও শাস্তির নীতি রয়েছে এবং সৎ কর্মের প্রতিদান হলো সৎ এবং অসৎ কর্মের প্রতিদান হলো মন্দ ও অসৎ।
এ সম্রাটপুত্রের নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি পরবর্তীতে ‘ বুদ্ধ ’ নাম ধারণ করেন। তিনি তাঁর সাধনা অর্জিত শিক্ষার অনুবর্তী হয়ে জীবহত্যা ,উপাস্যদের উপাসনা ও প্রার্থনা হতে নিষেধ করেন। তিনি স্রষ্টা ও উপাস্যদের অস্বীকার করে বিশ্বজগতের চিরস্থায়ীত্বে বিশ্বাস করতে বলেন। ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রার্থনা ও কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছে এবং জন্মগতভাবে মানুষদের শ্রেণী বিন্যাস করেছে। বুদ্ধ এগুলোকে সমালোচনা ও অস্বীকার করেছেন।
বুদ্ধের চিন্তাকে ধর্ম সদৃশ না বলে দর্শন সদৃশ বলা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে বৌদ্ধের অনুসারীরা একে এক ধর্মের রূপ দান করে এবং প্রার্থনা ও উপাসনাকে অস্বীকারকারী বৌদ্ধকে উপাস্যের স্থানে স্থান দেয়। তারা বৌদ্ধের মূর্তি তৈরি করে ও তাঁর উপাসনার জন্য মন্দির প্রস্তুত করে। তাঁর বক্তব্য ও উপদেশ বাণীসমূহকে গ্রন্থাকারে ‘ ত্রিপিটক ’ বা ‘ জ্ঞানের ত্রিঝুড়ি ’ নামে সংকলন করে ।
বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য অনুসারী পান। পিতার সম্রাজ্য ছাড়াও ভারতের অন্য একটি প্রদেশের অধিবাসীরা তাঁর অনুসারী হয় এবং ধীরে ধীরে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ ’ সালে ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ সম্রাট ‘ অশোক ’ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাঁর নির্দেশে অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও অগণিত অনুসারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে রাজকীয়ভাবে হিন্দুধর্মের প্রচারণা এবং বিশেষত ইসলামের আগমনের পর এ ধর্ম এর জন্মভূমি হতে পাততাড়ি গুটিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়। এখনও বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারীরা এখন শ্রীলঙ্কা ,বার্মা ,থাইল্যান্ড ,ভিয়েতনাম ,তাইওয়ান ,জাপান ,কোরিয়া ,মঙ্গোলিয়া ,তিব্বত ও চীনে বসবাস করে। বৌদ্ধধর্ম ভারত হতেই ইরানে আগমন করে। এ সম্পর্কে ক্রিস্টেন সেন বলেন ,
“ আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর গ্রীকদের আধিপত্যের সময় বৌদ্ধধর্ম ইরানের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে। ভারতীয় সম্রাট অশোক যিনি খ্রিষ্টপূর্ব 260 সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি গান্ধারের পশ্চিমাঞ্চলে ও কাবুল উপত্যকায় অভিযান চালান। ...বৌদ্ধরা প্রথম খ্রিষ্ট শতাব্দীতে গান্ধারে বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরসমূহ তৈরি করে যার চি হ্ন এখনও ধ্বংসাবশেষ হিসেবে রয়েছে এবং সেগুলোতে হিন্দী (সংস্কৃত অথবা পালি) ও গ্রীক ভাষার মিশ্রণে পাথরে খোদিত লেখাসমূহ রয়েছে... কাবুলের পশ্চিমাঞ্চলের বামিয়ানে পাহাড়ে খোদিত বৌদ্ধের একটি বৃহৎ মূর্তি রয়েছে...67
চীনা পর্যটক হিউয়ান সাং-এর বর্ণনা মতে সপ্তম খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত ইরানে বৌদ্ধমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল এবং ইরানের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে ভারতীয় অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও বর্তমান ছিল। ”
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,
“ খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ও প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাবুল উপত্যকার সম্রাট মানান্দার ভারতবর্ষেও ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও এর অনুসারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ”
তাঁর বর্ণনা মতে 125 খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহারে ও পাঞ্জাবে ‘ কানিস্কা ’ নামে এক বৌদ্ধ সম্রাট প্রসিদ্ধি লাভ করেন যিনি বৌদ্ধধর্মের একজন বড় প্রচারক ছিলেন।68
বৌদ্ধ ধর্মও এ অঞ্চল হতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি বৌদ্ধ ও মনীরা ইরানের সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী ছিল। তদুপরি তারা যারথুষ্ট্র অনুসারীদের অপেক্ষা স্বীয় ধর্মকে রক্ষার জন্য অধিকতর সক্রিয় ছিল। তবে বালখের বৌদ্ধবিহারের সেবক বার্মাকী গোষ্ঠী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল (এবং তাদের অনেকেই ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল) ।
ইসলামের আবির্ভাবের পর ইরানে বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকতে পারেনি ;বরং তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও আস্তে আস্তে অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে পা বাড়ায়। ‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে :
‘ আফগানিস্তানের কাবুলের নিকটবর্তী বামিয়ানের ধর্মীয় গুরুত্ব ও সপ্তম খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধমন্দিরসমূহের উপস্থিতির বিষয়টি হিউয়ান সাং হতে বর্ণিত হয়েছে। এক কোরীয় পর্যটক পরবর্তী শতাব্দীতে সেখানে একজন ইরানী বৌদ্ধ শাসকের উপস্থিতির উল্লেখ করেছেন। তিনি এই শাসকের অধীন এক শক্তিশালী সেনাদলের অস্তিত্বের কথাও বলেছেন। কিন্তু এর পরের শতাব্দীতেই ইয়াকুব লাইস সাফারী এ এলাকা দখল করেন। ’ 69
সুতরাং বোঝা যায় ইরানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ভারত হতে আগত বৌদ্ধধর্ম ইরানে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছিল। যেমনটি ইরানের পশ্চিমাঞ্চল ও দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে আসা খ্রিষ্টধর্ম ইরানে বিস্তৃতি লাভ করছিল। বৌদ্ধধর্ম পশ্চিম দিকে এবং খ্রিষ্টধর্ম পূর্ব দিকে অগ্রসরমান ছিল। যদিও শাসনকর্তাদের পক্ষ হতে যারথুষ্ট্র ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় এর পুরোহিতগণ এ দু ’ অগ্রসরমান ধর্মের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। পূর্বে যারথুষ্ট্র পুরোহিত কিরিতারের শিলালিপির উদ্ধৃতি আমরা উল্লেখ করেছি যিনি বলেছেন ,বিদেশী ধর্মসমূহের কিছু প্রচারক যাঁদের ইরানে অবস্থান কল্যাণকর ছিল না তাঁদের ইরান হতে বহিষ্কার করা হয়। যেমন ইহুদী ,বৌদ্ধ ধর্মযাজক ,ব্রা হ্ম ,খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ,সামানিগণ...।
কিন্তু যে ধর্মটি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারতার পথ রুদ্ধ করে বৌদ্ধ ধর্মের কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও খ্রিষ্টধর্মকে নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তা হলো ইসলাম যার অনুশোচনা ও কষ্ট আজও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ এবং তাঁদের অনুসারী প্রাচ্যবিদদের লেখনী হতে স্পষ্ট বোঝা যায়।
যা হোক বৌদ্ধধর্ম তৎকালীন ইরানের অন্যতম ধর্ম ছিল এবং খ্রিষ্টান ,মনী ও মাযদাকীদের ন্যায় তাদের কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল না। তাই তারা তেমনভাবে উপস্থাপিতও হয় নি।
আর্য বিশ্বাসসমূহ
আমরা তৎকালীন ইরানের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জানলাম। আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো ,সে সময় ইরানে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব ছিল এবং একক কোন ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না। কোন্ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা কত ছিল সঠিকভাবে তা বলা সম্ভব না হলেও এটি স্পষ্ট ,রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে যারথুষ্ট্র ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাও কোন ক্রমে কম ছিল না।
ইসলাম চিন্তা ও বিশ্বাসগত কি কি বিষয় ইরান হতে নিয়েছে ও ইরানকে কি দিয়েছে তা জানার জন্য ইরানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই ;বরং এ জন্য আমাদের এ দেশের অধিবাসীদের খোদা ,বিশ্ব ,সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে লালনকৃত চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে হবে।
ইরানী ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই। বাহ্যত অন্যান্য ইহুদীদের মতই তারা তাওরাত ও তালমুদের অনুসরণ করত। তাদের বিশ্বাস যা-ই হোক যেহেতু তারা নগন্য সংখ্যালঘু হিসেবে পরিগণিত হতো সেহেতু তৎকালীন ইরানী সমাজে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু খ্রিষ্টানদের সেসময়ে রমরমা অবস্থা ছিল। কারণ তারা ত্রিত্ববাদ ও ঈসা মাসীহের প্রভুত্বের ধারণা প্রচার করত। আমরা এখানে খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ ও এর সঙ্গে একত্ববাদের ধারণার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব না । কারণ প্রথমত বিষয়টি পরিষ্কার বলে আলোচনার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত খ্রিষ্টধর্ম সংখ্যালঘু হিসেবে ইরানে ছিল এবং এই সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের খুব কমই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইরানের অধিকাংশ মানুষ যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিল এবং মনী ও মাযদাকীরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যারথুষ্ট্র ধর্মের অনুরূপ ছিল। তাই আমরা আমাদের আলোচনা মূলত যারথুষ্ট্র ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এবং সেই সাথে মনী ও মাযদাকী বিশ্বাস নিয়েও কিছুটা আলোচনা রাখব। মোট কথা ,ইরানী আর্যদের মধ্য হতে উত্থিত ধর্মসমূহ নিয়েই মূলত আমাদের আলোচনা আবর্তিত।
প্রশ্ন হলো ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন যারথুষ্ট্র ,মনী ও মাযদাকী ধর্ম স্রষ্টা ও উপাসনা নিয়ে কিরূপ বিশ্বাস লালন করত ? তারা কি খোদা পরিচিতির ক্ষেত্রে একত্ববাদী ছিল নাকি দ্বিত্ববাদী ?
নিঃসন্দেহে ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন যারথুষ্ট্র ,মনী ও মাযদাকী সকলেই দ্বিত্ববাদী ছিল। ইসলাম পরবর্তী সময়েও তারা এ বিশ্বাস রাখত ,এমনকি মুসলিম শাসনামলেও তারা মুসলিম মনীষী ও আলেমদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্ক করত ও দ্বিত্ববাদের পক্ষাবলম্বন করত। মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্ব হতে তারা পূর্বের সকল কিছুকে অস্বীকার করে একত্ববাদী সেজেছে। এতে অবশ্য আমরা খুশী হয়েছি ,যারথুষ্ট্রগণ দ্বিত্ববাদের কুসংস্কার একেবারে ত্যাগ করে এক খোদার উপাসনা শুরু করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এক খোদার উপাসনার অপরিহার্যতা হলো প্রকৃতই ধর্মীয় গোঁড়ামিসমূহ পরিত্যাগ করা ও সত্যকে স্বীকার করা। তাই একত্ববাদের প্রতি আহ্বানকারীদের জন্য ঠিক নয় তাদের অতীত ইতিহাসকে বাস্তবের বিপরীতরূপে উপস্থাপন করা।
অবশ্য এতে ভুল বোঝা ঠিক হবে না যে ,হয়তো ভাবা হবে আমরা বলতে চাচ্ছি যারথুষ্ট্র ধর্ম প্রকৃতই প্রথম হতে দ্বিত্ববাদী ছিল ও এ ধর্মের প্রধান ব্যক্তি যারদুশত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছেন। না ,এমনটি নয়। আমরা এরূপ কথা বলছি না। মুসলমানরা প্রথম হতেই যারথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আহলে কিতাবগণের ন্যায় আচরণ করত। কারণ তারা মনে করত এ ধর্ম মূলে একটি একত্ববাদী ও ঐশী ধর্ম ছিল ,পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিষ্টধর্মের ন্যায় বিচ্যুত হয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম যেরূপ ত্রিত্ববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে ,এ ধর্মও সেরূপ দ্বিত্ববাদের জন্ম দেয়। এজন্যই স্বয়ং যারদুশত আমাদের নিকট সম্মানিত।
এখানে আমরা যা বলতে চাই তা হলো ইসলামের আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে যারথুষ্ট্র ধর্ম একশ ’ ভাগ দ্বিত্ববাদী ছিল এবং একত্ববাদের সঙ্গে তার কোন মিলই ছিল না। অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল ছিল।
আমাদের এখনকার আলোচনাকে তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করব :
1. যারদুশতের আবির্ভাবের পূর্বের আর্য বিশ্বাসসমূহ কি ছিল ?
2. যারদুশত সেখানে কি পরিবর্তন ও সংস্কার করেছেন ?
3. ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত যারথুষ্ট্র ধর্মে কিরূপ বিচ্যুতি সাধিত হয়েছিল ?
যারদুশতের আবির্ভাবের পূর্বে আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস
1. প্রথম ভাগ: প্রাচীন যুগে ইরানী আর্যরা দ্বিত্ববাদী হিসেবে প্রকৃতির উপাসনা করত অর্থাৎ তারা প্রকৃতির কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উপাদানসমূহের উপাসনা করত। একদিকে প্রকৃতির কল্যাণকর উপাদান হিসেবে মাটি ,পানি ,বৃষ্টি প্রভৃতির এবং অকল্যাণকর উপাদান হিসেবে মেঘ ,বজ্রপাত ,ক্ষতিকর প্রাণীসমূহ প্রভৃতির আরাধনা করত। কল্যাণকর উপাদানসমূহকে ইবাদাত করা হতো এ উদ্দেশ্যে যে ,তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে কল্যাণ অব্যাহত রাখা এবং অকল্যাণকর বস্তুসমূহের অকল্যাণ হতে রক্ষা পাওয়া। সম্ভবত তারা প্রকৃতির এ সকল উপাদানের প্রাণ ,অনুভব ও বোধশক্তিকে বিশ্বাস করত। এ পর্যায়ে দু ’ ধরনের বস্তু ও উপাদানের তারা উপাসনা করত-ভাল বা কল্যাণকর উপাদান ও মন্দ বা অকল্যাণকর উপাদান। কল্যাণকর উপাদানসমূহকে মঙ্গলের আশায় এবং অকল্যাণকর উপাদানকে অমঙ্গলের ভয়ে উপাসনা করা হতো। বাস্তবে তারা প্রথম হতেই দু ’ ধরনের উপাস্যে বিশ্বাসী ছিল।
পরবর্তী সময়ে তারা কল্যাণকর ও অকল্যাণকর প্রতিটি উপাদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা শুরু করে এবং এ সকল উপাদানের উপাসনার পরিবর্তে প্রতিটির খোদাকে ইবাদাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন আগুনের প্রভু ,বাতাসের প্রভু ,মেঘের প্রভু ,বৃষ্টির প্রভু ,বজ্রপাতের প্রভু এভাবে অন্যান্য খোদাসমূহ। এ পর্যায়ে খোদাগণকে দু ’ ভাগে বিভক্ত করা হতো এবং তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের ছায়ামূর্তি হিসেবে দেখা হতো। এ দু ’ ধরনের খোদার কল্যাণকামী ও অকল্যাণকামী বা কল্যাণদানকারী ও ক্ষতিসাধনকারী বা সৎ আত্মা ও অসৎ আত্মা নামে অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ এ যুগেও আর্যদের মাঝে দ্বিত্ববাদের রাজত্ব ছিল।
সাঈদ নাফিসী বলেছেন ,
“ ইরানের আর্যদের স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য শহর গড়ে তোলা শুরু করল। তারা ধীরে ধীরে প্রকৃতির ভাল-মন্দ ,সুন্দর-অসুন্দর ,কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন শুরু করল। ভাল উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো সূর্য ,ঔজ্জল্য ,বৃষ্টি প্রভৃতি আর মন্দ উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো রাত্রি ,শৈত্য ,খরা ,দুর্ভিক্ষ ,রোগ ,মৃত্যু ও অন্যান্য আপদসমূহ। তারা কল্যাণকর উপাদানসমূহের জন্য প্রার্থনা ,দোয়া ,উপহার ও নযর প্রেরণ করত। আর অকল্যাণকর বস্তুসমূহ হতে মুক্তির জন্য মন্ত্রসমূহ পাঠ করত। ধীরে ধীরে এ কর্ম যাদুবিদ্যা ও তাবিজ-কবজে পরিণত হলো। সম্ভবত সিরীয় ,আশিরীয় ও ব্যাবিলনের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসার সমকালীন সময়ে এ বিষয়টি ইরানী আর্যদের মধ্যে আসে। কারণ সেমিটিক আশিরীয় ব্যাবলনীয়রা যাদুমন্ত্র ও তাবিজ-কবজে যথেষ্ট বিশ্বাস করত। ইরানীরা তাদের থেকেই এগুলো গ্রহণ করেছে। এ সময়েই ইরানীদের মাঝে যারদুশতের আগমন ঘটে এবং তিনি এ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ” 70
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ আর্যদের প্রাচীন ধর্ম প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও আকাশমণ্ডলীর তারকা ও অন্যান্য উপাদানসমূহের উপাসনানির্ভর ছিল। তদুপরি প্রাকৃতিক এই উপাস্যসমূহ সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল। বাহ্যত ইরানী ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বিভাজনের পূর্বেও এই উপাস্যসমূহ দু ’ ভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে দেও বা দেবগণ যাদের প্রধান হলেন যুদ্ধবাজ দেবতা ‘ ইন্দ্র ’ এবং অন্যদিকে ছিলেন ‘ অসুরগণ (ফার্সী ভাষায় অহুর) যাদের অন্যতম হলেন ‘ অরুণ ’ ও ‘ মিত্র ’ । অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন ইরানীদের প্রাচীন প্রভু ‘ মাযদা ’ যার অর্থ জ্ঞানী তিনি অসুরদের প্রধান সেই ‘ অরুণ ’ । কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর প্রকৃত নাম ইরানীরা ভুলে গিয়েছিল। ” 71
ভাল ও মন্দের দু ’ টি উৎস রয়েছে এ অর্থে দ্বিত্ববাদ প্রাচীন আর্যদের চিন্তাতেও ছিল। প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি প্রাচীন কাল হতে তাদের চিন্তামগ্ন করে রেখেছিল তা হলো সৃষ্টি জগতে দু ’ ধরনের বস্তুর অস্তিত্ব-ভাল ও মন্দ।
ডক্টর মুহাম্মদ মুঈন বলেছেন ,
“ আর্যরা প্রাচীন কাল হতে কল্যাণ ও অকল্যাণের দু ’ টি ভিন্ন উৎসে বিশ্বাস করত। একদিকে খোদাগণ আর অন্যদিকে আহ্রিমানগণ। ভাল ও কল্যাণকর বিষয়সমূহ ,যেমন আলো ও বৃষ্টিকে খোদাগণের সঙ্গে সম্পর্কিত করত আর মন্দ ও অকল্যাণকর বিষয়সমূহকে যেমন অন্ধকার ও খরাকে আহ্রিমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত।
আকাশপুত্র অগ্নি আলো ,উষ্ণতা ও জীবনকে ধারণকারী হিসেবে ,অন্ধকার ,খরা ও মন্দ আত্মা বহনকারী সত্তার সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বজ্রপাত নিয়ে আবির্ভূত হয়। ”
দুমযিল তাঁর ‘ ইরানের প্রাচীন ধর্মসমূহ ’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন , ‘ আলো প্রাচুর্য ও উন্নতির প্রতিভূ খোদা ও ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে মন্দ ও অন্ধকারের প্রতিভূ দেওগণ (দানব) অবস্থান নেয়। দ্বিত্ববাদ ইরানীদের প্রাচীন ধর্ম বৈশিষ্ট্য ছিল ,মন্দের জগতে ধ্বংস ,অন্ধকার ,অন্যায় ও পচনশীলতা ভিন্ন কিছু নেই। এই জগৎ আহ্রিমান বা আহরা মাইনিও নামের এক মন্দ আত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয়। ” 72
ডক্টর মুঈন আরো বলেছেন ,
“ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যের এই যুদ্ধ মহাশূন্যে সংঘটিত হয়। ভূমণ্ডলে বিক্ষুব্ধ যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে আমরা খুব কমই তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি । কিন্তু প্রাচীন শৈল্পিক ও অনুভূতিশীল আর্য জাতির নিকট এটি এক সংঘর্ষের প্রতিরূপ হিসেবে প্রতিফলিত হতো যা মানবের ঊর্ধ্বের ভাল ও মন্দের দুই প্রতিভূ শক্তির মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। তারা তাদের মনের পর্দায় তা মঞ্চায়িত করত... । ”
2. দ্বিতীয় ভাগ: যারদুশতের আগমনের পর যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে মাযদিসনা নবী যারদুশত73 ও তাঁর আনীত ধর্মগ্রন্থ ‘ উসতা ’ বা ‘ আভেস্তা ’ নিয়ে যে সংশয় রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব: যারদুশত রুস্তম বা ইসফানদিয়ারের ন্যায় একজন কাল্পনিক ব্যক্তি নাকি তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব ছিল ? যদি তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব থেকেই থাকে তাহলে তা কখন ?
যারদুশতের আগমন কালকে কেউ খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শ ’ বছর ,আবার কেউ ছয় হাজার বছর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক সম্রাট কে ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তিনি কি প্রকৃতই ‘ ভীশতাসব ’ বা ‘ গুশতাসব ’ -এর সমকালীন ছিলেন ?
তাঁর জন্মস্থানই বা কোথায় ছিল ? আজারবাইজান নাকি বালখ ? ফার্স নাকি রেই ? খাওয়ারেজম নাকি মারভ ? হেরাত নাকি ফিলিস্তিন ? কোথায়ই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ?
উপরিউক্ত বিষয়গুলো ঐতিহাসিকভাবে জানতে হবে। তবে বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর জন্মস্থান আজারবাইজান এবং জন্মকাল খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শ ’ বছর বলা হয়েছে।
তাকী যাদেহ বলেছেন ,
“ দৃঢ়ভাবে ধারণা করা যায় যারদুশত আলেকজান্ডারের ইরান অভিযান ও সম্রাট দারার হত্যার (খ্রিষ্টপূর্ব 330-331) 258 বছর পূর্বে অথবা আলেকজান্ডারের মৃত্যুর (খ্রিষ্টপূর্ব 323) 272 বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন মতে তিনি নবুওয়াত পান। আবার কারো মতে সম্রাট গুশতাসব তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। সুতরাং যারদুশতের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব 588 অথবা 618 অথবা 630। আর যদি আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সময় হতে 272 বছর পূর্বে ধরি তবে তাঁর জন্ম বছর হবে খ্রিষ্টপূর্ব 595 অথবা 625 অথবা 637। ’
অন্যদিকে ‘ আভেস্তা ’ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে যে ,আসলেই কি আভেস্তা মাযদা ইয়াসনাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা যারথুষ্ট্র কর্তৃক আনীত কিন্তু লিখিত হয় নি ;বরং বংশ পরম্পরায় মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছিল এবং মুসলিম শাসনামলে যারথুষ্ট্রগণ নিজেদের আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ ধর্মগ্রন্থের লিখিত রূপ দেয় নাকি তা পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল পরে সুবিন্যাসিতরূপে উপস্থাপিত হয় ? যদি তা পূর্বে লিখিত ও সংকলিত হয়ে থাকে তাহলে তা কোন্ সময়ে হয়েছিল ?
কেউ কেউ বিশ্বাস করেন ‘ আভেস্তা ’ হাখামানেশী আমলেই সংকলিত হয়েছিল। তবে আলেকজান্ডারের আক্রমণে তা ধ্বংস হয় অথবা আলেকজান্ডার তা পুড়িয়ে দেন। প্রাচ্যের ঐতিহাসিকদের মতে আলেকজান্ডার আভেস্তাকে ভস্মীভূত করেন ,কিন্তু পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞদের মতে এ বিষয়টি অপ্রমাণিত। তাঁদের অনেকে অবশ্য বলেছেন ,আলেকজান্ডারের আক্রমণে আভেস্তা বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। আশকানীদের শাসনামলে আভেস্তাকে পুনরায় সংকলনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু নিশ্চিত যে ,সাসানী শাসনামলের প্রারম্ভ পর্যন্ত আভেস্তা বিন্যস্ত ও সংকলিত হয় নি। সাসানী সম্রাট আরদশিরের নির্দেশে প্রথম একজন যারথুষ্ট্র পুরোহিত আভেস্তা সংকলন ও পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দেন। কিন্তু এই ধর্মজাযক কিসের ভিত্তিতে কাজটি করেছেন তা জানা যায় নি। সাসানী আমলে সংকলিত আভেস্তার সঙ্গে প্রকৃত আভেস্তার কতটা সাদৃশ্য রয়েছে ও কতটা বৈসাদৃশ্য তাও অজ্ঞাত। তবে এটি নিশ্চিত ,এ দু ’ য়ের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। কেনই বা সাসানী আমলে সংকলিত আভেস্তার কিছু অংশ মাত্র এখনও অবশিষ্ট আছে তাও অজ্ঞাত।74
ক্রিস্টেন সেন এ বিষয়ে বলেছেন ,
“ কখনও কখনও কেউ হয়েতো এ বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন কেন সাসানী আমলে সংকলিত আভেস্তার বেশির ভাগ অংশ ইসলামী আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি মুসলমানগণ যারথুষ্ট্রদের আহলে কিতাব বলে মনে করে। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থটির বিনাশের জন্য মুসলিমদের গোঁড়ামি নিশ্চয় দায়ী ছিল না। কারণ আভেস্তার অধিকাংশই নবম খ্রিষ্টাব্দ (তৃতীয় হিজরী শতক) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল অথবা অন্তত আভেস্তার পাহলভী ভাষার ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ যাকে ‘ যান্দ ’ বলে অভিহিত করা হতো যারথুষ্ট্রদের হাতে ছিল। কিন্তু তৎকালীন সময়ে যারথুষ্ট্রগণ বস্তুগতভাবে যে অবস্থায় ছিল তাতে এরূপ বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থটিকে পুনর্লিখনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছান তাদের জন্য সম্ভব হয়নি।
আমরা এ থেকে বুঝতে পারি কেন এর বিধানাবলী বিস্মৃত হয়েছিল। তা এজন্য যে ,যেহেতু সে সময় যারথুষ্ট্র শাসন ছিল না সেহেতু আইনগত বিধি-বিধান অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। তবে কেন স্রষ্টা ,আখেরাত ,সৃষ্টি জগৎ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহকে তারা সংরক্ষণ করেনি ? এর জবাবে বলা যায় আমাদের হাতে কিছু প্রমাণ রয়েছে যাতে বোঝা যায় যারথুষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অবির্ভাবের পরবর্তী একশ ’ বছরে অনেক সংস্কারকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ স্বয়ং যারথুষ্ট্রগণ আগ্রহী ছিলেন আভেস্তায় বর্ণিত কাল্পনিক ও বানোয়াট কাহিনীসমূহ ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসসমূহকে পরিশুদ্ধ করতে ও মুছে ফেলতে। ” 75
ক্রিস্টেন সেন সাসানী আভেস্তা হতে সৃষ্টি সম্পর্কে কাল্পনিক যে বর্ণনা এসেছে তার উল্লেখ করে বলেন ,
“ ...বিশ্ব জগতের বয়স বার হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির তিন হাজার বছর পর্যন্ত আহুরমাযদা (আলোর স্রষ্টা) ও আহ্রিমান (অন্ধকারের স্রষ্টা) পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিলেন। এ দু ’ জগৎ তিন দিকে সীমাহীনভাবে প্রসারিত ছিল এবং এক দিকে মাত্র পরস্পর সীমিত ছিল। আলোর জগৎ ওপরে এবং অন্ধকারের জগৎ নীচে ছিল। এর মাঝামাঝি ছিল বায়ুমণ্ডল। এ তিন হাজার বছর আহুরমাযদার সৃষ্টিসমূহ সম্ভাব্যের পর্যায়ে ছিল। তা পূর্ণতা পেলে আহ্রিমান এর ঔজ্জ্বল্য দেখে তা ধ্বংস করতে মনস্থ করল। আহুরমাযদা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকায় আহ্রিমানের সঙ্গে যুদ্ধ নয় হাজার বছর পিছিয়ে দিলেন। আহ্রিমান শুধু অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকায় তাঁর এ প্রস্তাবে রাজী হলো। আহুরমাযদা আহ্রিমানকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এ যুদ্ধে অন্ধকারের পরাজয়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ কথা শুনে আহ্রিমান ক্রুদ্ধ হলো কিন্তু তিন হাজার বছরের জন্য অন্ধকারের জগতে স্থির হয়ে রইল। এ সময়ে আহুরমাযদা বিশ্ব সৃষ্টির কাজে হাত দিলেন এবং যখন সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত হলো তখন একটি গাভী সৃষ্টি করলেন-যা সর্বপ্রথম গাভী। অতঃপর তিনি গিওমারদ (কিউমারস) নামে এক বৃহৎ মানুষ তৈরি করলেন-যা সর্বপ্রথম মানুষ । এ মুহূর্তে আহ্রিমান তার সৃষ্টি জগতে আক্রমণ করল ও বিষাক্ত পোকামাকড় ,সরীসৃপ ও সৃষ্টিকে কলুষিত করার উপাদানসমূহ তৈরি করল। আহুরমাযদা আকাশে একটি পরিখা খনন করলেন। আহ্রিমান তাঁর রাজ্যে উপর্যুপরি আক্রমণ করতে লাগল ও অবশেষে গিওমারদ ও গাভীটিকে হত্যা করল। কিন্তু গিওমারদদের বীজ যা মাটির নীচে প্রোথিত ছিল তা হতে চল্লিশ বছর পর প্রথম জোড়া মানুষ ‘ মেশিগ ’ ও ‘ মেশইয়ানাগ ’ -এর সৃষ্টি হলো। এ পর্যায়ে আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ যা ‘ গেমিজেশেন ’ নামে অভিহিত তা শুরু হলো। মানুষ কল্যাণ ও অকল্যাণের এ যুদ্ধে ভাল ও মন্দ কর্মের মাধ্যমে এ দু ’ দলের একটিকে বেছে নেয়। ’ 76
এখন আমরা যারদুশতের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব। যাঁরা যারদুশতকে একজন ঐতিহাসিক বাস্তব অস্তিত্বের ব্যক্তিত্ব মনে করেন তাঁরা স্বীকার করেছেন যারদুশত তাঁর সমাজের সামাজিক ,অর্থনৈতিক ও বিশ্বাসগত সংস্কার সাধন করেছেন।
যারদুশতের অন্যতম সংস্কার কর্ম ছিল দেও-দৈত্যদের উপাসনা নিষিদ্ধকরণ। যারদুশত শুধু আহুরমাযদার উপাসনার প্রতি আহ্বান জানাতেন এবং দেওদের অভিশপ্ত ,নিকৃষ্ট ও উপাসনার অযোগ্য বলে প্রচার চালাতেন। তিনি গরুসহ সকল প্রকার প্রাণীর কুরবানী নিষিদ্ধ করেন।
‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ গ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ লেখক দুমযিল বলেছেন ,
“ যারদুশতের সংস্কার কার্যক্রম বেশ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ছিল। তিনি সামাজিক গঠনের নতুন কোন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন নি ,তদুপরি তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। সাধারণ প্রচলিত ধারণা এটি যে ,আর্য জাতির একাংশ তখন যাযাবর অবস্থা হতে শহুরে ও গ্রামীণ সমাজ গঠনের অবস্থায় পৌঁছেছিল। তাই এ পর্যায়ে তারা পশু চারণের জন্য অনির্দিষ্ট চারণভূমিগুলোকে প্রত্যেক গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। গবাদি পশুনির্ভর হওয়ায় তারা নর ও মাদী গরুকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। নতুন শহর বা গ্রাম নির্মাণে পশুর মলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো ,এমনকি গরুর মূত্র পবিত্রকারী হিসেবে পরিগণিত হতো। ”
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,
“ যারদুশত খ্রিষ্টের জন্মের ছয়শ ’ অথবা এক হাজার বছর পূর্বে পশু কুরবানী ও নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় ,যেমন ‘ সুমে ’ -যা ইরানী ও ভারতীয়দের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্মেও প্রচলন ছিল বলে জানা যায়-এগুলোকে নিষিদ্ধ করেন।
যারদুশতের নিকট সৎ চিন্তা ,সৎ কর্ম ও সদুপদেশ ইবাদত বলে বিবেচিত হতো। মানুষের এই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রচেষ্টাই মানুষকে ভাল-মন্দের চিরন্তন সংগ্রামে জয়ী হিসেবে বের করে আনে। অন্যান্য বিষয় কুসংস্কার ও গুনাহ বলে পরিত্যাজ্য। যারদুশত বলেছেন , ‘ নেশাকর পানীয় কিরূপে মানুষকে সৎ কর্মে উৎসাহিত করতে পারে যখন তা নিজেই নোংরা ? যে গরু গৃহস্থের কৃষি কাজের সহায়ক ও একান্ত প্রয়োজনীয় তা দেহহীন ও খাদ্যের প্রয়োজনশূন্য খোদার জন্য কুরবানীর কি প্রয়োজন ? ’
‘ সুমে ’ বা ‘ হুমে ’ নামের যে পানীয়কে যারদুশত নিষিদ্ধ করেন তা এক বিশেষ বৃক্ষের রস হতে তৈরি হতো ,তবে কোন্ বৃক্ষ হতে তা প্রস্তুত হতো তা জানা যায় নি। নেশাকর এ পানীয়টি প্রাচীন আর্যগণ উপাসনার অনুষ্ঠানে পান করত।
ডক্টর মুঈন বলেছেন ,
“ আর্যদের দৃষ্টিতে... এ ধরনের অনুষ্ঠান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য আয়োজন করা হতো।... খোদাগণ এরূপ বন্ধুদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। মানুষ যেমন খাদ্য গ্রহণে শক্তি অর্জন করে তেমনি খোদাগণও এ ধরনের আমন্ত্রণে খাদ্য গ্রহণ করে শক্তিশালী হন। বিশেষত এরূপ শক্তি ‘ সুমে ’ নামক পবিত্র বৃক্ষের রসে রয়েছে। এর পানীয় প্রাণে সজীবতা আনয়ন করে...। পাহাড়ী এ বৃক্ষের কাণ্ড নরম ও আঁশযুক্ত এবং তা হতে দুধের ন্যায় সাদা রস নিঃসৃত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থে এ বৃক্ষকে ‘ হাউমুল মাজুস ’ বলা হয়ে থাকে।... এ বৃক্ষের রসকে রং ধারণ করা পর্যন্ত জ্বাল দেয়া হতো। এই পানীয়টি আর্যদের প্রাচীন ও জাঁকজমকপূর্ণ (সর্বোত্তম!) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে কুরবানীর সময় ব্যবহার করা হতো। এতে অ্যালকোহল থাকায় আগুনের ওপর ছিটিয়ে দেয়া হতো। এতে আগুন দ্বিগুণ হারে জ্বলতে শুরু করত। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্নের সময় পুরোহিতগণও পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় পান করত। সুমে শুধু পবিত্র পানীয় হিসেবেই নয় ;বরং আর্যদের নিকট এর বৃক্ষ খোদার মর্যাদা লাভ করেছিল। ’ 77
যারদুশত এই কুসংস্কারের অবসান ঘটান যদিও পরবর্তীতে সাসানী আমলে এ সংস্কৃতি পুনর্জীবিত হয় এবং যারথুষ্ট্রদের অন্যতম আচারে পরিণত হয়। বলা হয়ে থাকে সাসানী
আভেস্তাতে উল্লিখিত হয়েছে :
“ সকল মদের প্রতিক্রিয়ায়ই রক্ত গরম ও উষ্ণ হয়ে ওঠে ,কিন্তু ‘ সুম ’ -এর পানীয় শান্তি ও স্বস্তিদায়ক। ‘ সুম ’ -এর নেশা মানুষকে হালকা করে। যে ব্যক্তি ‘ সুম ’ কে নিজ শিশু পুত্রের ন্যায় স্নেহ করে ‘ সুম ’ তাদের দেহকে আরোগ্য দান করে। ” (ইয়াসনা 10 ,ধারা 8)
আমরা পুনরায় যারদুশতের সংস্কার কার্যক্রমে ফিরে আসি। জন নাস-এর ‘ ধর্মসমূহের ইতিহাস ’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে :
“ যারদুশতের দৃষ্টিতে সঠিক ও মঙ্গল হলো ভূমি কর্ষণ ,বীজ বপন ,ফসল উৎপাদন ,শুষ্ক ভূমিকে আবাদকরণ ,পানি সেচন ,আগাছা-পরগাছা দূরীকরণ ,উপকারী প্রাণী সংরক্ষণ বিশেষত কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বলদের যত্ন ,পরিচর্যা এবং খাদ্য প্রদান। ভাল মানুষ সব সময় সত্য কথা বলে ,মিথ্যা হতে দূরে থাকে। অন্যদিকে মন্দ লোক এর বিপরীত কাজ করে ও কৃষি কাজের বিষয়ে কখনও চিন্তা করে না। কারণ ‘ আনগারা মাইনিও ’ (মন্দ আত্মা) কল্যাণকর কৃষিকর্মের শত্রু। ”
জন নাস আরো উল্লেখ করেছেন ,
“ যারথুষ্ট্রগণ প্রাচীন কালে তাদের প্রার্থনায় বলতেন: আমি দেওদের শত্রু মনে করি ও মাযদার উপাসনা করি। আমি ইয়াযদানদের নবী ও দেওগণের শত্রু যারদুশতের অনুসারী। আমি পবিত্র আত্মা ‘ এমশাসে পান্দী ’ র প্রশংসা করি এবং জ্ঞানের খোদার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি ,সব সময় সৎ কর্ম ও কল্যাণের পথ অনুসরণ করব ,সত্যকে গ্রহণ করব ,মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদন করব। ব্যক্তির কল্যাণের জন্য যে গরু প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি সহৃদয় হব। আকাশ ও ভূমণ্ডলের আলোকরশ্মি ও তারকাসমূহ এবং ন্যায়নীতি যা প্রভু ইয়াযদানের রহমতস্বরূপ-এ সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। আমি ‘ এরমিতি ’ (সেপানদার মায) পবিত্র ও কল্যাণের ফেরেশতাকে গ্রহণ করলাম। আশা করি তিনি আমার সহযোগী হবেন। আমি চুরি ,অকর্ম ,প্রাণীদের কষ্ট দান ও মাযদার উপাসনাকারীদের শহর ও গ্রামসমূহ নষ্ট করা হতে বিরত থাকব। ” 78
যারদুশতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্ম ছিল খোদা ,সৃষ্টি ও বিশ্ব জগৎকে নিয়ে। যারদুশত বিশ্বের স্রষ্টা খোদা সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করতেন ? তার দাওয়াত কি তাওহীদের দিকে ছিল নাকি তাওহীদ ভিন্ন অন্য কিছুর দিকে ? আমরা ‘ দ্বিত্ববাদ ’ শিরোনামে ভিন্ন এক অধ্যায়ে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।
3. যারদুশতের পরবর্তী সময়ে আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস কিরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল :
ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের কেউই এ বিষয়টি অস্বীকার করেননি ,যারদুশতের মৃত্যুর পরবর্তী যুগে বিশেষত সাসানী আমলে আর্য বিশ্বাসসমূহ অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল। যারদুশতের উচ্চতর ও সুন্দর শিক্ষাসমূহ কুৎসিত ও নিকৃষ্ট চিন্তায় পর্যবসিত হয়। সাসানী আমলে যারথুষ্ট্র ধর্মের মধ্যে অসংখ্য কুসংস্কার ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ প্রবেশ করানো হয়। এ বিষয়ে সকলেই একমত। প্রসিদ্ধ পারস্য বিশারদ দুমযিল তাঁর ‘ যারদুশতের সংস্কার ’ শিরোনামের প্রবন্ধে বলেছেন ,
“ প্রকৃতই যারদুশতের শিক্ষা ও চিন্তা অত্যন্ত অগ্রগামী ও সাহসিকতাপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বর্তমানে প্রচলিত যারথুষ্ট্র ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের পরিণতি লাভ করেছিল। সহজভাবে বলা যায় তার শিক্ষা প্রচলিত রীতি ,প্রবণতা ও অনুসারীদের বস্তুগত প্রয়োজনের আবর্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশেষ ধরনের ‘ র্শিক ’ তাওহীদের স্থান অধিকার করে। ফেরেশতাগণকে মহান খোদার সমকক্ষ বানান হয়। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে পশু কুরবানী প্রচলন লাভ করল। নৈতিকতা বিবেকের হাতে মূল্যায়নের জন্য অর্পিত হলো। ” 79
পি. জে. দুমানাশেহ্ বলেছেন ,
“ যারদুশতের মৌলিক সংস্কারের পর পুনরায় প্রাচীন কাল্পনিক ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলো ,এমনকি যারদুশতকে তাদের নিজেদের মতো রূপ দিল ও ‘ গাতা ’ সমূহে পরিবর্তিত করে ‘ সুমে ’ পানোৎসবের মতো ধর্মবিরোধী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এভাবে মহান খোদা আহুরমাযদা ও নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ খোদা হিসেবে সমকক্ষ হয়ে গেলেন ,অথচ মাযদার ধর্ম এ চিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। ” 80
পুর দাউদ এবং ডক্টর মুঈনও স্বীকার করেছেন প্রকৃত আভেস্তার সঙ্গে সাসানী আভেস্তার লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে এবং সাসানী আভেস্তা যারদুশতের পূর্ববর্তী কুসংস্কারগুলোকে পুনর্জীবিত করেছে। তাঁরা দাবি করেছেন ,
“ যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে হলে ‘ গাতা ’ সমূহ দেখতে হবে। পরবর্তীতে ‘ গাতা ’ সমূহে পরিবর্তন ও বিকৃত সাধন করা হয়েছে। বিশেষত সাসানী আমলে যারথুষ্ট্র ধর্ম এর প্রকৃত উৎস হতে অনেক দূরে সরে পড়ে। ” 81
যে ‘ গাতা ’ সমূহের বিষয়ে পুর দাউদ ও ডক্টর মুঈন বলেছেন ,তা সাসানী আভেস্তার (ইয়াসনাসত ওয়া ইয়াসনা) পাঁচটি অংশের একটি অংশ। ‘ গাতা ’ সমূহ আভেস্তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশ যা যারদুশতের নিকট হতে বর্ণিত বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশেষজ্ঞদের হাতে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে ,সম্পূর্ণ ‘ গাতা ’ অথবা গাতাসমূহের যে অংশে কবিতা আকারে দোয়া ও মুনাজাত রয়েছে সে অংশ স্বয়ং যারদুশত কর্তৃক পঠিত হয়েছে। এ অংশ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য অংশে যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা ও বিশ্বাসের উপস্থিতি রয়েছে এ অংশে তা নেই অথবা খুবই কম রয়েছে ,কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশের বিপরীত বক্তব্য রয়েছে। যাঁরা যারদুশতকে একত্ববাদী মনে করেন তাঁরা গাতাসমূহে বর্ণিত বিষয়সমূহ হতে এর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন। আভেস্তার অন্যান্য অংশ পরবর্তীতে সংযুক্ত হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।
যা হোক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ,পরবর্তী যুগে বিশেষত সাসানী শাসনামলে যারথুষ্ট্র ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সব বিষয়েই ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছিল। এর সপক্ষে সর্বোত্তম দলিল হলো পরবর্তী সময়ে আহুরমাযদার দৈহিক রূপ দেয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতিকৃতি ও মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল।
পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যারদুশত খোদার যে ধারণা প্রচার করতেন তাতে তাঁকে দেহহীন অবস্তুগত সত্তা বলে বিশ্বাস করতেন এবং এজন্যই কুরবানী না করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলতেন , ‘ খোদার দেহ নেই ,তাই তাঁর খাদ্যের প্রয়োজন নেই ’ ।82
সাসানী আমলে খোদা আনুষ্ঠানিকভাবে দৈহিক আকৃতি ,শ্মশ্রুমণ্ডিত ও বস্ত্রাবৃত হয়ে লাঠিসহ আগমন করেন। রাজাব ,রুস্তম ও বুস্তানের শিলালিপি ও খিলানের ওপর যে সকল চিত্র অংকিত হয়েছে তাতে দেখা যায় আহুরমাযদা (খোদা) সাসানী সম্রাট আরদ্শির ,শাহপুর বা খসরুকে স্বহস্তে রাজমুকুট পড়িয়ে দিচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে যারদুশতের নিরাকার খোদা (আহুরমাযদা) সাসানী আমলের যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের মাধ্যমে কিভাবে মূর্তির আকার ধারণ করেছিল।
ক্রিস্টেন সেন রুস্তমের চিত্রকর্মকে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :
“ (আহুরমাযদা) একটি খাঁজকাটা মুকুট পরিধান করে রয়েছেন এবং তাঁর কুঞ্চিত দু ’ বেণী মাথা ও মুকুটের মাঝ হতে বেরিয়ে ঝুলে রয়েছে। তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু ,বলয়াকৃতি বেণী ও চৌকোণাকৃতি চেহারায় প্রাচীনত্বের ছাপ থাকলেও পোশাকের দৃষ্টিতে সাসানী সম্রাটের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই ,তাঁর মুকুট হতেও কুঞ্চিত ফিতাসমূহ ঝুলে রয়েছে ,তাঁর ঘোড়াটিও সম্রাটের ঘোড়ার ন্যায় সজ্জিত। তবে এ খোদার ঘোড়ায় ফুল চিত্রিত রয়েছে। আর সম্রাটের ঘোড়ার অগ্রভাগে দু ’ টি বাঘের ছবি চিত্রিত হয়েছে। ” 83
বর্তমান সময়েও যারথুষ্ট্রদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে শ্মশ্রুমণ্ডিত ,রাজদণ্ডধারী ,কেশরযুক্ত খোদার (আহুরমাযদা) চিত্র সাসানী আমলের চিন্তাগত অবক্ষয়ের চি হ্ন হিসেবে শোভিত হচ্ছে।
যারথুষ্ট্রগণ একদিকে নিজেদের একত্ববাদী বলে দাবি করে বলে , ‘ আহুরমাযদা ’ মুসলমানদের সেই ‘ আল্লাহ্ ’ যাঁকে কোরআনلا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللّطيف الْخبير ‘ দৃষ্টিসমূহ তাকে অনুধাবন করতে পারে না ,অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে অনুধাবন করেন এবং তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ’ 84 বলে উল্লেখ করেছে। আবর অন্যদিকে খোদার বিভিন্ন প্রতিকৃতি এঁকে ও তাঁর লাঠি ,দাড়ি ও মুকুটধারী মূর্তির আকৃতি দান করে।
যে ইরানের মানুষ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে একত্ববাদের সর্বোচ্চ ধারণা অর্জন করেছে ও একত্ববাদের ওপর বিস্ময়কর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছে আশ্চর্যের বিষয় হলো তাদের জন্য শিং ও ডানাযুক্ত খোদার প্রতিকৃতি তৈরি করে একদল লোক চায় তারা একে জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করুক। যদি এটি অবক্ষয় না হয় তাহলে অবক্ষয় কোন্টি ? যদি এর নাম মূর্তি পূজা না হয় ,তবে মূর্তি পূজা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।
ইরানী মুসলমানগণ ইসলামী যে সকল পরিভাষা ফার্সীতে অনুবাদ করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো ‘ আল্লাহ্ ’ যার ফার্সী অনুবাদ হলো ‘ খোদা ’ যা ‘ খুদঅ ’ -এর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ যিনি সৃষ্ট হন নি। ইরানিগণ ‘ আল্লাহ্ ’ শব্দকে ‘ আহুরমাযদা ’ অনুবাদ করে নি কারণ ‘ আহুরমাযদা ’ শব্দটিকে যারথুষ্ট্রগণ এমন অবস্থায় এনেছিল যে ,তাঁর দৈহিক মূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এ মনীষীদের দৃষ্টিতে তা কখনই ‘ আল্লাহ্ ’ শব্দের অনুবাদ হতে পারে না (বলে মনে করেছেন)।
আমরা জানি সাসানী আমলের ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর একটি হলো ‘ র্ফারা আইযাদী ’ । বাহ্যত এটি সাসানী রাজনীতিরই জন্ম যদিও প্রাথমিকভাবে একে একটি অবস্তুগত এবং নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এ শব্দটিও বস্তুগত ও দৈহিক সত্তাসম্পন্ন।
ডক্টর মুঈন বলেছেন ,
“ আভেস্তার বর্ণনা মতে ‘ ফারেহ ’ কে ঈগল বা চিল জাতীয় কোন পাখি হিসেবে ধারণা করা হয়..। জামশিদ (সম্রাট) মিথ্যা ও কটু কথা বললে ফার (অন্য সম্রাট) তার সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হলেন... অন্যদিকে আরদ্শিরের জীবনীতে ‘ ফার ’ একটি ‘ মেষ শাবক ’ বা ‘ হরিণ শাবক ’ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। ” 85
অতঃপর ডক্টর মুঈন আরদ্শির ও তাঁর দাসীর পালিয়ে যাবার ঘটনা ও আরদাওয়ান কর্তৃক তাঁদের অনুসরণের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন ,
“ আরদাওয়ান আরদ্শির ও তাঁর দাসীর অনুসন্ধানে বেরিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে অমুক স্থান দিয়ে তাদের দ্রুত ধাবমান হতে দেখেছে এবং একটি মেষ শাবকও তাঁদের পেছনে পেছনে ছুটছিল। আরদাওয়ান মেষ শাবকের ধাবিত হওয়ার বিষয়টি শুনে এক যারথুষ্ট্র পুরোহিতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন এই খোদায়ী ‘ ফারেহ্ ’ তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আমাদের তাঁর নিকট পৌঁছা উচিত। হয়তো ‘ ফারেহ্ ’ তাঁর নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই আমরা তাঁকে ধরতে পারব। ’ 86
সাসানী আমলে আগুন ‘ খোদার কন্যা ’ বলে পরিচিত হয়ে ওঠে।87 যারথুষ্ট্র ধর্মের কোন কোন শিক্ষা মতে আহুরমাযদা সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং পবিত্র জ্ঞানদাতা সেপান্ত মাইনিও ও মন্দ আত্মা (আনগারা মাইনিও বা আহ্রিমান) উভয়েই তাঁর সৃষ্টি ও পরস্পরের বিপরীতে স্থান নেয়। আবার আভেস্তার কোন কোন বর্ণনা মতে ‘ আহুরমাযদা ’ ও ‘ আহ্রিমান ’ উভয়েই ‘ যারওয়ান ’ নামের তৃতীয় এক অস্তিত্বের সৃষ্টি। যারওয়ান হলো সীমাহীন সময়। এ সম্পর্কে একটি কাল্পনিক বর্ণনাও প্রস্তুত হয়েছে :
“ যারওয়ান হলেন প্রাচীন ও প্রকৃত খোদা ,তিনি সন্তান পাওয়ার লক্ষ্যে অনেকগুলো কুরবানী করেন ও সঙ্কল্প করেন সন্তানের নাম রাখবেন ‘ আহুরমাযদা ’ । তিনি কুরবানী দেয়ার এক হাজার বছর পর সন্দেহে পতিত হলেন যে ,তাঁর কুরবানীসমূহের মধ্যে কোন্টি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে। পরিশেষে তার গর্ভে দু ’ সন্তানের সৃষ্টি হলো। তাদের একজন হলেন ‘ আহুরমাযদা ’ যাঁর নামে তিনি কুরবানী করেছিলেন এবং অন্যজন হলো ‘ আহ্রিমান ’ যে তাঁর সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা হতে সৃষ্টি হয়েছে। যারওয়ান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন ,যে প্রথম উদর হতে বেরিয়ে আসবে তাকেই রাজত্ব দেবেন। আহ্রিমান সর্বপ্রথম পিতার উদর ফেঁড়ে বেরিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। যারওয়ান তাকে প্রশ্ন করলেন: তুমি কে ? আহ্রিমান জবাব দিল: আমি তোমার পুত্র। যারওয়ান বললেন: আমার পুত্র সুন্দর ও সুগন্ধপূর্ণ ,কিন্তু তুমি কুৎসিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময় আহুরমাযদা উজ্জ্বল ও সুগন্ধযুক্ত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হলেন। যারওয়ান তাঁকে পুত্র হিসেবে চিনতে পেরে বললেন: এতদিন আমি তোমার জন্য কুরবানী করতাম ,আজ হতে তুমি আমার জন্য কুরবানী করবে। ” 88
সাসানী আভেস্তার পাঁচ অংশের নাম হলো ‘ ভানদিদাদ ’ যা তৎকালীন যারথুষ্ট্র ধর্মীয় বিধি ও আচার সম্বলিত গ্রন্থ। এর একটি অংশে দেওদের বন্দী করার দোয়া ও মন্ত্রসমূহ লেখা রয়েছে। ‘ ভানদিদাদ ’ শব্দের অর্থ হলো দেওবিরোধী। এ শব্দটিও তৎকালীন সমাজের চিন্তার প্রতিনিধি। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তৎকালীন ধর্মীয় বিশ্বাসকে তুলে ধরেছে। ‘ ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ’ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে পারস্য বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টেন সেন যারথুষ্ট্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন অগ্নি উপাসনা পর্ব ,মাথার খুলির ওপর মৃতদের জন্য খাদ্য ও পানীয় উপস্থাপন ,হিংস্র প্রাণী বিতাড়ণ ,শতাব্দী বর্ষ উদযাপনে অগ্নিশিখার ওপর পাখিদের নিক্ষেপ ,আগুনের চারিদিকে সমাবেশ ও মদ্যপান প্রভৃতি বিষয়সমূহ।89
ক্রিস্টেন সেন তাঁর ‘ ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন ,
‘ ধর্মযাজকগণ সমাজে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন ,যেমন পবিত্রতার বিধি-বিধান কার্যকর করা ,পাপীদের স্বীকারোক্তি শ্রবণ ও তাদের ক্ষমা প্রদর্শন ,কাফ্ফারার (জরিমানা) পরিমাণ নির্ধারণ ,শিশুর জন্ম কালীন আচারাদি পালন ,পবিত্র কোমরবন্ধনী পরিধান করানো ,বিবাহ ,শবযাত্রা ,ধর্মীয় ঈদ উৎসব উদযাপন... ,প্রতিদিন চারবার সূর্যের উপাসনা ও একবার চন্দ্র ও পানির উদ্দেশে প্রতি দোয়া করা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে যেমন শয়ন ,জাগ্রত হওয়া ,ধৌতকরণ ,কোমরবন্ধনী পরিধান ,খাদ্য গ্রহণ ,মলমূত্র ত্যাগ ,হাঁচি দেয়া ,নখ কাটা ,বেণী বাঁধা ,প্রদীপ জ্বালানো প্রভৃতি কর্মের শুরুতে অবশ্যই সকলকে নির্দিষ্ট দোয়া পড়তে হবে। চুলার আগুন কখনও নেভানো যাবে না ,সূর্যের আলো যেন আগুনের ওপর না পড়ে ,পানি যেন আগুনের সঙ্গে মিশ্রিত না হয় ,ধাতব জিনিসে যেন মরিচা না পড়ে ,কারণ ধাতব বস্তুসমূহ পবিত্র। এ সকল বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তিকে অথবা ঋতুমতী নারীকে বা যে নারী সদ্য বাচ্চা প্রসব করেছে তাকে বিশেষত যদি মৃত সন্তান প্রসব করে থাকে ,স্পর্শ করে তাদের পবিত্র করার জন্য ক্লান্তিকর ও কষ্টবহুল আচার পালন করা হতো। যারদুশতের অনুসারী আরদাই ভিরয নামের এক আউলিয়া ‘ মিরাজ ’ অথবা ‘ মুকাশাফায় ’ জাহান্নামের আযাবগ্রস্তদের ,যেমন হত্যাকারী ,সমকামী ,কাফের ,পাপী ও অপরাধীদের জাহান্নামের আগুনের মধ্যে বিভিন্ন রকম আযাবে রত দেখেন। গরম পানিতে গোসল করা ,নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা পানি ও আগুনকে অপবিত্র করা ,খাদ্য গ্রহণের সময় কথা বলা ,মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা এবং জুতা ব্যতীত খালি পায়ে হাঁটার অপরাধে তারা অন্যান্য পাপীদের সঙ্গে আযাব ভোগ করছিল। ’ 90
গরু বিশেষত ষাঁড় গরুর জন্য বিশেষ পবিত্র স্থান ছিল। যারদুশতের মৌল শিক্ষায় গরুসহ যে কোন প্রাণী কুরবানী নিষিদ্ধ ছিল এজন্য যে ,এর পূর্বে দরিদ্রদের খাদ্য দানের জন্য নয় ;বরং এ ধরনের প্রাণীর রক্ত ঝরানোর ফলে খোদাগণ শক্তিশালী হন এ বিশ্বাসে কুরবানী করা হতো। তাই যারদুশত তাগিদ দেন- যেন এ ধরনের পশু কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। এ শিক্ষার কারণে (সম্ভবত প্রাচীন কালের প্রকৃতি পূজার প্রভাবও ছিল) যারদুশতের পরবর্তী সময়ে গরু ধীরে ধীরে পবিত্র স্থান লাভ করে ও বিশ্ব সৃষ্টির কাল্পনিক গল্পে সৃষ্টির প্রথম প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রথম মানব (গিওমারদ)-এর সঙ্গে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। সেই সাথে গরুর মূত্র পবিত্রকারী হিসেবে স্বীকৃতি পায় । যেমনটি ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
‘ ভানদিদাদ গ্রন্থে পানি এবং পবিত্রকরণে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে পানি হতে পবিত্রতর একমাত্র বস্তু হিসেবে গরুর মূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ’
প্রসিদ্ধ আরব কবি আবুল আলা মুয়াররী তাঁর প্রসিদ্ধ এক কবিতায় ইসলাম ,খ্রিষ্ট ,ইহুদী ও যারথুষ্ট্র ধর্মকে একত্রে সমালোচনা করে বলেছেন ,
‘ আশ্চর্য হই আমি পারস্য সম্রাট ও তাঁর অনুসারীদের জন্য
যখন গরুর মূত্র দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল দেখি ধৌত করতে ,
আশ্চর্য হই আমি ইহুদীর জন্য যখন বলে তারা
পছন্দ করেন খোদা ভূনা মাংসের গন্ধ আর তরুণাস্থি খেতে।
আশ্চর্য হই আমি নাসারাদের ব্যাপারে যখন বলে প্রভু হয়েছেন নির্যাতিত
অথচ সাহায্য করা হয় নি তাকে যখন তিনি ছিলেন জীবিত!
দূরবর্তী শহর হতে এলো এক জাতি নতুন
পাথর ছুঁড়ে মারে আবার পাথরেই করে চুম্বন! ’
সাসানী আভেস্তার অন্যতম কঠোর নীতি হলো মাটিকে কলুষিত না করা এবং মৃতদের দাফন না করা। আভেস্তার একটি অংশ ভানদিদাদে অন্য সকল বিষয়ের চেয়ে এ বিষয়ে অধিকতর তাগিদ দেয়া হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুদের ন্যায় যারথুষ্ট্রগণও অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব পর্যন্ত মৃতদের দাফন করত না। যারথুষ্ট্রগণ তাদের মৃতদের একটি উঁচু স্তম্ভের ওপর রেখে আসত যাতে শকুন ও অন্যান্য পাখি তা ভক্ষণ করে। অর্ধ শতাব্দী হলো ইরান সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এটি নিষিদ্ধ করে। সেই সাথে যারথুষ্ট্রদের সচেতনতার কারণে বিষয়টি বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। শুনেছি ইয়ায্দ শহরে এখনও মরদেহের জন্য স্থাপিত স্তম্ভ রয়েছে।
ডক্টর মুঈন এ বিষয়ে বলেছেন ,
‘ মাযদা ধর্মে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের অনেক কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। মাযদা ধর্মে মূল উপাদান হলো আগুন। বেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে অবিরাম জ্বালানী সরবরাহের মাধ্যমে নির্বাপিত হওয়া হতে রক্ষা করা হতো... তদুপরি পারসিক ধর্মে প্রশংসা নিবেদনের রীতিতে বিশেষ ভিন্নতা ছিল। যেহেতু তারা বিশ্বাস করত আগুন ও মাটি পবিত্র উপাদান সেহেতু মৃতদেহ দাফন বা ভস্মীভূত করার মাধ্যমে একে অপবিত্র করাকে সঠিক মনে করত না। তাই শবদেহকে মরুভূমি বা উন্মুক্ত কোন প্রান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো এবং বিভিন্ন আচারাদি পালনের পর সেখানে ফেলে আসা হতো। ’ 91
সুতরাং বোঝা যায় মাযদা ধর্মে পানি ,মাটি ও আগুনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। কিন্তু এ উপাদানগুলো অন্য বস্তুকে পবিত্র করতে পারে তাদের এ ধারণা ছিল না। ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
‘ অগাটিয়াস স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ,সাসানী আমলে শবদেহ বিশেষ স্থানে (ছাদহীন উন্মুক্ত সমাধিস্থলে) ফেলে আসার রীতি ইরানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হিউয়ান সাংও ইরানীদের রীতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলেছেন তারা মৃতদেহকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে আসত। ’ (বিল ,খ. 2 ,পৃ. 278)
তিনি সাসানী শাসক কাবাদের সেনাপতি সিয়াভাসের প্রতি পুরোহিতদের অসন্তুষ্টির বিষয়টি বর্ণনা করে বলেছেন ,
‘ পুরোহিতদের সর্বোচ্চ বিচারালয় তাঁদের প্রতি গুরু অপরাধের অভিযোগ এনেছিল এজন্য যে ,তাঁরা প্রচলিত ধর্মীয় রীতিতে জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন না এবং এর কাঠামোর বাইরে নতুন খোদাগণের উপাসনা করেছেন এবং প্রয়াত স্ত্রীকে যারথুষ্ট্র রীতি (শবদেহকে উন্মুক্ত সমাধিস্থলে শিকারী পাখিদের ভক্ষণের জন্য ফেলে আসা) লঙ্ঘন করে দাফন করেছেন। ’ 92
‘ ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ’ গ্রন্থের ফার্র্সী অনুবাদক রাশিদ ইয়াসেমী বলেছেন ,
‘ ...হাখামানেশী সম্রাটগণ যারথুষ্ট্র ধর্মের রীতি অনুযায়ী সকল আচরণ করেছেন কিনা তা বলা মুশকিল। কারণ তাঁদের ‘ আনাহিতা ’ র উপাসনা ও মৃতদের দাফন করার রীতি যারথুষ্ট্র ধর্মরীতির পরিপন্থী ছিল। ’ 93
জনাব ইয়াসেমী দাবি করেছেন হাখামানেশী আমলেও যারথুষ্ট্র ধর্মে মৃতদের দাফন করা নিষিদ্ধ ছিল।
যারথুষ্ট্র ধর্মে দ্বিত্ববাদ
ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে ইরানে দ্বিত্ববাদ প্রচলিত ছিল কিনা তৎকালীন ইরানের চিন্তা ও বিশ্বাসগত অবস্থা জানার জন্য এ প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। কারণ ইহুদী ,খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধগণ সংখ্যালঘু হিসেবে সামগ্রিক চিন্তা-বিশ্বাসে তেমন ভূমিকা রাখেনি। তাই ইসলামপূর্ব সময়ে এ ক্ষেত্রে ইরানে কিরূপ বিশ্বাস ছিল তা এখানে আমরা আলোচনা করব। পূর্ববর্তী আলোচনায় যারদুশতের আগমনের পূর্বে প্রকৃতি পূজার পর্যায়ে আর্যদের মধ্যে দ্বিত্ববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ করেছি। দুমযিলের মতে দ্বিত্ববাদ ইরানী আর্যদের চিন্তাগত বিশেষত্ব। এটি প্রচলিত ধারা হলেও আমাদের জানতে হবে যারদুশত যিনি আর্যদের মাঝে
চিন্তাগত সংস্কার সাধন করেছেন তিনি এ বিষয়ে কি ধারণা পোষণ করতেন ? তিনি সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন এনেছিলেন ?
যদি সাসানী আভেস্তাকে মানদণ্ড হিসেবে ধরি তবে নিঃসন্দেহে যারদুশত দ্বিত্ববাদী ছিলেন ,কিন্তু আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি বিশেষজ্ঞগণ সাসানী আভেস্তার একটি ক্ষুদ্র অংশ গাতাসমূহকেই কেবল যারদুশতের বলে মনে করেন এবং বাকী অংশকে নতুন সংযোজন বলে বিশ্বাস করেন। গাতাসমূহতে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এর বিষয়বস্তু দ্বিত্ববাদ অপেক্ষা একত্ববাদের নিকটবর্তী।
একত্ববাদের বিভিন্ন পর্যায় ও ভাগ রয়েছে ,যেমন সত্তাগত একত্ববাদ (তাওহীদে যাতী) ,গুণগত একত্ববাদ (তাওহীদে সিফাতী) ,কর্মগত একত্ববাদ (তাওহীদে আফআলী) এবং উপাসনাগত একত্ববাদ (তাওহীদে ইবাদী)।
সত্তাগত একত্বের অর্থ আল্লাহর সত্তা এক ,তাঁর কোন অংশীদার নেই ,তিনিই একমাত্র অসীম ,চিরন্তন ও স্বাধীন সত্তা। তিনি ভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সত্তা সসীম ও নির্ভরশীল এবং তাদের এ নির্ভরশীলতা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বয়ং আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেছেন ,
ليس كمثله شيء ‘ কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় ’ 94 এবংو له المثل الأعلى ‘ সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই ’ ।95
আল্লাহর গুণগত একত্বের অর্থ তাঁর সকল গুণাবলী তাঁর সত্তাগত। তিনি জ্ঞানী ,শক্তিমান ,জীবন্ত (প্রাণের অধিকারী) এবং আলোকিত। এর অর্থ তাঁর সত্তাই জ্ঞান ,শক্তি ,প্রাণ ও ঔজ্জ্বল্য এবং এগুলো সবই এক অর্থাৎ তিনি পূর্ণরূপে এক ও সত্তাগতভাবে একক।
তাঁর সত্তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অসীমত্বের অর্থ তিনি ব্যতীত এরূপ কোন অস্তিত্ব নেই এবং তাঁর পর্যায়ে তিনি একক। অন্যভাবে তাঁর সত্তাগত পূর্ণতার অর্থ তাঁর গুণাবলী ও সত্তা একই বস্তু। কারণ সত্তা ও গুণাবলী পৃথক হবার অর্থ সীমাবদ্ধতা এবং শুধু সীমাবদ্ধ সত্তারই সত্তা ও গুণাবলী পৃথক হওয়া সম্ভব ;অসীম সত্তার নয়।
তাঁর কর্মগত একত্বের অর্থ বিশ্ব জগতে প্রকৃত কর্তা ও কার্যশীল সত্তা একমাত্র তিনি। অন্য সকল কর্তা ও প্রভাবশীল সত্তা তাঁর ইচ্ছা ও প্রভাবের সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করে। বস্তুগত ও অবস্তুগত কোন সত্তাই তাঁর ইচ্ছা ও প্রভাব ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম নয়। বিশ্বের কার্যকারণ সূত্রসমূহ তাঁরই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। অস্তিত্ব জগৎ তাঁরই মালিকানাধীন এবং এ ক্ষেত্রে কেউই তাঁর অংশীদার নয়।
لم يَتَّخِذ صاحبةً و لا وَلَداً و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيراً
‘ যিনি কোন বন্ধু বা সন্তান গ্রহণ করেন নি ,যাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই ,যাঁর অসীম ক্ষমতায় কোন সহযোগীর প্রয়োজন নেই। তাঁরই উপযুক্ত মহত্ত্ব বর্ণনা কর। ’ 96
তাঁর উপাসনাগত একত্বের অর্থ যেহেতু তিনি সত্তা ,গুণ ও কার্যগতভাবে একক সেহেতু মানুষ তাঁর বান্দা ও সৃষ্টি হিসেবে কেবল তাঁরই উপাসনা করবে।و ما أمروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين ‘ তাদের এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয় নি ,তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত করবে। ’ 97
যারদুশতের বিষয়ে যা জানা যায় তা হলো তিনি ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাতেন। যারদুশতের দৃষ্টিতে মানুষ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা অদৃশ্যমান আহুরামাযদা উপাসনার জন্য একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। তিনি নিজেকে আহুরমাযদার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হিসেবে দাবি করে তৎকালে প্রচলিত দিভগণের (দৈত্যদের) উপাসনা করা হতে নিষেধ করেন।
যারদুশতের পূর্বে আর্যদের প্রকৃতির ক্ষতিকর শক্তি ও উপাদানের উপাসনার বিষয়টিকে ডক্টর মুঈন অস্বীকার করে বলেছেন ,তৎকালীন সময়েও আর্যরা শুধু উপকারী শক্তি ও আত্মাসমূহের উপাসনা করত। তিনি বলেন , ‘ আর্যগণ ক্ষতিকর আত্মা ও বস্তু হতে বিরক্ত বোধ করত এবং তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করত। তারা কখনই তাদের সন্তুষ্ট ও আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কুরবানী ও তাদের উপাসনা করত না (যাতে করে তাদের রাগ রহমতে পরিবর্তিত হয় এ চেষ্টা করত না)। প্রাচীন তুর্কী ও মোঘল জাতির সঙ্গে এ ক্ষেত্রেই আর্যদের পার্থক্য ছিল। কারণ অনার্য এ সকল জাতির বিশ্বাস ছিল কুরবানী ও ইবাদতের মাধ্যমে ক্ষতিকর আত্মাকে সন্তুষ্ট করে তাদের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।98
যদি ডক্টর মুঈনের এ কথা মেনে নিই তবে বলতে হবে যে ,যারদুশত আর্যদের মাঝে এ ক্ষেত্রে কোন সংস্কারই করেন নি। কারণ ক্ষতিকর আত্মাসমূহের (দিভগণের) উপাসনা আর্যদের মধ্যে ছিলই না যাতে করে নিষেধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাহ্যত এ ধারণাটি সঠিক নয় এবং সকল বিশেষজ্ঞই এর বিপরীত মত পোষণ করেন। বিশেষত স্বয়ং যারদুশতের পক্ষ হতে যতটা গুরুত্ব সহকারে এ কর্মটিকে নিষেধ করা হয়েছে বলে উদ্ধৃত আছে তা থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে এরূপ উপাসনার প্রচলন ছিল।
জনাব আলী আসগার অনূদিত জন নাস-এর ‘ ধর্মসমূহের ইতিহাস ’ গ্রন্থে ‘ আহুরা ’ ও ‘ দিভ ’ শব্দ দু ’ টি ভারতীয় ও ইরানীদের নিকট অর্থগতভাবে কিরূপ পরিবর্তন লাভ করেছে তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে :
‘ যারদুশত... পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন ‘ দিভগণ ’ (তুর্কী ও মুগদের উপাস্য) মন্দ আত্মার অধিকারী ও ক্ষতিকর। তারা ভাল আত্মার সঙ্গে সব সময় সংঘর্ষে লিপ্ত। তারা সকল অকল্যাণ ও মন্দ কর্মের উৎস ,তারা মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে আহুরামাযদার উপাসনা হতে বিরত রাখে। তাই তিনি তাদের উপাসনা হতে নিষেধ করেছেন। ’ 99
জন নাস যারদুশতের দাওয়াতকে সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরেছেন :
ক. তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘোষণা ও তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান।
খ. তৎকালীন সময়ে প্রচলিত সকল আত্মার বিশ্বাস হতে শুধু ভাল ও কল্যাণমূলক আত্মা আহুরামাযদার বিশ্বাসকে গ্রহণ এবং তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও জ্ঞানী হিসেবে সবচেয়ে মর্যাদাবান প্রভু বলে ঘোষণা দান। প্রাচীন লোকদের বিশ্বাসের বিপরীতে যারথুষ্ট্র সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক কিছু ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন ,এই প্রাচীন নবীর মতে সকল সৃষ্টিই আহুরামাযদার ইচ্ছা ও শক্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। গাতাসমূহের শেষাংশের ধারাসমূহে উল্লিখিত হয়েছে আহুরমাযদা আলো ও অন্ধকার উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা।
গ. আহুরামাযদা তাঁর পবিত্র ও ঐশী ইচ্ছাকে ‘ সেপান্ত মাইনিও ’ (পবিত্র জ্ঞান) নামের এক পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সম্ভাব্য অবস্থা হতে কার্যকর অবস্থায় এনেছেন।100
ঘ. যদিও আহুরামাযদার সম্মানিত সিংহাসনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তদুপরি যারদুশত বিশ্বাস করেন প্রতিটি কল্যাণের বিপরীতে একটি অকল্যাণ রয়েছে। যেমন সত্য ও হকের বিপরীতে রয়েছে মিথ্যা ও বাতিল ,জীবনের বিপরীতে রয়েছে মৃত্যু। তেমনি পবিত্র আত্মা সেপান্ত মিনিউয়ের বিপরীতে রয়েছে অপবিত্র আত্মা আনগারা মাইনিও। ...প্রথম দিনই তারা একত্রে
অস্তিত্বে আসে ও পরস্পরের বিপরীতে একজন জীবন ও গঠন এবং অন্যজন মৃত্যু ও ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে। অবশেষে মিথ্যা ও মন্দের অনুসারীরা চিরস্থায়ী দোযখে স্থান নেবে এবং সত্যের অনুসারীরা পবিত্র চিন্তার চিরস্থায়ী বেহেশত লাভ করবে... বিশ্ব সৃষ্টির প্রথমে পবিত্র ও সৎ কর্মশীল আত্মা তার শত্রু অপবিত্র আত্মাকে বলে , ‘ আমরা চিন্তা ,কথা ও কর্মে দেহ ও আত্মার দু ’ জগতের কোনটিতেই পরস্পরের সমমনের হতে পারব না। ’
ঙ. যারথুষ্ট্র ধর্মের নৈতিকতা এ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ,প্রত্যেক মানব সন্তানের অন্তর ভাল ও মন্দের চিরন্তন সংগ্রামের ময়দান এবং মানুষের হৃদয় (বক্ষ) চুল্লীর ন্যায় যেখানে সব সময় এই যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। যে দিন আহুরামাযদা মানুষকে তৈরি করেন সে দিন তাকে স্বাধীন ক্ষমতা দান করেন। অর্থাৎ এ শক্তি দান করেন ,যেন সে স্বেচ্ছায় ঠিক ও ভুল পথ বেছে নিতে পারে।101
অবশ্য জন নাস যেরূপ স্পষ্টভাবে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন তা গাতাসমূহের মুনাজাতসমূহে এভাবে পরিষ্কার করে বলা হয় নি। অবশ্য গাতাসমূহের কোন কোন বাক্য ও অংশ হতে এ বিষয়ে ধারণা করা যায় যদিও কোন কোন বাক্য বা শ্লোকে এর বিপরীত কথাও বলা হয়েছে। তাই সমগ্র গাতা যারদুশত হতে বর্ণিত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। স্বয়ং জন নাস এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে ,যারদুশতের মতে আনগারা মাইনিও বা আহ্রিমানকে আহুরামাযদা স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন নাকি তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন। এজন্য তিনি বলেছেন , ‘ যারথুষ্ট্র ধর্মের গ্রন্থসমূহে মন্দ আত্মা আহ্রিমানের উৎপত্তিতে আহুরামাযদার ভূমিকার বিষয়টি অস্পষ্ট। তাই বোঝা যায় না স্বয়ং আহুরামাযদার সঙ্গেই সৃষ্টির শুরুতে উৎপত্তি লাভ করেছে নাকি আহুরামাযদা তাকে পরবর্তীতে সৃষ্টি করেছেন। অন্যভাবে বলা যায় ,প্রশ্ন হলো: মন্দ আত্মা আহ্রিমানকে মাযদা সৃষ্টি করেছেন নাকি তার অস্তিত্ব ছিল ,মাযদা তাকে আবিষ্কার করেছেন এ অর্থে যে ,যেখানেই ভাল রয়েছে তার বিপরীতে মন্দও রয়েছে এবং যেখানে আলো রয়েছে তার সঙ্গে অন্ধকারও জন্ম লাভ করে। ’
জাওযাফ গিওর তাঁর ‘ প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহ ’ নামক গ্রন্থে দাবি করেছেন যারদুশত যখন বাল্খের সম্রাট গুশতাসবের দরবারে যান তখন রাজসভার পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়। পণ্ডিতগণ তাঁকে প্রশ্ন করেন , ‘ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা কে ? ’ তিনি বলেন , ‘ বিশ্ব জগৎ ও জ্ঞানবানদের প্রতিপালক আহুরমাযদা। ’ তাঁরা বলেন , ‘ তুমি কি মনে কর সমগ্র বিশ্ব জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন ? ’ যারদুশত বলেন , ‘ তিনি যা কিছু কল্যাণকর তা সৃষ্টি করেছেন। কারণ আহুরামাযদা কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ করতে অক্ষম। ’
তাঁরা বলেন , ‘ তাহলে মন্দ ও অকল্যাণ (কুৎসিত) কার সৃষ্টি ?
তিনি বলেন , ‘ আনগারা মাইনিও মন্দ ও কুৎসিতকে এ পৃথিবীতে এনেছে। ’
তাঁরা বলেন , ‘ তাহলে বিশ্বে দু ’ জন খোদার অস্তিত্ব রয়েছে। ’
তিনি বলেন , ‘ হ্যাঁ ,বিশ্বে দু ’ জন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে...। ’
বাহ্যত মনে হয় জাওযাফ গিওর ইতহাস হতে নয় যারথুষ্ট্রগণের বর্ণনা হতে উপরোক্ত বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। যদি যারথুষ্ট্রদের প্রচলিত বর্ণনায় বিশ্বাস করি তবে নিঃসন্দেহে যারদুশত দ্বিত্ববাদী ছিলেন বলে মেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলিল হলো সাসানী আভেস্তার অংশ ‘ ভানদিদাদ ’ যাতে বিশ্ব জগৎকে দু ’ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যার এক ভাগ ‘ আহুরমাযদা ’ র সৃষ্টি এবং পূর্ণ কল্যাণ ও বরকতময় এবং অন্যভাগ আহ্রিমানের সৃষ্টি ও অকল্যাণে পূর্ণ।
গাতাসমূহের বিভিন্নতার কারণে বিশেষজ্ঞগণ যারদুশতের একত্ববাদী বা দ্বিত্ববাদী হওয়ার বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।
প্রসিদ্ধ ইরান বিশেষজ্ঞ গিরিশম্যান তাঁর ‘ প্রাচীন যুগ হতে ইসলামী যগ পর্যন্ত ইরান ’ শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ,
‘ যারথুষ্ট্র ধর্ম একত্ববাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু সাসানী আমলে বৃহৎ এক ধর্মের (খ্রিষ্টবাদ) প্রভাবে একত্ববাদ গ্রহণ করে। ’
এর বিপরীতে দুমযিল বিশ্বাস করেন (যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) যারদুশত তাওহীদবাদী ছিলেন।
শাহরেস্তানী তাঁর ‘ মিলাল ওয়ান নিহাল ’ গ্রন্থে যারদুশতকে একত্ববাদী বলে উল্লেখ করেছেন। শাহরেস্তানী ইসলামী দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোকে ভাল-মন্দকে যেমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা শুধু ইসলামী চিন্তাশাস্ত্রের সঙ্গেই সমঞ্জস্যশীল ,যারদুশতের চিন্তাশাস্ত্রের সঙ্গে নয়।
বাস্তব কথা হলো একত্ববাদকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যারথুষ্ট্র ধর্মকে একত্ববাদী ধর্ম বলা সত্যিই মুশকিল। যারথুষ্ট্র ধর্ম একত্ববাদী নাকি দ্বিত্ববাদী তা জানার জন্য সাধারণত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হলো যারদুশত আহুরামাযদাকে আহ্রিমানের সৃষ্টিকর্তা ও আহ্রিমানকে তাঁর দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করেন কিনা ? নাকি আহ্রিমানকে আহুরামাযদার মতই চিরন্তন মনে করেন ? তাঁরা ধরে নিয়েছেন যারদুশতের দৃষ্টিতে যদি আহ্রিমান আহুরামাযদার সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে প্রমাণিত হবে যারথুষ্ট্র ধর্ম একত্ববাদী ছিল।
এ ধারণাটি সত্তাগত একত্ববাদের ক্ষেত্রে সঠিক হলেও কর্মগত একত্ববাদের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কারণ প্রচলিত যারথুষ্ট্র ধর্মগ্রন্থসমূহ বিশেষত গাতাসমূহ হতে যতটা বোঝা যায় যারদুশত প্রাচীন আর্যদের ন্যায় অমঙ্গলকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন । তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্ব যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত নেই। কারণ এতে একদিকে বাস্তবিক অর্থেই মন্দ ও কুৎসিতের
অস্তিত্বসমূহ রয়েছে যা পবিত্র অস্তিত্ব যেমন আহুরামাযদা অথবা সেপান্ত মিনিউয়ের প্রতি সম্পর্কিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই মন্দসমূহের অস্তিত্ব এমন এক অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যা সত্তাগতভাবেই মন্দ ও কুৎসিত।
এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করলে আহুরামাযদা আহ্রিমানের সৃষ্টিকর্তা হোক বা না হোক ,একত্ববাদের ভিত্তি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আহ্রিমান যদি আহুরামাযদার সৃষ্টি না হয় তবে বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাওহীদ পরিপন্থী। আর যদি সে আহুরামাযদারই সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে প্রথমত প্রশ্ন আসে আহুরামাযদা নিজেই যখন অকল্যাণের কর্তা সেখানে তাঁর বা সেপান্ত মাইনিওয়ের বিপরীতে আনগারা মাইনিওয়ের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি ? বরং এই মন্দকে অবশ্যম্ভাবী একক অস্তিত্ব হিসেবে আহুরমাযদার প্রতি অথবা তাঁর প্রথম সৃষ্টি (صدر أوّل ) হিসেবে সেপান্ত মাইনিওয়ের প্রতি সম্পর্কিত করব। যদি মন্দসমূহকে আহুরামাযদার সঙ্গে সম্পর্কিত করা না যায় তবে কিরূপে তিনি সকল অকল্যাণ ও মন্দের উৎস আনগারা মাইনিওকে সৃষ্টি করলেন ? দ্বিতীয়ত আনগারা মাইনিও জন্মের পর কি ভূমিকা পালন করছে ? সে কি স্বাধীনভাবে মন্দসমূহকে সৃষ্টি করছে নাকি আহুরমাযদার ইচ্ছার অধীনে তা করছে ? যদি সে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে তবে আহুরামাযদার অংশীদার রয়েছে কারণ সৃষ্টি ও কর্মের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এটিই র্শিক। আর যদি স্বাধীন না হয়ে থাকে ও কোরআনের এ আয়াতের উদাহরণو ما تشاؤون إلّا أن يشاء الله ‘ তারা কোন ইচ্ছাই করে না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ’ -সে ক্ষেত্রে আনগারা মাইনিওয়ের উপস্থিতি আহুরামাযদা হতে মন্দকে দূরীভূত করার বিষয়ে কোন প্রভাবই রাখে না।
মূলত দ্বিত্ববাদের উৎপত্তি এখান হতে যে ,মানুষ সৃষ্টি জগৎকে দু ’ ভাগে বিভক্ত দেখে: ভাল ও মন্দ। তারা ভালর জন্য এক উৎস ও মন্দের জন্য ভিন্ন উৎস রয়েছে বলে মনে করে। ভালর কর্তাকে তারা পূর্ণতম ও সর্বোচ্চ সকল গুণের অধিকারী হিসেবে কল্যাণময় ও ক্ষতিকর সকল অস্তিত্বকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করাকে সঠিক মনে করে নি। এজন্যই তাদের সৃষ্টিকে ভিন্ন এক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধরে নিয়েছে যে সকল অকল্যাণের উৎস। অর্থাৎ খোদা কর্তৃক অমঙ্গলের সৃষ্টিকে অস্বীকার ,অমঙ্গলের জন্য ভিন্ন খোদার বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে।
যদি অমঙ্গলের উৎস ও সৃষ্টিকর্তা খোদার সমান্তরালে না হয় ;বরং তাঁরই সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর পাশাপাশি স্বতন্ত্র স্বাধীন এক সত্তার উপস্থিতিকে অস্বীকার করলে ও অকল্যাণকর সৃষ্টিসমূহকে তাঁর প্রতি সম্পর্কিত না করার বিষয়টি থেকেই যায়। অন্যভাবে বললে যদিও আল্লাহর সত্তাগত পর্যায়ে কোন অংশীদারকে অস্বীকার করা হয়েছে ,কিন্তু তাঁরই এক সৃষ্টিকে তাঁর সৃষ্টিতে অংশীদার ধরে নেয়া হয়েছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রেও খোদার সঙ্গে অংশীদার থাকার বিশ্বাস সকল নবীর শিক্ষার পরিপন্থী। দর্শনের উচ্চতর প্রজ্ঞায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অংশীদার সাব্যস্ত করা খোদার সত্তার সঙ্গে অংশীদারিত্বের শামিল।
বাস্তব বিষয় হলো ভাল-মন্দের বিষয়ে এরূপ সন্দেহে পতিত হওয়া কোন অর্ধ দার্শনিকের জন্যও মানানসই নয়। সেখানে কোন নবী বা পূর্ণ দার্শনিকের কথা তো ভাবাই যায় না। একজন নবী যিনি সমগ্র অস্তিত্ব জগৎকে ওপর হতে (উচ্চতর এক স্থান) দেখেন তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি জগতে আলো ,উজ্জ্বলতা ,মঙ্গল ,প্রজ্ঞা ও রহমত ছাড়া কিছুই নেই এবং একটি মাত্র ইচ্ছাই পূর্ণতম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কার্যকারণ সূত্রের এ বিশ্ব জগৎ পরিচালনা করছে ,অন্য কারো সেখানে অন্তর্ভুক্তি ও অংশীদারিত্ব নেই। একজন নবী ও আল্লাহর ওলীর জন্য অসম্ভব ,এরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হবেন এবং এমন চিন্তার উপস্থাপন করবেন ,এমনকি একজন পূর্ণ দার্শনিকও সকল মন্দ ও অকল্যাণকে আপেক্ষিক ও অস্তিত্বহীন বলে মনে করেন। এই আপেক্ষিক ও সম্পর্কমূলক বিষয়গুলো নিয়েই বিশ্ব জগৎ পূর্ণতম ও সর্বোত্তম শৃঙ্খলা লাভ করেছে এবং মহান আল্লাহর পূর্ণতম প্রজ্ঞার ফলশ্রুতিতেই তা ঘটেছে। যদি তা না থাকত তাহলে বিশ্ব জগৎ অপূর্ণ হতো।
একত্ববাদী ধর্মের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্ সকল দিক হতে পূর্ণতম। তিনি সকল রকম ত্রুটি হতে মুক্ত। সকল অস্তিত্বশীলই তাঁর পূর্ণ প্রজ্ঞা ও মহান ইচ্ছার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাঁর ইচ্ছায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাঁর কোন সৃষ্টিই অর্থহীন নয়। বিশ্বের কিছুই প্রকৃত মন্দ (নিরঙ্কুশ মন্দ) নয়। সকল কিছুই কল্যাণকরভাবে সৃষ্ট হয়েছে।
তিনি বলেছেন ,الذي أحسن كلّ شيء خلقه ‘ তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। ’ 102 يحيي و يميت و يميت و يحيي ‘ তিনি অস্তিত্বে আনেন ,ধ্বংস করেন ,জীবন দান করেন ,মৃত্যু দান করেন ’ অর্থাৎ তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যুবরণ করান এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন ও তাকে পুনর্জীবিত করেন।103 يولج اللّيل في النّهار و يلج النّهار في اللّيل ‘ তিনিই দিবা-রাত্রি ও আলো-অন্ধকার আনয়ন করেন ,তিনিই রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান। ’ 104 তিনিই আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেনالحمد لله الّذي خلق السّماوات و الأرض و جعل الظّلمات و النّور ‘ সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ’ 105
আমরা পূর্বে জাওযাফ গিওরের ‘ প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহ ’ গ্রন্থ হতে যারদুশতের সঙ্গে সম্রাট গুশতাসবের সভাসদ পণ্ডিতদের কথোপকথনের উল্লেখ করেছি যেখানে যারদুশত খোদাকে শুধু ভাল ও কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা বলে উল্লেখ করে মন্দ ও অকল্যাণসমূহকে অন্য এক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলেছেন। তিনি খোদাকে এরূপ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মনে করেন। যদিও এ ধরনের কোন সংলাপের অস্তিত্বের বিষয়ে আমরা সন্দেহ পোষণ করছি। তবে এটি সত্য ,এ সংলাপ সকল যারথুষ্ট্রের চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংলাপের সঙ্গে আল্লাহর নবী হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-এর সঙ্গে ফিরআউনের সংলাপের যে বর্ণনা কোরআন দিয়েছে তা তুলনা করুন। ফিরআউন হযরত মূসা ও হারুনকে লক্ষ্য করে বলে , ‘ হে মূসা! তোমাদের দু ’ জনের প্রতিপালক কে ? ’ তিনি জবাবে বলেন , ‘ আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে তার যোগ্য আকৃতি (যোগ্যতা অনুযায়ী) দিয়েছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। ’ 106
হযরত মূসা (আ.) একটি ক্ষুদ্র বাক্যের মাধ্যমে বলেছেন ,সকল কিছু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর মহান প্রজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্ট বস্তুসমূহের উপযুক্ততা অনুসারে তাদের দিয়েছেন ,কোন বস্তুই যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে কম পায় নি ,প্রত্যেক বস্তুই তার স্থানে সুন্দর ,কোন বস্তুই নিরঙ্কুশ মন্দ নয় যে ,বলা যাবে তিনি তা সৃষ্টি করেন নি ;বরং অন্য কেউ তা সৃষ্টি করেছে। এটিই নবিগণের যুক্তি।
সুতরাং বোঝা গেল আনগারা মাইনিওকে মন্দের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে অকল্যাণকর জগতের উপস্থিতির ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা (যদিও এ ক্ষেত্রে সে আহুরমাযদার সৃষ্ট হয়েছে বলা হয়) একত্ববাদের মৌলনীতি বিরোধী এবং নবিগণের নিশ্চিত যুক্তির বিরোধী।
তাই যারথুষ্ট্র ধর্ম অপূর্ণ একত্ববাদী ধর্ম বলে ক্রিস্টেন সেন যে দাবি করেছেন তা সঠিক নয় ;বরং যারদুশতের কথাকে অপূর্ণ দর্শন বলা যেতে পারে যা কোন অর্ধ দার্শনিকের কথার সদৃশ হলেও কোনক্রমেই একজন নবী বা পূর্ণ দার্শনিকের কথা হতে পারে না।
পি.জে. দুমানাশের বরাত দিয়ে ডক্টর মুহাম্মদ মুঈন বর্ণনা করেছেন ,
‘ কোরআনে অকল্যাণের উৎপত্তি ও মানুষের পাপের উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মাযদায়ী ধর্ম এ বিষয়ে সহজ ও মৌলিক উত্তর দান করেছে এভাবে ,অকল্যাণকে খোদার বিপরীতে অপর এক অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে যা খোদার মতই চিরন্তন। নিঃসন্দেহে মন্দ আত্মা শক্তি ও মর্যাদায় কখনই খোদার সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হবে। কিন্তু যেহেতু তার প্রচেষ্টা খোদার কর্মকাণ্ডের অন্তরায় সৃষ্টি করে তাই তিনি তার কর্মকে সীমিত করে দিয়েছেন। ভাল-মন্দের বিষয়ে মাযদায়ী ধর্ম যে উত্তর দান করে তা অন্তত বিশ্বে বিদ্যমান মন্দসমূহের দায়িত্ব হতে খোদাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ’ 107
বাহ! বাহ! কেমন সুন্দর এ যুক্তি! খোদা পি.জে. দুমানাশেহ এবং মাযদায়ী ধর্মের ছায়াকে নিজ ও ঊর্ধ্ব জগৎ হতে কম না করুন। কারণ তিনি (দুমানাশেহ) ও এ ধর্ম তাঁর মুখ রক্ষা করেছে।
মাযদায়ী ধর্ম যদি মূল হতে খোদাকে অস্বীকার করত তবে এই মন্দের দায়িত্ব হতে আরো উত্তমরূপে তিনি মুক্তি পেতেন। মাযদায়ী ধর্ম খোদার ভ্রূ সুন্দর করতে গিয়ে চোখই নষ্ট করে ফেলেছে। মন্দসমূহ যা একপ্রকার আপেক্ষিক বিষয় এবং গভীরতর ব্যাখ্যায় গেলে মূলত
অনস্তিত্বশীল ,তারা একে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন করতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টির অর্ধেককে তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় রত হয়েছে।
মাযদায়ী ধর্মে মন্দের অস্তিত্বহীনতা ,প্রকৃতি হতে তথাকথিত এ মন্দের অবিচ্ছিন্নতা ,এরূপ বস্তুসমূহের উপকারিতা ও এদের সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় নি বলেই তারা এ সমস্যা হতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে কুঠার হাতে মন্দের মূলোৎপাটনে উদ্যত হয়েছে।
আমরা এখানে ভাল-মন্দের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারছি না। কারণ আলোচনাটি অত্যন্ত গভীর ,দীর্ঘ ও আকর্ষণীয় এবং এটি এমন এক ঘূর্ণাবর্ত যাতে সহস্র তরণি নিমজ্জিত হয়েছে-তীরে ফিরে আসতে পারে নি। মাযদায়ী ধর্ম তাদেরই একটি।
শয়তান
একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করা প্রয়োজন মনে করছি আর তা হলো এই যে ,কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যারথুষ্ট্র ধর্মের আহ্রিমানের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের শয়তানের কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ আহ্রিমানকে আহুরমাযদার সৃষ্টি ধরে নিলেই সে আর শয়তান এক হয়ে যাবে এ দৃষ্টিতে যে ,শয়তানও আল্লাহর সৃষ্টি ও অকল্যাণের উৎস।
না ,এরূপ চিন্তা সঠিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শয়তান সৃষ্টিতে কোন ভূমিকাই রাখে না। ইসলামে কোন কিছুর সৃষ্টিকেই শয়তানের ওপর আরোপ করা হয় না। ইসলামে এমন কোন
চিন্তার অস্তিত্ব নেই যে ,বলা যাবে বিশ্ব জগতে অনাকাক্সিক্ষত বস্তুসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে যা না থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল ,কিন্তু যেহেতু আছে সেহেতু তা মন্দ কিছু হতে উৎসারিত হয়েছে। না ,এমনটি নয় ;বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সকল বস্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সবই সুন্দর-الذي أحسن كلّ شيء خلقه ‘ তিনি সকল বস্তুকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন ’ 108 এবংربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى ‘ আমাদের পালনকর্তা তিনি ,যিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার যোগ্যতানুসারে দিয়েছেন ,অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। ’ 109
ইসলামের দৃষ্টিতে শয়তানের কেবল নির্দেশসূচক ক্ষমতা (তাশরীয়ী) রয়েছে ,বাধ্যকরণের ক্ষমতা (তাকভীনী) নেই। অর্থাৎ শয়তান আদম সন্তানদের পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ও প্ররোচনা (ওয়াস্ওয়াসা) দিতে পারে। মন্দ কাজে আমন্ত্রণ জানান ব্যতীত মানুষের ওপর তার কোন শক্তি ও প্রভাবই নেই। কোরআনের বর্ণনা মতে কিয়ামতের দিন শয়তান নিজেই বলবে ,
و ما كان لي عليكم من سلطان إلّا أن دعوتكم فاستجبتم لي ‘ এবং তোমাদের ওপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না ,কিন্তু এতটুকু যে ,আমি তোমাদের আহ্বান জানিয়েছি। অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ (আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ)। ’ 110
শয়তানের স্বরূপ যা-ই হোক না কেন ,মানুষ হওয়ার অর্থ সে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ,স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। প্রথমত যখন তার নির্বাচনের ক্ষমতা রয়েছে তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভাবনা রয়েছে তার সম্মুখে দু ’ টি পথ আসার। এ দু ’ টি শর্ত ও পর্যায় যদি না থাকে তাহলে স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকে না এবং বাস্তবে মনুষ্যত্বই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ,
إنّا خلقنا الإنسان من نطفة إمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنّا هدينا السّبيل إمّا شاكرا و إمّا كفورا
“ আমি মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে ,তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হবে ,না হয় অকৃতজ্ঞ। ” 111
মানুষকে প্ররোচিত করা শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির কাজ। অন্যদিকে নির্বাচন ক্ষমতা মানুষের মনুষ্যত্বের অংশ। একদিকে যেমন ভালর দিকে আহ্বান ও ঐশী নির্দেশনা (ইলহাম) রয়েছে তেমনি অন্যদিকে মন্দের আহ্বান ও শয়তানী প্ররোচনাও রয়েছে যাতে করে মানুষ এ দু ’ য়ের মধ্য হতে একটিকে বেছে নিয়ে মনুষ্যত্বের পথে পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমনটি মাওলানা রুমী বলেছেন ,
“ বিশ্বে রয়েছে দু ’ দিক হতে বিপরীত আহ্বান
কোন্ আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাতে সে কান
এক আহ্বান সেই পরিশুদ্ধ আত্মাসমূহের
অন্য আহ্বান কলুষিত নিন্দিত অসুরের। ”
কোরআনে জিন বা শয়তান ,ফেরেশতাদের সমান্তরালের কোন অস্তিত্ব নয় ;বরং প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টির পাশাপাশি অবস্থানকারী এক অস্তিত্ব। কোরআনের দৃষ্টিতে ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী (فالمدبّرات أمرا ) । কিন্তু জিন ও শয়তান সৃষ্টি জগতে সৃষ্টির কোন বিষয়েই সংশ্লিষ্ট নয়।112 তাই এ ক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর অন্যান্য অস্তিত্বশীলদের ন্যায়। এখান হতে স্পষ্ট বোঝা যায় ,অকল্যাণকর বস্তুসমূহের অস্তিত্বের কারণে সৃষ্টি জগৎ অপূর্ণ-এরূপ ধারণার কোন অবকাশই কোরআনে নেই ।
এখানে প্রয়োজন মনে করছি একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার। আর তা হলো কেউ কেউ কোরআন বা হাদীসের অনুবাদ করতে গিয়ে শয়তানের ফার্সী অনুবাদ ‘ আহ্রিমান ’ বা ‘ দিভ ’ লিখে থাকেন যা সঠিক নয়। কারণ শয়তানের সমার্থক শব্দ ফার্সীতে নেই। তাই ফার্সীতে এটিই ব্যবহার করা উচিত অথবা আবরীতে শয়তানের অনুরূপ শব্দ ‘ ইবলিস ’ লেখা যেতে পারে। কোরআনের দৃষ্টিতে ‘ আহ্রিমান ’ বা ‘ দিভ ’ -এর প্রকৃত অর্থে কোন অস্তিত্ব নেই এবং কোরআনে উল্লিখিত শয়তান ভিন্ন এক অস্তিত্ব।
ইসলামী ফিকাহ্শাস্ত্রের দৃষ্টিতে যারথুষ্ট্র ধর্ম
এ আলোচনার উপসংহারে উল্লেখ্য ,যারথুষ্ট্র ধর্ম একত্ববাদী ছিল না দ্বিত্ববাদী উপরোক্ত অংশে আমরা বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সূত্রকে মানদণ্ড ধরলে প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের সঙ্গে একত্ববাদী ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণে যারথুষ্ট্র ধর্মকে একত্ববাদী ধর্ম বলা যায় না। এ সকল দলিল মতে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে যারথুষ্ট্রের তত্ত্ব ,এমনকি যদি আহ্রিমানকে আহুরামাযদার সৃষ্টিও ধরি তবুও তা একত্ববাদের সঙ্গে সংগতিশীল নয়।
কিন্তু আমরা মুসলমানগণ যারথুষ্ট্র ধর্মকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হতেও দেখতে পারি এবং ভিন্ন এক মানদণ্ডের আলোকে এ ধর্মকে বিচার করতে পারি। অর তা হলো ইসলামী ফিকাহ্ ,হাদীস গ্রন্থ ও ইসলামের নিজস্ব যে সকল মানদণ্ড রয়েছে। ঈমানদার মুসলমানদের নিকট এগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল ও ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য। এ দৃষ্টিকোণ হতে যারথুষ্ট্র ধর্মকে একত্ববাদী একটি ধর্ম বলে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে এ ধর্ম মূলে একত্ববাদী থাকলেও পরবর্তিতে দ্বিত্ববাদ ,অগ্নি উপাসনা ও অন্যান্য শিরকমিশ্রিত বিষয়সমূহ এতে সংযুক্ত হয়েছে । যদি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে কোন ধর্মের মূল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তদুপরি ফিকাহ্শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হতেও তা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। বিশেষত যারথুষ্ট্র ধর্মের মূল দ্বিত্ববাদী হওয়ার বিষয়টি যখন অনিশ্চিত তখন যদি ফিকাহর মানদণ্ডে তা তাওহীদী বলে প্রমাণিত হয় তাহলে যারথুষ্ট্রগণও আহলে কিতাব হিসেবে পরিগণিত হবে। অতীত সময়ে মুসলমানগণ তাদের আহলে কিতাব হিসেবে এ মানদণ্ডেই গ্রহণ করতেন যদিও ফকীহ্গণের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা ছিল। ইরানী বংশোদ্ভূত ফকীহ্গণের মধ্যেও তাদের আহলে কিতাব না হওয়ার মত অন্যদের হতে কম নয়।
এ বিষয়ে ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রগত আলোচনা এ গ্রন্থের বিষয় বহির্ভূত। তবে এ গ্রন্থের ‘ পারিবারিক ব্যবস্থা ’ র আলোচনায় মাহ্রামগণের সঙ্গে বিবাহের বিষয়ে এতদ্সংক্রান্ত কিছু কথা বলব।
যারদুশতের পর দ্বিত্ববাদ
স্বয়ং যারদুশত ও মাযদায়ী যারথুষ্ট্র ধর্মের মূল একত্ববাদী ছিল না দ্বিত্ববাদী এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও পরবর্তী সময়ে বিশেষত সাসানী আমল অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের সময়ের যারথুষ্ট্র ধর্মের দ্বিত্ববাদী হওয়ার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে সকল ব্যক্তি যারদুশতকে একত্ববাদী বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা আফসোস করে বলেন ,যারদুশতের একত্ববাদ দ্বিত্ববাদের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। জন নাস যিনি মোটামুটিভাবে যারদুশতকে একত্ববাদী বলে মনে করেন তিনি বলেছেন , “ ত্রুটি ও ধ্বংসের স্বতন্ত্র কারণ এবং অকল্যাণের ভিন্ন উৎসের প্রতি বিশ্বাস যারথুষ্ট্র ধর্মকে যুগের পরিক্রমায় নৈতিকভাবে এক দ্বিত্ববাদী ধর্মে পরিণত করে।... সময়ের পরিবর্তনে শয়তানী শক্তি ‘ আনগারা মাইনিও ’ শক্তি সঞ্চয় করে আহুরামাযদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ও তারা পরস্পর যেন সম দু ’ শক্তি হিসেবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আভেস্তার নতুন সংকলনে (সাসানী আভেস্তা) আনগারা মাইনিও আহুরমাযদার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় যেন আবির্ভূত হয়েছে। ” 113
যাঁরা যারথুষ্ট্রকে দ্বিত্ববাদী মনে করেন তাঁদের মতে যারদুশতের আবির্ভাবের পরেই দ্বিত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন পি.জে. দুমানাশেহ বলেছেন ,
“ গাতাসমূহের দ্বিত্ববাদী ধারণা যারদুশতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়তর হয়েছিল। কারণ তিনি সমগ্র অস্তিত্ব জগৎকে ভাল ও মন্দ এ দু ’ ভাগে ভাগ করেন...। ” 114
বর্তমানে প্রচলিত আভেস্তার একাংশ যা ভানদিদাদ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে আনগারা মাইনিওকে বিশ্বের মন্দসমূহের ,যেমন বরফজমা শীত ,চরম উষ্ণ গ্রীষ্মকাল ,সর্প ও অন্যান্য বিষধর সরীসৃপ প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা বলে উল্লেখ করেছে।
ইসলামের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়েও যারথুষ্ট্রগণ স্বাধীনভাবে তাদের দ্বিত্ববাদী বিশ্বাস প্রকাশ করত ও পক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করত। তারা প্রায়ই নবী (সা.)-এর আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ ,অন্যান্য আলেম ও কালামশাস্ত্রবিদদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতো। শিয়া হাদীসগ্রন্থসমূহ ,যেমন শেখ সাদুকের তাওহীদ ,আল্লামা তাবারসীর ‘ ইহতিজাজ ’ , ‘ উয়ুনু আখবারুর রিদ্বা ’ ,আল্লামা মাজলিসীর ‘ বিহারুল আনওয়ার ’ প্রভৃতি গ্রন্থে এ সকল বিতর্কের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। সাসানী শাসনামলের যারথুষ্ট্রগণ যে দ্বিত্ববাদী ছিলেন এটি তার প্রমাণ। এই বিশ্বাস তারা ইসলামী শাসনামলেও সংরক্ষণ করেছে ও এর সপক্ষে বিতর্কে অংশ নিয়েছে ।
ইসলামী শাসনামলে (3য় হিজরী শতাব্দী) রচিত যারথুষ্ট্রগণের প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হলো ‘ দিনকারত ’ । জানা যায় এ গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে ইহুদী ,খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিপরীতে দ্বিত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
ক্রিস্টেন সেন বিশ্বাস করেন ,সাসানী শাসনামলে যারওয়ানী ধারণা-প্রাচীনতম যে খোদা হতে আহুরামাযদার জন্ম হয়েছে (এ সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি)-যারথুষ্ট্রদের মধ্যে প্রচলন লাভ করে। যারওয়ানী ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ,জটিল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি বিশ্বাস। ক্রিস্টেন সেনের মতে ইসলামের আবির্ভাবের পর যারথুষ্ট্রগণ যারওয়ানী বিশ্বাস ত্যাগ করে ও আত্মপক্ষ সমর্থনযোগ্য কিছুটা যুক্তিসঙ্গত দ্বিত্ববাদের পক্ষাবলম্বন করে। তিনি বলেন ,
“ যারথুষ্ট্র ধর্ম সাসানী শাসনামলে রাষ্টধর্ম হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ধর্মটি তখন এমন কিছু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে ,সাসানী আমলের শেষ দিকে তা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল ও অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল। ইসলাম যখন যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের মদদপুষ্ট সাসানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় তখন যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকগণ উপলব্ধি করলেন এ ধর্মকে ধ্বংস ও পতন হতে রক্ষা করতে হলে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। তাই যারওয়ানী ধারণাসহ অন্যান্য শিশুসুলভ কাল্পনিক বিশ্বাসসমূহকে বাদ দিয়ে মাযদায়ী ধর্মকে যারওয়ানী উপাসনা মুক্ত করলেন। ফলে বিশ্ব সৃষ্টির কাহিনী পরিবর্তিত হয়ে গেল। সূর্য উপাসনা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হলো। এতে আহুরামাযদার উপাসনা কিছুটা একত্ববাদী রূপ নিল। মিত্রের (সূর্য) মর্যাদা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ‘ ইয়াশত ’ -এর অনুরূপ অবস্থায় নেয়া হলো। ধর্মীয় অসংখ্য বিবরণ হয় পরিবর্তিত করা হলো নতুবা পুরোটাই বাদ দেয়া হলো। সাসানী আভেস্তা ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থের যে অংশ যারওয়ানী ধারণামিশ্রিত ছিল তা গ্রন্থাগারের তাকেই পরিত্যাগ অথবা ধ্বংস করা হলো। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত যে অংশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে ‘ দিন কারত ’ -এ এসেছে তার ওপর এতটা বিশ্লেষণ হয়েছে যে ,তা কয়েক লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এ অংশ হতে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। এই পরিবর্তনসমূহ যারথুষ্ট্র ধর্মের অন্ধকার যুগে (সাসানী সাম্রাজ্যের পতন) সাধিত হয়। ফার্র্সী ভাষার কোন গ্রন্থেই এই সংস্কারের বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি । এই সংস্কারকৃত যারথুষ্ট্র ধর্ম তার প্রাচীন রূপ যেন দ্বিতীয়বার ফিরে পেয়েছে। ” 115
আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করব ,যারথুষ্ট্র ধর্ম ও এর অনুসারীদের প্রতি ইসলামের এ সেবা ইসলামের অন্যান্য অবদান হতে কোনক্রমেই কম নয়। ইসলাম যারথুষ্ট্র ধর্মে পরোক্ষ যে সংস্কার ঘটিয়েছে ইরানের প্রাচীন ধর্মে যারদুশতের সংস্কার হতে তার প্রভাব অবশ্যই অধিক ছিল।
মনী (মনাভী) ধর্মে দ্বিত্ববাদ
এতক্ষণ যারথুষ্ট্র ধর্মে দ্বিত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা হলো। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ,তৎকালীন সময়ে প্রচলিত অন্য দু ’ টি ধর্মও দ্বিত্ববাদনির্ভর ছিল। এ দু ’ টি ধর্ম হলো মনী ও মাযদাকী। মনী ধর্মের দ্বিত্ববাদ যারথুষ্ট্র ধর্মের দ্বিত্ববাদ হতে অধিকতর স্পষ্ট। মাযদাকী দ্বিত্ববাদ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মনী ধর্মের দ্বিত্ববাদের অনুরূপ। শাহরেস্তানী তাঁর ‘ মিলাল ওয়া নিহাল ’ গ্রন্থে যারদুশতকে দ্বিত্ববাদী না বলে মনীকে দ্বিত্ববাদী বলেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ ও প্রাচ্যবিদগণ মনী ও তাঁর ধর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তাকী যাদেহ তাঁদের প্রথম সারির একজন। তাঁর বক্তব্য হতে কিছু অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি :
“ ... মনী ধর্ম ভাল-মন্দ বা আলো-অন্ধকার এবং তিন পর্যায়ের (অতীত ,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) মৌল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সকল অস্তিত্বের মূল হলেন দু ’ জন খোদা। একজন আলো ,অন্যজন অন্ধকার। ফার্সী গ্রন্থসমূহে তাদের ‘ দুবোন ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এ দু ’ জন পরস্পর স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁরা দু ’ জন মনুয়ীদের ভাষায় ‘ অতীত ’ নামে অভিহিত। আলোর জগৎ ওপর হতে পূর্ব ,পশ্চিম ও উত্তরে প্রসারিত ছিল এবং অন্ধকারের জগৎ নীচ হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত ছিল। একই স্থানে সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে ব্যবধান ছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে যেহেতু দক্ষিণ অংশের এক-তৃতীয়াংশও আলোর অধিকারে ছিল সেহেতু আলোর জগৎ অন্ধকার হতে পাঁচ গুণ বেশি ছিল। এ দু ’ মৌল শক্তি নিজ অধিকৃত অংশে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। আলোর জগতে সকল সৎ গুণাবলী ,যেমন শৃঙ্খলা ,শান্তিপ্রিয়তা ,সাফল্য ,সৌভাগ্য ,বুদ্ধিমত্তা ,সমঝোতা প্রভৃতির আধিপত্য ছিল। কিন্তু অন্ধকারের জগৎ বিশৃঙ্খলা ,বিদ্রোহ ,আবর্জনা প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। মনিগণ এ দু ’ মৌল সত্তাকে কখনও কখনও দুই বৃক্ষ বলে অভিহিত করেছে। যার একটি হলো জীবন বৃক্ষ ও অন্যটি হলো মরণ বৃক্ষ। আলোর জগতে শ্রেষ্ঠত্বের সম্রাটের (পিতার) শাসন আর অন্ধকার জগতে মন্দ ও অন্ধকারের সম্রাটের শাসন। আলোর জগতের পাঁচ দিকে খোদার পাঁচ সদস্য যথাক্রমে বুদ্ধি ,চিন্তা ,বিশ্লেষণ ,ইচ্ছা ও খোদার প্রকাশস্বরূপ অসংখ্য চিরন্তন সৃষ্টিসমূহ বসবাস করে। অন্যদিকে অন্ধকারের জগতেও পাঁচ স্তর ওপর হতে নীচে যথাক্রমে ধোঁয়া ,আগুন ,ধ্বংসকারী বাতাস ,কর্দমাক্ত নোংরা পানি ও অন্ধকার। ” 116
আমাদের দাবির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপরোল্লিখিত অংশটুকুই যথেষ্ট। আগ্রহীরা এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন।
মাযদাকী ধর্মে দ্বিত্ববাদ
মাযদাকী ধর্ম মনী ধর্মেরই বিচ্ছিন্ন একটি অংশ। তাই মনী ধর্মের কুসংস্কারসমূহ সামান্য কিছু তফাৎ ছাড়া পুরোটাই মাযদাকী ধর্মে স্থানান্তরিত হয়েছে। ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ বুনদেস (যারদুশতে ফাসায়ী) ও মাযদাকের মিলিত এ ধর্ম মূলত মনী ধর্মেরই একটি সংস্কৃারকৃত রূপ। মনী ধর্মের ন্যায় এ ধর্মটিও তার আলোচনা প্রাচীন দুই মৌল অস্তিত্ব আলো ও অন্ধকার দিয়ে শুরু করেছে। মনী ধর্মের সঙ্গে মাযদাকীদের এ ক্ষেত্রে পার্থক্য এতটুকু যে ,মাযদাকী মতে অন্ধকারের আন্দোলন ইচ্ছা ও পূর্বজ্ঞান নির্ভর ছিল না ;বরং আকস্মিকভাবে পূর্ণজ্ঞানহীনভাবে ঘটেছিল। এর বিপরীতে আলোকের আন্দোলন ইচ্ছা ও জ্ঞাননির্ভর ছিল। সুতরাং এ আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের মাধ্যমে বস্তুজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে মনী ধর্মে যে পূর্ব পরিকল্পনার কথা রয়েছে তা মাযদাকীরা গ্রহণ করে নি ;বরং একে পরিকল্পনাহীন আকস্মিক ঘটনা বলে জানে। ফলে মাযদাকী ধর্মে আলোর শ্রেষ্ঠত্ব মনী ধর্ম হতে অধিকতর লক্ষণীয়।... ” 117
অগ্নি উপাসনা
ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন যারথুষ্ট্র ধর্মের চিন্তা ,বিশ্বাস ও ব্যবহারিক অবস্থার অন্যতম লক্ষণীয় দিক ছিল অগ্নিকে পবিত্র ও সম্মানিত মনে করে এর উপাসনা।
এ কর্ম প্রাচীন সময় হতেই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং এখনও এর প্রচলন রয়েছে। যেমন বু আলী সিনা তাঁর শিফা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম প্রবন্ধে প্রকৃতি ও বস্তু সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন :
“ প্রাচীন সময়ে (পূর্ববর্তীদের) কেউ কেউ বৈপরীত্যের দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত সকল কিছুই দু ’ বিপরীত বস্তুর মিলনে অস্তিত্ব লাভ করে। এ কারণে ভাল-মন্দ ,আলো-অন্ধকারকেও বিপরীতমুখী দু ’ টি শক্তি হিসেবে ভিন্নরূপ মূল্যায়ন করত। আগুনকে সম্মান প্রদর্শনের পথে বাড়াবাড়ি করে একে মহাপবিত্র ও উপাসনার উপযোগী বলে তারা মনে করত। কারণ আগুন আলোর উৎপত্তির উপাদান হিসেবে পরিচিত ছিল। এর বিপরীতে মাটি ও পৃথিবী অন্ধকারের উপাদান হিসেবে ঘৃণ্য ও অসম্মানিত ছিল। ”
যদি ইবনে সিনার কথাকে গ্রহণ করি তবে অস্তিত্বের দ্বৈততা ও ভাল-মন্দ এবং আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্যের দর্শনের কারণেই অগ্নি উপাসনার চিন্তার উদ্ভব হয়েছে বলতে হবে। আর যদি আধুনিক বিশেষজ্ঞদের ধারণাকে গ্রহণ করি তবে বলতে হবে ,প্রকৃতির উপাসনার যুগ হতেই অগ্নি উপাসনা ছিল এবং তার কল্যাণকর উপাদানসমূহ হতে অধিকতর কল্যাণ পাবার লক্ষ্যে এবং অকল্যাণকর উপাদানসমূহের ক্ষতি হতে নিজেদের রক্ষার জন্যই তাদের উপাসনা করত। অর্থাৎ বস্তুসমূহ ভাল-মন্দ বা আলো-অন্ধকারের মিশ্রণ হতে সৃষ্টি কিনা তা জানার পূর্ব হতেই তারা অগ্নি উপাসক ছিল। সময়ের এই পর্যায়ে তারা শুধু বস্তুসমূহকে ভাল ও মন্দ এ দু ’ ভাগে ভাগ করত। সেই সাথে এ দু ’ ধরনের অস্তিত্বের পেছনে ভিন্ন দুই খোদার হাত রয়েছে বলে মনে করত। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুতেই দু ’ টি উপাদান রয়েছে এবং যৌগ হিসেবে তারা দুই বিপরীত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এরূপ ধারণা পরবর্তী সময়ে মানুষের চিন্তার বিকাশের পর্যায়ে জন্ম লাভ করেছে। তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার ,অগ্নির পবিত্রতা ও মর্যাদার বিশ্বাস আর্যদের মধ্যে প্রাচীনকাল হতেই ছিল এবং অন্য সকল উপাদান হতে আগুনের প্রতি আকর্ষণ অধিক ছিল।
ডক্টর মুঈন বলেছেন ,
“ সাতশ হতে এগারশ ’ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে লিখিত আভেস্তা বিশেষত গাতাসমূহের কথা বাদ দিলে ইরানের প্রাচীন নিদর্শনসমূহের অন্যতম যে নিদর্শনটি এখনও বিদ্যমান তা হলো
বেহেস্তানের (বিস্তুনের) দক্ষিণের আসহাক আভেন্দের নকশা যা খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে (মেডিয়ানদের সময়ে) খোদিত হয়েছিল। একই নকশাটি ‘ দুককানে দাউদ ’ নামে পরিচিত এবং পাহাড়ের গায়ে খোদিত করে একে রূপ দেয়া হয়েছে। নকশাটি হলো একজন ইরানী আগুনের সামনে উপাসনার ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গিরিশম্যান বলেছেন: আমরা হাখামানেশী আমলের তিনটি উপাসনালয়ের কথা জানি। সেগুলো হলো কুরেশের (সাইরাসের) নির্দেশে নির্মিত পাসারগাদের উপাসনালয় ,দ্বিতীয়টি তাঁরই নির্দেশে নির্মিত দারভীশের রণাঙ্গনের সমাধির ‘ নাকশে রুস্তম ’ -এর উপাসনালয় এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয় আরদ্শিরের সময়ে নির্মিত ‘ শুশ ’ -এর উপাসনালয়। ” 118
এখন প্রশ্ন হলো অগ্নি উপাসনার বিষয়ে যারদুশতের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ? তিনি কি এ মর্মে নিষেধ করেছেন ? যদি নিষেধ করে থাকেন তবে কি তাঁর পরে এটি পুনরায় শুরু হয়েছিল ও যারথুষ্ট্র ধর্মের অন্যতম আচারে বা স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল নাকি তিনি আগুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রচলিত রীতিকেই সমর্থন করেছিলেন ? যদি যারথুষ্ট্রদের বর্ণনাসমূহ বিশেষত প্রচলিত আভেস্তাকে মানদণ্ড ধরি তবে বলতে হবে তিনি এ কর্মের সঙ্গে একমত ছিলেন।
ডক্টর মুঈন বলেছেন ,
“ অযার (অগ্নি) মাযদা ইয়াসনার (খোদার) একজন ফেরেশতার নাম। আভেস্তায় সাধারণত তাঁকে আহুরামাযদার পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে ।119 এ নামে অভিহিত করার মাধ্যমে তাঁর উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা পৃথিবীর সংরক্ষক ফেরেশতা ‘ ইসপানদারামেয ’ কে আহুরামাযদার কন্যা বলে থাকে।120 আভেস্তার 25 নং ইয়াসনার 7 নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে ,আহুরমাযদার পুত্র অযারের গুণকীর্তন করি। হে পবিত্র অগ্নি! খোদার (আহুরামাযদা) পুত্র ও সত্যের নেতা! আমরা আপনার প্রশংসা করি। আমরা সকল প্রকার অগ্নির উপাসনা করি। যামইয়াদ ইয়াশতের 46-50 নম্বর ধারায় অযার ফেরেশতাকে অযীদাহাকের (অযীযাহাক) প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সেপান্ত মাইনিওয়ের পক্ষ হতে নিযুক্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি অযীদাহাকের ক্ষমতা লাভের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছেন। ” 121
আগুনকে পবিত্র ও সম্মানিত মনে করে উপাসনার বিরুদ্ধে যারদুশতের কোন ভূমিকাই ইতিাহাসে পাওয়া যায় না। আভেস্তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশ গাতাসমূহ যা স্বয়ং যারদুশতের বলে প্রসিদ্ধ তাতে তাঁর অগ্নির আরাধনার কথা রয়েছে। যদিও কেউ কেউ উপরোল্লিখিত ইয়াসনা ও ইয়াশতের ধারার বিষয়বস্তুর বিপরীত কথা বলেছেন। যেমন জন নাস বলেছেন ,
“ যারথুষ্ট্র ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিধানসমূহের কিছুই বর্তমানে নেই। শুধু এতটুকু জানা যায় ,প্রাচীন আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা ,যাদু-মন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে যে সকল আচার-অনুষ্ঠানাদি ছিল যারদুশত তা পুরোপুরি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। যারদুশতের সময় হতে প্রচলিত শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা এ উপলক্ষে যে ,যারদুশত এক উপাসনা অনুষ্ঠানে পবিত্র অগ্নি বেদীর পাশে উপাসনারত অবস্থায় নিহত হন। গাতাসমূহে বর্ণিত এক সংগীতে উল্লিখিত হয়েছে যে ,যারদুশত বলেছেন: যখন পবিত্র অগ্নির প্রতি কিছু নিবেদন করি তখন সৎ কর্ম করেছি বলে অনুভব করি। অন্য স্থানে তিনি পবিত্র অগ্নিকে আহুরামাযদার পক্ষ হতে মানুষের জন্য উপহৃত এক ফেরেশতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের জানতে হবে ,যারদুশত স্বয়ং অগ্নির উপাসনা করতেন না এবং তাঁর পূর্ববর্তী বংশধরগণ অগ্নির প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত তিনি তা করতেন না। অগ্নির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ,তাঁর পরবর্তীতে অগ্নি উপাসকগণের বিশ্বাস হতে ভিন্ন ছিল। তিনি অগ্নিকে আহুরমাযদার পক্ষ হতে উপহৃত মূল্যবান এক চিহ্ন ও পবিত্র রহস্য বলে মনে করতেন যার মাধ্যমে মহা জ্ঞানী খোদার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ” 122
যারদুশত অগ্নি উপাসনা করুন বা না-ই করুন বা করলেও তা যেভাবেই করুন না কেনো এ কথা সত্য যে ,তাঁর পরবর্তীতে অগ্নির প্রতি বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন ও উপাসনা তুঙ্গে উঠেছিল এবং যারথুষ্ট্রগণের অন্যতম প্রধান চিহ্ন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং এখনও তা রয়েছে। মুসলমান ও খ্রিষ্টানগণ যেরূপ মসজিদ ও গীর্জা তৈরি করে তেমনি যারথুষ্ট্রগণও বিপুল সংখ্যক অগ্নিমন্দির নির্মাণ করে।
সাসানী শাসনামলে যারথুষ্ট্রগণ অগ্নি উপাসক নামেই পরিচিত ছিল। সাসানী আমলের শেষ দিকে যখন খ্রিষ্টানগণ ইরানে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভ করেছিল ,এমনকি সাসানী রাজ দরবারেও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল তখন প্রায়ই তারা যারথুষ্ট্রগণের সঙ্গে অগ্নি উপাসনা নিয়ে বিতর্ক করত। ক্রিস্টেন সেন আর্মেনিয়ায় খ্র্রিষ্টধর্মের প্রসারের কারণে ইরান সম্রাটের অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া এবং যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে যারথুষ্ট্র ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দান করে পত্র প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন ,তারা এর জবাবে ধৃষ্টতার সাথে লিখে , “ আমাদের ধর্মের মৌল নীতি সম্পর্কে এটি বলতে চাই যে ,আমরা তোমাদের মত সূর্য ,চন্দ্র ,অগ্নি ও বায়ুর মত উপাদানের উপাসনা করি না...। ” 123
তিনি তাঁর গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে লিখেছেন ,
“ ...যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকগণ প্রতিদিনই পিছু হটছিলেন। পূর্বের ন্যায় তাঁদের প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না। ফলে বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন না। ধর্মীয় নিপীড়ন বেশ কমে এসেছিল। নতুন চিন্তার প্রসারের ফলে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সন্দেহ বাসা বাঁধতে লাগল। মাযদা ইয়াসনা ধর্মের প্রাচীনকালের যে কল্পকাহিনীসমূহ প্রবেশ করেছিল তা স্বয়ং এর ধর্মযাজকদের উদ্বিগ্ন ও সন্দেহপরায়ণ করে তুলেছিল। তাই তাঁরা এরূপ বিষয়সমূহের সপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টায় রত হলেন। যারথুষ্ট্র ধর্মের একজন পুরোহিত খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গিওরগিসের সঙ্গে আলোচনায় বলেন: আমরা কখনই অগ্নিকে খোদা মনে করি না ;বরং অগ্নির মাধ্যমে খোদারই উপাসনা করি যেমন তোমরা ক্রসের মাধ্যমে তাঁর উপাসনা কর। গিওরগিস একজন ধর্মান্তরিত ইরানী খ্রিষ্টান ছিলেন। তাই তিনি এর জবাবে আভেস্তা হতে কিছু অংশ পাঠ করেন যেখানে খোদার ন্যায় অগ্নির প্রতি সাহায্য চেয়ে দোয়া করা হয়েছে। পুরোহিত পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে জবাব দেন: আমরা এজন্য অগ্নি উপাসনা করি যে ,অগ্নি ও আহুরামাযদা একই প্রকৃতির। গিওরগিস প্রশ্ন করলেন: যা কিছু অগ্নিতে আছে তার সবই কি আহুরামাযদার মধ্যেও রয়েছে ? পুরোহিত বললেন: হ্যাঁ। গিওরগিস বললেন: অগ্নি ঘোড়ার মলসহ সকল অপবিত্র বস্তুকে পুড়িয়ে ফেলে। যদি আহুরামাযদাও একই প্রকৃতির হয়ে থাকেন তবে তিনিও এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেন। তাই নয় কি ? এ কথায় পুরোহিত নির্বাক হয়ে গেলেন। ” 124
যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ ইসলামী শাসনামলে যখন মুসলিম মনীষীদের মুখোমুখি নিজ ধর্মের প্রতিরক্ষায় দাঁড়ালেন তখন ‘ অগ্নি ও আহুরামাযদা একই প্রকৃতির বলে আমরা অগ্নি উপাসনা করি ’ এ কথা আর বললেন না ;বরং অগ্নি উপাসনাকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে বললেন , “ আমরা আহুরামাযদাকেই উপাসনা করি ,কিন্তু অগ্নিকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করি ,যেমন মুসলমানগণ কাবার উপাসনা করে না ,কিন্তু আল্লাহর উপাসনার লক্ষ্যে কাবার দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে ” ।
যারথুষ্ট্রগণ একদিকে পূর্ববর্তীদের অনুসরণে যেখানেই অগ্নির পবিত্রতার কথা আসত সেখানেই তার উপাসনার কথা বলত। অন্যদিকে মুসলমানদের আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য উপাসনার স্থলে কিবলার ধারণা উপস্থাপন করত। বিশিষ্ট যারথুষ্ট্র কবি দাকীকী ,যিনি ফেরদৌসীর অগ্রণী এ অর্থে যে ,তিনিই সর্বপ্রথম শাহনামা রচনার কাজে হাত দেন এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেই ফেরদৌসী এর পূর্ণতা দান করেন-যিনি যারথুষ্ট্র রীতি অনুযায়ী তাঁর কবিতায় অগ্নির উপাসনার কথা বলেছেন। তিনি যারদুশতের প্রতি ফেরেশতার অগ্নি সম্পর্কিত বাণীর উল্লেখ করে বলেছেন :
“ আমার পক্ষ হতে রাজা গুশতাসবের নিকট নিয়ে যাও বাণী
বল তাকে হে রাজাধিরাজ! হে মহান ও জ্ঞানী!
অর্পিত হয়েছে তোমার হস্তে অগ্নিকুণ্ডকে
যেন সকল দেশের অগ্নির হও তুমি রক্ষক।
এ অগ্নিকে হতে দিও না কখনও নির্বাপিত ,
কর না তাকে স্বচ্ছ সলিল বা মৃত্তিকা দ্বারা হত।
পুরোহিতগণের হও সহযাত্রী ও অনুসারী ,
মন্দগণ কর অন্তরকে পুতঃপবিত্র জন্য তারই।
এ ব্রত নিয়েই কর সাধনা ,
সকলে অগ্নির কর উপাসনা। ”
কবি ফেরদৌসীও যারথুষ্ট্র নীতির অনুসরণে অনেক স্থানেই ‘ উপাসনা ’ শব্দটি এনেছেন। ফেরদৌসী তাঁর ‘ আগুন অবিষ্কার ’ নামক প্রসিদ্ধ কল্পকাহিনীতে বলেছেন , ‘ হুশাঙ একটি বড় সাপ দেখে হত্যার নিমিত্তে এক বৃহৎ পাথর তার প্রতি ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তা সাপকে আঘাত না করে অপর এক শিলায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয় এবং এরূপেই অগ্নি আবিষ্কৃত হয়। ’
অতঃপর কবিতা আকারে বলেছেন :
“ দু ’ শিলাখণ্ড হতে দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল
শিলাভ্যন্তর যেন অগ্নি রং ধারণ করল।
সাপ না মরে এক রহস্য উদ্ঘাটিত হলো ,
ঐ শিলাদ্বয় হতেই অগ্নির সৃষ্টি হলো।
যদি লোহা দিয়ে আঘাত করে কেউ পাথরের ওপর
উৎপত্তি হয় তা হতে প্রজ্বলিত শিখার।
বিশ্বপ্রভু জানালেন তাকে নব সৃষ্টির অভিনন্দন
প্রশংসিত হলো সে ,পেল শুভ সম্ভাষণ।
অগ্নিদেব তাকে দিল এক মহান উপহার।
অগ্নি ঘোষিত হলো কিবলা সবার
অগ্নিদেব বলল তাকে এ মহাবীর
যদি হও বুদ্ধিমান কর উপাসনা অগ্নির। ”
ফেরদৌসী ইসলামের আবির্ভাবের পর অগ্নির মর্যাদা ও পবিত্রতার বিশ্বাসের প্রতি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন ,তারা অগ্নিকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে যদিও তাঁর কবিতায় অগ্নির উপাসনার বিষয়টিও উল্লিখিত আছে।
ফেরদৌসী তাঁর কোন কবিতায় তাদের পক্ষাবলম্বন করে বলেছেন ,অগ্নিবেদী যারথুষ্ট্রগণের মেহরাব এবং অগ্নি হলো কেবলা। তিনি কেউকাউস ও কেইখসরুর অযার গুশাস্ব-এর মন্দিরে গমন সম্পর্কে বলেছেন :
“ সাত দিনব্যাপী অগ্নিদেবের নিকট পেয়েছিল তারা ছন্দ
ভেব না এই অগ্নি উপাসকগণ বড় মন্দ
কারণ অগ্নি তাদের নিকট মেহরাবের ন্যায়
উপাসনার সময় তাদের চক্ষুও সিক্ত হয়। ”
অন্যত্র বলেছেন :
“ সেখানে রাখা সুন্দর রঙের অগ্নিকে চেন ?
আরবদের পাথরে সাজান মেহরাব যেন। ”
ইবাদতের মেহরাব নাকি উপাস্য
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দ্বিত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছি ,এটি বিশ্ব জগতের সৃষ্টিপদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একত্ববাদী চিন্তার পরিপন্থী মতবাদ (সত্তাগত ও কর্মগত উভয় ধরনের একত্ববাদবিরোধী একটি মতবাদ)।
অগ্নিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা ও এর উপাসনা করার সঙ্গে বিশ্ব সৃষ্টির ধারণার কোন সম্পর্ক নেই এবং এটি সত্তাগত ও কর্মগত একত্ববাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি বিষয়। বিষয়টি উপাসনাগত একত্ববাদের দৃষ্টিতে যারথুষ্ট্রগণ কি ছিলেন অথবা বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত তাদের ধারণা দ্বিত্ববাদী ছিল কিনা এ সবের আলোচনা এখানে করা আমাদের কাম্য নয় ;বরং এখানে আমরা দেখব উপাসনার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা কি ছিল। অর্থাৎ যদি ধরেও নিই ,বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সত্তাগত ও কর্মগত একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তদুপরি আমাদের জানতে হবে যে ,বিশ্ব স্রষ্টার উপাসনার ক্ষেত্রে তারা একত্ববাদী ছিল না অংশীবাদী ? উপাসনাগতভাবে একত্ববাদী হওয়া সত্তা ও কর্মগতভাবে একত্ববাদী হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নয়। ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে আরবগণ এ দৃষ্টিতে একত্ববাদী ছিল। যেমন কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে :
و لئن سئلتهم من خلق السّماوات و الأرض ليقولنّ الله ‘ যদি তাদের প্রশ্ন কর ,আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা কে ? তারা বলবে ‘ আল্লাহ্ ’ । ’ 125 জাহেলী যুগের আবরগণও মূর্তিসমূহকে বিশ্বের স্রষ্টা বলত না ,কিন্তু এগুলোর উপাসনা করত। সাধারণত সকল মূর্তিপূজকই এরূপ ধারণা পোষণ করে। তাই যদি যারথুষ্ট্র ধর্মকে সত্তাগত ও কর্মগতভাবে একত্ববাদী বলে ধরেও নিই তবু তা উপাসনার ক্ষেত্রে একত্ববাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
যারথুষ্ট্রগণ প্রাচীনকাল হতেই অগ্নিমন্দিরে ও অগ্নিশিখার সামনে উপাসনা করে এসেছে। এ কর্মের উদ্দেশ্য কি ? তারা কি অগ্নির সামনে আহুরমাযদাকেই উপাসনা করত নাকি অগ্নিকেই ? যেমনটি জাহেলী যুগের আরবগণ মূর্তিসমূহকে তাদের মধ্যস্থতাকারী126 বলত আবার স্বীকার করতما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى زلفى ‘ আমরা তাদের উপাসনা করি না এ উদ্দেশ্য ব্যতীত যে ,তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে। ’
ডক্টর মুঈন বলেছেন ,
“ ...অগ্নির প্রতি বিশেষ দৃষ্টির কারণেই ইরানী মুসলমানগণ যারথুষ্ট্রদের অগ্নি উপাসক বলে অভিহিত করত। কিন্তু বাস্তবে তাদের নিকট অগ্নি স্বতন্ত্র কোন খোদা ছিল না (যেমনটি যারদুশতের পূর্বে প্রাচীন আর্যদের ধারণায় ছিল) ;বরং মুসলমানরা যেমন কাবার প্রশংসা করে তেমনি মাযদা ইয়াসনা ধর্মাবলম্বীরাও অগ্নির প্রশংসা করে ও এর পবিত্রতায় বিশ্বাস করে। ”
তিনি আরো বলেছেন , “ প্রকৃতির সকল সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মধ্যে অগ্নি সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান। মানুষসহ সকল প্রাণীর অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ও প্রাণ প্রবৃত্তির মূল হলো অগ্নি। এ অগ্নিই তার অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের উৎস। উদ্ভিদ ও পাথরের মধ্যেও এক ধরনের অগ্নিপ্রভাব রয়েছে। ”
মাওলানা রুমী তাঁর এক গজলে বলেছেন ,
‘ বাঁশীতে প্রেমের অগ্নিই যেন বাজে
ভালবাসার উদ্যমেই সে সুর খুঁজে।
বাঁশীর সুরে নেই লালসা ,অগ্নি রয়েছে।
যার মাঝে নেই অগ্নি ,সেই ধ্বংস হয়েছে। ’
ডক্টর মুঈন তাঁর বক্তব্যে যে ভুল করেছেন সে ভুলের প্রতি আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি। তিনি উপাসনার ক্ষেত্রে অংশীবাদকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে অংশীবাদ বলে ভুল করেছেন। তিনি ভেবেছেন উপাসনার ক্ষেত্রে র্শিক করার অর্থ যার উপাসনা করা হবে তিনি সৃষ্টি জগতে সৃষ্টিমূলক কোন কর্মকাণ্ড করেছে এরূপ বিশ্বাস রাখা এবং যেহেতু যারথুষ্ট্রগণ অগ্নির ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস রাখে না সেহেতু তারা মুশরিক বা অংশীবাদী বলে পরিগণিত হবে না। যদি এমনটিই হয়ে থাকে তবে অন্ধকার যুগের আরবরাও মুশরিক ছিল না। কারণ মূর্তিসমূহ সৃষ্টিকর্মে কোন ভূমিকা রেখেছে বলে তারা মনে করত না ;বরং তারা যে সকল কর্ম আল্লাহর জন্য করা উচিত (যেমন নামাজ ,কুরবানী) সেগুলো মূর্তির জন্য করত। কখনই হোবাল ,উজ্জা বা অন্যান্য মূর্তিকে স্বাধীন খোদা বলে মনে করত না। তাঁর অন্যতম ভুল হলো তিনি মনে করেছেন ,কোন কিছু মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী হলে তার উপাসনা করা যাবে।
নামাজের সময় কাবার দিকে মুখ করাকে অগ্নি উপাসনার সঙ্গে তুলনার বিষয়টি একটি বড় ভুল। একজন সাধারণ মুসলমানও কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সময় এ চিন্তা করে না যে ,কাবা পবিত্র ,তাই এর উপাসনা করতে হবে। ইসলাম কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে নামাজের সময় কাবামুখী হওয়ার নির্দেশ দেয়নি। তাই নামাজে মুসলমানদের মাথায় কখনও এরূপ চিন্তা আসে না। কাবামুখী হওয়ার নির্দেশ ,মুসলমানদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে যদি দক্ষিণমুখী হয়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়া হতো ,তার অনুরূপ বলেই পরিগণিত হতো। মসজিদুল হারাম বা কাবার সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ কোন সম্পর্কের কথা কোরআন বলে নি ;বরং এর বিপরীতে কোরআনের শিক্ষা হলোفإينما تولّوا فثمّ وجه الله তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও মহান আল্লাহ্ সে দিকেই রয়েছেন। কাবাকে ‘ বায়তুল্লাহ্ ’ বলার অর্থ সকল গৃহই যেখানে আল্লাহর উপাসনা করা হয় তা আল্লাহর গৃহ (এ অর্থে সকল মসজিদই আল্লাহর গৃহ যদিও নামাজের সওয়াবের ক্ষেত্রে কোন কোন মসজিদের বিশেষত্ব রয়েছে)। তাই কাবামুখী হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ বিশেষ এক সামাজিক দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর হা হলো প্রথমত মুসলমানগণ যেন ইবাদাতের (নামাজ) সময় বিভিন্ন দিক নির্বাচন না করে একটি দিককেই নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়ত যে দিকটি তারা নির্ধারণ করবে তা যেন একক খোদার উপাসনার জন্য নির্মিত প্রথম স্থানটি হয় যা একক খোদার উপাসনার প্রতীক ও মহান খোদার প্রতি সম্মানের চিহ্ন।
অথচ যারথুষ্ট্রগণ ও স্বয়ং ডক্টর মুঈনের কথায় এর স্বীকারোক্তি রয়েছে ,তারা অগ্নিকেই সম্মানিত মনে করে উপাসনা করে। যদি তাই হয় তাহলে কিরূপে তা আহুরামাযদার উপাসনা বলে পরিগণিত হবে ?
ইসলামী জ্ঞানকোষে ইবাদাত (উপাসনা) শব্দের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন যে কোন আনুগত্যই হোক ,তা প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের অনুসরণ-ইসলামের দৃষ্টিতে র্শিক হিসেবে ধরা হয়। অবশ্য এরূপ র্শিক শিরকের নিম্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে কেউ ইসলাম হতে বেরিয়ে গেছে বলা যায় না। কিন্তু যদি কোন কর্ম ইবাদাতের লক্ষ্যে বা উপাসনা প্রকাশার্থে করা হয় অর্থাৎ যে কর্ম উপাসনা ও আত্মিক পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে কোন সত্তার সামনে সম্পাদিত হয় ,যেমন রুকু ,সিজদাহ্ ,কুরবানী প্রভৃতি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয় ,এমনকি নবী ,ইমাম ,ফেরেশতা সকলের ক্ষেত্রেই হারাম। এরূপ কর্মসমূহ একক মহান সত্তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হলে তা র্শিক বলে বিবেচিত হবে। এরূপ উপাসনার সঙ্গে সত্তা ,সৃষ্টি ও গুণগত তাওহীদের সমন্বয় হোক বা না হোক তা র্শিক।
এ বিষয়টির ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। যে কোন কিছুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই র্শিক নয় ;বরং কোন কিছুকে পবিত্র মনে করে তার সামনে অবনত হওয়া ইবাদাত বলে গণ্য হবে। যদি কেউ নিজেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখানোর লক্ষ্যে বিনয় প্রকাশ করে তাহলে একে নম্রতা নামে অভিহিত করা হয়। আবার অন্যকে সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিনয় প্রকাশ করলে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন বলা যেতে পারে। এরূপ নম্রতা প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনকে ইবাদাত বলা যায় না। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটি নিজেকে ক্ষুদ্র হিসেবে উপস্থাপন এবং দ্বিতীয়টি অন্যকে সম্মানিত হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।
কিন্তু কোন বস্তুকে পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত মনে করে তার সামনে অবনত হওয়া ইবাদত বলে গণ্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তা বৈধ নয়। কারণ একমাত্র ত্রুটিহীন ও পবিত্র সত্তা হিসেবে যাঁর সামনে অবনত হওয়া যায় তিনি হলেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্।
কোন বস্তুকে পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দু ’ ভাবে দেয়া যায় ,যথা মৌখিক ও কর্মের মাধ্যমে। মৌখিক পবিত্রতার ঘোষণা কোন শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে করা হয় ,যেমন ‘ সুবহানাল্লাহ্ ’ অর্থাৎ পরম পবিত্র ও মহিমাময় আল্লাহ্ বা ‘ আলহামদুলিল্লাহ্ ’ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এরূপে আল্লাহ্কে সকল পূর্ণতা ,কল্যাণ ,নিয়ামত ও বরকতের উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এমনি ‘ আল্লাহু আকবার ’ বলার মাধ্যমে তাঁকে সকল কিছু হতে শ্রেষ্ঠ ,এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত বলে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ সবই মৌখিক পবিত্রতা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ শব্দমালা তাঁর পবিত্র সত্তা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার বৈধ নয় ,এমনকি যদি সে সত্তা নবী বা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন ফেরেশতাও হয়ে থাকেন। এরূপ আরেকটি বাক্য হলোلا حول و لا قوّة إلّا بالله আল্লাহ্ ব্যতীত কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।
কর্মের মাধ্যমে পবিত্রতা হলো এই যে ,মানুষ কোন সত্তার জন্য এমন কর্ম সম্পাদন করে যাতে ঐ সত্তার পবিত্রতার ধারণা প্রতিফলিত হয় ,যেমন রুকু ,সিজদাহ্ ও কুরবানী। অবশ্য কর্ম মৌখিক স্বীকৃতির ন্যায় সুস্পষ্ট পবিত্রতার ঘোষণা নয়। কারণ একই রকম সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যেও সম্পাদিত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তা ইবাদাত বলে পরিগণিত হবে না এবং এরূপ কর্ম পবিত্র হিসেবে স্বীকৃত নয় ;বরং সাধারণ একটি কর্ম বলে বিবেচিত। কিন্তু মূর্তি বা অগ্নির সামনে যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা পবিত্রতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ এগুলো পবিত্র মনে করেই তারা তা করে। মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তা (ফিতরাত) পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী এবং ফিতরাতগতভাবেই সে ত্রুটিহীন ,পূর্ণ ও পবিত্র কোন সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতে চায়। যেহেতু পবিত্র সত্তার উপাসনা মানুষের সহজাতপ্রবৃত্তি সেহেতু এ সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এ কর্মে বাধ্য করে। এ ক্ষেত্রে উপাস্য বস্তুটির স্বাধীনতার ধারণা সচেতন বা অচেতনভাবে তার মনে থাকে যদিও ভুলবশত সে কোন সত্তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় ,যেহেতু মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ তাড়নায় মানুষ পবিত্র সত্তার উপাসনা করে সেহেতু বাস্তব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতেও উপাস্য বস্তুটিকে সত্তাগতভাবে সে স্বাধীন ও ত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করবে এমনটি নয়।
এটিই হলো উপাসনা। সুতরাং সম্মান প্রদর্শন ,বিনয় ও উপাসনা করার মধ্যে পার্থক্য যেমন আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো তেমনি কিবলা হিসেবে গ্রহণ ও পবিত্রতার ধারণায় কোন সত্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার মধ্যকার পার্থক্যও বোঝা গেল। তাই যারথুষ্ট্রগণ অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে যা করেন তা বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন যেমন নয় ,তেমনি একে কিবলা হিসেবে গ্রহণও বলা যায় না। কোন সত্তাকে (বস্তুকে) পবিত্র মনে করে তার মহিমা কীর্তন ঐ সত্তার ইবাদাত বলেই পরিগণিত ,যদিও এ কর্ম ঐ বস্তুর প্রতি প্রতিপালক ও খোদার বিশ্বাস বা ধারণা নিয়ে সম্পাদিত না হয়েও থাকে।
ডক্টর মুঈনের দাবির বিপরীতে যারথুষ্ট্রগণ অগ্নির জন্য খোদা হতে নিম্নতর কোন মর্যাদায় বিশ্বাসী নয় ;বরং তারা অগ্নির অলৌকিক (অতি প্রাকৃতিক) শক্তি ও আত্মিক প্রভাবে বিশ্বাসী ছিল এবং এখনও এ বিশ্বাস রাখে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি ‘ আভেস্তা ’ তে অগ্নির ফেরেশতা ‘ অযার ইযাদ ’ কে আহুরামাযদার পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ক্রিস্টেন সেন বলেছেন , “ এ ধর্মে অগ্নি অন্য সকল বস্তু হতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত। ”
তিনি তাঁর গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন ,
“ মি. হারটেল তাঁর ‘ ভারত ও ইরানী গবেষণামূলক উৎসসমূহ ’ নামক ধারাবাহিক নিবন্ধে বলেছেন... ইরানীরা অগ্নিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় বিশ্বে প্রভাবশীল একটি উপাদান বলে বিশ্বাস করত। ”
অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন , “ আমি মনে করি হারটেলের কথাটি অবাস্তব নয়। ”
স্বয়ং ডক্টর মুঈন ইরানের প্রাচীন তিনটি অগ্নিমন্দিরের অন্যতম অযার বারযিন মেহের-এর অগ্নিমন্দির সম্পর্কে বলেছেন ,
‘ বুন্দহেশের সতেরতম অধ্যায়ের অষ্টম ধারায় উল্লিখিত হয়েছে অযার ,বারযিন ,মেহের-এর অগ্নিমন্দির গুশতাসবের শাসনামল পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল এবং ‘ বিশ্বের আশ্রয় ’ বলে পরিগণিত হতো। যখন যারদুশত অনুশেহ রাওয়ান নতুন ধর্ম আনয়ন করেন গুশতাসব তা গ্রহণ করে এবং অযার বারযিন মেহেরকে রিভান্দ পর্বতে যা ‘ পুশত ওয়া পুশতাসেপান ’ নামে প্রসিদ্ধ সেখানে স্থাপন করেন। ’
অতঃপর তিনি আভেস্তার অংশবিশেষ হতে উল্লেখ করেছেন:
“ অগ্নির সাহায্য পেয়েই কৃষকগণ কৃষি কর্মে জ্ঞান ,দক্ষতা ও পবিত্র পথে উন্নতি করার সুযোগ পেয়েছে। এই অগ্নির সঙ্গেই গুশতাসব প্রশ্নোত্তর বিনিময় করেন। ”
তিনি যারথুষ্ট্রদের অন্যতম প্রধান অযার ফারানবাগ-এর অগ্নিমন্দির সম্পর্কে বলেছেন ,
“ এ অগ্নিমন্দির পুরোহিতগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আভেস্তার প্রার্থনা সম্বলিত অংশের পাহলাভী তাফসীরের পঞ্চম ধারায় বাহরামের অগ্নির বর্ণনায় এসেছে ,এই অগ্নির নাম ‘ অযার ফারানবাগ ’ । এ অগ্নিটিই সকল অগ্নির রক্ষক ও অগ্রগামী এবং এ অগ্নির সাহায্যেই পুরোহিগণ জ্ঞান ,সম্মান ও মর্যাদা (ক্ষমতা) লাভ করেন। এ অগ্নিই দাহাকের (যাহাক) সঙ্গে যুদ্ধ করে। ” 127
বুন্দহেশের সতের অধ্যায়ে তৃতীয় বৃহত্তম ও প্রধান ‘ অযার গুশতাসব ’ -এর অগ্নিমন্দির সম্পর্কে স্বয়ং ডক্টর মুঈন তাঁর ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ গন্থের 311 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ,
“ সম্রাট কেইখসরু ও হোমারেহ্-এর শাসনামলে অযারগুশনাসবের অগ্নিমন্দির বিশ্ববাসীর আশ্রয়স্থল ছিল। যখন কেইখসরু ‘ চাচাস্ত ’ হরদ ধ্বংস করেন তখন এই অগ্নিকুণ্ড তাঁর অশ্বসমূহের পদতলে মাটিতে দেবে যায় ও এর কালচে ভাব দূর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এর আলোতে তিনি মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি তার নিকটবর্তী পর্বতে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে অযার গুশতাসবকে পুনঃস্থাপন করেন। ”
বুন্দহেশ হতে এ অগ্নি সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন , “ তিনটি স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের একটি বিশ্ববাসীকে সাহায্যের লক্ষ্যে আজারবাইজানে এসে অবস্থান নেয়। ”
ফেরদৌসী কায়কাউস ও কেইখসরুর ‘ অযারগুশাসবের ’ অগ্নিমন্দিরে গমনের কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন ,
“ অগ্নির পাদমূলে বসিয়া লইব সবক
মহান খোদা হইবেন মোর পথ প্রদর্শক
স্বয়ং না আসিয়া তিনি পবিত্র এ মন্দিরে
পাঠাইলেন প্রতিনিধি পথ দেখাইবার তরে। ”
আমরা কোন মূর্তিপূজককে ও তাদের মূর্তিরূপ প্রভুর বিষয়ে এরূপ অতি প্রাকৃতিক ও আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখি না।
তেহরানের যারথুষ্ট্র সংস্থা হতে প্রকাশিত পত্রিকা ‘ হুখত ’ -এ আরদ্শির অযারগুসাব নামের এক পুরোহিত তাঁর প্রবন্ধে দাবি করেছেন যারথুষ্ট্রগণ কখনই অগ্নি উপাসক ছিল না। ‘ অপপ্রচারের জবাব ’ নামক এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ,
‘ আমরা ঐশী গ্রন্থসমূহ হতে এ বিষয়টি প্রমাণ করব ,মহান খোদা স্বয়ং সকল জ্যোতির উৎস হিসেবেنور الأنوار বা ‘ জ্যোতিসমূহের জ্যোতি ’ বলে গণ্য। যারথুষ্ট্রগণ উপাসনার সময় অগ্নির দিকে মুখ করে মূলত অগ্নির মাধ্যমে খোদার সঙ্গেই গোপন কথোপকথন করে থাকে ও তাঁর নিকট হতেই সাহায্য প্রার্থনা করে। এ বিষয়টি (আলো বা অগ্নির দিকে মুখ করে আহুরামাযদার উপাসনা) তাদের একত্ববাদী বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কারণ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নামাজ পড়ার সময় কিবলামুখী হয় এবং তাদের এ কর্মকে কেউ মৃত্তিকা উপাসনা বা প্রস্তর উপাসনা বলে অভিহিত করে না। ’
এই যারথুষ্ট্র পুরোহিত ‘ আরদ্শির অযারগুশাসব ’ পবিত্র একটি বস্তু হিসেবে অগ্নির নানাবিধ উপকারিতা বর্ণনা করে বলেছেন , ‘ প্রথম যুগের মানুষের সকল রকম উন্নতি এই লাল ও উজ্জ্বল অগ্নির কারণেই হয়েছিল। তাই অগ্নি তাদের নিকট সম্মানিত হওয়ার অধিকার রাখত এবং একে এক ঐশী শক্তি হিসেবে মানুষের সাহায্যে এসেছে বলেই ধারণা করা উচিত। এর জন্য উপাসনালয় প্রস্তুত করা ,ঘরের চুলাকে অবিরত জ্বালিয়ে রেখে নির্বাপিত হওয়া হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য ছিল। ’
পুরোহিত আরদ্শির অযারগুশাসবের কথার জবাবে বললেন , “ হ্যাঁ ,খোদা ‘ নুরুল আনওয়ার ’ কথাটি সঠিক কিন্তু তা এ অর্থে নয় যে ,তারা বস্তুকে দু ’ ভাগে ভাগ করত যার এক ভাগ আলো অন্যভাগ অন্ধকার। ” অতঃপর বলব খোদা ‘ জ্যোতিসমূহের জ্যোতি ’ অন্ধকারসমূহের জ্যোতি নন ;বরং আল্লাহ্ সকল জ্যোতির জ্যোতি এ কথার অর্থ হলো সমগ্র অস্তিত্বই আলো (আলো = অস্তিত্ব) এবং অনস্তিত্ব হলো অন্ধকার। তাই মহান আল্লাহ্ সকল কিছুর জ্যোতি-
الله نور السّماوات و الأرض মহান আল্লাহ্ আকাশ ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি । এ দৃষ্টিতে অগ্নি ,সূর্য ,প্রদীপের সঙ্গে মাটির ঢিলা ও পাথরের কোন পার্থক্য নেই। তাই যদি অগ্নির দিকে মুখ করি খোদার দিকে মুখ করেছি আর মাটির দিকে মুখ করলে খোদার দিকে মুখ করি নি বলা অর্থহীন।
তিনি বলেছেন , “ যারথুষ্ট্রগণ অগ্নির দিকে মুখ করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির সাহায্যে মহাজ্যোতির সঙ্গে গোপন সংলাপ করে থাকে। ”
কিন্তু আমরা বলব ,এক আল্লাহর উপাসনার অর্থ মানুষ যখন তাঁর প্রতি মুখ করবে কোন কিছুকেই যেন মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে। তাই তিনি বলেছেন ,وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب “ যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (তাকে বল) আমি তার নিকটবর্তী আছি। ” অর্থাৎ মহান খোদার দিকে মুখ করার জন্য কোন কিছুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের কোন প্রয়োজনই নেই।
হ্যাঁ ,অবশ্য যদি কোন মানুষ আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয় (মুখ ফেরায়) এবং তাঁর পরিচয় লাভের মাধ্যমে আল্লাহর ওলীতে পরিণত হয় অর্থাৎ ইবাদাতের উচ্চতর পর্যায় অতিক্রমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয় (ফানাফিল্লাহ্) ,এ পর্যায়ে অন্যরা দোয়া ও গুনাহ মাফের (ইস্তিগফার বা পাপ মার্জনা) জন্য তাঁদের উসিলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু তাঁরা একদিকে আল্লাহর পূর্ণ ও সৎ কর্মশীল বান্দা ,অন্যদিকে জীবিত ,সেহেতু অন্যান্যরা তাঁদের হতে হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পাপ মার্জনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া প্রত্যাশা করেন যেন তিনি তাঁর করুণায় গুনাহসমূহকে মার্জনা করেন।
সাহায্য প্রার্থনা এজন্য বৈধ ,যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তিনি জীবিত ,রিযিকপ্রাপ্ত এবং উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন ;তিনি আমাদের চেয়ে উত্তমরূপে আল্লাহর উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা করতে সক্ষম এবং এ কারণেই তিনি আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী। আমরা মুসলমানগণ রাসূলে করিম (সা.)-এর যিয়ারতে পড়ে থাকি :
اللّهمّ إنّي أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته و أعلم أنّ رسولك و خلفائك عليهم السّلام أحياء عندك يُرزقون,يرون مقامي و يسمعون كلامي و يردّون سلامي
“ হে আল্লাহ্! আমি এই পবিত্র স্থানের অধিকারীর সম্মান তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জীবিতাবস্থার অনুরূপ মনে করি। আমি জানি তিনি আপনার রাসূল (সা.) এবং আপনার মনোনীত প্রতিনিধিগণ (আ.) সকলেই আপনার নিকট জীবিত ও আপনার নিকট হতে রিযিকপ্রাপ্ত। তাঁরা আমার অবস্থানকে দেখছেন ও আমার কথা শুনছেন এবং আমার সালামের জবাব দান করছেন। ”
এ যিয়ারতের শেষাংশে আমরা পড়ি:
أللّهمّ إنّك قلتَ: ((و لو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً.)) و إنّي أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي و إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي و ربّك ليغفرلي ذنوبي
“ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আপনি (পবিত্র কোরআনে) বলেছেন: তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করে ও আপনার নিকট আসে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী ও দয়াশীলরূপে পাবে। (অতঃপর নবীকে উদ্দেশ করে পড়া হয়) হে প্রিয় নবী! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও গুনাহ হতে অনুশোচনাকারী হয়ে প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে এসেছি। আপনি আল্লাহর সৎ কর্মশীল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে আমার ও আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি যাতে তিনি আমার গুনাহসমূহ মার্জনা করেন। ”
যেহেতু আল্লাহর ওলীদের শরণাপন্ন হয়ে দোয়া চাওয়া এরূপ বিশ্বাস নিয়ে সম্পাদিত হয় সেহেতু তা শিরক তো নয়ই ;বরং ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত।
অগ্নিকে কাবার ন্যায় কিবলা হিসেবে গ্রহণের বিষয়টির জবাব আমরা পূর্বে দিয়েছি এবং বলেছি অগ্নির প্রতি পবিত্রতার ধারণা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়ার সঙ্গে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার (আল্লাহর ইবাদাতের) মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না।
পুরোহিত আরদ্শির বলেছেন ,
‘ যেহেতু অগ্নি মানুষের প্রচুর উপকারে আসে সেহেতু মানুষের অধিকার রয়েছে অগ্নির প্রতি বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার ও একে মূল্য দেয়ার । ’
তাঁর কথার সারবস্তু এখানেই। প্রকৃতপক্ষে নবিগণের আগমনের (নবী প্রেরণের) লক্ষ্য এটিই যে ,তাঁরা মানুষকে সকল কল্যাণ ,নিয়ামত ও বরকতের উৎসের সঙ্গে পরিচিত করাবেন এবং তাদের এমন চক্ষু দান করবেন যা দ্বারা মূল কারণকে তারা দেখতে পারে। তাঁরা এসেছিলেন মানুষকে কারণ হতে সকল কারণের মূলের দিকে নিয়ে যাবেন এবং তাদের বোঝাবেন
الحمد لله ربّ العالمين ‘ সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। ’
তাছাড়া আমাদের দেখতে হবে শুধু অগ্নিই ঐশী বস্তু নয় যা মানুষকে সাহায্য করার জন্য আসমান হতে এসেছে। অবশ্য যদি আসমান বলতে আমাদের মাথার ওপর বিদ্যমান মহাশূন্য বোঝানো হয়ে থাকে তবে তা ঐশী বা বিশেষ কোন বস্তু বলে গণ্য নয়। আর যদি আসমান বলতে অদৃশ্য জগৎ বোঝানো হয় তবে সকল বস্তুই আসমান হতে এসেছে এবং এ ক্ষেত্রে অগ্নির কোন বিশেষত্ব নেই।
) و إن من شيء إلّا عندنا خزائنه و ما ننَزّله إلّا بقدر معلوم (
‘ আমাদের নিকট প্রত্যেক বস্তুরই ভাণ্ডার রয়েছে এবং তা হতে নির্দিষ্ট পরিমাণেই আমরা অবতারণা করি। ’ 128
ধর্মীয় আচার ও আনুষ্ঠানিকতা
অগ্নি উপাসনা বা অগ্নির প্রতি বিশেষ রীতিতে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি সাধারণ নয় ;বরং শোনার মত একটি অনুষ্ঠান এটি। আমরা ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ নামক গ্রন্থ থেকে এ অনুষ্ঠানের কিছু বিবরণ দান করব তাতে অগ্নির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবিদার ও পক্ষাবলম্বনকারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। এ গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও এ অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে এবং বর্তমানে বিদ্যমান যারথুষ্ট্রগণের মধ্যেও এর প্রচলন লক্ষণীয়।
উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে :
“ ইসলামের বিপরীতে যারথুষ্ট্র ধর্মে খ্রিষ্টধর্মের ন্যায় বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার ও বিশেষ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান। এরূপ আনুষ্ঠানিকতা অগ্নিমন্দিরগুলোতেও প্রচলিত। অগ্নিকুণ্ডকে এমন স্থানে রাখা হয় যাতে চারিদিক উন্মুক্ত থাকে। প্রতিটি অগ্নিমন্দিরের অগ্নি প্রজ্বলনের বিশেষ রীতি রয়েছে এবং ‘ অতারবান ’ (অগ্নিরক্ষক পুরোহিত) ব্যতীত অন্য কেউ সেখানে প্রবেশের অধিকার রাখে না। অগ্নিরক্ষক পুরোহিতগণ অগ্নির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁদের মুখমণ্ডল বেঁধে নেন যাতে করে তাঁদের নিঃশ্বাস অগ্নিকে অপবিত্র না করে ফেলে। অগ্নিকুণ্ডের ডানদিকে একটি চৌকোণা ঘর রয়েছে যা কয়েকটি সমান ভাগে বিভক্ত এবং এর প্রতিটি অংশ বিশেষ বিশেষ আচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কক্ষকে ‘ ইয়াযশেনগাহ্ ’ (বিশেষ ইবাদাত ও আচারের স্থান) বলা হয়।... যারথুষ্ট্র ধর্ম গ্রন্থে পুনঃপুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে সূর্য কখনই অগ্নির ওপর আপতিত না হয়।129 তাই অগ্নিমন্দিরসমূহ বিশেষ গঠন ও আকৃতিতে তৈরি করা হয়। অগ্নিমন্দিরের মাঝামাঝি অন্ধকার একটি কক্ষ তৈরি করা হতো এবং অগ্নিচুল্লীটি সেখানে স্থাপন করা হতো।...
ইরানের অভিজাত শ্রেণীর রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অগ্নির উপস্থিতি ছিল ,যেমন গৃহের অগ্নি ,গোত্রের অগ্নি ,আঞ্চলিক অগ্নি ,প্রাদেশিক অগ্নি প্রভৃতি। গৃহের অগ্নিরক্ষককে ‘ মনবায ’ বলা হতো এবং দু ’ জন পুরোহিত এর রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আঞ্চলিক অগ্নির প্রতিরক্ষার জন্য একজন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মযাজকের অধীনে গঠিত পুরোহিতগণের কমিটি ছিল...।
সাসানী আভেস্তার একটি অংশের নাম হলো ‘ সুযগার ’ যেখানে অগ্নি উপাসনার প্রকৃতি ও এ সম্পর্কিত কিছু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক অগ্নিমন্দির ধূলা ও অন্যান্য সুগন্ধীতে ভরপুর ছিল। এক পুরোহিতের নিজ নিঃশ্বাসে যাতে অগ্নি নির্বাপিত না হয় সেজন্য মুখমণ্ডল বেঁধে ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে পবিত্রকৃত কাঠের টুকরাসমূহ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখার কাজে রত ছিলেন। এই কাঠের টুকরোসমূহ ‘ হাযানে আপতা ’ নামক বৃক্ষ হতে সংগৃহীত হতো। ঐ পুরোহিত টুকরোগুলোকে বিশেষ রীতিতে ‘ বেরাসম ’ নামক কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অগ্নিতে ফেলছিলেন ও বিশেষ মন্ত্র ও দোয়া পড়ছিলেন। অন্যান্য পুরোহিতরা ‘ হুমে ’ 130 ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন এবং পান ও উৎসর্গ করছিলেন। দোয়া ও মন্ত্র পাঠের (আভেস্তা হতে) মাধ্যমে ‘ হুমের ’ কাষ্ঠকে পবিত্র করে ‘ হুউন ’ -এর দ্বারা আঘাত করছিলেন... অগ্নি উপাসনার বিশেষ স্থানে (ইয়াযশেনগাহ্) নিম্নোক্ত বস্তুসমূহ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হতো :
1. ‘ হাউন ’ ও হাউনের দণ্ড যা খ্রিষ্টানদের ঘণ্টার ন্যায় এবং এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যদিও পূর্বে তা পবিত্র বৃক্ষ হুমের কাষ্ঠে আঘাত করার জন্য ব্যবহৃত হতো।
2. বেরাসম্ পবিত্র সিক্তবৃক্ষ ,যেমন ডালিম গাছ হতে প্রস্তুত হতো। বর্তমানে রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ দণ্ড দ্বারা এটি প্রস্তুত করা হয়।
3. বেরাসম্দান।
4.বেরাসম্চিন যা ক্ষুদ্র ছুরি বিশেষ ।
5. পবিত্র পানি ও হুমের জন্য কয়েকটি পাত্র।
6. কয়েকটি বাটি বৌল বা গামলা।
7. ভারস যা গরুর লোম ও চুল (লেজের) দ্বারা তৈরি ছোট দড়ি যা বেরাসমের সঙ্গে বাঁধা হয়।
8. আরভিস নামের বড় এক পাথর খণ্ড (চৌকোণা) যার ওপর উপরোক্ত বস্তুসমূহ রাখা হতো ।
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন :
‘ ফার্সী অভিধানসমূহে এসেছে: বারসাম গিটহীন সরু এক বিঘত দৈর্ঘ্যরে হুম বৃক্ষের শাখা। এ বৃক্ষটি ঝাউ বৃক্ষের মত দেখতে। তাই যদি হুম বৃক্ষ না পাওয়া যায় ঝাউ বৃক্ষের শাখা নতুবা ডালিম গাছের ডাল ব্যবহৃত হবে। এই শাখা কাটার রীতি হলো বেরাসম্চিন নামক ছোট ছোরা যার হাতলটি লৌহ নির্মিত পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে ও ধোয়ার সময় দোয়া পড়তে হবে অর্থাৎ অগ্নি উপাসনা ,গোসল করা ও খাওয়ার সময় পড়ার দোয়াসমূহ এ সময় পড়তে হবে ও শাখা কাটতে হবে। ’
তাঁর বর্ণনা মতে বর্তমান ইরানের যারথুষ্ট্রগণের অগ্নি উপাসনার রীতি হলো যখন একজন পুরোহিত প্রার্থনা করতে থাকেন অন্য পুরোহিত অগ্নির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন (যাতে তা প্রজ্বলিত থাকে) ও বারসামদানের ওপর রাখা কাঠের টুকরোগুলোকে হাতে হাতে দিয়ে দিবেন এবং পরে তা পুনরায় বারসামদানের ওপর সাজিয়ে রাখবেন।
অন্যত্র তিনি বলেছেন :
“ দার মাসতাতার আভেস্তার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,দু ’ ধরনের অগ্নিমন্দির রয়েছে। বড় অগ্নিমন্দিরকে ‘ অতাশ বাহরাম ’ বলা হয় এবং ক্ষুদ্র মন্দিরকে ‘ অদারান ’ বা ‘ অগইয়ারী ’ বলা হয়। ভারতের মুম্বাই (বোম্বে) তিনটি বড় অগ্নিমন্দির ও প্রায় একশ ’ টি ক্ষুদ্র অগ্নিমন্দির রয়েছে। ‘ অতাশ বাহরাম ’ ও ‘ অগইয়ারী ’ র মধ্যে অগ্নির আকৃতি ও প্রস্তুতরীতিগত পার্থক্য রয়েছে। অতাশ বাহরাম প্রস্তুতের জন্য এক বছর সময় লাগে ও তের ধরনের অগ্নি হতে তা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই তের ধরনের অগ্নিকে সকল ধরনের অগ্নির নির্যাস বলা যেতে পারে। এগুলোকে পবিত্রকরণের রীতি ও আনুষ্ঠানিকতা সাসানী আভেস্তার ভানদিদাদ অংশে বর্ণিত হয়েছে। যারথুষ্ট্র রীতি অনুযায়ী প্রতি অঞ্চলে অবশ্যই একটি ‘ অতাশ বাহরাম ’ থাকতে হবে। কোন কোন যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকের মতে এক অঞ্চলে একের অধিক ‘ অতাশ বাহরাম ’ থাকতে পারবে না। কারণ এক দেশে কয়েক রাজা থাকতে পারে না।... যেহেতু সে রাজা তাই তার সিংহাসন দু ’ ভাগে ভাগ করে সিংহাসন আকৃতিতে সাজিয়ে ধাপযুক্ত সিংহাসনের রূপ দেয়া হয়েছে। ”
এ হলো যারথুষ্ট্রগণের অগ্নি উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা। এ আনুষ্ঠানিকতা কতটা তাওহীদভিত্তিক বা র্শিকমিশ্রিত তা নিয়ে এখন আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। একে মূর্তিপূজা বা খোদা উপাসনা কিছুই বলব না। শুধু সম্মানিত পাঠকগণকে এরূপ আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলব যে ,এর হতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোন আচার-অনুষ্ঠান পৃথিবীতে আছে কি ? অতঃপর ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এগুলোর তুলনা করুন। যেমন নামাজ ,আযান ,জুমআ ,জামায়াত ,হজ্ব ,তাসবীহ-তাহলীল ,আল্লাহর শোকর আদায়ের প্রক্রিয়াসহ মসজিদকেন্দ্রিক অন্যান্য ইবাদতসমূহের সঙ্গে এ ধরনের আচারের তুলনা করে দেখুন এ দু ’ য়ের মধ্যে পার্থক্য কত ? অতঃপর বলুন ,ইরানের জনসাধারণের এ অধিকার ছিল কি না যে এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার ?
এ আলোচনার শেষে এক পেঁচার আর্তনাদের বর্ণনা দান করব যা থেকে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এরূপ আর্তনাদসমূহের মূল্য বুঝতে পারবেন।
ভারতের নওসারী শহরের ‘ ইরান শাহ ’ নামের প্রসিদ্ধ অগ্নিমন্দির যা বড় অগ্নিমন্দিরের (অতাশ বাহরামের) অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে ইবরাহীম পুর দাউদ বলেছেন :
‘ ইরানী মুহাজিররা ভারতবর্ষে ‘ অতাশ বাহরাম ’ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের এ কর্ম সঠিক বলেই প্রতিভাত হয়। কারণ তারিখে তাবারী ও মাসউদী থেকে জানা যায় ,পরাজয়ের যুগে ইরানীরা শত্রুর হাতে পড়ে নির্বাপিত হওয়ার ভয়ে অগ্নিকে দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়।131 যদিও ইরানের জাঁকজমকপূর্ণ অগ্নিমন্দিরসমূহ মসজিদের রূপান্তরিত ও অগ্নিকুণ্ডসমূহ নিভে গিয়েছিল তদুপরি ইরানিগণ তাদের সাধ্যমত তা রক্ষায় চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় ইয়াযদ গারদ নাহাভান্দের যুদ্ধে পরাজয়ের পর স্বয়ং রেই শহরের পবিত্র অগ্নিটিকে মারভে নিয়ে যান। যদিও ‘ ইরানশাহ ’ অগ্নিমন্দির ইরানী মুহাজিরদের সেনজানে প্রবেশের পর নির্মিত হয়েছিল (716 খ্রিষ্টাব্দ) তদুপরি 1230 বছর হলো তারা সব সময় এই বিদেশ বিভূঁইয়ে শত্রু হতে এ অগ্নির বিষয়ে চিন্তিত ছিল। কিন্তু এই অগ্নি দিনের টানাপড়েনে রংহীন হয়ে পড়েনি ;বরং তার সহযোগীদের উষ্ণ কণ্ঠে সমবেদনা জানিয়ে উৎসাহিত করে এসেছে। সেনজানের পতনের পর সেটি নসারীতে আশ্রয় নেয় ও দীর্ঘ 235 বছর সেখানে বিদ্যমান ছিল। এই অগ্নি শুধু দু ’ বছর (1733-1736) সূরাটে নির্বাপিত ছিল। কিন্তু এরপর 204 বছর হলো এই গ্রামে তা পুনঃস্থাপিত হয়েছে। পুরোহিতগণের নির্দেশে সহস্র যারথুষ্ট্র এই অগ্নির চারপাশে সমবেত হচ্ছে। ইরানী ও ভারতীয় পারসিকগণ সেখানে যিয়ারতে গিয়ে থাকেন।
বিশেষত ফার্সী বর্ষের ‘ উরদিবেহেশত ’ ও ‘ অযার ’ মাসে সেখানে যিয়ারতে ভীড় হয়। ইরানশাহ নামের এই অগ্নিমন্দির হতে প্রতিদিন সকাল ,মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় সাদা পোশাক পরিহিত পুরোহিতগণের আভেস্তার গজল পাঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। ইরানশাহ অগ্নিমন্দিরের সেবকদের কণ্ঠধ্বনি সাসানী শাসনামলের জাঁকজমকপূর্ণ রেই ,শিজ ও ইসতাখরের অগ্নিমন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।132
কেউ কি বিশ্বাস করবেন ,বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দাবিদার একজন শিক্ষক এতটা অজ্ঞতার পরিচয় দেবেন ? জানি না এটি অজ্ঞতা নাকি অজ্ঞতার ভান ? নাকি কালো সাম্রাজ্যবাদের হাতে প্রতিপালিতের কণ্ঠধ্বনি ?
‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ এই শিরোনামেই ডক্টর মুঈন গ্রন্থটি লিখেছেন। আমরা আমাদের আলোচনায় এ গ্রন্থ হতে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই গ্রন্থের নাম ও লেখকের ভূমিকা হতে বোঝা যায় ফার্সী সাহিত্যে মাযদা ইয়াসনা শব্দসমূহ ও এ চিন্তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এরূপ কর্ম উপকারীই শুধু নয় জরুরীও বটে। কিন্তু এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তাঁর শিক্ষক ও নির্দেশক দাউদ ইবরাহীম। মূলত ডক্টর মুঈন তাঁর নির্দেশকের দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে ,ইরানী মানসিকতা গত কয়েক হাজার বছরে ,এমনকি ইসলামী শাসনামলেও পরিবর্তিত হয় নি ,কোন চিন্তাই তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি এবং এখনও ইরানী মানসিকতা মাযদা ইয়াসনা মানসিকতা হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে ,এমনকি এ চিন্তা অন্য চিন্তাসমূহকেও তার দ্বারা প্রভাবিত করে ফেলে। তাই তিনি বলেছেন :
‘ বিজয়ী আরবরা ইরানে যে ধর্ম এনেছিল (অর্থাৎ পৃকৃত ইসলাম) তা শিয়া রং ধারণ করে। ’
পুর দাউদের ধারণায় মানুষের মানসিকতার প্রভাবক উপাদানসমূহ প্রধানত ভূমি ,বংশ ও ভাষা। তিনি তাঁর দর্শনকে এ ভিত্তির ওপর রেখেই বলেছেন ,ইরানী মানসিকতা মাযদা ইয়াসনা মানসিকতা। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যে বলতে পারে আমি নিখাঁদ এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। তুর্কী ,মোগল ,আরব ,এমনকি গ্রীক ও ভারতীয় রক্ত প্রাচীন ইরানীদের সঙ্গে এতটা মিশ্রিত হয়েছে যে ,বিশেষত অসংখ্য অসম বিবাহের ফলশ্রুতিতে তাতে কেউ আজকে দাবি করতে পারে না যে ,আমি খাঁটি আর্য ও ইরানী। তাই খোদ পুর দাউদের রক্তে কোন্ জাতির মিশ্রণ ঘটেছে বলা মুশকিল। হয়তো পিতৃ দিক হতে তিনি উমাইয়্যা আরব ও মাতৃ দিক হতে মোগল চেঙ্গিস খানের বংশধর হতে পারেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।
ভাষার অবস্থাও জাতির মত। যদি ভিন্ন ভাষার শব্দের কথা বাদও দিই তবু বর্তমানের ফার্সী ভাষা ইরানের প্রাচীন ভাষাভাষীদের কোন ক্ষুদ্র অংশের ভাষা হয়ে থাকবে ,সমগ্র ইরানীর নয়। বিশেষত বর্তমান ফার্সীর সঙ্গে আভেস্তা আমলের ফার্সীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য।
শুধু বাকী থাকে ভূমি। কিন্তু স্বয়ং পুর দাউদের ভাষায় আমাদের বর্তমান ভূমিটি প্রাচীন ভূমির ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। তবে পুর দাউদের দর্শন অনুযায়ী সকল রহস্য মাটি ও পানির (জন্মভূমি) মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এবং ইরানী মানসিকতার ভিত্তিও এ ভূমির মাটি ও আবহাওয়ার মধ্যে নিহিত। তাই যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কাল্পনিক বিষয়ের নমুনা আমরা দেখলাম এ ভূমিতেই উৎপন্ন মাযদা ইয়াসনা ধর্মের মধ্যে রয়েছে বলে তাকেই আমরা ইরানী মানসিকতা বলব।
পুর দাউদ দাবি করেছেন :
“ জীবন ও চিন্তাধারা জাতিসত্তা ও ভাষার ন্যায় আমাদের কয়েক হাজার বছর পূর্বের প্রজন্ম হতে অপরিবর্তিতভাবে বংশগতভাবে বাহিত হয়ে এসেছে। ”
আমি বলব ,আমাদের জীবন ও চিন্তাধারা আমাদের জাতিসত্তা ও ভাষার ন্যায় নয় ;বরং এর থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ইরানীরা তাদের আল্লাহ্প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও সুপ্ত প্রতিভার গুণে দ্বিত্ববাদ ,অগ্নি উপাসনা , ‘ হুমে ’ উপাসনা ,সূর্য ও মানব উপাসনা ও এরূপ হাজারো কুসংস্কারকে ইসলামী শিক্ষার ছত্রছায়ায় দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে।
পুর দাউদ নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় যেন খড়কুটাকে ধরে বাঁচতে চান। তাই ইরফানের (অধ্যাত্মিক) বিশেষ ভাষায় যে সকল ইরানী কবি কথা বলেছেন তাঁদের কথাকে তাঁর পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন ,অথচ এই সকল কবি133 শতাব্দীকাল ধরে ইসলামের বিশ্বজনীন ধারণার রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে জাতি ,ভাষা ও জন্মভূমির অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং ‘ সকল জাতি সমান ’ -এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। পুর দাউদ তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও তাঁদের কবিতায় ব্যবহৃত মদ ,পুরোহিত ,অগ্নি ,অগ্নিমন্দির প্রভৃতি শব্দের অধ্যাত্মিক অর্থকে পরিত্যাজ্য ও বিবর্তিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন ,
“ অগ্নিমন্দিরসমূহ নির্বাপিত হওয়ার পরও ইরানী কবিদের হৃদয় প্রেমের অগ্নিমন্দির হয়ে রয়েছে। এখনও তার ব্যথার আরোগ্যের জন্য দূরবর্তী অঞ্চলের পুরোহিতগণের শরণাপন্ন হতে চায় যদিও তাদের ভূমি হতে তারা উৎখাত হয়েছে এবং কেউ তাদের শরণাপন্ন হতে অক্ষম। ’
আমিও বলি একজন প্রকৃত ইরানী যার মধ্যে ইরানী জাতীয়তার জ্ঞান রয়েছে ,যেমন হাফিয ,সা ’ দী ,মাওলানা রুমী ,জামী ও এরূপ শত কবির অন্তর প্রেমের অগ্নিমন্দির এবং তার মনের ব্যথা সারানোর জন্য বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে যেতে চায়। কিন্তু তার প্রেমের ঐ অগ্নিমন্দির প্রকৃতির উপাদানের উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত বারসাম ,বারসামদান ,বারসামচিন ,ছিদ্রহীন পানপাত্র বহনকারী চার দেয়ালের কোন অগ্নিমন্দির নয় এবং সে তার মনের ব্যথা আরোগ্যের জন্য যে বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে যেতে চায় তিনি সাদা পোশাক পরিহিত ,বারসামধারী অগ্নিকে নিয়ে কুসংস্কারপূর্ণ অনর্থক কর্মে লিপ্ত (জীবনের মূল্যবান সময়ক্ষেপণকারী) কোন যারথুষ্ট্র পুরোহিত নন ;বরং এই পুরোহিত একক আল্লাহর পথের যাত্রী ,আল্লাহর ওলী ও মানুষকে মহা সত্যের দিকে হেদায়েতকারী। তাঁরা ইসলামী শাসনামলে ইসলামের মহান মানবীয় উদ্দেশ্য ও ইরফানের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।
তাই পুর দাউদ যে বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা বলেছেন ইরানীরা সহস্র বছর পূর্বে তাঁদের ইরান হতে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। তাঁর বক্তব্য মতে কেউ তাঁদের নিকট পৌঁছতে অক্ষম। কথাটি ভুল এ অর্থে যে ,তাঁরা ইরানীদের নিকট পৌঁছতে সক্ষম নন। তবে অন্য কেউ তাঁদের নিকট পৌঁছতে অক্ষম হলেও পুর দাউদ যে তাঁদের নিকট পৌঁছতে সক্ষম তা বোঝা যায়। এই পুরোহিতগণের পকেট বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় নির্যাতিত মানুষের অর্থে (যা ইংরেজগণ তাঁদের সঙ্গে হাত মিলানোর কারণে দিত) পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা মর্যাদাশীল ইরানী জাতিকে পেছন হতে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ইরানী জাতিকে পুনরায় তাঁদের প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত শেকল দিয়ে বাঁধতে যা অগ্নিধারক ,বারসাম ,বারসামচিন ,হুমে ও অন্যান্য কুসংস্কার দ্বারা প্রস্তুত।
দুঃখজনকভাবে ড. মুঈন তাঁর এ গ্রন্থ রচনায় পুর দাউদের চিন্তা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন যদিও তার জীবনের শেষদিকে দেয়া তাঁর কিছু সাক্ষাৎকারে তাঁকে ইসলামের মৌলনীতি ও কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে। তদুপরি কেন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য হতে পশ্চাদ্ধাবন করেছেন ও ইসলামের উৎস হতে যারথুষ্ট্র ধর্মের আচারকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।
উদাহরণস্বরূপ তিনি তাঁর গ্রন্থের 76 পৃষ্ঠায় যারথুষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন ,
‘ কোন কোন ইতিহাসবিদ যেমন হুশানগের মতে যারথুষ্ট্র রুস্তম ,যাল ও ইসফানদিয়ায়ের মত এক কাল্পনিক অস্তিত্ব ,কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে নবী ও ধর্মীয় পুরোধাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের বিষয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ’
অতঃপর টীকায় উল্লেখ করেছেন , ‘ এমনকি হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কেও। ’
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ,কেউ যারথুষ্ট্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে রাসূল (সা.)-এর অস্তিত্বের সাথে তুলনা করেন। একজন বিশেষজ্ঞের যারদুশত সম্পর্কে মতকে ইসলামের কোন শত্রু কর্তৃক রাসূল সম্পর্কে মন্তব্যের সাথে তুলনা সত্যিই আশ্চর্যের।
তিনি তাঁর গ্রন্থের 273 পৃষ্ঠায় অগ্নির পবিত্র হওয়া বিষয়ক আলোচনায় বলেছেন , “ আর্য ধর্মসমূহ ,যেমন ব্রাহ্মণ ধর্ম ,যারথুষ্ট্র এবং সামী ধর্মসমূহ ,যেমন ইহুদী ,খ্রিষ্টান ও ইসলাম ,এমনকি আফ্রিকার মূর্তিপূজকদের মধ্যেও অগ্নি বিশেষ গুরত্ব রাখে। ”
আমার নিকট বোধগম্য নয় ,বংশ পরম্পরায় মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে তিনি কিরূপে এমন মন্তব্য করলেন ? ইসলামের কোথায় তিনি অগ্নির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন ? কোরআনে যা এসেছে তা হল জ্বিন ও শয়তান আগুন হতে তৈরি হয়েছে এবং মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি হতে।
মাটির মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হলে অগ্নির শয়তান তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়।
415 পৃষ্ঠায় ‘ ফার ইযাদি ’ সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন ,
‘ যামইয়াদিশতের বর্ণনা মতে ,ফার ইযাদির (অগ্নির ফেরেশতা)ই জ্যোতি তা যার ওপর আপতিত হয় সে সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এই জ্যোতির প্রভাবেই কেউ সম্রাট হন ,সিংহাসন ও রাজমুকুট পরিধান করেন ,সব সময় জয়ী ও সমৃদ্ধ থাকেন ,ন্যায়বান হন। এই জ্যোতির শক্তিতেই কেউ আত্মিক পূর্ণতা লাভ করেন এবং খোদার পক্ষ থেকে নবী হিসেবে মনোনীত হন।
420 পৃষ্ঠায় বলেছেন ,
‘ আভেস্তার বর্ণনানুযায়ী (যামইয়াদিশত ,ধারা: 33 ও 40) তারা ‘ ফার ’ কে পাখি ও ঈগলের মত বলে মনে করত। ’
415 পৃষ্ঠায় এ অন্ধবিশ্বাসকে বুদ্ধিবৃত্তিক হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোরআনের ‘ সুলতান ’ শব্দকে ‘ ফার ’ শব্দের সমার্থক বলা হয়েছে অথচ ‘ সুলতান ’ শব্দটি কখনোই এই কুসংস্কারপূর্ণ ধারণার সমার্থক নয়। ‘ সুলতান ’ কোরআনে কখনো ‘ শক্তি ও ক্ষমতা ’ অর্থে ,কখনো ক্ষমতার উৎস ,কখনও ‘ হুজ্জাত ’ ও প্রমাণ অর্থে ,কখনো ‘ সুলতান ’ মানুষের ওপর শয়তানের আধিপত্য অর্থেও এসেছে। যেমনاِنّما سلْطانُهُ على الّذين يَتَولَّونَهُ ‘ তার আধিপত্য তো তাদের ওপরই চলে ,যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং অংশীদার মানে। ’ 134 কখনও কোন বিশেষ কর্মের ওপর মানুষের প্রভাব ও ক্ষমতা অর্থে এসেছে। যেমন:و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا ‘ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় ,আমি তার উত্তরাধিকারীকে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা দিয়েছি। ’ 135 এ অর্থের সাথে ইযাদির জ্যোতির কোন সম্পর্ক নেই যা কোন ব্যক্তির অন্তরে পতিত হওয়ার ফলে সম্রাট বা নবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং কখনও ভেড়া ,হরিণশাবক বা ঈগলের আকৃতি ধারণ করে এমন অস্তিত্ব ইসলামে নেই।
ডক্টর মুঈনের জন্য এটিই কি উত্তম ছিল না যে ,তিনি ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ লিখেই ক্ষান্ত হবেন এবং ‘ মাসদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে কোরআনী ’ নিয়ে কিছু লিখার চেষ্টা করবেন না ?
ডক্টর মুঈন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যারদুশত শুধু চেয়েছেন অগ্নিকে কেবলা করতে ,কিন্তু এর উপাসনায় উৎসাহিত করতে চান নি। যেমনটি কাবা মুসলমানদের নিকট কেবলা হিসেবে পরিগণিত ,অথচ যে কেউ এমনকি স্বয়ং তিনিও জানেন মুসলমানগণ নামাজের জন্য যখন কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান তখন কাবাকে সম্মান প্রদর্শন করা বা কাবা হতে শক্তি অর্জন করা বা ঐশী শক্তির অধিকারী হিসেবে তার সাহায্য কামনা কখনই তাদের লক্ষ্য নয় এবং তারা এরূপ বিশ্বাসও করে না ।
একজন মুসলমান নামাজের সময় সরাসরি আল্লাহর উদ্দেশে কথা বলেإياّك نَعْبُدُ و إياك نسْتعين ‘ একমাত্র আপনার ইবাদত করি ও আপনার কাছেই সাহায্য চাই। ’ মুসলমানদের নিকট কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ,ওযু করা ,পবিত্র কাপড় পরিধান ও সতর ঢাকার ন্যায়ই একটি বিষয়। অর্থাৎ এটি নামাজের নিয়ম (আদাব) ;নামাজের উদ্দেশ্য নয়। অথচ যারথুষ্ট্রগণ খোদ অগ্নির ঐশী প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে ইবাদাতের মাধ্যমে তার পবিত্রতা ও সম্মান ঘোষণা করে থাকে।
এর থেকেও দুঃখজনক ,তিনি তাঁর গ্রন্থের ‘ পুরোহিতগণের শরাব ’ নামক অধ্যায়ে পুর দাউদের অনুকরণে ইরানী কবিদের কবিতায় পুরোহিত ,শরাব ও এরূপ শব্দের ব্যবহারকে তাঁদের যারথুষ্ট্র আচার-নীতির প্রতি ভক্তি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এ অধ্যায়ের শেষে হাতেফ ইসফাহানির ‘ অস্তিত্বের একতা ’ (ওয়াহ্দাতে উজুদ) সম্পর্কিত একটি কবিতার পঙ্ক্তিমালা আনা হয়েছে যার প্রথম হলো এরূপ :
“ হে যার জন্য আমার জীবন ও অন্তর উৎসর্গীকৃত
যার পথে আমার এ দু ’ সত্তা নিবেদিত। ”
ডক্টর মুঈনের কাছে এ কবিতার যে অংশগুলো তাঁর (কবির) ইরানের প্রাচীন রীতির প্রতি ভালবাসার নিদর্শন বলে মনে হয়েছে সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন। যেমন এই বাক্যটি ‘ আমি এ মুসলমান হওয়ায় লজ্জিত ’ ।
ডক্টর মুঈন ভালভাবেই জানেন ,ইরফান ও সূফীধারার কবিগণ বাহ্যিক ধার্মিকতা ও মুসলমানিত্বের প্রকাশকে বিশেষ পরিভাষায় উপস্থাপন করে থাকেন। যেখানেই দুনিয়াত্যাগ বা কখনও কখনও মুসলমানিত্বকে তিরস্কার করেছেন সেখানেই এর উদ্দেশ্য মিথ্যা মুসলমানিত্ব ও দুনিয়াবিমুখতা। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মুসলমানিত্ব ও দুনিয়াবিমুখতার ভান করাকে তাঁরা নিন্দা করেছেন যা প্রকৃত ইসলাম ও মুসলমানিত্বের অন্তরায় ,এমনকি যে সকল বড় আলেম ইজতিহাদের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন এবং শরীয়তের মসনদে আরোহণ করে ফতোয়া দিতেন ,যেমন শেখ বাহায়ী136 (তিনি আরব তবে হিজরত করে ইরানে বসবাস শুরু করেন)।
হাজী মোল্লা মুহাম্মদ নারাকী137 ,মির্জা মোহাম্মদ তাকী সিরাজী ,হাজী মির্জা হাবিব রাযাভী খোরাসানী ,শেখ মুহাম্মদ হুসাইন ইসফাহানী এবং আল্লামা তাবাতাবায়ীর লেখাতেও এরূপ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এ সকল কবিতা হতে কিরূপে পুর দাউদ ও ড. মুঈনের দাবি প্রমাণিত হয় ?
এমনকি কবি হাতেফ ইসফাহানীর যে কবিতা হতে ডক্টর মুঈন এরূপ যুক্তি দিয়েছেন তারই পঙ্ক্তিমালায় কবি উল্লেখ করেছেন ,এরূপ শব্দের ইরফানী বা আধ্যাত্মিক অর্থ ভিন্ন এবং এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। তিনি বলেছেন ,
“ হাতেফ! মারেফাতের পীরদের কখনও ‘ মাতাল ’ ও ‘ হুশিয়ার ’ বলা হয়েছে
যেন দফ ,বীণা ,শরাব ,পেয়ালা তাঁদের শরাবখানায় সাজানো রয়েছে।
জেনে রাখ ,নর্তকী ,সাকীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রহস্য ও হেতু
ইশারায় তাঁরা বলতে চান যেন ভিন্ন কিছু। ”
এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করার পরও আমরা কিরূপে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে পারি ?
তদুপরি এই রূপক শব্দগুলো যারথুষ্ট্র পরিভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত মেই (বিশেষ মদ) ,মাগ (পুরোহিত) ও অগ্নিমন্দির শব্দগুলোর মধ্যেই সীমিত নয়। যদি তা হতো তবে আমরা বলতে পারতাম কেন ইরানী আরেফ ও সুফিগণ ইরফানী পরিভাষায় শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন ? যেহেতু তা নয় সেহেতু কি করে এগুলো তাঁদের প্রাচীন ধর্ম প্রীতির চিহ্ন হতে পারে ?
এ কবিগণ মূর্তি ,পাদ্রী ,মঠ ,ক্রশ ,দাবার গুটি ,জুয়ারী প্রভৃতি শব্দ ও পরিভাষা তাঁদের কবিতায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এগুলো তাঁদের মূর্তিপূজা ,খ্রিষ্টবাদ ও জুয়া খেলার প্রতি আসক্তির চিহ্ন বলতে হবে। কয়েক বছর পূর্বে একজন লেখক এমন চিন্তার ফাঁদে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ,হাফিযের নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ গজলটি তাঁর তীব্র জাতীয় চেতনার প্রমাণ। তিনি এর মাধ্যমে অতীতের স্মরণ করেছেন। যখন ইরানে ইসলামের আগমন ঘটেনি এবং পাহলভী ভাষা ইরানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও যারথুষ্ট্র ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল তখনকার কথা তিনি বলেছেন। গজলটি এভাবে শুরু হয়েছে :
“ বুলবুলি সারভের138 ডালে বসে পাহলভীতে গাইছে
যেন আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাই সে দিচ্ছে। ”
কবি এ কথার মাধ্যমে ইসলামপূর্ব ইরানের ধর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাই বলেছেন।
বস্তুবাদী চিন্তার লেখক ডক্টর আরানী তাঁর ‘ আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদী নীতি ’ শীর্ষক প্রবন্ধে এর জবাবে বলেছিলেন , “ যদি এমনটিই হয়ে থাকে তবে এর পরবর্তী কবিতায় যেখানে বলেছেন :
‘ অগ্নির সন্ধানে গিয়ে মূসা পেলেন সর্বোত্তম ধ্বনি
শুনতে পেলেন বৃক্ষ হতে তাওহীদের বাণী ’ -তা হাফিযের ইহুদীপ্রীতির আলামত। ”
আর এই গজলেই তিনি বলেছেন ,
“ এক আজব গল্প শোন এ ভাগ্য বিড়ম্বিত
থেকে ,ঈসায়ীদের বন্ধুত্বের কারণে তারা মোদের হত্যা করত। ”
এটিও তাঁর খ্রিষ্টপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে বলতে হবে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ,এ সকল শব্দের ইরফানী অর্থ রয়েছে এবং তা বক্তার বিশেষ কোন ধর্মের ,যেমন খ্রিষ্টান ,ইহুদী বা যারথুষ্ট্রের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ হতে পারে না। ইরফানী ধারার প্রসিদ্ধ কবি শামসুদ্দীন মাগরেবী (মৃত্যু নবম হিজরী শতাব্দী) এ ধরনের পরিভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন ,
“ লক্ষ্য কর এ সকল গজল ও কবিতায়
মাতাল ,মদ বিক্রেতা আর শুঁড়িখানার বিষয়-
মূর্তি ,ক্রস ,কটিবন্ধ ,জিকির ও তাসবীহ্ ,
সন্ন্যাসী-মঠ ,অগ্নিপূজক ,পাদ্রী আর ইহুদী
শরাব ,রূপসী ,মুসল্লির শয়ন কক্ষ আর বারান্দায়
জ্বলে প্রদীপ ,বীণা বাজে ,মাতালরা গান গায়।
প্রতিদ্বন্দ্বী ,সাকী ,জুয়াড়ী ,মুনাজাত
অরগানের সুর আর বাঁশীর আর্তনাদ।
মদ ,মদের দোকান ,মদ্যপায়ীদের আসর
পেয়ালার পর পেয়ালা পানে সকলে বিভোর।
পূর্ণ কর মদের পিপা ও শুঁড়িখানার পেয়ালা
শুরু হয়েছে শরাব পানের প্রতিযোগিতার পালা।
মসজিদ হতে পানশালার দিকে ধাবিত হওয়া
সেখানে কিছুক্ষণ শান্তি করে বিশ্রাম নেয়া।
নিজ পেয়ালাকে বন্ধক রেখে অপেক্ষা করা
দেহ-প্রাণ সবই মদের পায়ে উৎসর্গ করা।
পুষ্পোদ্যানে বসে মল্লিকার জন্য দিন গোনা
শিশির ,বৃষ্টি আর তুষারের কথা শোনা।
দেহের গড়ন ,উচ্চতা ,ভাঁজ ,ভ্রু ,তিলক
চেহারা ,মুখমণ্ডল ,বেণী ,গণ্ডদেশ ও চিবুক।
অধর ,চঞ্চল চোখ ,মাতাল নেশা
মাথা ,হাত ,পাঞ্জা ,পা আর মধ্যভাগ।
সাবধান! উত্তেজিত হয়ো না ,এ সব কথা থেকে
জেনে নাও এ সবের অর্থ জ্ঞানীদের হতে।
পরিভাষার বাহ্যিক অর্থে নিজেকে ফেল না গুলিয়ে
জ্ঞানীরা ইশারায় যা বোঝেন তার সাথে নাও মিলিয়ে।
যদি দৃষ্টিকে কর সুন্দর সবই সুন্দর লাগবে
খোসাকে অতিক্রম করে তার শাঁস দেখবে।
যদি না পার ফিরিয়ে রাখতে দৃষ্টি বাহ্যিকতা থেকে
কভু পারবে না তুমি রহস্যের অধিপতি হতে।
এর প্রতিটি শব্দের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে প্রাণ ,
প্রতিটি শব্দ যেন এক বিশ্ব ও জাহান।
দেহকে অতিক্রম করে প্রাণকে বোঝ ,
শব্দকে ভুলে গিয়ে নামকরণের রহস্য খোঁজ।
মুহূর্তকে নষ্ট না করে হও এর উপযোগী
যাতে হতে পার মহাসত্যের সহযোগী। ”
এ ছাড়া এরূপ পরিভাষা ফার্র্সীভাষী ইরানীদের বক্তব্যই শুধু নয় ,ভারতীয় ফার্সীভাষী ,আরবগণ ও আরবীভাষী আরেফগণের বক্তব্যেও লক্ষণীয়। যেমন মিশরীয় সুফী ইবনুল ফারেয মিসরী ও স্পেনীয় সুফী মুহিউদ্দীন আরাবী আন্দালুসীর বক্তব্যের পরিভাষা। তাই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ কথা বলতে পারেন না ,তাঁদের ব্যবহৃত শরাব ও এ জাতীয় পরিভাষা তাঁদের যারথুষ্ট্র মতবাদের প্রতি আসক্তির কারণে ছিল।
তদুপরি ঐশী জ্ঞান লাভ ,ইলহাম অর্জন ,আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টি ও খোদায়ী দিকনির্দেশনার মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হওয়ার ফলে আন্তরিক পরিতৃপ্তি লাভকে কোরআন ও নাহজুল বালাগায় কোথাও কোথাও শরাব বলে উল্লিখিত হয়েছে।
পবিত্র কোরআনের সূরা দাহারের 21 নং আয়াতে বলা হয়েছে :
) و سقاهم ربّهم شرابا طهورا (
‘ এবং তাদের পালনকর্তা তাদের পান করাবেন ‘ শরাবান তাহুরা ’ । ’ মুফাসসিরগণের মতে যদিও এর বাহ্যিক অর্থ অত্যন্ত পবিত্র পানীয় বা শরাব ,তদুপরি এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন কিছু তাদের দেয়া হবে যা সব কিছু থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করবে। নাহজুল বালাগাতেও ঐশী ব্যক্তিত্বদের এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:
و يغبقون كأس الحكمة بعد الصّبوح
‘ সকালের শরাবের পর তাদের রাতের প্রজ্ঞার শরার পান করানো হয়। ’ শাব্দিক অর্থেغبوق হলো রাতের শরাব এবংصبوح অর্থ সকালের শরাব। ডক্টর মুঈন এ ক্ষেত্রে কি বলবেন ? এ ক্ষেত্রেও কি বলা হবে বক্তাগণ যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণের শরাবেরই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন এবং এটি যারথুষ্ট্র আচার-নীতির প্রতি তাঁদের আসক্তির প্রমাণ ?
ডক্টর মুঈন তাঁর গ্রন্থের 13 পৃষ্ঠায় ঔদ্ধত্য সহকারে সার্জন ম্যালকমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন , ‘ আরব নবীর অনুসারীরা ইরানের শহরগুলোকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ,অগ্নিমন্দিরগুলোকে জ্বালিয়ে দেয় ,যারথুষ্ট্র ধর্মযাজকদের হত্যা করে ,গ্রন্থসমূহ ও এর সংরক্ষকদের নিশ্চিহ্ন করে ,পুরোহিতদের ‘ যাদুকর ’ বলে অভিহিত করে ও তাঁদের রক্ষিত গ্রন্থগুলোকে ‘ যাদুর গ্রন্থ ’ বলে প্রচার করেন। ’
ডক্টর মুঈন স্যার জন ম্যালকম অপেক্ষা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অধিকতর অবগত এবং তিনি ভালভাবেই জানেন এ কথাগুলো সার্জন ম্যালকমের নিজস্ব কথা এবং এগুলোর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। দুঃখের বিষয় তদুপরি তিনি ইরান ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অনবহিত যুবকদের ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার লক্ষ্যে এরূপ ব্যক্তির নিকট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
ডক্টর মুঈন তাঁর গ্রন্থের 22 পৃষ্ঠায় মুসলিম শাসনাধীনে যারথুষ্ট্রদের নির্যাতিত দেখানোর উদ্দেশ্যে বলেছেন ,
“ যে সকল মানুষ মাসদা ইয়াসনা ধর্মের ওপর বিদ্যমান থেকে এ দেশে বসবাস করত তাদেরকে বিজয়ী জাতি ও তাদের এ দেশীয় অনুসারীদের অনাকাক্সিক্ষত ও রুঢ় আচরণের শিকার হতে হয়েছিল। তারা সর্বদা তিরস্কার ,অপমান ও চাপের মুখে পিতৃধর্মকে গোপন করতে বাধ্য হতো। তাদের ধর্মীয় আচার-বিধি পালনের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদেরকে তিক্ত সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল। ‘ তারিখে সিস্তান ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন , ‘ যিয়াদ বিন আবিহ্ সিস্তান হতে রাবীকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি বাকরাহকে প্রেরণ করেন (51 হিজরী) ও নির্দেশ দেন সেখানে পৌঁছে সকল যারথুষ্ট্র পুরোহিতকে হত্যা করার ও তাদের অগ্নিমন্দিরগুলোকে জ্বালিয়ে দেবার। তিনি সেখানে পৌঁছলে সিস্তানের পুরোহিত ও সম্ভ্রান্তরা তাঁর বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিলেন। ’
ডক্টর মুঈন সেখানে ঘটনাটির এ পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন। এর উপসংহার টানেন নি। যারথুষ্ট্রগণ ধর্মীয় আচার পালনে স্বাধীন ছিল না ও তাদের পিতৃধর্মীয় বিশ্বাস গোপনে বাধ্য হতো তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে তিনি এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
তিনি তাঁর গ্রন্থের অপর একটি স্থানে (463 পৃষ্ঠায়) এ ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে বলেছেন ,সিস্তানের মুসলমানগণ এ নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও বলে এটি নবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতি বিরোধী ও ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। বিষয়টি সিরিয়ায় অবস্থানরত খলীফার নিকট জানানো হলে উত্তর আসে যারথুষ্ট্রগণ মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাই তাদের রক্ত ও সম্পদ সম্মানিত (পবিত্র) এবং কেউ তা হরণের অধিকার রাখে না।
ডক্টর মুঈন তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র (27 পৃষ্ঠায়) সিস্তানের এ ইতিহাসই বর্ণনা করে বলেছেন ,46 হিজরীতে (অর্থাৎ এ ঘটনার পাঁচ বছর পূর্বে) রাবী যখন সিস্তানে আসেন তখন এর অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচারণের নীতি গ্রহণ করেন ও মুসলমানদের কোরআন ,তাফসীর ও জ্ঞান শিক্ষায় বাধ্য করেন এবং ন্যায়বিচার কায়েম করেন। অনেক যারথুষ্ট্র তাঁর আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়।
হ্যাঁ ,বাস্তবে খোলাফায়ে রাশেদীন ও মুয়াবিয়ার আমলে রাবীয়ুল হারেসীর অধীনস্থ এলাকায় যারথুষ্ট্রদের অবস্থা এরূপই ছিল। তাই যখন যিয়াদ ইবনে আবিহ্ অত্যাচারের পথ গ্রহণ করে মুসলমানদের প্রতিবাদের মুখোমুখি হয় তখন তিনি মুয়াবিয়ার ন্যায় অত্যাচারী শাসক ও তাঁর গভর্ণরের বিপরীতে সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনে পত্র পাঠান।
তাই ইতিহাস হতে খণ্ডিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করার মাধ্যমে যারথুষ্ট্ররা ধর্মবিশ্বাসকে গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিল প্রচার করে এর জন্য ক্রন্দনের কি প্রয়োজন ?
আমরা উমাইয়্যাদের অত্যাচার-নির্যাতনকে অস্বীকার করছি না ,কিন্তু তা সাসানী সম্রাটদের অত্যাচার ও নির্যাতনের তুলনায় কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত উমাইয়্যাগণ তাদের তরবারীর ধারালো অংশটি হযরত আলী (আ.)-এর বংশধর ও অনুসারীদের প্রতিই উত্তোলন করে রেখেছিল। কারণ তাঁদের নিজ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। সুতরাং অবশ্যই যারথুষ্ট্ররা নবীর আহলে বাইত অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় ছিল।
অবশ্য উমাইয়্যাদের রাজনীতি জাতিভিত্তিক ছিল বিধায় তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল আরবীয় ;ইসলামী নয়। তাই তারা আরব-অনারবের মধ্যে পার্থক্য করত ,এমনকি তারা একজন আরব ও অনারব মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের নীতি গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ ধর্ম কোন বিষয়ই ছিল না। তাই যারথুষ্ট্ররা ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীর সাধারণ শর্তানুসারে পূর্ণ নিরাপত্তাসহই জীবন যাপন করত।
যারথুষ্ট্ররা আব্বাসীয় শাসনামলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। তারা আহলে বাইতের ইমাম ও মুসলিম আলেমগণের সঙ্গে ইসলাম ও যারথুষ্ট্র ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক করত। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে ,যারথুষ্ট্র ধর্ম হতে অধিকাংশ ইরানীদের ইসলামে প্রবেশ ও অগ্নিমন্দিরসমূহ ধ্বংস করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা আরবদের শাসনামলের অবসানের পর ইরানী আর্য শাসনামলেই ঘটেছিল। কয়েক জন মধ্যপ্রাচ্যবিদের রচিত গ্রন্থ ‘ তামাদ্দুনে ইরানী ’ তে পি. জে. দুমানাশেহ ‘ যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রতিরোধ ও অনুবর্তন ’ নামক নিবন্ধে বলেছেন ,
“ আরবদের হাতে সাসানী সাম্রাজ্যের পতন ও পরাজয় ইরানী মানসিকতার হৃৎস্পন্দনকে স্তব্ধ করতে পারে নি এবং যারথুষ্ট্র ধর্মও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নি ;বরং ইরানীরা প্রশিক্ষিত ও পরিশোধিত এক সভ্যতা ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং ইসলাম ধর্ম এতে নতুন জীবন সঞ্চার করেছিল।
...ইরান এক দফায় মুসলমান হয় নি এবং এর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে নি। যারথুষ্ট্র ধর্ম এর বিপরীতে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা উপেক্ষা করার মত নয়। ”
পি.জে. দুমানাশেহ বলেন , “ মুসলমানরা মাজুসীদের আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করত। ” তিনি বলেন ,
“ আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ (এ বিষয়ে আমাদের প্রধান উৎস) উল্লেখ করেছেন তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত ইরানের বিভিন্ন শহরে অগ্নিমন্দিরসমূহ ছিল । যদি অগ্নিমন্দিরসমূহ থেকে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেখানে যারথুষ্ট্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিতগণ ছিলেন ও তাঁরা এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখতেন। তা ছাড়া যারথুষ্ট্রদের জীবনধারা অনুযায়ী অবশ্যই ধর্মীয় বিধিবিধান ও মৌলনীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষিত লোকগণ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং যারথুষ্ট্র ধর্মে শ্রেণীবিভেদ বিদ্যমান ছিল ও এই শ্রেণী বৈষম্যের বিষয়টি সংখ্যালঘু যারথুষ্ট্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করত যে ,এ দু ’ ধর্মের কোন্টি গ্রহণ করবে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যারথুষ্ট্র পণ্ডিতগণ জ্ঞানগত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ” 139
সমাজ ব্যবস্থা
ইরানে ইসলামের প্রভাব ও অবদানকে মূল্যায়নের জন্য যে সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলাম পরিবর্তিত করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তার পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
সাসানী আমলের ইরান শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ছিল। শ্রেণীভেদের বিষয়টি কঠোরভাবে সেখানে আরোপিত হতো। অবশ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সাসানীদের উদ্ভূত বিষয় নয় ;বরং হাখামানেশী ও আশকানী আমলেও তা বিদ্যমান ছিল। তবে সাসানীরা তা নবায়ন ও শক্তিশালী করেছিল।
মাসউদী তাঁর ‘ মুরুজুয যাহাব ’ গ্রন্থের 152 পৃষ্ঠায় বলেছেন , “ আরদ্শির ইবনে বাবাক সাসানী জনসাধারণকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। ”
তিনি তাঁর ‘ তাম্বীহ্ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থের 76 পৃষ্ঠায় লিখেছেন ,
“ তাই কাভে যিনি একজন সাধারণ কামার ছিলেন তাঁর পোশাককে পতাকা ও ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করে অত্যাচারী সম্রাট জাহাকের পতন ঘটাতে পেরেছিলেন। আরদ্শির তাঁর এক প্রসিদ্ধ বক্তব্যে তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর পক্ষ হতে বিপদের আশঙ্কা থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ”
কামিলে ইবনে আসিরে এসেছে :
যখন মুসলমান ও পারস্যের (ইরানের) বাহিনী কাদেসিয়ায় পরস্পরের মুখোমুখি হলো তখন পারস্য সেনাপতি ফারাখযাদ মুসলিম সেনাদলের অগ্রগামী দলের নেতা যিনি প্রাথমিক সেনাদল নিয়ে সেখানে ক্যাম্প করেছিলেন তাঁকে ডেকে পাঠান। তাঁর এ কর্মের উদ্দেশ্য ছিল সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টির ফয়সালা করা যাতে যুদ্ধের বিষয়টি অবধারিত না হয়। তিনি অগ্রদলের সেনাপতি যোহরা ইবনে আবদুল্লাহ্কে বলেন , “ তোমরা আবররা আমাদের প্রতিবেশী এবং আমরা তোমাদের প্রতি সদাচরণ করেছি ,শত্রু হতে রক্ষা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। ” যোহরা ইবনে আবদুল্লাহ্ বললেন , “ তুমি যে আরবদের কথা বলছ তার সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও আমাদের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের ভূমিতে পদার্পণ করত। আর আমরা আখেরাতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। তুমি যা বলেছ আমরা সেরূপই ছিলাম ,তবে আল্লাহ্ আমাদের মধ্য হতে একজনকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং আমরা তাঁর আহ্বানকে গ্রহণ করেছি। তিনি আমাদের নিশ্চিত করেছেন ,যে এ ধর্ম গ্রহণ না করবে সে হীন ও লাঞ্ছিত হবে এবং যে তা গ্রহণ করবে সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। ” রুস্তম বলেন , “ তোমাদের ধর্মকে আমার নিকট বর্ণনা কর। ” যোহরা বলেন , “ আমাদের ধর্মের ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি। ” রুস্তম বলেন , “ সুন্দর! তাতে আর কি রয়েছে ? ” যোহরা বললেন , “ আল্লাহর বান্দাদের মানুষের দাসত্ব হতে মুক্তি দেয়া যাতে তারা আল্লাহর বান্দা হয় ,মানুষের বান্দা নয়। ” তিনি বললেন , “ আর কি ? ” যোহরা বললেন , “ সকল মানুষ এক পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) হতে সৃষ্ট হয়েছে এবং তারা সকলেই সমান। ” তিনি বললেন , “ এও সুন্দর! ” অতঃপর রুস্তম বললেন , “ যদি এগুলো মেনে নিই তাহলে তোমরা কি করবে ? ফিরে যেতে রাজী আছ ? ” যোহরা বললেন , “ আল্লাহর শপথ ,অবশ্যই এবং ব্যবসার প্রয়োজন ব্যতিরেকে তোমাদের শহরগুলোর নিকটবর্তী হওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না। ” রুস্তম বললেন , “ তোমার কথাকে সত্যায়ন করছি ,কিন্তু দুঃখজনক হলো আরদ্শিরের সময়কাল হতে এ রীতি চালু হয়েছে ,নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উচ্চ শ্রেণীর কাজ করতে দেয়া হবে না। কারণ যদি তারা নিজেদের পরিসরের বাইরে পা ফেলে তাহলে উচ্চ শ্রেণীর কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। ” যোহরা ইবনে আবদুল্লাহ্ বললেন , “ সুতরাং সাধারণ মানুষদের জন্য আমরা সবার চেয়ে উত্তম। আমরা কখনই নিম্ন শ্রেণীর প্রতি এরূপ আচরণ করতে পারব না। আমরা নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করব যদি তারা আমাদের বিষয়ে তাঁর নির্দেশ পালন নাও করে। ” 140
পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞগণ গ্রীক ,রোমান ,সিরীয় ,আর্মেনীয় ও আরবী ভাষার ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও যেহেতু খনন কার্য হতে উদ্ঘাটিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীও কাজে লাগিয়েছেন সেহেতু আরো উত্তমরূপে ইরানের শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীনত্বকে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। ক্রিস্টেন সেন এ উৎসসমূহের সবগুলোকেই ব্যবহার করেছেন এবং সাসানী আমলের ইরান নিয়ে ত্রিশ বছর কাজ করেছেন। সম্ভবত অন্য কেউ এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ নন। তিনি ইরানের শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নিয়ে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
ক্রিস্টেন সেন দাবি করেছেন ,মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সাসানী আমলের উচ্চ শ্রেণীর যে বিভিন্ন নামকরণ করেছেন যেমন ‘ আল উযমা ’ ,আহুলুল বুয়ুতাত ’ ও ‘ আল আশরাফ ’ তা যথাক্রমে পাহলভী ভাষার ‘ ওয়াসপুহ্রান ’ , ‘ আযাযন ’ এবং ‘ বুযুর্গান ’ শব্দের অনুবাদ।
আমরা সাসানী আমলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ক্রিস্টেন সেন ও অন্যদের নিকট থেকে উদ্ধৃতি দেব। ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে ‘ মাযদাকী ’ শীর্ষক আলোচনার ভূমিকায় ইরানের সামাজিক আইনের বিষয়ে বলেছেন ,
‘ ইরানের সমাজ দু ’ টি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যথা: মালিকানা ও বংশ। তানসুরের পত্রানুযায়ী অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের থেকে নিম্ন শ্রেণীকে কঠোর আইন দ্বারা পৃথক করা হতো। তারা পোশাক ,বাহন ,বাসস্থান ,স্ত্রী ,সেবক ও বাগানের অধিকারী ছিল... তদুপরি বিভিন্ন শ্রেণী সামাজিকভাবে বিভিন্ন অবস্থান লাভ করেছিল এবং প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সাসানী আমলের কঠোর আইনের একটি হলো কেউ তার ওপরের পর্যায়ের কোন শ্রেণীর বলে দাবি করতে পারবে না।... রাষ্ট্রীয় আইন বংশসমূহের রক্তের বিশুদ্ধতা ও স্থাবর সম্পদের নিরাপত্তাকবচ ছিল। ‘ ফার্সনামা ’ তে সম্ভবত সাসানী আমলের ‘ নামাগ আইন ’ হতে বর্ণনা করা হয়েছে: ‘ পারস্য সাম্রাজ্যের নীতি ছিল তার পাশ্ববর্তী রোম ,তুরস্ক ,চীন ও ভারতের নারীদের বিবাহ করা যাবে ,কিন্তু তাদের নিকট কন্যা দান করা যাবে না। পারস্য নারীদের স্ববংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের নাম বিশেষ দফতরে নথিবদ্ধ করা হতো ও রাষ্ট্র তার হেফাজত করত। সাধারণ লোকদের অভিজাতদের সম্পদ ক্রয়ের অধিকার ছিল না। এরূপ আইনসমূহের কারণে কোন কোন সম্ভ্রান্ত বংশ কয়েক প্রজন্ম পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল... সাধারণ শ্রেণীর মাঝেও লক্ষণীয় পার্থক্য সৃষ্ট হতো। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল এবং কেউ খোদাপ্রদত্ত ধারার বাইরে অন্য পেশায় নিয়োজিত হতে পারত না। ’
সাঈদ নাফিসী বলেছেন ,
‘ ধর্মমতগত পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও যে বিষয়টি মানুষের মধ্যে কপট চিন্তার জন্ম দিয়েছিল তা হলো সাসানীদের শ্রেণী বৈষম্যমূলক কঠোর নীতি যার মূল ইরানের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে নিহিত ছিল। সাসানী আমলে তা আরো প্রকট করে তোলা হয়। প্রথম ধাপে সাতটি অভিজাত পরিবারের স্থান ছিল ,পরবর্তী ধাপে পাঁচটি বিশেষ পরিবারের অবস্থান নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু ’ গ্রুপের বিশেষ অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। মালিকানা প্রথম ধাপের সাত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাসানী সাম্রাজ্য একদিকে জাইহুন নদী হতে ককেশাস পর্বত ও ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল ও সেখানে প্রায় 14 কোটি মানুষ বসবাস করত। যদি এই সাত পরিবারের (বংশের) প্রতিটির সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ ধরে নিই তবে সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত লক্ষ। যদি সৈনিক ,সীমান্ত রক্ষী ও কৃষকদের একাংশেরও মালিকানার অধিকার ছিল ধরে নিই তাহলেও তাদের সংখ্যা সাত লক্ষের অধিক ছিল না। তাই বলা যায় এ চৌদ্দ কোটি অধিবাসীর মধ্যে 14 লক্ষ লোক সম্পত্তির অধিকারী ছিল। বাকী সকলেই খোদাপ্রদত্ত এ অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। এ ক্ষেত্রে যে কোন নতুন ধর্ম এই বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করত ,কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিত এবং শ্রেণী সুবিধার বিলুপ্তি ঘটাত সে ধর্মের প্রতি মানুষ উদ্দীপনা ও চরম আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ত। ’
ফেরদৌসীর শাহনামার সকল উৎস হলো ইরানী ও যারথুষ্ট্র চিন্তা। এতে একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যাতে স্পষ্টরূপে তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত ও শ্রেণী শৃংখলে আবদ্ধ সমাজের আশ্চর্য চিত্র ফুটে উঠেছে। তাতে দেখা যায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার শুধু বিশেষ শ্রেণীর জন্য ছিল।
বর্ণিত হয়েছে রোম সম্রাট ও পারস্য অধিপতি অনুশিরওয়ানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে রোম সম্রাট আনুশিরওয়ানের অধীনে শামাত অঞ্চলে সেনা অভিযান চালায়। ইরানী সেনাবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে ইরানের কোষাগার শূন্য হয়ে পড়ে। অনুশিরওয়ান তাঁর পরামর্শদাতা বুজার জামহারের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করার। একদল ব্যবসায়ীকে দাওয়াত করা হলো যাঁদের মধ্যে একজন চামড়ার মোজা ব্যবসায়ীও ছিলেন। যেহেতু তিনি চর্মকার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেহেতু নিম্ন শ্রেণীর বলে বিবেচিত ছিলেন। তিনি বললেন , ‘ আমি পূর্ণ ঋণ এক সাথে দিতে রাজী আছি যদি আমার একমাত্র শিশু সন্তানকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষকের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। ’ কিন্তু এটি সে সময়ের নীতি বিরোধী হওয়ায় তাঁকে এ অনুমতি দেয়া হয়নি।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া বৈধ ছিল ন। কিন্তু কখনও কখনও ব্যতিক্রম দেখা যেত। যখন প্রজা গোষ্ঠীর কোন এক সদস্য বিশেষ কোন যোগ্যতা বা শিল্প প্রতিভা প্রদর্শন করত তখন তা সম্রাটের নিকট উপস্থাপন করা হতো। অতঃপর পুরোহিতগণের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি তাঁরা তাকে এর যোগ্য মনে করেন তবে সে ঐ শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অনুমতি পেত।... শহরের অধিবাসীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল যদিও তারা গ্রামের অধিবাসীদের মত মাথাপিছু কর প্রদান করত। কিন্তু তারা সামরিক কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করত। তারা ব্যবসায় ও শিল্পের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হতো ও সামাজিক অবস্থান লাভ করত। কিন্তু সাধারণ প্রজাদের অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল। তারা সারা জীবন এক স্থানে বসবাসে বাধ্য ছিল ও তাদের সামরিক বাহিনীতে বেকার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হতো। অমিউনুস মরসিলিনিউসের বর্ণনানুসারে গ্রামসমূহ হতে দলে দলে লোকেরা পদব্রজে সেনাদলে যোগ দিতে যেত যেন তারা চির দাসত্ব অর্জন করেছিল। কোন অবস্থাতেই তাদের পারিশ্রমিক বা পুরস্কার দেয়া হতো না।
... সম্ভ্রান্তদের অধীনে যে সকল প্রজা বাস করত তাদের অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য আমি পাই নি। অমিউনুসের মতে সম্ভ্রান্তগণ নিজেদের প্রজা ও দাসদের জীবনের মালিক বলে মনে করত। এ ক্ষেত্রে প্রজা ও দাসদের অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না।... এতদ্সত্ত্বেও যারথুষ্ট্র ধর্মে কৃষি কাজের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ বাড়াবাড়িও করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের অধিকার-আইন যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে প্রণীত হয়েছিল। আভেস্তার কয়েকটি খণ্ড ও অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে। ” 141
তিনি আরো বলেন ,
“ ইরানের সমাজ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থের উৎসসমূহে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় যদিও তা অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত ,তদুপরি তা আমাদের এমন এক সমাজের সঙ্গে পরিচিত করায় যার অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ও সত্তাগত শক্তি অভিজাতদের মধ্যে বিদ্যমান প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। রক্ত ,বংশ ও সম্পদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আইন তৈরি করা হয়েছিল এবং এ পন্থায় শ্রেণীশ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের বিষয়টি সর্বোত্তমভাবে রক্ষার চেষ্টা করেছিল...। ” 142
ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগত কঠোর শোষণের চিত্র ও উদাহরণ তুলে ধরেছেন। দ্য মযিল ‘ প্রাচীন ইরানের সামাজিক শ্রেণীসমূহ ’ শিরোনামের প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় পণ্ডিত হওয়ার মধ্যকার সম্পর্কটি একটি বিশেষ সম্পর্ক। সাঈদ নাফিসী বলেছেন ,
“ সে যুগে পুরোহিতগণ ইরানী সমাজের সকল শ্রেণীর ওপর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। পুরোহিতগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথমত ধর্মযাজক শ্রেণী... ধর্মযাজকদের প্রধানকে ‘ মুবাদে মুবাদন ’ বলা হতো। তিনি শাসনকেন্দ্রে অবস্থান করতেন ও রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর ক্ষমতা কোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না... মুবাদনদের পরে অবস্থান ছিল ধর্মীয় শিক্ষক ‘ হিরাবদন ’ দের যাঁরা বিচার কার্য ও তাঁদের নিকট প্রেরিত সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করতেন। তৎকালীন সময়ে কেবল ধর্মীয় পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষার অধিকার ছিল। অন্যান্য ইরানী এ অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। ‘ হিরাবদন ’ দের পরে অবস্থান ছিল অগ্নিরক্ষক বা ‘ অযারাবদন ’ দের। তাঁরা অগ্নিমন্দিরের অগ্নিসমূহের খাদেম ও মুতাওয়াল্লী হিসেবে কাজ করতেন। তাঁরা অগ্নিমন্দির সমূহের সংরক্ষণ ,অগ্নিমন্দিরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ,যেমন নামায ,দোয়া ,শিশুদের বাজুবন্ধনী বাঁধা ,বিবাহ ,মৃতদের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করতেন। ” 143
ইরানের সামাজিক ব্যবস্থার একটি সাসানী শাসকবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাসানী শাষক গোষ্ঠী স্বৈরাচারী ছিল। তারা নিজেদেরকে স্বর্গীয় বংশধারার ও খোদার প্রকাশস্থল বলে মনে করত। তাই সাধারণ মানুষের নিকট হতে সিজদা অপেক্ষা নিম্নতর আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিল না এবং তারাও এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন সামাজিক অবস্থাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ইচ্ছুকগণ এডওয়ার্ড ব্রাউনের ‘ তারিখে আদাবিয়াত ’ (আলী পাশা সালেহ কর্তৃক অনূদিত) ,কয়েকজন মধ্যপ্রাচ্যবিদ রচিত ‘ তামাদ্দুনে ইরানী (ডক্টর বাহনাম অনূদিত) ,সাঈদ নাফিসীর ‘ তারিখে ইজতেমায়ীয়ে ইরান এবং দিনেমার (ডেনিস) লেখক ক্রিস্টেন সেনের ‘ ইরান দার যামানে সাসানীয়ান (রশিদ ইয়ামেনী অনূদিত) বইটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন।
আমরা এখানে এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন দেখছি না। আমাদের আলোচনার বিষয় ‘ ইসলামে ইরানের অবদান ’ অংশে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা রাখব।
পারিবারিক ব্যবস্থা
সাসানী আমলের সামাজিক যে দিকটি পুরোহিতগণ কর্তৃক সবচেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ ,বিবর্তন ও ব্যবচ্ছেদের শিকার হয়েছিল তা ব্যক্তিগত অধিকার। বিশেষত বিবাহ ও উত্তরাধিকারের বিধানসমূহ এতটা জটিল ও অস্পস্ট ছিল ,তারা যা খুশি তাই করত। কোন ধর্মেই পুরোহিতদের এ বিষয়ে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।
একাধিক স্ত্রীর বিষয়টি সাসানী আমলে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। যদিও সম্প্রতি যারথুষ্ট্ররা এটি অস্বীকার করতে চায় ,কিন্তু অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ সকল ঐতিহাসিকই তা লিখেছেন-হাখামানেশী শাসনামল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরুডুট ও ইসতারাবুন হতে ক্রিস্টেন সেন পর্যন্ত সকলেই। হিরোডেটাস হাখামানেশী আমলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে বলেছেন ,
‘ তাদের প্রত্যেকেরই কয়েকজন স্ত্রী ছিল। এর বাইরে বিবাহ বন্ধনবহির্ভূত নারীর সংখ্যা আরো অধিক ছিল। ’
এদের সম্পর্কে ইসতারাবুন বলেছেন ,
“ তারা বহু স্ত্রী গ্রহণ করত এবং বিবাহ বহির্ভূত নারীর সংখ্যাও তাদের অনেক ছিল। ”
আশকানী শাসনামলের ঐতিহাসিক জুসতেন সে সময় সম্পর্কে বলেন ,
“ বিবাহ বহির্ভূত নারী রাখা বিশেষত শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে শহুরে জীবনে ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী হওয়ার সময় হতে প্রচলন লাভ করে। কারণ যাযাবর জীবনে অধিক স্ত্রী রাখা সম্ভব ছিল না। ”
প্রাচীন ইরানের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যা প্রচলিত ছিল তা কয়েকজন স্ত্রী রাখার মতো বিষয় হতে অনেক ব্যাপক ছিল অর্থাৎ এর কোন সীমা ছিল না। সংসার ক্ষেত্রে যেমন সাম্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রেও তেমনি নারীদের মধ্যে কোন সমতা রক্ষা করা হতো না। সামাজিক জীবনে যেরূপ চরম বৈষম্য ও শ্রেণীবিভক্তি লক্ষণীয় ছিল সেরূপ পারিবারিক ক্ষেত্রেও।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ কয়েকজন স্ত্রী রাখা পরিবারিক গঠনের অন্যতম শর্ত বলে বিবেচিত ছিল। একজন ব্যক্তির কতজন স্ত্রী থাকবে এ বিষয়টি ব্যক্তির আর্থিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করত। সম্ভবত আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তির একের অধিক স্ত্রী ছিল না। পরিবারের প্রধান অভিজাত শ্রেণীর প্রধান হওয়ার অধিকার রাখত। পরিবারে একজন নারী প্রধান স্ত্রী বা ‘ পদশা যান ’ বলে স্বীকৃতি পেত। সম্মানিতা স্ত্রী হিসেবে তার পূর্ণ অধিকার ছিল। তার থেকে নিম্ন পর্যায়ে সেবিকা নারী থাকত যাদের ‘ খেদমতকার ’ বা ‘ চাকর যান ’ বলা হতো। এ দু ’ ধরনের স্ত্রীর জন্য আইনগত অধিকার ছিল।...
প্রধান স্ত্রীকে সারা জীবন ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর কর্তব্য বলে বিবেচিত ছিল। পুত্ররা প্রাপ্তবয়স্ক এবং কন্যারা বিবাহযোগ্যা হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ অধিকার পেত। এর বিপরীতে খেদমতকার স্ত্রীদের শুধু পুত্র সন্তান পিতার বলে গৃহীত হতো। ফার্সী গ্রন্থসমূহে যদিও পাঁচ ধরনের বিবাহের কথা বলা হয়েছে ,কিন্তু সম্ভবত সাসানী আমলে উপরোক্ত দু ’ ধরনের বিবাহ ব্যতীত অন্যরূপ বিবাহ ছিল না।
কন্যা সন্তান স্বামীর পূর্ণ অধিকারে থাকত না ;বরং বিবাহের পরও কন্যার ওপর পিতার পূর্ণ অধিকার ছিল। যদি পিতা জীবিত না থাকত তাহলে অন্য কারো ওপর বিবাহ দানের অধিকার বর্তাতো। প্রথমত মা এ অধিকার লাভ করত। যদি মাতাও জীবিত না থাকত তাহলে কোন চাচা বা মামা এ অধিকারপ্রাপ্ত হতো।
স্বামী স্ত্রীর সম্পদের ওপর পূর্ণ অধিকার রাখত। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তার সম্পদ ব্যয় করতে পারত না। বিবাহ আইনে একমাত্র স্বামীর আইনগত ব্যক্তি অধিকার ছিল। সে স্ত্রীকে তার সম্পদে আইনগত সনদের ভিত্তিতে অংশীদার করতে পারত। এভাবে স্ত্রী স্বামীর অধিকার লাভ করত ও তা হতে ব্যয় করতে পারত। কেবল এ পদ্ধতিতেই স্ত্রী তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনের অধিকারপ্রাপ্ত হতো।
কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে বলত , ‘ এখন থেকে তুমি নিজের ওপর অধিকার প্রাপ্ত ’ তাহলে স্ত্রী সে স্বামী হতে বিতাড়িত হতো না তবে স্বাধীনভাবে ‘ চাকর যান ’ হিসেবে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারত। প্রথম স্বামীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় স্বামী থেকে কোন সন্তান তার গর্ভে আসলে তা প্রথম স্বামীর বলে পরিগণিত হতো এবং সেও প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই থাকত।
স্বামী তার একমাত্র স্ত্রী বা কোন স্ত্রীকে (যদি প্রথম স্ত্রীও হয়ে থাকে) কোন অপরাধ ছাড়াই অন্য পুরুষের নিকট সমর্পণ করার অধিকার রাখত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামত শর্ত ছিল না। দ্বিতীয় স্বামী এই নারীর সম্পদে কোন অধিকার রাখত না এবং তাদের সন্তান প্রথম স্বামীর সন্তান বলে বিবেচিত হতো...। এ ধরনের কাজকে তারা সৎ কর্ম বলে মনে করত ও স্বধর্মী দরিদ্রদের প্রতি এক প্রকার অনুগ্রহ ও সাহায্য বলে বিশ্বাস করত।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ সাসানী ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের অন্যতম বিশেষ বিধান ছিল প্রতিস্থাপন বিবাহ। তানসুর তাঁর পত্রে এর উল্লেখ করেছেন এবং আল বিরুনী তাঁর ‘ আল হিন্দ ’ গ্রন্থে ইবনুল মুকাফ্ফার সূত্রে এর বিবরণ দিয়েছেন। বিষয়টি এরূপ যে ,যাতে করে বংশের নাম টিকে থাকে ও মালিকানার অধিকার প্রাপ্ত পরিবারসমূহের সম্পদের মালিকানা হাতছাড়া না হয় ও অন্যের হাতে হস্তান্তরিত না হয় সেজন্য কোন ব্যক্তি ,পুত্র সন্তান ব্যতিরেকে মারা গেলে তার জন্য ‘ প্রতিস্থাপন ’ বা ‘ বদল ’ বিবাহের ব্যবস্থা করত। এ বিবাহের নিয়ম ছিল তার নামে তার স্ত্রীকে ঐ ব্যক্তির নিকটতম কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ দান। যদি স্ত্রী জীবিত না থাকে তার কন্যা বা অন্য কোন নিকটতম নারীকে তার নামে নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ দান। যদি তার নিকট সম্পর্কীয় কোন নারী না থাকে তাহলে অন্য কোন নারীকে তার সম্পদ হতে যৌতুক দান করে তার নামে নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ দান। এই বিবাহ হতে যে পুত্র সন্তান জন্ম নেবে সে ঐ মৃত ব্যক্তির পুত্র হিসেবে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। যে ব্যক্তি এরূপ কর্মে রাজী না হবে সে যেন অনেক ব্যক্তির হত্যার ন্যায় অপরাধ করল। কারণ সে মৃত ব্যক্তির বংশধারাকে কর্তন করেছে ও তার নাম মুছে ফেলার ব্যবস্থা করেছে।
উত্তরাধিকার আইন এরূপ ছিল: প্রধান স্ত্রী ও তার পুত্ররা সমান সম্পত্তি পেত। অবিবাহিত কন্যারা তাদের অর্ধেক ভাগ পেত। খেদমতকার স্ত্রী ও তার সন্তানরা কোন সম্পত্তি পেত না। তবে পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাদের কিছু ওসিয়ত বা হিবা করে যেতে পারত। ক্রিস্টেন সেন উল্লেখ করেছেন ,বংশধারার বিলুপ্তি প্রতিরোধে পোষ্যপুত্র গ্রহণের নীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় তার উল্লেখ করছি না।
পারিবারিক আইনের বিধিবিধান বংশ ও সম্পত্তি এ দু ’ টিকে রক্ষার চিন্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো অর্থাৎ বংশ ও সম্পত্তিই পারিবারিক আইনের মানদণ্ড ছিল ।
মাহরামদের144 সঙ্গে বিবাহের যে রীতি সে সময় ও তার পূর্ব হতে প্রচলন লাভ করেছিল এ দু ’ মৌল নীতির ভিত্তিতেই। অভিজাতরা ভিন্ন রক্তের মিশ্রণ প্রতিরোধ ও সম্পদ অন্যের হাতে চলে যাওয়া হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব নিকট সম্পর্কিত কাউকে বিবাহ করত। যেহেতু এ বিষয়টি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি বিরোধী সেহেতু ধর্মীয়ভাবে ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহিত করে এরূপ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হতো। যেমন বলা হতো ,যে এরূপ বিবাহ করে তার স্থান বেহেশতে এবং যে তা না করে তার স্থান দোযখে।
‘ আবদারে ভিরফ নামেহ্ ’ নামক যে গ্রন্থটি প্রথম খসরু অনুশিরওয়ানের আমলের নিক শাপুর নামের একজন পণ্ডিতের বলে উল্লিখিত হয়েছে তাতে আত্মার পরিভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ‘ ভিরেফ ’ দ্বিতীয় আসমানে এমন ব্যক্তিদের আত্মাকে দেখেছেন যারা মাহরামদের বিবাহ করার কারণে চিরতরে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং দোযখে চিরস্থায়ী আজাবের নারীদের দেখেছে যারা মাহরামদের বিবাহ করতে অস্বীকার করেছিল। শেষে উল্লিখিত হয়েছে ,ভিরফ স্বয়ং তাঁর সাত ভগ্নিকে বিবাহ করার কারণে এই ঐশী ভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ‘ দিনকারত ’ নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ ধরনের বিবাহের জন্য ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
আর তা হলো ‘ নিকট বিবাহ ’ অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ। সেখানে পিতা-কন্যা এবং ভ্রাতা-ভগ্নির বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নওসায়ে বুরযমেহের নামের এক যারথুষ্ট্র পুরোহিত দিনকারদের এই অংশের ব্যাখ্যায় এরূপ বিবাহের বিভিন্ন কল্যাণকর দিক উল্লেখ করে বলেছেন ,নিকট বিবাহ যন্ত্রণাদায়ক গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ রক্ত-বংশের বিশুদ্ধতা ইরানী সমাজে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ,তারা মাহরামদের সঙ্গে বিবাহকে বৈধ মনে করত। এ ধরনের বিবাহকে আভেস্তায় ‘ খুইযোগাদস ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই রীতি হাখামানেশী আমল হতেই প্রচলিত ছিল। যদিও ‘ খুইযোগাদস ’ বা ‘ খাওয়ায়েত ওয়াদাস ’ শব্দটিকে বর্তমানের আভেস্তায় ব্যাখ্যা করা হয় নি ,কিন্তু প্রাচীন আভেস্তায় এটি মাহরামদের সঙ্গে বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হতো। ”
যারথুষ্ট্রগণ বিশেষত ভারতের পারসিকরা সাম্প্রতিক সময়ে বিষয়টির অপকৃষ্টতা অনুভব করে ত্যাগ করেছে। তাদের কেউ কেউ গোঁড়া হতেই বিষয়টিকে যারথুষ্ট্র ধর্মের অন্যতম রীতি হিসেবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। তারা এখন ‘ খাওয়ায়েত ওয়াদাস ’ শব্দটির ভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা দান করেছেন।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ যারথুষ্ট্র সূত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাসানী আমলের অ-ইরানী ঐতিহাসিকদের বিবরণ হতে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে ,বর্তমানের ইরানীরা যারথুষ্ট্র ধর্মে মাহরাম বিবাহের বিষয়টিকে অস্বীকারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা প্রমাণযোগ্য নয়। ”
সাঈদ নাফিসী বলেছেন ,
“ তৎকালীন সময়ের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ হতে প্রমাণিত ,তাদের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মাহরামদের বিবাহ অবশ্যই প্রচলিত ছিল ,যদিও বর্তমানে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত তা অস্বীকারের চেষ্টা করছে। ”
সাঈদ নাফিসী অতঃপর যারথুষ্ট্র ধর্মের পবিত্র কিছু গ্রন্থ ,যেমন দিনকারত এবং মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ,যথা মাসউদী ,আবু হাইয়ান তাওহীদী ,আবু আলী ইবনে মাসকুইয়া প্রমুখের বর্ণনা হতে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি সাসানী সম্রাট কাবাদের সঙ্গে তাঁর কন্যা অথবা ভাগিনীর বিবাহ ,বাহরামের সঙ্গে তাঁর সহোদরা ভগ্নির বিবাহ ,মেহরান গুশনাসবের সঙ্গে তাঁর আপন ভগ্নির বিবাহের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন।
মাশিরুদ্দৌলা তাঁর ‘ ইরানে বসতন ’ নামক আকর্ষণীয় গ্রন্থে গ্রীক ঐতিহাসিক ইসতারা বুনের সূত্রে হাখামানেশীদের সম্পর্কে বলেছেন , “ তাদের পুরোহিতগণ ,এমনকি তাঁদের মাতাদের বিবাহ করতেন। ”
তিনি আশকানীদের সম্পর্কে বলেছেন ,
“ অ-ইরানী ঐতিহাসিকদের অনেকেই ঘৃণার সঙ্গে আশকানী সম্রাটদের মাহরাম বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। হাখামানেশী সম্রাট দ্বিতীয় আরদ্শিরের বিষয়ে ঐতিহাসিক প্লুটারিক এবং আশকানী সম্রাট কাম্বুজিয়া সম্পর্কে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডেটাস এরূপ বিবাহের কথা বলেছেন। কিন্তু কোন কোন পারসিক যারথুষ্ট্র এ বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন , “ আশকানীদের ক্ষেত্রে ‘ ভগ্নি ’ শব্দটি প্রকৃত অর্থে গ্রহণ সঠিক হবে না ,কারণ রাজকীয় বংশের সকল নারীদের তারা এক বংশোদ্ভূত হওয়ায় ভগ্নি বলে ডাকত। যদিও তারা চাচাত বোন ,খালাত বোন বা ফুপাত বোন ,এমনকি তাদের কন্যাও হয়ে থাকে তবুও তারা বোন বলে অভিহিত হতো। ”
অতঃপর মাশিরুদ্দৌলা মন্তব্য করেছেন ,
“ কিন্তু যেহেতু ইতিহাস লিখনে সত্যকে অনুসন্ধান করতে হয় সেহেতু অস্বীকার করার উপায় নেই ,অতি নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের রীতি যা ‘ খুইতাকদাস ’ নামে প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইরানীদের নিকট পছন্দনীয় বিষয় ছিল। সম্ভবত বংশীয় ও পারিবারিক বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে তা করা হতো। ”
তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইরানী ঐতিহাসিক ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 152 পৃষ্ঠায় বলেছেন ,
“ ইরানীরা মাতা ,ভগ্নি ও কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো এবং তাদের নিকট এ কর্ম ইবাদাত ও আত্মীয়ের হক বলে বিবেচিত হতো। ”
ক্রিস্টেন সেন ইরানী খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন ,
“ তারাও যারথুষ্ট্রদের অনুকরণে নিজ ধর্মের নির্দেশের বিপরীতে অতি নিকটজনদের বিবাহ করত। ‘ মারব ’ গণ 540 খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের জাসেলিক (ঈধঃযড়ষরপ) ধর্মযাজক খ্রিষ্টধর্মের নির্দেশের বিপরীতে তাঁর অনুসারীদের এরূপ বিবাহে বিপুলভাবে উৎসাহিত করত। ” 145
এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের সময়েও ইরানের যারথুষ্ট্রদের মধ্যে ‘ মাহরাম বিবাহ ’ প্রচলিত ছিল। তাই দেখা যেত কখনও কখনও কোন কোন মুসলমান যারথুষ্ট্রদের কাউকে কাউকে তাদের মধ্যে এ কর্মের প্রচলন থাকার কারণে তিরস্কার করে ‘ জারজ সন্তান ’ বলে ডাকত। কিন্তু পবিত্র ইমামগণ মুসলমানদের এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন এজন্য যে ,প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরই বিবাহের নিজস্ব রীতি রয়েছে এবং তারা তাদের রীতি অনুযায়ী বিবাহ করলে তাদের জারজ সন্তান বলে অভিহিত করা উচিত হবে না।
হুদুদের (দণ্ডদান) অধ্যায়ে একটি হাদীসে এসেছে একবার ইমাম সাদিক (আ.)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল: ‘ তোমার ঐ পাওনাদারের সঙ্গে কি করেছ ?
সে বলল: ‘ আমার পাওনাদার এক জারজ সন্তান। ’
ইমাম এ কথা শুনে বেশ রাগান্বিত হয়ে বললেন: ‘ এ কেমন কথা ? ’
সে বলল , ‘ আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। ঐ ব্যক্তি মাজুসী আর তার মাতা হলো তার বোন। তাই সে জারজ সন্তান। ’ ইমাম বললেন , ‘ তাদের ধর্মে কি এটি বৈধ নয় ? সে তাদের ধর্ম অনুযায়ী এরূপ করেছে। তাই তুমি তাকে জারজ সন্তান বলতে পার না। ’ 146
সাদুক তাঁর ‘ তাওহীদ ’ গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা ‘ ওয়াসায়েলুশ শিয়া ’ গ্রন্থের ‘ নিকাহ্ ’ অধ্যায়েও এসেছে। হাদীসটি এরূপ যে ,একদিন হযরত আলী (আ.) দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ,سلوني فبل أن تفقدوني ‘ আমাকে হারাবার পূর্বেই আমাকে প্রশ্ন করে জেনে নাও। ’ আশআস ইবনে কাইস নামে একজন প্রশ্নকারী ছিল যে ইরানীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। পূর্বে হযরত আলীর সঙ্গে তার বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা আমরা বর্ণনা করেছি। সে হযরত আলীকে প্রশ্ন করল , “ কেন মাজুসদের সঙ্গে আহলে কিতাবদের ন্যায় আচরণ কর ,তাদের হতে জিজিয়া নাও ,অথচ তাদের নিকট কোন ঐশী গ্রন্থ নেই ? ”
আলী (আ.) বললেন , “ তাদের আসমানী কিতাব ছিল। আল্লাহ্ তাদের মধ্যে নবীও প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের ধর্মে মাহরামদের সঙ্গে বিবাহ হারাম ছিল। তাদের এক সম্রাট মদ্যপ অবস্থায় তার কন্যার সঙ্গে সঙ্গম করে। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও তার ওপর হাদ (দণ্ড) জারীর দাবি জানায়। ঐ সম্রাট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদের বলল: সকলে সমবেত হয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। যদি তা সঠিক না হয় তাহলে তোমাদের দাবি আমি মাথা পেতে নেব। তারা সমবেত হলে সে বলল: তোমরা জান হযরত আদমের সন্তানের কেউই তাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সমকক্ষ নয়। তারা বলল: হ্যাঁ ,সঠিক। সে বলল: তাঁদের থেকে যে পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ দিয়েছেন। তারা বলল: সঠিক। সে বলল: সুতরাং বোঝা যায় ভাই-বোন ,পিতা-কন্যা বিবাহে তথা মাহরাম বিবাহে কোন বাধা নেই। জনসাধারণ এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় ও পরবর্তীতে বিষয়টি বৈধ হিসেবে তাদের মাঝেও প্রচলিত হয়ে যায়। ” 147
এ ধরনের প্রশ্নোত্তর হতে বোঝা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারথুষ্ট্রগণের মধ্যে মাহরাম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলেই এ ধরনের প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত হতো।
ইরানী-অ-ইরানী ,সুন্নী-শিয়া সর্বোতভাবে সকল ফকীহ্ ফিকাহ্শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাহ্যিক উদাহরণ ও নমুনার উপস্থিতির কারণেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ সকল ফকীহর অধিকাংশই ইরানী ছিলেন। এদের কারো কারো পূর্বপুরুষ মাজুসী (অগ্নি উপাসক) ছিলেন। যেমন ইমাম আবু হানিফার দু ’ পুরুষ পূর্বের সকলেই মাজুসী ছিলেন। যদি যারথুষ্ট্রদের মধ্যে এরূপ বিবাহের প্রচলন না থাকত তাহলে ইসলামের প্রথম যুগের ফিকাহ্শাস্ত্রে তা আলোচিত হতো না।
শেখ আবু জাফর তুসী তাঁর ‘ আল খিলাফ ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘ আল ফারায়িজ ’ অধ্যায়ে মাজুসীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আলোচনায়- যেখানে কোন ব্যক্তির নিকট হতে কেউ দু ’ ভাবে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ওয়ারিস একদিকে মৃতের মাতা ,অপরদিকে পিতার কন্যা হিসেবে ভগ্নি হওয়ায় উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হয় তার উত্তর দান করেছেন এবং এ বিষয়ে অন্যান্য ফকীহর মতামতও এনেছেন।
যারথুষ্ট্রদের মধ্যে যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল তা অস্বীকার করা সূর্যের উপস্থিতিকে অস্বীকারের শামিল। কিন্তু যারথুষ্ট্রগণ আরেক বারের মত তাদের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি ধর্মীয় মৌল নীতি ও আচারকে অস্বীকার করে কল্যাণমূলক মিথ্যা বলা শুরু করেছে।
নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
যদিও তৎকালীন সময়ে নারীদের অবস্থা তেমন সুখকর ছিল না তদুপরি লক্ষ্য করা যায় সে সময়ের কিছু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পর্যায় লাভ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ তৎকালীন সময়ের একটি আইন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন যার নাম ‘ মদিগান হেযার দযসেতান ’ এবং এর অর্থ হলো এক হাজার বিচারের রায় বা হুকুম। এ গ্রন্থের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ,যেমন বার তালমা তা অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের কিছু প্রসিদ্ধ বিচারকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে এ গ্রন্থের অধিকাংশ হুকুম আভেস্তা ও যান্দ হতে নেয়া হয়েছে । এতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা এরূপ :
‘ একজন বিচারক বিচারালয়ে যাওয়ার সময় পাঁচ জন নারী তাঁকে ঘিরে ধরে জামানত ও মুক্তিপণের বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে। সর্বশেষ প্রশ্নটির জবাব দিতে না পেরে বিচারক চুপ করে রইলেন। একজন নারী বলল: হে শিক্ষক! আপনার মাথাকে ক্লান্ত না করে বলুন: জানি না। আমরা ‘ গেলুগণ আনদারয বুরয ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এর জবাব খুঁজে দেখলে অবশ্যই পাব। ’
এ কাহিনী তৎকালীন সময়ের নারীরা যে সাধারণ শিক্ষার সুবিধাপ্রাপ্ত ছিল তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট কি ?
এ বিষয়ে বার তালমাহ গবেষণা চালিয়েছেন এবং ক্রিস্টেন সেন তাঁর দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই মূলত মূল্যায়ন করেছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে নারীরা কখনও কখনও উচ্চ শিক্ষা লাভ করত । অর্থাৎ অন্যান্য দিকের মত এ ক্ষেত্রেও শ্রেণীভিত্তিক সমাজের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সাসানী আমলে খসরু পারভিজের দু ’ কন্যা পুরান দুখত ও অযারমি দুখত স্বল্প সময়ের জন্য রাজত্বও করেছিলেন। তাঁদেরকে সম্রাজ্ঞীর জন্য মনোনীত করার পেছনে ইরানীদের রাজবংশীয়দের প্রতি গভীর বিশ্বাসের বিষয়টিই মুখ্য ছিল। কারণ তারা রাজবংশকে স্বর্গীয় মনে করত। সাসানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আরদ্শির বাবাকান তাঁর বংশকে ইরানের প্রাচীন এক সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে দেখান যাতে করে জনগণের পক্ষ হতে প্রতিবাদ না ওঠে যে ,তিনি রাজবংশীয় নন ও তাঁর দেশ পরিচালনার অধিকার নেই। খসরু পারভিজের পরবর্তী গোলযোগপূর্ণ সময়ে দু ’ ব্যক্তি রাজবংশীয় না হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় শাসন ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ কারণেই ব্যর্থ হয়। এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ হলো খসরু পারভিজের পুত্র শিরাভেই তাঁর সাতজন ভ্রাতাকে হত্যা করে ফলে রাজ সিংহাসনের জন্য ঐ দু ’ জন কন্যা ব্যতীত অন্য কোন দাবিদার ছিল না। তাই রক্ত-বংশের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টিকে নারী অধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ভুল হবে। পুরান দুখত ও অযারমি দুখতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সম্ভ্রান্ত কিছু নারীর উচ্চ শিক্ষা লাভের বিষয়কে মানদণ্ড ধরে নারীদের সার্বিক অবস্থার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ ঐতিহাসিক যে সকল উৎস হাতে রয়েছে তা হতে নারী শিক্ষার বিষয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বার তালমাহর মত হলো নারী শিক্ষার বিষয়টি গৃহ পরিচর্যার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল। তা ছাড়া বাগনাসাক তৎকালীন সময়ের নারীদের গৃহ পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। তদুপরি কিছু কিছু অভিজাত পরিবারের নারী বা সাধারণ শিক্ষায়ও গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। ”
ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে মাসদাকী আন্দোলনের আলোচনায় বলেছেন :
“ সাসানী শাসনামলে নারী অধিকারের বিষয়ে বার তালমার গবেষণার ফলে অনেক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হলো সাসানী শাসনামলে বিভিন্ন পর্যায়ে নারী অধিকার আইনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বার তালমাহর মতে শিক্ষা ও চিন্তাগতভাবে সেসময় নারীর অধিকার অন্যের অধিকারের ছায়ায় ছিল অর্থাৎ তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি অধিকার না থাকলেও নির্দিষ্ট অধিকার অবশ্যই ছিল। সাসানী আমলে নতুন আইনের পাশাপাশি প্রাচীন আইনও বিদ্যমান ছিল এবং বাহ্যিক বৈপরীত্য এ কারণেই ছিল। আরব মুসলমানগণ ইরান জয়ের পূর্বেই ইরানের নারীরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করেছিল। ” 148
নৈতিক অবস্থা
তৎকালীন সময়ের ইরানী সমাজের নৈতিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেও পর্যাপ্ত দলিল আমাদের হাতে নেই। অবশ্য বিভিন্ন নমুনা ও নিদর্শন হতে সাধারণ নৈতিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
নৈতিকতা ও মানসিকতা দু ’ প্রকারের। যথা: প্রাকৃতিক ও অর্জিত। কোন জাতির প্রাকৃতিক নৈতিকতা হলো ঐ জাতির ভৌগোলিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বংশীয় উত্তরাধিকারের বিষয়টি মানুষের দৈহিক ,যেমন গায়ের রং ,চোখের বর্ণ ও চুলের ধরন প্রৃভৃতিতে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি আত্মিক ,নৈতিক ও মানসিক অবস্থায়ও প্রভাব রাখে। অবশ্য এ দু ’ য়ের পার্থক্য হলো জাতি ও বংশগত উত্তরাধিকারের বিষয়টি বিবাহ ,সংমিশ্রণ ,
স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে ভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ধারণ করে ,কিন্তু ভৌগোলিক ও অঞ্চলগত বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল। ভালবাসা ,দয়াশীলতা ,অতিথিপরায়ণতা ,মেধা ,বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ,সহনশীলতা ও সম্মানবোধের বৈশিষ্ট্যের কারণে ইরানীরা সকল সময়ই প্রশংসিত হয়েছে।
অর্জিত নৈতিকতা ও মানসিকতা সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য সভ্যতার অর্থ এখানে মানবিক ও নৈতিক সভ্যতা ;শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতা নয়। অর্জিত নৈতিকতা একদিকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং অন্যদিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আদব-কায়দা ,রীতি-নীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব হলো প্রত্যক্ষ এবং সামাজিক পরিবেশের প্রভাব হলো পরোক্ষ।
মানুষের সাধারণ চরিত্র ও মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধারার বিপরীতে তাঁর আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষত যে সকল প্রচলিত রীতি ও আচার মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব রাখে সেগুলো লক্ষণীয়।
ইরানীরা প্রাকৃতিক নৈতিকতা অর্থাৎ জাতি ও বংশগত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নৈতিকতার অধিকারী ছিল। তারা প্রাচীনকাল হতেই উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য প্রশংসিত ছিল । খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস যিনি ইতিহাসের জনক বলে খ্যাত এবং মূলত এশিয়া মাইনরের মানুষ তিনি তৎকালীন সময়ের ইরানী সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি সার্বিক আলোচনা রেখেছেন। তিনি যা লিখেছেন তাতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় ইতিবাচক ও সুন্দর দিক অধিক এসেছে এবং অসুন্দর দিক কম এসেছে।
সক্রেটিসের ছাত্র গাযানফুন যিনি হিরোডোটাসের একশ ’ বছর পরের ব্যক্তি তিনিও ইরানীদের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু হিরোডোটাসের বিপরীতে তিনি ইরানীদের পতনের যুগও দেখেছেন অর্থাৎ হিরোডোটাস কেবল ইরানীদের উত্থানের যুগ দেখেছিলেন ও প্রশংসা করেছিলেন। গাযানফুন কুরুশের (সাইরাসের) যুগের ইরানীদের নৈতিকতা ও মানসিকতার সঙ্গে তাঁর যুগের ইরানীদের আচার ও নৈতিকতার তুলনা করেছেন এবং তাঁর যুগের ইরানীদের অধঃপতন ও পরিবর্তনীয় অবস্থায় ব্যাখ্যা দান করেছেন। যদি ইরানীদের প্রকৃতিগত চরিত্রকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনা করি নিঃসন্দেহে বলা যায় অন্যদের নিকট হতে তা উত্তম না হলেও অধম ছিল না। বক্তব্য দীর্ঘায়িত যাতে না হয় এ জন্য তাঁদের উল্লিখিত ইরানী মানসিকতার ভাল-মন্দ দিকসমূহ নিয়ে আর আলোচনা করছি না।
ইসলামী সূত্রের বিভিন্ন বর্ণনায় দু ’ টি দৃষ্টিকোণ হতে ইরানীদের চরিত্র ও মানসিকতার প্রশংসা করা হয়েছে :
1. চিন্তার স্বাধীনতা ,কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত মানসিকতা ,2. জ্ঞান পিপাসা।
পবিত্র কোরআনে এসেছে:
) و لو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين (
“ যদি আমি একে (কোরআন) কোন ভিন্ন ভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম ,অতঃপর সে তা তাদের (আরবদের) কাছে পাঠ করত তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। ” 149
ইমাম সাদিক (আ ,) বলেছেন , “ হ্যাঁ ,যদি এই কোরআন কোন অনারবের ওপর প্রেরণ করা হতো তাহলে এ আবররা কখনই ঈমান আনত না। কিন্তু তা আরবের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে ও অনারব এতে ঈমান এনেছে এটি অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব। ” 150
ইমাম সাদিক আরো বলেছেন ,
“ যে ব্যক্তি ভালবেসে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ঐ ব্যক্তি হতে উত্তম যে ভয়ে ইসলামকে মেনে নিয়েছে। আরবের মুনাফিকরা ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই তাদের ঈমান প্রকৃত ঈমান নয়। কিন্তু ইরানীরা ভালবেসে ও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। ” 151
আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাসূল (সা.)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন ,তিনি বলেছেন , ‘ স্বপ্নে এক পাল কালো মেষকে দেখলাম যাতে অসংখ্য সাদা মেষ প্রবেশ করছে। ’ সকলে তাঁকে প্রশ্ন করল , ‘ হে রাসূলাল্লাহ্! এ স্বপ্নকে কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন ? ’ তিনি বললেন , ‘ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো অনারবরা তোমাদের ধর্ম ,রক্ত ও বংশে অংশীদার হবে অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে ঈমান আনবে ,তোমাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তাদের রক্ত তোমাদের সঙ্গে মিশ্রিত হবে। ’ সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল , ‘ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আমাদের রক্তে অংশীদার হবে ? ’ রাসূল (সা.) বললেন , ‘ হ্যাঁ ,ঈমান যদি সুরাইয়া তারকাতেও পৌঁছায় আজমদের (অনারবদের) একদল সেখানেও পৌঁছবে। ’
ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের শেষাংশে কয়েক পৃষ্ঠায় ইরানীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ,
‘ পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ যেমন আমিওজুস মারসলিনুস152 এবং প্রকুপিউস153 প্রমুখ যেভাবে ইরানের সমাজকে ভাল-মন্দ উভয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মনে হয় তা একটি অভিজাত সমাজ। অর্থাৎ শুধু অভিজাত শ্রেণী এ সমাজের পরিচায়ক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইরান জাতির বিশেষ দীপ্তির প্রকাশ ঘটেছে। ’
আমিওনুস মারসলিনুসের বিবরণ হতে ক্রিস্টেন সেন যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অভিজাত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত বিধায় স্বাভাবিকভাবেই ভাল দিক হতে খারাপ দিকগুলো তাদের মধ্যে অধিক ছিল। তাই সেগুলোর উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“ আরব লেখকগণ প্রাচ্যের শাসকবর্গের আদর্শ হিসেবে সাসানী শাসকদের সম্মান ও প্রশংসা করেছেন এবং ইরানী জাতিকে মর্যাদার সাথে স্মরণ করেছেন। ”
অতঃপর তিনি ‘ খোলাসাতুল আজায়েব ’ গ্রন্থ হতে নিম্নোক্ত বর্ণনা দান করেছেন , ‘ পৃথিবীর সকল জাতিই ইরানীদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। বিশেষত রাষ্ট্র পরিচালনা ,যুদ্ধ কৌশল ,চিত্রকলা ,খাদ্য প্রস্তুত ,ঔষধ প্রস্তুত ,পোশাকের ধরন ,প্রদেশ প্রতিষ্ঠা ,কোন বিষয়কে যথার্থ স্থানে সংরক্ষণ ,কবিতা ,গজল ,বক্তৃতা ,চিন্তা শক্তি ,সততা ,পবিত্রতা এবং সম্রাটদের প্রশংসা প্রভৃতি বিষয় বিশ্বের অন্যান্য জাতির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এ জাতি এর পরবর্তী শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসমূহের জন্য আদর্শ। ’
আশ্চর্যের বিষয় হলো এত কিছু উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন ,
“ ইরানীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের নৈতিক মর্যাদাকে ইসলামী জাতিগুলোর মাঝে সমুন্নত রেখেছে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও স্বভাবগত প্রতিভা সাসানী সাম্রাজ্যের পতনের পর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। কারো কারো মতে এ দুর্বলতার কারণ এটি নয় যে ,ইসলাম ধর্মের নৈতিক ভিত্তি পারসিকদের ধর্ম হতে দুর্বল ;বরং ইরানী জাতির অধঃপতনের কারণ ইসলাম সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান ক্ষুন্ন হতে শুরু করে ও এ শ্রেণী সাধারণের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের শ্রেয়তর গুণসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। ”
অবশ্য ক্রিস্টেন সেন রাজনৈতিক প্রতিভার পাশাপাশি স্বভাবগত যে প্রতিভার কথা বলেছেন তা এমন এক রাজনৈতিক স্বভাব যা মানবিক স্বভাবের বিপরীতে অবস্থান করে। রাজনৈতিক স্বভাব ও চরিত্রের যে দৃষ্টিতে ক্রিস্টেন সেন দেখেছেন তাতে অভিজাত শ্রেণীর পতন ও তাদের বিশেষ স্বভাবের দুর্বল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ স্বভাবের কারণেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সকল ক্ষমতা ও সম্পদ হস্তগত ও অন্যান্য সকলের অধিকারকে হরণ করে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদের শোষণ ক্রিয়া চালাত। এই রাজনৈতিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে তারা ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। বিষয়টি দুঃখজনক। তাই মানবীয় চরিত্রের মানদণ্ড ও দৃষ্টিতে এরূপ অভিজাত শ্রেণীর পতন হয়ে সাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠা দুঃখজনক তো নয়ই বরং কাক্সিক্ষত ও পূর্ণ আনন্দের বিষয়।
সাসানী আমলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কিরূপ ও কিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়ে পূর্ণ কোন তথ্য জানা যায় না। তবে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন তা যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণের মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং তাঁরা আভেস্তার বিষয়সমূহ মানুষকে শিক্ষা দিতেন ,এর বাইরের কিছু তাঁদের নিকট ছিল না।
যে দর্পণ অন্য সকল দর্পণ হতে তৎকালীন ইরানের মানুষের নৈতিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তা হলো সেসময়ের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। সেসময়ের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। আমরা পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি ।
ভারসাম্যহীন এ সমাজে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু শ্রেণী এভাবে বিভক্ত ছিল যে ,সংখ্যালঘুরা সম্পদশালী ও সুবিধাভোগী এবং সংখ্যাগুরুরা ছিল দরিদ্র ও সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত।
সম্পদশালী সুবিধাভোগীরা তাদের অবস্থার কারণে এক ধরনের চরিত্র এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতরা ভিন্ন ধরনের চরিত্রের অধিকারী ছিল। তবে উভয় শ্রেণীর চরিত্রই ছিল ভারসাম্যহীন। সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল আত্মতুষ্ট ,অহংকারী ,কর্মহীন ,চাটুকার ,ভীতু ,ধৈর্যহীন ,অসহিষ্ণু ,বদ মেজাজী ,অপচয়কারী ,আয়েশী ও আদুরে। আমিওনুস মারসলিনুস ইরানী অভিজাতদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কম-বেশি এ সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বঞ্চিত শ্রেণী ছিল হতাশাগ্রস্ত ,অসন্তুষ্ট ,হিংসুক ,প্রতিশোধপরায়ণ ,অহিতৈষী ,কুসংস্কারাচ্ছন্ন ,বিশ্বে ন্যায় ও শৃঙ্খলার অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসী। যদিও ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন ইরানের সাধারণ জনগণের বিবরণ দান করেন নি তদুপরি বলা যায় ঐরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এমন অবস্থাই স্বাভাবিক। ইরানে সেসময় মাথা পিছু কর নেয়া হতো ,কিন্তু যে শ্রেণীটি করের জন্য অধিকতর উপযোগী ছিল আইনগতভাবে তারা কর হতে মুক্ত ছিল। আনুশিরওয়ান কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করলেও অভিজাত শ্রেণী ,সেনাপতি ,রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ,পুরোহিত ও সরকারী সেবকদের কর বহির্ভূত রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই করদাতা শ্রেণী এই ব্যতিক্রম ও বৈষম্যের প্রতি অসন্তুষ্ট ও প্রতিবাদী ছিল।
তৎকালীন সময়ের কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা হতে সেসময়ের সাধারণ শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যেতে পারে। ইবনে আসির তাঁর ‘ কামিল ’ গ্রন্থে লিখেছেন ,
“ যখন পারস্য সেনাপতি রুস্তম ফারাখযাদ দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী মুসলিম সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে এক আরবের সঙ্গে দেখা হয়। আরব ব্যক্তিটি রুস্তমের সঙ্গে কথোপকথনের পর ইরানীদের পরাস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ঘোষণা করল। রুস্তম তাকে বিদ্রূপ করে বললেন: আমরা তাহলে ধরে নেব এখন হতে তোমাদের অধীনে রয়েছি। আরব বলল: তোমাদের অপকর্মই তোমাদের এরূপ নিয়তি ডেকে আনবে। রুস্তম এ আরবের কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে তার শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর সেনাদল নিয়ে ‘ বুরসে ’ পৌঁছে ছাউনী পাতলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁর সেনাবাহিনী জনসাধারণের সম্পদ লুটপাট শুরু করল ,তাদের নারীদের জোরপূর্বক ছাউনীতে ধরে এনে নিপীড়ন চালাল। অতঃপর মদ ও নারী নিয়ে মেতে উঠল। সাধারণ মানুষের আর্তনাদ শুরু হলো। তখন রুস্তম তাঁর সেনাদলের প্রতি উদ্দেশ্য করে বললেন: হে ইরানীরা! এখন বুঝতে পারছি ঐ আরব সত্য বলেছে। প্রকৃতই আমাদের অপকর্ম আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ডেকে আনবে। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে আরবরা আমাদের ওপর জয়ী হবে। কারণ তাদের চরিত্র ও আচরণ আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। খোদা পূর্বে তোমাদের শত্রুদের ওপর বিজয় দান করতেন এ জন্য যে ,তোমরা উত্তম স্বভাবের ছিলে ,মানুষের ওপর অত্যাচারের অবসান ঘটাতে ও তাদের সঙ্গে সদাচারণ করতে ,কিন্তু এখন তোমরা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছ। তাই অবশ্যই তোমাদের ওপর হতে নিয়ামত তুলে নেয়া হবে। ”
ইরান ও মিশরের গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগ
ইরান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মুসলিম বিজেতাদের মাধ্যমে ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংসের তথাকথিত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এ বিষয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যে সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত ও স্বতঃসিদ্ধ কেবল সেগুলোই স্কুল ,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং যে সকল বিষয় সন্দেহজনক ও অপ্রমাণিত এবং শিক্ষার্থীদের কাঁচা মনে প্রভাব ফেলতে পারে তা বর্ণনা হতে বিরত থাকা উচিত। অথচ এরূপ একটি বিষয়ে অনবরত প্রচারণা চালানো হচ্ছে।
যদি মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান বা মিশরের গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে তবেই আমরা তা আলোচনা করতে পারি ইসলামের প্রকৃতি গঠনমূলক না ধ্বংসাত্মক এবং মতামত দিতে পারি ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি তৈরি করে থাকলেও অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসও করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ইরানে বিভিন্ন অবদান রাখলেও এর পাশাপাশি নেতিবাচক কর্মও করেছে । অর্থাৎ একদিকে সৌভাগ্য আনলেও অপরদিকে বিপর্যয় ডেকে এনেছে।
ইরানে গ্রন্থাগারসমূহ ও বিভিন্ন শিক্ষালয় ,যেমন স্কুল ,কলেজ ,বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিদ্যমান ছিল এবং সেগুলো বিজয়ী মুসলিমদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে এত বেশি প্রচারণা চালানো হয়েছে যে ,অনভিজ্ঞদের নিকট নিশ্চিত ঘটনা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
কয়েক বছর পূর্বে একটি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার (তানদুরুসত নামে) একটি সংখ্যায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এক ইরানী চিকিৎসকের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ঐ বক্তব্যে কবি শেখ সা ’ দীর প্রসিদ্ধ কবিতার ,যাতে তিনি সকল আদম সন্তানকে এক দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন ,উল্লেখ করে বলা হয়েছে প্রথম বারের মত একজন ইরানী কবি বিশ্বসমাজের ধারণার জন্ম দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন :
‘ প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার লালনকেন্দ্র যেখানে দার্শনিক ও বিশিষ্ট মনীষিগণ ,যেমন সক্রেটিস ও অন্যান্যদের জন্ম হয়েছিল ;কিন্তু বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরূপ শিক্ষাঙ্গন সর্ব প্রথম ইরানে সাসানী সম্রাট খসরু পারভিজের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানের তৎকালীন রাজধানী শুশে ‘ জান্দী শাপুর ’ নামের এক বৃহৎ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল...। এই বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ দিন কার্যকর ছিল তবে আবরদের ইরান আক্রমণের সময় ইরানের অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনের মত এটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদিও ইসলাম ধর্ম জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে চীন পর্যন্ত যেতে বলেছে ,তদুপরি আরবরা ইসলামের নবীর নির্দেশের বিপরীতে ইরানের জাতীয় গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগ করে ও আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে। এরপর দু ’ শতাব্দী ইরানীরা আরবদের অধীনে ছিল। ’
এ রকম সনদ ও সূত্রবিহীন লেখার সংখ্যা অসংখ্য। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণাভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এরূপ দাবিদারদের উপস্থাপিত দলিলসমূহের পর্যালোচনাভিত্তিক জবাব দান করব। এই সম্মানিত চিকিৎসক যিনি এক বিদেশী সেমিনারে ইরানের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞাত একদল শ্রোতার সম্মুখে দ্বিধাহীন ও অকাট্যভাবে এ বিষয়ে তাঁর মত দিয়েছেন ,তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে চাই:
প্রথমত গ্রীস ও ইরানের জান্দি শাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অনেক বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যার সঙ্গে জান্দি শাপুরের ঐ ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন তুলনা হয় না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে মুসলমানগণ প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে বিদেশী ভাষার গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ শুরু করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন।
দ্বিতীয়ত জান্দি শাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় যা একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৈ অন্য কিছু ছিল না আরবদের দ্বারা কোনরূপ আক্রমণের শিকারই হয় নি এবং চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত তা চালু ছিল। এ সময় বাগদাদে একটি বৃহৎ শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ধীরে ধীরে জান্দি শাপুরের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়টি স্তিমিত হয়ে পড়ে। আব্বাসীয় খলীফারা বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণকেই তাঁদের দরবারে ডাকতেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বাখতিশু এবং মসাভীয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে এ মহাবিদ্যালয় হতেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সুতরাং জান্দি শাপুরের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আরব বিজেতাদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলা এ বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচায়ক।
তৃতীয়ত জান্দি শাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়টি ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে রোমের খ্রিষ্টান আলেমদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ইরানী যারথুষ্ট্রীয় মনোবৃত্তির নয় ;বরং রোমীয় খ্রিষ্ট মনোবৃত্তির ছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়টি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে ইরানে অবস্থিত ছিল ,কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তা ও জ্ঞানের খোরাক ইরানী যারথুষ্ট্র চিন্তার বাইরের অর্থাৎ ইরানের বাইরে এর অভিভাবক গোষ্ঠী রোমানদের নিকট থেকে সকল পৃষ্ঠপোষকতা পেত। এরূপ আরো কিছু শিক্ষা কেন্দ্র বৌদ্ধদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য ইরানীদের মানসিকতা জ্ঞানপিপাসু মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করলেও সাসানী আমলে প্রতিষ্ঠিত যারথুষ্ট্র পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা জ্ঞানবিরোধী হওয়ায় তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলে জ্ঞানের বিকাশকে প্রতিরোধ করতেন। এ কারণেই ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল যা যারথুষ্ট্র পুরোহিত প্রভাবাধীন ছিল না সেখানে বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল ;কিন্তু তাঁদের প্রভাবাধীন এলাকায় তা হয়নি।
সাধারণত ইতিহাস ,ভূগোল ও সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে কম-বেশি আলোচ্য প্রচারণাটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। রেজা যাদেহ শাফাক যিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব তিনি তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছুটা ইনসাফ রক্ষা করেছেন। তিনি দশম শ্রেণীর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন , ‘ সাসানী আমলে ধর্ম ,সাহিত্য ,বিজ্ঞান ,ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যাপকভাবে লিখিত ও অনূদিত হতো। তা ছাড়া রাজকীয় কবি ও গায়কদের সম্পর্কে যে সকল কথা বর্ণিত হয়েছে তা হতে বোঝা যায় ,সে সময়ে সাহিত্যের প্রচলন অধিক বিস্তৃত ছিল না এবং বিশেষত পুরোহিত ও রাজ দরবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাসানী আমলের শেষ দিকে পুরোহিত ও রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপক চরিত্রিক স্খলন ও বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং এ ধর্মের বিভিন্ন বিচ্যুত দলের সৃষ্টি হয়। তাই ইসলামের আবির্ভাবের সময় ইরানের সাহিত্যও এ দু ’ শ্রেণীর বিচ্যুতির ফলে অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছেছিল। ’
চতুর্থত এ মহামান্য চিকিৎসক অন্যান্যদের অনুকরণে তোতা পাখির মত বলেছেন ,আরব বিজেতাগণ ইরানের জাতীয় গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগ করেছিল ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছিল। যদি তিনি বলতেন ঐ জাতীয় গ্রন্থাগার কোথায় ছিল তাহলে ভাল হতো। তা কি হামেদানে নাকি ইসফাহানে ,শিরাজে নাকি আজারবাইজানে ,তিসফুনে নাকি নিশাবুরে ,আকাশে না পৃথিবীতে ? কোথায় ছিল তা বললে বাধিত হতাম। তাঁর মতো যাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগার ধ্বংসের ধূয়া তোলেন তাঁরা এই গ্রন্থাগার কোথায় অবস্থিত ছিল তার উল্লেখ করেন না কেনো ? নাকি এ বিষয়ে তাঁদের নিকট কোন তথ্য নেই ?
কোন তথ্যসূত্রেই এ বিষয় উল্লিখিত হয়নি। যদিও আরবদের ইরান বিজয়ের ইতিহাস সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থেই এসেছে তদুপরি তাতে ইরানের কোন গ্রন্থাগারের নাম দিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ হয়েছে কি হয় নি তাও আলোচিত হয়নি ;বরং ঐতিহাসিক দলিলসমূহে এর বিপরীতে বলা হয়েছে যারথুষ্ট্র পরিমণ্ডলে জ্ঞানের প্রতি কোন অনুরাগ ছিল না। আরব লেখক জাহেয যিনি আরবীয় গোঁড়ামিমুক্ত ও আরবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লিখেছেন তাঁর নিকট থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করব। তিনি তাঁর ‘ আল মুহাসিন ওয়াল আযদাদ ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ ইরানীরা গ্রন্থ প্রণয়নে তেমন আগ্রহী ছিল না ,তারা স্থাপত্য শিল্পে অধিকতর আগ্রহী ছিল। ’ ‘ কয়েকজন মধ্যপ্রাচ্যবিদের দৃষ্টিতে পারস্য সভ্যতা ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে ,সাসানী আমলে যারথুষ্ট্র ধর্মে লেখার প্রচলন ছিল না ,এমনকি গবেষকগণের মতে যারথুষ্ট্রদের ধর্মীয় গ্রন্থ আভেস্তার পাণ্ডুলিপির অনুলিপিও নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবত আলেকজান্ডারের ইরান আক্রমণের সময় আভেস্তার দু ’ টি মাত্র পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল যার একটি ইসতাখরে ছিল ও আলেকজান্ডার কর্তৃক তা ভস্মীভূত হয়।
যেহেতু তৎকালীন সময়ে জ্ঞান ,শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও পুরোহিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু অন্যান্য শ্রেণীর লোক শিক্ষা হতে বঞ্চিত ছিল। সাধারণত বঞ্চিত শ্রেণী হতেই মনীষীদের জন্ম হয় ;অভিজাত শ্রেণী হতে নয়। কামার-কুমার ,চর্মকার প্রভৃতি শ্রেণী হতেই ইবনে সিনা ,আল বিরুনী ,ফারাবী ,জাকারিয়া রাযীদের জন্ম হয়েছে ;অভিজাত শ্রেণী হতে নয়। তদুপরি মরহুম ডক্টর শাফাকের উদ্ধৃতিতে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি ,সাসানী আমলে এ উভয় শ্রেণী এতটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ,তাদের নিকট হতে কোন সংস্কৃতি ও জ্ঞানগত বিষয় আশা করা সম্ভব ছিল না।
অবশ্য সাসানী আমলে নিঃসন্দেহে কিছু সাহিত্যিক কর্ম বিদ্যমান ছিল। এগুলোর অধিকাংশই মুসলিম শাসনামলে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ও বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে অনেক সাহিত্যকর্মই বিলুপ্ত হয়ে গেছে সংরক্ষণের অভাবে ;গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগের মত কারণে নয়। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই যখন মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে এবং এক সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে তখন অমনোযোগ ও বাড়াবাড়ির কারণে প্রাচীন সংস্কৃতি উপেক্ষিত ও এর সাহিত্য ,সংস্কৃতি মানুষের মাঝে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে বিনাশের কবলে পড়ে। বর্তমানে এর নমুনা আমরা ইসলামী সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে লক্ষ্য করেছি। ইরানের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ফ্যাশান বলে পরিগণিত হচ্ছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি সেকেলে বলে উপেক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণে তাই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। গণিত ,দর্শন ,সাহিত্য ,প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ধর্মীয় মূল্যবান গ্রন্থসমূহ যা কয়েক বছর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল বর্তমানে কোথায় রয়েছে তা অজ্ঞাত। সম্ভবত মুদির দোকানে কাজে লাগছে অথবা লুটপাট হয়ে গেছে। অধ্যাপক জালালুদ্দীন হুমায়ীর বর্ণনা মতে মরহুম আল্লামাহ্ মাজলিসীর ব্যক্তিগত সংগহের মূল্যবান কিছু হস্তলিখিত গ্রন্থ যা তিনি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বীয় প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন তা কয়েক বছর পূর্বে সের দরে বিক্রি হয়েছে।
স্বাভাবিকভাবেই ইরান বিজয়ের সমকালীন সময়ে কিছু মূল্যবান গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহশালায় ছিল এবং দু ’ বা তিন শতাব্দী তাঁদের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে আরবী লিখন পদ্ধতি প্রচলনের ফলে পাহলভী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলো সাধারণের ব্যবহার বর্জিত হয়ে পড়ে এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ইরানে গ্রন্থাগারসমূহ ও শিক্ষাঙ্গন ছিল এবং আরবরা তা ধ্বংস করে এমন কথা কল্পকাহিনী বৈ অন্য কিছু নয়।
ইবরাহীম পুর দাউদের মত লোক যাঁর সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে-মরহুম কাযভিনীর ভাষায় যা কিছু আরবদের থেকে এসেছে সবই খারাপ এমন ধারণা পোষণকারী-ইতিহাস হতে হস্ত-পদ কর্তিত কোন আলামত এ বিষয়ে পেলে কিংবা যদি নাও পাওয়া যায় তবু বর্ণনাতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করে হলেও আরব কর্তৃক ইরানের গ্রন্থাগার ও শিক্ষাঙ্গনসমূহ ধ্বংসের বিবরণ দান অস্বাভাবিক কিছু নয়। তদুপরি কিছু লোক যাঁদের নিকট থেকে এরূপ আশা করা যায় না তাঁরাও পুর দাউদের অনুকরণে এমন কথা বলেছেন ও তাঁর অনুসরণ করেছেন। ডক্টর মুঈনও তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর ‘ মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ’ গ্রন্থে আরবদের ইরান আক্রমণের পরিণাম শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়ে যা বলেছেন তার অধিকাংশই পুর দাউদের বর্ণনা হতে নেয়া হয়েছে। তিনি প্রমাণ হিসেবে যাঁদের নিকট থেকে বর্ণনা দিয়েছেন ও যে সকল দলিল উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ :
1. ইংরেজ স্যার জন ম্যালকমের ইতিহাস হতে।
2. এরূপ বর্ণনা ,ইসলামের আবির্ভাবের সমকালীন সময়ে আরবরা অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ছিল। ওয়াকেদীর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময়ে কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতের জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। আরব বেদুইনদের সর্বশেষ কবি ‘ যুররামা ’ সাক্ষর হলেও তা গোপন করে বলতেন সাক্ষরতা আমাদের নিকট অভদ্রতা বলে পরিগণিত।
3. জাহেযের ‘ আল বাইয়ান ওয়াত তানবীহ্ ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ,এক কুরাইশ গোত্রপতি এক বালককে ‘ সিবাভেই ’ -এর গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে দেখে চীৎকার করে বলে , ‘ হে বালক! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত এ জন্য যে ,এই কাজ শিক্ষক ও ভিক্ষুকদের ’ অর্থাৎ সে সময়ে শিক্ষা দান বা শিশুদের অক্ষরজ্ঞান শিখানো আরবদের নিকট অপমানের বিষয় ছিল। কারণ শিক্ষকদের বেতন ছিল ষাট দিরহাম এবং তাদের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত নগণ্য।
4. ইবনে খালদুন ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় ‘ আল উলুমুল আকলিয়া ওয়া আছনাফুহা ’ অধ্যায়ে বলেছেন: ‘ ইরান বিজয়ের সময় এ ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থান আরবদের হাতে আসে। সা ’ দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হযরত উমরের নিকট পত্র লিখে বিদ্যমান গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদের অনুমতি চেয়েছিলেন। হযরত উমর ঐ গ্রন্থগুলো পানিতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: আল্লাহ্ হেদায়েতের জন্য আমাদের ঐ সব গ্রন্থ হতে উত্তম কিছু দান করেছেন এবং যদি তাতে কোন পথভ্রষ্টতা থাকে তবে মন্দ হতে তিনি আমাদের রক্ষা করুন। ফলে ঐ গ্রন্থসমূহতে অগ্নি সংযোগ করা হয় অথবা পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। এ কারণেই ইরানীদের লিখিত জ্ঞান এর সাথে বিলুপ্ত হয়। আবুল ফারাজ ইবনুল ইবরী তাঁর ‘ তুখতাছারুদ্দৌলা ’ ,আবদুল লতিফ বাগদাদী তাঁর ‘ কিতাবুল ইফাদাহ্ ওয়াল ই ’ তিবার ’ ,কাফতী তাঁর ‘ তারিখুল হুকামা ’ গ্রন্থে ইয়াহিয়া নাহওয়ার জীবনী আলোচনায় ,হাজী খলীফা তাঁর ‘ কাশফুয যুনুন ’ গ্রন্থে ,ডক্টর সাফা তাঁর ‘ তারিখে উলুমে আকলী ’ গ্রন্থে আরবদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ভস্মীকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। তাই যদি প্রতিষ্ঠিত হয় ,আরবরা মিশরের এই গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগ করেছিল তবে অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগারসমূহও তারা ধ্বংস করেছিল বলে প্রমাণিত হয়। তাই অসম্ভব নয় ,ইরানেও তারা এ কাজ করেছে। কিন্তু শিবলী নোমানী তাঁর ‘ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ’ শিরোনামের লেখায় (নিবন্ধে) এবং মুজতবা মিনুয়ী ‘ সুখান ’ পত্রিকার এক প্রবন্ধে এরূপ অগ্নি সংযোগের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
5. আবু রাইহান বিরুনী তাঁর ‘ আসারুল বাকীয়াহ্ ’ গ্রন্থে ‘ খাওয়ারেজম ’ অঞ্চলের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন , ‘ খাওয়ারেজমের জনসাধারণ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়ার পর কুতাইবা ইবনে মুসলিম কর্তৃক তা দ্বিতীয় বারের ন্যায় বিজিত হয়। তিনি ‘ আসাক জামুক ’ কে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং যারা খাওয়ারেজম লিখন পদ্ধতি জানত ও পূর্ববর্তী জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিল তাদের ছিন্নভিন্ন করেন এবং অতীত নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করেন। ফলে তাদের অবস্থা এতটা সংকটময় হয়ে পড়েছিল যে ,ইসলামের আবির্ভাবের পর এ অঞ্চলের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। আবু রাইহান ঐ গ্রন্থেই লিখেছেন , ‘ যেহেতু কুতাইবা ইবনে মুসলিম খাওয়ারেজমী লেখকদের হত্যা করেন ,তাদের পুরোহিতদের নির্বংশ ও লেখা ধ্বংস ও ভস্মীভূত করেন সেহেতু খাওয়ারেজমের অধিবাসীরা অজ্ঞ থেকে যায়। তারা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুধু তাদের মুখস্থ শক্তির ওপর নির্ভর করত। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা এ বিষয়গুলোর ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পার্থক্যের ক্ষেত্রসমূহ ভুলে যায় এবং শুধু সার্বিক বিষয়গুলো তাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ছিল। ’
6. দৌলত শাহ সামারকান্দীর ‘ তাযকিরাতুশ শুয়ারা ’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহির কর্তৃক গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিবরণ।
উপরিউক্ত দলিলসমূহ ডক্টর মুঈন ইরানের গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগের প্রমাণস্বরূপ এনেছেন। দলিলসমূহের মধ্যে চতুর্থটি যা ইবনে খালদুন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনুল ইবরী ,বাগদাদী ও কাফতী কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। হাজী খলীফা তাঁর ‘ কাশফুয যুনুন ’ গ্রন্থেও বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন।
এ ছাড়াও সপ্তম দলিল হিসেবে অপর যে বিষয়টির উল্লেখ ডক্টর মুঈন করেন নি কিন্তু জর্জি যাইদান ও কিছু ইরানী লেখক করেছেন তা হলো আরবদের জ্ঞান ও গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতি অনীহা ও বিদ্বেষ। যেমন দ্বিতীয় খলীফা হাদীসসমূহ লেখার বিরোধী ছিলেন ও সব সময বলতেন ,
حسبنا كتاب الله ‘ আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। ’ এরূপে তিনি সকল ধরনের লেখা ও সংকলনকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। যে কেউ এ কাজ করত সে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হতো। এই নিষেধাজ্ঞা দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল ও সময়ের চাপে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।
এটি স্পষ্ট ,যে জাতি কমপক্ষে একশ ’ বছর লেখা ও সংকলনের অনুমতি দেয়নি সে জাতি বিজিত জাতির বিদ্যমান পুস্তক ও লেখালেখিকে অব্যাহত থাকতে দিতে পারে না।
আমরা প্রথমে ডক্টর মুঈনের উপস্থাপিত প্রথম দলিলের পর্যালোচনা করব। অতঃপর যথাক্রমে সপ্তম ও চতুর্থ দলিলের উত্তর দান করব।
প্রথম দলিলটি স্যার জন ম্যালকমের। ‘ বিভিন্ন মত ’ এবং ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ (মাযদা ইয়াসনা ও ফার্সী সাহিত্য) শীর্ষক আলোচনায় আমরা তাঁর লক্ষ্য ,উদ্দেশ্য ও দলিলসমূহের ভিত্তিহীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। স্যার জন ম্যালকম সম্ভবত ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মানুষ। তাঁর সঙ্গে বর্ণিত ঘটনার তেরশ ’ বছর সময়ের ব্যবধান ছিল। তাই এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত ছিল। তদুপরি তাঁর লেখায় যেরূপ ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ঐ বর্ণনার কোন ভিত্তিই থাকে না।
তিনি দাবি করেছেন ,আরব নবীর অনুসারীরা ইরানের শহরগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। এরূপ মিথ্যা কোন পণ্য বিক্রেতার কৌটার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো ডক্টর মুঈন স্যার জন ম্যালকমের অসংলগ্ন কথাগুলোকে তাঁর গ্রন্থে দলিল হিসেবে এনেছেন।
জাহেলী (অজ্ঞ) আরবদের নিরক্ষরতার বিষয়টিকে পবিত্র কোরআনও বর্ণনা করেছে। কিন্তু এটি কেমন যুক্তি যে ,জাহেলিয়াত যুগের আরবগণ যেহেতু মূর্খ ছিল তাই তারা ইসলামী শাসনামলে গ্রন্থসমূহে অগ্নি সংযোগ করেছে ? তা ছাড়া জাহেলী যুগ হতে ইসলামের বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিল পঁচিশ বছর। সে সময়কালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আরবে বিশেষত মদীনায় সাক্ষরতার এক আশ্চর্য বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছিল।
অন্ধকার যুগের আরবরা এমন এক ধর্মে ঈমান এনেছিল যে ধর্মের নবী মুসলমান শিশুদের লিখন-পঠন শিক্ষাদানকে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। ঐ ধর্মের নবী তাঁর কিছু সঙ্গীকে অনারব বিভিন্ন ভাষা ,যেমন সুরিয়ানী ,হিব্র “ ও ফার্সী শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশ ব্যক্তির একদল সহযোগী ছিলেন। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বা কয়েকজন মিলে একেকটি বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। এই অজ্ঞ আরবরা এমন ধর্ম গ্রহণ করেছিল যার ঐশী গ্রন্থে কলম ও লেখার শপথ করা হয়েছেن و القلم و ما يسطرون ‘ নুন-শপথ কলমের এবং সেই বিষযের যা তারা লিপিবদ্ধ করে ’ এবং যার প্রথম প্রত্যাদেশ পড়ালেখার আহ্বান দিয়ে শুরু হয়েছে :
) إقرأ باسم ربّك الّذي خلق,خلق الإنسان من علق,إقرأ و ربّك الأكرم,الذي علّم بالقلم,علّم الإنسان ما لم يعلم (
‘ পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ,সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন ,আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু ,যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন ,শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। ’ -(সূরা আলাক: 1-5)
প্রশ্ন হলো এই নবীর গৃহীত পন্থা ,তাঁর ওপর অবতীর্ণ কোরআনের লিপিবদ্ধকরণ ,পঠন ও শিক্ষণের আহ্বানের বিষয়টি তাঁর অনুসারী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কোরআন ও তাঁর প্রতি অগাধ ভালবাসা পোষণ করতেন তাঁদের অনুভূতিতে জ্ঞান ,সংস্কৃতি ,লিখন ও পঠনের প্রতি কি আগ্রহ ও সুদৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারেনি ?
কেউ কেউ কুরাইশ ও অন্যান্য আরবদের শিক্ষকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের যুক্তি এনে বলেছেন ,কুরাইশ ও আরবরা শিশুদের লিখন-পঠন শিক্ষাদান ও শিক্ষকতার পেশাকে অপমানজনক মনে করত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হওয়াকে অপমান ও ঘৃণার চোখে দেখত।
প্রথমত তাঁরা স্বীকার করেছেন আরবরা স্বল্প আয়ের অজুহাতে শিক্ষকতার পেশাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করত ও একে খারাপভাবে দেখত। এ বিষয়টি আমরা বর্তমান ইরানেও লক্ষ্য করছি। আলেম সমাজ ,শিক্ষকগণ এবং কেরানী শ্রেণী সমাজের নিম্ন বেতনভুক্তদের অন্তর্গত এবং এ কারণেই অনেকে এরূপ পেশা পরিবর্তন করে অন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।
যদি কোন যুবক শিক্ষক ,আলেম বা কেরানী পদের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে ঐ মেয়ের অভিভাবক যদি ঠিকাদার ,কাঠ মিস্ত্রী ,ঝুড়ি বিক্রেতা বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও হয়ে থাকে আর তাদের মেয়ে অশিক্ষিতও হয় তবুও বিয়ে দিতে রাজী হয় না। তারা কোন শিক্ষক ,আলেম বা কেরানীর চেয়ে কোন ঠিকাদার বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু কেন ? এ কারণে কি যে ,তারা শিক্ষা ও নৈতিকতাকে হীন ও মন্দ মনে করে ? অবশ্যই না। এ বিষয়টি শিক্ষার সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয় ;বরং এরূপ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বিবাহ দিতে হলে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় ,কিন্তু সকলের এমন মানসিকতা নেই।
আজব যুক্তি এই যে ,কুরাইশদের কোন এক ব্যক্তি গ্রন্থ পাঠের কারণে এক বালককে তিরস্কার করেছে তাই আরবরা জ্ঞান ও লিখন-পঠনের শত্রু এবং যেখানেই তারা গ্রন্থ পেয়েছে পুড়িয়ে দিয়েছে। আরবদের এরূপ কথা ইরানী কবি ও সাহিত্যিক ওবায়েদ যাকানীর কবিতার মত যিনি বলেছেন ,
‘ হে মহৎ জন জ্ঞান অন্বেষণের পথ কর না অবলম্বন
এতে এক দিনের রুজী যোগাতেই তুমি হবে অক্ষম।
গান ও কৌতুক শেখার পথ ধর
আপন বাক প্রাঞ্জলতায় সকলকে খুশী কর। ’
এখন ইরানী এ কবির কথার সূত্র ধরে কি আমরা বলব ইরানীরা জ্ঞান ও শিক্ষার বিরোধী ও শত্রু। তাই যেখানেই তারা গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার পায় তাতে অগ্নি সংযোগ করে। শুধু তাই নয় তারা গান ও কৌতুক করে জীবিকার্জনের পক্ষপাতী। কিংবা আবু হাইয়ান তাওহীদী অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের কারণে তাঁর সকল গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন-এ যুক্তিকে ভর করে কি আমরা বলব তাঁর দেশীয়রাও (ইরানীরা) জ্ঞানবিরোধী ও গ্রন্থ ভস্মীভূত করে।
আবু রাইহান আল বিরুনী খাওয়ারেজম সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তার কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। তদুপরি তিনি অন্যান্য জ্ঞানের বাইরেও একজন বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক হিসেবে ভিত্তিহীন কথা বলতে পারেন না। যেহেতু তিনি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন ব্যক্তিত্ব এবং এ ঘটনার সময়কাল হতে তাঁর ব্যবধান খুব বেশি নয় সেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে ঘটনাটি সত্য হওয়ার। তা ছাড়া তিনি স্বয়ং খাওয়ারেজমের অধিবাসী ছিলেন। খাওয়ারেজম ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সময় অর্থাৎ 93 হিজরীতে বিজিত হয়।
কিন্তু আবু রাইহান যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা শুধু খাওয়ারেজম ও খাওয়ারেজমী ভাষা সম্পর্কিত। এর সঙ্গে পারস্যের পাহলভী ভাষা ও আভেস্তার মত ধর্মীয় গ্রন্থ ধ্বংসের কোন সম্পর্ক নেই।
দ্বিতীয়ত স্বয়ং আবু রাইহান তাঁর ‘ সাইদানা ’ বা ‘ সাইদালাহ্ ’ নামক গ্রন্থে জ্ঞানগত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনায় ভাষাসমূহের দক্ষতার তুলনা করতে গিয়ে আরবী ভাষাকে খাওয়ারেজমী বা ফার্সীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষত খাওয়ারেজমী ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন , ‘ এই ভাষা কখনই জ্ঞানগত বিষয় বর্ণনার উপযোগী ছিল না। যদি কোন ব্যক্তি এ ভাষায় এরূপ বিষয় বর্ণনা করতে চায় তবে তা ছাদের পার্শ্বস্থ পানির পাইপ হতে উট বের হওয়ার মত বিষয়। ’ 154
সুতরাং খাওয়ারেজমী ভাষায় যদি মূল্যবান কোন গ্রন্থ থাকত তবে আবু রাইহান এ ভাষাকে এতটা অক্ষম বলে পরিচয় দিতেন না। তাই তিনি খাওয়ারেজমের যে গ্রন্থসমূহ ধ্বংস হয়েছে বলেছেন তা ইতিহাসের কিছু গ্রন্থ বৈ অন্য কিছু ছিল না। তদুপরি খাওয়াজেমের অধিবাসীদের সঙ্গে এরূপ আচরণ ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সময় ঘটেছিল ,খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় নয়। যদি প্রকৃতই ঘটনাটি সত্য হয়ে থাকে তবে তা অমানবিক ও অনৈসলামী ছিল।155 যে সকল মুসলিম বিজয়ী পারস্য ও রোম জয় করেন সাধারণত তাঁরা রাসূল (সা.)-এর সাহাবী ও তাঁর (রাসূলের শিক্ষা) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বিধায় পরবর্তী শাসকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল।
তাই বনী উমাইয়্যার শাসনামল যা ইসলামী খেলাফতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সময় বলে পরিগণিত সে সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনাকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিদের দ্বারা ইরান বিজিত হওয়ার ঘটনার তুলনা হতে পারে না।
যা হোক ,এখানে উল্লেখ্য যে ,ইরানে যদি কোন গ্রন্থাগার সে সময়ে বিদ্যমান থেকে থাকে তা খাওয়ারেজমে ছিল না ;বরং তিসফুন (মাদায়েন) ,হামেদান ,নাহভান্দ ,ইসফাহান ,ইসতাখর ,রেই ,নিশাবুর বা আজারবাইজানে ছিল এবং পাহলভী ভাষায় ছিল। ইসলামী শাসনামলে ইরানের যে সকল গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয় তন্মধ্যে ‘ কালিলা ও দিমনা ’ গ্রন্থটি ইবনে মুকাফফাহ্ কর্তৃক এবং তাঁর পুত্র কর্তৃক অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা বইয়ের কিয়দংশ পাহলভী ভাষা হতে আরবীতে অনূদিত হয়েছিল ;খাওয়ারেজমী বা অন্য ভাষা হতে নয়।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন , “ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান পাহলভী ভাষার গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদের নির্দেশ দেন। ”
কোন হামলা বা আক্রমণের কারণে যদি বিশেষ কোন ভাষা বিলুপ্ত হয় ও সে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মূর্খে পরিণত হয় এবং এ নিরক্ষরতার কারণে পূর্ববর্তী ইতিহাস ভুলে যায় তবে বুঝতে হবে সে ভাষা সীমিত ও আঞ্চলিক কোন ভাষা। এটি স্বাভাবিক ,কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা সীমাবদ্ধতার কারণে জ্ঞানধারক হতে পারে না এবং সম্ভব নয় এ ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ,অংকশাস্ত্র ,প্রকৃতিবিজ্ঞান ,জ্যোতির্বিজ্ঞান ,সাহিত্য ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে পুস্তক রচনার।
যদি কোন ভাষা এতটা ব্যাপক হয় যে ,তা বিভিন্ন জ্ঞানসম্বলিত পুস্তক রচনা ও অনূদিত হওয়ার উপযোগী তাহলে কোন এক আক্রমণের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হতে পারে না এবং জনগণ এতে মূর্খে পরিণত হওয়া সম্ভব নয় । আমরা জানি মোগলদের আক্রমণের চেয়ে ভয়াবহ কোন আক্রমণ কখনও হয়নি। গণহত্যা প্রকৃত অর্থেই তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল ,গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারসমূহ তারাই সর্বাধিক হারে ধ্বংস ও ভস্মীভূত করেছিল। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর আক্রমণও আরবী ও ফার্সীর জ্ঞানগত নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি ;বরং পূর্ববর্তী মোগল ও পরবর্তী প্রজন্মের (মোগলদের) মধ্যে সংস্কৃতির ভেদরেখা টেনে দিয়েছিল। কারণ আরবী ও ফার্সীর জ্ঞানগত ভিত্তি এতটা দৃঢ় ও ব্যাপক ছিল যে ,মোগলদের কয়েক দফা গণহত্যাতেও তা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বোঝা যায় খাওয়ারেজমে যা বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা যারথুষ্ট্র ধর্মীয় ও সাহিত্যের কিছু গ্রন্থ বৈ অন্য কিছু ছিল না। আবু রাইহান আল বিরুনীও এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি। তাঁর লেখনীর প্রতি দৃষ্টি দিলে এটিই বোঝা যায়।
আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের কর্তৃক গ্রন্থাগার ধ্বংসের যে বিবরণ ডক্টর মুঈন দিয়েছেন তা আরো হাস্যকর। তিনি এ ঘটনাকে বিজয়ী আরবগণ কর্তৃক ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংসের দলিল বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের যুল ইয়ামিনাইন আব্বাসীয় খলীফা আমিন ও মামুনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে খোরাসানের সেনাদলের প্রধান ছিলেন। তিনি হারুনুর রশীদের পক্ষ হতে তাঁর পুত্র মামুনের সহযোগী ছিলেন এবং হারুনের অপর পুত্র আমিনের নিযুক্ত আরব সেনাপতি আলী ইবনে ঈসার ওপর ঐ যুদ্ধে জয়ী হন ও বাগদাদকে মামুনের অধীনে আনেন। তিনিই আমিনকে হত্যা করেন এবং মামুনের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন।
আবদুল্লাহর পিতা তাহের একজন আরববিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারুনুর রশীদের জ্ঞানকেন্দ্রে (বাইতুল হিকমাহ্) কাজ করতেন এবং আরবদের ত্রুটি ও অসৎ দিক তুলে ধরে ‘ মাসালিবে আরব ’ নামক গ্রন্থ রচনা করে হারুন কর্তৃক ত্রিশ হাজার দিনার বা দিরহাম পুরস্কৃত হন।156
অগ্নি সংযোগের দায়ে অভিযুক্ত আবদুল্লাহ্ তাহেরীয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রথম বারের মত তিনি খোরাসানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন ইরানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
স্বাভাবিকভাবেই আবদুল্লাহ্ও তাঁর পিতার ন্যায় আরববিরোধী ছিলেন। তথাপি ইসলামের ঐতিহাসিক আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করুন এই আরববিরোধী ইরানী বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ্ বাগদাদের খলীফাকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার মত শক্তি অর্জন করলেও ইসলামপূর্ববর্তী ইরানী গ্রন্থসমূহকে কোরআনের উপস্থিতিতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। মিস্টার ব্রাউন তাঁর ‘ সাহিত্যের ইতিহাস ’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন :
“ এক দিন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের দরবারে (নিশাবুরে) আসে এবং একটি প্রাচীন ফার্সী গ্রন্থ উপহার দেয়। তিনি প্রশ্ন করেন: এটি কি গ্রন্থ ? সে জবাব দেয়: ওয়ামেক ও আজরার সেই কাহিনী যা সাহিত্যিকরা রচনা করে সাসানী সম্রাট আনুশিরওয়ানকে উপহার দিয়েছিল। তিনি বললেন: আমরা কোরআন অধ্যয়ন করি ,আমাদের এ গ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস আমাদের জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া যে গ্রন্থ তুমি এনেছ তা মাজুসীরা (অগ্নিপূজক) রচনা করেছে বিধায় আমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য। অতঃপর গ্রন্থটি পানিতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন এবং ফার্সী ভাষায় মাজুসী চিন্তার যে গ্রন্থই পাওয়া যাবে তা ধ্বংস করার হুকুম জারি করেন। ”
কেন তিনি এমনটি করেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে সম্ভবত ইরানী যারথুষ্ট্রদের প্রতি ঘৃণা হতেই তিনি এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। যা হোক এ কর্ম আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের নামের এক ইরানী করেছিল ;আরবরা নয়। এখন আমরা আবদুল্লাহর এ কর্মকে সকল ইরানীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলতে পারি কি ? আমরা কি বলব ইরানীরা কোরআন ব্যতীত যা পায় তা ভস্মীভূত করে দেয় ? অবশ্যই না।
আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের কাজটি সঠিক ছিল না। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যখন এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নতুন সংস্কৃতির প্রেমিক ও অনুসারীরা কখনও কখনও বাড়াবাড়ি করে পুরাতন সংস্কৃতির নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নকে উপেক্ষা করে থাকে। ইরানীরাও ইসলামের নতুন সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে পুরাতন ও নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়েছিল।
আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের ন্যায় অনেক ইরানীই ছিলেন যাঁরা আরববিরোধী (আত্মগর্বী সেই সব আরব যারা অন্যদের এক রক্তবংশের অধীনে আনতে চেয়েছিল) হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ও গোঁড়ামি ভাব প্রকাশ করতেন এবং মাজুসীদের স্মৃতিচিহ্নের ওপর ঐ গোঁড়ামির প্রকাশ ঘটাতেন।
আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের ন্যায় গ্রন্থসমূহ ধ্বংসের নজীর ইতিহাসে যদি আরো থেকে থাকে তবে এ বিষয়টি দলিল হিসেবে উপস্থাপন অপ্রয়োজনীয়। বিশ্ব এর চেয়েও ব্যাপক আকারে গ্রন্থ ধ্বংসের সাক্ষী। আমাদের সময়ে আহমাদ কাসরাভী গ্রন্থ ভস্মীকরণ উৎসব পালন করেছেন। খ্রিষ্টানরা স্পেনের বিপর্যয়ে মুসলমানদের গণহত্যা ও তাদের আশি হাজার গ্রন্থ অগ্নিতে ভস্মীভূত করে।157 জর্জি যাইদান (খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক) স্বীকার করেছেন ,ক্রুসেডের যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কয়েক লক্ষ গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়েছিল।158 তুর্কীরা মিশরে গ্রন্থাগার ধ্বংস করে।159 সুলতান মাহমুদ গজনভী রেই শহরে গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দেন।160 মোগলরা বাগদাদ ও খোরাসানের গ্রন্থাগারসমূহ ভস্মীভূত করে।161 যারথুষ্ট্ররা সাসানী আমলে মাযদাকীদের গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেয়।162 আলেকজান্ডার ইরানে গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগ করেন।163 রোমানরা প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ আরশমিদাদের গ্রন্থগুলো অগ্নিদগ্ধ করে।164 আমরা পরবর্তীতে খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিষয়ে আলোচনা করব।
জর্জ সার্টন তাঁর ‘ বিজ্ঞানের ইতিহাস ’ গ্রন্থে বলেছেন ,
“ ভাববাদী গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাস তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছিলেন: খোদাগণ আছেন আমরা তা যেমন বলতে পারি না ,তেমনি তাঁরা নেই এমনও বলতে পারি না। কারণ এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের সামনে তা প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রধান যে বিষয় তা হলো: খোদ এ বিষয়টির অস্পষ্টতা এবং মানুষের স্বল্পায়ু। ” 165
সার্টন বলেছেন , “ এ কারণেই খ্রিষ্টপূর্ব 411 সালে তাঁর গ্রন্থসমূহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে এনে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। ইতিহাসে গ্রন্থ ভস্মীভূতকরণের প্রথম ঘটনা হিসেবে এটি বিধৃত হয়েছে। ” 166
ইসলামী বিশ্বে গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন নিষিদ্ধ হওয়া এবং একশ ’ বছর তা অব্যাহত থাকার ঘটনাটি জনশ্রুতি মাত্র। যদিও আমরা এই গ্রন্থের তৃতীয়াংশ ‘ ইসলামে ইরানীদের অবদান ’ শীর্ষক আলোচনার সাংস্কৃতিক অংশে ‘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন কখন শুরু হয়েছিল ’ শিরোনামে এ বিষয়ে আলোচনা করব তদুপরি এখানেও কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি বিশেষত দ্বিতীয় খলীফা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন নিষিদ্ধ করেননি ;বরং হাদীস লিপিবদ্ধকরণ অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন।
ইসলামের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর হাদীস সংকলনের বিষয়ে হযরত উমর ও কিছু সাহাবী একদিকে এবং হযরত আলী (আ.) ও কিছু সাহাবী অন্যদিকে অবস্থান নেন। তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা দেখা দেয়।
হযরত উমরসহ প্রথম দল হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা জায়েয মনে করলেও তা লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলন মাকরুহ মনে করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এতে করে কোরআনের গুরুত্ব কমে যাওয়া ও হাদীসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ভয় ও সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত আলীসহ দ্বিতীয় দল প্রথম হতেই হাদীস সংকলনকে উৎসাহিত করতেন। আহলে সুন্নাত দ্বিতীয় খলীফার অনুকরণে একশ ’ বছর হাদীস সংকলন হতে বিরত থাকে। কিন্তু একশ ’ হিজরী হতে তারাও হযরত আলী (আ.)-এর মতের অনুসরণ শুরু করলে প্রথম মতটি পরিত্যক্ত হয়। এ কারণেই হাদীস সংকলনে শিয়ারা সুন্নীদের চেয়ে এক শতাব্দী অগ্রগামী। সুতরাং এ বিষয়টি সঠিক নয় যে ,আরবদের মধ্যে যে কোন প্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন নিষিদ্ধ ছিল। তাই এ যুক্তিও সঠিক নয় যে ,যেহেতু তারা সংকলনের বিরোধী ছিল সেহেতু অন্যদের লিখিত গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করেছে। প্রথমত এই নিষিদ্ধের বিধান শুধু হাদীসের বিষয়ে ছিল ,অন্য বিষয়ে নয়। দ্বিতীয়ত আহলে সুন্নাতের মধ্যে এটি বিদ্যমান থাকলেও শিয়াদের মধ্যে ছিল না এবং এ বিষয়টির সঙ্গে গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনের কোন সম্পর্ক নেই।
জর্জি যাইদান তাঁর ‘ তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ’ এবং ডক্টর যাবিউল্লাহ্ সাফা তাঁর ‘ তারিখে উলুমে আকলী ’ গ্রন্থে এ বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন এখানে তার উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। ডক্টর সাফা বলেছেন :
“ অন্যান্য মুসলমানদের মতো আরবদেরও বিশ্বাস ছিলإنّ الإسلام يهدم ما قبله অর্থাৎ ইসলাম পূর্ববর্তী সকল কিছুকে ধ্বংস করে। এ কারণেই মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মেছিল কোরআন ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ কোরআন অন্যান্য সকল ঐশীগ্রন্থের রহিতকারী এবং অন্যান্য ধর্মসমূহের বিলোপ সাধনকারী। শরীয়তের ইমামরাও তাই কোরআন ব্যতীত অন্য সকল ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করেছিলেন।
বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা.) একদিন হযরত উমরের হাতে তাওরাতের কিছু পাতা দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ক্রোধে তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে ওঠে। তিনি বলেন :
ألم اتكم بِها بيضاء نقيّة و الله لو كان موسى حيّا ما وسعه إلّا أتّباعي
‘ আমি কি তোমাদের জন্য পবিত্র ও উজ্জ্বল এক ধর্ম আনি নি ? আল্লাহর শপথ! যদি হযরত মূসাও এখন জীবিত থাকতেন তাহলে আমার শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পথ ছিল না। ’
অতঃপর বলেন :
) لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذّبوهم و قولوا آمنّا بالّذي أنْزل علينا و أنزل إليكم و إلهنا و إلهكم واحد (
‘ আহলে কিতাবরা ধর্মের নামে যা বলে তা সত্যায়নও কর না আবার মিথ্যাও বল না ;বরং বল আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমাদের নিকট যা এসেছে (অর্থাৎ প্রকৃতই যা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন) আমরা তার প্রতি বিশ্বাসী এবং আমাদের ও তোমাদের উপাস্য একই। ’
সে সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত একটি হাদীস হলো :
كتاب الله فيه خبر ما قبلكم و نبأ ما بعدكم و حكم ما بينكم
‘ আল্লাহর কিতাবে (কোরআনে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর যেমন রয়েছে তেমনি তোমাদের ভবিষ্যতের খবরও রয়েছে এবং সে সাথে তোমাদের মধ্যকার মীমাংসাকারী বিষয়সমূহ। ’
পবিত্র কোরআন এ সত্যকে এভাবে বর্ণনা করেছে :و لا رطت و لا يابس إلّا في كتاب مبين ‘ কোন আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু নেই যা প্রকাশ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। ’ এ সকল বর্ণনা মুসলমানদের মধ্যে এক দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। তাই তারা কোরআন ও হাদীসের ওপর নির্ভর করাকে যথেষ্ট মনে করত ও অন্যান্য গ্রন্থ ও নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত...। ’
আমি এই মনীষীদের কথায় আশ্চর্য বোধ করছি। তাঁরা কি জানেন নাالإسلام يهدم ما قبله হাদীসটির অর্থ হলো ইসলামের আগমনের ফলে সকল অতীত ধর্মীয় আচার ও নিয়ম-রীতি অচল ঘোষিত হয়েছে। মানুষ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এখন পর্যন্ত এই বাক্য হতে এরূপ অর্থই বুঝেছেন। এ হাদীস জাহেলী যুগের সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিশেষত মুশরিক ও আহলে কিতাবের অধর্মীয় আচারসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অর্থাৎ ধর্মের নামে যে সকল অধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা অবৈধ ঘোষণা করেছে। এর সঙ্গে ধর্মীয় নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান বহির্ভূত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। অন্য একটি হাদীসالإسلام يجبّ ما قبله ‘ ইসলাম পূর্ববর্তী বিষয়সমূহকে বিলুপ্ত করে ’ এর অর্থ পূর্ববর্তী বিষয়ের ওপর আবরণ টেনে দেয় ও বর্তমানের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে না। যেমন ইসলামী আইনে কাউকে আহত বা নিহত করার মত অন্যায় সাধিত হলে ‘ দিয়াত ’ বা ‘ কিসাস ’ -এর ন্যায় বিশেষ বিধান রয়েছে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশরিক অবস্থায় যদি কেউ এরূপ অন্যায় করে থাকে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর তার পূর্ববর্তী অপরাধকে ধরা হয় না। সকল মুসলমানই এ বাক্য হতে এমন অর্থ বোঝে। কিন্তু এই মনীষীরা এ সব বাক্যের যে অর্থ বোঝেন প্রকৃত অর্থ হতে তার ব্যবধান অনেক বেশি।
তা ছাড়া হযরত উমরের হাদীসটিতে রাসূল (সা.) বলেছেন ,কোরআন ও সর্বশেষ শরীয়তের আগমনের ফলে তাওরাত ও হযরত মূসার শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। তাই নবী কোন গ্রন্থই ,এমনকি ধর্মীয় হলেও তা অধ্যয়ন করতে নিষেধ করেন নি। তিনি কেবল রহিত ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়নে নিষেধ করেছেন। মুসলমানরা যেন রহিত কোন শরীয়তের সঙ্গে ইসলামী শরীয়তের মিশ্রণ না ঘটায় এজন্যই তাওরাত অধ্যয়নে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর নবী (সা.) বলেছিলেন আহলে কিতাবের হতে তা শ্রবণ কর কিন্তু তা সত্যায়ন বা মিথ্যা প্রতিপন্ন কোনটিই কর না। তার মধ্যে ধর্মীয় কাহিনী ও শরীয়তের বিধান উভয়টিই বিদ্যমান এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি সত্য। নবী (সা.) তাঁর এ বাক্যের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন ,আহলে কিতাবদের নিকট যা রয়েছে তা সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত এবং তোমরা যেহেতু পার্থক্য করতে সক্ষম নও সেহেতু সত্যায়ন কর না কারণ তা মিথ্যা হতে পারে আবার মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না হয়তো তা সত্য। এ বিষয়টি নাহজুল বালাগাতেও এসেছে যে ,কোরআনে অতীতের ঘটনা ,ভবিষ্যতে যা ঘটবে এবং মানুষের মধ্যে মীমাংসাকারী বিধানসমূহ রয়েছে। এ বাণীটি ধর্মীয় বিধান ,পরকালীন জীবন ও ধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে কোরআনের আগমনের ফলে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে (প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে)।
সবচেয়ে হাসির বিষয় হলো সূরা আনআমের 59 নং আয়াতের মাধ্যমে দলিল উপস্থাপন- যেখানে বলা হয়েছে ,কোন আদ্র ও শুষ্ক বস্তু নেই যা প্রকাশ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। আমার জানা মতে কোন তাফসীরকারই এ আয়াতটিতে ‘ প্রকাশ্য গ্রন্থ ’ বলতে কোরআন বোঝানো হয়েছে বলেন নি ;বরং প্রকাশ্য গ্রন্থ বলতে ‘ লাওহে মাহফুয ’ -কে বোঝানো হয়েছে বলেছেন।
এই আয়াত ও ঐ হাদীসগুলোর অর্থ মুসলমানগণ কখনই এই ব্যক্তিদের অনুরূপ বোঝেননি ,অথচ তাঁরা ভেবেছেন এই আয়াত ও বাণীসমূহই মুসলমানদের এ ধরনের চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে ,কোরআন ব্যতীত যে কোন জ্ঞান ও শিল্পকলার বই-ই ধ্বংস করতে হবে।
এখন আমরা ডক্টর মুঈনের চতুর্থ যুক্তিটির পর্যালোচনা করব। তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ,ইবনে খালদুন স্পষ্টভাবে ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংসের ব্যাপারে মত দিয়েছেন এবং আবুল ফারাজ ইবনুল ইবরী ,আবদুল লতিফ বাগদাদী ,কুফতী এবং হাজী খলীফা প্রমুখের বর্ণনায় কোন ভুলই নেই ,অথচ তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি মুসলমানদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের ইতিহাসকে ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন। ডক্টর মুঈন শিবলী নোমানী এবং ডক্টর মিনুয়ীও যে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন তার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন ,অথচ তাঁদের উপস্থাপিত অকাট্য দলিলসমূহের প্রতি কোন মনোযোগই দেননি।
আমরা এখানে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মতের পাশাপাশি যে বিষয়গুলো আমাদের চিন্তায়ও এসেছে তার উল্লেখ করব। অতঃপর ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ভস্মীভূত হওয়ার বিষয়ে ইবনে খালদুন ও হাজী খলীফার নামে যা বলা হয়েছে তার জবাব দেব।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ,মুসলমানদের হাতে ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংসের দাবিদাররা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগের যুক্তি নিয়ে আসেন। যখন জাহেলী যুগের আরবদের মূর্খতা ,কুরাইশদের কোন এক ব্যক্তির কোন এক বালককে গ্রন্থ পাঠের কারণে তিরস্কার ,ইরানী আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের কর্তৃক গ্রন্থসমূহ ধ্বংস ,ইসলামী শাসকদের প্রথম দেশ জয়ের শত বর্ষ পরে খাওয়ারেজমে কুতাইবা ইবনে মুসলিম কর্তৃক গ্রন্থ ভস্মীভূতকরণের মতো বিষয়সমূহ ইরানে গ্রন্থাগার ধ্বংসের প্রমাণ হিসেবে এসেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই আমর ইবনে আস-এর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি কিনা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ও দর্শন শিক্ষা করতেন তাঁর দ্বারা গ্রন্থাগার ধ্বংসের (তাও আবার ইসলামী শাসনের কেন্দ্র মদীনার খলীফার সরাসরি নির্দেশে ,খাওয়ারেজমের ন্যায় কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তে নয়) বিষয়টিও দলিল হিসেবে আসবে। এ বিষয়টি মুসলমাদের ইরানে গ্রন্থাগার ধ্বংসের দলিল হিসেবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে।
ভূমিকা হিসেবে বলতে চাই ইসলাম ও ইসলামের বিজয় সম্পর্কিত ইতিহাস সামগ্রিকভাবে (বিশেষ স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিহাস) দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছে এবং এই ইতিহাসগ্রন্থগুলো এখনও আমাদের হাতে রয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও কয়েকজন খ্র্রিষ্টান ঐতিহাসিকও আরব মুসলমানদের দ্বারা মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ক্রসেড যুদ্ধের পূর্ববর্তী কোন মুসলিম ,খ্রিষ্টান ও ইহুদী ইতিহাস গ্রন্থেই আলেকজান্দ্রিয়া বা ইরানের গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগের বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রথম বারের মত ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ ও সপ্তম হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইরাকী খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক আবদুল লতিফ বাগদাদী তাঁর ‘ আল ইফাদাহ্ ওয়াল ই ’ তিবার ফিল উমুরিল মুশাহাদা ওয়াল হাওয়াদিসিল মায়াইনাহ্ বি আরদে মিস্র ’ নামক গ্রন্থে (যা তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন ও এক কথায় সফরনামার ওপর ভিত্তি করে রচিত) ‘ আমুদুস্ সাওয়াদি ’ স্তম্ভের আলোচনায় আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের বিবরণ দিয়ে বলেছেন ,
“ এবং বলা হয়ে থাকে এই স্তম্ভ ঐ সকল স্তম্ভের একটি যার ওপর ঝুলন্ত বারান্দা ছিল এবং অ্যারিস্টটল এই বারান্দায় বসে শিক্ষা দান করতেন ও এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল যা মদীনার খলীফার নির্দেশে আমর ইবনে আস ভস্মীভূত করেন। ’
আবদুল লতিফ বলতে চান নি তাঁর স্বধর্মী খ্রিস্টানগণ এরূপ বলে থাকেন বা সাধারণ মানুষের মধ্যে এরূপ গুজব ছড়িয়েছে তাই বক্তব্য শুরু করেছেন ‘ বলা হয়ে থাকে ’ দিয়ে। আমরা সকলেই জানি হাদীস বা ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণনা করতে হলে অবশ্যই তথ্যসূত্র ও সনদ উল্লেখ করতে হয়। যেমনটি হাদীসবেত্তা ও ঐতিহাসিকগণ করে থাকেন। তাবারী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এমনটিই করেছেন। এর মাধ্যমে পাঠককে বিষয়টি গবেষণা ও যাচাই করার সুযোগ দেয়া হয় যাতে করে তথ্যসূত্র সঠিক হলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। যদি কোন হাদীস বা ঐতিহাসিক তথ্যের সনদ বা তথ্যসূত্র জানা না থাকে তাহলে তা দু ’ ভাবে বলা যায়: প্রথম পদ্ধতিতে ‘ উল্লিখিত আছে ’ বলে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত আছে অমুক বছর অমুক ঘটনা ঘটেছিল ;দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ‘ বলা হয়ে থাকে ’ বলে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়। প্রথমভাবে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বোঝা যায় বক্তা সেটি বিশ্বাস করেন যদিও অন্যরা তথ্যসূত্র ও সনদবিহীন এরূপ হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও তথ্যসূত্রহীন বর্ণনাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। এ বিষয়ের উল্লেখ করলে বলে থাকেন অমুক ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন নি অর্থাৎ ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা নেই।
কিন্তু যদি দ্বিতীয়ভাবে বর্ণনা করা হয় এবং বক্তা বা বর্ণনাকারী ‘ কথিত আছে ’ বা ‘ বলা হয়ে থাকে ’ বলে বিষয়টির উল্লেখ করেন তাহলে বোঝা যায় স্বয়ং বর্ণনাকারী বিষয়টি নির্ভরযোগ্য মনে করেন না।
আবদুল লতিফ ঘটনাটিকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি বিষয়টিকে বিশ্বাস করেন না। তদুপরি ,আবদুল লতিফ অন্তত নিশ্চিতভাবে জানতেন অ্যারিস্টটল গ্রীসে ছিলেন এবং কখনও মিশরে আসেননি। তাই ঐ বারান্দায় বসে তাঁর পক্ষে শিক্ষাদানও সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি আলেকজান্ডারের মিশর আক্রমণের পর নির্মিত হয় অর্থাৎ অ্যারিস্টটল আলেকজান্ডারের সমসাময়িক হলেও তাঁর পরে এই শহর গড়ে ওঠে ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।
সুতরাং আবদুল লতিফ বর্ণনাটি বিশ্বাস করলেও তা অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল বলে প্রতিপন্ন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিশ্চিতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কোন বর্ণনায় যদি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে যার কোন কোনটি মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাকী অংশটিও অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। তাই অ্যারিস্টটলের ঐ বারান্দায় বসে শিক্ষাদানের মতো মুসলমানগণ কর্তৃক ঐ গ্রন্থাগার ভস্মীভূতকরণও অসত্য ও ভিত্তিহীন।
সুতরাং আবদুল লতিফের বর্ণনা তথ্যগতভাবে দুর্বল যেহেতু তিনি কোন তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন নি এবং বিষয়বস্তুও দুর্বল যেহেতু তাতে স্পষ্ট একটি মিথ্যা রয়েছে। তাছাড়া বর্ণনার দিক হতেও দুর্বল যেহেতু ‘ বলা হয়ে থাকে ’ বলে শুরু করে তিনি বিষয়টির প্রতি নিজের অবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
যদি আবদুল লতিফ প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মুসলমানদের আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সময়কার কোন ব্যক্তি হতেন অথবা যারা ঐ সময়ের নিকটবর্তী তাদের হতে সরাসরি বা তাদের সূত্রে অন্য কারো হতে বর্ণনা করতেন তবে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য ছিল। কিন্তু এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ আবদুল লতিফ ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষার্ধ হতে সপ্তম হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের (17 হিজরী) সময় হতে তাঁর সময়ের ব্যবধান ছিল ছয়শ ’ বছরের মত। এই ছয়শ ’ বছরে কোন অমুসলিম বা মুসলিম ঐতিহাসিকের নিকট হতে এরূপ বর্ণনা দেখা বা শোনা যায় নি। হঠাৎ করে ছয়শ ’ বছর পর আবদুল লতিফের গ্রন্থে তা খুঁজে পাওয়া গেছে। তাঁর বক্তব্য সনদবিহীন বর্ণনা হতেও নিম্নমানের এবং বাহ্যিক বর্ণনার দিক হতেও অসত্য হিসেবে প্রমাণিত।
উপরন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মতে মুসলমানদের হাতে আলেকজান্দ্রিয়া পতনের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া কয়েকবার বিভিন্ন শক্তির হামলার শিকার হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মুসলমানরা যখন আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে তখন সেখানে পূর্বের ন্যায় কোন গ্রন্থাগারই ছিল না। শুধু কিছু ব্যক্তির হাতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল এবং চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা তা থেকে উপকৃত হতো।
এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের ‘ তারিখে তামাদ্দুন ’ 167 গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করব। তিনি বলেছেন , ‘ আবদুল লতিফের যুক্তি ও বর্ণনার দুর্বলতাসমূহ নিম্নরূপ :
1. আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ 392 খ্রিষ্টাব্দে আর্চ বিশপ তুফিনসের সময় গোঁড়া খ্রিষ্টানরা পুড়িয়ে দেয় অর্থাৎ মুসলমানগণ আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের 250 বছর পূর্বে এই গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্রন্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।
2. ধারণাকৃত ঘটনাটির সঙ্গে আবদুল লতিফ রচিত গ্রন্থের পাঁচ শতাব্দীর অধিক সময়ের ব্যবধান ছিল এবং ইতোপূর্বে কোন ঐতিহাসিকই এ বিষয়টি উল্লেখ করেন নি ,অথচ 322 হিজরীতে (933 খ্রিষ্টাব্দ) আলেকজান্দ্রিয়ার দায়িত্বশীল খ্রিষ্টান আর্চ বিশপ ‘ উতকিউস ’ আরবদের হাতে এ শহর বিজিত হওয়ার ইতিহাস বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেন নি এবং বানোয়াট বলেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছিল যা ইতিহাসের অন্যতম দুঃখজনক ঘটনা।168
উইল ডুরান্ট তাঁর উক্ত গ্রন্থে খ্রিষ্টানদের হাতে গ্রন্থাগারটি ধ্বংসের বিবরণ দিয়েছেন। আগ্রহীরা ফার্সীতে অনূদিত তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ ,নবম ও একাদশ খণ্ডটি দেখতে পারেন।
গুসতাভ লুবুন তাঁর ‘ ইসলাম ও আরব সভ্যতা ’ গ্রন্থে বলেছেন ,
“ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি ধ্বংসের জন্য মুসলমানদের অভিযুক্ত করা হয় এটি আশ্চর্যের বিষয় এজন্য যে ,কিভাবে এমন একটি বানোয়াট ও অসত্য বিষয় এতকাল ধরে প্রচারিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে! কিন্তু বর্তমানে বিষয়টির অসত্যতা প্রমাণিত হয়েছে ;বরং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ,ইসলামের পূর্বে খ্রিষ্টানরাই আলেকজান্দ্রিয়ার সকল উপাসনালয় ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেছিল সেই সাথে এই মূল্যবান গ্রন্থাগারটিও জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইসলামী শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হওয়ার সময় তেমন কিছুই সেখানে বিদ্যমান ছিল না যা মুসলমানরা পুড়িয়ে দিতে পারে। ”
খ্রিষ্টপূর্ব 332 সালে আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে এর পতন পর্যন্ত এক হাজার বছর ব্যাপী এ শহরটি পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল একটি শহর হিসেবে পরিগণিত হতো।
সম্রাট আলেকজান্ডারের প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ বাতালাসাদের সময় পৃথিবীর সকল দার্শনিক ও পণ্ডিত এ শহরে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু এ উন্নয়ন বেশি দিন অব্যাহত থাকেনি। খ্রিষ্টপূর্ব 48 সালে সিজার-এর নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে হামলা করা হয় ও এই জ্ঞানকেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অবশ্য রোমানদের রাজত্বে ও পরিচালনায় শহরটি পুনরায় উন্নত হয় ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করে। কিন্তু তাও বেশি দিন টিকে নি। কারণ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং রোমের সম্রাটের পক্ষ হতে রক্তক্ষয়ী দমন অভিযান পরিচালনার পরও তা অব্যাহত ছিল। এমতাবস্থায় রোমে খ্রিষ্টবাদ রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়। রোম সম্রাট থিওডর মূর্তিপূজকদের169 সকল খোদা ,তাদের উপাসনালয় ও গ্রন্থাগারসমূহ জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।170
আলেকজান্দ্রিয়া শহর মিশরের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর যা রোম সম্রাট আলেকজান্ডারের নির্দেশে খ্রিষ্টপূর্ব চারশ ’ অব্দে (চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীতে) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছিল ‘ আলেকজান্দ্রিয়া ’ ।
আলেকজান্ডারের মিশরীয় প্রতিনিধি ও গভর্ণরদের ‘ বাতালাসাহ্ ’ বলে অভিহিত করা হতো। তাঁরা ঐ শহরে যাদুঘর ও গ্রন্থাগার তৈরি করেন যা প্রকৃতপক্ষে একটি ‘ একাডেমী ’ ছিল এবং পরবর্তীতে জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব গ্রীকদের সমকক্ষ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।
আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানকেন্দ্রটি খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ ’ বা দু ’ শ ’ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আলেকজান্ডার ও তাঁর পরবর্তীদের শাসনামলে মিশর গ্রীকদের রাজনৈতিক অধিকারে ছিল। কিন্তু গ্রীক সভ্যতা পতনের দিকে ধাবিত হলে রোম সাম্রাজ্য-যার রাজধানী বর্তমানের ইতালীর রোম ছিল-যুদ্ধে গ্রীসকে পরাজিত করে তখন মিশর ও আলেকাজান্দ্রিয়াও রোমের রাজনৈতিক অধিকারে চলে যায়। রোম সাম্রাজ্য চতুর্থ খিষ্ট শতাব্দীতে দু ’ ভাগে বিভক্ত হয়। যথা: পূর্ব রোম-যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে তুরস্কের
ইস্তাম্বুল) এবং পশ্চিম রোম-যার রাজধানী বর্তমানে ইতালির রাজধানী রোম। পূর্ব রোম খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে। খ্রিষ্টবাদ গ্রীস ও রোম উভয় সভ্যতার ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রোমের বিভক্তির সময় হতেই ইউরোপের মধ্যযুগ (অন্ধকার যুগ) শুরু হয়। পূর্ব রোম খ্রিষ্টবাদ গ্রহণের ফলে তৎকালীন খ্রিষ্টবাদী চিন্তার প্রভাবে-যারা বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাকে খ্রিষ্টধর্মের মৌলনীতি বিরোধী মনে করত এবং দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অধার্মিক ও বিচ্যুত বলে ফতোয়া দিত-আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষা কেন্দ্রটির ওপর খড়গহস্ত হলো। 48 খ্রিষ্টাব্দে সিজারের আক্রমণের পর রোমের শাসকবর্গ দ্বিতীয় বারের মত এই শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারটি অগ্নি সংযোগ ও ধ্বংসের শিকার হলো। কনস্টানটাইন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট যিনি খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেন। কনস্টানটাইনের প্রতিনিধিগণের অন্যতম জাস্টিনিয়ান ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দীতে এথেন্সের জ্ঞানকেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন। ইতোপূর্বে চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্রটি 529 খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ ঘোষিত হয় অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর জন্মের 41 বছর ,তাঁর নবুওয়াত ঘোষণার 81 বছর ,হিজরতের 94 বছর ,তাঁর ইন্তেকালের 105 বছর এবং মুসলমানদের হাতে আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হওয়ার 120 বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিল।
এ আলোচনা হতে পরিষ্কার হলো যে ,আলেজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার মূর্তিপূজকরা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং খ্রিষ্টানরা তা ধ্বংস করেছে। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধের (যা পঞ্চম হতে ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে) পর খ্রিষ্টানরা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এ সভ্যতা তাদের সচেতনতা দান করে। অন্যদিকে মুসলমানদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর তারা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা কোরআন ,ইসলাম ,রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত বেশি অপপ্রচার ও গুজব রটাতে থাকে যাকে আধুনিক খ্রিষ্ট সভ্যতার লজ্জা বলা যেতে পারে। এই লজ্জার ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে অনেক খ্রিষ্টান লেখক গ্রন্থ রচনা করেছেন ,যেমন জন ডেভেন পোর্ট ‘ মুহাম্মদ ও কোরআনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ’ শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মুসলমানদের হাতে গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিষয়টি উপস্থাপন করে একে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলেছেন। মুসলমানদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের গুজবটি সপ্তম হিজরী শতাব্দীর পর হতে কোন কোন মুসলিম লেখকও অজ্ঞতাবশত ‘ কথিত আছে ’ , ‘ বর্ণিত হয়েছে ’ বা ‘ বলা হয়ে থাকে ’ প্রভৃতি লিখে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা জানেন না ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বদনাম ও কুৎসা রটনার উদ্দেশ্যে এ গুজব ছড়িয়েছে। গত শতাব্দী (বিংশ) হতে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলাম ও প্রথম যুগের মুসলমানদের প্রতি বর্তমান মুসলমানদের বিতৃষ্ণ করে তুলতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে । তাই পুরদাউদের মত ব্যক্তিদের দ্বারা এরূপ কাল্পনিক ও বানোয়াট কাহিনী তৈরি করিয়ে ও আবদুল লতিফের ন্যায় ঐতিহাসিকদের বিবরণকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইতিাহাসের রূপ দিয়ে শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করেছে যারা ইতিহাস সম্পর্কে তেমন অবগত নয় ।
এতক্ষণ আমরা আবদুল লতিফের বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আবুল ফারাজ ইবনুল ইবরীর বর্ণনা নিয়ে পর্যালোচনা করব।
আবুল ফারাজ ইবরী একজন ইহুদী চিকিৎসক যিনি 623 হিজরীতে এশিয়া মাইনরের মালাতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হন। আবুল ফারাজও তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে খ্রিষ্ট ধর্ম অধ্যয়নে সময় ব্যয় করেন। তিনি আরবী ও সুরিয়ানী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুরিয়ানী ভাষায় এক ইতিহাস গ্রন্থ লিখেন যার তথ্যসমূহ আরবী ,সুরিয়ানী ও গ্রীক ভাষার গ্রন্থসমূহ হতে নেয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে মুসলমানদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের কোন বিবরণই নেই। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে ‘ মুখতাছারুদ দোয়াল ’ নামে প্রকাশিত হয়। কথিত আছে এ গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয় হলো এ গ্রন্থটি সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হলেও এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা ঐ মূল গ্রন্থে নেই ,যেমন মুসলমানদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের কাহিনী।
‘ মুখতাছারুদ দোয়াল ’ গ্রন্থটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পোকুক নামের এক অধ্যাপক কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। এই ভদ্রলোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় বেশ কিছু বই লিখেছেন যেগুলো ল্যাটিন ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। এই ব্যক্তির মাধ্যমেই মুসলমানদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের বানোয়াট কাহিনীটি ইউরোপে প্রচারিত হয়। অবশেষে গত শতাব্দীতে কিছু ইউরোপীয় গবেষক যেমন গীবন ,গুসতাব লুবন ,কুরিল ও অন্যান্যদের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।
আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিবরণটি ‘ মুখতাছারুদ দোয়াল ’ গ্রন্থে এভাবে এসেছে :
‘ তৎকালীন সময়ে ইয়াহিয়া নাহভী যিনি আমাদের ভাষায় গারমাতিকুস অর্থাৎ ব্যাকরণবিদ উপাধিধারী ছিলেন তিনি আবরদের মাঝে বিশিষ্ট অবস্থান লাভ করেছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের ইয়াকুবী ধারার আভেরী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করেন। ফলে মিশরের সকল খ্রিষ্টান ধর্মযাজক তাঁর নিকট এসে উপদেশ দানের মাধ্যমে তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ধর্মযাজকগণ তাঁর একগুঁয়েমীর কারণে তাঁর পদ হতে অপসারণ করেন। এরূপ নাস্তিক অবস্থায়ই তিনি বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করেন। এ সময়ই মিশর বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনে আস মিশরে আসেন।
একদিন ইয়াহিয়া আমর ইবনে আসের নিকট উপস্থিত হলে আমর তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হন ও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান। এই বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে প্রজ্ঞাজনোচিত এমন এক বক্তব্য দান করেন যা আরবরা কখনও শুনে নি। তাঁর বক্তব্য আমর ইবনে আসের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করল যে ,তিনি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। যেহেতু আমর ইবনে আস একজন চিন্তাশীল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন সেহেতু তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সব সময় তাঁকে নিজের কাছে রাখতেন।
একদিন ইয়াহিয়া আমর ইবনে আসকে বললেন: আলেকজান্দ্রিয়ার সকল কিছু আপনার অধিকারে রয়েছে। তন্মধ্যে আপনাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ আমরা চাই না কিন্তু যে বস্তুগুলো আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই তা আমাদের অধিকারে দিন যাতে আমরা তা থেকে অধিক উপকৃত হতে পারি। আমর ইবনে আস প্রশ্ন করলেন: ঐ বস্তুসমূহ কি কি ? তিনি বললেন: দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ যা সরকারী গ্রন্থাগারে বিদ্যমান।
আমর বললেন: আমি নিজের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু করার অধিকার রাখি না। তাই মদীনায় খলীফার (হযরত উমর) নিকট হতে এ বিষয়ে অনুমতি চাইব। আমর খলীফার নিকট অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলে তিনি জবাবে লিখেন: যদি এই গ্রন্থসমূহ কোরআনের মতের অনুরূপ হয় সে ক্ষেত্রে এগুলোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই আর যদি কোরআনের মতের পরিপন্থী হয় সেগুলো ধ্বংস কর।
এ উত্তর পাওয়ার পর আমর ইবনে আস গ্রন্থাগার ধ্বংসের কাজে ব্রতী হলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার গোসলখানাগুলোর কর্মচারীদের মধ্যে গ্রন্থসমূহ বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। এভাবে ছয় মাসের মধ্যে সকল গ্রন্থ গোসলখানার পানি গরমের কাজে পুড়িয়ে ফেলা হলো। বিষয়টিকে আশ্চর্য না ভেবে তা গ্রহণ কর। ’ 171
এ বিষয়টি স্বয়ং আবুল ফারাজ ইবনুল ইবরীই বর্ণনা করে থাকুন বা প্রফেসর পোকুক উভয় ক্ষেত্রেই দুঃখজনকভাবে তাঁর কথা মত আশ্চর্য বোধ না করে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা আবদুল লতিফের বক্তব্যের পর্যালোচনায় বলেছি ঐতিহাসিক কোন বিবরণকে সনদ ,গ্রন্থ বা তথ্যসূত্র ব্যতিরেকে আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না বিশেষত ছয়শ ’ বছর পর যখন কেউ সনদবিহীনভাবে এরূপ বর্ণনা দান করে ,এমনকি পূর্বেও কেউ সনদহীন এ ঘটনার কোন বর্ণনা দেন নি। তদুপরি গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন মুসলমানগণ আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সময় সেখানে কোন গ্রন্থাগারই ছিল না অর্থাৎ যে বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা তা-ই বিদ্যমান ছিল না। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণও রয়েছে।
প্রথমত এ ঘটনার অন্যতম মূল নায়ক প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইয়াহিয়া নাহভী। সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যানুযায়ী আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের একশ ’ বছর পূর্বে পরলোক গমন করেছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে আমর ইবনে আসের সাক্ষাতের ঘটনা কাল্পনিক ।172 আশ্চর্যের বিষয় হলো শিবলী নোমানী যদিও লিখেছেন ইয়াহিয়া ঐ সাত জন দার্শনিকের একজন যাঁরা সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রোষানলে পড়ে ইরানে আগমন করেন এবং ইরান সম্রাট খসরু আনুশিরওয়ান সাদরে তাঁদের গ্রহণ করেন ,অথচ তিনি তাঁর সঙ্গে আমর ইবনে আসের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেন নি। তিনি লক্ষ্য করেননি ঐ বিশিষ্ট মনীষীদের ইরানে আগমন হতে মুসলমানদের আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সময়ের মধ্যে একশ ’ বিশ বছরের অধিক সময়ের ব্যবধান ছিল। সম্ভব নয় যে ,যে ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের একশ ’ বিশ বছর পূর্বে ছিলেন ব্যতিক্রমীভাবে জীবিত থেকে (এক অতিশয় বৃদ্ধ হিসেবে) আমর ইবনে আসের সঙ্গে দেখা করবেন। তাই যে সকল বর্ণনা গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেও ঐ সাক্ষ্যকে স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছে।
আবুল ফারাজ কর্তৃক বর্ণিত ইয়াহিয়া নাহভীর সঙ্গে আমর ইবনে আসের সাক্ষাতের ঘটনা আবদুল লতিফ কর্তৃক বর্ণিত অ্যারিস্টটলের আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষাদানের ঘটনার ন্যায়ই অবান্তর যাতে ঘটনার লেখকরা ঐতিহাসিক সময়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।
দ্বিতীয়ত কাহিনীতে বলা হয়েছে খলীফার নির্দেশ পৌঁছার পর আমর ইবনে আস গ্রন্থগুলোকে গণ-গোসলখানার কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং ছয় মাস ধরে সেগুলো গোসলখানাগুলোতে ব্যবহৃত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া সে সময় মিশরের সবচেয়ে বড় শহর ছিল এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহর বলে পরিগণিত হতো। স্বয়ং আমর ইবনে আস এই শহরের আশ্চর্যের বর্ণনা দিয়ে খলীফাকে লিখেছিলেন , ‘ এ শহরে চার হাজার গোসলখানা ,চার হাজার ভবন ও ইমারত ,চল্লিশ হাজার জিযিয়া দানকারী ইহুদী ,চারশ ’ টি সরকারী বিনোদন কেন্দ্র ,বারো হাজার সব্জি বিক্রেতা রয়েছে । তাই আমাদের ধরে নিতে হবে ছয় মাস এই গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে এই চার হাজার গোসলখানার পানি উত্তপ্ত হতো অর্থাৎ এত অধিক গ্রন্থ ছিল যে ,প্রতিদিন চার হাজার না হয়ে একটি গোসলখানার পানি উত্তপ্ত করলে ঐ গ্রন্থ দিয়ে (4 হাজারের সঙ্গে 6 মাস অর্থাৎ 180 দিন গুণ করলে দাঁড়ায় 720000 দিন বা দুই হাজার বছর) দুই হাজার বছর চলত। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো আবুল ফারাজের বর্ণনায় এসেছে ,ঐ গ্রন্থসমূহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও দর্শন সম্পর্কিত ছিল ,অন্য কোন গ্রন্থ নয়। এখন চিন্তা করে দেখব সভ্যতার জন্ম হতে ছাপাখানার সৃষ্টি পর্যন্ত যদি অনবরত দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বই বের করা হতো তাহলেও তা চার হাজার গোসলখানার ছয় মাসের পানি উত্তপ্ত করার জন্য যথেষ্ট হতো কি ?
আরো চিন্তা করে দেখব এই পরিমাণ গ্রন্থের জন্য কি পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন ? গ্রন্থসমূহ তো খড়ের গাদার মত স্তুপীকৃত ছিল না ;বরং তাকসমূহে বা আলমারীতে সাজানো ছিল। কারণ মানুষ সেগুলো অধ্যয়ন করত। চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দীতে রোম সম্রাটের পক্ষ হতে গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংসের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ধর্মযাজক আলেকান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার সম্পর্কে এরূপ বিবরণ দিয়েছেন , ‘ আমি ঐ গ্রন্থাগারের আলমারীগুলোতে কোন গ্রন্থই পাইনি। ’ 173
আবদুল লতিফ আলেকজান্দ্রিয়ায় শুধু একটি ঝুলন্ত বারান্দা দেখেছেন। এরূপ ঝুলন্ত বারান্দা কেন ইবনুল ইবরীর পরিসংখ্যানের গ্রন্থের জন্য পুরো এক শহরও যথেষ্ট নয়।
বর্তমানে ছাপাশিল্পের ও অন্যান্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত আমেরিকা ও রাশিয়ায় বৃহৎ শহর ও গ্রন্থাগার তৈরির সর্বাধিক সুবিধা রয়েছে তদুপরি আমার জানা নেই ঐ শহরগুলোর গোসলখানাগুলোকে ছয় মাস ধরে গরম রাখার মত পর্যাপ্ত গ্রন্থ সেখানে আছে কিনা ?
এ যুক্তিগুলো বর্ণিত বিষয়টি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। সম্ভবত কল্পনায় এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কথিত আছে এক ব্যক্তি আফগানিস্তানের হেরাত শহর কতটা বড় ও এ শহরে কত অধিক সংখ্যক মানুষ আছে তা বুঝাতে বলেছিল। হেরাত শহরে শুধু আহমাদ নামের এক চক্ষুবিশিষ্ট পাচকের সংখ্যা ছিল একুশ হাজার ,তাহলে বুঝুন আরো আহমাদ ছিল যারা এক চক্ষুবিশিষ্ট ও পাচক ছিল না ,আবার সবার নাম আহমাদও ছিল না ,তবে কত লোক এ শহরে বাস করত ? এক আহমাদ নামে যদি এত লোক থাকে অন্যান্য প্রতিটি নামে কত লোক হতে পারে ? অবশ্যই সৃষ্টির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সকল লোককে গণনা করলেও এত হবে কিনা সন্দেহ।
স্পষ্ট যে ,আবুল ফারাজের এই বর্ণনা আহমাদ নামের এক চক্ষুবিশিষ্ট একুশ হাজার পাচকের কাহিনীর ন্যায়। এ কারণেই এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখকগণ আবুল ফারাজের এই বর্ণনাকে শিবলী নোমানের বর্ণনা মতে কৌতুকময় মনে করেছেন।
তৃতীয়ত শিবলী নোমান এবং কিছু পাশ্চাত্য গবেষক বলেছেন ,তৎকালীন সময়ে গ্রন্থসমূহ চামড়ায় লিখিত হতো এবং কখনই তা পোড়ানোর কাজে লাগা সম্ভব নয়। তাই সেগুলোকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার অযৌক্তিক। ’ শিবলী নোমান মসিয়ে দ্যাঁ পিয়ের নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন: ‘ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পানি গরমের জন্য যখন অন্য জ্বালানী পর্যাপ্ত ছিল তখন গোসলখানার কর্মচারীরা চামড়া নির্মিত গ্রন্থসমূহ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। ’
চতুর্থত যদি বাস্তবেই আলেকজান্দ্রিয়ায় এত বড় গ্রন্থাগার থাকত তাহলে আমর ইবনে আস তার বিবরণ খলীফার নিকট লিখিত পত্রে উল্লেখ করতেন। ইতিহাসে বিধৃত তাঁর পত্রে শহরের বিনোদন কেন্দ্র ও সব্জি বিক্রেতার বর্ণনা থাকলেও কোন গ্রন্থাগারের বিবরণ নেই কেন ?
পঞ্চমত আমর ইবনে আস আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের পর নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে ‘ জিম্মি চুক্তি ’ তে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে আচরণ করতেন। অর্থাৎ তাদের প্রাণ ,সম্পদ ,পরিবার ,উপাসনালয়সমূহ প্রভৃতি রক্ষা ও সংরক্ষণ ইসলামী হুকুমতের কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো। আমর ইবনে আস মিশরের জনগণের সাথে লিখিত চুক্তিতে উল্লেখ করেন: ‘ এই নিরাপত্তা চুক্তি আমরের পক্ষ হতে মিশরের জনসাধারণের রক্ত ,প্রাণ ,সম্পদ ,গৃহ ও অন্যান্য বিষয়ের নিরাপত্তা দান করছে। ’ 174 ‘ মুজামুল বুলদান ’ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে চুক্তিতে বলা হয়েছে: ‘ মিশরের জনসাধারণের ভূমি ,সম্পদ ও পুঁজি তাদেরই মালিকানা ও অধিকারে থাকবে। কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। ’ 175
আমরা জানি আহলে কিতাবের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ এরূপ ছিল যে ,তাদের ভূমি দখলে আসলে তাদের সঙ্গে ‘ জিম্মি চুক্তি ’ করে তাদের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করত।
জিযিয়ার বিপরীতে তাদের জীবন ,সম্পদ ,সম্মান ও উপাসনালয়সমূহের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিত। আলেকজান্দ্রিয়াতেও তাই করা হয়েছে। যদি আবুল ফারাজ তাঁর বর্ণনায় বলতেন ,মুসলমানরা তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই এই কাজ করেছিল তবে হয়তো কেউ কেউ বিশ্বাস করত। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মতে আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের বেশ পরে ইয়াহিয়া নাহভীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খলীফার নির্দেশে তা করা হয়েছে। এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে ,মুসলমানরা কারো সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করার পর এমন কাজ করবে কারণ তা তাদের নীতির পরিপন্থী।
ষষ্ঠত আমর ইবনে আস সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি তা এ বিষয়টিকে সমর্থন করে না। কারণ আমর ইবনে আস একজন স্বাধীন চিন্তার বিচক্ষণ ও দক্ষ পরিচালক ছিলেন ,এমনকি নিজে যা মনে করতেন খলীফাকে যেভাবেই হোক তা বুঝিয়ে বাধ্য করতেন। ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে খলীফা হযরত উমর মিশর জয়ের তেমন আগ্রহ পোষণ করেননি ,কিন্তু আমর ইবনে আস তাঁকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করেন ,এমনকি বলা হয়েছে ,খলীফার অনুমতি পত্র আসার পূর্বেই তিনি মিশরে আক্রমণ চালান। ইবনুল ইবরীর বর্ণনা মতে ইয়াহিয়া নাহভী আমর ইবনে আসের প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রজ্ঞাজনোচিত জ্ঞান হতে লাভবান হতেন। তাই আমর এমনভাবে খলীফাকে পত্র লিখতেন যাতে তাঁর বন্ধুর পছন্দের গ্রন্থাগারটি সংরক্ষিত হয়। যদি খলীফা এর বিপরীত কিছূ করতেন তাহলে দ্বিতীয়বার তাঁকে পত্র লিখে বুঝানোর চেষ্টা করতেন ও তাঁর বন্ধুর প্রাণ হতে প্রিয় গ্রন্থসমূহকে রক্ষার প্রচেষ্টা নিতেন। তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার বিজয়ী হিসেবে আমর ইবনে আসের নীতি একজন অত্যাচারী শাসক যেমন কুতাইবা ইবনে মুসলিমের ন্যায় ছিল না ;বরং তিনি সেখানে সংস্কার ,নির্মাণ ও পুনর্গঠনের ব্রত নিয়ে কাজ করতেন। উইল ডুরান্ট বলেছেন :
‘ আমর ন্যায়ের সাথে শাসন করতেন। ভূমিকর ও রাজস্বের একটি বিরাট অংশ খাল খনন ,পুল সংস্কার এবং নীল নদ হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত খালটির পুনর্খননে ব্যয় করতেন। এর ফলে জাহাজসমুহ ভূমধ্যসাগর হতে ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করতে পারত। খালটি 114 হিজরীতে দ্বিতীয়বারের মত ভরাট ও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ’ 176
যে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ এত বেশি তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার ধ্বংস করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।
খলীফা উমর যদিও রুক্ষ্ণ প্রকৃতির ছিলেন কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাঁর দূরদর্শিতার বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না ,এমনকি তিনি সব দায়িত্ব যাতে নিজে পালন না করতে হয় এজন্য অন্যদের পরামর্শ নিতেন। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বিশেষত হিজাযের বাইরের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য পরিষদ গঠন করতেন যার নমুনা ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে। হযরত আলী (আ.)ও ‘ নাহজুল বালাগা ’ য় এরূপ দু ’ টি বিষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। কোন ইতিহাস গ্রন্থেই পাওয়া যায় নি যে ,তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের বিষয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেছিলেন। এমন একটি বিষয়ে তিনি পরামর্শ ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেবেন তা সম্ভব নয়। যদি খলীফ উমর এমন চিন্তা পোষণ করতেন ,কোরআনের উপস্থিতিতে অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন নেই তাহলে নিঃসন্দেহে এ চিন্তাও করতেন ,সমজিদ থাকতে গীর্জা ,ইহুদীদের উপাসনালয় ও অন্যান্য ধর্মের মন্দিরসমূহও থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তবে কেন তিনি ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,এমনকি যারথুষ্ট্রদের অগ্নিমন্দিরসমূহও সংরক্ষণ করতেন এবং ইসলামী হুকুমতের জন্য জিম্মি শর্তানুযায়ী তার সংরক্ষণ দায়িত্ব বলে মনে করতেন ?
সপ্তমত যদি ধরেও নিই আমর ইবনে আস এ রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন তদুপরি কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি আলেজান্দ্রিয়ার ইহুদী ও খ্রিস্টান অধিবাসী তাদের দীর্ঘদিনের অর্জন ঐ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই জ্বালানী হিসেবে গ্রহণ করল ও পুড়িয়ে দিল ? অথচ তারা ঐ গ্রন্থগুলো গোপনে লুকিয়ে ফেলতে পারত।
কাফতীর বর্ণনাও আবুল ফারাজের বর্ণনার অনুরূপ। তাই যে সকল ত্রুটি আবুল ফারাজের বর্ণনায় রয়েছে তাঁর বর্ণনাতেও তা রয়েছে। আবুল ফারাজ যেমন সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত তাঁর বিস্তারিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ঘটনার উল্লেখ করেন নি ,কিন্তু আরবীতে তাঁর ঐ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদে তা এনেছেন আশ্চর্যজনকভাবে কাফতীও তাঁর মিশরের ইতিহাস গ্রন্থে এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি বর্ণনা করেন নি।177 কিন্তু তাঁর দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক ‘ আখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা ’ নামক গ্রন্থে ইয়াহিয়া নাহভীর জীবনী আলোচনায় কোন সূত্র ছাড়াই উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ঐ ঘটনার অন্যতম নায়ক ইয়াহিয়া নাহভী সম্পর্কে কাফতীর বর্ণনাও পূর্বের ন্যায় এবং সেখানেও দর্শন গ্রন্থের পরিমাণ চার হাজার গোসলখানার ছয় মাসের জ্বালানীর সমপরিমাণ বলা হয়েছে।
তবে কাফতীর দাবি অনুযায়ী ইয়াহিয়া নাহভী প্রথম জীবনে নাবিক ছিলেন পরে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জ্ঞানের পিপাসা জাগ্রত হলে দর্শন ,চিকিৎসা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয়ভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপের পদমর্যাদা লাভ করেন।
মোট কথা ,ইয়াহিয়া নাহিভীর জীবনী ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট বিষয়। যতটুকু জানা যায় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহিয়া নাহভী নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি একদিকে দার্শনিক ,অন্যদিকে আর্চ বিশপ ছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটল ও আবারকিলুসের মতামত খণ্ডন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। খ্রিষ্টধর্মের মৌল বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একটি গ্রন্থও লিখেছেন। ইবনে সিনা আবু রাইহান বিরুনীর প্রতি লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রে এই দার্শনিকের তীব্র সমালোচনা করে তাঁর মতকে সাধারণ খ্রিষ্টানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে রচিত বলেছেন। অন্যদিকে ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেসত ’ গ্রন্থে ইয়াহিয়া নাহভীর সঙ্গে আমর ইবনে আসের সাক্ষাতের কথা লিখেছেন ,কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। আবু সুলাইমান মানতেকী তাঁর ‘ সাওয়াবুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থে বলেছেন ,তাঁকে খলীফা উসমান ও মুয়াবিয়ার আমলে দেখা গেছে। তদুপরি বলা যায় ইবনুন নাদিম ও আবু সুলাইমানের বর্ণনা হয় ভিত্তিহীন নতুবা খলীফা উসমান ও মুয়াবিয়ার শাসনামলে যে ইয়াহিয়া ছিলেন তিনি ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছিলেন ,যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপ ছিলেন না এবং অ্যারিস্টটলের মত খণ্ডন করে গ্রন্থও লিখেননি। অসম্ভব নয় যে ,যাঁরা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের কাহিনী তৈরি করেছেন তাঁরা ইবনুন নাদিম ও আবু সুলাইমানের গ্রন্থ হতে ইয়াহিয়া নাহভীর নামটি ব্যবহার করেছেন। যা হোক এটি প্রমাণিত যে ,আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ দার্শনিক ,চিকিৎসক ,আর্চ বিশপ ও অ্যারিস্টটলের মতবিরোধী ইয়াহিয়া নাহভী মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আসের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।
এখন আমরা ইবনে খালদুনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করব। তিনি সরাসরি ইরানের গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিষয়ে কথা বলেননি। যদি আমরা ইবনে খালদুনের মূল ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য না করে পুর দাউদের ‘ ইয়াশতা ’ যেখান হতে ডক্টর মুঈন বর্ণনা করেছেন তার ওপর নির্ভর করি তদুপরি বলতে হবে ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আবদুল লতিফের মত এক চিকিৎসক যিনি ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন বা আবুল ফারাজ যিনিও এক চিকিৎসক তাঁদের মত নন ,এমনকি ‘ তারিখুল হুকামা ’ র লেখক কাফতীর সঙ্গেও তিনি তুলনীয় নন। তিনি নিজে একজন ঐতিহাসিক ও সর্বজনীন ইতিহাস রচয়িতা। তাই তিনি যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট মত দেন তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোন তথ্যসূত্র তাঁর হাতে ছিল।
কিন্তু দুঃখজনক হলো ইবনে খালদুনও এ বিষয়ে মতামত দেননি এবং কর্মবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। তিনিও তাঁর বক্তব্যকে ‘ এমনটি বলা হয়ে থাকে ’ বলে শুরু করেছেন। তদুপরি ইবনে খালদুন তাঁর বক্তব্যের মাঝে এমন এক বাক্য যোগ করেছেন যা ঘটনাটির ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। তিনি প্রথমে একটি সামাজিক মৌলনীতির কথা বলেছেন। আর তা হলো যেখানেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও নগর উন্নয়ন ঘটে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানসমূহের বিস্তার ঘটে ;যদিও অধিকাংশ সমাজবিদ তাঁর এই মৌলনীতি অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। অতঃপর তিনি এই মৌলনীতির ভিত্তিতে বলেছেন যেহেতু ইরানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও নগর উন্নয়ন ঘটেছিল সেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান প্রসার লাভ না করে পারে না। তিনি বলেন , ‘ বলা হয়ে থাকে আলেকজান্ডার ইরান আক্রমণের পর সম্রাট দারাকে হত্যা করেন এবং বৃহৎ এক রাষ্ট্রের ওপর তিনি প্রভুত্ব লাভে সক্ষম হন ও প্রচুর গ্রন্থ তাঁর হস্তগত হয়। সে সময়েই বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ইরান হতে গ্রীসে স্থানান্তরিত হয়। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইরান জয়ের পর খলীফা উমরকে পত্র লিখেন... । ’
আলেকজান্ডার ইরান হতে গ্রীসে বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়ে গেছেন ও তাঁর মাধ্যমে ইরান বিজিত হওয়ার ফলে গ্রীস নতুন এক জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিল কোন ঐতিহাসিকই তা বলেন নি। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। পুর দাউদ ধূর্ততার সাথে ইবনে খালদুন যে তাঁর বক্তব্যে কর্তা উহ্য রেখেছেন ও ‘ বলা হয়ে থাকে ’ বলে শুরু করেছেন তার যেমন উল্লেখ করেননি আবার ইরান হতে গ্রীসে আলেকজান্ডার কর্তৃক গ্রন্থ পাচারের ভিত্তিহীন কাহিনীও আনেননি ,অথচ ইবনে খালদুনের বক্তব্য হতে উপসংহার টেনেছেন।
যে গুজবটির কথা ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন তার উৎস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের উৎস হতে ভিন্ন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের গুজবটি খ্রিস্টানরা তৈরি করেছে এজন্য যে ,যেহেতু ঐ গ্রন্থাগার তারাই ধ্বংস করেছে সেহেতু তা মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে ইবনে খালদুনের বর্ণিত গুজবটি সম্ভবত ‘ শুয়ূবীয়া ’ রা178 ছড়িয়েছে। ইবনে খালদুনও যে আরববিরোধী ও ‘ শুয়ূবীয়া ’ প্রভাবিত ছিলেন না তা বলা মুশকিল।
ইরানের শুয়ূবীয়াদের অন্যতম স্লোগান ছিল ‘ শিল্পজ্ঞান শুধু ইরানীদের রয়েছে ’ । ইবনে খালদুনের বর্ণনা হতে বোঝা যায় হয়তো তিনি বলতে চেয়েছেন গ্রীকদের সকল জ্ঞান ইরানীদের নিকট থেকে নেয়া। কিন্তু আমরা জানি অ্যারিস্টটলের জীবদ্দশায় আলেকজান্ডার ইরান আক্রমণ করেন এবং গ্রীস তখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিখরে অবস্থান করছিল।
অন্যদিকে ইবনে খালদুন হতে উপরোক্ত যে বিবরণটি দেয়া হয়েছে তা তাঁর ‘ সামাজিক দর্শন ’ গ্রন্থের ভূমিকা হতে নেয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর ‘ আল ইবর ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ’ নামক ইতিহাস গ্রন্থ হতে এটি বর্ণনা করেন নি। যদি ইবনে খালদুন উক্ত বর্ণনাটিকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তার উল্লেখ করতেন।
আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যেমন বর্ণনাকারীদের কর্মবাচক ক্রিয়ার মাধ্যমে বিবরণ দান বিষয়টির অনির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ ছিল এবং এর পাশাপাশি বাহ্যিক কিছু কারণও বিদ্যমান ছিল যা হতে বোঝা যায় ইসলামের আবির্ভারের অনেক পূর্বেই ঐ গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইরানের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বাহ্যিক কিছু কারণ বিদ্যমান যা থেকে ঐ গুজবের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। তদুপরি ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ইরানে এরূপ কোন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব উল্লেখ করেনি। অন্যদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী হতে চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে।
যদি ইরানে কোন গ্রন্থাগার থাকত তবে তাতে অগ্নি সংযোগের ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও অন্তত এরূপ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের বিষয়টি উল্লিখিত হতো। বিশেষত যখন বিশ্বের অন্যান্য স্থানের চেয়ে ইরানের ইতিহাস ইরানী ও আরব ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে অধিক বিবৃত হয়েছে।
তাছাড়া ইরানীদের মাঝে আরব শাসনামলে এমন এক আন্দোলন শুরু হয়েছিল যারা ইরানে গ্রন্থাগার ধ্বংসের মত কোন ইস্যু পেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করত আর তা হলো ‘ শুয়ূবী ’ আন্দোলন। যদিও প্রথম দিকে ‘ শুয়ূবী ’ আন্দোলন ইসলামের সাম্য ও ন্যায়ের পবিত্র অনুভূতি নিয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা আরববিরোধী ইরানী জাতীয়তাবাদী এক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনের ব্যক্তিরা আরবদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করত এবং যেখানেই আরবদের কোন দুর্বলতা পেত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করত ,এমনকি ইতিহাস হতে আরবদের খুঁটিনাটি সব বিষয় ঘাটিয়ে দেখত।
যদি আরবরা গ্রন্থাগার (বিশেষত ইরানের গ্রন্থাগার) ধ্বংসের মত কোন বড় অপরাধ করত নিঃসন্দেহে বলা যায় শুয়ুবীদের উত্তরণের সেই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে যখন বনি আব্বাস আরববিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিল তখন তাদের পক্ষে নিশ্চুপ বসে থাকা অসম্ভব ছিল ;বরং তারা এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিলকে তাল বানাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। অথচ শুয়ুবীরা এমন কোন প্রচারণা চালায় নি। এটি ইরানের গ্রন্থাগার ধ্বংসের কাহিনী বানোয়াট হওয়ার পক্ষে একটি অকাট্য দলিল।
শিবলী নোমানী আলেকাজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের বিবরণ প্রত্যাখ্যান করে প্রশ্ন করেছেন এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে ? এটি কি ঐ গ্রন্থসমূহের প্রতি তাঁদের সহমর্মিতা নাকি অন্য কোন রাজনৈতিক স্বার্থ বিদ্যমান ? যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর জন্য তাঁরা সমব্যথী হয়ে থাকেন তবে কেন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ ধ্বংসের ইতিহাসের যেমন স্পেন জয় ও ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় খ্রিষ্টানরা যে সকল গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছে তার জন্য তাঁরা সমব্যথী হন না ?
শিবলী নোমানী এর উত্তর দিয়ে বলেছেন প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টানরাই ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল। তাদের অপরাধ ঢাকার উদ্দেশ্যেই তারা এমনটি করছে ।
শিবলী যে কারণ উল্লেখ করেছেন তর বাইরেও অন্যান্য কারণ বিদ্যমান এবং মূল কারণ হলো সাম্রাজ্যবাদ। কারণ তাঁরা জানেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ তখনই সফল হবে যখন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ মানুষকে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাসী করতে পারলেই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সফলতা লাভ করবে। সাম্রাজ্যবাদ যথার্থভাবে বুঝেছে মুসলমানরা যার প্রতি নির্ভর করে তা হলো তাদের মতাদর্শ ও সংস্কৃতি। তাই মুসলমানদের স্বীয় ঈমান ও আকীদার প্রতি সুধারণার অপনোদন ঘটিয়ে পাশ্চাত্য মাতদর্শ গ্রহণে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে যুবকদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন তারা মানবতার মুক্তিদাতা হিসেবে যাদের মনে করে তাদের মতাদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। এরই নমুনাস্বরূপ কল্পিত কাহিনী প্রস্তুত করে বলা হচ্ছে দেখ তারা কিরূপ হিংস্রভাবে অন্য সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে।
ইরানে ইসলামের কর্মতালিকা
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহ অধ্যয়নে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে পবিত্র ও সম্মানিত ইসলাম ধর্ম আমাদের এ প্রিয় দেশে আগমনের প্রাক্কালে এই দেশ কিরূপ অবস্থায় ছিল এবং ইসলাম আমাদের কি দিয়েছে এবং আমাদের নিকট থেকে কি নিয়েছে ?
যা কিছু ইতোপূর্বে অধ্যয়ন করেছেন সেগুলো স্মরণে রাখুন। ইসলাম ইরানকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তার দিক থেকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পেয়েছিল এবং এ দেশের মানুষের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের একতা দান করেছিল। এ ভূখণ্ডে ইসলামের মাধ্যমেই প্রথম বারের মত এই ঐক্য সাধিত হয়েছিল। ইরানের উত্তর-দক্ষিণ ,পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সেমিটিক ও আর্য বংশের বিভিন্ন মানুষ ভাষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে শক্তি ও ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বাস করছিল। ইসলামই তাদের এ অবস্থা হতে বের করে এনে একক দর্শনের ছায়ায় আশ্রয় দেয়। প্রথম বারের মত তারা একক
চিন্তা ,মূল্যবোধ ও আদর্শ লাভ করে এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যদিও এ প্রক্রিয়া চার শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয় তদুপরি তা সফল হয়। তখন হতে এখন পর্যন্ত এ দেশের আটানব্বই ভাগ মানুষ এমনই রয়েছে। যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণও প্রায় চার শতাব্দী এ দেশে শাসন পরিচালনা করেছিলেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যারথুষ্ট্র চিন্তার ছায়ায় বিশ্বাসের ঐক্য সাধনের কিন্তু সফল হন নি। কিন্তু ইরানে দু ’ শ ’ বছরের প্রবর্তিত ইসলামী শাসনের অবসান ঘটলেও ইসলামের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ও প্রশান্তিদায়ক অভ্যন্তরীণ শক্তির কারণে যুগ যুগ ধরে তা টিকে রয়েছে।
ইসলাম ইরান ও প্রাচ্যে খ্রিষ্টবাদের প্রভাব ও বিস্তারকে প্রতিহত করে। ইরান ও প্রাচ্য খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে কিরূপ পরিণতি লাভ করত আমরা অকাট্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে না পারলেও এতটুকু নিশ্চিত বলতে পারি ,তৎকালীন খ্রিষ্ট বিশ্বের দেশগুলোর ন্যায় ইরানে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ নেমে আসত। কিন্তু সে সময়ের খ্রিষ্টান দেশসমূহ যখন অন্ধকার মধ্যযুগ অতিক্রম করছিল তখন ইরান ইসলামের ছায়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের অগ্রভাগে উজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত ইসলামী সভ্যতার মশাল বহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল।
এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি খ্রিষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য ঐরূপ হয়ে থাকে এবং ইসলামের এরূপ তবে কেন বর্তমানের পরিস্থিতি ভিন্ন কথা বলে ? উত্তরটি পরিষ্কার যে ,তারা আট শতাব্দী পূর্বে খ্রিষ্টবাদ ত্যাগ করে মুক্তি পেয়েছে আর আমরা এখনই ইসলামকে ত্যাগ করে পতনের সম্মুখীন হয়েছি।
ইসলাম ইরানের চারিদিক হতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বেড়াজাল (যা এ জাতিকে আবদ্ধ করে রেখেছিল তা) উপড়ে ফেলে এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে ইরানীদের প্রতিভা বিকাশের যে পথ দীর্ঘ দিন রুদ্ধ ছিল এবং এ জাতি নিকট ও দূরবর্তী অন্যান্য জাতির জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়েছিল তা হতে মুক্তি দেয়। ইসলাম ইরানের দ্বারকে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য যেমন উন্মুক্ত করে তেমনি ইরানীদের জন্যও অন্যান্য দেশগুলোর দ্বারসমূহ উন্মোচিত করে। এর মাধ্যমে ইরানীরা এমনভাবে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভা অন্যদের সামনে তুলে ধরেছিল যে ,অন্যদের নেতা ও আদর্শে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার পূর্ণতা ও বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বে এক নতুন সভ্যতা উপহার দিতে পেরেছিল।
এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করি ইরানী জাতির ইতিহাসে প্রথম বারের মত ইরানীরা ধর্মীয় বিষয়ে অন্য জাতির জন্যও ইমাম ও নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। যেমন লাইস ইবনে সাদ একজন ইরানী হিসেবে মিশরের জনগণের ফিকাহর ইমাম হন ,আবু হানিফা যদিও ইরানের মধ্যে আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের প্রভাবের কারণে ইরানী অনুসারী লাভ করেন নি তদুপরি যে জাতিসমূহ আহলে বাইত সম্পর্কে অবগত নন তাদের মাঝে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফকীহ্ ও ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনুল মুসান্না ,ওয়াসিল ইবনে আতা প্রমুখ কালামশাস্ত্রের অন্যতম পুরোধা হিসেবে দৃশ্যপটে আসেন। কিসায়ী ও সিবাভেই আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের পণ্ডিত ও অভিধান রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। হিশাম ইবনে আবদুল মালিক কুফার একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করেন :
‘ যে সকল আলেম ও ফকীহ্ ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন শহরে মুফতী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাদের চেন কি ? ’ তিনি বলেন , ‘ হ্যাঁ।
হিশাম প্রশ্ন করেন , ‘ বর্তমানে মদীনার মুফতী কে ? ’
উত্তরে বলেন , ‘ নাফে। ’
হিশাম প্রশ্ন করেন , ‘ সে কি আরব না মাওলা ? ’ 179
-সে ইরানী মুক্ত দাস।
-মক্কার ফকীহ্ ও মুফতী কে ?
-আতা ইবনে রিবাহ্।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-ইয়েমেনের ফকীহ্ ও মুফতী কে ?
-তাউস ইবনে কিসান।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-ইয়ামামার ফকীহ্ কে ?
-ইয়াহিয়া ইবনে কাসির।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-সিরিয়ার (শাম) ফকীহ্ কে ?
-মাকহুল।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-জাজিরার ফকীহ্ কে ?
-মাইমুন ইবনে মাহান।
-মাওলা না আরব ?
-মাওলা।
-খোরাসানের ফকীহ্ কে ?
-যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-বসরার ফকীহ্ কে ?
-হাসান ও ইবনে সিরীন।
-আরব না মাওলা ?
-মাওলা।
-কুফার ফকীহ্ কে ?
-ইবরাহীম নাখয়ী।
-আরব না মাওলা ?
-আরব।
হিশাম বললেন: ‘ আমার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যার বিষয়েই প্রশ্ন করছিলাম তুমি বলছিলে ‘ মাওলা ’ ,অন্তত একজন আরব খুঁজে পাওয়া গেল। ’ 180
ইরানীদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থান যথা হিজায ,ইরাক ,ইয়েমেন ,সিরিয়া ,মিশর ও আরব উপদ্বীপের মানুষদের ধর্মীয় ইমাম হওয়ার এরূপ সুবর্ণ সৌভাগ্য ইতোপূর্বে কখনও লাভ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী সময়ে তাদের এই ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রভাব আরো বিস্তৃত হয়।
আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে ইরানীদের এই জ্ঞানগত ও নৈতিক পুনর্জাগরণে ও প্রতিভা বিকাশের সময়কে স্যার জন ম্যালকম ইরানীদের স্থবিরতার কাল বলে অভিহিত করেছেন। স্যার জন ম্যালকম উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদের প্রচারক হিসেবে জাতিগত গোঁড়ামীর চশমা পড়ে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এ বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। ম্যালকমের দৃষ্টিতে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হলো কোন্ ব্যক্তি ও কোন্ গোত্র-বর্ণের মানুষ ঐ জাতির ওপর শাসনকার্য চালাচ্ছে। তাঁর দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ দাস ও শোষিত বা অন্য কোন্ অবস্থায় রয়েছে তা দেখার প্রয়োজন নেই। ম্যালকমের মত ব্যক্তিদের এ জন্য কোন আফসোস নেই ,হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত লোকেরা কেন মানুষ হত্যা ও মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে: বরং তাঁর আফসোস হলো হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরিবর্তে কেন এক ইরানী এরূপ কাজ করল না।
ইসলামের আবির্ভাবের পরবর্তী ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় ,সেসময় ইরানীদের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির এক নব উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল যাকে পানিবঞ্চিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সন্ধানী তৎপরতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়েই তারা স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে প্রথম বারের মত অন্যান্য জাতির ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম হতে সপ্তম হিজরী শতাব্দীর ঐ সকল ইরানী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতা এখনও বিদ্যমান।
অন্যদিকে এই দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ফলেই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরেও গ্রীক ,ভারতীয ,মিশরীয় ও অন্যান্য জাতির জ্ঞান ও সংস্কৃতি এখানে আসার সুযোগ পায় এবং এর ওপর ভিত্তি করেই বৃহৎ ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব হয। এর ফলেই আবু আলী ,ফারাবী ,আবু রাইহান বিরুনী ,খাইয়াম (গণিতজ্ঞ) ,খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী ,মোল্লা সাদরাসহ এরূপ শত শত আরেফ (আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব) ,দার্শনিক ,সাহিত্যিক ,চিকিৎসক ,ভূগোলবিদ ,ঐতিহাসিক ,গণিতবিদ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
হাস্যকর বিষয় হলো পুর দাউদ বলেছেন ,যদি আরবদের আক্রমণ ও সেমিটিকদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা না পেত তাহলে ইবনে সিনা ও খাইয়ামদের মত মনীষীরা ‘ নওরুজ নামে ’ ও ‘ দানেশ নামে ’ গ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করতেন এবং বর্তমানের ফার্সী ভাষা আরো সমৃদ্ধ হতো।
আমার প্রশ্ন হলো যদি আরবরা আক্রমণ না করত তবে যারথুষ্ট্র পুরোহিতরা যে দেয়াল তৈরি করে রেখেছিলেন তাতে ইরানীদের প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগই হতো না এবং কোন ইবনে সিনা ও খাইয়ামেরও জন্ম হতো না। ফলে ‘ দানেশ নামে ’ , ‘ নওরুজ নামে ’ এবং ফার্সী ভাষায় এরূপ সহস্র গ্রন্থও সৃষ্টি হতো না। ইরানী মনীষিগণ আরবী ও ফার্সী ভাষায় সহস্র গ্রন্থ বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন তা ঐ আরবদের হামলারই ফল। কারণ তারাই প্রতিটি মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য ঘোষণার মাধ্যমে পূর্বের রচিত দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে ভিন্ন এক ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিল।
পুর দাউদের কথাটি এরূপ ,যদি দিনে সূর্য না উঠত তবে আমাদের মস্তিষ্কও উত্তপ্ত হতো না এবং আমরা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবে সূর্য না উঠলে দিনেরও অস্তিত্ব থাকত না।
এ দু ’ ধারা (অন্যান্য জাতির ওপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব লাভ ও সহস্র মনীষীর জন্ম) শুধু বাহ্যিক এ দেয়াল ধ্বংসের ফলে দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার কারণেই নয় ;বরং অন্য একটি কারণও এর পাশে বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো ইরানের সাধারণ ও বঞ্চিত শ্রেণীর ওপর হতে শিক্ষা গ্রহণের যে নিষেধাজ্ঞা যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ আরোপ করেছিলেন তা উপড়িয়ে ফেলা। ইসলাম সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণী বলে কিছু মানে না এবং জ্ঞানকে পুরোহিত বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে চর্মকার ও কর্মকার শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়কের পুত্রের সমান অধিকার রাখে এবং এই শ্রেণী হতেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। এই অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও ঐ বাহ্যিক দেয়াল ভাঙ্গার কারণেই ইরানীরা অন্য জাতিসমূহেরও অগ্রদূত হওয়ার যোগ্যতা ও বিশাল ইসলামী সভ্যতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়ার সুযোগ লাভ করে।
ইসলাম ইরানীদের আপন সত্তাকে চিনতে যেমন সাহায্য করে তেমনি বিশ্বকে তাদের নিকট পরিচিত করায়। পূর্বে বলা হতো ইরানীদের প্রতিভা ও যোগ্যতা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সীমিত ,অন্যান্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই ,এ কথাটি সঠিক নয়। বিভিন্ন সময়ে ইরানীরা যে পিছিয়ে ছিল তা তাদের যোগ্যতার অভাবে নয় ;বরং তা প্রাচীন পুরোহিত শাসিত সমাজের শৃংখলে আবদ্ধতার কারণে ঘটেছিল। এ কারণেই ইসলামী আমলে ইরানীরা তাদের জ্ঞান-প্রতিভার উচ্চ অবস্থানকে প্রমাণে সক্ষম হয়েছিল।
প্রতিভা দমনকারী প্রাচীন পুরোহিত শাসনের কারণে কোন কোন বিদেশী ভুল করে গোঁড়া হতেই ইরানীদের প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রতি তিরস্কার করেছেন। যেমন গুসতাভ লুবুন বলেন ,
“ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইরানীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকলেও সভ্যতার ইতিহাসে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। প্রাচীন ইরানীরা দু ’ শত বছর পর্যন্ত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের অধিপতি হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ এক রাজকীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করে কিন্তু জ্ঞান ,সাহিত্য ,শিল্পকলা ও স্থাপত্যে তেমন কিছু দিতে পারেনি এবং পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের অবশিষ্ট যে সকল জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যমান ছিল তার কোন উত্তরণও ঘটায় নি।... ইরানীরা সভ্যতার স্রষ্টা ছিল না ;বরং সভ্যতার বিস্তারক ছিল। এ দৃষ্টিতে সভ্যতার সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। ” 181
ফরাসী ঐতিহাসিক কিলম্যান হাওয়ার তাঁর ‘ ইরানে বাসতানী ও তামাদ্দুনে ইরান ’ গ্রন্থে বলেছেন ,
“ ইরান একটি সামরিক দেশ ছিল। তই সেখানে জ্ঞান ,শিল্প ও স্থাপত্যকলা বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনে প্রশিক্ষিত গ্রীক চিকিৎসকগণ ইরানের একমাত্র জ্ঞানের ধারক ছিলেন। স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও গ্রীক ,লিডীয় ও মিশরীয় স্থাপকগণই ছিলেন তাদের প্রতিনিধি । তাদের রাজকীয় হিসাবরক্ষকগণও ছিলেন সেমিটিক বংশোদ্ভূত ব্যাবিলনীয় বা আর্মেনীয়রা। ” 182
জে. রাও লিনসন তাঁর ‘ প্রাচ্যের পাঁচ বৃহৎ সাম্রাজ্য ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন ,
“ প্রাচীন ইরানীরা জ্ঞানের উন্নয়নে কোন ভূমিকাই রাখে নি। এ জাতির মন-মানসিকতা কখনই গবেষণার ন্যায় কর্মের জন্য ধৈর্য ধারণের উপযোগী ছিল না। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য যে চিন্তা ,গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন তাদের নিকট তা পছন্দনীয় বিষয় ছিল না।...
ইরানীরা তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কখনই জ্ঞানের বিষয়ে মনোযোগী ছিল না এবং ভাবত তাদের নৈতিক শক্তিকে প্রদর্শনের জন্য ‘ শুশের প্রাসাদ ,তাখতে জামশিদ (জামশিদ সিংহাসন) ,বৃহৎ রাজকীয় পরিচালনা পরিষদ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাই যথেষ্ট। ’ 183
সন্দেহ নেই এরূপ মন্তব্য তাঁদের অযৌক্তিক মন্দ ধারণার ফল। ইসলামপূর্ববর্তী প্রাচীন ইরানকে এরূপে উপস্থাপিত করা একরকম বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত বিষয় (এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা ‘ পারস্য সভ্যতার মৌলিকতা ’ শিরোনামে আলোচনা করব)। কারণ পুরোহিত শাসকদের গুনাহের বোঝা সাধারণ মানুসের কাঁধে চাপান ঠিক হবে না এবং তাঁদের কর্মের ত্রুটিকে ইরানীদের প্রতিভাহীনতা বলে চালানোও অযৌক্তিক। এর পক্ষে সর্বোত্তম প্রমাণ হলো ঐ জাতিই ইসলামী শাসনামলে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে।
কিলম্যান184 ,গুসতাভ লুবুন ও রাও লিনসন ভুলবশত ‘ ইসলামী সভ্যতা ’ কে ‘ আরব সভ্যতা ’ বলে উল্লেখ করেছেন ,অথচ ইসলামী সভ্যতা পারস্য বা ভারত সভ্যতার মত নয় (বরং এতে আরবদের ভূমিকা অন্যদের হতে কম এবং ইসলাম নতুন এক সভ্যতা নিয়ে এসেছিল যার সঙ্গে আরবদের তেমন কোন পরিচয়ই ছিল না)।
ইসলাম ইরানীদের বিষয়ে উপরোক্ত মন্তব্যগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে। ইসলাম ইরানীদেরকে তাদের আপন সত্তাগত প্রতিভা ও যোগ্যতার সঙ্গে পরিচিত করায় ও বিশ্ববাসীকেও তা জানায়। অন্যভাবে বলা যায় ইরানীরা ইসলামের মাধ্যমে নিজেদের চিনতে পারে ও ইসলামকে অন্যদের নিকট পরিচিত করায়।
কেন ইসলামপূর্ব যুগে লাইস ইবনে সা ’ দ ,নাফে ,আতা ,তাউস ,ইয়াহিয়া ও মাকহুলের ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হলো না যাঁরা মিশর ,ইরাক ,তিউনিসিয়া ,মরক্কো ,হিজায ,ইয়েমেন ,সিরিয়া ,আলজিরিয়া ,ভারত ,পাকিস্তান ,ইন্দোনেশিয়া ,স্পেনসহ ইউরোপের একাংশের মানুষদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতা হতে পারেন। কেন সেসময় মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযী ,ফারাবী ও ইবনে সীনার আবির্ভাব হয় নি ?
তৎকালীন ইরানী শাসক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ইসলাম তাদের ওপর এক আক্রমণ হিসেবে পরিগণিত হলেও ইরানের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এটি সর্বাঙ্গীনভাবে এক বিপ্লব ছিল। ইসলাম ইরানীদের বিশ্বদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়। ইরানীদের অন্তর হতে দ্বিত্ববাদ এবং তা হতে উৎসারিত সকল মন্দ চিন্তাকে দূরীভূত করে। কয়েক হাজার বছরের সেই দ্বিত্ববাদ যার সঙ্গে যারদুশত যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন ও তাঁর ধর্ম এর দ্বারা কলুষিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল ইসলাম তাকে ইরানীদের অন্তর হতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে ও ইরানীদের মস্তিষ্ককে পরিশোধিত করে।
একটি বিপ্লব কি করে ? অবশ্যই মানুষের বিশ্বদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায় ,তাকে নতুন লক্ষ্য ,পরিকল্পনা ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করায় ,তার পূর্ববর্তী বিশ্বাসের পরিবর্তন সাধন করে ,সামাজিক অবকাঠামোর এমন পরিবর্তন ঘটায় যে ,পূর্বের কোন চিহ্নই না থাকে ,শোষকদের ওপর হতে টেনে নীচে নামায় ও শোষিতদের টেনে ওপরে ওঠায় ,মানুষের আচার-আচরণ ও চরিত্রের পরিবর্তন করে জীবন্ত করে তোলে ,বলপ্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষুব্ধ মনোভাবের জন্ম দেয় ,ঈমান ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ,ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ইরানে কি তাই ঘটেনি ?
তাঁরা বলেন তরবারী দিয়ে তা করা হয়েছে। হ্যাঁ ,তরবারীর সাহায্য নিয়েই তা করা হয়েছে ,কিন্তু ইসলামের তরবারী কি করেছে ? ইসলামের তরবারী শয়তানের শক্তিকে ভূলুণ্ঠিত করেছে ,পুরোহিতদের অনিষ্টকারী ছায়াকে কর্তিত করেছে ,চৌদ্দ কোটি মানুষের গর্দান হতে শিকল ছিন্ন করেছে ,বঞ্চিত ও মানুষেদের মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামের তরবারী সব সময় বলদর্পীদের হাতকে কর্তন করেছে ও অত্যাচারীদের মস্তকের ওপর নিপীড়িতের সাহায্যে আপতিত হয়েছে। ইসলামের তরবারী সব সময় শোষিত ও বঞ্চিতদের পক্ষে কাজ করেছে। কোরআন বলেছে ,
) و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرّجال و النساء و الولدان (
‘ তোমাদের কি হয়েছে যে ,তোমরা সংগ্রাম করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য ? ’ (সূরা নিসা: 75)
ইসলাম ইরান হতে দ্বিত্ববাদ ,অগ্নি ,সূর্য ও হুমের উপাসনাকে উচ্ছেদ করে তাওহীদ ও খোদা উপাসনা উপহার দিয়েছে। এ দৃষ্টিতে আরবের চেয়ে ইরানে ইসলামের অবদান অধিকতর মূল্যবান। কারণ ইসলাম আরবদের উপাসনার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের জাহেলিয়াত হতে মুক্তি দেয় ,কিন্তু ইরানীদের সৃষ্টিকর্তার চিন্তার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব হতে মুক্তি দিয়েছিল।
ইসলাম শৃঙ্গ ও ডানাযুক্ত ,গোঁফ ও শ্মশ্রুমণ্ডিত ,হাতে ছড়ি বা দণ্ডধারী ,জোব্বা পরিহিত ,কুঞ্চিত কেশ ও খাঁজকাটা মুকুট পরিহিত খোদার অস্তিত্বের চিন্তাকে চিরস্থায়ী185 ,নিরাকার ,সকল ধারণা ,কল্পনা ও তুলনার ঊর্ধ্বে এক মহান ও সম্মানিত অস্তিত্বের চিন্তায় রূপান্তরিত করে। ইসলাম তাদের এমন খোদার সঙ্গে পরিচিত করায় যিনি বর্ণনার ঊর্ধ্বে186 ,তিনি সকল কিছুর সঙ্গে আছেন187 ,কিন্তু সকল কিছু তাঁর সঙ্গে নেই ,তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ ,তিনিই গুপ্ত ও প্রকাশ্য188 ,তিনি সকল কিছুকে দেখেন কিন্তু কেউ তাঁকে দেখে না189 ।
ইসলাম সত্তাগত ,কর্মগত ও গুণগত একত্ববাদের সর্বোত্তম রূপকে ইরানী অ-ইরানী সকল মুসলমানকে শিখিয়েছে। ইসলাম একত্ববাদকে তার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর যেমন দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে তেমনি এটি চিন্তার সবচেয়ে গতিশীল উদ্দীপক হিসেবে পরিগণিত।
ইসলাম যারথুষ্ট্র ধর্মের সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা যেমন আহুরামাযদা ও আহ্রিমানের নয় হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ ,সন্তান ধারণের লক্ষ্যে যারওয়ানের এক হাজার বছর ধরে কুরবানী করা ,দিভদের (দৈত্যদের) প্রার্থনা কবুল হওয়া ,অগ্নি উপাসনার আশ্চর্যজনক আচার-অনুষ্ঠান ,মৃতদের জন্য ছাদের ওপর মদ্যপান ,অগ্নির মধ্যে বন্য প্রাণী ও পাখি নিক্ষেপ ,মাসে চার বার সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা ,অগ্নির ওপর আলোর পতন প্রতিরোধ ,মৃতদের দাফন না করা ,মৃত ব্যক্তি ও নারীদের অপবিত্র দেহে হাত দেয়ার কঠিন আচার ,গরম পানিতে গোসল নিষিদ্ধকরণ ,গরুর প্রস্রাব দ্বারা পবিত্রকরণ এবং এরূপ হাজারো বিষয়কে ইরানীদের চিন্তা ও কর্মজীবন হতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।
ইসলাম অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে অনর্থক বুলি আওড়ানো ,মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে অগ্নিকে নাড়াচাড়া করা ,অগ্নির সম্মুখে মুখ বেঁধে অবনত হওয়ার মতো অর্থহীন ইবাদাতসমূহের স্থলে যুক্তিপূর্ণ ,নৈতিকতা ও পূর্ণতার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরতম রূপের ইবাদাতকে প্রতিস্থাপন করে। ইসলামের নামায ,রোযা ,হজ্ব ,জুমআ ,জামায়াত ,মসজিদ ,ধর্মীয় সমাবেশ ,জিক্র ও দোয়াসমূহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানপূর্ণ হিসেবে তার উচ্চ মর্যাদার সাক্ষী।
ইসলাম মাযদাকী ,মনী ,যারথুষ্ট্র ও খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা অর্থাৎ দেহ ও আত্মার সৌভাগ্যের ভিন্ন পথ ,দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মের বিপরীত অবস্থান ,কঠোর সাধনার দর্শন ,কঠিন আচার-অনুষ্ঠান ,বৈবাহিক জীবনের প্রতি অনীহা ,মনাভী ও মাযদাকী ধর্মের পুরোহিত এবং খ্রিষ্টধর্মের ধর্মযাজকদের (পোপ ও কার্ডিনালদের) অবিবাহিত থাকা ইত্যাদিকে সভ্যতার শত্রু হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম ইরানে প্রসারমান এরূপ শিক্ষাকে ইরানের ভূমি হতে বিতাড়িত করে আত্মিক পরিশুদ্ধির190 সঙ্গে পৃথিবীর পবিত্র নিয়ামত হতে উপভোগের শিক্ষার191 প্রচলন ঘটায়।
ইসলাম তৎকালীন সময়ে প্রচলিত রক্ত ও মালিকানার ওপর ভিত্তি করে রচিত প্রাচীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং ঐ দু ’ য়ের আবর্তে কেন্দ্রীভূত আইন ,সামাজিক রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে শ্রেণীহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে যার কেন্দ্র ছিল জ্ঞান ,কর্মপ্রচেষ্টা ,তাকওয়া ,আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদা।
ইসলাম বংশগত উত্তরাধিকারভিত্তিক বিশেষ শ্রেণীর পেশাদার পুরোহিত ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। ফলে সকল শ্রেণী হতেই ধর্মীয় আলেম হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং জ্ঞান ও তাকওয়ার মৌল ভিত্তিতে তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়।
ইসলাম ঐশী বংশধারার বাদশাগণের রাজত্বের ধারণাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে। ক্রিস্টেন সেন বলেছেন:
‘ সাসানী সম্রাটগণ তাঁদের শিলালিপিগুলোতে নিজেদের মাযদার উপাসক বলে উল্লেখ করলেও নিজেদেরকে ঐশী বলে দাবি করে স্রষ্টা ইয়াসদান বংশোদ্ভূত পরিচয় দান করতেন। ’ 192
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,
‘ দ্বিতীয় খসরু (পারভেজ) নিজেকে তাই মনে করতেন ও নিজেকে খোদাগণের মাঝে আদমরূপী অবিনাশী এবং মানুষের মাঝে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এক খোদা বলে পরিচয় দিতেন। ’ 193
এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেছেন ,
“ সম্ভবত সাসানী আমলের ইরানের ন্যায় কোন রাজত্বেই সম্রাটগণের ঐশী বংশোদ্ভূত হওয়ার বিষয়ে দৃঢ়তর বিশ্বাসসম্পন্ন প্রজাকুল বিদ্যমান ছিল না। নাওলাদকা বলেছেন: বাহরাম চুবিনের ন্যায় যাঁরাই সম্রাটের বংশধারার না হয়ে অভিজাত অন্য কোন বংশীয় হিসেবে রাজত্ব দাবি করেছেন এ দেশের মানুষ তাঁর অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করেছে। শাহর বারাজের রাজত্ব লাভের বিষয়টি তাই অনেকটা অবিশ্বাস্য ও তাঁর লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। ”
ইরানীরা এরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে ,শুধু এক বংশধারাই এ দেশে রাজত্বের যোগ্যতা রাখে। এডওয়ার্ড ব্রাউন বাহরাম চুবিনের পলায়নের প্রসিদ্ধ কাহিনীতে তাঁর সঙ্গে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা রমনীর কথোপকথনের ঘটনায় স্বর্গীয় বংশধারার না হওয়া সত্ত্বেও রাজত্ব দাবির কারণে তিরস্কৃত হওয়ার বিষয়টি এনেছেন। ডক্টর মাহমুদ সাজারী ‘ অযাদীয়ে ফারদ ওয়া কুদরাতে দৌলাত ’ নামক গ্রন্থে ইউরোপীয় কিছু দার্শনিক যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজকীয় পাদমর্যাদা ঐশী বলে মনে করেন সে সম্পর্কে বলেছেন , ‘ এ মতটি নতুন নয় ;বরং এর মূলকে আমাদের (ইরানের) ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইরানীরা এরূপ মতেই বিশ্বাসী ছিল। ’ 194
ইসলাম এই ইতিহাসকেও ব্যাপকভাবে পাল্টিয়ে দেয়। ইসলামে রাজকীয় বংশোদ্ভূত বলে কিছু নেই। ইসলাম কাঁসা শিল্পী ,জেলে ,দাস ,দরবেশ195 ও ফকির সকলের মধ্যেই এরূপ প্রতিভা ও যোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করে। যদি কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহস থাকে সে তাতে পৌঁছতে পারে। তাই ইসলামী শাসনামলে যাঁরা আত্মনির্ভরভাবে রাজত্ব লাভ করেছেন তা তাঁদের যোগ্যতার বলেই অর্জন করেছেন ,বংশের কারণে নয়।
ইসলাম ইরানীদের মধ্য হতে এ চিন্তার অপনোদন ঘটায় যে ,ধর্মীয় পুরোহিত ও আলেমগণ এক বংশীয় হতে হবে। ইসলাম অভিজাত শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থার চিন্তা ইরানীদের মস্তিষ্ক হতে মুছে দিয়ে সর্বজনীন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটায়।
ইসলাম নারীদের আইনগত অধিকার দান করে। শর্ত ও বিধিহীনভাবে অসংখ্য স্ত্রী রাখার বিষয়টির বিলোপ সাধন করে তদস্থলে নারী ও স্ত্রীদের সম অধিকারের ভিত্তিতে পুরুষের সক্ষমতার আলোকে সীমিত পরিসরে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার খাতিরে একাধিক বিবাহের অনুমোদন দেয়।
ইসলাম স্ত্রীকে ভাড়া বা বন্ধক দেয়া ,প্রতিস্থাপন বিবাহ ,অন্যের ঔরসে নিজ স্ত্রীর গর্ভের
সন্তানকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করা ,মাহ্রাম বিবাহ ,স্ত্রীর ওপর স্বামীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রভৃতি রীতিকে অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করে।
যে সকল ইরানী মুসলমান হয়েছিল তাদের জন্যই শুধু নয় ,ইসলাম যারথুষ্ট্র ধর্মের জন্য অশেষ বরকত বয়ে আনে। পরোক্ষভাবে ইসলাম যারথুষ্ট্র ধর্মের গভীরে সংস্কার সাধন করে। এ বিষয়ে আমরা ক্রিস্টেন সেন থেকে বর্ণনা করেছি যে ,ইসলাম যখন যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণের পৃষ্ঠপোষক সাসানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় তখন যারথুষ্ট্র পুরোহিতগণ উপলব্ধি করলেন এ ধর্মকে ধ্বংস ও পতন হতে রক্ষা করতে হলে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। তাই যারওয়ানী ধারণাসহ অন্যান্য শিশুসুলভ কাল্পনিক বিশ্বাসসমূহকে বাদ দিলেন ,সূর্য উপাসনা পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন। ধর্মীয় অসংখ্য বিবরণ হয় পরিবর্তন করা হলো নতুবা পুরোটাই বাদ দেয়া হলো। সাসানী আভেস্তা ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের যে অংশ যারওয়ানী ধারণামিশ্রিত ছিল তা গ্রন্থাগারের তাকেই পরিত্যাগ অথবা ধ্বংস করা হলো...।
ইরানে ইসলামের অবদান প্রথম দিকের (হিজরী) শতাব্দীগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ;বরং এ দেশে যে দিন হতে ইসলামের ছায়া পড়েছে সে দিন হতে এ দেশের জন্য যত বিপদই এসেছে ইসলামের মাধ্যমে তা প্রতিহত হয়েছে। ইসলামই মোগলদেরকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে মানব হত্যাকারী হতে জ্ঞানপ্রেমিকে পরিণত করেছে। ইসলামই চেঙ্গিস খাঁনের বংশধর হতে মুহাম্মদ খোদাবান্দের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং তৈমুর লং-এর বংশধর হতে বৈসংকর ও আমির হোসেন বৈকরার মত শাসকদের সৃষ্টি করেছিল।
আজও বিদেশীদের ধ্বংসাত্মক দার্শনিক চিন্তার বিপরীতে ইসলাম আমাদের টিকিয়ে রেখেছে এবং আমাদের মধ্যে আত্মসম্মান ,মর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতার অনুভূতিকে জিইয়ে রেখেছে। ইরান জাতি আজ যা নিয়ে গর্ব করতে পারে তা হলো কোরআন ও নাহজুল বালাগাহ্ ;আভেস্তা ও যান্দ নয়।
আমরা ‘ ইরানে ইসলামের অবদান ’ শীর্ষক আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এর পরবর্তী অংশে আমরা ইসলামে ইরানের অবদান নিয়ে আলোচনা করব।
ইসলামের প্রতি ইরানের অবদান
অবদানের সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা
আলোচনার এ অংশে ইরান ও ইরানীরা ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতায় যে অবদান রেখেছেন তা উল্লেখ করব। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে আমরা বলেছি একটি ধর্মের প্রতি কোন জাতির অবদানকে এভাবে দেখা হয় যে ,সে তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তি ,তার চিন্তা ,সৃষ্টিশীলতা ,দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কিভাবে এ দীনের সেবায় নিয়োজিত করেছে এবং তার এ কর্মে কতটা আন্তরিক ও বিশুদ্ধ নিয়্যতের পরিচয় দিয়েছে।
ইরানীরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা নিজ শক্তিসমূহকে ইসলামের সেবায় অধিকতর উত্তমরূপে নিয়োজিত করেছে এবং অন্য সকল হতে এ ক্ষেত্রে অধিকতর আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে। কোন জাতিই এ দু ’ ক্ষেত্রে ইরানীদের সঙ্গে তুল্য নয় ,এমনকি যে আরব জাতির মাঝে ইসলাম প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তারাও নয়। এ আলোচনায় এ দু ’ টি বিষয়কে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য ,বিশেষত দ্বিতীয় বিষয়টি।
ইসলামের সেবায় ইরানীদের অবদান সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয় ,কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি কমই লক্ষ্য করা হয়েছে। ইরানীরা ইসলামের সেবায় মৌলিক ভূমিকা রেখেছে এবং গভীর ভালবাসা ও পূর্ণ ঈমান ব্যতীত এরূপ মৌলিকত্বের সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাস্তবে ইসলামই ইরানীদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগরিত করেছে এবং তাদের মধ্যে নতুন আত্মার জন্ম দিয়ে উদ্দীপিত করেছে। যদি তা না হয় ,অর্থাৎ ইসলামের কারণে তাদের মধ্যে এরূপ উদ্দীপনা যদি সৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন দেখা দেয় কেন ইরানীরা প্রথম (হিজরী) শতাব্দীতে তাদের পূর্ববর্তীদের ধর্মের পথে এই সাহস প্রদর্শন ঘটাতে সক্ষম হয়নি ?
যেহেতু ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম সেহেতু মানব জীবনের সকল দিকের ওপরই প্রভাব রয়েছে। ইরানীদের অবদানও তাই ইসলামের সকল দিক ও অঙ্গনে বিস্তৃত। আমরা এ বিষয়ে আমাদের সুযোগ ও জ্ঞানের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দিক ও বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব।
প্রথম যে অবদানের কথা আমরা উল্লেখ করব তা হলো ইরানীদের প্রাচীন সভ্যতা নতুন ইসলামী সভ্যতায় কি ভূমিকা রেখেছে। এই প্রাচীন সভ্যতা নবীন ও মর্যাদাপূর্ণ ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এ আলোচনা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় (ইসলামে ইরানীদের আন্তরিক ও সততাপূর্ণ ভূমিকা) বহির্ভূত তদুপরি যেহেতু নবীন এক বিকাশমান সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা হতে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবেই অনেক কিছু নিয়ে থাকে এবং ইরানীদের অবদানের বিষয়টিও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই বিষয়টি উল্লেখ ব্যতীত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে করছি।
তা ছাড়াও বইটির নাম যেহেতু ‘ ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান ’ সেহেতু ইরান সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপনে আমরা সাধারণভাবে ইরানী মুসলমানদের অবদানের বাইরের বিষয়ও উপস্থাপনে অনেকটা বাধ্য। কারণ এ পর্যায়ে পাঠকগণ স্বাভাবিকভাবেই এ সম্পর্কেও জানতে চাইবেন।
ইসলামে ইরানী মুসলমানদের অবদানের আলোচনার শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা রেখেছে তার দিকে আমরা আলোকপাত করব। যেমন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ,অন্য জাতিসমূহের নিকট এর আহ্বান ও উপস্থাপন ,শিক্ষা ও সংস্কৃতি ,শিল্প-বিজ্ঞান ,সামরিক ,যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি। প্রথমেই নবীন ইসলামী সভ্যতায় প্রাচীন ইরানী সভ্যতার অবদান নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি।
ইরানী সভ্যতা
ইরানী সভ্যতার স্বরূপ ও এর মূল্যবোধসমূহের যথার্থতা যাচাই এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। তাই হাখামানেশীয় যুগ হতে সাসানী আমল পর্যন্ত এ সভ্যতায় যে রূপান্তর ঘটেছে তার আলোচনাতে আমরা প্রবেশ করতে চাই না। কারণ প্রথমত এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ন্যায় মত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। আমরা এখানে বিশেষজ্ঞদের সমর্থিত প্রামাণ্য ইতিহাস ও তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করে আলোচনা শুরু করব। সুতরাং এ বিষয়ে যা কিছুই বলব তা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে উদ্ধৃতি মাত্র। এ ক্ষেত্রে দু ’ টি বিষয় প্রমাণিত ও অকাট্য হিসেবে স্বীকৃত।
এক ,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ইরান এক দীর্ঘ ও উজ্জ্বল সভ্যতার ধারক ছিল। এ সভ্যতা বেশ প্রাচীন।
দুই ,ইরানে ইসলামের প্রবেশের পরবর্তীকালে ইসলামী সভ্যতা এ সভ্যতা হতে উপকৃত হয়েছে।
পি.জে. দুমানাশের বর্ণনায় রয়েছে , “ ইরানীরা এক বর্ণাঢ্য ও প্রশিক্ষিত সভ্যতা ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং ইসলামও ইরানীদের দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। ” 196
ইরান যে বর্ণাঢ্য ও প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী ছিল যদিও তা ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন নেই তদুপরি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অর্থহীন হবে না।
ড. রেজা যাদেহ্ শাফাক তাঁর ‘ মধ্যপ্রাচ্য-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ইরান ’ গ্রন্থে ব্রেমস্টেডের ‘ প্রাচীন সভ্যতার দিনকাল ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হাখামানেশী আমলের সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন , “ একদিকে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত ,অন্যদিকে ভারত মহাসাগর হতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত প্রসারিত ইরানী ভূখণ্ডের রাজকার্য পরিচালনা সহজ কাজ নয়। ইতোপূর্বে কোন শাসক এত বড় সম্রাজ্যের গুরুদায়িত্বে ছিলেন না যা সাইরাসের রাজত্বকালে শুরু হয় এবং দরভীশের রাজত্বকাল পর্যন্ত (585-525 খ্রিষ্টপূর্ব) বিদ্যমান ছিল। এরূপ বৃহৎ পরিসরে রাজ্য শাসন ও পরিচালনার নমুনা তৎকালীন সময়েই প্রথমবারের মত স্থাপিত হয়- যাকে মধ্য এশিয়ায় ,এমনকি সমগ্র বিশ্ব সভ্যতায় প্রথম উদাহরণ বলা যেতে পারে এবং এটি মানব ইতিহাসের লক্ষণীয় পর্যায়সমূহের একটি বলে পরিগণিত... । ”
একই গ্রন্থে হাখামানেশী আমলের নৌশক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে , ‘ দরভীশের পুত্র খাশাইয়ারশার আমলে ভূমধ্যসাগরে ইরানের কয়েকশ ’ রণতরী ছিল এবং তারা সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী ছিল।
ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে , ‘ দরভীশের শাসনামলে একজন প্রসিদ্ধ মিশরীয় আলেম ইরানীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। দরভীশ তাঁকে মিশরে একটি চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করেন...। ”
সাসানী আমলের প্রত্নতত্ত্ব শিল্প সম্পর্কে লিখা হয়েছে :
“ ইরানী প্রত্নতত্ত্ব শিল্পের ইতিহাসে সাসানী আমলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দালান নির্মাণ শিল্প ঐ সময়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। এখনও তৎকালীন সময়ের দালান ,প্রাসাদ ,উপাসনালয় ,সাঁকো ও নির্মিত বাঁধের ধ্বংসাবশেষ হতে এগুলোর উচ্চ শৈল্পিক কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্স প্রদেশের ফিরুযাবাদ ,শাপুর ও সুরুস্তান এবং মাদায়েন (তিসফুন) ও কাসরে শিরিনের প্রাসাদসমূহ সাসানী আমলের প্রসিদ্ধ প্রত্মতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নমুনা। ” 197
জাহেয তাঁর ‘ আল মাহাসেন ওয়াল আয্দাদ ’ গ্রন্থে দাবি করেছেন , “ সাসানী আমলের ইরান অন্য সব কিছুর চেয়ে স্থাপত্য অর্থাৎ দালান নির্মাণ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। তৎকালীন শিলালিপি হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন তারা বইয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু ইসলামী শাসনামলে দালান ও গ্রন্থ দু ’ য়ের প্রতিই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। ” 198
উইল ডুরান্ট তাঁর ‘ তারিখে তামাদ্দুন ’ গ্রন্থে (ফার্সী অনুবাদের দশম খণ্ডে) সাসানী শাসনামল ও সভ্যতার বিষয়াবলী নিয়ে ষাট পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। এ আমলের জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন , “ আশকানীদের শাসনামলে ইউরোপীয় ইরান ও ভারতবর্ষে প্রচলিত পাহলভী ভাষা সাসানী আমলেও প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ের প্রচলিত শব্দের মধ্যে শুধু ছয় লক্ষ শব্দ এখন অবশিষ্ট রয়েছে যার সবগুলোই ধর্ম সম্পর্কিত। তৎকালীন সাহিত্য অত্যন্ত ব্যাপক হলেও যেহেতু এর সংরক্ষক ও বর্ণনাকারী যারথুষ্ট্র পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন সেহেতু তাঁরা অধর্মীয় চিহ্নসমূহ (ধর্মবহির্ভূত শব্দসমূহ) ব্যবহার হতে বিরত থাকতেন। ফলে তা দিন দিন বিলুপ্ত হতে থাকে। সাসানীরা সাহিত্য ও দর্শনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন। খসরু আনুশিরওয়ান এ বিষয়ে অন্যদের হতে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই আফলাতুন (প্লেটো) ও অ্যারিস্টটলের চিন্তাদর্শন পাহলভী ভাষায় অনূদিত হয় এবং তা জান্দি শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হতো। ” 199
আমরা অবগত যে জান্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানী খ্রিষ্টানরা এটি পরিচালনা করত এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে এটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলামী শাসনামলে ও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। আব্বাসীয় আমলের কয়েকজন প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান চিকিৎসক ,যেমন বাখতীশু ,ইবনে মাসুইয়া ও অন্যান্যরা এ বিশ্ববিদ্যালয় হতেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে যখন বাগদাদ বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন জান্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হতে লাগল ও সময়ের পরিক্রমায় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।
উইল ডুরান্ট সাসানী আমলের শিল্পকলা সম্পর্কে বলেছেন , ‘ সাসানী আমলের শাপুর ,ক্বাবাদ ও খসরুদের সম্পদ ও প্রতিপত্তির চিহ্ন হিসেবে তৎকালীন শিল্পকলা ব্যতীত কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। তবে মহান সম্রাট দরভীশের শাসনকালের রাজধানী পার্সপুলিস হতে শাহ আব্বাস সাফাভীর স্থাপিত ইসফাহান পর্যন্ত ইরানী শিল্পকলার স্থিতিস্থাপকতা ও বিবর্তন আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে। ” 200
তৎকালীন সময়ের বুনটশিল্প সম্পর্কে তিনি বলেছেন ,
“ সাসানী আমলের বুনট শিল্প ,চিত্রকর্ম ,ভাস্কর্য ,মৃৎশিল্প প্রভৃতি সৌন্দর্য বর্ধিত ও অলংকারমূলক শিল্প সমন্বিত ছিল। মসৃণ রেশমী কাপড় ,সূক্ষ্ম সূচীকর্মযুক্ত ‘ দিবা ’ ও ‘ দামেস্কী ’ সিল্ক ,টেবিল ক্লথ ও চেয়ারের আবরণ ,ছাদ ও বারান্দার বর্ধিত অংশ ,বিছানার চাদর ও কার্পেট প্রভৃতিতে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অভিজ্ঞতার পরশ দিয়ে হলুদ ,সবুজ ও নীল রং দিয়ে নকশা অংকিত হতো। ” 201
মৃৎ শিল্প সম্পর্কে বলেছেন , “ সাসানী আমলের প্রতিদিনের ব্যবহৃত কিছু মাটি ও চীনামাটির পাত্র ব্যতীত বর্তমানে কিছু অবশিষ্ট নেই। মৃৎশিল্প হাখামানেশী আমলে অগ্রগতি লাভ করেছিল এবং সাসানী আমলেও তা অব্যাহত ছিল ও আরব শাসনামলে তা পূর্ণতায় পৌঁছায়। ” 202
উইল ডুরান্ট দাবি করেছেন ,আশকানী শাসনামলের চার শতাব্দীর স্থবিরতা ও অধঃপতনের পর সাসানী আমলে শিল্পকলা ইরানে পুনরুজ্জীবন লাভ করে। যদি সে সময়কার অবশিষ্ট স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে যাচাই করি তাহলে দেখব পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে তা হাখামানেশী আমলের শিল্প বিশেষত্বের সঙ্গে একেবারেই তুলনীয় নয়। তেমনি সৃজনশীলতা ,সূক্ষ্মকারুকার্য এবং রুচির দিক হতে তা ইসলাম পরবর্তী ইরানী শিল্পেরও সমকক্ষ নয়।
উইল ডুরান্ট ঐ অধ্যায়ের উপসংহারে বলেছেন , “ তবে সামানী শিল্পকলার বিভিন্ন অবয়ব ও চিত্ররূপের প্রভাব পূর্বে ভারতবর্ষ ,তুর্কিস্তান ও চীনে এবং পশ্চিমে সিরিয়া ,এশিয়া মাইনর ,
কনস্টান্টিনোপল ,বলকান ,মিশর ও স্পেনে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। এ শিল্পকলা গ্রীক শিল্প ও স্থাপত্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে ,গ্রীকরা সনাতন শিল্পকলা হতে সৌন্দর্য ও সৌকর্যমূলক বাইজান্টাইন শিল্পকলার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খ্রিষ্টীয় ,রোমীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলাতে এর প্রভাবের কারণেই তারা গীর্জার কাঠের ছাদের স্থানে ইট ও পাথরের গম্বুজ সংযোজনের ধারা গ্রহণ করে এবং স্তম্ভযুক্ত দেয়ালের দিকে আকৃষ্ট হয়।
সাসানী স্থাপত্য হতেই ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের মসজিদে দালান কোঠা ও ভবনগুলোতে বড় বড় দরজা ও গম্বুজ তৈরির প্রচলন লাভ করে। কোন কিছুই ইতিহাসে হারিয়ে যায় না ,তবে সময়ের পরিক্রমায় সৃজনশীল সকল চিন্তা ও কর্মই পরিবর্তন লাভ করে এবং এর রং ও উৎকর্ষ মানব সভ্যতায় নিজের স্থান করে নেয়। ” 203
‘ মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে ইরান ’ 204 গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ‘ ইসলামী শিল্পকলার উৎস ’ অধ্যায়ে মেট্রোপল জাদুঘরের মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যের শিল্পকলা বিভাগের প্রধান দিমান্ড রচিত ‘ এক নজরে ইসলামী শিল্পকলা ’ গ্রন্থ হতে উল্লিখিত হয়েছে ,হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে আরবদের মধ্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার কোন চর্চা ছিল না বা থাকলেও উল্লেখ্য নয় বললেই চলে। কিন্তু সিরিয়া ,টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল (ইরাক) ,মিশর ও ইরান জয়ের পর আরবরা এতদঞ্চলের শিল্প ও স্থাপত্যকলা গ্রহণ করে। চীনা গ্রন্থ হতে জানা যায় উমাইয়্যা শাসকগণ বিজিত সকল অঞ্চল হতে স্থপতি ও বিশেষজ্ঞদের প্রাসাদ ,শহর ও মসজিদসমূহ নির্মাণের জন্য উচ্চ মজুরী দানের মাধ্যমে আকর্ষণ করতেন। দামেস্কের মসজিদগুলোতে কারুকার্য করার জন্য সিরিয়ান ও বাইজান্টাইন কারুশিল্পীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা একজন ইরানী শিক্ষকের অধীনে এ কাজ করত।
মক্কাতেও বিভিন্ন দালান নির্মাণের জন্য মিশর ও দামেস্কের কুদ্স হতে স্থপতি ও কারিগর আনা হতো। গৃহ নির্মাণের উপাদান হতে কারিগর পর্যন্ত সব কিছুই এ সকল স্থান হতে সংগৃহীত হতো। আব্বাসীয়দের সময়কাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,বাগদাদের প্রাসাদসমূহ নির্মাণের জন্যও সিরিয়া ,ইরান ,মুসেল ও কুফা হতে সহযোগিতা নেয়া হতো। সুতরাং ইসলামী স্থাপত্য ও শিল্পকলা প্রাচ্যের খ্রিষ্টীয় ও সাসানী এ দু ’ শিল্পকলা হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। একই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ,ইতোপূর্বে কোন কোন বিশেষ ইসলামী স্থাপত্য ও শিল্পকলায় সাসানী স্থাপত্য ও শিল্পের প্রভাবের বিষয়টি উদ্ঘাটন করলেও বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায় নি ,কিন্তু সম্প্রতি বাগদাদের নিকটবর্তী তিসফুন (মাদায়েন) ,দজলা-ফোরাতের (টাইগ্রীস ,ইউফ্রেটিস) মধ্যবর্তী কিশ এবং ইরানের দামেগান অঞ্চলে যে সকল খননকার্য সম্পাদিত হয়েছে তাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের প্রত্নতাত্ত্বিক সৌন্দর্যমূলক চূর্ণকর্মের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে যেগুলো ইসলামী স্থাপত্য ও প্রত্নকলার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,সাসানী স্থাপত্য ও শিল্পকলা ইসলামী শিল্প ও স্থাপত্যকলায় মিশে গিয়েছে। স্থপতি ও কারুশিল্পীরা কখনও কখনও একই নকশা ও কারুকার্য ব্যবহার করতেন। কখনও আবার পরিবর্তন করে বিশেষ কোন নতুন নকশা প্রণয়ন করতেন।
নেহরু তাঁর ‘ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ’ 205 গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘ ইরানের প্রাচীন রীতির ধারাবাহিকতা ’ নামক একটি পৃথক আলোচনায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইরানী শিল্প ও সংস্কৃতি দু ’ হাজার বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে।
তিনি বলেন ,
“ ইরানী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উজ্জ্বল ও দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য দু ’ হাজার বছর ধরে চলে এসেছে যা অশুরীয় সভ্যতার পর থেকে শুরু হয়েছিল। ইরানে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর ভূখণ্ড কখনও দেশীয় শাসকবর্গ কখনও বিজাতীয়দের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইসলাম এ দেশে প্রবেশ করে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন সাধন করেছে। তদুপরি ইরানী শিল্পকলা এখনও পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রয়েছে । ” 206
তিনি আরো বলেছেন ,
“ আরব সেনাদল মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় অগ্রাভিযানে শুধু নতুন ধর্ম নয় ;বরং সে সাথে নব বিকাশমান এক সভ্যতাকে বহন করে নিয়ে যায়। সিরিয়া ,দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল ,মিশর সকল স্থানই আরবীয় (ইসলামী) সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে আরবী ভাষা তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হলো ,এমনকি জাতিগতভাবেও তারা আরবদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সদৃশে পরিণত হলো। দামেস্ক ,কায়রো আরবদের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। নব সভ্যতার শক্তিশালী বিবর্তন ক্রিয়ার প্রভাবে সেখানে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদসমূহ তৈরি হলো... ইরান আরবদের সদৃশে পরিণত না হলেও ইসলামী আরব সভ্যতা তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভারতবর্ষের ন্যায় ইরানেও ইসলাম শিল্পকলায় নতুন জীবন দান করে। ইসলামী আরব সভ্যতাও ইরানী সভ্যতা ও শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ” 207
আমরা জানি উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় আমলে বেশ কিছু ফার্সী গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয় যদিও অন্যান্য ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থের তুলনায় এটি তেমন কিছু নয়। তদুপরি একে ইসলামী সভ্যতায় ইরানী সভ্যতার এক প্রকার সহযোগিতা বলা যায়। আমরা পরবর্তীতে ইরানী অনুবাদসমূহের আলোচনায় এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করব।
মুসলমানগণ রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা পদ্ধতি ইরানীদের নিকট হতে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় কার্যালয় ও অফিস-আদালত প্রাচীন ইরানী পদ্ধতির অনুকরণে সাজানো হয়েছিল। এমনকি সাধারণত সরকারী কার্যালয়ে ফার্সী ভাষাই ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে ইরানী মুসলমানগণ তা আরবীতে রূপান্তরিত করেন।
ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,
‘ সর্বপ্রথম খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নির্দেশে অন্য ভাষা হতে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। তিনি জ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিশেষত রসায়নবিদ্যার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। তিনি মিশরের অধিবাসী কতিপয় গ্রীক দার্শনিককে দামেস্কে আহ্বান জানান। যেহেতু তাঁরা আরবী ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন তাই তিনি তাঁদের গ্রীক ও কিবতী ভাষার এতদ্সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। এটিই আরবীতে অনুবাদের সূচনা।
অতঃপর বলেছেন ,
‘ হাজ্জাজের আমলে সালেহ ইবনে আবদুর রহমান নামের এক ইরানী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সরকারী কার্যালয় ও আদালতসমূহের কাগজপত্র ফার্সী হতে আরবীতে অনুবাদ করেন যা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুবাদ কার্যক্রম বলে পরিগণিত। সালেহ হাজ্জাজের মন্ত্রী যদানফারাখের অধীনে কাজ করতেন। যেহেতু সালেহ আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন সেহেতু তাঁর প্রতি হাজ্জাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একদিন সালেহ যদানফারাখকে বলেন: আমার ভয় হয় ভবিষ্যতে হাজ্জাজ তোমার ওপর আমাকে প্রাধান্য দিতে পারে এবং তার নিকট তোমার অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। যদানফারাখ বলেন: তুমি ভয় কর না। এটি কখনও হবে না। কারণ তোমার চেয়ে আমাকে হাজ্জাজের অধিক প্রয়োজন। হিসাবকার্যে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই। সালেহ বলেন: আল্লাহর শপথ! যদি চাই সরকারী কাগজপত্র সবই আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারি তখন ফার্সীর আর কোন প্রয়োজন পড়বে না। যদানফারাখ পরীক্ষা করে দেখলেন সালেহ সত্য বলেছেন। তাই সালেহকে বললেন: তুমি কয়েকদিন অসুস্থতার অজুহাতে দরবারে এসো না। হাজ্জাজ তার বিশেষ চিকিৎসককে সালেহের নিকট প্রেরণ করলে তিনি ফিরে এসে হাজ্জাজকে জানালেন তাঁর মধ্যে অসুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ ইবনে কায়েসের বিদ্রোহের দাঙ্গায় যদানফারাখ নিহত হলে স্বাভাবিকভাবেই সালেহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। একদিন যদানফারাখের সঙ্গে নিজ কথোপকথনের বিষয়টি সালেহ হাজ্জাজের নিকট উপস্থাপন করলে অনুবাদের এ কর্ম বাস্তব রূপ লাভ করে।
কিন্তু এ বিষয়টি ফার্সী ভাষাভাষীদের ক্ষুব্ধ করে তুলল। বিশেষত যারা ফার্সীভাষী হওয়ার কারণে এরূপ কর্মে নিয়োগ লাভ করেছিল তারা খুবই মনক্ষুন্ন হলো। একদিন যদানফারাখের পুত্র সালেহকে হিসাব সম্পর্কিত কয়েকটি ফার্সী পরিভাষার আরবী রূপ কি হবে তা জানতে চাইলে তিনি সমার্থের আরবী পরিভাষা বর্ণনা করেন। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলে: আল্লাহ্ তোমার শিকড় ধ্বংস করুন। কারণ তুমি ফার্সী ভাষার শিকড় কেটেছ। একদল ফার্সীভাষী সালেহকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে এ কর্মে অপারগতা প্রকাশ করতে বললে তিনি রাজী হননি। ”
ইবনুন নাদিম বলেন ,
“ সিরিয়ার দরবারীরা রাজকীয় নথিপত্র ও হিসাব রোমীয় ভাষায় লিখত (ফার্সী ভাষায় নয়)। হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সময়ে তা-ও আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। ” 208
এ বিষয়গুলো তৎকালীন খলীফা ও শাসকবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আরবদের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর ইরানী শাসকবর্গ তাঁদের সরকারী নথিপত্র ও হিসাব পুনরায় ফার্সীতে লেখা শুরু করেন। গজনভীদের শাসনামলে এটি আবার আরবীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ইতিহাসও দীর্ঘ।
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ,এ আলোচনায় আমরা প্রাচীন ইরানী সভ্যতা নবীন ইসলামী সভ্যতায় কি ভূমিকা রেখেছে তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তবে এ কর্মের যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে দু ’ টি বিষয়কে আমরা তুলে ধরেছি: প্রথমত ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ইরান স্বতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার অধিকারী ছিল এবং এ সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম উৎস বলে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়ত ইরানের পতনশীল সভ্যতা ইসলামের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ইসলাম ইরানকে নতুন জীবন ও রূপ দান করে। এ দু ’ টি বিষয় অনস্বীকার্য। অনুসন্ধিৎসুরা এ সম্পর্কিত বিদ্যমান পর্যাপ্ত সূত্রে তা অধ্যয়ন করতে পারেন।
ইসলাম ও আন্তরিকতা
এখন আমরা আমাদের প্রকৃত আলোচনায় প্রবেশ করব। তা হলো ইরানীরা ইসলামে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা ঈমান ,ইসলাম ও আন্তরিকতার ভিত্তিতেই করেছে। আমরা প্রথমে ইরানীদের ইসলাম ও আন্তরিকতা নিয়ে আলোচনা করব । তারপর তাদের অবদানের বিষয়টি আলোচনায় আনব।
ইরানীদের অবদানের বিষয়টি নিয়ে অতিরঞ্জিত করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা এ দাবিও করছি না যে ,সকল ইরানীই ইসলামের প্রতি নিবেদিত ও আন্তরিক ছিল বা তাদের সকলের অবদানই পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সম্পাদিত হয়েছিল। আমরা যা দাবি করছি তা হলো অধিকাংশ ইরানী ইসলামের প্রতি আন্তরিক ছিল ,তারা ইসলামের খেদমত ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেনি এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরব-অনারব কেউই ইরানীদের সমকক্ষ নয়। তারা এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অনন্য অর্থাৎ কোন জাতিই কোন ধর্মের প্রতি এতটা খেদমত করেনি বা এতটা নিবেদিত সেবা দেয়নি।
একটি জাতিকে শক্তি প্রয়োগে অনুগত করা যায় ,কিন্তু বাহুবলে তাদের মাঝে ঈমানী চেতনা ,প্রেম-ভালবাসা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় না। শক্তি ও ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে পরিসীমিত। মানব জাতির সেরা সৃষ্টি ও অবদানসমূহ ভালবাসা ও ঈমানের ফল।
কেউ কেউ ইসলামী সংস্কৃতিতে ইরানীদের অভূতপূর্ব অবদানের পেছনে কাদেসীয়া ,জালুলা ,হালওয়ান ও নাহাভান্দে আরবদের নিকট পরাজয়ের ক্ষতিপূরণের মনোবৃত্তি কার্যকর ছিল বলে মনে করেন। কারণ ইরানীরা জানত সামরিক পরাজয় সার্বিক পরাজয় নয় ;বরং প্রকৃত পরাজয় হলো সাংস্কৃতিক পরাজয়। ইরানীরা জাতীয় চেতনার অনুভূতিতে অন্য জাতির বিরুদ্ধে বিশেষত আরবদের মুকাবিলায় স্বকীয় সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের প্রয়াসে ইসলামী বৈশিষ্ট্যসমূহের আবরণে নিজ চিন্তা-চেতনা ,রীতি-নীতি ও আচারকে আচ্ছাদিত করে এবং এ লক্ষেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালায়। অন্যভাবে বলা যায় ,ইসলামকে বাস্তবতার কারণে প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে কিভাবে একে ইরানী রূপ দেয়া যায় সে চিন্তায় মগ্ন হয়। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইসলামী জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা উত্তম কোন পথ ছিল না বলে এ পথকে মনোনীত করে।
আমাদের বিশ্বাস এরূপ ব্যাখ্যা সত্য হতে অনেক দূরে। কারণ প্রথমত পূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি ,মুসলমানদের হাতে ইরানের সামরিক পরাজয়ের অনেক পূর্ব হতেই ইরানীরা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল । ইরানীরা সামরিক পরাজয়ের পরে ইসলামের যে খেদমত করেছে তা সামরিক পরাজয়ের পূর্বের মতই। দ্বিতীয়ত যদি এ আন্তরিক উদ্দীপনা না থাকত তবে তা চৌদ্দ শতাব্দী যাবত অব্যাহত থাকতে পারত না। কোন ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনকে এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া যায় ,কিন্তু শতাব্দীকাল ধরে বহমান কোন আন্দোলনকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।
সময়ের দীর্ঘতার বিষয়টি বাদ দিলেও আন্দোলনের ধরন ও প্রকৃতিও ঐরূপ প্রবণতার উপস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানীদের কর্ম পদ্ধতি ও ধরন যে তাদের ঈমান ও নিষ্ঠার প্রমাণ দেয় তা আমরা দেখব।
তদুপরি যদি সামরিক পরাজয়ের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে ইরানীরা ইসলামের সেবায় রত হয়ে থাকে তবে স্বয়ং তারা কেন ইসলামের প্রচারক সেজে অন্যান্য জাতি হতে নিজেদের সংখ্যার কয়েকগুণ মানুষকে ইসলামের পতাকা তলে নিয়ে আসল ? যখন ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে ইরানী দৃষ্টিতে তা ক্ষতিকর কিছু না হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা নিজেদের জীবন বাজী রেখে ইসলামকে রক্ষার প্রচেষ্টায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে ? কেন ইসলামের বিপক্ষে অন্যায় প্রচারণা ও অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে তারা অন্যদের চেয়ে অধিকতর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ?
পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। এখন ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।
উদ্দীপনাসমূহ
প্রথমেই উদ্দীপনার দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ইসলামী বিশ্বকে মূল্যায়নের প্রয়োজন মনে করছি। ইসলামী বিশ্ব জ্ঞান ও সাংস্কৃতির যে আন্দোলন শুরু করে তাতে আরব ,ইরানী ,ভারতীয় ,মিশরীয় ,আলজিরীয় ,তিউনিসীয় ,মরোক্কীয় ,সিরীয় ,এমনকি ইউরোপীয় স্পেনও অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে ইসলামী ভূখণ্ডের দূরপ্রাচ্য হতে দূরপাশ্চাত্য পর্যন্ত যেমন সংযুক্ত হয়েছিল তেমনি ইসলামী বিশ্বের উত্তর প্রান্ত হতে দক্ষিণ প্রান্তও সংযুক্ত ছিল। এ আন্দোলনে যেমন ইরানের ইবনে সিনা ,রাযী ও সিবাভেইরা অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি স্পেনের (আন্দালুসের) ইবনে মালিক ইবনে রুশদও ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু এ বৃহৎ আন্দোলনের উদ্দীপক কি ছিল ? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মত হতে পারে।
1. এ সকল জাতির মধ্যে আরবীয় জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা সকলেই আরব জাতীয়তাবাদের ছায়ায় এরূপ সমঝোতাপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল।
অবশ্যই এরূপ ধারণা সঠিক নয় ;যদিও কোন কোন সাম্প্রতিক আরব লেখক ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
কোন কোন ইউরোপীয় লেখক ইসলামী সভ্যতাকে আরবীয় সভ্যতা হিসেবে দেখাতে চান। এর উদ্দেশ্য হলো একদিকে আরবদের আত্ম-অহংকারী করার মাধ্যমে পূর্ব হতে অধিকতর আরব জাতীয়তাবাদের ওপর নির্ভরশীল করে ইসলামী বিশ্ব হতে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়া ও বিচ্ছিন্ন করা। অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম জাতিকে এরূপ মিথ্যা প্রচারণার কারণে আরবদের ওপর অসন্তুষ্ট করা।
2. ইসলামী জাতিসমূহ প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতি ও গোত্রের চিন্তার আলোকে কার্যক্রম চালাত। তাদের প্রত্যেকের প্রবণতা নিজস্ব জাতীয় অনুভূতি হতে জাগরিত হয়েছিল।
এ মতও যে গ্রহণযোগ্য নয় তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আমরা এ গ্রন্থের প্রথমাংশে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি। ইসলামী জাতিসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরে প্রবেশের কারণেই ভারতীয় ,ইরানী ,আফ্রিকীয় বা স্পেনীয় মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছিল।
3. মুসলিম জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও জাতিগত বিশেষত্ব সত্ত্বেও জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে একক চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে জীবন যাপন করত এবং তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত কর্মকাণ্ডের উদ্দীপনা তারা ইসলাম ,ইসলামের বিশ্বজনীন ও মানবিক শিক্ষা হতে লাভ করেছিল। ইতিহাস এ সত্যকেই সমর্থন ও প্রমাণ করেছে।
কোন ব্যক্তি বা জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকার পশ্চাতে কোন্ উদ্দীপনা কাজ করেছে তা জানতে হলে তার কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইরানীদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করব যা তাদের এ ঐতিহাসিক অবদানের পশ্চাতের উদ্দীপনাসমূহকে আমাদের নিকট তুলে ধরবে।
এখানে আমরা আত্তারাদীর লেখা হতে কিছু অংশ ‘ ইরানীদের ইসলামী কর্মকাণ্ড ’ শিরোনামে তুলে ধরছি।
ইরানীদের ইসলামী কর্মকাণ্ড
ইয়েমেনের ঘটনায় সেখানকার ইরানী মুসলমানদের আত্মত্যাগী ভূমিকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে ,ইরানীরা উন্মুক্ত মন নিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছিল এবং এ ধর্মের প্রচারে কোন আত্মত্যাগেই পিছপা হয়নি। যে সকল লেখক এ কথা বলেন ,এ জাতির ওপর তরবারীর সাহায্যে ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ;হয় জাতীয়তার গোঁড়ামি তাঁদের এ কথা বলতে বাধ্য করে নতুবা তাঁরা ইরানী জাতিতে ইসলামের প্রবেশ সম্পর্কে অজ্ঞাত। সকল ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন ইসলাম আশ্চর্যজনক গতিতে ইরানে প্রসার লাভ করেছিল এবং এ জাতি কোন যুদ্ধ ও বিতর্ক ছাড়াই এ ধর্মকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই সমগ্র ইরানের ভূমি একদিকে ফোরাত হতে যেইহুন নদীর বেলাভূমি অন্যদিকে সিন্ধু নদী হতে খাওয়ারেজম অববাহিকা পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। যদিও কয়েকস্থানে আরব মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তদুপরি যুদ্ধগুলো শাসকবর্গ ,ধর্মীয় গুরু ও অভিজাতদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে যারা ইসলামের আগমনকে তাদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বুঝতে পেরেছিল।
বৃহৎ পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এ দেশের অধিকাংশ মানুষ (মাযেনদারান ও দাইলামী পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা ব্যতীত) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ দেশের মানুষ ইসলামের প্রচার ও এর পবিত্র শরীয়তের বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম তিন শতাব্দী ইরান বনী উমাইয়্যা ও বনী আব্বাসের খলীফাদের হাতে শাসিত হয়। সে সময়েও ইরানীরা ইসলামী বিধিবিধানের ব্যাখ্যা ,আরবী সাহিত্য ,ইসলামের সামাজিক ,রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করে ভূমিকা রাখে।
তদুপরি প্রথম শতাব্দীতে যখন তাফসীর ,হাদীস ,কালামশাস্ত্র ,দর্শন ও তাসাউফশাস্ত্র প্রবর্তিত হয় তখন ইরানীরা এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে অবস্থান নিয়েছিল। ইরানের নিশাবুর ,হেরাত ,বাল্খ ,মারভ ,বুখারা ,সামারকান্দ ,রেই ,ইসফাহান ও অন্যান্য শহর এ সকল জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিল। শত শত হাদীসশাস্ত্রবিদ এ সকল শহরে শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষিত হয়েছেন। তাঁরা ইসলামের উজ্জ্বল সভ্যতাকে পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ইরানে বিশেষত খোরাসানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হলো হাদীসশাস্ত্র। ইনসাফের সাথে বলতে গেলে হাদীসশাস্ত্রে ইরানীদের সর্বাধিক ভূমিকাকে স্বীকার করা যথেষ্ট নয় ;বরং বলা উচিত ইরানীরা হাদীসশাস্ত্রের পত্তনকারী। হাদীসশাস্ত্রবিদদের অনেকেই স্বয়ং হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের জন্য প্রায়শই মদীনা ,কুফা ,বসরা ,সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করতেন এবং এই হাদীসসমূহকে তাঁদের ‘ সিহাহ ’ (সহীহ হাদীস গন্থসমূহ) ও ‘ মাসানিদ ’ গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ করেছেন। খোরাসানের হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র মুসলিম বিশ্বে তৎকালীন সময়ে এতটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছিল যে ,মিশর ,আফ্রিকা ,হিজায ,ইরাক ও সিরিয়া হতে কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য খোরাসানের নিশাবুর ,মারভ ,হেরাত ,বালখ ও বুখারার হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট আসতেন।
যাঁরা হাদীস ,মুসনাদ ,সিহাহ ও মাশায়িখদের (বিভিন্ন হাদীস শিক্ষক যাঁরা সরাসরি হাদীস শুনেছেন ও সংকলন করেছেন) বিষয়ে জানেন তাঁরা অবগত আছেন ,আহলে সুন্নাতের সকল হাদীস সংকলক এবং শিয়া মাযহাবের প্রসিদ্ধ চার গ্রন্থের সংকলক ইরানী। হাদীস সংকলকদের মধ্যে শেখ তুসী ,মুসলিম নিশাবুরী ,আবু আবদুর রহমান নাসায়ী ,মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ,আবু দাউদ সাজেস্তানী ,তিরমিযী ,বায়হাকী এ সাত ব্যক্তি খোরাসানের ,শেখ সাদুক কোমের এবং ইবনে মাযা কাযভীনের। এ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ছাড়াও কয়েকশ ’ হাদীসশাস্ত্রবিদ ইরানী ছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ,কালামশাস্ত্রবিদ ,ঐতিহাসিক ,আরবী অভিধান রচয়িতা ,আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ কবিতা রচনাকারী ,মুফাসসির ,রাজনীতিবিদ ,সম্রাট ও পর্যটকদের অধিকাংশই ইরানী ছিলেন। যেমন বার্মাকীরা ,নওবাখতী ,কাশরীয়ান ,সামানীয়ান ,তাহেরীয়ান ,আলেবুইয়া ,গজনভী ,ঘুরী ,খাজা নেজামুল মুলক ,সায়েদীয়ান ,খাজা নাসিরুদ্দীন ,সামআনী ,সারাবদারানসহ অসংখ্য শাসক যাঁরা ইসলামী সভ্যতার প্রচার ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা ইরানী ছিলেন।
আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ চার ইমামের দু ’ জন ইরানী এবং উভয়ই খোরাসানের। তাঁদের প্রথমজন হলেন আবু হানিফা যিনি নিসা (দারগেয) ,কারো কারো মতে কাবুলের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বাল। তিনি খোরাসানের মার্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও বাগদাদে বয়ঃপ্রাপ্ত হন।
সার্বিকভাবে ইরানীরা প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে শক্তিশালী মৌলনীতি ও ভিত্তির ওপর স্থাপন করে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে যায়। যেহেতু বিষয়টি খুবই পরিষ্কার সেহেতু বিস্তারিত আলোচনা হতে বিরত থাকছি।
চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর ঊষালগ্নে ইরানের উত্তরাঞ্চলের তাবারিস্তান ও গিলান মুসলমানদের
হস্তগত হয়। এ শতাব্দীতেই ইরানীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে এবং সামানিগণ বাগদাদের খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে খোরাসান ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। কারণ ধর্মীয় জ্ঞানের জন্যও তাদের খেলাফতের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন ছিল না।
ভারতবর্ষে ইরানীদের কর্মকাণ্ড
গজনভীরা প্রথম ইরানী হিসেবে পবিত্র ইসলামকে ভারতবর্ষে নিয়ে যায়। গজনভীদের সময় পাঞ্জাব প্রদেশ তাদের অধীনে ছিল এবং এ প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর লাহোর ছিল গজনভীদের প্রাদেশিক রাজধানী। এই বংশের শাসনামলে বেশ কিছু মনীষী ভারতে গমন করেন। তন্মধ্যে খোরাসানের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি আল বিরুনীর নাম উল্লেখ্য। যদিও গজনভীদের আক্রমণের লক্ষ্য লুটপাট ও হত্যা ছাড়া কিছু ছিল না এবং তারা ইসলামের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিত না ,কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বলয়কে ধ্বংস করতে এ আক্রমণ ফলপ্রসূ ছিল এবং এতে উত্তরসূরিদের পথ উন্মুক্ত হয়।
ঘুরিগণ
ঘুরী সম্রাটগণ মূলত হেরাতের ঘুর হতে গিয়েছিলেন। ঘুরদের পূর্বপুরুষ শানসাব নামক এক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় যিনি হযরত আলী (আ.)-এর সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আলী তাঁকে ঘুর অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন বনু উমাইয়্যাদের শাসনকালে যখন মসজিদের মিম্বারগুলোতে হযরত আলীর ওপর লানত পড়া হতো এবং বনু উমাইয়্যা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এ কর্মে বাধ্য করত তখন ঘুর অঞ্চলের অধিবাসীরা এতে কোন ক্রমেই রাজী হয়নি ,এমনকি ঘুর ও গুর্জেস্তানের শাসনকর্তারাও এ কর্মে রাজী হননি। প্রথম ঘুরী শাসক যিনি ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান চালান তিনি হলেন সুলতান মুহাম্মদ সাম ঘুরী। তিনি দিল্লী জয় করেন ও একে রাজধানী ঘোষণা করেন। সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে দিল্লী ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের রাজধানী হওয়ার পর হতে ইংরেজদের পদানত হওয়া পর্যন্ত তা-ই ছিল। ঘুরীরা ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়েছিল। তাদের শাসনকালে অসংখ্য আলেম ও মনীষী ভারতে যান ও সেখানেই থেকে যান। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ইসলামের কাজ ঘুরীদের শাসনামলেই শুরু হয়। এ সময়েই মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনসমূহ বিস্তৃতি লাভ করে।
ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও মনীষী যিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন তিনি হলেন খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতি। তিনি ভারতবর্ষে ব্যাপক অবদান রাখেন ও প্রচুর ছাত্র তৈরি করেন যাঁরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হন। তাঁর ধারার শিক্ষা এখনও ভারতবর্ষে বিদ্যমান। তাঁর মাযার ভারতের আজমীরে অবস্থিত এবং সকলেই তাঁকে সম্মান করে থাকেন।
তৈমুরিগণ (মোগলগণ)
তৈমুর লংয়ের বংশধর জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবর ভারতবর্ষে আক্রমণ চালান ও দিল্লী অধিকার করে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ চার শতাব্দী ভারতে রাজত্ব করেন। তৈমুরীদের সঙ্গে সাফাভী শাসকদের সুসম্পর্ক ছিল। এ সময় অনেক ইরানী ভারতে যায়। তৈমুরীদের সময় রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সকল পদ ইরানীদের দখলে ছিল। অসংখ্য সুফী ,কবি ,আলেম ও ফকীহ্ ভারতে হিজরত করে বসবাস শুরু করেন ও সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ চালান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে যে ইরানী ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষে খেদমতের উৎসে পরিণত হয়েছিলেন তিনি হলেন এতেমাদ্দৌলা মির্জা গিয়াস বেগ। তিনি পূর্বে খোরাসানে বসবাস করতেন এবং সম্রাট তাহমাসাবের পক্ষ হতে মারভের শাসনকর্তা ছিলেন। সম্রাট তাহমাসাব তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সকল সম্পত্তি ক্রোক করলে তিনি ভারতবর্ষে হিজরত করেন। সম্রাট জালালউদ্দীন আকবর তাঁকে রাজসভায় গ্রহণ করেন। আকবর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মির্জা গিয়াসের কন্যার বিবাহ দেন। নূর জাহান ভারতের সম্রাজ্ঞীর পদে অধিষ্ঠিত হন।
মির্জা গিয়াসের নাতনী (প্রপৌত্রী) মমতাজ মহলের সঙ্গে জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানের বিবাহ হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নজীরবিহীন ঐতিহাসিক নিদর্শন তাজমহল এই রমণীরই সমাধিস্থল। মির্জা গিয়াস শিয়া ছিলেন ,তাঁর সঙ্গে অনেক ইরানীই ভারতবর্ষে গমন করেন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
দক্ষিণাত্যের কুতুবগণ
মুহাম্মদ আলী কুতুবশাহ ইরানের হামেদানে জন্মগ্রহণ ও যৌবনের প্রারম্ভেই ভারতে হিজরত করেন। তিনি পরবর্তীতে দক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও পরমর্শদাতা হন। যেহেতু তাঁর যথেষ্ট প্রতিভা ছিল তাই দিন দিন তাঁর পদমর্যাদা বাড়তে থাকে ও তিনি ‘ কুতুবুল মূলক ’ উপাধি লাভ করেন। 918 হিজরীতে তিনি দক্ষিণাত্যের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। কুতুবশাহ শেখ সাফিউদ্দীন আরদিবিলীর ভক্ত ছিলেন। তাই যখন তিনি শুনলেন শাহ ইসমাঈল ইরানে শিয়া মাযহাবকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তিনি দক্ষিণাত্যেও তা করার সিদ্ধান্ত নেন ও শিয়া মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাব ঘোষণা করেন।
কুতুবশাহ বংশ দক্ষিণাত্যে ইসলাম ও শিয়া মাযহাবের প্রচারের প্রচেষ্টা চালায় এবং তাঁদের শাসনামলে ইরানীদের এক দল সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তৎকালীন সময়ে যে সকল ইরানী ভারতবর্ষে হিজরত করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন মীর মুহাম্মদ মুমেন আসতারাবাদী। তিনি একজন বড় আলেম ও হাদীসশাস্ত্রবিদ ছিলেন ও পঁচিশ বছর সুলতানের পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি তৎকালীন সময়ের প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক209 ও বর্ণনামূলক210 জ্ঞানসমূহে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন। কুতুবশাহ বংশ এ অঞ্চলে দু ’ শ ’ বছরের মত রাজত্ব করেছে। তাঁদের উজ্জ্বল ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বিধৃত হয়েছে।
বিজাপুরের আদিল শাহ বংশ
এ রাজবংশের প্রধান হলেন ইউসুফ আদিল শাহ যিনি একজন ইরানী ও ‘ সাভে ’ প্রদেশে শৈশব অতিবাহিত করেছেন। তিনি তাঁর যৌবনকালের প্রারম্ভে ইরান হতে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং ভারতে পৌঁছে বিজাপুরের শাসনকর্তার অধীনে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এতদঞ্চলের সুলতান হন এবং ইউসুফ আদিল শাহ সাভেঈ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনিও শিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর শাসনামলে মধ্যভারতের হিন্দুশাসিত বৃহৎ অংশ মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাঁর রাজদরবারে সব সময়ই ইরানী আলেম ও মনীষীদের উপস্থিতি ছিল। মদীনা মুনাওয়ারা ,নাজাফে আশরাফ ও কারবালার সাইয়্যেদগণের এক বড় অংশও তাঁর রাজদরবারে আলেমদের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রচার কাজে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখতেন। তাঁর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োজিত অধিকাংশ ব্যক্তি ছিলেন ইরানী। এই শাসকবর্গের রাজত্বের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ‘ ভারতবর্ষের ইসলামী ইতিহাস ’ গ্রন্থের নাম স্মরণীয়।
আহমাদ নগরের নিজামশাহী বংশ
এ রাজবংশের প্রধান হলেন তিমাভাট নামের এক ভারতীয় যিনি সুলতান আহমাদ শাহ বাহনামীর শাসনামলে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। সুলতান তাঁকে বুদ্ধিমান ও সম্ভাবনাময় লক্ষ্য করে নিজ পুত্র মুহাম্মদ শাহের সঙ্গী হিসেবে মক্তবে প্রেরণ করেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ফার্সী পঠন ও লিখন পদ্ধতি শিক্ষালাভ ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুলতান তাঁকে ‘ মুলকে হাসান বাহরী ’ উপাধি দান করেন। পরবর্তীতে তিনি এতদঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন ও সিংহাসন লাভের পর শিয়া মাযহাব গ্রহণ করে জাফরী ফিকাহর প্রসারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান।
নিজামশাহী শাসকবর্গের রাজদরবারের অধিকাংশ রাজকীয় ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতেন। এ রাজবংশের শাসনকালেই শাহ তাহের হামেদানী (দাক্কানী বা দুকনী নামে প্রসিদ্ধ) ভারতবর্ষে আশ্রয় নেন। তিনি প্রথমে শাহ ইসমাঈল সাফাভীর কৃতজ্ঞভাজন থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর বিরোধিতার কারণে বিরাগভাজন হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেন। তাই গোপনে ভারতে পালিয়ে যান ও নিজামশাহীদের রাজদরবারে আশ্রয় নেন এবং সেখানে মহাসম্মানের সঙ্গে গৃহীত হন। ভারতবর্ষে শাহ তাহেরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইসলামের বিবিধ বিষয়ে আলেমদের প্রশিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীনী মাদ্রাসা ভারতবর্ষের তৎকালীন অন্যতম বৃহত্তম মাদ্রাসা ছিল। তিনি যেমন সম্মানিত ছিলেন তাঁর ভূমিকাও তেমনি মূল্যবান ছিল। তাঁর অবদানের প্রেক্ষিতে তাঁর নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। নিজামশাহী বংশের অবদানও ইতিহাসগ্রন্থসমূহে বিধৃত হয়েছে তবে তাঁদের কর্মকাণ্ড ও ভূমিকার ওপর পুরু একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক।
অযোধ্যার নিশাবুরী সুলতানগণ
শাহ সুলতান হুসাইন সাফাভীর সময়কালে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নামের নিশাবুরের একজন আলেম ভারতে যান ও দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সন্তানরা বিভিন্ন সরকারী (রাজদরবারে) পদ লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে শুরু করেন। বোরহানুল মূলক নামের তাঁর এক প্রপৌত্র এই অযোধ্যার সুবেদার হন। বেশ কিছুদিন পর তিনি স্বাধীনতা লাভ করে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সন্তানরা এ প্রদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করে।
নিশাবুরের এই শাসকগণের সময় মাশহাদ ,নিশাবুর ও খোরাসানের অন্যান্য শহর হতে উল্লেখযোগ্য ইরানী ভারতবর্ষে গমন করেন এবং এ প্রদেশের রাজধানী লক্ষে èৗতে বসবাস শুরু করেন। তাই এ শহরের প্রায় সকল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। নিশাবুরের নাকাভী সাইয়্যেদগণ (ইমাম আলী নাকীর বংশধর) এ সময়েই ভারতবর্ষে যান। ‘ আবাকাতুল আনওয়ার ’ গ্রন্থের রচয়িতা মরহুম মীর হামিদ হুসাইন নিশাবুরী এই শাসকবর্গের সময়েই তাঁর ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। নিশাবুরের এ সম্রাটগণের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।
কাশ্মীরে ইসলাম
মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে 710 হিজরী পর্যন্ত কাশ্মীরের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ শতাব্দীতেই একজন ইরানী দরবেশের পোষাক পরিধান করে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং ধর্মীয় প্রচার শুরু করেন। যেহেতু ভারত ও কাশ্মীরের মানুষ দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের পছন্দ করত তাই তারা তাঁর চারিদিকে ভীড় জমাল। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাব বাড়তে লাগলো।
কাসিম ফিরিশতা তাঁর ‘ তারিখে ফিরিশতা ’ গ্রন্থে লিখেছেন , “ এ ব্যক্তির নাম ছিল শাহ মির্জা। তিনি রাজা সিয়েদেব-এর শাসনামলে কাশ্মীরের শ্রীনগরে যান ও তাঁর দরবারে চাকুরী নেন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই রাজার মনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন ও নিজের জন্য পথ উন্মুক্ত করতে থাকেন। কিছুদিন পর সিয়েদেবের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রঞ্জন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহ মির্জাকে মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সময় মির্জা অধিকতর ক্ষমতা লাভ করায় তাঁর সন্তানরা বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইত্যবসরে রাজা রঞ্জনের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী রাজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শাহ মির্জা ও তাঁর সন্তানরা তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করেন। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে শাহ মির্জাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইসলাম কবুল করেন । এর ফলে শাহ মির্জা স্বয়ং রাজার দায়িত্ব নেন ও নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি শামসুদ্দীন উপাধি ধারণ করে তাঁর নামে খুতবা পড়ার নির্দেশ দেন। ”
তিনিই কাশ্মীরে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং মানুষের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টায় ব্রত হন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হয়।
অন্য যে ব্যক্তিটি কাশ্মীরে ইসলামের সেবায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তিনি হলেন মীর সাইয়্যেদ আলী হামেদানী। ইসলামের প্রবাদ এই ব্যক্তিত্ব কাশ্মীরে সহস্র ছাত্র তৈরি করেছেন যাঁদের প্রত্যেকেই পরবর্তীতে উঁচু মানের শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন। কাশ্মীরে এখন তাঁর নাম সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়। তাঁর কবরে সহস্র লোক যিয়ারত করে। আশুরার দিন শোকাহত জনতা তাঁর মাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পতাকাসমূহ তাঁর সম্মানে নীচু করে।
চীনে ইসলাম
স্পষ্টরূপে বলা সম্ভব নয় যে ,চীনে ইসলাম কিভাবে ও কখন প্রবেশ করেছিল। এতটুকু জানা যায় ,ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীগুলোতেই সামারকান্দ ,বুখারা ও খাওয়ারেজমের কিছু ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ইসলাম সেখানে প্রচারিত হয়। খাওয়ারেজম শাহী আমলে বিশেষত আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারেজম শাহ যখন তুর্কিস্তান ও আতরাবা দখল করেন তখন ইরানীদের চীনে যাতায়াত ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মোগলদের ইরান জয়ের পর প্রচুর সংখ্যক ইরানী চীনে গমন করে। চেঙ্গিস খান খোরাসান দখলের পর সেখানকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে চীন ও মঙ্গোলিয়ায় তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি জ্ঞান ও স্থাপত্যকলায় পারদর্শী এই সকল ব্যক্তিকে চীন ও মঙ্গোলিয়ার মানুষদের প্রশিক্ষিত ,স্থাপত্য ও শিল্পকলা শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। ইরানের প্রচলিত শিল্প ও স্থাপত্যকলা ছাড়াও তাঁরা তাদের ধর্ম শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই ইরানীদের মাধ্যমে ইসলাম চীনে পরিচিত হয়। চীনা মুসলমানদের সকল ধর্মীয় গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ইসলাম
পবিত্র ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষ ,পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহ ও ওমান সাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ,ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছায়। এসব অঞ্চলেও ইসলাম প্রসারে ইরানী নাবিক ও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল । মোগলদের ইরান আক্রমণের সময় এতদঞ্চলের শহরসমূহ ধ্বংস হওয়ায় অনেক মনীষী ও ব্যবসায়ী এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। ইরানের পূর্বাঞ্চলের লোকজন ভারতবর্ষে হিজরত করে এবং মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে অন্য দেশে পাড়ি জমায়।
ইরানের দক্ষিণাঞ্চল ,পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা মোগলদের বিশেষত তৈমুর লংয়ের আক্রমণের পর বাধ্য হয়ে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে পুঁজিসহ হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুঁজি নষ্ট বা হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে তাদের অনেকেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রবাসী হয়। পূর্ব আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় হিজরতকারী অধিকাংশ ইরানীই এ অঞ্চলের। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই প্রবাসী ইরানীদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। তারা তাদের বক্তব্য ও উপদেশের মাধ্যমে স্থানীয়দের ইসলামের মহাসত্যের পথ প্রদর্শন করত। ইরানীদের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন এখনও এতদঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণানির্ভর গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত।
উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার ইরানীদের ইসলাম প্রচারে অবদান
এ নিবন্ধের প্রথমে আমরা উল্লেখ করেছি পূর্ব ইরানের খোরাসানের অধিবাসীরা সাহসী এক আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়্যা শাসনের পতন ঘটায়। আব্বাসীরা ক্ষমতায় আরোহণের পর নিজস্ব কিছু লোক ছাড়া আরবদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতার বিভিন্ন পদ হতে দূরে সরিয়ে রাখে। যেহেতু খোরাসানীদের পক্ষ হতে অভ্যুত্থানের কারণে তাদের ক্ষমতা লাভ সম্ভব হয়েছিল সেহেতু অধিকাংশ প্রদেশেই তারা খোরাসানীদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।
মামুনের শাসনকালে যখন তিনি খোরাসান হতে বাগদাদে ফিরে আসেন তখন খোরাসানের কিছু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। মামুন তাঁদের সকলকেই বিভিন্ন পদ দান করেন ও বিভিন্ন শহরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। বিশেষত যে অঞ্চলটির প্রতি বনি আব্বাস বিশেষ দৃষ্টি রাখত ও তার বিষয়ে ভীত ছিল সেটি হলো উত্তর আফ্রিকা ও দূর পাশ্চাত্য। কারণ তখনও স্পেন (আন্দালুস) উমাইয়্যাদের হাতে ছিল এবং তারা ঐ দিক হতে আক্রমণের ভয় করত।
এ কারণেই আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দীর শাসনামল হতে মিশর ও আফ্রিকার শাসনকর্তাদের খোরাসানীদের মধ্য হতে নির্বাচন করত ;কারণ তারা বনু উমাইয়্যার চরম শত্রু ছিল। এ সময়ে ইরানের পূর্বাঞ্চলের ও খোরাসানের অধিবাসীদের প্রভাব মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপক বেড়ে যায় এবং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পায়। সে সাথে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপনের ক্ষমতাও লাভ করে।
এ ইরানী পরিবারসমূহ দূর পাশ্চাত্য ,ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও এশিয়া মাইনরের দেশগুলোতে ইসলামের প্রচারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। আমরা নিম্নে মাহ্দী আব্বাসীর সময়কাল হতে ফাতেমীদের সময়কাল পর্যন্ত যে সকল ইরানী মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় শাসনকর্তা ছিলেন তার উল্লেখ করছি :
1. ইয়াহইয়া ইবনে দাউদ নিশাবুরী
2. মুসল্লামাহ্ ইবনে ইয়াহইয়া খোরাসানী
3. ইবাদ ইবনে মুহাম্মদ বালখী
4. সারী ইবনে হাকাম বালখী
5. মুহাম্মদ ইবনে সারী বালখী
6. আবদুল্লাহ্ ইবনে সারী বালখী
7. আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের বুশানজী
8. উমাইর বদগাইসী হারভী
9. ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া সামারকান্দী
10. আবদুল ওয়াহেদ বুশানজী
11. আনবাসাহ্ ইবনে ইসহাক হারভী
12. ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ্
13. মুযাহিম ইবনে খাকান
14. আহমাদ ইবনে মুযাহিম
15. আরখুজ ইবনে আউলাগ
16. আ হমাদ ইবনে তুলুন ফারগানী
17. খামারুইয়াহ্ ইবনে আহমাদ ফারগানী
18. জাইশ ইবনে খামারুইয়াহ্ ফারগানী
19. হারুন ইবনে খামারুইয়াহ্ ফারগানী
20. ঈসা নুশাহরী বালখী
21. শাইবান ইবনে আহমাদ ফারগানী
22. মুহাম্মদ ইবনে আলী খালানজী
23. মুহাম্মদ ইবনে তাগবাজ ফারগানী
24. আনুজুর ইবনে আখশিদ ফারগানী
25. আলী ইবনে আখশিদ
26. আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আখশিদ
27. শো ’ লে আখশিদী
28. হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ আখশিদী
29. ফাতেক আখশিদী আমীরে শাম
30. হুসাইন ইবনে আহমাদ ইবনে রুস্তম
উপরিউক্ত 30 ব্যক্তি খোরাসানের। তাঁরা ধারাবাহিকভাবে দু ’ শ ’ বছর মিশর ,উত্তর আফ্রিকা ,দূর পাশ্চাত্য ,ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলসহ আটলান্টিক মহাসাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত দেশসমূহে যা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষা ,ইসলামী শরীয়তের প্রচার এবং স্পেনসহ ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের বিজয়ে তাঁরা ভূমিকা রেখেছিলেন। এই সময়কালে খোরাসান ও ইরানের অন্যান্য শহর হতে শত শত আলেম ,ফকীহ্ ,মুজতাহিদ ,মুফাসসির ,মুহাদ্দিস ,কাযী (বিচারক) ,বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলে হিজরত করেন এবং সেখানে ইসলামের শিক্ষা ও মৌলনীতিকে দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করেন। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার ইসলামের ইতিহাস ,সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রচুর ইরানীর নাম লক্ষ্য করা যায় যা ‘ বৃহত্তর খোরাসানের ইতিহাস ’ গ্রন্থে তিউনিসিয়া ও মরক্কোর বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সূত্রে আজিজুল্লাহ্ আত্তারাদী বর্ণনা করেছেন।
প্রতিক্রিয়াসমূহ
ইরানীদের ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা ও ইখলাস প্রমাণের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি উদাহরণ হলো দ্বিতীয় হিজরীতে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের বিরোধী কিছু ধারার বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে তারা এ বিরোধী ধারাসমূহকে শক্তিশালী করেছে নাকি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তা আমরা আলোচনা করব।
তিনটি ভিন্ন ধারা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল :
একটি ধারা হল জিন্দিক বা নাস্তিক্য ধারা। জিন্দিকরা দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমভাগে তাওহীদ ও ইসলামের অন্যান্য মৌল বিশ্বাসসমূহের বিরুদ্ধে প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়।
দ্বিতীয় ধারাটি হলো আরব জাতীয়তাবাদ যার ভিত্তি নির্মাতা উমাইয়্যা শাসকগণ। তারা ইসলামের বৈষম্যহীন সমাজ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইসলামের মৌলনীতিকে পদদলিত করে।
তৃতীয় বিষয় হলো বিলাসব্যসন ,সংগীত ও অনর্থক কর্মের প্রচলন। এটিও উমাইয়্যাগণ শুরু করে ও আব্বাসীয় আমলে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এই তিন ধারা পর্যায়ক্রমে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ,সামাজিক মৌলনীতি ,নৈতিক ও ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঘটনাক্রমে তিনটি আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষেই ইরানীদের ভূমিকা ছিল।
সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষকগণ দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে জিন্দিক চিন্তাধারার উদ্ভবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যেমন প্রথমত ‘ জানাদাকা ’ বা ‘ জিনদিকাহ্ ’ শব্দটির মূল কোথা হতে এসেছে ?زنديق (জিন্দিক) শব্দটিزنديك হতে এসেছে নাকি অন্য কোন শব্দ হতে ? কাদেরকে জিন্দিক বলা হতো ? তারা কি মনী ধর্মের অনুসারী ? তারা কি সেই সকল ইরানী যারা তাদের প্রাচীন ধর্মে অটল ছিল ,যেমন যারথুষ্ট্র ,মনী ও মাযদাকী নাকি তারা অতি প্রাকৃতিক কোন অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ছিল যারা কোন ধর্মকেই স্বীকার করত না ?
বাস্তব সত্য হলো এদের সকলকেই ‘ জিন্দিক ’ বলে ডাকা হতো ,এমনকি যে সকল মুসলমান বিভিন্ন অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতো ,ধার্মিক ব্যক্তিদের উপহাস করত বা কোন কোন সময় গদ্য ,কবিতা বা ছন্দের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে তিরস্কার করত তাদেরকেও জিন্দিক বলা হতো।
আরবদের মধ্যে জিন্দিকী প্রবণতা কখন হতে শুরু হয়েছে ? ইসলামের আবির্ভাবের পর অন্যান্য জাতি বিশেষত ইরানীদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ,নাকি পূর্ব হতেই তারা এরূপ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিল ?
জিন্দিক শব্দটির মূল ও ভাবার্থ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা এ শব্দটি প্রথমদিকে শুধু মনুয়ীদের (মনী ধর্মের অনুসারীদের) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে দাহরী ,মাজুসী ,এমনকি যে কোন নাস্তিকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়।
এ ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে ইসলাম-পূর্ব আরবদের মাঝে এরূপ চিন্তার
অস্তিত্ব ছিল। ইবনে কুতাইবার ‘ আল মাআরিফ ’ এবং ‘ রাসতাহর আল-আলাকুন নাফিসা ’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে জাহেলিয়াতের সময় কুরাইশরা হীরার আরবদের মাধ্যমে এ শব্দের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছিল।
যা হোক নিশ্চিত যে ,ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীগুলোতেই একদলকে এ নামে অভিহিত করা হতো। তাদের কেউ কেউ আরব ,আবার কেউ ইরানী ছিল। যেমন আবদুল কারিম ইবনে আবিল আউজাহ্ ,সালিহ ইবনে আবদুল কুদ্দুস ,আবু শাকির দাইছানী ,ইবনুর রাভান্দী ,বেশর ইবনে বারেদ ,আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফফা ,ইউনুস ইবনে আবি ফারওয়া ,হাম্মাদ আজরাদ ,হাম্মাদ রাভিয়া ,হাম্মাদ ইবনে যিবারকান ,ইয়াহ্ইয়া ইবনে যিয়াদ ,মুতী ইবনে আইয়াম ,ইয়াযদান ইবনে বাজান ,ইয়াযীদ ইবনুল ফাইয ,আফশিন ,আবু নাওয়াস ,আলী ইবনুল খালিল ,ইবনে মুনাযার ,হুসেইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ,আবদুল্লাহ্ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ,দাউদ ইবনে আলী ,ইয়াকুব ইবনে ফাযল ইবনে আবদুর রহমান মাতলাবী ,ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মূলক ,আবু মুসলিম খোরাসানী ,বারামাকে প্রমুখ।
এদের কেউ কেউ যেমন ইবনে আবিল আউজাহ্ নিশ্চিতভাবেই অতি প্রাকৃতিক কোন অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল। শিয়া হাদীসগ্রন্থ সমূহের বর্ণনামতে সে পবিত্র ইমামগণ ও তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে যে বিতর্কসমূহ করেছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ,সে অতিপ্রাকৃতিক কোন অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না। উপরোক্ত ব্যক্তিসমূহের কারো কারো জিন্দিক হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও কারো কারো বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।
দলিল-প্রমাণ হতে জিন্দিকদের উদ্ভব যে অর্থেই হয়ে থাকুক-যেমন মনুয়ী অর্থাৎ আলো ও অন্ধকারের জন্য দু ’ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী অথবা খোদায় অবিশ্বাসী নাস্তিক বা দাহ্রী-এ বিষয়টি রাজনৈতিক ব্যক্তি ও ক্ষমতাশালীদের হাতে বড় একটি অস্ত্র হয়েছিল যার মাধ্যমে তারা বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করত । তাই কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না ,যাদের জিন্দিক বলে অভিহিত করা হয়েছে তাদের সকলেই আসলেও জিন্দিক ছিল। যখন অভিযুক্ত এ সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই ইসলামের প্রতি নিবেদিত ,দুনিয়াত্যাগী ও সৎকর্মশীল বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদের কেউ কেউ প্রতিশ্রুতবদ্ধ শিয়া ও পবিত্র ইমামগণের বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং স্পষ্ট ,ক্ষমতাসীন খলীফাদের বিরোধিতার কারণেই তাঁদের এরূপ নামে অভিহিত করা হয়েছিল।
তাদের কেউ কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের চর্চার কারণে এরূপ নামে অভিহিত হয়েছেন। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরস্ত ’ নামক গ্রন্থে আবু যাইদ আহমাদ ইবনে সাহল বালখী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ,তিনি জিন্দিক বলে অভিযুক্ত। অতঃপর যাইদের এক নিকটতম ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন , “ এই ব্যক্তি মজলুম ছিলেন। তিনি একত্ববাদী ও খোদা উপাসক ছিলেন। অন্যদের হতে আমি তাঁকে উত্তমরূপে চিনতাম। আমরা একত্রে বড় হয়েছি ,তিনি যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করায় জিন্দিক নামে অভিহিত হয়েছিলেন। আমরা দু ’ জন একত্রে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করতাম এবং কেউই নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়িনি। ” 211
আহমাদ আমিন212 আল আগানী হতে বর্ণনা করেছেন , “ হামিদ ইবনে সাঈদ মুতাজিলাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি আব্বাসীয় খলীফা মোতাসিমের রাজকীয় কাজী ইবনে আবি দাউদের বিরোধিতা করতেন। ইবনে আবি দাউদ তাঁকে জিন্দিক বলে অভিহিত করে মুতাসিমের কান ভারী করেন। ” 213
ইবনে মুনাযির সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে ইউনুস ইবনে আবি ফারওয়া প্রকাশ্য সভায় তাঁকে জিন্দিক বলে প্রচার করেন এবং ঐ সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তি সভা হতে বেরিয়ে মসজিদে গিয়ে দেখে ইবনে মুনাযির এক কোণায় নামাজে রত।
আফশিন নামক অপর এক ব্যক্তিকে জিন্দিক বলা হতো ,অথচ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তাঁর ব্যক্তিত্বহানির জন্য এরূপ করত ।
আব্বাসীয় খলীফা মনসুর দাওয়ানেকী এবং তাঁর বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুফিয়ান ইবনে মুয়াবিয়া মাহলাবীর সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফফার কোন এক কারণে শত্রুতা ছিল। তাই মনসুরের গোপন নির্দেশে সুফিয়ান তাঁকে হত্যা করেন এবং বলেন ইবনে মুকাফফা বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করত ,কিন্তু আন্তরিকভাবে জিন্দিক ছিলেন। ইবনে মুকাফফা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ও মনীর গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। তার কোন কোন লেখায় ইসলামের প্রতি নিবেদিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মনীর রচিত গ্রন্থসমূহ অনুবাদ বা জিন্দিকদের সমাবেশে উপস্থিতি তাঁর জিন্দিক হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।
বার্মাকীদের ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালীন আসমায়ী তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। যখন বার্মাকীদের উজ্জ্বল দিনের অবসান ঘটল তখন তিনি তাদের জিন্দিক বলে প্রচার শুরু করলেন।
আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দী জিন্দিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক জিন্দিককে হত্যা করেন ও বলেন তাঁর পিতামহের প্রপিতা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁকে স্বপ্নে এ কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন ,অথচ প্রসিদ্ধ জিন্দিক বেশার ইবনে বারেদ তাঁর দরবারের প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিল এবং আশি বছর এ পথে (কুফরীর) অতিবাহিত করা সত্ত্বেও মাহ্দী তাকে কিছু বলেননি ;বরং বিশিষ্ট ফকীহ্গণের নিকট তিনি বেশারের মতামতের ইতিবাচক ব্যাখ্যা দান করতেন। কিন্তু শেষ বয়সে যখন বেশার রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে মাহ্দীর অসম্মানে বনু উমাইয়্যার প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তখন খলীফা মাহ্দী আব্বাসীর জিন্দিক বিরোধী অনুভূতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তিনি তাকে চাবুক দ্বারা প্রহারের নির্দেশ দেন ও এভাবেই তার মৃত্যু হয়।
জিন্দিকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়া
যদিও জিন্দিকী চিন্তাধারার মূল ভিত্তি কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু কিছু ইরানীর মধ্যে প্রোথিত ছিল তদুপরি জিন্দিকতার ধারা ইরানীদের মধ্যে কখনোই বিস্তার লাভ করেনি ;বরং ইরানীদের পক্ষ হতে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। ইরানী মুসলমান আলেমগণ একদিকে কালামশাস্ত্রের মাধ্যমে অন্যদিকে ইরানী ফকীহগণ ফেকাহ্শাস্ত্রের মাধ্যমে এ ধারার জবাব দেন।
আমরা জানি ইরাক ইরানী ফকীহ্ ,আলেম ও অন্যান্যদের কেন্দ্র ছিল। ইরাকের ফকীহ্গণ214 জিন্দিকদের বিরুদ্ধে অন্যদের চেয়ে কঠোরতর প্রতিক্রিয়া দেখান। আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীরা ইরানী ফকীহ্গণের অংশ হিসেবে ইরাকে বসবাস করতেন। জিন্দিকদের বিষয়ে শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের চেয়ে ইরানী আবু হানিফার ফতোয়া কঠোরতর। শাফেয়ী ‘ মুরতাদের তওবা কবুল ’ -এর অধ্যায়ে মুরতাদ ও জিন্দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি এবং উভয়ের তওবাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এর বিপরীতে আবু হানীফা তাঁর দু ’ মতের একটিকে প্রাধান্য দিয়ে জিন্দিকের তওবা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।
কথিত আছে আবু হানিফার অনুসারীরা তাঁর পক্ষ হতে জিন্দিকদের তওবা অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ফতোয়াটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতেন যা জিন্দিকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের কঠোর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত।
দ্বিতীয় ধারাটি হলো জাতিগত গোঁড়ামি ও গরিমা এবং জাতি-বৈষম্য যা ইসলামের সাম্য ধারণার বিরোধী। আরবগণ এ বিচ্যুতির জন্ম দেয়। উমাইয়্যাগণ আরব ও অনারবের মধ্যে পার্থক্যের নীতির ওপর তাদের রাজনীতির ভিত্তি রচনা করে। মুয়াবিয়া তাঁর অধীন বিভিন্ন শাসনকর্তাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে ,আরবদের অন্যদের ওপর সব বিষয়ে যেন প্রাধান্য দেয়া হয়। এ বিষয়টি ইসলামের দেহে মারাত্মক আঘাত হানে। ইসলামী শাসন ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ ছিল এটি। স্বাভাবিকভাবেই কোন জাতি তাদের ওপর অপর জাতির প্রাধান্য ও শাসন কর্তৃত্বকে মেনে নেয় না। ইরানীরা ইসলামকে গ্রহণ করেছিল ;আরবদের প্রভুত্বকে নয়। অন্যান্য জাতির ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল ইসলাম জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন ও মানবতাবাদী ধর্ম। তাই ইরানীসহ অন্যান্য জাতি কখনই আরবদের প্রাধান্যকে মেনে নেয়নি।
এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইরানীরা যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা অত্যন্ত মানবিক ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। তারা আরবদের আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান জানায়। তাদের এ কর্ম রাসূলের এ কথার সত্যতাকে প্রমাণ করে , “ আল্লাহর কসম! পরবর্তীতে ইরানীরাই তোমাদের ইসলাম ও আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে ঠিক যেমনটি তোমরা প্রথমে তাদের দাওয়াত করেছিলে। ” 215 ইসলামের প্রথম যুগে ইরানী মুসলমানগণ এ ধারার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করে তার মূলে ছিল ইসলামের সাম্যের ধারণা ;আরবদের ওপর ইরানীদের প্রাধান্যের ধারণা নয়।
উমাইয়্যাদের বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে খোরাসানের কৃষ্ণ পোশাকধারিগণ যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা ইসলাম ও ন্যায়ের দাবিতে ছিল ;অন্য কোন দাবিতে নয়। আব্বাসীয়দের তৎকালীন প্রতিনিধিগণ গোপনে যে আহ্বান রাখতেন তাতে ইসলামের ন্যায়বিচার ও রাসূল (সা.)-এর বংশধরদের সন্তুষ্টির দিকে আহ্বান করতেন। খোরাসানের মানুষদের এ পথে আহ্বানকারীর নাম গোপন থাকলেও তাঁর পক্ষে যে কৃষ্ণ বর্ণের দাওয়াত পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে লেখা ছিল :
) أُذِن للّذين يقاتلون بأنَّهم ظلموا و إنَّ الله على نصرهم لقدير (
“ যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে ,আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। ” (সূরা হজ্ব: 39)
এ আন্দোলনের শুরুতে আলে আব্বাস বা আবু মুসলিমের নাম যেমন ছিল না তেমনি ইরানী জাতীয়তাবাদের কথাও সেখানে ছিল না ;বরং শুধু ইসলাম ,কোরআন ,রাসূলের আহলে বাইতের সন্তুষ্টি ,ন্যায়বিচার ও ইসলামের সাম্যের কথা উপস্থাপিত হতো। অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র স্লোগানগুলোই এ আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছিল। আবু মুসলিম পরবর্তী সময়ে ইবরাহীম ইমামের পক্ষ হতে এ আন্দোলনের নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। একবার আব্বাসীয় প্রতিনিধি গোপনে হজ্বে আসলে ইবরাহীম ইমাম তাঁকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করান। আবু মুসলিম সম্পর্কে জানা যায়নি তিনি আরব না ইরানী। তবে যেহেতু তিনি খোরাসান হতে আন্দোলন শুরু করেন সেহেতু আবু মুসলিম খোরাসানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
সাম্প্রতিক কোন কোন ইরানী ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কৃষ্ণ পোশাকধারীদের সমগ্র আন্দোলনকে আবু মুসলিম খোরাসানীর কৃতিত্ব বলে চালাতে। সন্দেহ নেই আবু মুসলিম একজন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন ,কিন্তু তাঁর সাফল্যের পরিবেশ সৃষ্টির কারণ ছিল ভিন্ন। ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে যখন আবু মুসলিম মনসুরের দরবারে তাঁর ক্রোধের শিকার হয়ে আনীত হন তখন আবু মুসলিম আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতি তাঁর সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনসুরের ক্রোধকে প্রশমনের চেষ্টা করেন। মনসুর জবাবে বলেন , “ যদি কোন ক্রীতদাসী এ কথা বলত তাহলে হয়তো সফল হতো ,কিন্তু তুমি তোমার নিজ ক্ষমতা বলে এরূপ অভ্যুত্থানে কখনই সক্ষম ছিলে না ,এমনকি এক ব্যক্তির ওপরও তোমার কর্তৃত্ব কার্যকর ছিল না। ” যদিও মনসুরের কথায় অতিরঞ্জন রয়েছে তদুপরি কথাটি সত্য। এ কারণেই মনসুর তাঁকে ক্ষমতা ও সম্মানের শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও হত্যা করতে সক্ষম হন এবং কেউই আবু মুসলিমের পক্ষে প্রতিবাদ করেনি।
আব্বাসীয়গণ ইরানীদের ইসলামী চেতনাকে ব্যবহার করে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবংأُذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا আয়াতটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবীর আহলে বাইতের মাজলুমিয়াতের কথাই বলত এবং ইরানীদের ওপর উমাইয়্যাদের নির্যাতনের কথা কমই বলত।
129 হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিনে কৃষ্ণ পোশাকধারীরা দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অভ্যুত্থান করে এবং ঈদের খুতবায় তাদের বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। ঈদের খুতবা সুলাইমান ইবনে কাসির নামক এক আরব যিনি সম্ভবত আব্বাসীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন ,পাঠ করে। তাদের স্লোগানের মধ্যে তাদের লক্ষ্য নিহিত ছিল। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাদের অন্যতম স্লোগান ছিল :
) يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر و أُنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوآ إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم (
“ হে মানব জাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। ” 216
এ আয়াতে ব্যবহৃত ‘ শুয়ুব ’ শব্দ হতে ইরানীদের ‘ শুয়ুবীয়া ’ বলা হতো। কারণ মুফাসসিরদের বর্ণনানুযায়ী শুয়ুবীয়া হলো যাদের সম্মিলনে গোত্রীয়তার রং নেই। ইরানীরা সাম্যের পক্ষে ও জাতিগত বৈষম্যের বিরোধী হওয়ায় তখন এ নামে অভিহিত হয়েছিল।
আরবদের এরূপ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ইরানীদের এ প্রতিক্রিয়া তাদের ইসলামী চরিত্রের ও ইসলামের প্রতি ঐকান্তিকতার সাক্ষ্য বহন করে। যদি ইসলামের প্রতি ইরানীদের ঐকান্তিকতা না থাকত তবে তারাও আরবদের ন্যায় তাদের ইতিহাস ও জাতিগত ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করতে পারত এবং সে ক্ষেত্রে আরবদের পেছনে ফেলে দিত। কারণ আরবদের চেয়ে ইরানীদের জাতিগত ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি ;বরং আরবদের চেয়ে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।
অবশ্য শুয়ুবী আন্দোলন পরবর্তীতে বিচ্যুত হয়ে আরব জাতীয়তাবাদের পরিণতি লাভ করেছিল। অর্থাৎ আরবদের ওপর ইরানী (আর্য) জাতি ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে পর্যবসিত হয়।
তবে যখনই শুয়ুবী আন্দোলন এ পর্যায়ে পৌঁছে তখনই ইরানের তাকওয়াসম্পন্ন আলেম ও সাধারণ মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান অর্থাৎ ইরানীদের পক্ষ হতে আরেকটি ইসলামী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় যা তাদেরই বিচ্যুত এক অংশের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়। ফলে শুয়ুবী আন্দোলন পরাস্ত হয়। যদি সকল ইরানীই ইসলামের প্রথম পথকে আঁকড়ে থাকত তবে সাধারণভাবে ইসলামী বিশ্বে ও বিশেষভাবে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে আরো উত্তম ভূমিকা রাখতে পারত।
কোন কোন ইরানী এই শুয়ুবী আন্দোলনের প্রতি এতটা অসন্তুষ্ট ছিলেন যে ,একে ইসলামের জন্য বড় বিপদ মনে করে নিজ জাতিসত্তার বিরুদ্ধে আরবীয় গোঁড়ামি প্রদর্শন শুরু করেন। এটি ইতিহাসের অন্যতম আশ্চর্যজনক ঘটনা যা ইরানীদের অন্তরে ইসলামের গভীর ছাপের প্রমাণ।
‘ কাশশাফ ’ তাফসীরের লেখক ‘ জামাখশারী একজন ইরানী বড় আলেম ও তাঁর সময়ের বিরল প্রতিভা ,তিনি ইরানের খোরাসানের খাওয়ারেজমের অধিবাসী। তিনি তাঁর জীবন বায়তুল্লাহর পাশে কাটিয়েছেন বলে ‘ জারুল্লাহ্ ’ বা আল্লাহর প্রতিবেশী উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ‘ সারফ ’ ও ‘ নাহু ’ সম্পর্কিত তাঁর ‘ আল মুফাস্সাল ’ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন , “ একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাকে আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত হওয়ার ও আরবদের পক্ষাবলম্বনের প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুগ্রহে আমি তাদের সহযোগীদের হতে বিচ্ছিন্ন হইনি ও শুয়ুবীয়াদের খপ্পরে পড়িনি। শুয়ুবীরা কোন কল্যাণই লাভ করেনি ;লানতকারীর লানত ও তিরস্কারকারীদের তীরবিদ্ধ হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যতীত। ”
জামাখশারীর শেষ কথাটি হতে বোঝা যায় ‘ শুয়ুবী ’ হওয়ার বিষয়টি ইরানীদের নিকট কতটা নিন্দনীয় ও প্রত্যাখ্যাত ছিল। তাই এর পক্ষাবলম্বনকারীদের ভাগ্যে সমালোচনা ,অভিশাপ ও লানত ছাড়া কিছুই জোটেনি।
‘ ইয়াতিমাতুদ দাহর ’ গ্রন্থের লেখক সায়ালাবী নিশাবুরী (মৃত্যু 329 হিজরী) জামাখশারীর ন্যায় ইরানী মুসলমানদের গৌরব বলে বিবেচিত হতেন। এই প্রখ্যাত আলেম জামাখশারী হতেও তীব্রভাবে শুয়ুবীদের বিরুদ্ধে ও আরবদের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর ‘ সিররুল আদাব ফি মাজারী কালামিল আরাব ’ গ্রন্থে একজন গোঁড়া আরবের ন্যায় অনারবদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর ওপর দরূদ পড়ে বলেন ,
“ যে কেউ আল্লাহ্কে ভালবাসে সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেও ভালবাসবে। আর যে কেউ রাসূলকে ভালবাসবে সে আরবদের ভালবাসবে । যারা আরবদের ভালবাসবে এই শ্রেষ্ঠ জাতির ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাষাকেও ভালবাসবে। যে আরবী ভাষাকে ভালবাসবে সে এ ভাষার প্রতি গুরুত্ব দেবে। আল্লাহ্ যাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করেন সে বিশ্বাস করবে মুহাম্মদ (সা.) সর্বোত্তম নবী ,ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট পথ। আরব শ্রেষ্ঠ জাতি ও আরবী সর্বোত্তম ভাষা। ”
তবে সায়ালাবীর ‘ আরব সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ’ এ কথাটি ভ্রান্ত। ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে আরবদের শ্রেষ্ঠ মনে করার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এ ধরনের চিন্তা ইসলামী চিন্তার পরিপন্থী। তাই যে ইসলাম বিশ্বাস করবে সে অবধারিতভাবে বিশ্বাস করবে- কোন জাতিরই অপর জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এই যে ,মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হয় জ্ঞানের কারণে ,নতুবা তাকওয়া ও আমলের কারণে।
) هل يستوي اللذين يعلمون و اللّذين لا يعلمون (
“ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে ? ” 217
) إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم (
“ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন। ” 218
) فضّل الله الْمجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً (
“ আল্লাহ্ মুজাহেদীনকে (তাঁর পথে যুদ্ধ ও প্রচেষ্টাকারীকে) উপবিষ্টদের ওপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ” 219
সায়ালাবী তাঁর বক্তব্যে যে পর্যায়ক্রম উল্লেখ করে আরবদের প্রতি ভালবাসার ফল আরবী ভাষার প্রতি ভালবাসা বলে দাবি করেছেন তাও সঠিক নয় ;বরং কোরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার সরাসরি ফল হলো আরবী ভাষার প্রতি ভালবাসা। শুয়ূবীদের বিপরীতে অবস্থান নিতে গিয়ে সায়ালাবীর মতো বিচ্যুত ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।
দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ইরানী কালামশাস্ত্রবিদ আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনে মুসান্নাও এরূপ আরব গোঁড়ামি পোষণ করে অনারবদের ছোট করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হলো ‘ মাকাতিলু ফারসানুল আরাব ’ ।
এর বিপরীতে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বংশধর এবং ‘ মুরুজুয যাহাব ’ ও ‘ আত তানবিহ্ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থের লেখক মাসউদী (মৃত্যু চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধ) আবু উবাইদার গ্রন্থের জবাবে ‘ মাকাতিলু ফারসানুল আজাম ’ গ্রন্থ রচনা করেন। মাসউদী তাঁর ‘ আত তানবিহ্ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থের 49 পৃষ্ঠায় সাসানী সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ,
“ চব্বিশতম মনোরম শহরে তিনি চল্লিশ দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। আমরা তাঁর জীবনী ,তিনি ও তাঁর সহযোগীদের নিহত হওয়ার কারণ এবং যে সকল ইরানী সাহসিকতা ও মর্যাদায় ইতিহাসে স্মরণীয় তাঁদের গৌরবময় জীবনী ‘ মাকাতিলু ফারসানুল আজাম ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। গ্রন্থটি আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনে মুসান্না রচিত ‘ মাকাতিলু ফারসানুল আরাব ’ গ্রন্থের জবাবে লেখা হয়েছে। ”
মাসউদী আরব মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যখন দেখলেন ইরানীদের বিরুদ্ধে ও আরবদের পক্ষে অন্যায় প্রচার হচ্ছে তখন তিনি ইরানীদের সপক্ষে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও ইসলামের অন্যতম আশ্চর্য ও সৌন্দর্য।
আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ;এর পক্ষে-বিপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলনটি স্তিমিত হওয়ার কারণ নিয়ে পূর্ণ বিশ্লেষণ নয়। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য হলো এটি বলা যে ,শুয়ূবীয়া আন্দোলন আরবদের জাতি বৈষম্যভিত্তিক নীতির বিরুদ্ধে ইরানীদের ইসলামী চেতনার এক পবিত্র প্রতিক্রিয়া ছিল যা পরবর্তী সময়ে ইরানীদের ক্ষুদ্র একটি অংশের দ্বারা বিচ্যুত হয়ে জাতীয় গোঁড়ামি ও জাতীয়তাবাদের রং ধারণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী জিন্দিক চিন্তায় পর্যবসিত হয়। এ ধারা ইরানের পরহেযগার আলেম ও সর্বসাধারণের দ্বারা নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা এক হাজার বছর পূর্বেই এই ধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। যদিও বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এক হাজার বছর পর এ চিন্তাকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টায় রত কিন্তু কখনই তারা সফল হবে না।
তৃতীয় যে ইসলামবিরোধী ধারার বিরুদ্ধে ইরানীরা অন্য সকলের চেয়ে অধিক প্রতিক্রিয়া দেখায় তা হলো গান-বাজনা ,আনন্দ-ফুর্তি ও বিলাসিতা।
ইরানের সংগীত ও গানের ইতিহাস বেশ পুরোনো। এ দেশের মানুষের জীবন এর সঙ্গে জড়িত ছিল। মশিরুদ্দৌলা তাঁর ‘ ইরানের ইতিহাস ’ গ্রন্থের 201 পৃষ্ঠায় বলেছেন , “ বাহরাম গুর ভারত হতে বারো হাজার সংগীত শিল্পী এনেছিলেন। ”
‘ ফাজরুল ইসলাম ’ গ্রন্থে হামযা ইসফাহানীর ইতিহাস গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ,
‘ বাহরাম জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেন অর্ধেক দিবস কাজ করার ও অর্ধেক দিবস
গান-বাজনা ও আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকার। এই অর্ধেক দিবস যেন তারা মদ্যপান ও গান বাজনা করে। এর ফলে সংগীত শিল্পীদের কদর বেড়ে যায়। একদিন কিছু লোককে শুধুই মদ্যপানে রত দেখে প্রশ্ন করা হলো শুধুই পান করছ ,শুনছ না কেন ? সংগীত শিল্পী কোথায় ? তারা বলল ,তাদের মজুরী বেড়ে যাওয়ায় পাওয়া যায়নি ? বাহরাম ভারতের রাজাকে পত্র লিখে সংগীত শিল্পী পাঠাতে বলেন। তিনি বার হাজার সংগীত শিল্পী প্রেরণ করেন। বাহরাম তাদেরকে ইরানের বিভিন্ন শহরে বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।
আরবগণ গান-বাজনার ক্ষেত্রে সাদাসিধে ছিল। কিন্তু ইরানীদের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্যেও গান-বাজনা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে গান-বাজনার কেন্দ্র ইরাক ও সিরিয়া হতেও তারা এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হেজায হাদীস ও ফিকাহর ক্ষেত্রে যেমন ঠিক তেমনি সংগীত ও গানের ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উমাইয়্যা শাসকগণ ও তাদের প্রদেশিক শাসনকর্তারা এগুলোর প্রচারে ব্যাপক উদ্যোগ নেয় ও নিজেরাও এতে নিমজ্জিত হয়। এর বিরুদ্ধে নবীর আহলে বাইতের ইমামগণ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান যা শিয়া ফিকাহ্ ও হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।
ইমামগণের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ পর্যায়ের মানুষের মধ্যে দেখলে বিষয়টি ইরানী মুসলমান ও আলেমগণের দ্বারাও ব্যাপকভাবে আক্রমণের শিকার হয় ,এমনকি আবরদের চেয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া অনেক তীব্র ছিল যদিও এ বিষয়ে তাদের পূর্ব-ঐতিহ্য ছিল।
আহমাদ আমিন উল্লেখ করেছেন ,হেজায যেমন ফিকাহ্ ও হাদীসের কেন্দ্র ছিল তেমনি গান ও সংগীতেরও। কিন্তু কিভাবে ফিকাহ্ ও হাদীসের কেন্দ্র গান-বাজনার কেন্দ্র হতে পারে ? সম্ভবত এর কারণ হেজাযের অধিবাসীদের সুন্দর প্রকৃতি ও নরম হৃদয় ,এমনকি হেজাযের সুন্নী ফকীহ্গণ এ সকল বিষয়ে ইরাকের ফকীহ্দের চেয়ে কম কঠোর ছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ,ইরাকে এরূপ বিষয়ে কঠোরতার মূলে ছিলেন ইরানী ফকীহ্গণ। তাঁরা দীনের সীমার বিষয়ে অধিকতর স্পর্শকাতর ছিলেন। অতঃপর তিনি আবুল ফারজ ইসফাহানী হতে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন :
‘ উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর আমরী বলেন: হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছিলাম। একজন সুন্দর নারীকে ইসলামের নির্দেশের বিপরীতে সেখানে কৌতুকময় ও অশ্লীল কথা বলতে দেখলাম ,আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম: হে আল্লাহর দাসী! তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে ,হজ্বে এসেছ ? তোমার আল্লাহর ভয় নেই ,ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অশ্লীল কথা বলছ ? এ কথা শুনে সে তার নেকাব উন্মুক্ত করে অদ্ভুত সুন্দর চেহারাটি দেখিয়ে বলল: চাচাজান! দেখুন আমি এই কবিতার নারী:
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة |
و لكن ليقتلن البرئ المغفّلا |
“ ঐ নারীর অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহর জন্য হজ্ব করতে আসেনি ;বরং অসচেতন ও বোকাদের হত্যা করার (ফাঁদে ফেলার) জন্য এসেছে। ”
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব-এর বংশের এই মনীষী ও সাধক বলেন , “ আমি এই সফরে দোয়া করব যেন আল্লাহ্ তোমার এত সুন্দর চেহারাকে আজাব না দেন। ”
এ ঘটনাটি মদীনার বিশিষ্ট ফকীহ্ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে বললে তিনি বলেন , “ আল্লাহর কসম! এই নারী ইরাকের কোন ফকীহর মুখোমুখি হলে এরূপ জবাব দিতেন না ;বরং বলতেন: দূর হও! আল্লাহ্ তোমার চেহারাকে কুৎসিত করে দিন! কিন্তু কি করার রয়েছে হেজাযের মানুষের আচরণ মোলায়েম। ”
তিনি আগানী হতে বর্ণনা করেছেন ,
‘ মদীনার অন্যতম ফকীহ্ ইবনে জারীহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারাকসহ ইরাকের কিছু ফকীহর সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন সংগীত শিল্পী আসলে ইবনে জারীহ্ তাকে সংগীত পরিবেশনে অনুরোধ জানালেন। সে রাজী হচ্ছিল না । কিন্তু জারীর নাছোড়বান্দা হওয়ায় সে কিছক্ষণ গান গাইল ,কিন্তু বুঝতে পারল শ্রোতারা তা পছন্দ করছে না। তাই সংক্ষিপ্ত করে বলল: যদি এই সম্মানিত ব্যক্তিরা না থাকতেন তবে আপনাকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতাম। ইবনে জারীহ্ উপবিষ্টদের উদ্দেশে বললেন: আপনারা বোধ হয় আমার এ কর্মকে খারাপ ভেবেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক যিনি একজন ইরানী বংশোদ্ভূত কুফার ফকীহ্ ছিলেন তিনি বললেন: হ্যাঁ ,ইরাকে আমরা এসবের বিরোধী...। ’
যে বিষয়টি আশ্চর্যের তা হলো প্রথমত ইরানীদের সংগীত শিল্পে প্রসিদ্ধ হিসেবে দীর্ঘ ইতিহাস ছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হওয়া উচিত ,তারা এ বিষয়কে শরীয়তসম্মত ভেবে বৈধ ব্যাখ্যা করার সুযোগ খুঁজবে ,কিন্তু তার বিপরীতে দেখা গেছে তারা এ বিষয় হতে দূরে থাকত ও এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। দ্বিতীয়ত হেজাযে সংগীতের প্রসারে প্রথমদিকে ইরানীরাই অধিক ভূমিকা রেখেছিল এবং তৎকালীন সময়ের সংগীত শিল্পীদের অধিকাংশই ইরানী ছিল। এইরূপ পরিবেশেও ইরানী ফকীহ্ ও সাধারণ জনগণ বিষয়টিকে কোমলভাবে নেয় নি ;বরং কঠোরতা দেখিয়েছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ,এ ধর্মীয় অবস্থাটি সাধারণের মাঝে বিরাজমান থাকলেও ধর্মহীন পরিবেশে ,যেমন আব্বাসীয়দের বা বার্মাকীদের রাজদরবারের অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ।
ইসলামের প্রচার ও প্রসার
বিশ্বে ইসলামের প্রচারের কারণ ও পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্পষ্ট যে ,এ ধর্ম যুক্তিভিত্তিক ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বিধায় দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে।
খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহকে ইসলামের প্রসারের প্রধান কারণ দেখিয়ে এ ধর্মকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রসারিত ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। যদি কোন ধর্ম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেককে সন্তুষ্ট করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা না রাখে তবে শক্তি প্রয়োগে মানুষের মধ্যে ঈমান ,ভালবাসা ,উদ্দীপনা ও ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে না। হ্যাঁ ,ইসলামের প্রাথমিক সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং তা এজন্য যে ,ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম হিসেবে শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাফল্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি এবং ব্যক্তিগত সাফল্য ও সামাজিক সাফল্যের মধ্যে পার্থক্যকে স্বীকার করে না। তাই ইসলামে ‘ সম্রাটকে তার অধিকার ও কর্মে স্বাধীনতা দাও এবং আল্লাহর অধিকার আল্লাহ্কে দাও ’ এ মৌলনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই ইসলাম জিহাদকে দীনের অংশ বলে মনে করে ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করে। অবশ্য দেখতে হবে ইসলামের জিহাদের উদ্দেশ্যে কি এবং প্রথম যুগের মুসলমানগণ কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ? সেই যুদ্ধগুলোতে কোন শ্রেণীর শক্তি ব্যবহার করেছে ও কোন শ্রেণীকে মুক্তি দিয়েছে ?
এসব বাদ দিলেও দেখতে হবে ইসলামের যোদ্ধারা কোন্ কোন্ অঞ্চলে গিয়েছেন ? বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত কোন্ কোন্ দেশে যুদ্ধ ও জিহাদ সংঘটিত হয়নি ? মুসলিমপ্রধান দেশসমূহ এবং যে সব অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেগুলোর কোন্ কোন্টিতে মুজাহিদদের পদধূলি পড়েনি ?
প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসার স্বাভাবিক গতিতেই হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বর্ণনা করেছি ইরানে ইসলাম পর্যায়ক্রমে বিশেষত আরব শাসনের অবসানের পর ইরানীদের দ্বারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে গৃহীত হয় এবং ইরানীদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভের পরই যারথুষ্ট্র ধর্মের অবধারিত মৃত্যু হয় এবং ইতোপূর্বে কোন শক্তিই তাদের পূর্বধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করতে পারেনি।
দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলাম ইরানে ব্যাপকভাবে প্রসারমান খ্রিষ্ট ,মাজুসী ও অন্যান্য ধর্ম হতে যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল তার কারণ হলো এ ধর্মের প্রচারক ছিল সাধারণ মানুষ ;কোন ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় প্রচার দফতর নয়। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিবেকের তাড়নায় উদ্দীপিত হয়ে এ ধর্মের প্রচার কার্য চালাত। কোন আলেম শ্রেণী বা অন্য কেউ তাদের উদ্দীপিত করেনি। এ বিষয়টিই এ ধর্মের প্রচারে ভিন্ন এক মূল্যবোধ দান করেছিল ও ইসলামকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছিল।
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে একে একে পর্যালোচনা করে দেখব যে ,এ সব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পশ্চাতে কি উপাদান কার্যকর ছিল। কারণ প্রথমোক্ত এ বিষয়টি এ গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। দ্বিতীয়ত এর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আমরা এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইরানীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব যাতে বিশ্বে ইসলাম প্রচারের পদ্ধতিটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে।
বর্তমানে পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা নব্বই কোটি (1979 সালের হিসাব অনুযায়ী)। ইরানের বর্তমান লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। বর্তমানের এই তিন বা সাড়ে তিন কোটি মানুষই মুসলিম বিশ্বের অর্ধেক মানুষের মুসলমান হওয়ার পেছনে অবদান রেখেছে। অর্থাৎ ইরানীদের আহ্বান ও প্রচারের ফলেই জাতিসমূহের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক পরিচয় ও ভিত্তি রচিত হয়েছিল।
মুসলিম বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইন্দোনেশিয়া ,ভারত ,পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাস করে। কিভাবে এই দেশগুলোর মানুষ মুসলমান হয়েছিল ? ইরানীরা তাদের ইসলাম গ্রহণে কি ভূমিকা রেখেছিল ? প্রথমে ইন্দোনেশিয়া দিয়ে শুরু করছি।
‘ রাস্তোখিযে ইন্দোনেযি ’ 220 নামক গ্রন্থের ‘ ইন্দোনেশিয়ায় ধর্ম ’ নামক অধ্যায়ে বলা হয়েছে :
“ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার যেভাবে ঘটেছিল ,ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামও একইভাবে প্রবেশ করেছিল। অবশ্য এটি ঘটেছিল দু ’ জন ইরানী বংশোদ্ভূত আরব ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। যাঁরা হলেন আবদুল্লাহ্ আরিফ ও তাঁর ছাত্র বুরহান উদ্দীন। তাঁরা উভয়েই ভারতের গুজরাটে বসবাস করতেন এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত করতেন। তাঁরাই সেখানে ইসলামের মহান শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার করেন। ”
একই গ্রন্থের ঐ আলোচনায় বলা হয়েছে :
‘ সুমাত্রায় মুসলমানদের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রভাব জাভা ও কালিমানতানেও পড়ে এবং এ বিষয়টি মুসলমান ও রাজকীয় বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা মুচু পহিতের পতনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই শতাব্দী (চতুর্দশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দী) হতে একশ ’ বছর ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়।221 এই প্রচার কার্য ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা ভালবাসা ,আমানতদারী ,ন্যায়পরায়ণতা ,ভ্রাতৃত্ব ,সাম্য ও অন্যান্য উন্নত গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলো ইন্দোনেশিয়ার মানুষের কাছে আকাক্সিক্ষত বিষয় ছিল ও তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ সাতশ ’ বছর (700-1400 খ্রিষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণের পর তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল।... ইসলামের অগ্রগতির সাথে সাথে ব্রা হ্ম ধর্ম ও এর সংস্কৃতিও জাভা হতে দূরে সরে দূরবর্তী গ্রাম ও পাহাড়াঞ্চলে চলে যায়। এ সময় বৌদ্ধ ,শিবায়ী ও স্থানীয় অন্যান্য ধর্ম পরস্পর সমন্বিত হয়ে প্রচেষ্টা চালায় ,কিন্তু ইসলাম ক্রমবর্ধমানভাবে প্রসারিত হতে থাকে ও অন্যান্য ধর্মকে প্রভাবিত করে ফেলে। ’
উক্ত গ্রন্থে ডক্টর সুকর্ণের বক্তব্য হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে : ‘
“ মর্যাদা ,সততা ,সাম্য ও যথার্থতা হলো তা-ই যা ইসলাম ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের জন্য উপহার হিসেবে এনেছিল। ”
‘ ইসলাম: সিরাতে মুস্তাকিম ’ 222 নামক গ্রন্থে ‘ বি.এ. হুসাইন জাজা ওয়ানিনগারাত ’ 223 তাঁর ‘ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন , “ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে প্রাচীনতম যে তথ্য পাওয়া যায় তা বিশ্বখ্যাত পর্যটক মার্কপোলোর ভ্রমণকাহিনী হতে। তিনি দীর্ঘ সময় চীনের সম্রাট কুবলাই কানের (মৃত্যু 789 হিজরী) রাজদরবারে থাকার পর 692 হিজরীতে সুমাত্রার উত্তর তীরের পারলাকে যাত্রাবিরতি করেন ও এতদঞ্চলে আরব সওদাগরদের ধর্মীয় প্রচারের ফলে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করেন...। ’ মরক্কোর প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে বতুতা (মৃ. 779 হি.) 746 হিজরীতে চীনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে সুমাত্রায় আসেন। সে সময় বাদশাহ সালিহের প্রপৌত্র বাদশাহ জহির সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। ইবনে বতুতা বলেন , ‘ তখন সেখানে ইসলামী শাসনের একশ ’ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। অধিকাংশ মানুষ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিল। বাদশার বদান্যতা ,ধর্মপরায়ণতা ও দুনিয়াবিমুখ জীবন সকলকে আকর্ষণ করত। ” তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। বাদশাহ জহির আলেম ও কালামশাস্ত্রবিদদের নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত ও দীনী আলোচনার সভা বসাতেন। তিনি হেঁটে জুমআর নামাজে যেতেন এবং মাঝে মাঝেই দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহী অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন।
উক্ত প্রবন্ধে তিনি নয়জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। তাঁদের একজন হলেন সেসিতি জানার যিনি মনসুর হাল্লাজের ন্যায় সুফীবাদে বিশ্বাস রাখতেন ও অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন ,
‘ যদিও সেসিতির আকীদা ইরানী মনসুর হাল্লাজের আকীদার ন্যায় ছিল তদুপরি এটি জাভায় ইসলাম ইরানীদের মাধ্যমে গিয়েছিল বলে প্রমাণ করে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ,যে ইসলাম জাভায় প্রচলিত তা ইরান হতে পশ্চিম ভারতে ও পরবর্তীতে সুমাত্রা হয়ে জাভায় পৌঁছায়। ’ উপরোক্ত বিষয়টি প্রমাণের জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। শিয়ারা দশই মুহররম হুসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর শাহাদাত উপলক্ষে শোকানুষ্ঠান পালন করে। এই দিন ইন্দোনেশিয়ায় বিশেষ একটি খাদ্য তৈরি করা হয় যার নাম ‘ বুবুদসুরা ’ । সম্ভবত এটি ইরানীদের ‘ দাহুমে মাহে মুহররম ’ শব্দের প্রতিশব্দ। জাভাতেও মুহররমকে ‘ সুরা ’ বলা হয়। সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলের ‘ আতজাহ ’ তে শিয়াদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। ঐ অঞ্চলে মুহররম মাসকে ‘ মাহে হাসান-হুসাইন ’ বলা হয়।
ইরানীদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রভাব প্রমাণের জন্য আরেকটি বিষয় হলো সঠিকভাবে কোরআন শিক্ষাদানের জন্য আরবী পরিভাষা ব্যবহার না করে ইরানী পরিভাষায় আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। অধ্যয়নের মাধ্যমে এরূপ অন্যান্য প্রমাণও হাতে পাওয়া যাবে। ’
ইন্দোনেশিয়ার সুরাবাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রফেসর ইসমাইল ইয়াকুবের সঙ্গে ফার্সী 1349 সালের (1971 খ্রি.) ফারভারদিন (মার্চ) মাসে অনুষ্ঠিত শেখ তুসীর সহস্র বর্ষ পালন অনুষ্ঠানে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি ঐ সেমিনারে ‘ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ: ইরানী মনীষীদের অবদান ও বিশ্বের জ্ঞানগত উত্তরাধিকার ’ শিরোনামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে বলেন , “ নবীজীর হাদীসে যে পারস্যের কথা আছে ,বর্তমানে তা ইরান নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের নিকট এটি প্রসিদ্ধ। কারণ আমরা জানি ইসলাম ধর্ম যে বিদেশী প্রচারকদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল ইরানীরা তাদের অন্যতম। ইরানী ধর্ম প্রচারকগণ ইন্দোনেশিয়ায় হিজরত করে এর সমগ্র ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচার করেন। এর ফলেই আজ ইন্দোনেশিয়ার এগারো কোটি মানুষের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা নব্বই ভাগ। ”
ভারত ও পাকিস্তানেও ইসলামের প্রচার-প্রসারে ইরানীদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এ বিষয়ে আজিজুল্লাহ্ আত্তারাদীর ‘ ইরানীদের ইসলামী কর্মকাণ্ড ’ শীর্ষক প্রবন্ধ হতে আমরা উল্লেখ করেছি। সেখান হতে ভারত ও পাকিস্তানে ইসলামের প্রচারে ইরানীদের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে জানা যাবে। ভারত ও পাকিস্তানে ইরানী ও অ-ইরানী বিভিন্ন সুফীর মাধ্যমে ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে।
পাকিস্তানের সিন্ধের হায়দারাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী ‘ ভারত ও পাকিস্তানে ইসলামী সংস্কৃতি ’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ,
“ আরবগণ ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত। নবী (সা.)-এর অবির্ভাবের পর তাদের বাণিজ্য অব্যাহত থাকে ,কিন্তু তখন ব্যবসায়ের সঙ্গে ইসলামের প্রচারও যুক্ত হয়। পঞ্চাশ হিজরী হতে প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষলগ্ন পর্যন্ত ভারতবর্ষে ধর্মীয় উত্তেজনা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগকে নওমুসলিম আরবরা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ভারতবর্ষে হিজরত করে এবং মালাবার তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইসলাম ধর্মের সহজ সাবলীলতা ও স্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ হিন্দুদের মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ প্রথম পঁচিশ বছরেই তাদের (মালাবার অঞ্চলের) অনেকেই ,এমনকি মালাবারের সুলতানও এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন । যদিও আরবগণ ভারতবর্ষে সমুদ্রপথেই বাণিজ্য করত ,কিন্তু ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে ইরান ও মধ্য এশিয়া হতে স্থলপথেই অধিকতর প্রসার লাভ করে। ”
তিনি আরো বর্ণনা করেছেন ,
“ ধর্মীয় আলেমদের চেয়ে সুফীরা অধিকতর প্রিয় ছিলেন। কারণ তাঁরা রাজনীতি হতে দূরে থাকতেন ,যদিও কখনও কখনও সুলতান ও বাদশাদের কিছু কাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াতেন। দিল্লীর শাসনকর্তারা প্রায় সকলেই এই সুফী বা পীরদের মুরীদ অথবা ভক্ত ছিলেন। সালার মাসউদ গাজী ও শেখ ইসমাঈল নামের দু ’ জন প্রসিদ্ধ সুফী-সাধক পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তখন সেখানে হিন্দু শাসন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কয়েক সহস্র হিন্দুকে মুসলমান করতে সক্ষম হন। অন্যতম প্রসিদ্ধ সুফী খাজা মুঈনউদ্দীন যিনি সামারকান্দে জন্মগ্রহণ করেন ;তিনি ঘুরী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে চিশতীয়া তরীকার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই তরীকা ভারত ও পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ সুফী তরীকা।
ভারতের আজমীরে তাঁর মাজারটি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের যিয়ারতে মুখরিত হয়। চিশতিয়া তরীকার কিছু দিন পর ভারতে সোহরাওয়ার্দী তরীকার জন্ম হয়। এই তরীকার ধর্মীয় নির্দেশের অনেক বিষয়েই চিশতীয়া তরীকার সঙ্গে পার্থক্য ছিল। কারণ সোহরাওয়ার্দী চিশতীয়া ও অন্যান্য তরীকায় প্রচলিত বিশেষ ধরনের সামা ও রাকসের (নাচ-গান) বিরোধী ছিলেন। মোগলদের ভারত আগমনের পূর্বে আরো দু ’ টি তরীকা যথাক্রমে কাদেরিয়া ও নাকশেবন্দিয়া ভারতবর্ষে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। ”
এই সুফিগণের অধিকাংশই ইরানী ছিলেন। মুঈনউদ্দীন চিশতী নামক যে ইরানী সুফী-সাধক ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তাঁর সম্পর্কে আজিজুল্লাহ্ আত্তারাদী এ গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে যে গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন তা হতে হুবহু এখানে তুলে ধরছি। তিনি এই প্রবন্ধে অপর এক ইরানী সুফী-সাধক নিজামউদ্দীন আউলিয়া যিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হিসেবে ভারতবর্ষে ছিলেন তাঁর সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা তাঁর বর্ণনাটি নিম্নে তুলে ধরছি :
“ খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী হারভী ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে সিস্তানে224 জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি জ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে হেরাতের225 চাশতে হিজরত করে সাধানায় লিপ্ত হন এবং চিশতী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি চাশত হতে তুসে যান এবং তুসের তাবেরানে খোরাসানের প্রসিদ্ধ সুফী খাজা উসমান হারুনীর খানকায় ওঠেন। চিশতী খাজা উসমানের নিকট আধ্যাত্মিক চর্চার পূর্ণতার প্রশিক্ষণ নেন এবং খাজা উসমানের বিশেষ প্রতিনিধি বা খলীফার পদ লাভ করেন।
খাজা মুঈনউদ্দীন অতঃপর বাগদাদে যান। বাগদাদ তখন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। সেখানেও তিনি বিশিষ্ট সুফীদের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং কিছুদিন সেখানে ধর্মীয় পাঠদানও করেন। অনেকেই তাঁর নিকট আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন মক্কা ,মদীনা ,মিশর ও সিরিয়ায় ভ্রমণ করেন এবং ঐ স্থানসমূহের অনেকেই তাঁর নিকট হতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাগ্রহণ করেন।
সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে হেরাতের পূর্বাঞ্চলের পর্বতময় ফিরুযকুহ অঞ্চলের শাসক মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে অভিযান চালান। তিনি লাহোরের গজনভী শাসকদের পতন ঘটিয়ে পাঞ্জাব অধিকার করেন ও দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন এবং কিছু দিনের মধ্যে দিল্লী তাঁর অধীনে চলে আসে। তিনি দিল্লীকে রাজধানী ঘোষণা করেন। ঘুর বংশ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আলেম ও মুসলিম মনীষী পাঞ্জাব ও রাজস্তানে হিজরত করে দীনী প্রচার কাজ শুরু করেন। খাজা মুঈনউদ্দীনও ঘুরী বংশের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ভারতে হিজরত করে
রাজস্তানের আজমীরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি আজমীরে মসজিদ ও দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামের মৌলনীতি ও বিধিবিধান শিক্ষাদান শুরু করেন।
তিনি ভারতীয়দের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও উপযোগী তাসাউফ (সুফী) চিন্তার আলোকে ইসলাম শিক্ষাদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ফলে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল অঞ্চল হতে মানুষ দলে দলে তাঁর পাশে ভীড় জমাতে শুরু করল ও তাঁর নিকট হতে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে লাগল।
ভারতের মুসলিম শাসকরা তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতেন। ফলে সবদিক হতেই তিনি সহযোগিতা পেতে শুরু করলেন। তাঁর শিক্ষায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদের পথে পা বাড়াল। তাঁর প্রচারেই উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ইসলাম প্রসার লাভ করে। তিনি প্রচুর মুরীদ তৈরি করেন। তাঁর প্রশিক্ষিত অনেক ছাত্রই ভারতে ইসলাম প্রচারে মূল্যবান অবদান রাখেন। ফরিদউদ্দীন গাঞ্জে শেকার এবং কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী তাঁর স্বনামধন্য দু ’ ছাত্র যাঁরা ইসলামের প্রাণবন্ত উৎসে পরিণত হয়েছিলেন।
খাজা মুঈনউদ্দীন তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে আজমীরেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানগণ তাঁর কবরের ওপর জাঁকজমকপূর্ণ যে গম্ভুজ তৈরি করে তা আট শতাব্দী পরও বিদ্যমান। তাঁর মাযার ভারতীয় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ যিয়ারতের স্থান। নাসিরুদ্দীন খিলজী থেকে হায়দারাবাদের নিজামগণ সকলেই এ মাযারে স্মরণীয় হিসেবে কিছু রেখেছেন। তাঁর মাযারে ও কবরের দেয়াল ও বিভিন্ন স্থানে তৎকালীন ভারতের রাজকীয় ভাষা হিসেবে প্রচুর ফার্সী কবিতা লিখিত রয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের জন্য তার একটি এখানে তুলে ধরছি :
“ খাজাগণের নেতা মুঈনউদ্দীন
অলিকুলের শিরোমণি শ্রেষ্ঠ পীর।
তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য বর্ণনাহীন
তিনি ছিলেন দীনের সুরক্ষিত দুর্গ শির
তাঁর গুণের প্রশংসায় বলছি দু ’ টি ছত্র
তাঁর কথা ছিল যেন মূল্যবান রত্ন।
ওহে! যার গৃহ ছিল বিশ্বাসীদের কেবলা
ওহে! যার পদে ঠেকাত ললাট চন্দ্র ,সূর্য
লক্ষ কোটি বাদশার যেথায় আনাগোনা সর্বদা
চীনের বাদশাও তাঁর নিকট করেন নত মাথা
তোমার সেবকেরা সকলে জান্নাত অধিবাসী
তোমার বেহেশেতের বাগানে হয়েছে তারা চিরস্থায়ী
তোমার সমাধির মাটির সুবাস প্রাণহারা
সেথা হতে বয়ে চলেছে সুপেয় পানির ঝরনা-ধারা। ”
ভারতের তৈমুর বংশের শাসকগণ (মোগলগণ) খাজা মুঈনউদ্দীনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ পোষণ করতেন। সম্রাট জালাল উদ্দীন আকবর তাঁর রাজধানী আগ্রা হতে একবার পায়ে হেঁটে আজমীরে মুঈনউদ্দীন চিশতীর মাজার যিয়ারত করেন। ভারতবর্ষের শিয়া-সুন্নী সকল মুসলমানই তাঁর প্রতি অনুরক্ত। প্রতি বছর এই মহান সুফীর স্মরণে রজব মাসে বৃহৎ সভার আয়োজন করা হয় এবং সমগ্র ভারত হতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজমীরে ভীড় জমায়। তারা ইসলামের সেবায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে। ‘ তাযকিরাহ ’ সমূহে তাঁর জীবনী ও কর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।
নিযামউদ্দীন আউলিয়া
মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ নিযামউদ্দীন আউলিয়া ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন্মভূমি বোখারা হতে ভারতবর্ষে হিজরত করেছিলেন। কিছুদিন তিনি লাহোরে বসবাসের পর বাদাউনে যান ও বসতি স্থাপন করেন। নিযামউদ্দীন সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে মাতাই তাঁকে লালন-পালন করেন। তাঁর মাতা একজন আল্লাহ্প্রেমিক তাকওয়াসম্পন্না পবিত্র মহিলা ছিলেন। তিনি সন্তানকে প্রতিপালনে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। নিযামউদ্দীন বাদাউনেই তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন। অতঃপর মাতার সঙ্গে দিল্লী যান। সেখানে শামসুদ্দীন দামগানী ,আলাউদ্দীন উসূলী এবং ফরিদউদ্দীন মাসউদ গাঞ্জে শেকারের নিকট শিক্ষা জীবনের পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি ফরিদউদ্দীন মাসউদের খলীফা ও প্রতিনিধিত্বের সৌভাগ্য লাভ করেন।
নিযামউদ্দীন প্রথম দিকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করলেও কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিম শাসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর শরণাপন্ন হতে শুরু করলেন। সম্রাট জালালউদ্দীন খিলজী তাঁর সাক্ষাৎ লাভে উদগ্রীব ছিলেন। সে সময়ের প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরু দেহলভী সামারকান্দী তাঁর মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন ।
নিযামউদ্দীন ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে অনেক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর ছাত্ররা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দীনী প্রচার চালান। তাঁর অন্যতম ছাত্র খাজা নাসিরুদ্দীন পাঞ্জাব ,গুজরাট ও অন্ধপ্রদেশে দীনী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক ও ম্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর অপর ছাত্র সিরাজুদ্দীন বাংলা ,বিহার ও আসামে দীনী প্রচার কার্য চালান। তাঁর অন্যতম ছাত্র বুরহানউদ্দীন দক্ষিণাত্য ও মধ্য প্রদেশে ইসলাম প্রচার করেন। মোটামুটি বলা যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রসার তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ,তাঁর ছাত্র ও প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিল। তিনি 725 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার দিল্লীতেই এবং প্রতি বছর তাঁর স্মরণে সেখানে ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র মুসলমান তাঁর মাযারে সমবেত হয়ে তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য শুনেন।
খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী ও নিযামউদ্দীন আউলিয়ার জীবনী ঐতিহাসিক ফিরিশতা ও শাহ আসতারাবাদীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।226
ইরানের মুসলমানগণ ভারতে ইসলাম প্রচারে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইরানে ইসলামের আবির্ভাবের সময়কালের ঠিক বিপরীত অবস্থা তখন ভারতে সৃষ্টি হয়। কারণ আমরা দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় উল্লেখ করেছি ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ভারতের উত্তর দিকে প্রসারমান ছিল এবং ইরানের পূর্বাংশেও প্রভাব বিস্তার শুরু করে। যদি ইসলামের আবির্ভাব না ঘটত তাহলে ভারত হতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম ইরানে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর ধমনীতে সজীব রক্ত প্রবাহের ফলে ইরানীরা নতুন জীবন লাভ করে ,পরিস্থিতি পাল্টে যায় ;ইরান তখন ভারতবর্ষকে নিজ ধর্মে প্রভাবিত করতে শুরু করে ও বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত হতে বিতাড়িত করে।
ইসলামই ফার্সীকে ভারতবর্ষে নিয়ে যায়। তাই এই ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলন লাভের জন্য ইসলামের নিকট ঋণী। ভারতের ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময় এ ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচলিত হওয়ার সময় হতেই এই ভাষা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী ভাষা ছিল।
এ শতাব্দীতে পাকিস্তানী কবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের ন্যায় অনেকেই ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষাকে শক্তিশালী করেছেন। যে সকল ইরানী জাতীয়তাবাদের মিথ্যা অথবা সত্য দাবিতে ইসলামকে বাদ দিয়ে ফার্সী ভাষাকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রচার করতে চাইছেন তাঁরা এক অসম্ভব চিন্তা করছেন। তাঁরা কখনই সফল হতে পারবেন না।
চীনে ইসলামের প্রবেশ ও বিস্তার
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান মতে চীনে বর্তমানে পাঁচ কোটি মুসলমান বাস করেন। চীনে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার একদল মুসলমান-যাঁরা সেখানে হিজরত ও বসতি স্থাপন করেছিলেন ,তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। চীনে ইসলামের প্রচারে ইরানী মুসলমানদের ভূমিকা বেশ ব্যাপক ছিল।
‘ সিরাতে মুস্তাকিম ’ নামক গ্রন্থে ‘ চীনে ইসলামী সংস্কৃতি ’ 227 শিরোনামের এক প্রবন্ধে চীনে ইসলামের প্রবেশ ,উন্নয়ন ও ক্রমাবনতির যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইরানীদের ভূমিকা এ প্রবন্ধে লক্ষণীয়।
তিনি চীনে ইসলামের প্রবেশের এক নাতিদীর্ঘ ইতিহাস চীনের বিভিন্ন গ্রন্থসূত্র ও উৎস হতে উল্লেখ করেছেন। কোন ইসলামী উৎসে তা উল্লিখিত হয়নি বলে তিনি বলেছেন। তিনি বলেন ,
“ তাং বংশের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে সম্রাট ইয়াংভির শাসনামলের দ্বিতীয় বর্ষে (31 হিজরীতে) মদীনা হতে দূত তাঁর দরবারে কিছু উপঢৌকন ও উপহার নিয়ে আসেন। দূত বর্ণনা করেন যে ,একত্রিশ বছর হলো তাঁদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... সম্রাট দূতকে কিছু প্রশ্ন করার পর ইসলাম সম্পর্কে যা শুনতে পান তাতে একে কনফুসিয়াসের শিক্ষার অনুরূপ বলে বুঝতে পারেন। তিনি ইসলামকে সত্যায়ন করেন ,কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও বছরে এক মাস রোযার বিষয়টি পালন কষ্টকর মনে করেন। তাই তা পালনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি মদীনা হতে আগত দূত সা ’ দ228 ও তাঁর সঙ্গীদের চীনে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন এবং ‘ চানগান শহর ’ -এ সর্বপ্রথম মসজিদ স্থাপনে নিজ সম্মতি ঘোষণা করেন । এভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন করেন। এই মসজিদটি ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম যা এখনও পুনঃপুন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে। ’ 229
যদি উপরোক্ত ঘটনা সত্য হয় তবে ইসলাম আরব মুসলমানদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম চীনে প্রবেশ করে । এ ঘটনা ছাড়াও চীনে মুসলমান বণিকগণ যাঁদের অনেকেই ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন তাঁরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
একই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ,
“ বনি উমাইয়্যা ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বনি উমাইয়্যার শাসনামলে অনেক আরব বণিকই চীনে গিয়েছিলেন যাঁদের ‘ আরব শুভ্র পোশাকধারী ’ বলা হতো। আব্বাসীয়দের খেলাফতকালে মুসলিম ও চীন সম্রাজ্যের মধ্যে অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে প্রচুর আরব বণিক সেখানে যান। তাঁরা ‘ কৃষ্ণ পোশাকধারী ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
...একশত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (31 হতে 184 হিজরী পর্যন্ত) প্রচুর সংখ্যক আরব ও ইরানী বণিক চীনে পৌঁছে এবং চীনের কুয়াংচু বন্দরে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে যায় ও ধীরে ধীরে উত্তর চীনের হাংচু শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে... ইতোমধ্যে দক্ষিণ চীনে মুসলিম বণিকদের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। তাদের অনেকেই চীনাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এই মুসলামানদের ভিন্ন সমাজ ছিল। তারা অন্য ধর্মাবলম্বী চীনাদের হতে স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের প্রাত্যহিক ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন শুরু করে ,এমনকি বিবাহ ,তালাক ,উত্তরাধিকার ও অন্যান্য ইসলামী বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ছিল। এটি তৎকালীন সময়ে মুসলিম সমাজের প্রভাব ও আধিপত্যের একটি প্রমাণ। ”
তিনি আরো বলেন ,
“ ইরানী ও আরব ব্যবসায়ীরা চীন হতে রেশমী বস্ত্র ,চীনামাটির পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত। আবার ঐ সকল অঞ্চল হতে মশলাদ্রব্য ,উদ্ভিজ্জ চিকিৎসা উপকরণ ,মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর ও সামগ্রী চীনে নিয়ে আসত। এ বণিকরা এই লাভজনক ব্যবসায়ের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম বণিকদেরও চীনে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। ফলে মুসলিম বণিকদের নতুন নতুন দল চীনে প্রবেশ করে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও ধর্মীয় প্রচারও বৃদ্ধি পায়। ” 230
ঐ গ্রন্থে আরো উল্লিখিত হয়েছে :
“ চীনের উত্তরাঞ্চলে অধিকাংশ ভারবাহী পশু (বাণিজ্য কাফেলার জন্য ব্যবহৃত) ,যেমন উট ,ঘোড়া ও গাধা মুসলমানদের অধিকারেই ছিল। এ ছাড়াও ইয়াংতিসি ও হাওয়াইহু231 নদী ও এদের শাখা-প্রশাখার তীরবর্তী অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হতো তা বেচাকেনা ও বহন ,মেষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় সবই মুসলমানদের দ্বারা সম্পন্ন হতো। এখনও বিভিন্ন প্রাণীর বেচাকেনায় ফার্সী পরিভাষার ব্যবহার তৎকালীন সময়ে এতদঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাবের বিষয়টিকে প্রমাণ করে। ” 232
তিনি অন্যত্র বলেছেন ,
“ চীনের মুসলমানগণ দু ’ ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল হলো সিকিয়াং-এর মুসলমানগণ যাদের পাগড়ীধারী মুসলমান বলা হয় এবং অন্যদল হলো ‘ হান ’ গণ... ‘ হান ’ মুসলমানগণ সাধারণত দীনী বিষয়ে আরবী ও ফার্সী পরিভাষা বিশেষত ফার্সী পরিভাষা বিশেষ গঠনরূপে ব্যবহার করে থাকে। ” 233
এ গ্রন্থে আরো উল্লিখিত হয়েছে ,
“ মসজিদের আলেমদের প্রধানকে ‘ আখুন্দ ’ অথবা ‘ অখুনাক ’ বলা হতো যার অর্থ ইসলামী বিধান শিক্ষাদাতা। জামায়াতের নামাজের ইমাম প্রধান আলেমের সহযোগী বলে বিবেচিত হতেন... চীনের তৎকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইরান ও আরবের অনুকরণে ছিল। ”
‘ হেযারেয়ে শেখ তুসী ’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সাইয়্যেদ জাফর শাহিদী ‘ বিশ্বে ইসলামের প্রসারে ইরান জাতির অবদান ’ শীর্ষক প্রবন্ধে (যা তিনি গত বছরে অনুষ্ঠিত শেখ তুসীর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পাঠ করেন) চীনে ইসলামের প্রবেশের বিষয়ে আতা মূলক জুয়াইনীর ‘ জাহান গুশাই ’ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ,
“ এ বিষয়টি (নবুওয়াতের সত্যতা) বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব এবং কল্পনা হতেও দূরে নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে দু ’ টি বিষয় রয়েছে: প্রথমত নবুওয়াতের প্রকাশ ,দ্বিতীয়ত নবুওয়াতের বাণী। এটি একটি শক্তিশালী অলৌকিক নিদর্শন যে ,ছয়শ ’ বছরের কিছু পর নবী (সা.)-এর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন: আমার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি পূর্ব-পশ্চিমের সেই প্রস্তুত হয়ে থাকা দেশগুলোকে যেখানে আমার উম্মতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ”
এটি বহিঃশত্রুর পতনের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে... এবং এর ফলে ইসলামের পতাকা সমুন্নত ,ইসলাম ধর্মের প্রদীপ প্রজ্বলিত এবং মুহাম্মদী দীনের আলো সকল ভূমিকে আলোকিত করবে ,অথচ এমন ভূমিতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল যেখানে পূর্বে ইসলামের সুগন্ধ কখনও পৌঁছেনি ,তাদের অধিবাসীরা আজান ও তাকবীরের ধ্বনি শুনেনি ,নাপাক লাত ও উজ্জার উপাসনা ছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। আর এই ভূমিতেই কিছু মুমিনের সৃষ্টি হয় যাঁরা নিজ ভূমির সীমা অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছেন ও সেখানে বসতি স্থাপন করে ইসলামের বাণী প্রচার করেন ।
অনারবদের কেউ কেউ খোরাসান ও উজবেকিস্তান (সামারকান্দ ও বোখারা) হতে মোগলদের মাধ্যমে কারিগর ও পশুপালক হিসেবে তাদের বিজিত ভূমিতে (চীনে) কাজের জন্য গৃহীত হয় এবং কেউ কেউ সিরিয়া ,ইরাক ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চল হতে ব্যবসায় অথবা পর্যটনের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে যায়। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই পরিচিতি লাভ করেছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ের পাশাপাশি মসজিদ ,মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আলেমগণ ধর্মীয় শিক্ষা ,জ্ঞান ও নিজ চিন্তা-মতকে সবার মধ্যে প্রচার করেন ও একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্ভবত এ সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল (সা.) বলেছিলেন , “ চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞান শিক্ষা কর। ”
ছয়শ ’ বছর পর ইরানী ও অ-ইরানী ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ চীনে যাবেন ও তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করবেন এ সম্পর্কিত নবীর ভবিষ্যদ্বাণীকে আতা মূলক জুয়াইনী তাঁর অন্যতম মুজিযা মনে করেছেন।
ইসলামের পথে আত্মোৎসর্গীকৃত সামরিক সেবা
ইসলামের পথে ইরানীদের সামরিক সেবা ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সামরিক সেবা তারা আন্তরিকভাবেই দিয়েছিল।
আমরা ইয়েমেনের অধিবাসী ইরানী মুসলমানদের আত্মত্যাগী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। উমাইয়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের আন্দোলন আব্বাসীয়দেরকে ক্ষমতায় বসায় তাও এরূপ ভূমিকার সাক্ষ্য। তাদের এই সামরিক অভ্যুত্থান শুধু আরবদের ইসলামের সঠিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করানো ও প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ছিল। যদিও এই সামরিক অভ্যুত্থানের বিজয়ে উমাইয়্যাদের পতন ঘটেছিল ,কিন্তু তার পরিবর্তে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের হতে উত্তম ছিল না। ফলে উত্তম কোন ফল হয়নি।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে ইরানের অভ্যন্তরেই কিছু আন্দোলন শুরু হয় যা ইসলামবিরোধী ছিল বিধায় দমন করা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ,এ ইসলামবিরোধী আন্দোলনগুলোকে আরবরা নয় ,ইরানীরাই দমন করে।
তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে আজারবাইজানে ববাক খুররাম দীনের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয় যদি ইরানী সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকরা না থাকত তাহলে আড়াই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তা দমন করা সম্ভব হতো না। আল মুকাননাহ্ ,সিনবাদ অথবা উসতাদাসিসের নেতৃত্বে যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল তাও অনুরূপ। সুলতান মাহমুদ গজনভী ভারতবর্ষে যে সকল সেনা অভিযান চালান তাতে ইসলামী জিহাদের রং দিয়েছিলেন বলেই ইরানীরা জিহাদের উদ্দীপনা নিয়ে ভারতের বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। তেমনিভাবে ইরানের বিভিন্ন সম্রাট পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে পরিচালিত ক্রুসেডের যুদ্ধগুলোতে ইরানী মুসলমানদের ইসলামী অনুভূতি ও চেতনাকে ব্যবহার করেছিলেন বলেই ভাল ফল পেয়েছিলেন।
ইরানী সৈন্যরাই এশিয়া মাইনরে ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ,আরবরা নয়। এখানে ‘ হাজারেয়ে শেখ তুসী ’ গ্রন্থের ডক্টর সাইয়্যেদ জাফর শাহিদীর প্রবন্ধ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন ,
“ মুসলমানগণ পূর্ব রোমকে রোমসাম্রাজ্য এবং ভূমধ্যসাগরকে ‘ রোম সাগর ’ বলে থাকে। এ কারণেই এশিয়া মাইনরকে (তুরস্ক ,লেবানন ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশও এর অন্তর্ভুক্ত) তারা রোম বলত।... মুসলমানরা যখন সমগ্র সিরিয়া দখল করে তখন এশিয়া মাইনরও হস্তগত করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। খলীফা হযরত উমরের শাসনামলে মুয়াবিয়া চেয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে আক্রমণ করতে ,কিন্তু খলীফা অনুমতি দেননি। খলীফা হযরত উসমানের শাসনামলে তাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি আমুবিয়া পর্যন্ত জয় করেন। কিন্তু তখন হতেই এই ভূমি নিয়ে মুসলমান ও রোমীয়দের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতদঞ্চলের ভূমি ,শহর ও দুর্গগুলো কখনও উমাইয়্যা বা আব্বাসীয় খলীফাদের আওতায় কখনও রোমীয়দের আওতায় হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মতে উমাইয়্যা বা আব্বাসীয় খলীফা কারো পক্ষেই সমগ্র অঞ্চলে ইসলামের স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।... দীর্ঘ সময় পর একমাত্র সালজুকীদের শাসনামলে এই অঞ্চলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং সমগ্র এশিয়া মাইনর তাদের অধীনে আসে। এ সময়েই ইসলামের বাণী ও শিক্ষা সেখানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং এতটা বিকাশ লাভ করে যে ,ইসলামী অধ্যাত্মবাদের প্রবাদ পুরুষ জালালুদ্দীন রুমীর ন্যায় ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ও এই জ্যোতি সকল ফার্সী ভাষী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।
এ অংশটি অকসারায়ী প্রণীত ‘ মুসামেরাতুল আখবার ’ নামক এশিয়া মাইনরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ হতে বর্ণনা করছি। কারণ এ গ্রন্থে এতদঞ্চলের ইরানী শাসক ও মুসলমান জনসাধারণের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। যদি ইরাক ও পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোতে মুসলিম খলীফাদের আক্রমণ এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে যে ,জিযিয়া লাভের মাধ্যমে বায়তুল মালের পরিমাণ বৃদ্ধি ;পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে ইরানী মুসলিম বিজেতাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ইসলামের প্রচার ও প্রসার। অকসারায়ী বর্ণনা করেছেন , ‘ রোম সম্রাট আরমিয়ানুস এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামী ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথমে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের
সীমান্তবর্তী নাকিসারুসিওয়াম ,তুকাত ,আবলিস্তান ও অন্যান্য অংশে আক্রমণের চিন্তা করেন। এতদঞ্চলের শাসক দানেশমান্দ মুসলিম শাসক কাল্জ আরসালানের নিকট দূত পাঠিয়ে কাফেরদের মোকাবিলায় উৎসাহিত করলেন ও প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি মুসলমানরা জয়ী হয় তাহলে তাদের এক লক্ষ দিনার ও আবলিস্তান উপহার দেবেন। কাল্জ আরসালান ইসলামী দৃষ্টিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে অন্যান্য মুসলিম শাসকদের সহযোগিতা নিয়ে বড় এক সেনাবাহিনী নিয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা বিজয় লাভ করেন এবং আরমিয়ানুস যুদ্ধ হতে পলায়নে বাধ্য হন ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর খুব কমই প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। সম্রাট দানেশমান্দ কাল্জ আরসালানের নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে আবলিস্তান হস্তান্তরে সম্মত হলেন। মুসলিম শাসক কাল্জ আরসালান এ কথা শুনে ঐ এক লক্ষ দিরহাম ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন , “ আমি ইসলামের জন্য এ যুদ্ধ করেছি। দিনার ও দিরহামের আমার কোন প্রয়োজন নেই। ”
একই গ্রন্থে ভারতবর্ষে মুসলমানদের সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে :
“ 43 হিজরীতে প্রথমবারের মতো আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার আবদী ,আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে কুরাইযের পক্ষ হতে সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ চালান ও ব্যর্থ হন। 44 হিজরীতে মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরাহ্ সেখানে আক্রমণ চালান ,কিন্তু সফল হননি। 89 হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এক যুদ্ধে সিন্ধুর রাজাকে পরাস্ত করেন ও তাঁকে হত্যার মাধ্যমে এ অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচারকার্য ইরানীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।
এখানেও আমরা ঐতিহাসিক সূত্র লক্ষ্য করলে দেখতে পাই ঐতিহাসিক জারফাদকানী বাদশাহ নাসিরুদ্দীন সাবক্তাকীন সম্পর্কে বলেছেন , “ তিনি কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও ইসলামের শত্রুদের দমনের কাজ শুরু করেন এবং মূর্তিসমূহের উপাসনালয় ও ইসলামের শত্রুদের আবাসস্থলকে ধর্মীয় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেন। ”
সুলতান মাহমুদ গজনভীর জীবনী আলোচনায় তিনি লিখেছেন , “ সুলতান ইয়ামিনুদ্দৌলা ও আমিনুল মিল্লাহ্ যখন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ দখল করতে শুরু করেন তখন এমন দূরবর্তী স্থানসমূহেও পৌঁছান যেখানে কখনও ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়নি ও কোন সময়েই মুহাম্মদী ধর্মের দাওয়াত ,কেরাআনের আয়াত ও মুজিযার কথা পৌঁছেনি। তাঁরা সেখান হতে র্শিক ও কুফরের অন্ধকার দূর করেন ,ইসলামের শরীয়তের মশালকে সেখানকার শহর ও গ্রামগুলোতে নিয়ে যান ,মসজিদসমূহ তৈরি করেন ,কোরআন পাঠ ও শিক্ষাদান শুরু করেন ,ইসলামের আজান ও ঈমানের আহ্বানকে প্রকাশ করেন...। ”
সুলতান মাহমুদ গজনভীর প্রাচ্যে বিজয় অভিযান ও শাসন পদ্ধতির সঙ্গে স্পেনে প্রথম মুসলিম শাসক আবদুর রহমানের আচরণের তেমন অমিল না থাকলেও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামের বিজয় অভিযানের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। আরব মুসলমানরা পাশ্চাত্যে তাদের বিজয় অভিযান ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত চালাতে সক্ষম হলেও ইতিহাসের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে তা মুসলমানদের আধিপত্যের বাইরে চলে যায় এবং ঐ অঞ্চলের নবীন মুসলমানরাও ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু ইরানী জাতিভুক্তদের মাধ্যমে প্রাচ্যে ইসলামী সভ্যতার যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তা এতটা দৃঢ় ও মজবুত ছিল যে শত শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও এতদঞ্চলের মানুষ মুসলমান হিসেবে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো ,যে বছর234 আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ ইসলামের শত্রুদের দ্বারা অধিকৃত হয়235 সে বছরই ইরানের পূর্ব দিকে 9 কোটি মানুষ স্বতন্ত্র ইসলামী ভূমি ও দেশ হিসেবে পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিজ সম্পৃক্ততার ঘোষণা দেয়।236
যদিও যে সকল মুসলিম বিজেতার নাম এখানে এসেছে ,যেমন কাল্জ আরসালান ,নাসিরুদ্দীন সাবক্তাকীন ,সুলতান মাহমুদ গজনভী ও অন্যান্য সকলেই ইরানী তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন ,কিন্তু যেমনটি ডক্টর শাহিদী বলেছেন যে ,তাঁরা ছিলেন তৎকালীন ইরানের প্রতিনিধি ও এ ভূখণ্ডের শক্তির প্রতীক ও এতদঞ্চলের মুসলমানদের শাসক এবং তাদের পক্ষে ইসলামের নামে ইরানীরাই জিহাদ করত ;অন্যরা নয়।
জ্ঞান ও সংস্কৃতি
ইরানীদের ইসলামের পেছনে অবদানের ক্ষেত্র হিসেবে সবচেয়ে ব্যাপক ও উদ্দীপনার স্বাক্ষরসম্পন্ন ক্ষেত্রটি হলো জ্ঞান ও সংস্কৃতি।
সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশ ,সামগ্রিকতা ও সর্বজনীনতা ,সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ,সামষ্টিক ও সুন্দর উদ্যোগসমূহের বিচিত্রতা প্রভৃতি দিকগুলো ইসলামী সভ্যতার তীব্র আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“ আরবগণ (মুসলমানগণ) এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময়ের মধ্যে অন্য ভাষা হতে বিভিন্ন জ্ঞানের যে বিপুল সংখ্যক অনুবাদ করে রোমীয়গণ কয়েক শতাব্দীতেও তা পারেনি। হ্যাঁ ,মুসলমানগণ সভ্যতা সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হয়েছিল। ” 237
মুসলমানগণ কোরআন ও সুন্নাতকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ ,যেমন কেরাআত ,তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ,হাদীস ,ফিকাহ্ ,সারফ ,নাহু (ব্যাকরণশাস্ত্র) ,মায়ানী ,বাদীই ও বায়ান (বর্ণনাভঙ্গী ও অলংকারশাস্ত্র) ,সীরাতুন্নবী (নবীর জীবন ও ইতিহাস) প্রভৃতি নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। এ সকল বিষয়ে যদি কিছু অন্যদের হতে নিয়েও থাকে তা অনুল্লেখ্য। যে সকল জ্ঞান তৎকালীন অন্যান্য জাতির নিকট ছিল ও ভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার ফল বলে বিবেচিত হতো ,যেমন অংকশাস্ত্র ,প্রকৃতিবিজ্ঞান ,জ্যোতির্বিজ্ঞান ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞান তা আরবীতে ভাষান্তরিত ও অনূদিত হয়েছিল। জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“ ইসলামী সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো গ্রীক ,পারসিক ,ভারতীয় ও ব্যাবিলনীয় ভাষার গ্রন্থগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করে সেগুলোর পরিবর্ধন সাধনের মাধ্যমে পূর্ণতা দান। ”
মুসলমানগণ বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান দর্শন ,অংকশাস্ত্র ,জ্যামিতি ,জ্যোতির্বিজ্ঞান ,সাহিত্য ,চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহকে আরবীতে অনুবাদ করে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহ যথা গ্রীক ,ভারতীয় (হিন্দী) ,ফার্সী ভাষা হতে গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করা হয়। বলা যায় প্রতিটি জাতিরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানগুলোকে তারা গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ গ্রীকদের নিকট থেকে দর্শন ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,জ্যামিতিবিজ্ঞান ,যুক্তিশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা ;ইরানীদের নিকট থেকে ইতিহাস ,সাহিত্য ,সংগীত ,উপদেশবাণী ও জ্যোতিষ্কবিদ্যা ;ভারতীয়দের নিকট থেকে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা ,উদ্ভিদবিজ্ঞান ,তারকাবিজ্ঞান ,হিসাবশাস্ত্র ,গল্পকাহিনী রচনা ও সংগীত শিল্প। ব্যাবিলনীয় ও নাবতীদের নিকট থেকে কৃষিকাজ ,উদ্ভিদের পরিচর্যা ,জ্যোতির্বিদ্যা ,যাদু ও হিপনোটিসম ;মিসরীয়দের নিকট থেকে রসায়ন ও বিশ্লেষণবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে আরবগণ (মুসলমানগণ) অ্যাসিরীয় ,ব্যাবিলনীয় ,মিশরীয় ,ইরানী ,ভারতীয় ও গ্রীক জ্ঞানসম্ভারকে (সাহিত্য ,স্থাপত্য ও অন্যান্য জ্ঞান) সমন্বিত করে ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয়।238
প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র
ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি (সার্বিকভাবে ইসলামী সভ্যতা) ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে গৌরবময় স্থানে পৌঁছায়। যেমনভাবে সজীব প্রাণীসমূহ প্রথমদিকে এককোষী হিসেবে উৎপত্তি লাভ করে ও ধীরে ধীরে তার অভ্যন্তরীণ প্রাণসত্তা ও ক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে শাখা-প্রশাখা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয় ও সবশেষে পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তেমনিভাবে ইসলামী সভ্যতাও বিকশিত হয়ে পূর্ণতায় পৌঁছায়।
মুসলমানদের জ্ঞান অন্বেষণের ধারা ও উদ্দীপনা একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে শুরু হয়। এখন আমরা দেখব কোন্ স্থানে এ আন্দোলনের ধারাটি শুরু হয় অর্থাৎ মুসলমানদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রটি কোথায় চালু হয় ?
মুসলমানদের জ্ঞানার্জন ও বিকাশের ধারা মদীনা হতে শুরু হয়েছিল। প্রথম যে গ্রন্থটি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও মুসলমানগণ তার অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করে তা হলো কোরআন। কোরআনের পর তাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল হাদীসসমূহ। হেজাযের আরবরা প্রথমবারের ন্যায় শিক্ষক-ছাত্রের মুখস্থকরণ ,সংকলন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। মুসলমানগণ আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতসমূহ মুখস্থ করত। যে সকল আয়াত তারা সরাসরি রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে না শুনত তা রাসূলের নির্দেশে কোরআন সংকলনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের239 নিকট থেকে শুনত ও মুখস্থ করত। তদুপরি তারা রাসূলের পুনঃপুন নির্দেশের কারণে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহকে পরস্পরের নিকট থেকে শ্রবণ করে মুখস্থ করত অথবা লিখে রাখত।
মদীনার মসজিদে নিয়মিত শিক্ষার আসর বসত এবং সেখানে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন দু ’ দল লোক ভিন্ন দু ’ ধরনের কর্মে মশগুল রয়েছে। একদল ইবাদাত ও যিকর-আযকারে মশগুল অপর দল জ্ঞানের আলোচনায়। রাসূল দু ’ দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন ,
كلاهما على خير و لكن بالتّعليم أُرسلت
“ দু ’ দলই কল্যাণময় কর্মে লিপ্ত রয়েছে ,তবে আমি শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। ” অতঃপর রাসূল জ্ঞানের আলোচনায় লিপ্তদের সঙ্গে গিয়ে বসলেন।240
মদীনার পর ইরাক জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সর্বপ্রথম ইরাকের বসরা ও কুফা এই দু ’ শহর জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। পরে বাগদাদ শহর নির্মিত হলে তা জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এখান হতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খোরাসান ,রেই ,বুখারা ,সামারকান্দ (বর্তমানের উজবেকিস্তানের দু ’ শহর) ,মিশর ,সিরিয়া ,আন্দালুস ও অন্যান্য স্থান জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়। জর্জি যাইদান মুসলিম শাসকদের উদ্যোগকে এ বিষয়ে সবচেয়ে কার্যকর প্রভাবশীল বলে মনে করেন। তিনি বলেন ,
“ ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহ ও উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের অনুরাগ ও জ্ঞান চর্চার মনোবৃত্তির ফলে ইসলামী দেশসমূহে গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচয়িতার পরিমাণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে ও গবেষণার পরিধির উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ঘটে। সম্রাট ,উজীর ,প্রাদেশিক শাসনকর্তা ,ধনী ,দরিদ্র ,আরব ,ইরানী ,রোমীয় ,ভারতীয় ,তুর্কী ,মিশরীয় ,ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,দাইলামী ,সুরিয়ানী সকলেই ইসলামী ভূখণ্ডের সকল স্থানে যথা সিরিয়া ,মিশর ,ইরাক ,ইরান ,খোরাসান ,উজবেকিস্তান ,সিন্ধু ,আফ্রিকা ,স্পেন প্রভৃতিতে দিবা-রাত্র গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ যেখানেই ইসলামী শাসন ছিল সেখানেই জ্ঞানের দ্রুত বিস্তার ঘটতে লাগল। এ সকল মূল্যবান রচনাসমগ্র ও সংকলনে পূর্ববর্তী যুগসমূহের সকল গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছিল। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান ,ঐশী জ্ঞান ,ইতিহাস ,অংকশাস্ত্র ,সাহিত্য ,দর্শন ,প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থসমূহে সমন্বিতভাবে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফল হিসেবে উপরোক্ত জ্ঞানসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত হয়। ’ 241
যখন অন্য ভাষার জ্ঞানসমূহ আরবীতে অনূদিত হওয়া শুরু হয় তখন খ্রিষ্টান মনীষীরা বিশেষত সিরীয় খ্রিষ্টানরা এ বিষয়ে অন্যদের হতে অগ্রগামী ছিলেন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মুসলমানগণ সে স্থান অধিকার করে।
জর্জি যাইদান বলেন ,
“ আব্বাসীয় খলীফাগণ জ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ বাগদাদের মাটিতে রোপন করেন এবং এর ফল পর্যায়ক্রমে খোরাসান ,রেই ,আজারবাইজান ,উজবেকিস্তান ,মিশর ,সিরিয়া ,আফ্রিকা ,স্পেন প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে খেলাফত ও ইসলামী ভূখণ্ডের সম্পদের কেন্দ্র হিসেবে পূর্বের ন্যায় মনীষীদের সম্মিলন কেন্দ্ররূপে এরপরও বিদ্যমান থাকে। আব্বাসীয় খলীফাদের সেবায় নিয়োজিত খ্রিষ্টান চিকিৎসকগণই প্রথমদিকে চিকিৎসা ও অনুবাদের কাজ করতেন। পরবর্তীতে বাগদাদ হতে কিছু মুসলিম পণ্ডিত এ কর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু সার্বিকভাবে বাগদাদের প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ পর্যায়ের মনীষীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ছিলেন যাঁরা খলীফাদের দরবারে কর্মের জন্য ইরাক ও অন্যান্য স্থান হতে নিয়োগ পেয়েছিলেন। মুসলিম মনীষীদের অধিকাংশই বাগদাদের বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিশেষত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তখন ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের শাসকগণ খলীফাদের অনুসরণে জ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করেন ও তাঁদের অধীন বিভিন্ন অঞ্চল ,যেমন কায়রো ,গাজনীন ,দামেস্ক ,নিশাবুর ,ইসতাখর ও অন্যান্য স্থান হতে পণ্ডিত ও গবেষকদের আহ্বান জানান। ফলে রেই হতে জাকারিয়া রাযী ;তুর্কিস্তানের242 বোখারা হতে ইবনে সিনা ;সিন্ধের বিরুন হতে আল বিরুনী ,উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনে জালিল ,দার্শনিক ইবনে বাজা ,চিকিৎসক ইবনে জাহরা ,দার্শনিক ইবনে রুশদ ;স্পেন হতে উদ্ভিদবিদ ইবনে রুমীয়া ও অন্যান্যদের সৃষ্টি হয়। ’ 243
সুতরাং প্রথম জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মদীনা এবং সেখানেই জ্ঞানের প্রথম বীজ রোপিত হয়।
জ্ঞানের প্রথম বিষয়বস্তু
প্রথম কোন্ বিষয়টি মুসলমানদের আকর্ষণ করে ও তাদের মধ্যে জ্ঞানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ? মুসলমানদের জ্ঞানের শুরু কোরআন দিয়ে। তারা প্রথম কোরআনের আয়াতের অর্থ ও বিষয়বস্তু অনুধাবন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর হাদীস গবেষণা শুরু করে। তাই যে শহরটিতে সর্বপ্রথম জ্ঞানের জাগরণ শুরু হয় তা হলো মদীনা। মুসলমানদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মসজিদ। তাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং তাদের প্রথম শিক্ষক ছিলেন রাসূল (সা.)। ইসলামের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল পঠন ,তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ,হাদীস ,রিজালশাস্ত্র ,ভাষাজ্ঞান ,অভিধান ,সারফ ও নাহু (ব্যাকরণশাস্ত্র) ,বাচনভঙ্গী ও অলংকারশাস্ত্র ,ইতিহাস ইত্যাদি। এ সকল জ্ঞান কোরআন ও সুন্নাতের স্বার্থে সৃষ্টি হয়েছিল। এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেছেন ,
“ বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ প্রফেসর দাখভিয়া এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার বাইশতম খণ্ডে তাবারী ও অন্যান্য আরব ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে প্রশংসনীয়ভাবে ইসলামী সমাজে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত কোরআনের আলোকে ইতিহাসের জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়টি সেখানে আলোচিত হয়েছে। তিনি এ জ্ঞানসমূহ কিরূপে ঐশী প্রজ্ঞার ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রথমত শব্দ ও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়। যখন অন্যান্য ভাষাভাষীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ শুরু করে তখন আরবী শব্দ ও বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের আশু প্রয়োজন অনুভূত হলো। কারণ পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআনে বর্ণিত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য আরবী প্রাচীন কবিতাসমূহ যথাসম্ভব সংকলনের প্রয়োজন পড়ল... এই কবিতাসমূহের অর্থ অনুধাবনের জন্য আরবদের বংশ পরিচিতিবিদ্যা ও তৎকালীন আরবদের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য হিসেবে দেখা দিল। কোরআনে অবতীর্ণ বিধিবিধানের পূর্ণতার জন্য জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট হতে নবীর বাণী ও কর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নের ফলশ্রুতিতে হাদীসশাস্ত্রের জন্ম হলো। হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের জন্য হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অপরিহার্য বিষয় বলে পরিগণিত হলো।... গবেষণার স্বার্থে সনদের বাস্তবতা ,ইতিহাসের জ্ঞান ,বর্ণনাকারীদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এর ফলে হাদীসশাস্ত্রবিদগণের জীবনী ,বিভিন্ন সময়ের জ্ঞান ,প্রশিক্ষণ ও ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান উদ্ভূত হলো। এ ক্ষেত্রে আরবের ইতিহাস যথেষ্ট ছিল না। তাই প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষত ইরানী ,গ্রীক ,হামিরী ,হাবাশী ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস জানাও কোরআনে সন্নিবেশিত জ্ঞান ও প্রাচীন কবিতা বোঝার জন্য অপরিহার্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ভূগোলবিদ্যাও এ উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। এরূপ অন্যান্য বিদ্যাও ইসলামী সাম্রাজ্যে দ্রুত বিস্তারের সাথে সাথে অপরিহার্য হিসেবে উদ্ভূত হয়। ” 244
জর্জি যাইদানের মত এটিই যে ,অন্যান্য জ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ কোরআনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মুসলমানগণ কোরআনের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং এর সঠিক তেলাওয়াত ও উচ্চারণের বিষয়ে গুরুত্ব দিত। কোরআন তাদের দীন ও দুনিয়ার সমস্যার সমাধান দিত এবং তারা কোরআনের বিধান বোঝার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাত। কোরআনের শব্দ ও অর্থ অনুধাবনের প্রচেষ্টা বিভিন্ন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটায়। ইসলামী সমাজে যে সজীব কোষটি জন্মের পর বিকাশ ও পূর্ণতার মাধ্যমে বৃহৎ ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয় সে কোষটি হলো কোরআনের প্রতি মুসলমানদের সীমাহীন ভালবাসা ও প্রেম। কোরআনের প্রতি মুসলমানদের অকুণ্ঠ ভালবাসাই যে জ্ঞানের সকল দ্বার উন্মোচনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই বলে জর্জি যাইদান মনে করেন। তিনি বলেন ,
“ মুসলমানগণ কোরআন লিখন ও সংরক্ষণে যথার্থ দৃষ্টি রাখত ও এ বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দিত যে ,ইতোপূর্বে অন্য কারো ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়নি। তারা এমনকি স্বর্ণ ,রৌপ্য ও হাতির দাঁতের পত্রের ওপরও কোরআন লিখত। কখনও রেশমী কাপড় বা দামী কোন কাপড়ের ওপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের কালি দ্বারা কোরআনের আয়াত লিখা হতো। গৃহ ,মসজিদ ,গ্রন্থাগার ,সভাকক্ষের দেয়াল ও দরবারসমূহ এরূপ কাপড় ও কোরআনের আয়াতের দ্বারা অলংকৃত করত। লেখার জন্য সুন্দর হাতের লেখা ব্যবহার করত। বিভিন্ন ধরনের চামড়া ও কাগজ কোরআন লিখনে ব্যবহৃত হতো এবং বিভিন্ন রংয়ের কালির মাধ্যমে লিখে তার চারিপাশের রেখাগুলো স্বর্ণ দিয়ে অলংকৃত করা হতো।... মুসলমানগণ কোরআনের শব্দ ও আয়াত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করত ,এমনকি কোরআনের বর্ণসংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে তারা গণনা করেছিল। ” 245
তিনি বলেছেন ,
“ ...তাদের সকল বক্তব্য ও লেখনীতে কোরআনের পথকে তাদের কর্মপদ্ধতির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদের লেখনীতে কোরআনের আয়াতসমূহ হতে উদাহরণ নিয়ে আসত। কোরআনের শিক্ষা ও আদব তাদের দৈনন্দিন জীবনের চরিত্রে ও আচরণে ব্যাপক প্রভাব রাখত। অথচ অধিকাংশ মুসলিম জাতির ভাষা কোরআনের ভাষা ছিল না এবং তারা এমন দেশে বাস করত যেখান হতে কোরআন অনেক দূরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী মুসলমানগণ শরীয়তের জ্ঞান ছাড়াও আরবী ব্যাকরণের বিষয়েও কোরআনের আয়াত ও অর্থ হতে উদাহরণ উপস্থাপন করত ,যেমন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণবিদ সিবাভেই তাঁর গ্রন্থে কোরআন হতে তিনশ ’ আয়াত উদাহরণ হিসেবে এনেছেন। যে সকল সাহিত্যিক ও লেখক তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীকে সুন্দর ও অলংকৃত করতে চাইতেন অবশ্যই কোরআনের আয়াতের সহযোগিতা নিতেন। ” 246
জর্জি যাইদান আরো উল্লেখ করেছেন ,
‘ সালাউদ্দীন আইউবী মিশর অধিকারের পর দ্বিতীয় ফাতেমী খলীফা আল আযিয বিল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে স্বর্ণ দ্বারা লিখিত ও অলংকৃত তিন হাজার চারশ ’ কোরআন পান। আল আযিয বিল্লার মন্ত্রী ইয়াকুব ইবনে কালাস তাঁকে এরূপ কোরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ” 247
ইরানের মাশহাদে ইমাম রেযা (আ.)-এর যাদুঘরে যে প্রাচীন কোরআন সংরক্ষিত আছে সেগুলোর আকর্ষণীয় ও আশ্চর্যজনক সুন্দর লিখনপদ্ধতি ও অলংকৃত পৃষ্ঠাসমূহ এ দেশের মানুষের কোরআনের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার প্রমাণ।
ইসলামের জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বর্ণিত পর্যায়ক্রমিক ধারাতেই বিকশিত হয়েছিল। এখন আমরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা করব।
যদিও ইসলামী বিশ্বের বাইরে হতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত যে সকল গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল তা ইরানী ছিল না ,কিন্তু ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় ও অন্যান্য জ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ ইরানী মুসলিম মনীষীদের মাধ্যমেই রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। এটিই ইসলামী শাসনামলে ইরানীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেছেন ,
“ তাফসীর ,হাদীস ,কালামশাস্ত্র ,দর্শন ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,অভিধান ,জীবনী ,ইতিহাস ,এমনকি আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ আরবদের নামে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে তার অধিকাংশই ইরানীদের রচনা এবং ইরানীদের অংশ বাদ দিলে এ সকল জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ও উত্তম অংশ আর অবশিষ্ট থাকবে না। ”
আমরা এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত মন্তব্য করে অ-ইরানী মুসলমানদের অবদানকে অস্বীকার করতে চাই না। কারণ ইসলামী সভ্যতা বিশেষ কোন জাতির নয় ;বরং সকল মুসলমানের। তাই আরব ,ইরানী বা অন্য কোন জাতি তাঁকে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে না। তবে প্রতি জাতিই তার অবদানের অংশটুকু বর্ণনা ও নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখে।
রচনা ও সংকলনের প্রারম্ভ
সাধারণত প্রাচ্যবিদগণ ও তাঁদের অনুসারীরা দাবি করে থাকেন ,ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রচলন ছিল না ;বরং তা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁরা এ ক্ষেত্রে রচনা ও সংকলনের বিষয়ে রাসূলের নিষেধাজ্ঞার একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটলে রচনা ও সংকলন শুরু হয় এবং তখনই মুসলমানগণ রচনা ও সংকলনের সুফল বর্ণনা করে রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীস উপস্থাপন শুরু করে ।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“ খোলাফায়ে রাশেদীন আরবদের বেদুইন অবস্থা হতে শহুরে জীবনে প্রবেশের বিষয়টিকে ভয় পেতেন। তাঁরা মনে করতেন শহুরে জীবন লাভ করলে তারা সরল সাধারণ জীবন ও উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন হতে দূরে সরে যাবে। এ কারণেই আরবদেরকে গ্রন্থ রচনা ও সংকলন হতে তাঁরা বিরত রাখতেন।... কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার ঘটলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে সাহাবীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং চিন্তা-বিশ্বাসের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত ও সে সবের উত্তর আহ্বান করা হলো। মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে হাদীস ,ফিকাহ্ ও কোরআন সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সংকলন শুরু করল। তারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন ও ইজতিহাদ শুরু করল।... ফলে তখন থেকে রচনা ও সংকলনকে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কর্ম মনে না করে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কর্ম বলা শুরু করল এবং এ বিষয়ে নবী (সা.)-এর নিকট হতে আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করল। ” 248
জর্জি যাইদান খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি যে বিষয়টি আরোপ করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। জর্জি যাইদান শহুরে জীবনের প্রতি অনীহা এবং রচনা ও সংকলন নিষিদ্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে যা বলেছেন তার কোনটিই ঠিক নয়। নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মদীনা হতে বহির্গত হওয়া ও অন্য স্থানে বসতি স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধকরণে নিষেধ ও বাধা প্রদানের বিষয়টি খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলীফার প্রতি আরোপ করা কখনই সঠিক নয়। কারণ এ বিষয়টি শুধু দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পূর্বে আমরা হাদীস সংকলনের বিষয়ে একদিকে হযরত আলী ও একদল সাহাবীর অবস্থান গ্রহণ ও অন্যদিকে হযরত উমর ও আরেকদল সাহাবীর তার বিপরীতে অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছি। আমরা পরে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। মদীনা হতে অন্যত্র হিজরত ও বসতি স্থাপনের বিষয়েও হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। এ কারণেই রাজধানী কুফায় স্থানান্তরের পর হযরত আলী তাঁর বিপরীত নির্দেশ দেন। তাই জর্জি যাইদানের বক্তব্য ভিত্তিহীন।
এডওয়ার্ড ব্রাউনের মতেও প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকলেও কোন গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। তাই জ্ঞান ও তথ্যসমূহ মুখস্থের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং বলতে গেলে একমাত্র কোরআনই লিখিতরূপে গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেছেন ,
“ প্রথম হিজরী শতাব্দীতে জ্ঞান অর্জন একমাত্র ভ্রমণ ও হিজরতের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। তারা জ্ঞানান্বেষণে দীর্ঘ সফর করত। প্রথমদিকে পরিস্থিতির কারণেই সফরের বিষয়টি অপরিহার্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সফর নিয়মে পরিণত হয় ও এক রকম উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নিম্নোক্ত হাদীসের ন্যায় জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সফরের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ এর সমর্থনে উপস্থাপিত হলো। যেমন নবী (সা.) বলেছেন: “ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের পথে পরিচালিত করেন। ” মিশরের অধিবাসী মাকহুল নামের একজন দাস তার মনিব কর্তৃক মুক্ত ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ততক্ষণ মিশর ত্যাগ করেনি যতক্ষণ মিশরের প্রচলিত জ্ঞানসমূহ অর্জন সমাপ্ত হয়নি। অতঃপর যখন তার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল তখন সে হেজায ,সিরিয়া ও ইরাকে যায় ও গনীমতের মাল বণ্টন সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ সংকলন করে। ” 249
কিন্তু এ মতটি ভিত্তিহীন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নিদর্শনসমূহ হতে বোঝা যায় নবী (সা.)-এর সময় হতেই লিখন ও সংকলন শুরু হয় ও অব্যাহত থাকে। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থিত। ব্রাউনের ‘ হিস্ট্রি অব লিটারেচার ’ গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদের প্রথম খণ্ডের টীকা অংশে ব্রাউনের মতো ব্যক্তিদের মতকে খণ্ডন করে আল্লামা শাইখুল ইসলাম যানজানীর ‘ মুসন্নাফাতুশ শিয়াতিল ইমামিয়া ফিল উলুমিল ইসলামিয়া ’ গ্রন্থ হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি এর বিপরীত মতকেই প্রমাণ করেছেন।250
মরহুম আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ হাসান সাদর (আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করুন) তাঁর ‘ তাসিসুশ শিয়া লি উলুমিল ইসলাম ’ নামক মূল্যবান গ্রন্থেও এ মতটির ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় সেখান হতে কিছু অংশ উপস্থাপন করব। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এখানে তা উল্লেখ হতে বিরত থাকছি।
দ্রুততার ভিত্তি ও কারণ
জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্রুত উন্নয়নের অন্যতম কারণ হলো তারা জ্ঞান ,শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন গোঁড়ামি পোষণ করত না। তারা যেখানেই বা যার কাছেই জ্ঞানের সন্ধান পেত তা আহরণ করত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তারা উদার মনোভাব পোষণ করত।
আমরা জানি যে ,নবী (সা.)-এর হাদীসেও জ্ঞান যেখানেই ও যার কাছেই পাওয়া যাক না কেন তা লাভ করতে বলা হয়েছে। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন ,
كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها
“ সঠিক প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ। তাই যেখানেই তা পায় তা অর্জনে তার অধিকার সর্বাধিক। ” 251
নাহজুল বালাগায় এসেছে :
الحكمة ضالّة المؤمن فخذ الحكمة و لو من أهل النّفاق
“ সঠিক জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। তাই তা গ্রহণ কর যদিও মুনাফিকের নিকট হতে হয়। ” 252
হযরত আলী (আ.) অন্যত্র বলেছেন ,
خذوا الحكمة و لو من المشركين
“ জ্ঞান শিক্ষা কর যদিও মুশরিকদের নিকট হতে হয়। ” 253
পবিত্র ইমামগণের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে ,হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন ,
خذوا الحقّ من أهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من أهل الحقّ و كونوا نقّاد الكلام
“ সত্য জ্ঞানকে ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের নিকট হতে হলেও গ্রহণ কর ,কিন্তু ভ্রান্ত ধারণাকে সত্যপন্থীর নিকট হতে হলেও গ্রহণ কর না এবং যে কোন কথা পর্যালোচনা কর। ” 254
সমুন্নত চিন্তা ,গোঁড়ামিমুক্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির এ সকল হাদীস অমুসলমানদের হতেও জ্ঞান অর্জনে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এ হাদীসসমূহ জ্ঞানার্জনে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কারহীন ও মুক্ত মনের সৃষ্টি করেছে।
এ কারণেই মুসলমানরা এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিত না যে ,কার নিকট হতে জ্ঞান লাভ করছে বা কার মাধ্যমে গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে ;বরং তাদের ইমামদের শিক্ষানুযায়ী মুমিন ও জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের মনে করত এবং অন্যদের নিকট তা গচ্ছিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করত। মাওলানা রুমীর ভাষায় :
“ জ্ঞান অন্যের নিকট তোমার ঋণ যেন
দাস বিক্রেতার নিকট ক্রীতদাসী সম। ”
মুসলমানরা বিশ্বাস করত ইলম ও ঈমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং ঈমানহীন পরিবেশে জ্ঞান অপরিচিত হিসেবে মূল্যহীন হয়ে রয়েছে। তাই তার প্রকৃত ও পরিচিত ভূমি মুমিনের অন্তরে ফিরে আসা প্রয়োজন।
তাই রাসূলেরكلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها এ কথা উপরোক্ত সকল কিছুকেই ধারণ করে। আর এজন্যই মুসলমানদের সকল প্রচেষ্টা এ চিন্তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যে ,কিরূপে বিশ্বের সকল জ্ঞানভাণ্ডার হস্তগত করা যায়।
জর্জি যাইদান ইসলামী সভ্যতার দ্রুত প্রসার ও বিস্তারের কারণ সম্পর্কে বলেন ,
“ ইসলামী সভ্যতার দ্রুত প্রসার এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারণ আব্বাসীয় খলীফাগণ অন্য ভাষার জ্ঞান অনুবাদের বিষয়ে ব্যয় করতে কোন দ্বিধা করতেন না এবং জাতি ,ধর্ম ও বংশের বিষয়টি লক্ষ্য করা ব্যতীতই সকল অনুবাদক ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁদের সকল ধরনের সহযোগিতা দিতেন। এ কারণেই ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,যারথুষ্ট্র ,সাবেয়ী ও সামেরী সকল ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিই খলীফাদের নিকট আসত। এ ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলীফাদের আচরণ সকল জাতি ও ধর্মের সেই সকল নেতা যাঁরা স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ চিন্তা করেন তাঁদের আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত। ” 255
জর্জি যাইদান সাইয়্যেদ শরীফ রাযী কর্তৃক সাবেয়ী ধর্মানুসারী আবু ইসহাক নামের এক ব্যক্তির প্রতি মর্সিয়া পাঠের প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন ,চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও মনীষীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি এতটা প্রচলিত যে ,একজন আলেম সম্পূর্ণ মুক্ত মনে একজন সাবেয়ী মনীষীর প্রশংসায় মর্সিয়া পাঠ করেছেন ।
জর্জি যাইদানের মতে খলীফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উদারতা ও তাঁদের সংস্কারমুক্ত হওয়ার কারণেই সাধারণ মানুষও তাঁদের অনুসরণে এরূপ করত। যদি নির্দেশদাতা ও সম্ভ্রান্তগণ স্বাধীন নীতি গ্রহণ করেন তাহলে অন্যরাও তাঁদের অনুসরণে তা-ই করে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ সাইয়্যেদ শরীফ রাযীর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ খলীফাদের অনুসরণ করতেন না এবং এ উদারতা ও সমুন্নত চিন্তা তাঁরা খলীফাদের নিকট হতে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তাঁরা এটি পবিত্র ইসলাম ধর্মের নীতি হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন যা মনে করে যে ,জ্ঞান সকল অবস্থায়ই সম্মানিত। তাই যখন মর্সিয়া পাঠের কারণে সাইয়্যেদের সমালোচনা করা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন , “ আমি জ্ঞানের প্রশংসায় মর্সিয়া পাঠ করেছি ;ব্যক্তির প্রশংসায় নয়। ”
ডক্টর যেররিন কুবও তাঁর ‘ করনামেহ ইসলাম ’ গ্রন্থে মুসলমানদের দ্রুত অগ্রগতির পেছনে গোঁড়ামিমুক্ত উদার নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।
মুসলমানদের জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ হলো জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলামের পুনঃপুন অনুপ্রেরণা দান ও তাকিদ। জর্জি যাইদান খ্রিষ্টধর্মের প্রতি গোঁড়ামি পোষণ সত্ত্বেও (যা তাঁর কোন কোন লেখায় স্পষ্ট ,যেমন তিনি বলেছেন , ‘ প্রথম যুগের মুসলমানগণ কোরআন ব্যতীত অন্য সকল গ্রন্থের বিরোধী ছিল ’ ) এটি স্বীকার করেছেন ,জ্ঞানের প্রতি ইসলামের অনুপ্রেরণা দানের বিষয়টি মুসলমানদের অগ্রগতিতে বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। তিনি বলেন ,
“ যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটল এবং মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষার প্রসার সম্পন্ন করল তখন ধীরে ধীরে শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত হলো। তারা নিজ সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ শুরু করল। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের পথে পা বাড়াল। যেহেতু তারা খ্রিষ্টান পাদ্রীদের হতে দর্শন সম্পর্কে শুনেছিল সেহেতু অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষা দর্শনের প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়ল। বিশেষত রাসূলের নিকট হতে জ্ঞান অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছিল ,যেমন ‘ জ্ঞান অর্জন কর যদিও তা চীনে গিয়ে অর্জন করতে হয় ’ , ‘ প্রজ্ঞা মুমিনের হারান সম্পদ ,যার কাছেই পাও তা গ্রহণ কর যদিও সে ব্যক্তি মুশরিকও হয় ’ , ‘ প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর জ্ঞান অর্জন ফরয ’ এবং ‘ দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর ’ তা তাদের এ পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ” 256
ডক্টর যেররিন কুব বলেছেন ,
“ ইসলাম ইলম (জ্ঞান) ও আলেমের (জ্ঞানীর) প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ দানের বিষয়ে এতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল যে ,তা মানবিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতির কারণ হয়েছিল। কোরআন মানব জাতিকে পুনঃপুন বিশ্বজগৎ ও কোরআনের আয়াতের রহস্য অনুসন্ধানে চিন্তা করতে বলেছে ,অনেক স্থানেই অন্যান্যদের ওপর জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছে ,একস্থানে আল্লাহ্ ও ফেরেশতামণ্ডলীর সাক্ষ্যের সমপর্যায়ে জ্ঞানীর সাক্ষ্যের মূল্য দিয়েছে ,এ বিষয়গুলো জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট বলে ইমাম গাজ্জালী মনে করেন। তদুপরি বিভিন্ন সূত্রে রাসূল (সা.)-এর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসসমূহও ইলম ও আলেমের মর্যাদার সাক্ষ্য। হাদীসসমূহ ও তাতে নির্দেশিত জ্ঞানের বিষয়ে মতানৈক্যও জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদের আসক্তির কারণ হয়েছিল। এ বিষয়টি বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে ও এ সম্পর্কে চিন্তা ও পর্যালোচনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাসূল স্বয়ং জ্ঞানার্জনে অনুপ্রেরণা দিতেন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বন্দী মুক্তিপণ হিসেবে অর্থ প্রদানে সক্ষম ছিল না তারা যদি মদীনার দশটি শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দান করত তবে মুক্তি পেত। রাসূলের অনুপ্রেরণাতেই যাইদ ইবনে সাবেত সুরিয়ানী ও হিব্র “ ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং অন্য সাহাবীরাও জ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যেমন প্রসিদ্ধ সূত্রমতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জিলে পণ্ডিত ছিলেন ,আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসও তাওরাতের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি সুরিয়ানী ভাষা জানতেন বলেও কথিত আছে। নবীর তাকিদ ও অনুপ্রেরণা যেমন মুসলমানদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি জ্ঞানী ও আলেমের সম্মানকে বর্ধিত করেছিল। ”
এখন আমরা ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ইরানীদের প্রভাব ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যও এটিই ,ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইরানীদের কার্যকর ভূমিকাসমূহ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ। ইতোপূর্বে যা বলেছি তা এ আলোচনারই ভূমিকাস্বরূপ এনেছি।
ইতোপূর্বে কয়েকবার বলেছি এবং এখানেও বলছি ইসলামী সভ্যতা বিশেষ কোন জাতির নয় ;বরং ইসলাম ও সকল মুসলমানের। তাই কোন জাতিরই অধিকার নেই তা নিজস্ব বলে দাবি করার। হোক সে আরব বা ইরানী অথবা অন্য কোন জাতির। তবে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব অবদান নিয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে।
কেরাআত ও তাফসীর
ইসলামী জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জ্ঞানটি উৎপত্তি লাভ করে তা হলো কেরাআত ,অতঃপর তাফসীর। কেরাআত কোরআনের শব্দমালার উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তাফসীর পবিত্র কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান।
কেরাআতশাস্ত্রে কোরআন পঠনে ওয়াক্ফ ,ওয়াস্ল ,মাদ ,তাশদীদ ,ইদগাম প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রে কোরআনের কোন কোন শব্দ উচ্চারণের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকে।
সাহাবীরা নবী (সা.)-এর নিকট হতে কোরআন শিক্ষা করতেন ,কোন কোন সাহাবীকে রাসূল সরাসরি কোরআন শিক্ষা দিতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দানের জন্য তাঁদের প্রেরণ করতেন। তাবেয়ীরা (যাঁরা রাসূলের সময়ে ছিলেন না ও তাঁর সাহচর্য লাভ করেননি) সাহাবীদের নিকট হতে কোরআন শিক্ষা লাভ করেন। এ যুগেই কেরাআতশাস্ত্রের একদল বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হয় যাঁরা সঠিকভাবে কোরআন পাঠ শিক্ষা দান শুরু করেন। সাধারণ মুসলমান যাদের সংখ্যা সে সময় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল তারা পরম আগ্রহ নিয়ে কোরআন শিক্ষা করত এবং এই সকল বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতো। এ বিশেষজ্ঞগণ কোন ইমাম বা সাহাবীর সূত্রে কোরআন পাঠ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতেন। তাঁরাও নিজ পদ্ধতিতে ছাত্রদের প্রশিক্ষিত করতেন। তাঁদের ইতিহাস ও কর্মপদ্ধতি ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
কোরআন পাঠ পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণ কি ? রাসূল (সা.)-এর সময়েও কি এ বিষয়ে ভিন্নতা ছিল ? স্বয়ং নবী কি কোরআনের কিছু কিছু শব্দকে কয়েকভাবে পঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন বা কোরআনের কিছু শব্দ কি বিভিন্ন পঠন পদ্ধতির মাধ্যমে নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল ? নাকি অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যায় যে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে পঠনে ভিন্নতার সৃষ্টি হয় কোরআনেও তেমনটি হয়েছে ? এ বিষয়গুলো অন্যত্র আলোচনা হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত ,নবী (সা.) যেরূপে কোরআন পাঠ ও তেলাওয়াত করতেন মুসলমানরা সেরূপেই তা পাঠ ও তেলাওয়াত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করত। যে সকল ব্যক্তি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাসূলের নিকট হতে কোরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাই তারা তাঁদের নিকট হতে কোরআন পাঠ শিক্ষাগ্রহণ করতেন।
প্রথমদিকে কারিগণ মৌলিকভাবে শুনে ও মুখস্থ করে শিক্ষকদের নিকট থেকে শিখতেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এ বিষয়ে গ্রন্থ সংকলিত ও লিখিত হয়।
কেউ কেউ দাবি করেছেন ,এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আবু উবাইদা কাসেম ইবনে সালাম (মৃত্যু 224 হিজরী) একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এ দাবি ভিত্তিহীন এজন্য যে ,এর একশ ’ বছর পূর্বেই সাতজন প্রসিদ্ধ কারীর (কোররায়ে সাবআ) একজন হামযা ইবনে হাবিব- যিনি শিয়া ছিলেন ,কোরআন পাঠ পদ্ধতির ওপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তদুপরি এ সম্পর্কিত গবেষণায় আয়াতুল্লাহ্ হাসান সাদর ইবনুন্ নাদিমের ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ ও নাজ্জাশীর ‘ ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থ হতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যয়নুল আবেদীন (আ.)-এর শিষ্য ও সাহাবী আবান ইবনে তাগলিব এরও পূর্বে এ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
তিনি আরো প্রমাণ করেছেন ,সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) কোরআন সংকলন করেন এবং তাঁরই শিষ্য ও সাহাবী আবুল আসওয়াদ দুয়ালী কোরআনে প্রথম ‘ নুকতাহ ’ সংযোজন করেন।257 সর্বপ্রথম কোরআন পঠন পদ্ধতির ওপর আবান ইবনে তাগলিব গ্রন্থ লিখেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম কোরআনের অর্থ ও কঠিন শব্দসূমহের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বপ্রথম কোরআনের ফযিলত বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা করেন প্রসিদ্ধ সাহাবী ও হযরত আলীর অনুসারী উবাই ইবনে কা ’ ব (রা.)। কোরআনের রূপক শব্দসমূহ নিয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ সংকলন করেন তিনি হলেন প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণবিদ ফাররা যিনি একজন ইরানী শিয়া ছিলেন। সর্বপ্রথম কোরআনের বিধিবিধান নিয়ে যিনি গ্রন্থ লিখেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবী। সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ লিখেন সাঈদ ইবনে যুবাইর।258
যা হোক প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তাবেয়িগণ ও তাদের ছাত্রদের মধ্য হতে দশ ব্যক্তি কোরআন পঠন পদ্ধতিতে (কেরাআতশাস্ত্র) বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে সাতজন প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে ‘ কোররায়ে সাবআ ’ নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন নাফে ইবনে আবদুর রহমান ,আবদুল্লাহ্ ইবনে কাসির ,আবু আমর ইবনুল আলা ,আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ,আছেম ইবনে আবিন নাজওয়াদ ,হামযা ইবনে হাবিব এবং আলী কিসায়ী।
এই সাতজনের চারজনই হলেন ইরানী এবং তাঁদের দু ’ জন হলেন শিয়া। অ-ইরানী তিনজন কারীর দু ’ জনও শিয়া অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারীর মধ্যে চারজন শিয়া। আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ হাসান সাদর তাঁর ‘ তাসিসুশ শিয়া লি উলুমিল ইসলাম ’ গ্রন্থের 346 পৃষ্ঠায় শেখ আবদুল জলিল রাযী-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন কেরাআতশাস্ত্রের পুরোধাদের সকলেই আদলীয়াদের (শিয়া ও মুতাযিলা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ,হোক তিনি কুফা ,বসরা ,মক্কা ,মদীনা বা অন্য কোন স্থানের অধিবাসী।
চার প্রসিদ্ধ ইরানী কারী হলেন :
1. আছেম ইবনে আবিন নাজওয়াদ একজন ইরানী। তিনি আবু আবদুর রহমান সালামীর নিকট কেরাআত শিক্ষা করেছেন। আবু আবদুর রহমান হযরত আলীর শিষ্য ছিলেন। আছেমের কেরাআতকে প্রসিদ্ধতম কেরাআত মনে করা হয়। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে , “ কোরআনের মূল লিখন ও পঠন পদ্ধতিটি সাধারণত আছেমের অনুকরণে লিখা হতো এবং অন্যান্য কারীদের কেরাআতের ধরন নিম্নে লাল কালি দ্বারা কারীর নাম উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ করা হতো।259 আসেম কুফায় থাকতেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ‘ মাজালিসুল মুমিনীন ’ গ্রন্থের লেখকসহ আরো কিছু গবেষক ,যেমন আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর তাঁর শিয়া হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত বলেছেন। তিনি 130 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. নাফে ইবনে আবদুর রহমান সম্পর্কে ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ তিনি ইরানের ইসফাহানের লোক হলেও মদীনায় বাস করতেন। ’ ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ,নাফে কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন। তিনি মদীনায় কেরাআতশাস্ত্রের ইমাম বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মদীনার লোকেরা কেরাআতের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর নির্ভর করত। তিনি প্রসিদ্ধ দশজন কারীর একজন ইয়াযীদ ইবনে কা ’ কা হতে কেরাআত শিক্ষা করেছিলেন। তিনি 159 বা 169 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. ইবনে কাসির সম্পর্কে ইবনুন নাদিম বলেছেন , “ কথিত আছে ইরান সম্রাট আনুশিরওয়ান ইরানীদের যে দলটিকে ইয়েমেনে হাবাশীদের নিকট হতে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন ইবনে কাসির তাদেরই বংশধর। ”
আমরা ইতোপূর্বে ইয়েমেনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এই ইরানীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে , “ ইবনে কাসির কেরাআতশাস্ত্রের মৌলনীতি মুজাহিদ-এর নিকট হতে ,তিনি ইবনে আব্বাস-এর নিকট হতে এবং ইবনে আব্বাস হরযত আলী (আ.)-এর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন। ইবনে কাসির 120 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ”
4. ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে কিসায়ীর নাম আলী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতা হলেন হামযা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বাহমান ইবনে ফিরুয। কিসায়ী একজন প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি আব্বাসীয় খলীফা হারুন উর রশীদের দু ’ পুত্রের শিক্ষক ছিলেন। খোরাসানে আগমনের সময় তিনি হারুনের সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি ইরানের রেই শহরে ইন্তেকাল করেন। ভাগ্যক্রমে হারুনের অন্যতম সফরসঙ্গী ও প্রধান কাযী মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানীও ঐ দিন রেই শহরে মৃত্যুবরণ করেন ও সমাধিস্থ হন। হারুন উর রশিদ এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে বলেন , “ আজকে ইসলামী ফিকাহ্ ও সাহিত্যকে রেইয়ে সমাহিত করেছি। ” কিসায়ী দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে মৃত্যুবরণ করেন। কিসায়ীও শিয়া ছিলেন।
তাফসীরের বিষয়ে বলা যায় ,রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় স্বাভাবিকভাবেই সাহাবিগণ কোরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য রাসূলেরই শরণাপন্ন হতেন। কোন কোন সাহাবী অন্যদের নিকট হতে কোরআনের অর্থ অনুধাবনে অধিকতর অগ্রসর ছিলেন ,এজন্য প্রথম হতেই আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে অন্যদের অনুসরণীয় ছিলেন ,যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। অবশ্য ইবনে আব্বাসের এ ক্ষেত্রে পরিচিতি অধিক ছিল এবং তাঁর মত তাফসীর গ্রন্থসমূহে অধিক বর্ণিত হয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস260 হযরত আলীর শিষ্য ছিলেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে গর্ব করতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদও হযরত আলীর ছাত্র ও শিয়া ছিলেন। গ্রন্থসূচী সম্পর্কিত ‘ আল ফেহেরস্ত ’ গ্রন্থগুলোতে ইবনে আব্বাস সংকলিত একটি তাফসীরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন এই গ্রন্থটি এখনও মিশরের রাজকীয় জাদুঘরে রাখা আছে। তাফসীরে ইবনে আব্বাসের স্বতন্ত্র মত থাকলেও হযরত আলীর এ সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কে তিনি বলেছেন , “ হযরত আলীর জ্ঞানের নিকট আমি মহাসমুদ্রের এক ফোঁটা পানির ন্যায়। ”
জর্জি যাইদান দাবি করেছেন ,প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত কোরআনের তাফসীর মুখে মুখে স্থানান্তরিত হতো এবং কোরআনের সর্বপ্রথম তাফসীর সংকলন করেন মুজাহিদ (মৃত্যু 104 হিজরী)। অতঃপর ওয়াকেদী ও ইবনে জারীর তাবারী দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে তাফসীর লিখেন।261
অবশ্য এ মতটি সঠিক নয়। ইবনে আব্বাস ছাড়াও সাঈদ ইবনে জুবাইর তাঁর পূর্বে তাফসীর সংকলন করেছেন। প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মুসলমানগণ কোন গ্রন্থই রচনা করেনি। এ মতের অনুবর্তী হয়েই জর্জি যাইদান উপরোক্ত মত দিয়েছেন। তাঁর এ মতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। তাই এ মতটি প্রত্যাখ্যাত। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনা করব।
কেরাআতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন ইরানীরা বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাফসীরের ক্ষেত্রেও তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের মূল হিসেবে তাফসীর ,ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রের প্রতি ইরানীরা যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য বিষয়ের প্রতি ততটা নয়। এখানে ইসলামের প্রথম যুগ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল ইরানী মুফাসসিরের নাম উল্লেখ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। কারণ প্রতি শতাব্দীতেই শত শত মুফাসসির ও তাফসীর গ্রন্থ ছিল। তাই তাঁদের মধ্য হতে বিভিন্ন জাতির মুফাসসিরদের পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। তবে তাফসীরশাস্ত্রে ইরানীদের অবদান তুলে ধরার জন্য এ সম্পর্কিত কিছু নমুনা প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও তাফসীর গ্রন্থসমূহের তালিকা হতে উল্লেখ করছি। লক্ষ্য করবেন ,এদের অধিকাংশই ইরানী ছিলেন।
প্রথম পর্যায়ের মুফাসসিরগণ হলেন যাঁদের নাম ও মত তাফসীর গ্রন্থসমূহে অধিকতর উল্লেখ করা হয় অথবা তাঁদের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ এখনো বিদ্যমান। এখানে আমরা তাঁদের মধ্য হতেই মনোনীত করব ।
প্রথম শ্রেণীর মুফাসসির যাঁদের নাম তাফসীর গ্রন্থসমূহে অধিকতর স্মরণ করা হয় তাঁদের কেউ সাহাবী ,কেউ তাবেয়ী ,কেউ তাবে তাবেয়ী আবার কেউ তাঁদের ছাত্র বা শিষ্য। এ ধরনের প্রসিদ্ধ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব হলেন ইবনে আব্বাস ,ইবনে মাসউদ ,উবাই ইবনে কাব ,সা ’ দী ,মুজাহিদ ,কাতাদা ,মুকাতিল ,কালবী ,সাবিয়ী ,আ ’ মাশ ,সুফিযান সাওরী ,জুহরী ,আতা ,আকরাম ,ফাররা প্রমুখ।
এদের কেউ শিয়া ,কেউ সুন্নী ,কেউ ইরানী আবার কেউ অ-ইরানী। স্বাভাবিকভাবেই এদের অধিকাংশই অ-ইরানী। শুধু মুকাতিল ,আ ’ মাশ ও ফাররা ইরানী বংশোদ্ভূত।
মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ইরানের খোরাসান অথবা রেইয়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন ব্যক্তিত্ব এবং 150 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মুকাতিল শাফেয়ী মাযহাবের লোক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং শাফেয়ী অতিরঞ্জিত মন্তব্য করে বলেছেন , “ অন্যরা তাফসীরের ক্ষেত্রে মুকাতিলের পরিবারস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর অনুসারী। ”
‘ রাইহানুল আদাব ’ গ্রন্থের 1ম খণ্ডের 150 পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে সুলাইমান ইবনে মেহরান আ ’ মাশের পিতা ইরানের দামাভান্দের অধিবাসী হলেও আ ’ মাশ কুফায় জন্মগ্রহণ করেন ও জীবন কাটান। আ ’ মাশ শিয়া হলেও আহলে সুন্নাতের আলেমগণও তাঁর প্রশংসা করেছেন। আ ’ মাশ রম্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন । তিনি 150 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফাররা ইয়াহিয়া ইবনে যিয়াদ আকতা একজন আরবী ব্যাকরণবিদ ও অভিধান রচয়িতা। আরবী সাহিত্যের গ্রন্থে তাঁর নাম প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। তিনি কেসায়ীর ছাত্র এবং আব্বাসীয় খলীফা মামুনের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।
‘ রিয়াজুল উলামা ’ ও ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ গ্রন্থের লেখকগণ তাঁকে শিয়া বলেছেন। তাঁর পিতা যিয়াদ আকতা ফাখের মর্মন্তুদ ঘটনায় হুসাইন ইবনে আলী ইবনে হাসানের262 সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয়ায় আব্বাসীয় খলীফার নির্দেশে হস্ত কর্তিত হন। এজন্যই তাঁকে ‘ আকতা ’ বা কর্তিত হস্ত বলা হয়। ফাররা 207 বা 208 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
দ্বিতীয় শ্রেণীর মুফাসসিরগণ হলেন তাঁরা যাঁরা তাফসীর বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে এত অধিক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে ,তা গণনা করা সম্ভব নয়। তাই শুধু এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের নাম এখানে উল্লেখ করব। আমাদের আলোচনা শিয়া মুফাসসিরগণের তাফসীর দিয়ে শুরু করছি। শিয়া মুফাসসিরগণ দু ’ অংশে বিভক্ত। একদল হলেন সে সকল মুফাসসির যাঁরা ইমামগণের উপস্থিতিতে ও বর্তমান অবস্থায় তাফসীর লিখেছেন ও অন্যদল হলেন যাঁরা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অন্তর্ধানের পরবর্তী সময়ে তাফসীর লিখেছেন। ইমামগণের সমকালীন সময়ে যাঁরা তাফসীর রচনা করেছেন তাঁদের কেউ ইরানী ,কেউ অ-ইরানী। ইমামদের সাহাবী এরূপ কয়েকজন মুফাসসির হলেন আবু হামযা সুমালী ,আবু বাছির আসাদী ,ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান ,হুসাইন ইবনে সাঈদ আহওয়াযী ,আলী ইবনে মেহযিয়ার আহওয়াযী ,মুহাম্মদ ইবনে খালিদ বারকী কুমী এবং ফাজল ইবনে শাজান নিশাবুরী।
ইমাম মাহ্দীর অন্তর্ধানের পরবর্তী সময়ের মুফাসসিরের সংখ্যা অসংখ্য। এখানে আমরা শুধু শিয়াদের প্রসিদ্ধ কিছু তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। এ হতেই বোঝা যাবে শিয়া মুফাসসিরগণের অধিকাংশই ইরানী ছিলেন।
1. তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী: এ তাফসীর গ্রন্থটি শিয়াদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ যা এখনও বর্তমান রয়েছে। আলী ইবনে ইবরাহীমের পিতা কুফা হতে কোমে আসেন। অসম্ভব নয় ,আলী ইবনে ইবরাহীম একজন আরব বংশোদ্ভূত ইরানী। তিনি শেখ কুলাইনীর শিক্ষক ও মাশয়িখ (যাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন)। তিনি 307 হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।
2. তাফসীরে আয়াশী: এই তাফসীরটি মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ সামারকান্দী লিখেছেন। তিনি প্রথম জীবনে সুন্নী ছিলেন এবং পরবর্তীতে শিয়া হন। তিনি শেখ কুলাইনীর সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তিন লক্ষ দিনারের পুরোটাই গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি লিখন ,সংকলন ,নকল ও ক্রয়ের কাজে ব্যয় করেন। যে সকল ব্যক্তি এরূপ কর্ম করতেন তাঁদের জীবিকা র্নিবাহের খরচ তিনি দিতেন। আয়াশী তাফসীর ,হাদীস ,ফিকাহ্শাস্ত্র ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে তাঁর রচিত বেশ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন ও দাবি করেছেন আয়াশীর রচিত গ্রন্থসমূহ খোরাসানে বেশ প্রচলিত ছিল। আয়াশী ইরানী হলেও আরব বংশোদ্ভূত বলে মনে হয়। ইবনুন নাদিম বলেছেন ,কথিত আছে তিনি তামীম গোত্রের উত্তর পুরুষ। তিনি তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব।
3. তাফসীরে নোমানী: এ তাফসীরটির রচয়িতা হলেন আবদুুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম। তিনি ইবনে আবি যাইনাব নামেও সুপরিচিত। তিনি শেখ কুলাইনীর ছাত্র। ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন ,তাফসীরে নোমানীর অনুলিপি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে। নোমানী ইরাকের না মিশরের অধিবাসী ছিলেন তা বলা মুশকিল। তিনি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর একজন আলেম।
নোমানীর এক দৌহিত্রের নাম আবুল কাসেম হুসাইন ,যিনি ইবনুল মারযবান নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার দিকে হতে তিনি সাসানী সম্রাট ইয়ায্দ গারদের বংশধর। তিনি কয়েকবার তৎকালীন শাসনকর্তার মন্ত্রী হওয়ায় ‘ ওয়াযিরে মাগরেবী ’ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইবনুল মারযবান চৌদ্দ বছর বয়সে কোরাআনের হাফেজ হন। তিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ ,হিসাবশাস্ত্র ,অংক ও জ্যামিতি ,যুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ মাপের সাহিত্যিক ও শক্তিমান লেখকও ছিলেন।
তিনি ‘ খাসায়িসুল কোরআন ’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 418 অথবা 428 সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জানাজা বাগদাদ হতে নাজাফে স্থানান্তরিত করা হয় ও তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী হযরত আলী (আ.)-এর কবরের নিকটবর্তী স্থানে দাফন করা হয়।
4. তাফসীরে তিবইয়ান: এ তাফসীরের রচয়িতা শেইখুত তায়িফা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী আত তুসী। তিনি তাফসীর ,ফিকাহ্ ,কালামশাস্ত্র ,হাদীস ও আরবী সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তিনি 385 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী তাঁর জন্ম হতে এখন এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গত বছর মাশহাদে তাঁর সহস্র বছর পূর্তি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিয়া-সুন্নী ,মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে প্রচুর মনীষী ও বিশেষজ্ঞ ঐ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র 460 হিজরীতে অস্তমিত হয়। তিনি 23 বছর বয়সে খোরাসান হতে ইরাকে আসেন এবং শেখ মুফিদ ও সাইয়্যেদ মুরতাজা আলামুল হুদার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁর সময়ের শিয়া মতাবলম্বীদের ফকীহ্ ও নেতা হন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও তিনি শিয়া আলেমদের শিরোমণি ছিলেন। মৃত্যুর বারো বছর পূর্বে বাগদাদের অনাকাক্সিক্ষত ঘটনার (মোগলদের আক্রমণ) ফলে নাজাফে চলে আসেন এবং নাজাফের ধর্মীয় মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন যা তাঁর মৃত্যুর এক হাজার বছর পরও বিদ্যমান রয়েছে।
5. মাজমাউল বায়ান: এ তাফসীর গ্রন্থটি ফাযল ইবনে হাসান তাবরেসী রচনা করেছেন। তিনি ইরানে তাফরেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 536 হিজরীতে তাঁর এই তাফসীর লেখা সমাপ্ত করেন। রচনা ও সাহিত্যিক মানের দিক দিয়ে এ তাফসীরটি সর্বোত্তম। আহলে সুন্নাত ও শিয়া উভয়েই এই তাফসীরকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই মিসর ,বৈরুত ও ইরানে পুনঃপুন ছাপা হয়েছে। আল্লামা তাবরেসী ‘ জাওয়ামেউল জামে ’ নামে অপর একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিখেছেন। এ তাফসীরটি তিনি তাঁর সমকালীন প্রসিদ্ধ মুফাসসির জারুল্লাহ্ যামাখশারী রচিত ‘ তাফসীরে কাশশাফ ’ হতে আকর্ষণীয় সাহিত্যিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করে সংযোজন করেছেন।
অবশ্য তাফসীর বিশেষজ্ঞরা জানেন তাফসীরে কাশশাফে এমন অনেক সাহিত্যিক ও অলংকারিক বিষয় রয়েছে যা মাজমাউল রায়ানে নেই। আবার মাজমাউল বায়ানেও এমন অনেক সাহিত্যিক ও তাফসীরগত বিষয় রয়েছে যা ‘ কাশশাফে ’ নেই।
6. রাউযুল জিনান: আবুল ফুতুহ রাযী তাফসীরটি রচনা করেছেন। এ তাফসীর ফার্সী ভাষায় রচিত। শিয়া তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সমৃদ্ধতম ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে ফখরুদ্দীন রাযী ও তাবরেসী উভয়েই এ তাফসীর গ্রন্থ হতে পর্যাপ্ত সাহায্য নিয়েছেন। গত চল্লিশ বছরে তাফসীরটি ইরানে ব্যাপকভাবে ছাপা হয়েছে। আবুল ফুতুহ রাযী নিশাবুরে জন্মগ্রহণ করলেও রেই শহরে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূ ইরানী। তিনি হযরত আলীর বিশিষ্ট সাহাবী ও সিফফিন যুদ্ধে তাঁর পক্ষে অংশগ্রহণকারী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার বংশধর।
আবুল ফুতুহ তাবরেসী ও যামাখশারীর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং শেখ তুসীর পরোক্ষ ছাত্র। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সাল জানা যায়নি। তবে এটি নিশ্চিত ,তিনি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর রেই শহরে বিদ্যমান।
7. তাফসীরে সাফী: বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ,মুফাসসির ,দার্শনিক ও আরেফ মোল্লা মুহাম্মদ ফাইয কাশানী এ তাফসীরটি লিখেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ শিয়া আলেমদের অন্যতম। তিনি একাদশ হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। এই বিশেষ ব্যক্তিত্ব তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। মরহুম ফাইয প্রথম জীবনে কোমে ছিলেন। তাঁর নামেই কোমের ধর্মীয় মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় ‘ মাদ্রাসায়ে ফাইযিয়া ’ । পরে তিনি কোম হতে সিরাজ যান ও সাইয়্যেদ মাজিদ বাহরানীর নিকট হাদীসশাস্ত্র এবং মহান দার্শনিক ও আরেফ সাদরুল মুতাআল্লেহীনের (মোল্লা সাদরা নামে প্রসিদ্ধ) নিকট দর্শন ও এরফান শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সাদরুল মুতাআল্লিহীনের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি 1091 হিজরীতে কাশানে মৃত্যুবরণ করেন।
8. তাফসীরে মোল্লা সাদরা: যদিও মোল্লা সাদরা দর্শন ও অধিবিদ্যাশাস্ত্রে অধিকতর পরিচিত ও স্বতন্ত্র মতবাদের প্রবক্তা তদুপরি তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি উসূলে কাফী নামক হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন। তিনি সূরা বাকারার 65 আয়াত পর্যন্ত ,সূরা সিজদাহ্ ,ইয়াসীন ,ওয়াকেয়া ,হাদীদ ,জুমআ ,ত্বারিক ,আলা ,যিলযাল ,আয়াতুল কুরসী ,সূরা নূরের কিছু আয়াত ও সূরা নামলেরوترى الجبال تحسبها جامدة আয়াতটি তাফসীর করেছেন। যদিও মোল্লা সাদরার তাফসীর পূর্ণ তাফসীর নয় ,তদুপরি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ এবং আয়তনে তাফসীরে সাফীর সমান।
গ্রন্থটি ইরানে কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। তিনি 1050 হিজরীতে পদব্রজে হজ্বে গমনের সময় বসরায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সপ্তমবারের মত হজ্বে যাওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন। কাবার আকর্ষণ তাঁকে এমনভাবে টানত যে ,কণ্টকময় পথ তাঁর নিকট রেশমী কাপড় বিছানো পথের ন্যায় মনে হতো।
9. মিনহাজুস সাদেকীন: এ তাফসীরটি ফার্সী ভাষায় রচিত। এটি তাবরীজ হতে তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। তাফসীরটি মোল্লা ফাতহুল্লাহ্ ইবনে শুকরুল্লাহ্ কাশানী কর্তৃক দশম হিজরী শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। এই লেখকের অধিকাংশ লেখা ফার্সীতে ছিল। যেমন নাহজুল বালাগার ফার্সী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
10. তাফসীরে শাব্বার: সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ শাব্বার এ তাফসীরটি লিখেন। তিনি কাশেফুল গেতা ও মির্যা কুমীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন চিন্তাশীল ,জ্ঞানী ও আবেদ ছিলেন। তিনি উসূল ,ফিকাহ্শাস্ত্র ,কালাম ,হাদীসশাস্ত্র ,তাফসীর ও রিজালশাস্ত্রে প্রচুর গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি 1242 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন ও ইমাম কাযিম (আ)-এর সমাধিস্থলের নিকটে সমাধিস্থ হন।
11. তাফসীরে বুরহান: এই তাফসীরটি সাইয়্যেদ হাশেম বাহরেইনী কর্তৃক রচিত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিয়া মুহাদ্দিস ও গবেষক। তাফসীরটি ‘ আখবারী ’ ধারায় লিখিত অর্থাৎ কোরআন শুধু হাদীসের সাহায্যেই তাফসীর করতে হবে-এই মনোবৃত্তিতে বিশ্বাসীদের ধারায় এটি লিখা হয়েছে। তাই শুধু আয়াতসংশ্লিষ্ট হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদীসটির বিষয়ে কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়নি। সাইয়্যেদ হাশেম বাহরেইনী 1107 অথবা 1109 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
12. নুরুস সাকালাইন: এ তাফসীরটি হুয়াইযের একজন আলেম কর্তৃক লিখিত যিনি সিরাজে বাস করতেন। তাঁর নাম শেখ আবদুল আলী ইবনে জুমাআ। তিনি মরহুম আল্লামা মাজলিসী ও শেখ হুররে আমেলীর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিশ্চিত নয়। তাঁর তাফসীরটিও হাদীসনির্ভর তাফসীর।
ওপরে আমরা যে সকল তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি সেগুলো দ্বাদশ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত শিয়াদের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ এবং শিয়া তাফসীর গ্রন্থসমূহের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের হাতের নিকটেই রয়েছে। তাই শিয়া ভিন্ন অন্যরাও চাইলে সহজেই তা পেতে পারেন। চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতেও অনেক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা এখানে তার উল্লেখ হতে বিরত থাকছি। যদি কেউ শিয়া তাফসীর গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান পেতে চান তাহলে আল্লামা শেইখ আগা বুযুরগে তেহরানী রচিত ‘ আয যারবিয়া ইলা তাসানিফুশ শিয়া ’ নামক গ্রন্থটি দেখতে পারেন।
ওপরে আমরা নমুনাস্বরূপ যে সকল তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি তা হতে স্পষ্ট ,প্রসিদ্ধ সকল শিয়া তাফসীর গ্রন্থই হয় ইরানীদের দ্বারা রচিত হয়েছে নতুবা আরব বংশোদ্ভূত কোন ইরানী বা শিয়া যাঁরা ইরানে বসবাস করতেন তাঁরা লিখেছেন।
আহলে সুন্নাতের তাফসীর গ্রন্থসমূহ :
1. জামেউল বায়ান ফি তাফসীরিল কোরআন: এই তাফসীর গ্রন্থটি ‘ তাফসীরে তাবারী ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং এর রচয়িতা হলেন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ,মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তাবারী। তাবারী আহলে সুন্নাতের প্রথম সারির আলেমগণের একজন। তিনি তাঁর সময়ের অধিকাংশ ইসলামী জ্ঞানের পণ্ডিত ছিলেন ও এ ক্ষেত্রে অন্যদের পুরোধা হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাবারী প্রথম জীবনে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলেও পরবর্তী জীবনে স্বতন্ত্র ফিকাহর প্রবর্তন করেন এবং চার মাযহাবের কোন ইমামেরই অনুসরণ হতে বিরত হন। তাঁর মাযহাব কিছুদিন পর বিলুপ্ত হয়। ইনবুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে বেশ কিছু ফকীহর নাম বলেছেন যাঁরা তাবারী ফিকাহর অনুসরণ করতেন।
তিনি ইরানের মাযেনদারানের আমুলের অধিবাসী ছিলেন । তিনি 224 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 310 হিজরীতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাফসীরে তাবারী প্রথম মিশরে মুদ্রিত হয়। তাফসীরটি সামানী শাসক নূহ ইবনে মনসুরের নির্দেশে তাঁর আরব বংশোদ্ভূত মন্ত্রী বালাআমী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। তাবারীর ফার্সী অনূদিত তাফসীরটি সম্প্রতি তেহরান হতে মুদ্রিত হয়েছে।
2. কাশশাফ: আহলে সুন্নাতের তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ তাফসীর। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বিশেষত অলংকারশাস্ত্রের দিক দিয়ে তাফসীরটি অনন্য। এ তাফসীরের রচয়িতা হলেন আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর যামাখশারী খাওয়ারেজমী যিনি জারুল্লাহ্ উপাধি লাভ করেছিলেন । যামাখশারী ইসলামের প্রথম সারির আলেমদের একজন। তিনি সাহিত্য ,হাদীস ও উপদেশমূলক অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যদিও তিনি ইরানের উত্তরাঞ্চলের তীব্র শীত প্রধান অঞ্চল খাওয়ারেজমের অধিবাসী তদুপরি দীর্ঘদিন মক্কায় বসবাস করেন ও মক্কার তীব্র উষ্ণতা সহ্য করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর গৃহের সান্নিধ্য নৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন কাবাগৃহের নিকট ছিলেন সেহেতু ‘ আল্লাহর প্রতিবেশী ’ বা ‘ জারুল্লাহ্ ’ উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্ভবত তিনি সেখানে অবস্থানকালেই তাফসীরে কাশশাফ রচনা করেন। যামাখশারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ কাশশাফের 3য় খণ্ডে সূরা আনকাবুতের 56 নং আয়াতيا عبادي الّذين آمنوا إنّ أرضي واسعة فإيّي فاعبدون - “ হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব ,তোমরা আমারই ইবাদত কর ” -এর ব্যাখ্যা দান করে বলেছেন ,মুমিনদের অবশ্যই ইবাদত ও দীনকে রক্ষার স্বার্থে সবচেয়ে উপযোগী ভূমি নির্বাচন করা উচিত। অতঃপর তিনি বলেছেন ,
“ আমার প্রাণের শপথ! স্থানসমূহের মধ্যে দৃষ্টিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা যেমন পরীক্ষা করে দেখেছি আমাদের পূর্ববর্তিগণও পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ,আল্লাহর হারাম (কাবা ঘর) ও এর নিকটবর্তী থাকার প্রভাব খুবই বেশি । বিশেষত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ,চিন্তার স্থিরতা ও মনোযোগ এবং আত্মিক পরিতৃপ্তিতে...। ”
যামাখশারী এরপর শীতকালে জ্ঞানসংশ্লিষ্ট কোন এক কাজের উদ্দেশ্যে খাওয়ারেজমে প্রত্যাবর্তন করেন ও দুর্ভাগ্যক্রমে এক পা হারান। কিন্তু এ অবস্থায়ই ক্রাচে ভর করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মক্কায় পৌঁছান ও কয়েক বছর কাবার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। যামাখশারী 467 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 538 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. তাফসীরে কাবীর বা মাফাতিহুল গাইব: এ তাফসীর গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আলী কর্তৃক রচিত। তিনি ফাখরে রাযী নামে প্রসিদ্ধ।
ফাখরে রাযী ইসলামের প্রসিদ্ধ আলেমদের অন্যতম। তাঁর তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন মত শিয়া-সুন্নী সকলের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি মাযেনদারানে জন্মগ্রহণ এবং পরবর্তীতে রেই শহরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি হেরাত ও খাওয়ারেজমেও গিয়েছিলেন। জীবদ্দশায়ই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। রাযী 543 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 60 হিজরীতে হেরাতে ইন্তেকাল করেন।
4. গারাইবুল কোরআন: এই তাফসীরটি তাফসীরে নিশাবুরী নামে প্রসিদ্ধ এবং আহলে সুন্নাতের প্রথম সারির তাফসীরসমূহের অন্যতম। হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন নিযামে নিশাবুরী তাফসীরটি রচনা করেন। নিযাম কোমের অধিবাসী হলেও নিশাবুরে বাস করতেন। তিনি পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 730 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. কাশফুল আসরার: দশ খণ্ডের এ তাফসীরটি ফার্সী ভাষায় লিখিত। কয়েক বছর পূর্বে তেহরানে এটি মুদ্রিত হয়েছে। তাফসীরটি আবুল ফাযল রশীদ উদ্দিন মাইবাদী ইয়াযদী কর্তৃক রচিত। তিনি পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ হতে ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের নিকট তাফসীরটি সমাদৃত হচ্ছে।
6. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাভীল: এ তাফসীরটি তাফসীরে বাইদাভী নামে প্রসিদ্ধ। এটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে আহমাদ কর্তৃক রচিত যিনি ইরানের বাইদার (বাইযা) অধিবাসী ও সেখানকার কাজী (বিচারক) ছিলেন। তাঁর তাফসীরটি তাফসীরে কাবীর ও কাশশাফের সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে রচিত। মরহুম ফাইয কাশানী তাঁর তাফসীরে সাফীতে এ তাফসীর গ্রন্থ হতে সাহায্য নিয়েছেন। মরহুম শেখ বাহায়ীও এই তাফসীরটির ওপর টীকা লিখেছেন। বাইদ্বাভী আল্লামা হিল্লী ও বিশিষ্ট গবেষক নাসিরুদ্দীন তুসীর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সপ্তম হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে মৃত্যুবরণ করেন।
7. তাফসীরে ইবনে কাসির: এটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে কাসির কর্তৃক প্রণীত যিনি তাঁর ‘ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ’ নামক ইতিহাস গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর উপনাম হলো আবুল ফিদা। তিনি কোরেশ বংশোদ্ভূত ,ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ও সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি 774 হিজরীতে মারা যান। তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি কায়রো হতে প্রকাশিত হয়েছে।
8. দুররুল মানসুর: তাফসীরটি ইসলামের সবচেয়ে জ্ঞানী আলেমদের অন্যতম ও সর্বাধিক গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী কর্তৃক রচিত। তাঁর কিছু গ্রন্থ খুবই মুল্যবান যেমন , ‘ আল ইতিকান ফি উলুমিল কোরআন ’ । দুররুল মনসুর একটি হাদীসনির্ভর তাফসীর অর্থাৎ আয়াতসমূহকে হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ দৃষ্টিতে তাফসীরটি আহলে সুন্নাতের অনন্য একটি তাফসীর। দুররুল মানসুর হাদীসনির্ভর তাফসীরের দৃষ্টিকোণ হতে শিয়াদের তাফসীরে বুরহানের অনুরূপ।
সুয়ূতী মিশরের অধিবাসী। ‘ রাইহানুতুল আদাব ’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের 148 পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে যে ,তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে কোরআন হেফয করেছিলেন। একই গ্রন্থে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা উনআশি বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যু 910 অথবা 911 হিজরীতে।
9. তাফসীরে জালালাইন: এ তাফসীরটি দু ’ ব্যক্তির দ্বারা লিখিত। সূরা ফাতেহা হতে সূরা কাহাফ পর্যন্ত (কোরআনের প্রায় অর্ধাংশ) ইয়েমেনের বিশিষ্ট শাফেয়ী আলেম জালালউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম মাহাল্লী কর্তৃক রচিত। তিনি 864 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করলে কোরআনের পূর্ণ তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী আল্লামা মাহাল্লাীর অনুসৃত পথেই কোরআনের বাকী অংশ অর্থাৎ সূরা কাহাফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত তাফসীর রচনা পূর্ণ করেন। এ কারণেই তাফসীরটি ‘ তাফসীরে জালালাইন ’ নামে পরিচিত হয়।
‘ রাইহানুল আদাব ’ গ্রন্থের রচয়িতার বর্ণনা মতে এ তাফসীরটি ভারত ,ইরান ও মিশরে কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে।
10. তাফসীরে কুরতুবী: এ গ্রন্থটি আবু বকর সায়েনউদ্দীন ইয়াহিয়া ইবনে সা ’ দুন আন্দালুসী কর্তৃক রচিত। তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ,মুহাদ্দিস ,ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ হিসেবে অন্যদের অনুসরণীয় ছিলেন । কুরতুবী স্পেনের (আন্দালুস) অধিবাসী ছিলেন ও 567 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
11. এরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযাইয়াযল কোরআনুল কারিম (তাফসীরে আবুস সাউদ নামে প্রসিদ্ধ): এটি আবুস সাউদ কর্তৃক রচিত যিনি দশম হিজরী শতাব্দীর উসমানী আলেমদের একজন। সুলতান দ্বিতীয় বাইজিদ এ তাফসীরের কারণে তাঁকে সম্মানিত করেন।
তিনি 962 হিজরীতে উসমানী খেলাফতের প্রধান বিচারক ও মুফতী হিসেবে শাইখুল ইসলাম খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর তাফসীরটি কায়রো হতে পুনঃপুন মুদ্রিত হয়েছে। আমি এ তাফসীরটি দেখিনি তবে আমাদের সমকালীন প্রথম সারির অনেক শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ এ তাফসীরটির মূল্য দেন। আবুস সাউদ 982 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
12. রূহুল বায়ান: এ তাফসীরটি আরবী-ফারসী মিশ্রিত। প্রচুর ফার্সী এরফানী কবিতা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। উসমানী আলেমদের অন্যতম শেখ ইসমাঈল হাককী তাফসীরটি লিখেছেন। তিনি ইস্তাম্বুলে দীনী শিক্ষা ও ওয়াজ মাহফিল চালাতেন। অতঃপর তুরস্কের অপর শহর বুরুসায় যান। তিনি সুফী ধারার একজন আলেম ছিলেন এবং তাঁর তাফসীরেও এর প্রভাব রয়েছে। সুফী বিশ্বাসের কারণে তিনি তাঁর সমকালীন অনেকের দ্বারাই মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি 1127 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
13. রূহুল মায়ানী: সাইয়্যেদ মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ্ বাগদাদী হাসানী হুসেইনী এ তাফসীরটি লিখেন। তিনি আলুসী নামে প্রসিদ্ধ। আলুসী শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলেও অনেক বিষয়েই হানাফী ফিকাহর অনুসরণ করতেন। তিনি হযরত আলী (আ.)-এর প্রশংসায় আবদুল বাকী মৌসেলী রচিত কাসীদায়ে আইনিয়ার ব্যাখ্যা লিখেন। এই কাসীদাটি প্রসিদ্ধ আলেম সাইয়্যেদ কাযিম রাশতীও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাসীদাগ্রন্থটি ‘ শারহুল কাসীদা ’ নামে পরিচিত। আলুসী ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। আলুস ইরাকের একটি স্থান যা ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে অবস্থিত। আলুসী 1270 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
14. ফাতহুল কাদীর: এ তাফসীরটি মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ শাওকানী ইয়ামানী রচিত। শাওকানী ইয়েমেনের সানআ শহরে বড় হয়েছেন এবং সেখানেই শিক্ষা ও ফতোয়া দান শুরু করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থের নাম ‘ নাইলুল আওতার মিন আসরারে মুনতাকাল আখবার ’ । তাঁর প্রসিদ্ধি এ গ্রন্থের কারণেই। শাওকানী 1250 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ওপরে যে চৌদ্দটি তাফসীরের নাম উল্লেখ করেছি সম্ভবত এগুলো তেরশ ’ শতাব্দী পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। চৌদ্দশ ’ শতাব্দীতেও তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অনেক তাফসীর রচিত হয়েছে। আমরা এখানে তার উল্লেখ হতে বিরত থাকছি। উপরোক্ত চৌদ্দটি তাফসীরের মধ্যে ছয়টির রচয়িতা হলেন ইরানী। ইরানীদের রচিত তাফসীরগুলোর কয়েকটি প্রথম সারির এবং এর অধিকাংশই সপ্তম হিজরী শতাব্দীর পূর্বে রচিত। এ চৌদ্দজনের দু ’ জন ইয়েমেনের ,দু ’ জন উসমানী সাম্রাজ্যভুক্ত অংশের ,একজন স্পেনের ,একজন সিরীয় ,একজন মিসরীয় ও একজন ইরাকী।
সুতরং দেখা যাচ্ছে তাফসীর ও কেরাআতশাস্ত্রে ইরানীদের প্রাধান্য ও মূল্যবান অবদান রয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ইরানী মুসলমানগণ অন্যদের চেয়ে অধিক ঈমান ,ইখলাস ,একাগ্রতা ও আগ্রহ পোষণ করেছে।
হাদীসশাস্ত্র
ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইরানীদের অবদানের অন্যতম ক্ষেত্র হলো হাদীসশাস্ত্র অর্থাৎ রাসূল (সা.) ও পবিত্র ইমামগণের মূল্যবান বাণী শ্রবণ ,লিখন ,মুখস্থকরণ ও সংকলনশাস্ত্র।
তাফসীরের ন্যায় হাদীসশাস্ত্রকেও শিয়া ও সুন্নী এ দু ’ শাখায় বিভক্ত করা যায়। হাদীস শিক্ষা ,বর্ণনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য প্রধান প্রেরণাদায়ক উপাদান ছিল প্রথমত ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের হাদীসের প্রতি মুখাপেক্ষিতা ;দ্বিতীয়ত সুন্নী ও শিয়া উভয় সূত্রে হাদীস লিখন ও সংকলনে রাসূলের পুনঃপুন তাকিদ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্ণনায় উদ্বুদ্ধকরণ। এ কারণেই ইসলামের প্রথম যুগ হতেই মুসলমানদের মধ্যে হাদীস সংকলন ও বর্ণনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটার পর সাহাবীরা তাদের কাছে রাসূলের নিকট হতে সরাসরি হাদীস শ্রবণকারী হিসেবে বেশ গুরুত্ব পান। আগ্রহী মুসলমানগণ সাহাবী বা তাবেয়ীদের নিকট হতে হাদীস শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় এক শহর হতে অন্য শহর বা অঞ্চলে সফর করতেন। কখনও কখনও একটি হাদীসের বিশ্বস্ততা যাচাই বা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী হতে হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে তারা শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট মুহাদ্দিসের নিকট পৌঁছতেন ও তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করে লিখে নিতেন।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“ মুসলমানরা কোরআনের অর্থ অনুধাবনের জন্য রাসূলের হাদীসের মুখাপেক্ষিতা অনুভব করল। এতে করে কোরআনকে অধিকতর ভালভাবে বোঝা সম্ভব হতো । অবশ্য নবীর হাদীসসমূহ সাহাবীদের নিকট হতে শুনত ,কারণ সাহাবীরা নবীর নিকট হতে হাদীস সরাসরি শুনে মুখস্থ করতেন। তাই মুসলমানরা হাদীস বুঝার জন্য সাহাবীদের শরণাপন্ন হতো। মুসলমানরা তাদের ভূমির সম্প্রসারণে রত হলে মুহাজিরদের প্রধান হিসেবে সাহাবীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ কারণেই যে কেউ হাদীস শ্রবণের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে দেশের পর দেশ অতিক্রম করে বিশেষ সাহাবীর নিকট পৌঁছত। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি হাদীস শুধু একজন সাহাবীর নিকটই শোনা যেত এবং অন্যরা তা জানতেন না। তাই যদি কেউ হাদীস শিক্ষা লাভ করতে চাইতেন তাহলে বাধ্য হয়ে মক্কা ,মদীনা ,কুফা ,বসরা ,রেই বা অন্য কোন শহরে যেতেন এবং যেখান থেকেই হোক তা শিক্ষা নিতেন। জ্ঞানান্বেষণে সফর হলো এটি যা মুসলমানরা পালন করত। ” 263
নবীর হাদীসসমূহ শ্রবণ ,বর্ণনা ও সংকলনের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ স্বয়ং রাসূলের জীবদ্দশায়ই সৃষ্টি হয়। বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যেমন নকল পণ্যে বাজার ছেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনি তাঁর উপস্থিতির যুগেই দুর্বল ঈমানের কিছু লোক তাঁর নামে হাদীস বর্ণনা করা শুরু করে। তাই তিনি নিজেই তা খণ্ডনের জিহাদে অবতীর্ণ হন এবং স্বতন্ত্র এক খুতবায় মিথ্যাবাদীদের উৎপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন ও হাদীসকে যাচাইয়ের জন্য মৌলিক মানদণ্ড পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রতি আরোপিত হাদীসকে কোরআনের সঙ্গে তুলনা (কোরআনের মানদণ্ডে যাচাইয়ের) করে বিশুদ্ধতা যাচাই করতে নির্দেশ দেন। হাদীস শ্রবণ ,লিপিবদ্ধকরণ ও বর্ণনার বিষয়টি সুন্নী ও শিয়া উভয়ের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও প্রথম হিজরী শতাব্দীতে এ ক্ষেত্রে সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পার্থক্যটি হলো আহলে সুন্নাত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ও কোন কোন সাহাবীর মতের অনুসরণে এ শতাব্দীতে হাদীস লিখনকে মাকরুহ মনে করতেন এ কারণে যে ,হাদীস কোরআনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে ও কোরআনের গুরুত্ব কমে হাদীসের গুরুত্ব বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে। এর বিপরীতে নবীর আহলে বাইতের অনুসারীরা প্রথম হতেই হাদীস শ্রবণ ,লিখন ও বর্ণনার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং তা সংকলন ও সংরক্ষণের বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন।
আহলে সুন্নাত প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ বছরে এই ভুলের বিষয়ে সচেতন হয় ও উমাইয়্যা খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ যিনি মাতৃকুলের দিক হতে খলীফা হযরত উমরের বংশধর এবং একজন দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব তিনি এ ভুলের অপনোদন ঘটান। তাই শিয়ারা আহলে সুন্নাত হতে হাদীস সংকলনে একশ ’ বছর এগিয়ে ছিল।
বিশিষ্ট গবেষক ,পণ্ডিত ও আলেম আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর তাঁর ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ নামক মূল্যবান গ্রন্থে ‘ সহীহ মুসলিম ’ ও ইবনে হাজারের ‘ ফাতহুল বারী ’ হতে বর্ণনা করেছেন ,
“ সাহাবীরা হাদীস লিখনের ক্ষেত্রে মতদ্বৈততা পোষণ করতেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ,আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ,আবু সাঈদ খুদরী এবং আরো কয়েকজন সাহাবী হাদীস লিখনকে মাকরুহ মনে করতেন। কিন্তু হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ,আনাস ইবনে মালেক ও অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এ কারণেই হযরত আলীর অনুসারীরা ইসলামের প্রথম যুগ হতেই হাদীস লিপিবদ্ধকরণ শুরু করেন। অনেকেই হযরত উমরের অনুসরণে তা হতে বিরত থাকেন। প্রায় একশ ’ বছর এ অবস্থা অব্যাহত থাকার পর দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথম বছর হাদীস সংকলনে ইজমা স্থাপিত হয়। ” 264
শিয়াদের প্রথম হাদীস গ্রন্থটি হযরত আলীর হাতে লিখিত যা নবীর আহলে বাইতের ইমামদের নিকট বিদ্যমান ছিল এবং তাঁরা কখনও কখনও তা অন্যদের দেখিয়েছেন বা তা হতে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ,হযরত আলীর লিখিত গ্রন্থে এমনটি বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীস গ্রন্থটি ‘ মুসহাফে ফাতিমা (আ.) ’ নামে প্রসিদ্ধ।
এ দু ’ গ্রন্থ বাদ দিলে প্রথম হাদীস গ্রন্থ রাসূলের আযাদকৃত দাস আবু রাফের লিখিত এবং এতে ধর্মীয় বিধিবিধান ও বিচার বিষয়ক বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু রাফে একজন মিশরীয় (কিবতী) দাস যাঁকে রাসূল মুক্ত করে দেন। তাঁর দু ’ পুত্র উবাইদুল্লাহ্ ও আলী ,হযরত আলীর উত্তম অনুসারী ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফের নাম হযরত আলীর লিপিকার অথবা বায়তুল মালের রক্ষক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। শিয়া আলেমদের মধ্যে নাজ্জাশী তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে তাঁকে প্রথম শিয়া লেখক বলেছেন।265
আবু রাফের পর হযরত সালমান ফারসী শিয়া হাদীস লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একজন রোমীয় পাদ্রী মদীনায় অনুসন্ধানের জন্য আসলে হযরত সালমান তাঁকে নবীর কিছু হাদীস ব্যাখ্যা করে শোনান। এটি তিনি তাঁর লিখিত সংকলন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
হযরত সালমানের পর হযরত আবু যার গিফারী ,আসবাগ ইবনে নাবাতা ও অন্যান্যদের নাম আসে। হযরত আলীর সাহাবীদের মধ্যে সালিম ইবনে কাইস হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন যা সম্প্রতি ছাপানো হয়েছে।
এর পরবর্তী স্তরের শিয়াদের নিকট হতে যে গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান তা হলো ‘ সহীফায়ে সাজ্জাদিয়া ’ । এটি ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর দোয়ার সংকলন। ইমাম সাজ্জাদ প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ দশকে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এ দোয়ার গ্রন্থটি মুহাম্মদ (সা.)-এর ‘ আহলে বাইতের যাবুর ’ নামে অভিহিত। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষার্ধে এটি সংকলিত হয়। ইতোপূর্বে তা শুধু পঠিত ও বর্ণিত হতো।
দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক (আ.)-এর সময়কালে শিয়াগণ মোটামুটি স্বাধীন ছিল এবং এ সময়কাল হাদীস লিখন ,বর্ণনা ও সংকলনের সুবর্ণ যুগ ছিল। ইমাম সাদিকের নিকট চার হাজার ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করতেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম সাদিক ও ইমাম কাযিম (আ.)-এর শিষ্যগণ চারশ ’ হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন যা ‘ উসূলে আরবায়া মিয়াতা ’ নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থগুলোর রচয়িতাগণ বিভিন্ন জাতির।
তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথমদিকে ‘ জাওয়ামে হাদীস ’ গ্রন্থ রচনা ও সংকলন শুরু হয়। বর্তমানে সুন্নী ও শিয়াদের মাঝে প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ ‘ জাওয়ামে হাদীস ’ ।266 এ সময়েই ইরানীরা ইসলামের প্রতি তাদের অবদান ও নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে।
বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান ইরানী হাদীসশাস্ত্রবিদগণের নাম এখানে উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এ জন্য কয়েক খণ্ড বই রচনার প্রয়োজন। এখানে আমরা শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করব যা হতে স্পষ্ট হবে ,সুন্নী ও শিয়া ‘ জাওয়ামে হাদীস ’ লেখকগণের অধিকাংশই ইরানী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে শিয়া ‘ জাওয়ামে হাদীস ’ গ্রন্থ দিয়ে শুরু করছি।
1. আল কাফি: এ হাদীস গ্রন্থটি সিকাতুল ইসলাম শাইখুল মুহাদ্দিসীন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনী রাযী রচিত। এ বিখ্যাত ব্যক্তি তেহরানের নিকটবর্তী রেই শহরের পাশ্ববর্তী কুলাইনের অধিবাসী। তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য শিয়া মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াকুব ও মামা আ ’ লান কুলাইনে বসবাস করতেন (ও মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন)।
তাই তিনি শিশুকাল হতেই হাদীসের সঙ্গে পরিচিত হন ও হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। অতঃপর তিনি রেই শহরে যান। কুলাইনী সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা হাদীস শিক্ষার জন্য প্রচুর সফর করেছেন। তিনি হাদীসের অর্থ অনুধাবন ,হাদীস সংকলন ও প্রসিদ্ধ হাদীসবিদদের নিকট শিক্ষা লাভের জন্য সফর করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ বিশ বছর বাগদাদে কাটান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এ সময়েই তিনি ‘ আল কাফি ’ গ্রন্থটি সংকলন করেন।
আল কাফি শিয়াদের একটি সামগ্রিক হাদীস গ্রন্থ যাতে মৌল বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা হতে চরিত্র ও ধর্মীয় বিধানগত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থে ষোল হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে এবং এটি শিয়াদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। কুলাইনী 329 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মান লা ইয়াহদারুহুল ফাকীহ্: এটি রাইসুল মুহাদ্দিসিন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বাবভেই কুমী কর্তৃক সংকলিত। তিনি শেখ সাদুক নামে প্রসিদ্ধ এবং তাঁর পিতা শিয়াদের প্রথম সারির আলেমদের অন্যতম। শেখ সাদুকের পরিবার শিয়াদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পরিবার। সাদুক তিনশ ’ গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম ‘ মান লা ইয়াহদারুহুল ফাকীহ্ ’ (অর্থাৎ যার নিকট ফকীহ্ উপস্থিত নেই বা নিজে নিজে ফিকাহ্ শিক্ষা) মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযীর ‘ মান লা ইয়াহদারুত তাবিব ’ (যার নিকট চিকিৎসক উপস্থিত নেই বা নিজে নিজে চিকিৎসা) গ্রন্থ হতে নিয়েছেন। তাঁর এ হাদীস গ্রন্থে পাঁচ হাজার নয়শ ’ বিশটি হাদীস রয়েছে।
শেখ সাদুক হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য সফর করেছেন। যৌবনকালে বাগদাদে যান। সেখানে অনেক বড় বড় হাদীসবেত্তাও তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হন এবং তাঁরা তাঁকে বিশেষ সম্মান দিতেন। শেখ সাদুক বিশিষ্ট রেজালশাস্ত্রবিদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খোরাসানের বিভিন্ন শহরে ,যেমন নিশাবুর ,তুস ,সারাখশ ,মারভ ,বুখারা ,ফারগানেহ প্রভৃতি স্থানে যান। তিনি তাঁর ‘ মান লা ইয়াহদারুহুল ফাকীহ্ ’ গ্রন্থের ভূমিকায় এ সফর সম্পর্কে বলেছেন।
শেখ সাদুক 381 হিজরীতে মারা যান। রেই শহরে হযরত শাহ আবদুল আযিম (রহ.)-এর কবরের নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। স্থানটি এখন তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ।
3. তাহযীবুল আহকাম: শাইখুত তায়িফা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আত তুসী এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে মুফাসসিরদের নামের তালিকায় এ বিরল প্রতিভাধরের বিষয়ে বলেছি। শেখ তুসী ইসলামী জ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় ,যেমন সাহিত্য ,ব্যাকরণ ,কালামশাস্ত্র ,তাফসীর ,ফিকাহ্ ,হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি ‘ মাবসুত ’ নামক ফিকাহ্ গ্রন্থটি রচনা করে ফিকাহ্শাস্ত্রকে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়েছেন। শেখ তুসী ‘ তাওযীবুল আহকাম ’ -এ ধর্মীয় বিধিবিধান (আহকাম) সম্পর্কিত তের হাজার পাঁচশ ’ নব্বইটি হাদীস সংকলন করেছেন।
4. ইসতিবসার: এটিও শাইখুত তায়িফা আবু জাফর তুসীর রচিত। এ গ্রন্থে পাঁচ হাজার পনরটি হাদীস রয়েছে। শেখ তুসী 460 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
উপরোক্ত চারটি গ্রন্থ শিয়াদের নিকট ‘ কুতুবে আরবায়া ’ নামে সুপরিচিত এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ বলে গৃহীত। এ গ্রন্থসমূহের তিনজন রচয়িতার নামই মুহাম্মদ এবং তাঁদের ডাক নাম ছিল আবু জাফর। তাঁরা ‘ মুহাম্মাদিন সালাসা মুতাকাদ্দিম ’ নামে প্রসিদ্ধ।
উপরোক্ত চারটি ছাড়াই অপর তিনটি জামে হাদীস গ্রন্থ শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। তা হলো :
1. বিহারুল আনওয়ার: এটি শাইখুল ইসলাম আল্লামাতুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ বাকের ইবনে মুহাম্মদ তাকী মাজলিসী রচিত। এটি সর্ববৃহৎ ,সামগ্রিক (বিষয়ভিত্তিতে) ও পূর্ণতম হাদীস গ্রন্থ। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন হাদীসসমূহকে এ গ্রন্থে সমন্বিত করা হয়েছে। এ হাদীস গ্রন্থটির রচনার পেছনে লেখকের মূল উদ্দেশ্যে ছিল যেন হাদীসসমূহ বিলুপ্ত না হয়। এ জন্য তিনি সহীহ ও ত্রুটিযুক্ত সকল হাদীসই এতে এনেছেন। আল্লামা মাজলিসী 1111 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. ওয়াফী: এটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ,আরেফ ও দার্শনিক মুহাম্মদ ইবনে মুরতাজা ফাইয কাশানী কর্তক রচিত। এ হাদীস গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ চার গ্রন্থের (কতুবে আরবায়া) একক সংকলন যাতে ঐ চার গ্রন্থের পুনারবৃত্তিসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। মোল্লা মুহসেন ফাইয কাশানী বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দু ’ শ ’ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 1191 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. ওয়াসায়েলুশ শিয়া: এ গ্রন্থটি স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশশামী যিনি হুররে আমেলী নামে প্রসিদ্ধ ,রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে ফিকাহ্গত বিষয়ের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে ফিকাহর বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হাদীসসমূহ স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আনার। এজন্য প্রতিটি হাদীসকে খণ্ডিত করে উপযোগী অধ্যায়ে খণ্ডিত অংশ আনা হয়েছে। হুররে আমেলী আল্লামা মাজলিসীর সমসাময়িক। তাই তাঁরা একে অপর হতে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। তিনি 114 হিজরীতে মাশহাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর ইমাম রেজা (আ.)-এর রওজার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত।
শেষোক্ত তিন মুহাদ্দিসের নামও মুহাম্মদ হওয়ার কারণে তাঁদের ‘ মুহাম্মাদিন সালাসায়ে মুতাআখখির ’ বলা হয়। এই সাতটি জামে হাদীস ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ‘ হাদীস সমগ্র ’ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে নুরিল্লাহ্ বাহরাইনীর ‘ আওয়ালেম ’ ,সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ শাব্বারের ‘ জামেউল আহকাম ’ এবং হাজী মির্জা হুসাইন নূরীর ‘ মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল ’ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত শেষোক্ত হাদীস গ্রন্থটি প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সংকলিত হলেও হাদীসবেত্তাদের নিকট বিশেষ স্থান লাভ করেছে।
তাই জানা গেল শিয়াদের প্রথম সারির (প্রসিদ্ধ) ছয়জন মুহাদ্দিসের পাঁচজন ইরানী ও একজন সিরিয়ার জাবালে আমেলের অধিবাসী এবং পরবর্তী স্তরের তিনজনের একজন হলেন ইরানী।
আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহ ও এগুলোর রচয়িতা
আহলে সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন তিনি হলেন আবদুল মালেক ইবনে জারিহ্। তিনি আরব নন ,তবে ইরানীও নন। তিনি 144 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
আহলে সুন্নাতের সর্বপ্রথম জামে হাদীস হলো মালেক ইবনে আনাসের ‘ মুয়াত্তা ’ যা এখনও বিদ্যমান। মালেক ইবনে আনাস চার মাযহাবের অন্যতম ইমাম।
আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থ ‘ সিহাহ সিত্তাহ্ ’ নামে পরিচিত। আমরা আহলে সুন্নাতের সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে ইরানীদের অবদানের উল্লেখের প্রয়োজনে এই ছয়টি হাদীস গ্রন্থের রচয়িতাদের পরিচয় দিচ্ছি :
1. সহীহ বুখারী: এ হাদীস গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী কর্তৃক রচিত। এটি আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। বুখারী 16 বছর ধরে গ্রন্থটিকে সংকলন করেন। ইবনে খাল্লেকান তাঁর ‘ ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান ’ গ্রন্থের 3য় খণ্ডের 330 পৃষ্ঠায় এবং মুহাদ্দিস কুমী তাঁর ‘ আল কুনী ওয়াল আলকাব ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ,বুখারী বলেছেন , “ যে কোন হাদীস লেখার পূর্বে আমি গোসল করে দু ’ রাকাত নামাজ পড়েছি। ” বুখারীর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা অনেকেই বলেছেন। বুখারী উজবেকিস্তানের বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংকলনের উদ্দেশ্যে খোরাসান ,ইরাক ,হেজায ,সিরিয়া ও মিশরে সফর করেছেন। তিনি 256 হিজরীতে সামারকান্দের খারতাঙ্গে ইন্তেকাল করেন।
2. সহীহ মুসলিম: মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাবুরী এ গ্রন্থের রচয়িতা। এ হাদীস গ্রন্থটি সহীহ বুখারীর পর আহলে সুন্নাতের নিকট সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। অবশ্য কেউ কেউ বুখারীর ওপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসলিম হাদীস সংগ্রহের লক্ষ্যে ইরাক ,হেজায ,মিশর ও সিরিয়ায় সফর করেছেন। তিনি নিশাবুরে কিছুদিন বুখারীর সান্নিধ্যেও ছিলেন। মুসলিম 261 হিজরীতে নিশাবুরের নাছরাবাদে মুত্যুবরণ করেন।
3. সুনানে আবু দাউদ: এ হাদীস গ্রন্থটি সুলাইমান ইবনে আশআস কর্তৃক সংকলিত। তিনি আবু দাউদ সাজেসতানী নামে প্রসিদ্ধ। আবু দাউদ ইরানের সিস্তানের অধিবাসী। তিনিও হাদীস সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। আবু দাউদ সম্ভবত আরব বংশোদ্ভূত ইরানী এবং আহমাদ ইবনে হাম্বলের সমসাময়িক। তিনি 275 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. জামে তিরমিযী: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী এ হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তিনি বুখারীর শিষ্য। তিনি উজবেকিস্তানের তিরমিযের অধিবাসী এবং 279 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. সুনানে নাসায়ী: এই হাদীস গ্রন্থটি আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে আলী ইবনে শুয়াইব নাসায়ী সংকলিত। তিনিও হাদীস সংগ্রহে অনেক সফর করেছেন। এরূপ এক সফরে তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণ করতে দেখেন। এ কারণে হযরত আলী ও রাসূলের আহলে বাইতের ফযিলত বর্ণনা করে ‘ খাসায়িছ ’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন যাতে তিনি আহমাদ ইবনে হাম্মলের মুসনাদ হতে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন। ইবনে খাল্লেকান বলেছেন , ‘ একবার দামেস্কে মুয়াবিয়ার ফযিলত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: মুয়াবিয়ার ফযিলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনা ছাড়া আর কিছু জানি না। নবী (সা.) একদিন মুয়াবিয়াকে পুনঃপুন ডেকে পাঠালেও তিনি আহাররত থাকায় আসেননি। রাসূল তখন তাঁর সম্পর্কে বলেন: “ আল্লাহ্ তার উদর কখনও পূর্ণ না করুন। ” তাঁর উমাইয়্যাবিদ্বেষী মনোভাব ও শিয়াদের প্রতি দুর্বলতার কারণে সিরিয়ার এক দল লোক তাঁকে বেদম প্রহার করে। এতে তিনি খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায়ই সিরিয়া হতে মক্কায় চলে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। নাসায়ী খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 303 হিজরীতে
ইন্তেকাল করেন।
6. সুনানে ইবনে মাজাহ: এ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা কাযভীনী। তিনি হাদীস সংকলনের জন্য সিরিয়া ,মিশর ,হেজায ও ইরাক সফর করেছেন এবং 273 হিজরীতে মত্যৃবরণ করেন।
ওপরে আমরা লক্ষ্য করেছি শিয়াদের নির্ভরযোগ্য চারটি হাদীস গ্রন্থের রচয়িতা যেমন ইরানী (প্রাচীন পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসী) তেমনি আহলে সুন্নাতের ছয়টি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের রচয়িতাও ইরানী অথবা আরব বংশোদ্ভূত ইরানী।
সিহাহ সিত্তাহ্ ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ,গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ রচয়িতা ও হাদীসের হাফিয ছিলেন এবং তাঁরা ইরানী ছিলেন। এখানে আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় তাঁদের নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।
ফিকাহ্শাস্ত্র
ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ফিকাহ্শাস্ত্র। ফিকাহ্শাস্ত্র হলো কোরআন ,সুন্নাত ,ইজমা ও আকলের সাহায্য নিয়ে ইসলামের বিধিবিধান উদ্ঘাটন করা। ফিকাহ্শাস্ত্র ইসলামের অভিমত সম্পর্কিত জ্ঞান যা ফকীহ্ কোরআন ও হাদীস হতে উদ্ঘাটন করে থাকেন। এ দৃষ্টিতে হাদীসশাস্ত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য রযেছে ,কারণ হাদীসশাস্ত্রে শুধু হাদীস মুখস্থ ও বর্ণিত হয়ে থাকে।
মুসলমানগণ প্রথম হিজরী শতাব্দী হতেই ইজতিহাদ শুরু করে। ইজতিহাদ ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বশেষ ধর্মের অপরিহার্য অংশ । যেহেতু একদিকে এ ধর্ম কোন জাতি ,বর্ণ বা ভূখণ্ডের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং অন্যদিকে সর্বশেষ দীন হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে সেহেতু মানব সভ্যতার সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে ও সকল পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য এ উপযোগী।
কেউ কেউ ধারণা করেন ইজতিহাদের বিষয়টি আহলে সুন্নাতের মধ্যে প্রথম হিজরী শতাব্দীতে শুরু হলেও শিয়াদের মধ্যে তা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। তাঁরা ফিকাহ্শাস্ত্রে ইজতিহাদের পথে অনুপ্রবেশে শিয়াদের বিলম্বের কারণ স্বয়ং আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের উপস্থিতি বলে মত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা ‘ ইজতিহাদ দার ইসলাম ’ এবং ‘ ইলহামী আয শাইখুত তায়িফা ’ শিরোনামের প্রবন্ধ দু ’ টিতে267 এ মতকে খণ্ডন করেছি। সার্বিক নির্দেশনা ও মৌলনীতির ভিত্তিতে বিশেষ বিষয় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া দানই হলো ইজতিহাদ। এ বিষয়টি ইসলামের প্রথম যুগ হতেই শিয়া ও সুন্নী উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। তবে ফিকাহর উৎস এবং কিয়াসের বৈধতার প্রশ্নে এই দু ’ ফিরকার মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে।
আহলে সুন্নাতের দাবি অনুযায়ী সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি ইজতিহাদ করেন তিনি হলেন রাসূল (সা.)-এর অন্যতম সাহাবী মায়ায ইবনে জাবাল যিনি রাসূলের পক্ষ হতে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মায়ায ইবনে জাবালের ইজতিহাদ সম্পর্কিত কাহিনীটি প্রসিদ্ধ।
আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর তাঁর ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ গ্রন্থে লিখেছেন , ‘ শিয়া ফিকাহর প্রথম গ্রন্থ হযরত আলী (আ.)-এর সময়ে তাঁর বায়তুল মাল রক্ষক উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে কর্তৃক লিখিত হয়। ’ আমরা ইতোপূর্বে হাদীসশাস্ত্রের আলোচনায় উবাইদুল্লাহ্ ও তাঁর পিতা আবি রাফের হাদীস সংকলনের কথা উল্লেখ করেছি। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে আহলে বাইতের ইমামদের সমকালীন শিয়া গ্রন্থ রচয়িতা ও তাঁদের রচিত ফিকাহ্ গ্রন্থের একটি তালিকা ‘ ফোকাহাউ শশিয়া ’ শিরোনামের আলোচনায় এনেছেন। ইমামদের সমকালীন শিয়া ফকীহ্দের মধ্যে ইরানীদের সংখ্যা স্বল্প।
মোটামুটিভাবে ইমামদের যুগ হতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত (সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত) সময়ে অধিকাংশ শিয়া ফকীহ্ অ-ইরানী ছিলেন। প্রথম যুগের শিয়া ফকীহ্গণ যাঁদের গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান ও ঐসব গ্রন্থ হতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মত বর্ণনা করা হয় তাঁদের অধিকাংশই অ-ইরানী।
প্রথম যুগের শিয়া ফকীহ্দের মধ্যে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে কুমী (প্রথম সাদুক) ,মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে বাবাভেই (দ্বিতীয় সাদুক) ,শেখ মুনতাজাবুদ্দীন রাযী (তিনিও হুসাইন ইবনে আলী ইবনে বাবাভেইয়ের বংশধর) ,শায়খুত তায়িফা আবু জাফর তুসী ,শেখ সালার ইবনে আবদুল আজিজ দাইলামী (মারাযিম গ্রন্থের রচয়িতা ,শেখ মুফিদ ও সাইয়্যেদ মুর্তাজার ছাত্র) , ‘ ওয়াসিলা ’ গ্রন্থের লেখক আবু হামযা তুসী ,বিশিষ্ট মুফাসসির আয়াশী সামারকান্দী (ইবনুন নাদিম তাঁর ফেহেরেস্ত গ্রন্থে ফিকাহ্শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের আলোচনায় তাঁর নাম অনেক বার উল্লেখ করেছেন ও খোরাসানে তাঁর রচিত গ্রন্থের আধিক্য ও প্রচলনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন) তৎকালীন ইরানী ফকীহ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
এদের বিপরীতে সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত অ-ইরানী শিয়া ফকীহ্দের মধ্যে রয়েছেন ইবনে জুনাইদ ,ইবনে আবি আকিল ,শেখ মুফিদ ,সাইয়্যেদ মুর্তাজা আলামুল হুদা ,কাযী আবদুল আজিজ ইবনে বাররাজ ,আবু সালাহ্ হালাবী ,আবুল মাকারেম ইবনে যাহরা ,ইবনে ইদরিস হিল্লী ,মুহাক্কেক হিল্লী ,আল্লামা হিল্লীসহ অন্যান্যরা । তৎকালীন সময়ে অ-ইরানীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ হলো ইরানে সে সময় শিয়া অত্যন্ত সংখ্যালঘু ছিল। তাই ইরাক ,হালাব ,লেবানন ও অন্যান্য স্থানে ইরানের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিয়া ছিল এবং তাদের অবস্থাও সুবিধাজনক ছিল।
সপ্তম হিজরী শতাব্দীর পর হতে বিশেষত গত চারশ ’ বছরে শিয়া ফকীহ্গণের মধ্যে ইরানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন যদিও এ সময়ে আরবদের মাঝে স্বনামধন্য ও বিশিষ্ট ফকীহর আবির্ভাব ঘটেছে। তন্মধ্যে শেখ জাফর কাশেফুল গেতা এবং জাওয়াহেরুল কালাম গ্রন্থের লেখক শেখ মুহাম্মদ হাসানের নাম উল্লেখযোগ্য।
এখানে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অন্তর্ধানের সময়কাল হতে এখন পর্যন্ত শিয়া ফিকাহ্ ও ফকীহ্দের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। এর ফলে শিয়া ফিকাহ্শাস্ত্রে ইরানের অবদানের মূল্যায়নের সাথে সাথে ইসলামী সংস্কৃতির এই দিকটি কিভাবে সহস্রাধিক বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে তা স্পষ্ট হবে। ফিকাহ্শাস্ত্র গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক হাজার একশ ’ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ এগার শতক ধরে ফিকাহ্শাস্ত্র মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাদান করা হচ্ছে ,শিক্ষকরা এ শাস্ত্রে ছাত্রদের প্রশিক্ষিত করে আসছেন ,সেই ছাত্ররাও আবার নতুন ছাত্রদের প্রশিক্ষিত করছেন। এভাবে তা অব্যাহত রয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত এবং শিক্ষক ,ছাত্র ও প্রশিক্ষণের এ ধারা কখনই থেমে থাকেনি।
তবে অন্যান্য জ্ঞান ,যেমন দর্শন ,যুক্তিবিদ্যা ,গণিতশাস্ত্র ,চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির ইতিহাস আরো প্রাচীন এবং এ সকল বিষয়ে অনেক পূর্বেই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তদুপরি এ সকল বিষয়ের কোনটিতেই সম্ভবত শিক্ষক ,ছাত্র ও প্রশিক্ষণের অবিচ্ছিন্ন যে ধারাটি ফিকাহ্শাস্ত্রে বিদ্যমান তা এভাবে ছিল না। একমাত্র ইসলামী বিশ্বে এরূপ একটি জ্ঞান এক হাজার বছরের অধিক সময় ধরে প্রাণবন্তভাবে কোন বিরতি ছাড়াই অব্যাহত রয়েছে। আমরা পরবর্তীতে অধিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের বিরতিহীন গতির বিষয়েও আলোচনা করব।
সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম মনীষিগণ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিক অবদান রেখেছেন তাঁদের নাম ও অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে লিখে রাখতেন। প্রথম এ রীতিটি হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রে শুরু হলেও পরবর্তীতে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও তা প্রচলিত হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। যেমন ফিকাহ্বিদদের সম্পর্কে আবু ইসাহাক সিরাজীর ‘ তাবাকাতুল ফোকাহা ’ ,চিকিৎসাবিদদের সম্পর্কে ইবনে আবি আছিবায়ার ‘ তাবাকাতুল আতেব্বাহ ’ ,আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে আবু আবদুর রহমানের ‘ তাবাকাতুল নাহুইয়ীন ’ এবং সুফীদের সম্পর্কে আবু আবদুর রহমান সালামীর ‘ তাবকাতুস সুফীইয়া ’ ইত্যাদি।
কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমার জানা মতে আহলে সুন্নাতের ফকীহ্দের সম্পর্কে গ্রন্থ রচিত হলেও শিয়া ফকীহ্দের সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই বিভিন্ন পর্যায়ের শিয়া ফকীহ্দের নাম জানতে হলে রেজালশাস্ত্র ও মাশায়েখগণের অনুমতিগ্রন্থে বর্ণিত হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের মাঝে অনুসন্ধান চালাতে হয়।
আমরা এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের শিয়া ফকীহ্দের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমরা কেবল বিশিষ্ট শিয়া ফকীহ্দের নাম তাঁদের গ্রন্থসহ উল্লেখ করব। এর মাধ্যমে বিভিন্ন
স্তরের ফকীহ্দেরও চেনা সম্ভব হবে।
আমরা শিয়া ফকীহ্দের ইতিহাস ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের (260-329 হিজরী) সময়কাল হতে শুরু করছি। দু ’ টি কারণে আমরা তা করছি: প্রথমত ইমাম মাহ্দীর স্বল্বকালীন অন্তর্ধানের পূর্ববর্তী সময়ে স্বয়ং আহলে বাইতের ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষিত শিষ্যদের অনেককেই মুজতাহিদ বা ফকীহ্ হিসেবে ফতোয়া দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেও স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা চান বা না চান ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে ইমামদের সরাসরি প্রভাব তাঁদের ওপর ছিল এবং জনসাধারণও পবিত্র ইমামগণের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হলে তাঁদের নিকট যেত। তবে প্রথমত তারা চেষ্টা করত স্বয়ং ইমামদের নিকট হতে ফতোয়া জানতে ,এমনকি ফকীহ্গণও যথাসম্ভব কষ্ট করে হলেও দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে ইমামদের নিকট পৌঁছে এ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান নিতেন। সুতরাং শিয়া ফিকাহর লিখিত রূপটি ইমাম মাহদীর স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের সময় হতে প্রচলন লাভ করেছে এবং এর পূর্বের ফকীহ্দের রচিত কোন গ্রন্থ এখন আমাদের হাতে নেই অথবা থাকলেও তা আমাদের জানা নেই।
কিন্তু আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের জীবদ্দশায়ও স্বনামধন্য শিয়া ফকীহ্গণ ছিলেন এবং অন্যান্য মাযহাবের তৎকালীন ফকীহ্গণের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করলে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইবনুন নাদিম তাঁর মূল্যবান ও বিশ্ব পরিচিত গ্রন্থ ‘ ফেহেরেস্ত ’ -এর (যা ফেহেরেস্তে ইবনুন নাদিম নামে প্রসিদ্ধ) একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে শিয়া ফকীহ্দের নিয়ে আলোচনা করেছেন । সেখানে তাঁদের নামের সঙ্গে তাঁদের রচিত হাদীস বা ফিকাহ্ গ্রন্থের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন ফিকাহ্শাস্ত্রে হুসাইন ইবনে সাঈদ আহওয়াযী ও তাঁর ভ্রাতার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন , “ ফিকাহ্ ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা তৎকালীন সময়ের আলেমদের গৌরব ছিলেন। ” আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী সম্পর্কে বলেছেন , “ প্রসিদ্ধ ফকীহ্দের একজন। ” মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে ওয়ালিদ কুমী সম্পর্কে বলেছেন , “ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিকাহ্ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ছিল। ” এ সমস্ত ফকীহর গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি অধ্যায়েই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোচনায় তাঁরা তদসংশ্লিষ্ট যে হাদীসের ওপর তাঁরা নির্ভর করে ফতোয়া দিয়েছেন তার উল্লেখ করতেন। তাই এ দৃষ্টিতে তাঁদের গ্রন্থসমূহ যেমন তাঁদের রচনা ছিল তেমনি হাদীস গ্রন্থ বলেও পরিগণিত হতো।
মুহাক্কেক হিল্লী তাঁর ‘ মুতাবার ’ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন , “ যেহেতু আমাদের ফকীহ্দের সংখ্যা অনেক এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর সে কারণে তাঁদের সকলের মত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই আমি গবেষণার ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ ও উত্তম মতসমূহই শুধু বর্ণনা করছি। এ ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রন্থে বর্ণিত যে মত প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিফলিত তা-ই গ্রহণ করেছি। পবিত্র ইমামদের সমকালীন ফকীহ্গণের মধ্যে যাঁদের নিকট হতে বর্ণনা করেছি তাঁরা হলেন হাসান ইবনে মাহবুব ,আহমাদ ইবনে আবি নাসর বাযানতী ,হুসাইন ইবনে সাঈদ আহওয়াযী ,ফাযল ইবনে শাজান নিশাবুরী ,ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান ও অন্যান্য। পরবর্তী পর্যায়ের ফকীহ্দের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে বাবাভেই কুমী (শেখ সাদুক) ,মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনী ,আলী ইবনে বাবাভেই কুমী ,আসকাফী ,ইবনে আবি আকিল ,শেখ মুফিদ ,সাইয়্যেদ মুরতাজা আলামুল হুদা ,শেখ তুসী প্রমুখ। শেষোক্ত ছয়জন মুফতী হিসেবে পরিগণিত।
মুহাক্কেক হিল্লী প্রথম সারির ব্যক্তিদের মুজতাহিদ বলে মনে করলেও ফতোয়া দানকারী ফকীহর অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁদের ইজতিহাদের ফল হলেও তা ফতোয়া আকারে বর্ণিত না হয়ে হাদীস গ্রন্থাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আমরা ইমাম মাহদীর স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের সমকালীন প্রথম সারির মুফতিগণের নাম উল্লেখ করব :
1. আলী ইবনে বাবাভেই কুমী (মৃত্যু 329 হিজরী ,কোমে সমাহিত): তিনি শেখ সাদুক অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বাবাভেই (যিনি রেই শহরে সমাহিত)-এর পিতা। পুত্র মুহাদ্দিস এবং পিতা ফকীহ্ ও মুফতী। এ পিতা-পুত্রকে ‘ সাদুকাইন ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।
2. আলী ইবনে বাবাভেই কুমীর সমসাময়িক বা কিছু পূর্বের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ হলেন আয়াশী সামারকান্দী যিনি তাঁর তাফসীরের জন্যও প্রসিদ্ধ। তিনি উঁচু স্তরের জ্ঞানী ছিলেন। যদিও তিনি মুফাসসির হিসেবে প্রসিদ্ধ তদুপরি প্রথম সারির ফকীহ্দেরও অন্তর্ভুক্ত। তিনি ফিকাহ্সহ বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ -এ বলেছেন , ‘ তাঁর গ্রন্থ খোরাসানে ব্যাপকভাবে পরিচিত হলেও ফিকাহর বিষয়ে কোথাও তাঁর মত উল্লিখিত হয়নি। সম্ভবত তাঁর ফিকাহ্ সম্পর্কিত গ্রন্থ কোন কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। ”
আয়াশী প্রথম জীবনে সুন্নী হলেও পরবর্তীতে শিয়া মাযহাব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে পর্যাপ্ত সম্পদ পান যার পুরোটাই গ্রন্থ রচনা ,সংকলন ,নকল ,ছাত্রদের শিক্ষা ,প্রশিক্ষণ ও ভাতার জন্য খরচ করেন।
অনেকে শেখ মুফিদের ফিকাহর শিক্ষক জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কৌলাভেইকে আলী ইবনে বাবাভেইয়ের সমকালীন মনে করে স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের সময়কার ফকীহ্ বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সা ’ দ ইবনে আবদুল্লাহ্ আশআরীর ছাত্র ও শেখ মুফিদের শিক্ষক এবং 367 বা 368 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন সেহেতু তাঁকে আলী ইবনে বাবাভেইয়ের সমসাময়িক বলা যায় না । অবশ্য তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে কৌলাভেইকে স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের যুগের আলেম বলা যায়।
দীর্ঘকালীন অন্তর্ধানের সময়কার ফকীহ্গণ
3. ইবনে আবি আকিল আম্মানী: তিনি ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। আম্মান ইয়েমেনের সমুদ্র তীরবর্তী একটি অঞ্চল। তিনি দীর্ঘকালীন অন্তর্ধানের শুরুর প্রাক্কালের একজন আলেম। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি।
বাহরুল উলুম তাঁকে জাফর ইবনে কৌলাভেইয়ের শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন যিনি শেখ মুফিদের শিক্ষক ছিলেন। ইবনে আবি আকিলের নাম ফিকাহ্শাস্ত্রে প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে।
4. ইবনে জুনাইদ আসকাফী: তিনিও শেখ মুফিদের অন্যতম শিক্ষক। তিনি 381 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। ইবনে জুনাইদ ও ইবনে আবি আকিলকে ফকীহ্গণ ‘ আল কাদিমাইন ’ বলে সম্বোধন করে থাকেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর মত প্রায়ই বর্ণিত হয়।
5. শেখ মুফিদ: তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নোমান। তিনি ফকীহ্ ও কালামশাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধের দ্বিতীয় আলোচনায় তাঁর নাম শিয়া কালামশাস্ত্রবিদদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন ও ‘ ইবনুল মুয়াল্লেম ’ নামে তাঁকে অভিহিত করেছেন। তিনি 336 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 413 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর গ্রন্থটি ‘ আল মুকান্নায়া ’ নামে প্রসিদ্ধ। শেখ মুফিদ শিয়া বিশ্বে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। শেখ মুফিদের জামাতা আবু ইয়ালী জাফরী বর্ণনা করেছেন ,শেখ মুফিদ রাত্রিতে খুব কম ঘুমাতেন। বাকী সময় ইবাদত ,নামাজ ,কোরআন তেলাওয়াত ,অধ্যয়ন বা লেখালেখির কাজে ব্যয় করতেন।
6. সাইয়্যেদ মুরতাজা: তিনি ‘ আলামুল হুদা ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 355 হিজরীতে জন্ম এবং 436 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা হিল্লী তাঁকে ইমামিয়া শিয়াদের শিক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন । বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ,যেমন সাহিত্য ,কালামশাস্ত্র এবং ফিকাহ্। তাঁর মতসমূহ ফকীহ্দের নিকট সম্মানার্হ। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ দু ’ টি গ্রন্থ হলো ‘ ইনতিছাব ’ ও ‘ জামালুল ইলম ওয়াল আমাল ’ । তিনি ও তাঁর ভ্রাতা সাইয়্যেদ রাযী পূর্ণাঙ্গ নাহজুল বালাগাহ্ শেখ মুফিদের নিকট শিক্ষা নিয়েছেন।
7. শেখ আবু জাফর তুসী: তিনি শাইখুত তায়িফা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইসলামী বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের অন্যতম। ফিকাহ্ ,উসূল ,হাদীস ,তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ও রিজালশাস্ত্রে তাঁর প্রচুর রচনা রয়েছে। তিনি খোরাসানের তুসের অধিবাসী।
শেখ তুসী 385 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 408 হিজরীতে (23 বছর বয়সে) তৎকালীন ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র বাগদাদে হিজরত করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত ইরাকেই ছিলেন। তাঁর শিক্ষক সাইয়্যেদ মুরতাজার ইন্তেকালের পর তিনি শিয়াদের জ্ঞান ও ফতোয়া দানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি শেখ মুফিদের নিকটও পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় শেখ মুফিদের ছাত্র সাইয়্যেদ মুরতাজার তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছেন ও তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করেছেন। তাঁর শিক্ষক সাইয়্যেদ মুরতাজা 436 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করার পরও তিনি 24 বছর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে 12 বছর বাগদাদে ছিলেন। কিন্তু বাগদাদে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে তাঁর গৃহে ও গ্রন্থাগারে হামলা হয়। ফলে তিনি বাগদাদ হতে নাজাফে হিজরত করেন এবং সেখানে দীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর নাজাফেই তিনি 460 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর নাজাফে অবস্থিত।
ফিকাহ্শাস্ত্রে শেখ তুসীর রচিত গ্রন্থের নাম ‘ আন নেহায়া ’ যা প্রাচীনকালে দীনী ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর রচিত অপর একটি গ্রন্থ হলো ‘ মাবসুত ’ । এ গ্রন্থটি ফিকাহ্শাস্ত্রকে নতুন অধ্যায় ও যুগে প্রবেশ করিয়েছে এবং তৎকালীন সময়ের শিয়া ফিকাহর সবচেয়ে ব্যাপক গ্রন্থ। ‘ খিলাফ ’ নামেও তাঁর একটি ফিকাহর গ্রন্থ রয়েছে যাতে আহলে সুন্নাত ও শিয়া উভয় মাযহাবের ফকীহ্দের মত সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ রয়েছে। এক শতাব্দী কাল পূর্বেও শিয়া আলেমগণ ‘ শেখের ফিকাহ্ ’ বলতে শেখ তুসীর ফিকাহ্ বুঝতেন। আর যদি ‘ শাইখানের ফিকাহ্ ’ বলতেন তবে শেখ মুফিদ ও শেখ তুসী বুঝা যেত। শিয়া ফিকাহ্শাস্ত্রের সব অধ্যায়েই যে সকল প্রসিদ্ধ ফকীহর নাম উচ্চারিত হয় শেখ তুসী তাঁদের অন্যতম। কয়েক শতাব্দী শেখ তুসীর বংশধারার বিভিন্ন ব্যক্তি ফকীহ্ ও আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র শেখ আবু আলী যিনি দ্বিতীয় মুফিদ নামে পরিচিত- তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্। ‘ মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ হলো ‘ আমালী ’ এবং তাঁর পিতার রচিত ‘ আন নেহায়া ’ গ্রন্থটিও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।268 ‘ লুলুউল বাহরাইন ’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে শেখ তুসীর কন্যারাও বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। শেখ আবু আলীর এক পুত্রের নাম শেখ আবুল হাসান মুহাম্মদ যিনি পিতার মৃত্যুর পর নাজাফের দীনী মাদ্রাসার প্রধান হন। ইবনে আম্মাদ হাম্বলী তাঁর ‘ শাযরাতুয যাহাব ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ এ মহৎ ব্যক্তির জীবদ্দশায় বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিয়া দীনী ছাত্ররা তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে আসতেন। তিনি একজন দুনিয়াবিমুখ ও খোদাভীরু আলেম ছিলেন। ’ 269 আম্মাদ তাবারী বলেছেন , ‘ যদি নবী ভিন্ন অন্য কারো ওপর দরুদ পড়া জায়েয হতো তবে আমি এ ব্যক্তির ওপর দরুদ পড়তাম। ’ শেখ আবুল হাসান মুহাম্মদ 540 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
8. কাজী আবদুল আজিজ হালাবী: তিনি ইবনুল বারাজ নামে প্রসিদ্ধ এবং সাইয়্যেদ মুরতাজা ও শেখ তুসীর শিষ্য। তিনি শেখ তুসীর পক্ষ হতে স্বীয় ভূমি সিরিয়ায় প্রেরিত হন। আবদুল আজিজ বিশ বছর সিরিয়ায় তারবেলেসে (ত্রিপোলী) বিচারক ছিলেন। তিনি 481 হিজরীতে মুত্যৃবরণ করেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ দু ’ টি গ্রন্থ হলো ‘ মুহাযযাব ’ ও ‘ জাওয়াহের ’ ।
9. শেখ আবুস সালাহ হালাবী: তিনি শামাতের অধিবাসী এবং সাইয়্যেদ মুরতাজা ও শেখ তুসীর ছাত্র। তিনি একশ ’ বছর জীবিত ছিলেন। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে তাঁকে সালার ইবনে আবদুল আজিজেরও ছাত্র হিসেক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এ বক্তব্যটি সঠিক হয় তবে তিনি তিন ব্যক্তির ছাত্র ছিলেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো কাফী। তিনি 447 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 447 হিজরীতে ইন্তেকাল করলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দু ’ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলা যায়। শহীদে সানী বলেছেন , “ তিনি হালাবে সাইয়্যেদ মুর্তাজার খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। ”
10. হামযা ইবনে আজিজ দাইলামী: তিনি সালার দাইলামী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 447 হিজরীতে মতান্তরে 463 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শেখ মুফিদ ও সাইয়্যেদ মুরতাজার ছাত্র ছিলেন। সালার ইরানের অধিবাসী ও তাবরীজের খসরুশাহে মারা যান। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ‘ মারাসিম ’ । যদিও তিনি শেখ তুসীর ছাত্র নন ;বরং সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব তদুপরি মুহাক্কেক হিল্লী তাঁর গ্রন্থের270 ভূমিকায় সালার ,ইবনুল বারাজ ও আবুস সালাহ এ তিনজন ব্যক্তিকে ‘ আতবাউস সালাসা ’ (তিন অনুসারী) নামে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ তাঁকে শেখ তুসীর অন্যতম অনুসারী বলেছেন। সম্ভবত তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য এটি যে ,উপরোক্ত তিন ব্যক্তি পূর্বোক্ত তিনজনের (শেখ মুফিদ ,সাইয়্যেদ মুর্তাজা ও শেখ তুসীর) অনুবর্তী।
11. সাইয়্যেদ আবুল মাকারেম ইবনে জুহরাহ: সাইয়্যেদ আবুল মাকারেম মধ্যবর্তী এক ব্যক্তির সূত্রে শেখ তুসীর পুত্র আবু আলী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ফিকাহ্শাস্ত্রে মধ্যবর্তী কয়েকজন শিক্ষকের মাধ্যমে শেখ তুসীর পরোক্ষ ছাত্র। তিনি সিরিয়ার হালাবের অধিবাসী ও 585 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হলো ‘ গানিয়াহ্ ’ । সেখানেই ফিকাহর পরিভাষায় ‘ হালাবীয়ান ’ বলা হয় তা ‘ আবুস সালাহ্ হালাবী ও ইবনে জুহরাহ হালাবী এ দু ’ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আর যদি ‘ হালাবীউন ’ বলা হয় তবে উপরোক্ত দু ’ ব্যক্তি ছাড়াও ইবনুল বারাজ হালাবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ‘ মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল ’ গ্রন্থে শেখ তুসীর পরিচিতি পর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে ,ইবনে জুহরাহ ইবনিল হুসাইনের (ইবনুল হাজেব হালাবী নামে প্রসিদ্ধ) নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ইবনে হাজেব এ গ্রন্থটি নাজাফে আবু আবদুল্লাহ্ যাইনুবাদীর নিকট ,তিনি তা শেখ রাশিদুদ্দীন আলী ইবনে সিরাক কুমী ও সাইয়্যেদ আবি হাশিম হুসাইনীর নিকট ,তাঁরা গ্রন্থটি শেখ আবদুল জাব্বার রাযীর নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শেখ আবদুল জাব্বার শেখ তুসীর ছাত্র ছিলেন। এই বর্ণনানুসারে ইবনে জুহরাহ মধ্যবর্তী চার ব্যক্তির সূত্রে শেখ তুসীর পরোক্ষ ছাত্র।
12. ইবনে হামযা তুসী: তিনি ইমাদউদ্দীন তুসী নামে পরিচিত। তিনি শেখ তুসীর ছাত্রদের ছাত্রের সারির একজন ফকীহ্। তবে কেউ কেউ তাঁকে আরো পরের বলেছেন। বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে। তাঁর মৃত্যুর বছর সঠিকভাবে জানা যায়নি। সম্ভবত ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি মারা যান। তিনি ইরানের খোরাসানের অধিবাসী। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর সুপরিচিত একটি গ্রন্থ হলো ‘ ওয়াসিলাহ্ ’ ।
13 ইবনে ইদরিসহিল্লী: তিনি শিয়া পণ্ডিত ও আলেমগণের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি আরব বংশোদ্ভূত। শেখ তুসী তাঁর মাতার পিতামহ। ইবনে ইদরিস স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর রক্তসম্পর্কীয় প্রপিতা শেখ তুসীর ভাবমূর্তিকেও ক্ষু ণ্ণ করেছেন ( তাঁর মতের তীব্র সমালোচনা করে ) । তিনি পূর্ববর্তী আলেমদের মতের আক্রমণাত্মক সমালোচনা করতেন। তিনি 598 হিজরীতে 55 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ সারাইর ’ । কথিত আছে ইবনে ইদরিস সাইয়্যেদ আবুল মাকারেম ইবনে জুহরার শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ইবনে ইদরিস তাঁর ‘ আল ওয়াদিয়া ’ গ্রন্থে ‘ আস সারাইর ’ গ্রন্থ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বুঝা যায় ইবনে জুহরাহ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন ও ফিকাহর কিছু বিষয়ে ইবনে জুহরার সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় ও সরাসরি আলোচনাই শুধু হয়েছে।
14. শেখ আবুল কাসেম জাফর ইবনে হাসান ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ হিল্লী (মুহাক্কেক হিল্লী নামে প্রসিদ্ধ): উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে ,যেমন মাআরিয ,মুতাবার ,আল মুখতাছার ,আন নাফে প্রভৃতি। মুহাক্কেক হিল্লী মধ্যবর্তী এক শিক্ষকের সূত্রে ইবনে জুহরাহ ও ইবনে ইদরিস হিল্লীর পরোক্ষ ছাত্র। ‘ আল কুনী ওয়াল আলকাব ’ গ্রন্থে ইবনে নামার জীবনী আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে , ‘ মুহাক্কেক কুরকী মুহাক্কেক হিল্লীর প্রশংসায় বলেছেন ,তিনি আহলে বাইতের ফিকার পণ্ডিতগণের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন মুহাম্মদ ইবনে নামায়ে হিল্লী ও ইবনে ইদরিস হিল্লী।
সম্ভবত মুহাক্কেক কারকীর এ কথার উদ্দেশ্য হলো ইবনে নামার শিক্ষক হলেন ইবনে ইদরিস হিল্লী এবং সেই সূত্রে তাঁকে তিনি ইবনে ইদরিসের পরোক্ষ ছাত্র বলেছেন। কারণ ইবনে ইদরিস 598 হিজরীতে মারা যান এবং মুহাক্কেক হিল্লী 676 হিজরীতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুহাক্কেকের পক্ষে ইবনে ইদরিসের ছাত্র হওয়া সম্ভব নয়। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে , ‘ মুহাক্কের হিল্লী তাঁর পিতা ,পিতামহ ,সাইয়্যেদ ফাখার ইবনে মায়াদ মুসাভী এবং ইবনে জুহরাহর নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইবনে জুহরার নিকট মুহাক্কেকের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিও সঠিক নয়। কারণ ইবনে জুহরা 865 হিজরীতে মারা যান। তাই নিশ্চিতভাবে তিনি ইবনে জুহরাহর ছাত্র ছিলেন না। তবে তাঁর পিতা ইবনে জুহরাহর ছাত্র হতে পারেন।
মুহাক্কেক হিল্লী আল্লামা হিল্লীর শিক্ষক ছিলেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে কাউকেই তাঁর ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় না। ফিকাহ্শাস্ত্রে ‘ মুহাক্কেক ’ পরিভাষাটি নাম হিসেবে শুধু তাঁর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী হিল্লায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ফিকাহর ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন। মুহাক্কেকের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ বিশেষত ‘ শারায়ে ’ নামক গ্রন্থটি দীনী ছাত্রদের পাঠ্য ছিল এবং এখনও আছে। অনেক ফকীহ্ই মুহাক্কেক হিল্লীর গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন অথবা তাতে টীকা সংযোজন করেছেন।
15. হাসান ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে মুতাহ্হারী হিল্লী (আল্লামা হিল্লী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি তৎকালীন সময়ের একজন বিরল প্রতিভা। তিনি ফিকাহ্ ,উসূল ,কালামশাস্ত্র ,যুক্তিবিদ্যা ,দর্শন ,রিজালশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক রচনা করেছেন। বর্তমানে তাঁর লেখা একশ ’ টি গ্রন্থ হস্তলিখিত অথবা ছাপানো অবস্থায় বিদ্যমান। ঐ গ্রন্থসমূহের কোন কোনটি যেমন ‘ তাযকেরাতুল ফোকাহা ’ তাঁর বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।
আল্লামা হিল্লীর ফিকাহ্ বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। যার অধিকাংশই পরবর্তী সময়ের ফকীহ্দের দ্বারা ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজিত হয়েছে। আল্লামা হিল্লীর প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থসমূহ হলো ইরশাদ ,তাবছেরাতুল মুতাআল্লেমীন ,কাওয়ায়েদ ,তাহরীর ,তাযকিরাতুল ফোকাহা ,মুখতালাফুশ শিয়া ও মুনতাহা। তিনি অনেকের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি ফিকাহ্শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর মামা মুহাক্কেক হিল্লীর নিকট অর্জন করেন। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিকাহ্সমূহ অধ্যয়ন করেন। আল্লামা হিল্লী 648 হিজরীতে জন্ম ও 726 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন ।
16. ফাখরুল মুহাক্কেকীন: তিনি আল্লামা হিল্লীর পুত্র। তিনি 682 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 771 সালে পৃথিবী হতে বিদায় নেন। আল্লামা হিল্লী তাঁর ‘ তাযকিরাতুল ফোকাহা ’ গ্রন্থের ভূমিকায় এবং ‘ কাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থে তাঁর এ পুত্রের প্রশংসা করেছেন। ‘ কাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থের শেষে তিনি এ আশা ব্যক্ত করেছেন ,তাঁর পুত্র তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে। ফাখরুল মুহাক্কেকীন ‘ ইয়াহুল ফাওয়াইদ ফি শারহি মুশকিলাতুল কাওয়ায়েদ ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর উপস্থাপিত মত পরবর্তী কালের ফকীহ্ ও আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
17. মুহাম্মদ ইবনে মাক্কী ( ‘ শহীদে আউয়াল ’ নামে প্রসিদ্ধ): তিনি ফাখরুল মুহাক্কেকীনের ছাত্র ও শিয়া ফকীহ্দের প্রথম সারির একজন অর্থাৎ মুহাক্কেক ও আল্লামা হিল্লীর সমপর্যায়ের। তিনি দক্ষিণ লেবাননের জাবালে আমেলের অধিবাসী। জাবালে আমেল শিয়াদের অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র। শহীদে আউয়াল 734 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 786 হিজরীতে মালেকী মাযহাবের এক আলেমের ফতোয়ার কারণে শহীদ হন। তিনি আল্লামা হিল্লীর ছাত্রগণের ছাত্র। শহীদে আউয়ালের প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থ হলো ‘ লোমআ ’ যা তিনি জেলখানায় বন্দী থাকাকালীন সময়ে (মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পরবর্তীতে) লিখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো দু ’ শতাব্দী পর তাঁর এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যিনি লিখেন তিনও তাঁর পরিণতি বরণ করে শহীদ হন ও ‘ শহীদে সানী ’ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
‘ শারহে লোমআ ’ শহীদ সানীর রচনা যা বর্তমানে ছাত্রদের ফিকাহর পাঠ্যগ্রন্থ। শহীদে আউয়ালের রচিত গ্রন্থসমূহ হলো দুরুস ,যিকরা ,বায়ান ,আলফিয়া ও কাওয়ায়েদ। তাঁর রচিত ফিকাহর সকল গ্রন্থই মূল্যবান। মুহাক্কেক হিল্লী এবং আল্লামা হিল্লীর ন্যায় তাঁর গ্রন্থসমূহেও পরবর্তী সময়ের আলেমদের দ্বারা ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজিত হয়েছে।
সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এ তিন ফকীহর (আল্লামা হিল্লী ,মুহাক্কেক হিল্লী ও শহীদে আউয়াল) গ্রন্থসমূহই শিয়া ফকীহ্দের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং এগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। অন্য কোন ফকীহর গ্রন্থের বিষয়ে এমনটি লক্ষ্য করা যায় না। এর পরবর্তী সময়ে কেবল শেখ মুর্তজা আনসারীর গ্রন্থের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে এবং এটি মাত্র শতাধিক বছর পূর্বের একটি গ্রন্থ।
শহীদ আউয়ালের পরিবারের সদস্যরা ফিকাহ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। এই পরিবারের সদস্যরা বংশ পরম্পরায় আলেম হিসেবে স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শহীদে আউয়ালের তিন পুত্রই স্বীকৃত ফকীহ্ ও আলেম ছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আলী ও কন্যা উম্মুল হাসানও ফিকাহ্শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারিনী ছিলেন। শহীদ তাঁর নিকট আগত নারীদের ফিকাহ্গত সমস্যার জন্য এ দু ’ রমণীর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিতেন। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে ,কোন কোন ফকীহ্ ও আলেম শহীদে আউয়ালের কন্যা ফাতেমাকে ‘ শাইখা ’ ও ‘ সিত্তুল মাশাইখ ’ বা ‘ সাইয়্যেদাতুল মাশাইখ ’ অর্থাৎ ফকীহ্দের নেত্রী উপাধি দিয়েছেন।
18. ফাযেল মিকদাদ: তিনি হিল্লীর অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম সুউর-এর অধিবাসী। তিনি শহীদে আউয়ালের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থ মুদ্রিত অবস্থায় আমাদের হাতে রয়েছে তা হলো ‘ কানযুল এরফান ’ । এ গ্রন্থে ইসলামের বিধিবিধান ও আহকাম সম্পর্কিত আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের যে সকল আয়াত হতে ইসলামের ফিকাহ্গত বিধান পাওয়া যায় (ইসলামী বিধিবিধানের দলিল উপস্থাপন করা যায়) তা উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শিয়া-সুন্নী উভয় মাযহাবে আহকামের আয়াতসমূহ নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ফাযেল মিকদাদের ‘ কানযুল এরফান ’ সবচেয়ে উত্তম। ফাযেল মিকদাদ 826 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তদুপরি তাঁকে নবম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ধরা হয়।
19. জামালুস সালেকীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ফাহদ হিল্লী আসাদী: তিনি 757 হিজরীতে জন্ম্ এবং 841 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শহীদে আউয়াল ও ফাখরুল মুহাক্কেকীনের ছাত্র। তিনি যাঁদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন- ফাযেল মিকদাদ ,শেখ আলী ইবনুল খাযেজ কাফী এবং শেখ বাহাউদ্দীন আলী ইবনে আবদুল কারিম।271 সম্ভবত তাঁর ফিকাহর শিক্ষকও এই তিন ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে ফাহদের বেশ কিছু ফিকাহ্ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে মুহাক্কেক হিল্লীর ‘ মুখতাছারুন নাফে ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ আল মুহাযযাবুল বারীঈ ,আল্লামা হিল্লীর ‘ আল মুকতাছের ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং শহীদে আউয়ালের ‘ আলফিয়াহ্ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইবনে ফাহদ বিশেষত চরিত্র ও আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর ‘ ইদ্দাতুদ দায়ী ’ নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে।
20. শেখ আলী ইবনে হেলাল জাযায়েরী: তিনি কোরআন ও হাদীসের ন্যায় ‘ নাকলী ’ জ্ঞানে যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রেও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি একজন পরহেজগার ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। অসম্ভব নয় ,ইবনে ফাহদের শিক্ষকগণই তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর সমকালের শিয়া ফকীহ্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ‘ শাইখুল ইসলাম ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ছাত্র মুহাক্কেক কারকী তাঁকে ‘ শাইখুল ইসলাম ’ সম্বোধন করে ফিকাহর ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন। বিশিষ্ট ফকীহ্ ইবনে আবি জামহুরও তাঁর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন।
21. শেখ আলী ইবনে আবদুল আলী কারকী: তিনি মোহাক্কেক কারকী ও মোহাক্কেক সানী নামে প্রসিদ্ধ। শেখ আলী লেবাননের জাবালে আমালের একজন ফকীহ্ এবং বিশিষ্ট শিয়া ফকীহ্দের একজন। তিনি ইরাকে ও সিরিয়ায় শিক্ষা লাভ করেছেন। অতঃপর সম্রাট প্রথম তাহমাসবের সময় ইরানে আসেন এবং ইরানে প্রথমবারের মতো একজন আলেমকে সম্মানিত করে ‘ শাইখুল ইসলাম ’ উপাধি দেয়া হয়। তাঁর পরবর্তীতে তাঁরই ছাত্র ও শেখ বাহায়ীর শ্বশুর শেখ আলী মিনশার এ উপাধি পান। অবশ্য পরে শেখ বাহায়ীও এ উপাধিপ্রাপ্ত হন। শাহ তাহমাসব তাঁর প্রতি একটি পত্র লিখে সম্পূর্ণ অধিকার দান করেন ও তাঁকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ঘোষণা করে নিজেকে তাঁর প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন। শেখ আলীর ফিকাহর যে গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ ও বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয় তা হলো ‘ জামেউল মাকাছেদ ’ যা আল্লামা হিল্লীর ‘ কাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থ ছাড়াও মুহাক্কেক হিল্লীর ‘ মুখতাছারুন নাফে ’ ও ‘ শারায়ে ’ এবং শহীদে আউয়াল ও আল্লামা হিল্লীর আরো কিছু গ্রন্থে টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। মুহাক্কেক কারকীর ইরান আগমনের ফলে কাযভীনে প্রথম দীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ইসফাহান ও অন্যান্য স্থানেও দীনি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ সকল মাদ্রাসায় বিশিষ্ট কিছু ছাত্র প্রশিক্ষিত হলে ‘ সাদুকাইনের ’ পর দ্বিতীয় বারের মত ইরান শিয়া ফিকাহ্শাস্ত্রের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুহাক্কেক কারকী 937 অথবা 941 হিজরীতে মারা যান। তিনি আলী ইবনে হেলাল জাযায়েরীর ছাত্র ছিলেন এবং আলী ইবনে হেলাল ইবনে ফাহদ হিল্লীর শিষ্য ছিলেন। ইবনে ফাহদ ফাযেল মিকদাদের সূত্রে শহীদে আউয়ালের পরোক্ষ ছাত্র ছিলেন। মুহাক্কেক কারকীর পুত্র শেখ আবদুল আলী ইবনে আলী ইবনে আবদুল আলীও অন্যতম শিয়া ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আল্লামা হিল্লীর ‘ ইরশাদ ’ ও শহীদে আউয়ালের ‘ আলফিয়াহ্ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছেন।
22. শেখ যাইনুদ্দীন (শহীদে সানী নামে প্রসিদ্ধ): শেখ যাইনুদ্দীন বিশিষ্ট শিয়া ফকীহ্দের একজন। তিনি বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও জাবালে আমালের অধিবাসী। তাঁর ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ সালিহ আল্লামা হিল্লীর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইরানের তুসের অধিবাসী ছিলেন । তাই কোন কোন স্থানে তিনি ‘ আত তুসুস শামী ’ স্বাক্ষর করেছেন। শহীদে সানী 911 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও 966 হিজরীতে শহীদ হন। তিনি অনেক দেশে সফর করেছেন ও অনেক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি মিশর ,দামেস্ক ,হেজায ,বাইতুল মুকাদ্দাস (ফিলিস্তিন) ,ইরাক ,ইস্তাম্বুল (তুরস্ক) ও অন্যান স্থানে গিয়েছেন। সকল শস্যক্ষেত্র হতেই তিনি শস্যদানা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্নী শিক্ষকের সংখ্যা বারোজন বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণেই তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র ছাড়াও দর্শন ,ইরফান ,চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন ,তিনি তাঁর পরিবারের জীবিকার জন্য রাত্রিতে কাঠ সংগ্রহে যেতেন ও দিনের বেলা পাঠ দানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় আসতেন। তিনি বা ’ য়ালা বাক্ক পাঁচটি মাযহাবের (জাফরী ,হানাফী ,মালেকী ,শাফেয়ী ও হাম্বলী) ফিকাহ্ পাঠ দান করতেন। তাঁর অসংখ্য রচনা রয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থে শহীদে আউয়ালের ‘ লোমআ ’ র ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ এবং মুহাক্কেক হিল্লীর ‘ শারায়ে ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেটির নাম ‘ মাসালিকুল আফহাম ’ । শহীদে সানী মুহাক্কেক কারকীর ইরান আগমনের পূর্বে তাঁর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র পড়তেন। ‘ মায়ালিম ’ গ্রন্থের লেখক শহীদে সানীর পুত্র এবং বিশিষ্ট শিয়া ফকীহ্দের একজন।
23. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আরদেবিলী (মুকাদ্দাস আরদেবিলী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি তাকওয়া ও যুহদের (দুনিয়া বিমুখতা) ক্ষেত্রে প্রবাদ পুরুষ ছিলেন এবং শিয়া ফকীহ্ ও বিশেষজ্ঞদের প্রথম সারির একজন। মুহাক্কেক আরদেবিলী নাজাফে বাস করতেন। তিনি সাফাভী শাসকদের সমসাময়িক। সাফাভী শাসক শাহ আব্বাস তাঁকে ইসফাহান আসার আমন্ত্রণ জানালেও তিনি আসেন নি। শাহ আব্বাস চাইতেন মুকাদ্দাস আরদেবিলী তাঁর কোন খেদমত করার সুযোগ দিন। একবার এক ব্যক্তি ইরান হতে শাহ আব্বাসের ভয়ে পালিয়ে নাজাফে মুকাদ্দাস আরদিবিলীর শরণাপন্ন হয় ও তাকে শাহ আব্বাসের নিকট সুপারিশ করার আহ্বান জানায়। মুকাদ্দাস শাহ আব্বাসকে নিম্নোক্ত পত্র লিখে পাঠান: ‘ সাফাভী শাসক আব্বাসের জেনে রাখা উচিত ,এই ব্যক্তি প্রথম অত্যাচার ও অপরাধ করলেও এখন অত্যাচারের শিকার। যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ্ তোমার কোন কোন অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। ’ -শাহে বেলায়েত আহমাদ আরদেবিলী।
শাহ আব্বাস এর জবাবে লিখেন ,
“ আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি ,শাহ আব্বাস আপনার নির্দেশকে আপনার অনুগ্রহ মনে করে পালন করেছে। আপনার এ ভক্তকে দোয়া করতে ভুলবেন না । ” - হযরত আলীর গৃহের প্রহরী কুকুর আব্বাস।272
মুকাদ্দাস আরদেবিলী ইসফাহানে আসতে অসম্মতি প্রকাশ করায় নাজাফের ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনটি পুনর্জীবিত হলো। যেমনিভাবে ইতোপূর্বে শহীদে সানী ,তাঁর পুত্র শেখ হাসান (মায়ালিম গ্রন্থের রচয়িতা) ইরানে হিজরত না করায় জাবালে আমাল ও সিরিয়ার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু ’ টি পূর্বের ন্যায় প্রাণবন্ত থাকে। ‘ মায়ালিম ’ ও ‘ মাদারিক ’ গ্রন্থের লেখকদ্বয় ইরানে থেকে যেতে বাধ্য হওয়ার আশংকায় অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মাশহাদে ইমাম রেযা (আ.)-এর কবর যিয়ারত হতে বিরত থাকেন।
আমার জানা নেই মুকাদ্দাস আরদেবিলী কার বা কাদের নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। শুধু এতটুকু জানা আছে ,তিনি শহীদে সানীর ছাত্রদের নিকট ফিকাহ্ পড়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ‘ মায়ালিম ’ ও ‘ মাদারিক ’ গ্রন্থদ্বয়ের লেখকদ্বয়ের নিকট ফিকাহ্ শিক্ষা লাভ করেছেন। জালাল উদ্দীন দাওয়ানীর জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে :
‘ মোল্লা আহমদ আরদিবিলী ,মাওলানা আবদুল্লাহ্ শুসতারী ,মাওলানা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী ,খাজা আফজালউদ্দীন তারাকা ,মীর ফাখরুদ্দীন হামাকি ,শাহ আবু মুহাম্মদ সিরাজী ,মাওলানা মির্জা জান এবং মির ফাতহে সিরাজী খাজা জামাল উদ্দীন মাহমুদের ছাত্র ছিলেন এবং জামাল উদ্দীন মাহমুদ মুহাক্কেক জালাল উদ্দীন দাওয়ানীর শিষ্য ছিলেন।273
সম্ভবত মুকাদ্দাস আরদেবিলী খাজা জামাল উদ্দীন মাহমুদের নিকট দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা পড়তেন ;ফিকাহ্ বা হাদীস নয়।
মুকাদ্দাস আরদেবিলী 993 হিজরীতে নাজাফে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ দু ’ টি ফিকাহ্ গ্রন্থ হলো ‘ শারহে ইরশাদ ’ এবং ‘ আয়াতুল আহকাম ’ । তাঁর সূক্ষ্ম ও যথার্য ফিকাহ্গত মত পরবর্তীকালের ফকীহ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
24. শেখ বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ আমেলী (শেখ বাহায়ী নামে প্রসিদ্ধ): শেখ বাহায়ী জাবালে আমালের অধিবাসী। তিনি তাঁর পিতা ও শহীদে সানীর ছাত্র শেখ হুসাইন ইবনে আবদুস সামাদের সঙ্গে শৈশবে ইরানে এসেছিলেন । তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এ কারণেই তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রহণের। তিনি বিরল প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক ,কবি ,দার্শনিক ,গণিতজ্ঞ ,স্থপতি ,ফকীহ্ ও মুফাসসির ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তাঁর মোটামুটি জ্ঞান ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ফার্সী ভাষায় ফিকাহ্গত বিভিন্ন বিধানসম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ‘ জামে আব্বাসী ’ নামে প্রসিদ্ধ।
শেখ বাহায়ী যেহেতু ফিকাহ্শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে অধ্যয়ন করেননি তাই তাঁকে প্রথম সারির ফকীহ্দের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না। অবশ্য তিনি অনেক ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করেছেন। মোল্লা সাদরায়ে সিরাজী , ‘ বিহারুল আনওয়ার ’ -এর লেখক আল্লামা মাজলিসীর পিতা মোল্লা মুহাম্মদ তাকী মাজলিসী (প্রথম মাজলিসী) ,মুহাক্কেক সাবযেওয়ারী , ‘ আয়াতুল আহকাম ’ গ্রন্থের লেখক ফাযেল জাওয়াদ প্রমুখ তাঁর ছাত্র। পূর্বে আমরা শেখ বাহায়ীর ‘ শাইখুল ইসলাম ’ উপাধি লাভের কথা শুনেছি। তাঁর শ্বশুর শেখ আলী মিনশার ইতোপূর্বে এ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও শেখ আলী মিনশারের কন্যাও একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্ ও আলেম ছিলেন। শেখ বাহায়ী 953 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও 1030 অথবা 1031 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ বাহায়ী একজন পর্যটকও ছিলেন। তিনি মিশর ,সিরিয়া ,হেজায ,ইরাক ,ফিলিস্তিন ,আজারবাইজান ও আফগানিস্তানের হেরাতে সফর করেছেন।
25. মোল্লা মুহাম্মদ বাকের সাবযেওয়ারী (মুহাক্কেক সাবযেওয়ারী): তিনি সাবযেওয়ারের অধিবাসী। তিনি ফিকাহ্ ও দর্শনের কেন্দ্র ইসফাহানে শিক্ষা লাভ করেন। তাই তিনি ‘ আকল ’ 274 ও ‘ নাকল ’ 275 উভয় জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন। ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে তাঁর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হয়ে থাকে। তার লিখিত ফিকাহ্ বিষয়ক দু ’ টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ যাখিরাহ ’ ও ‘ কিফায়াহ ’ । তিনি দার্শনিকও ছিলেন এবং ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থের ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ের টীকা লিখেছেন। তিনি 1090 হিজরীতে মারা যান। তিনি শেখ বাহায়ী ও মুহাম্মদ তাকী মাজলিসীর ছাত্র ছিলেন।
26. আগা হুসাইন খুনসারী (মুহাক্কেক খুনসারী): তিনিও ইসফাহানের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা লাভ করেছেন। এ কারণে ‘ আকল ’ ও ‘ নাকল ’ উভয় জ্ঞানেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মোল্লা মুহাম্মদ বাকের সাবযেওয়ারীর ভগ্নীপতি। তাঁর ফিকাহ্শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থের নাম ‘ মাশারিকুশ শুমুস ’ যা শহীদে আউয়ালের গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মুহাক্কেক খুনসারী 1098 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মোল্লা মুহসেন ফাইয কাশানী ও মোল্লা মুহাম্মদ বাকের মাজলেসীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা উভয়েই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন।
27. জামালুল মুহাক্কেকীন: তিনি আগা হুসাইন খুনসারীর পুত্র এবং ‘ আগা জামাল খুনসারী ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনিও তাঁর পিতার ন্যায় ‘ বুদ্ধিবৃত্তিক ’ (আকল) ও ‘ বর্ণনামূলক ’ (নাকল) উভয় জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন ,তিনি শহীদে সানীর ‘ শারহে লোমআ ’ য় টীকা সংযোজন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থের প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যায়েরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আগা জামাল সাইয়্যেদ মাহ্দী বাহরুল উলুমের পরোক্ষ শিক্ষক (মধ্যবর্তী দু ’ শিক্ষকের মাধ্যমে)। কারণ তিনি সাইয়্যেদ ইবরাহীম কাযভীনীর শিক্ষক। সাইয়্যেদ ইবরাহীম তাঁর পুত্র সাইয়্যেদ হুসাইন কাযভীনীর শিক্ষক এবং সাইয়্যেদ হুসাইন কাযভীনী বাহরুল উলুমের অন্যতম শিক্ষক।
28. শেখ বাহাউদ্দীন ইসফাহানী (ফাযেল হিন্দী): তিনি আল্লামা হিল্লীর ‘ কাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং তাঁর গ্রন্থের নাম রাখেন ‘ কাশেফুল লিসাম ’ । এ কারণেই তাঁকে ‘ কাশেফুল লিসাম ’ বলা হয়। তাঁর চিন্তা ও মত ফকীহ্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফাযেল হিন্দী 1137 হিজরীতে আফগানীদের দ্বারা সংঘটিত দাঙ্গায় নিহত হন। তিনিও বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক উভয় জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন।
29. মুহাম্মদ বাকের ইবনে মুহাম্মদ আকমাল বেহবাহানী (ওয়াহিদ বেহবাহানী নামে প্রসিদ্ধ): ‘ ওয়াফিয়া ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচয়িতা সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন রাজাভী কুমীর ছাত্র । তিনি সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন আগা জামাল খুনসারীরও ছাত্র।
ওয়াহিদ বেহবাহানী সাফাভী শাসনকালের পরবর্তী সময়ের আলেম ও ফকীহ্। সাফাভী শাসকদের পতনের পর ইসফাহানের দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার অবস্থান হারায়। ইসফাহানে আফগানীদের হামলা ও দাঙ্গার কারণে অনেক আলেমই ,যেমন ওয়াহিদ বেহবাহানীর শিক্ষক সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন রাজাভী আতাবাতে চলে যান।
ওয়াহিদ বেহবাহানী কারবালায় যান ও দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । সেখানে অনেক প্রতিভাবান ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করেন। যেমন সাইয়্যেদ মাহ্দী বাহরুল উলুম ,শেখ জাফর কাশেফুল গেতা ,মির্জা আবুল কাশেম কুমী (কাওয়ানীন গ্রন্থের লেখক) ,মোল্লা মাহ্দী নারাকী , ‘ রিয়ায ’ গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ আলী ,মির্জা মাহ্দী শাহরেস্তানী ,সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির শাফতী ইসফাহানী (যিনি ‘ হুজ্জাতুল ইসলাম ’ নামে প্রসিদ্ধ) ,মির্জা মাহ্দী শাহীদ মাশহাদী , ‘ মিফতাহুল কারামাহ্ ’ গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ জাওয়াদ এবং সাইয়্যেদ মুহসেন আয়ারজী।
তদুপরি তিনি তৎকালীন সময়ের আখবারী প্রবণতার276 বিরুদ্ধে ইজতিহাদের সপক্ষে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। আখবারীদের পরাজিত করে তিনি বেশ কিছু মুজতাহিদ তৈরি করেন। এ কারণে তাঁকে উঁচু স্তরের শিক্ষক বলা হয়। তাঁর নৈতিক চরিত্র তাকওয়ায় পূর্ণ ছিল। তাঁর ছাত্ররাও তাঁকে খুব সম্মান করতেন। ওয়াহিদ বেহবাহানী মায়ের দিক থেকে প্রথম মাজলেসীর বংশধর। প্রথম মাজলেসীর কন্যা ওয়াহিদ বেহবাহানীর মাতামহীর মাতা ,তাঁর নাম ছিল আমেনা বেগম। আমেনা বেগম মোল্লা সালেহ মাযেনদারানীর স্ত্রী এবং একজন ফকীহ্ ও মহীয়সী রমনী ছিলেন । যদিও তাঁর স্বামী মোল্লা সালেহ মাযেনদারানী একজন বড় আলেম ছিলেম তদুপরি কখনও কখনও ফিকাহর অনেক কঠিন সমস্যার সমাধানে স্ত্রীর শরণাপন্ন হতেন।
30. সাইয়্যেদ মাহ্দী বাহরুল উলুম: তিনি ওয়াহিদ বেহবাহানীর প্রতিভাধর ছাত্রদের একজন এবং একজন প্রসিদ্ধ শিয়া ফকীহ্। তিনি ফিকাহ্ বিষয়ে কবিতাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর মতামত অন্য ফকীহ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাহরুল উলুম ইরফান ও নৈতিকতায় উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণে শিয়া আলেমদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ও মাসুমের প্রতিচ্ছবি বলে পরিগণিত। তিনি অনেক কারামত দেখিয়েছেন। কাশেফুল গেতা (পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে আলোচিত হবে) তাঁর পাগড়ির কিনারা দিয়ে বাহরুল উলুমের জুতা পরিষ্কার করে দিতেন। বাহরুল উলুম 1154 অথবা 1155 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1212 হিজরীতে মারা যান।
31. শেখ জাফর কাশেফুল গেতা: তিনি ওয়াহিদ বেহবাহানী ও সাইয়্যেদ মাহ্দী বাহরুল উলুমের ছাত্র। তিনি একজন আরব এবং ফকীহ্ হিসেবে খুবই দক্ষ ছিলেন। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ কাশেফুল গেতা ’ । তিনি নাজাফে বসবাস করতেন। ‘ মিফতাহুল কারামাহ্ ’ গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ জাওয়াদ , ‘ জাওয়াহেরুল কালাম ’ গ্রন্থের লেখক শেখ মুহাম্মদ হাসান তাঁর ছাত্রদের অন্যতম। তাঁর চার পুত্রই প্রতিষ্ঠিত ফকীহ্ ছিলেন। তিনি সম্রাট ফাতহ্ আলী শাহের সমসাময়িক। তিনি তাঁর ‘ কাশেফুল গেতা ’ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি 1228 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ‘ কাশেফুল গেতা ’ ফিকাহ্শাস্ত্রে গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন। তাই এ শাস্ত্রে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হয়।
32. শেখ মুহাম্মদ হাসান: তাঁকে শিয়া ফিকাহর ‘ জ্ঞান ভাণ্ডার ’ বলা হয়। বর্তমান সময়ের কোন ফকীহ্ই শেখ মুহাম্মদ হাসানের রচিত ‘ জাওয়াহেরুল কালাম ’ গ্রন্থটির শরণাপন্ন না হয়ে পারেন না। এ গ্রন্থটি কয়েকবার লিথোগ্রাফী পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চাশ খণ্ডে (প্রতি খণ্ড চারশ ’ পৃষ্ঠা হিসেবে মোট বিশ হাজার পৃষ্ঠার) মুদ্রাক্ষরে বইটি ছাপা হচ্ছে। ‘ জাওয়াহেরুল কালাম ’ ফিকাহ্শাস্ত্রে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ এবং এর প্রতিটি পৃষ্ঠা যথেষ্ট সময় নিয়ে ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে পড়ার মতো। চিন্তা করুন বিশ হাজার পৃষ্ঠার এরূপ একটি গ্রন্থ রচনায় রচয়িতা কতটা শ্রম ও সময় দিয়েছেন! তিনি একাধারে ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে গ্রন্থটি রচনা করেন। তাই এ গ্রন্থটি একজন মানুষের সাহস ,হিম্মত ,প্রতিভা ,একাগ্রতা ,ভালবাসা ,ঈমান ও দৃঢ় চিত্তের স্বাক্ষর। তিনি ‘ কাশেফুল গেতা ’ এবং ‘ মিফতাহুল কারামাহ্ ’ গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ জাওয়াদের ছাত্র। তিনি নাজাফের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচুর ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করেছেন। শেখ মুহাম্মদ হাসান আরব ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে ‘ মারজা ’ (যে ফকীহর অনুসরণ করা হয়) ছিলেন। তিনি 1266 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
33. শেখ মুরতাজা আনসারী: তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারীর বংশধর। তিনি ইরানের দেজফুলে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পিতার নিকট পড়াশোনা করেন। অতঃপর পিতার সঙ্গে ইরাকের আতাবাতে চলে যান। সেখানে শিক্ষকগণ তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁর পিতাকে তাঁকে সেখানে রেখে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি ইরাকে চার বছর অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করেন। তাঁদের অনেকেই তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চার বছর পর এক অনাকাক্সিক্ষত ঘটনায় তিনি ইরানে ফিরে আসেন এবং দু ’ বছর পর পুনরায় ইরাকে ফিরে যান। ইরাকে দু ’ বছর অবস্থানের পর ইরানে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করেন। ইরানে আসার পর তিনি ইরানের বিভিন্ন আলেমের নিকট পড়াশোনা করেন। সর্বপ্রথম তিনি মাশহাদে ইমাম রেজার মাযার যিয়ারতে যান ও সেখান হতে কাশানে ‘ মুসতানাদুশ শিয়া ’ গ্রন্থের লেখক মোল্লা আহমদ নারাকী ও তাঁর পুত্র মোল্লা মাহ্দী নারাকীর ( ‘ জামেয়ুস সায়াদাত ’ গ্রন্থের রচয়িতা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন এবং তিন বছর তাঁদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর পুনরায় মাশহাদে যান ও সেখানে পাঁচ মাস অবস্থান করেন। শেখ আনসারী ইসফাহান ও বুরুজেরদ সফর করেন। তাঁর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল প্রখ্যাত শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ও শিক্ষাগ্রহণ। 1252/1253 হিজরীতে তিনি ইরাকের আতাবাতে ফিরে যান ও শিক্ষা দান শুরু করেন। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি শিয়াদের অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ ফকীহর (মারজা) পদ লাভ করেন।
শেখ আনসারীকে ‘ ফকীহ্ ও মুজতাহিদের অলংকার ’ উপাধি দেয়া হয়। তিনি বিষয়ের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা যাচাইয়ে বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফিকাহ্ ও উসূলশাস্ত্রকে তিনি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করিয়েছিলেন ও এ দু ’ শাস্ত্রে তিনি এমন কিছুর উদ্ভব ঘটান যা অভূতপূর্ব। তাঁর প্রসিদ্ধ দু ’ টি গ্রন্থ হলো ‘ রাসায়িল ’ এবং ‘ মাকাসিব ’ যা বর্তমানে দীনী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক। তাঁর পরবর্তী সময়ের আলেমগণ তাঁর চিন্তা ও মতেরই ছাত্র। ভিন্নভাবে বললে তাঁরই মানসপুত্র। পরবর্তীকালের আলেমগণ তাঁর গ্রন্থসমূহের সঙ্গে টীকা সংযোজন করেছেন। মুহাক্কেক হিল্লী ,আল্লামা হিল্লী এবং শহীদে আউয়ালের পর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর গ্রন্থসমূহ পরবর্তী আলেমদের দ্বারা ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজিত করে প্রকাশিত হয়ে আসছে।
তিনি দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রেও প্রবাদপুরুষ ছিলেন। শেখ আনসারী 1281 হিজরীতে নাজাফে মৃত্যুবরণ করেন ও সমাহিত হন।
34. মির্জা মুহাম্মদ হাসান সিরাজী: তিনি মির্জা সিরাজী বুযুর্গ নামে সুপরিচিত। প্রথম জীবনে তিনি ইসফাহানে পড়াশোনা করেন। অতঃপর নাজাফে যান । সেখানে শেখ মুহাম্মদ হাসানের ক্লাসে যোগদান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শেখ আনসারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শেখ আনসারীর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন। শেখ আনসারীর পর তিনি শিয়াদের মারজা হন। তিনি 23 বছর শিয়াদের একক মারজা ছিলেন। তিনিই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তৎপরতাকে নষ্ট করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ‘ তামাক আন্দোলন ’ অর্থাৎ তামাককে হারাম ঘোষণা করে ফতোয়া দেন। তাঁর নিকট হতে অনেক ছাত্র প্রশিক্ষিত হয়েছেন ,যেমন আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাযেম খোরাসানী ,সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কাযেম তাবাতাবায়ী ইয়াযদী ,আগা রেযা হামেদানী ,হাজী মির্জা হুসাইন সাবযেওয়ারী ,সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ফাশারাকি ইসফাহানী ,মির্জা মুহাম্মদ তাকী সিরাজী এবং অন্যান্য অনেকেই। তাঁর কোন গ্রন্থই এখন বিদ্যমান নেই। তবে তাঁর কিছু মত এখনও ফকীহ্দের নিকট সমাদৃত। তিনি 1312 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
35. আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাযেম খোরাসানী: তিনি 1255 হিজরীতে মাশহাদের এক অপ্রসিদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 22 বছর বয়সে তিনি তেহরানে হিজরত করেন। কিছু দিন সেখানে দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নাজাফে যান। তিনি দু ’ বছর শেখ আনসারীর ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় মির্জা সিরাজীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। মির্জা সিরাজী 1291 সালে নাজাফ ছেড়ে সামেরায় চলে যান ও বসবাস শুরু করেন। কিন্তু আখুন্দ খোরাসানী নাজাফেই থেকে যান ও নিজেই পাঠ দান শুরু করেন। তিনি একজন সফল শিক্ষক ছিলেন। প্রায় বারোশ ’ ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন যাঁদের মধ্যে দু ’ শ ’ জন পরবর্তীতে মুজতাহিদ ও ফকীহ্ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।
বিগত শতাব্দীর1 ফকীহ্দের অনেকেই ,যেমন সাইয়্যেদ আবুল হাসান ইসফাহানী ,শেখ মুহাম্মদ হুসাইন ইসফাহানী ,আগা হুসাইন বুরুজেরদী ,আগা হুসাইন কুমী ও জিয়াউদ্দীন আরাকী তাঁর ছাত্র ছিলেন। আখুন্দ খোরাসানীর পরিচিতি বিশেষত উসূলশাস্ত্রেই অধিক। তাঁর লেখা ‘ কিফায়াতুল উসূল ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক। এ গ্রন্থটির অনেক ব্যাখ্যা ও টীকাসম্বলিত গ্রন্থ ছাপা হয়েছে।
উসূলশাস্ত্রে তাঁর মতামত প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে ও তা দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। আখুন্দ খোরাসানী সেই ব্যক্তি যিনি শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে শর্তারোপের ফতোয়া দান করেন। ইরানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি 1329 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
36. হাজী মির্জা হুসাইন নাইনী: তিনি চৌদ্দ হিজরী শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও উসূলশাস্ত্রবিদ। তিনি মির্জা সিরাজী ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ফাশারাকীর নিকট পড়াশোনা করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। উসূলশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। তিনি আখুন্দ খোরাসানীর বিপরীতে উসূলশাস্ত্রে কিছু মত দেন যাতে নতুনত্ব ছিল। বর্তমান সময়ের অনেক ফকীহ্ই তাঁর ছাত্র। তিনি ফার্সী ভাষায় মূল্যবান কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন ,যেমন ‘ হুকুমাত দার ইসলাম ’ যাতে ইসলামের মৌল ভিত্তি এবং রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার (শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত) পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি 1355 হিজরীতে নাজাফে মৃত্যুবরণ করেন।
সারাংশ ও মূল্যায়ন
আমরা এখানে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর স্বল্পকালীন অন্তর্ধানের সময় হতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ফিকাহ্শাস্ত্রের ছত্রিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করলাম। আমরা ফকীহ্দের মধ্য হতে সেই সকল ব্যক্তিত্বকেই উপস্থাপন করেছি বর্তমান সময় পর্যন্ত উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হিসেবে গ্রন্থসমূহে যাঁদের মতামত উদ্ধৃত ও বর্ণিত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আলোচনা হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় :
প্রথমত তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিয়াদের মধ্যে ফিকাহ্ প্রাণবন্তরূপেই অব্যাহত ছিল ও আছে। অর্থাৎ এগার শতকের অধিক সময় ধরে ফিকাহ্শাস্ত্র দীনী মাদ্রাসাগুলোতে সক্রিয়রূপে বিদ্যমান ছিল। এ সময়ব্যাপী কখনই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়নি । উদাহরণস্বরূপ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ বুরুজেরদী হতে শুরু করে পূর্বক্রম অনুসরণ করলে ফিকাহ্শাস্ত্রের শিক্ষকতার ধারাটি পবিত্র ইমামগণের যুগের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। সম্ভবত সাড়ে এগার শতাব্দীব্যাপী কোন একটি জ্ঞানের অব্যাহত ধারা কোন সভ্যতাতেই এরূপ নিরবচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান ছিল না ,এমনকি কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অব্যাহত ধারার এরূপ উদাহরণ অভূতপূর্ব। একমাত্র ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন স্তরে পর্যায়ক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে এক প্রাণ ও আত্মার প্রভাবে পরস্পর সম্পর্কিত থেকে এর জীবনকে অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বিচ্ছিন্নতা ও স্থবিরতা লক্ষ্য করি।
এখানে উল্লেখ্য ,আমরা তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হতে শিয়া ফিকাহ্শাস্ত্রের বিকাশের ধারা আলোচনা করলেও তার অর্থ এ নয় যে ,শিয়া ফিকাহ্ সে সময় হতে শুরু হয়েছে ;বরং এর কারণ হলো এর পূর্বে ইমামগণ সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বলে শিয়া ফকীহ্গণ তাঁদের প্রভাবাধীন হিসেবে স্বাধীন ছিলেন না। তাই বলতে গেলে ইজতিহাদ ও ফিকাহ্শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা ও গবেষণার বিষয়টি শিয়াদের মাঝেও স্বয়ং সাহাবীদের সময়ে শুরু হয়েছিল। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি ,ফিকাহ্ বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থটি হযরত আলী (আ.)-এর বায়তুল মাল রক্ষক সাহাবী আলী ইবনে আবি রাফে রচনা করেন।
দ্বিতীয়ত কোন কোন ব্যক্তির এ ধারণা হয় ,শিয়া মাযহাবের জ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ বিশেষত ফিকাহ্ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ইরানী ফকীহ্দের দ্বারা লিখিত হয়েছে। এটি সঠিক নয়। বরং ইরানী
অ-ইরানী ফকীহ্রা সমবেতভাবে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষত দশম হিজরী শতাব্দীর পূর্ববর্তী ফকীহ্গণের অধিকাংশই অ-ইরানী ছিলেন। দশম হিজরী শতাব্দীর পরবর্তীতে সাফাভীদের শাসনকাল হতে ইরানী ফকীহ্দের প্রাধান্য শুরু হয়।
তৃতীয়ত সাফাভী শাসনামলের পূর্বে ইরান ফিকাহ্শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে শেখ তুসীর মাধ্যমে নাজাফের দীনী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা ফিকাহর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই লেবাননের জাবালে আমাল ও এর নিকটবর্তী ইরাকের হিল্লাতে ফিকাহ্ শিক্ষার দু ’ টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সিরিয়ার হালাবও কিছুদিন শিয়া ফিকাহর অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সাফাভীদের শাসনামলে ইসফাহান শিয়া ফিকাহ্শাস্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অবশ্য একই মুহূর্তে নাজাফের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুকাদ্দাস আরদিবিলী কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয় ও বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ইরানের শহরগুলোর মধ্যে একমাত্র কোম তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে আলী ইবনে বাবাভেই ও মুহাম্মদ ইবনে কৌলাভেই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফিকাহর কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তবে মধ্যবর্তী সময়ে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কাজার শাসনামলে মির্জা আবুল কাসেম কুমী কর্তৃক পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হয়। সর্বশেষ 1340 হিজরীতে মরহুম শেখ আবদুল করিম হায়েরী ইয়াযদি কোমকে শিয়া ফিকাহর সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন।
সুতরাং কখনও বাগদাদ ,কখনও নাজাফ ,কখনও জাবালে আমাল ,হালাব (সিরিয়া) ,হিল্লা (ইরাক) ,ইরানের কোম ও ইসফাহান ফকীহ্ ও শিয়া ফিকাহর কেন্দ্র ছিল। অবশ্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিশেষত সাফাভী শাসনামলে ইরানের অন্যান্য শহরেও ,যেমন মাশহাদ ,হামেদান ,সিরাজ ,ইয়াযদ ,কাশান ,তাবরীজ ,জানযান ,কাযভীন ও ফেরদৌসীতে দীনী শিক্ষার বৃহৎ ও নির্ভরযোগ্য কিছু কেন্দ্র ছিল। অবশ্য ইসফাহান ,কোম ও কাশান ব্যতীত অন্য কোন শহরই ফিকাহ্শাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্র বলে পরিগণিত হতো না। অবশ্য ইসলামী জ্ঞান ও ফিকাহ্শাস্ত্রের চর্চার কেন্দ্র হিসেবে এ শহরগুলোতে অবস্থিত বৃহৎ ও ঐতিহাসিক মাদ্রাসাসমূহ সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে যা তৎকালীন সময়ে দীনী ছাত্রদের কলোরবে মুখরিত হতো।
চতুর্থত জাবালে আমালের ফকীহ্গণ সাফাভী শাসকদের পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রথমদিকে সাফাভী শাসকগণ তাঁদের প্রাচীন দরবেশী রীতির পথে চলছিলেন। যদি তাঁদের এ পথ জাবালে আমালের গভীর ফিকাহ্শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা ভারসাম্য না পেত ,তাঁরা যদি ইরানে ফিকাহ্শাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করতেন তবে তাঁদের পরিণতি সিরিয়া ও তুরস্কের আলাভীদের (যারা হযরত আলীকে আল্লাহ্ মনে করে) ন্যায় হতো। অর্থাৎ জাবালে আমালের ফকীহ্দের প্রভাবেই ইরানের শাসক ও জনসাধারণ বিচ্যুতি হতে রক্ষা পায় এবং এরফানশাস্ত্র ইরানে ভারসাম্যপূর্ণ পথে বিকশিত হয়। জাবালে আমালের ফকীহ্গণ ,যেমন মুহাক্কেক কোরকী ,শেখ বাহায়ী এবং অন্যরা ইসফাহানের ফিকাহ্শাস্ত্রের কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে বড় দায়িত্ব পালন করেছেন সে কারণে ইরানী জাতি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।
পঞ্চমত যে সকল ব্যক্তি শিয়া মাযহাবকে ইরানীদের তৈরি বলে তা খণ্ডিত হয়েছে। শাকিব আরসালানের বর্ণনা মতে ইরানে শিয়া মতবাদের প্রসারের অনেক পূর্বেই জাবালে আমলে শিয়া ফিকাহর বিকাশ ও বিস্তার ঘটে অর্থাৎ জাবাল আমাল এ দিক থেকে ইরান হতে অগ্রগামী ছিল। অনেকে মনে করেন জাবালে আমাল ও লেবাননে শিয়া চিন্তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার গিফারী (রা.)-এর মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। কারণ আবু যার গিফারী সিরিয়ায় অবস্থানকালে বেশ কিছুদিন এখানে ছিলেন এবং তিনি মুয়াবিয়া ও উমাইয়্যাদের বায়তুল মাল আত্মসাৎ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের বিরুদ্ধে সেখানকার অধিবাসীদের উদ্দীপিত করতেন। তিনি সেখানে পবিত্র শিয়া ধারার প্রচার করতেন।277
আহলে সুন্নাতের ফকীহ্গণ
প্রথমে আমরা আহলে সুন্নাতের ফকীহ্গণ সম্পর্কে একটি ভূমিকা পেশ করছি। উমাইয়্যা খলীফাগণ অ-শিয়া আরব বংশোদ্ভূত ফকীহ্দের পৃষ্ঠপোষকতা করত। পরবর্তীতে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে অ-শিয়া অনারব ফকীহ্দের পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করে। জর্জি যাইদান উমাইয়্যা খলীফাদের সম্পর্কে বলেন ,
“ উমাইয়্যাগণ গোঁড়া আরব ছিল এবং অনারবদের অপাঙ্ক্তেয় মনে করত। মদীনার ফকীহ্গণ যেহেতু নবী (সা.)-এর পরিবারকে খেলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মনে করত ও উমাইয়্যাদের ক্ষমতার অবৈধ দখলদার হিসেবে অপছন্দ করত সেহেতু উমাইয়্যা শাসকগণ মদীনার ফকীহ্দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তদুপরি বাধ্য হয়ে তাঁদের প্রতি বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করত এবং কখনও কখনও তাঁদের বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। উমাইয়্যা শাসকদের মধ্যে সৎ শাসক হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আজিজ মদীনার ফকীহ্দের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। উমাইয়্যাদের পরে আব্বাসীয়রা ক্ষমতা লাভ করে। আব্বাসীয় খলীফা মনসুর আরবদের হেয় ও ইরানীদের বড় করার চেষ্টায় রত হন। কারণ আব্বাসীয় খেলাফত ইরানীদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মনসুর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলমানদের দৃষ্টিকে মক্কা ও মদীনা হতে অন্যত্র সরানোর চেষ্টায় রত হন। তিনি মদীনার লোকদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেন ও মক্কা হতে মুসলমানদের বিরত রাখার লক্ষ্যে ‘ কোব্বাতুল খাদরা ’ (সবুজ গম্বুজ) প্রতিষ্ঠা করে মক্কা যাওয়ার পরিবর্তে সেখানে গিয়ে হজ্বের বিধিবিধান পালন করার নির্দেশ দেন। সে সময় মদীনার ফকীহ্ ছিলেন আনাস ইবনে মালেক। তিনি মদীনার লোকদেরকে মনসুর হতে বাইয়াত প্রত্যাহারের ফতোয়া দেন। মদীনার লোকজন মনসুরের বাইয়াত প্রত্যাহার করে ইমাম হাসানের পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসানের হাতে বাইয়াত করে। মুহাম্মদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে মনসুর তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন ও বেশ প্রতিরোধের পর মুহাম্মদ পরাস্ত (বন্দী ও নিহত) হন। মদীনার লোকজন পুনরায় মনসুরের নিকট বাইয়াত করতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও ইমাম মালিক আব্বাসীয় খলীফাদের খলীফা হিসেবে মানতেন না। মনসুরের চাচা মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলায়মান এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হলে মালেককে ডেকে পাঠান ও তাঁর পৃষ্ঠ উন্মুক্ত করে চাবুক দ্বারা প্রহার করেন। ” 278
ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে ফকীহ্দের সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধে মুহাম্মদ ইবনে সুজার (ইবনুস সালজী নামে প্রসিদ্ধ) জীবনী আলোচনায় একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা আব্বাসীয় খলীফাদের রাজনীতিতে ইরানীপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ইসহাক ইবনে ইবরাহীম মাসআবীর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ,
“ খলীফা একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: আমার কর্মে সহযোগিতার জন্য একজন ফকীহ্ আলেমকে আন যে হাদীস বিষয়ে যেমন পণ্ডিত হবে তেমনি স্বাধীন মত প্রকাশের (কিয়াস করার) যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। খোরাসানীদের নিকট হতে আমাদের শাসনের অধীন প্রশিক্ষিত সুন্দর চেহারার এরূপ বৈশিষ্ট্যের এক ব্যক্তিকে মনোনীত কর যাকে বিচার বিভাগের কাযী নিয়োগ করব। ” ইসহাক বলেন , “ আমি খলীফাকে বললাম: মুহাম্মদ ইবনে সুজা সালজী ব্যতীত এরূপ কাউকে দেখছি না। যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। খলীফা বললেন: ঠিক আছে। যদি তিনি রাজী হন তাহলে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি মুহাম্মদ ইবনে সুজাকে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না ;বরং বললেন: এটি গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার অর্থ-সম্পদ ,সম্মান ও মর্যাদা কিছুরই প্রয়োজন নেই...। ” 279
আমরা জানি ,আহলে সুন্নাতের ফকীহ্দের মধ্যে চারজন স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। সাধারণ সুন্নী জনগণ এই চার মাযহাবের একটিকে অনুসরণ করে থাকে। এ চার ফকীহ্ হলেন আবু হানিফা ,শাফেয়ী ,মালেক ইবনে আনাস এবং আহমদ ইবনে হাম্বল। কিন্তু চার মাযহাবের মধ্যে দীনকে সীমিত করার বিষয়টি সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে সম্পন্ন হয়। এর পূর্বে আহলে সুন্নাতের মধ্যে দশটি মাযহাব প্রচলিত ছিল।
আমরা আহলে সুন্নাতের ফকীহ্দের সম্পর্কে আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে চার মাযহাবের উদ্ভবের পূর্বের সময়কাল ,দ্বিতীয় ভাগে চার মাযহাবের উৎপত্তির সমকালীন সময় ,তৃতীয় ভাগে চার মাযহাবের ইমামদের পরবর্তী সময়।
চার মাযহাবের পূর্ববর্তী সময়ে তাবেয়ীদের যুগ ছিল। তাবেয়ীন হলেন যাঁরা রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেননি কিন্তু তাঁর সাহাবীদের সাহচর্য পেয়েছেন। তাবেয়ীদের মধ্যে সাতজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ মদীনায় ছিলেন যাঁদের ‘ ফোকাহায়ে সাবআ ’ বলা হয়। তাঁরা হলেন :
1. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে মাখযুমী: তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি এবং কুরাইশ নেতা আবু জাহলের ভ্রাতার বংশধর। তিনি 94 হিজরীতে মারা যান।
2. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব মাখযুমী: তিনিও একজন কুরাইশ। তিনি ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে তিনি পঞ্চাশ বছর রাত্রি জেগে ইবাদত করেছেন ও রাত্রির এশার নামাজের ওজু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়েছেন। অবশ্য আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর ও অনেক শিয়া আলেম তাঁকে শিয়া বলেছেন।280 সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব 91 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
3. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকর: তিনি প্রথম খলীফা আবু বকরের বংশধর এবং ইমাম সাদিক (আ.)-এর নানা। আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদরও তাঁকে শিয়া বলেছেন। একটি বর্ণনা মতে কাসেম ইবনে মুহাম্মদের মাতা সাসানী শাসক ইয়ায্দ গারদের কন্যা ছিলেন। এ সূত্র মতে কাসেম পিতার দিক হতে কুরাইশ ও মাতার দিক হতে ইরানী ছিলেন। তিনি 110 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
4. খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী: তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিতের পুত্র। তিনি 99 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার: তিনি অনারব ,সম্ভবত ইরানী। তিনি 94 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
6. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ: তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি 98 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
7. উরওয়া ইবনে যুবাইর: তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী যুবাইর ইবনে আওয়ামের পুত্র। তিনিও 94 হিজরীতে মারা যান।
এ সাত ব্যক্তি হতে সম্ভবত একজন (সুলাইমান ইবনে ইয়াসার) ইরানী বংশোদ্ভূত। অন্যান্যরা মক্কা অথবা মদীনার অধিবাসী। অবশ্য এ স্তরে আরো কিছু প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন যাঁরা ইরানী ছিলেন। যেমন মালেকী মাযহাবের ইমাম মালেক ইবনে আনাসের শিক্ষক রাবীয়াতুর রাই। তিনিই ফিকাহ্শাস্ত্রে কিয়াসের উদ্গাতা। রাবীয়া 136 হিজরীতে মারা যান। তাউস ইবনে কাইসান এ সময়ের অপর প্রসিদ্ধ ইরানী ফকীহ্। তিনি 104 অথবা 106 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সুলাইমান আমাশও তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ ইরানী ফকীহ্।
সে সময়ের প্রসিদ্ধ ফকীহ্দের অন্যতম হলেন ইবনে আব্বাসের মুক্ত দাস আকরামা। আকরামা উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাফসীর ও ফিকাহ্শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন তাফসীর ও ফিকাহর গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে ।
প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফকীহ্
1. আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত ইবনে যোতী অথবা নোমান ইবনে সাবিত ইবনে নোমান ইবনে মারযবান (মৃত্যু 150 হিজরী)। আবু হানিফা একজন ইরানী বংশোদ্ভূত ফকীহ্। তাঁকে আহলে সুন্নাতের ফকীহ্দের প্রধান (ইমামে আযম) বলা হয়। অধিকাংশ সুন্নী সমাজে তাঁকে নবী (সা.) ,খোলাফায়ে রাশেদীন ,ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। ইরানে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা স্বল্প হলেও ইরানের বাইরে তাদের সংখ্যা অনেক।
2. মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী: শাফেয়ী কোরেশী আরব। অনুসারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে তিনি আবু হানিফার সমকক্ষ বা তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি হতে পারে। শাফেয়ী 204 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. মালেক ইবনে আনাস (মৃত্যু 179 হিজরী): মালেক কাহতান বংশীয় আরব। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ মুসলমান তাঁর অনুসারী।
4. আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু 241 হিজরী): আহমদ আরব বংশোদ্ভূত ,তবে সম্ভবত তাঁর পরিবার ইরানের খোরাসানের মারভে বাস করত। ইবনে খাল্লেকান বলেছেন ,তাঁর মাতা তাঁকে গর্ভধারণকালে মারভ হতে বাগদাদ রওয়ানা হন এবং বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়।
আহমদ ইবনে হাম্বলকে আরব বংশোদ্ভূত ইরানী বলা যেতে পারে। তাই আহলে সুন্নাতের চার ইমামের একজন ইরানী ,একজন আদনানী আরব ,একজন কাহতানী আরব এবং একজন আরব বংশোদ্ভূত ইরানী।
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ,এ স্তরের (সময়কালে) আরো কিছু ফকীহ্ ছিলেন যাঁদের মাযহাব বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে ,যেমন মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (মৃত্যু 310 হিজরী) এবং দাউদ ইবনে আলী জাহিরী ইসফাহানী (মৃত্যু 270 হিজরী)। দাউদ ইবনে আলী জাহিরী ফিকাহ্শাস্ত্রে জাহিরী মতবাদের উদ্গাতা। তাঁর ফিকাহর মত হলো হাদীসের বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোন অর্থই নেই। এ কারণে তাঁর মতবাদ এক প্রকার স্থবিরতা ছাড়া কিছু নয়। ইরানী বংশোদ্ভূত ফকীহ্ ইবনে হাযম আন্দালুসী উমাইয়্যাদের চরম ভক্ত ব্যক্তি। তাঁর নবী পরিবারের প্রতি এক রকম বিদ্বেষ ছিল। ফিকাহ্্র বিষয়ে তিনি দাউদ ইবনে আলী জাহিরীর অনুসারী ছিলেন।
এ সময়কালের আরো কিছু প্রসিদ্ধ ফকীহ্ যাঁদের কেউ স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রবক্তা ,আবার কেউ শুধুই ফকীহ্ ছিলেন। আমরা এখানে তাঁদের অনেকের পরিচয় তুলে ধরছি যাতে আহলে সুন্নাতের ফিকাহ্য় ইরানীদের অবদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।
1. মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী (মৃত্যু 189 হিজরী): তিনি আবু হানিফার ছাত্র ও হারুনুর রশীদের সহযোগী ছিলেন। তিনি সিরীয় হলেও ইরাকের ওয়াসেতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ইরানের রেই শহরে । একবার হারুনুর রশীদের সঙ্গে ইরানে আগমন করলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁকে সেখানে সমাহিত করা হয়।
2. আবু ইউসুফ (মৃত্যু 192 হিজরী): তিনিও আবু হানিফার ছাত্র এবং আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দী ,হাদী ও হারুনের সময় বিচার বিভাগের প্রধান কাযী ছিলেন। তাঁকে আনসার বংশীয় বলা হয়ে থাকে।
3. যাফর ইবনিল হাযিল (মৃত্যু 158 হিজরী): তিনি আদনানী আরব এবং আবু হানিফার অনুসারী।
4. লাইস ইবনে সা ’ দ ইসফাহানী (মৃত্যু 157 হিজরী): তিনি মিশরের ফকীহ্ ও স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন ,যদিও অনেকে তাঁকে আবু হানিফার অনুসারী বলেছেন।
5. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারাক মুরুজী (মৃত্যু 181 হিজরী): তিনি আবু হানিফা ,মালেক ও সুফিয়ান সাউরীর ছাত্র। তিনি ইরানের মারভের অধিবাসী।
6. আউযায়ী ,আবু আমর আবদুর বহমান ইবনে আমর (মৃত্যু 157 হিজরী): তিনি জুহরী ও আতা ইবনে আবি রিবাহর ছাত্র। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী। তাঁকে সিরীয় একক ফিকাহর ইমাম বলা হয়। তিনি ফিকাহর স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রবক্তা। তাঁর পূর্বপুরুষ ইয়েমেনের মুক্ত আরব ছিলেন নাকি বন্দী তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।
উপরিউক্তগণ আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ফকীহ্দের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ের ফকীহ্দের মধ্যে কেউ ইরানী আবার কেউ অ-ইরানী।
তৃতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ফকীহ্দের মধ্যে ইবনে সিরিজ শাফেয়ী ,আবু সাঈদ ইসতাখরী ও আবু ইসহাক মুরুজী চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ,আবু হামিদ ইসফারাইনী ,আবু ইসহাক ইসফারাইনী ,আবু ইসহাক সিরাজী ,ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী ,ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী ,আবুল মুজাফ্ফার খাওয়াফী ও কিয়াল হারাসী পঞ্চম হিজরীতে ,আবু ইসহাক আরাকী মৌসেলী ষষ্ঠ হিজরীতে ,আবু ইসহাক মৌসেলী সপ্তম হিজরীতে ,ইমাম শাতেবী আন্দালুসী অষ্টম হিজরীতে প্রসিদ্ধ ইরানী ফকীহ্দের অন্তর্ভুক্ত।
নবম হিজরী শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ইরানের মানুষ শিয়া মাযহাব গ্রহণ করলে তার প্রভাবে বিগত চারশ ’ বছরের ইরানী ফকীহ্গণের সকলেই শিয়া মাযহাবভুক্ত।
আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব
আরবী ভাষা বলতে আমরা আরবী ব্যাকরণ (সারফ ও নাহু) ,অভিধানশাস্ত্র ,অলংকার ,বাগ্মিতা ,কবিতা ও ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করছি। এ ক্ষেত্রে ইরানীরা প্রচুর অবদান রেখেছে।
ইরানীদের আরবী ভাষায় অবদান স্বয়ং আরবদের চেয়ে অনেক বেশি ,এমনকি ইরানীরা ফার্সী ভাষা অপেক্ষা আরবী ভাষায় অধিক অবদান রেখেছে। ইরানীরা এক পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতির উদ্দীপনায় আরবী ভাষায় অবদান রাখতে প্রয়াসী হয়েছিল। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় ইরানীরাও আরবী ভাষাকে আরবদের ভাষা মনে করত না ;বরং একে কোরআনের ও মুসলিম বিশ্বের ভাষা মনে করত। এ কারণেই তারা মুক্ত মনে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে এ ভাষা শিক্ষা করেছিল ও গবেষণায় রত হয়েছিল।
আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র আরবী ভাষার বিধিবিধান (নাহু) দিয়ে শুরু হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত ,এ শাস্ত্রের উদ্ভাবক আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)। বিশিষ্ট আলেম আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর তাঁর ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ গ্রন্থে এ দাবির সপক্ষে কিছু অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। হযরত আলী তাঁর প্রতিভাধর সাহাবী আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে এ (নাহু) শাস্ত্রের মৌলনীতি শিক্ষাদান করে এর ভিত্তিতে অন্যান্য বিধান তৈরির পরামর্শ দান করেন। আবুল আসওয়াদ এ পরামর্শের ভিত্তিতে অন্যান্য বিধান তৈরি করেন ও তাঁর দু ’ পুত্র আতা ইবনে আবিল আসওয়াদ ,আবা হারব ইবনে আবিল আসওয়াদ এবং তাঁর ছাত্র ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুর ,মাইমুন আকরান ,ইয়াহিয়া ইবনে নোমান এবং আনবাসাতুল ফিল প্রমুখকে তা শিক্ষাদান করেন। কথিত আছে ইসলামের প্রসিদ্ধ দু ’ জন সাহিত্যিক আবু উবাইদা ইরানী ও আসমায়ী আরব ,আতা ইবনে আবিল আসওয়াদের ছাত্র ছিলেন।
দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষাবিদদের মধ্যে আবু ইসহাক হাদারামী ,ঈসা সাকাফী এবং প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ সাত ক্বারীর অন্যতম বিশিষ্ট শিয়া ব্যক্তিত্ব আবু আমর ইবনুল আলা রয়েছেন।
আবু আমর ইবনুল আলা আরবী অভিধান ,ভাষা ও ব্যাকরণবিদ এবং সাহিত্যিক ছিলেন। বিশেষত কবিতায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। একবার হজ্ব যাত্রার সময় তিনি তাঁর হস্তলিখিত কবিতার মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের যে কবিতাসমূহ ছিল সেগুলো ধ্বংস করেন। তিনি একজন পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পবিত্র রমজান মাসে কখনও কবিতা পড়তেন না। আসমায়ী ,ইউনুস ইবনে হাবিব নাহভী ,আবু উবাইদা এবং সা ’ দান ইবনে মুবারাক তাঁর ছাত্র ছিলেন।281
তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের অন্যতম হলেন খলিল ইবনে আহমাদ আরুজী। তিনি একজন শিয়া ও বিরল প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি। বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ ‘ আল কিতাব ’ গ্রন্থের রচয়িতা সিবাভেই খলিলের ছাত্র। অন্যতম প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ আখফাশ ,খলিল ও সিবাভেই-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।
এর পরবর্তী সময়ের ব্যাকরণবিদগণ ‘ কুফী ’ ও ‘ বাসরী ’ এ দু ’ ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ কিসায়ী ,তাঁর ছাত্র ফাররা ,তাঁর ছাত্র আবুল আব্বাস সা ’ লাব এবং তদীয় ছাত্র ইবনুল আম্বারী কুফী ব্যাকরণবিদদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে সিবাভেই ,আখফাশ ,মাযানী ,মুবাররেদ ,জুজায ,আবু আলী ফারেসী ,ইবনে জুনা এবং আবদুল কাদের জুরজানী পর্যায়ক্রমে শিক্ষক ও ছাত্র এবং বাসরী ব্যাকরণবিদদের অন্তর্ভুক্ত।
উপরিউক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই ইরানী। ইরানী বংশোদ্ভূত আরবী ভাষাবিদগণের তালিকা ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো।
1. ইউনুস ইবনে হাবিব (মৃত্যু 183 হিজরী): ইবনুন নাদিম বলেছেন ,তিনি অনারব (ইরানী)।282 তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ‘ মায়ানিউল কোরআনুল কারিম ’ । তিনি সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। তিনি তাঁর সাতাশি বছরের জীবনকে জ্ঞানের সেবায় নিবেদন করেছিলেন।
2. আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনুল মুসান্না (মৃত্যু 210 হিজরী): ইবনুন নাদিম বলেছেন ,আবু উবাইদাও ইরানী ছিলেন।
3. সা ’ দান ইবনে মুবারাক: তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থের বর্ণনা মতে তিনি ইরানের তাখারিস্তানের অধিবাসী ও অন্ধ ছিলেন।283
4. আবু বাশার আমর ইবনে উসমান ইবনে কাম্বার (সিবাভেই নামে প্রসিদ্ধ): তিনি 180 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাইদায় জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন বসরায় কাটান ও এ সময়ে একবার বাগদাদ সফর করেন। তাঁর বাগদাদ সফরে বিশিষ্ট ক্বারী ও ব্যাকরণবিদ কিসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটি ‘ যাম্বরিয়ার ঘটনা ’ নামে প্রসিদ্ধ । তিনি বাগদাদ সফরের পর নিজ ভূমি ইরানের ফার্সে ফিরে আসেন এবং মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন ও সমাহিত হন। ব্যাকরণশাস্ত্রে (নাহু) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম ‘ আল কিতাব ’ যা আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাশাস্ত্রে অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা গ্রন্থ ও জ্যোতির্বিদ্যায় টলেমীর ম্যাজেস্টি গ্রন্থের মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর এ গ্রন্থ মিশর ,কলকাতা ,প্যারিস ও বার্লিনে কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। সাইয়্যেদ বাহরুল উলুম ও অনেকের মতে ‘ নাহুশাস্ত্রে সকল ব্যাকরণবিদ সিবাভেই-এর পরিবারভুক্ত ও অনুসারী। তাঁর এ গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের তিন শতাধিক আয়াত উদাহরণ হিসেবে এসেছে। বিশিষ্ট আরব ব্যাকরণবিদ অনেক মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়েও গ্রন্থটি একজন আহলে কিতাবকে শিক্ষাদানে রাজী হননি। এ কারণে যে ,এতে করে ঐ অমুসলমানের হাত পবিত্র কোরআনের আয়াতের ওপর পড়বে যা কোরআনের অবমাননার শামিল।
5. সাঈদ ইবনে মাসয়াদ আখফাশ (আখফাশ অথবা আখফাশে আওসাত নামে প্রসিদ্ধ): তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আরবী ভাষা ও ব্যাকরণবিদ। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি খলিল ইবনে আহমাদ লিখিত গ্রন্থে কবিতা ও ছন্দ সংযোজন করেন। ইবনুন নাদিমের বর্ণনা মতে এ ব্যক্তি ইরানের খাওয়ারেজমের অধিবাসী। তাঁকে ‘ মাজাশায়ী ’ ও বলা হয়েছে। তাই স্পষ্ট নয় ,তিনি আরব বংশোদ্ভূত ইরানী নাকি এ উপনামটি তৎকালীন সময়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এক আরব গোত্রের সঙ্গে (চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে) সংযুক্ত হয়েছে। তিনি 215 অথবা 221 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
6. আলী ইবনে হামযা কিসায়ী: তাঁর সম্পর্কে কারীদের আলোচনায় আমরা বর্ণনা দিয়েছি। কিসায়ী নিঃসন্দেহে ইরানী। তাঁর প্রপিতার নাম ফিরুয। তিনি প্রায় দু ’ শ ’ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে খোরাসান যাত্রাকালে রেই শহরে মৃত্যুবরণ করেন।
7. ফাররা: তিনিও একজন ইরানী। কারী ও কোরআনের মুফাসসিরদের আলোচনায় তাঁর নাম আমরা উল্লেখ করেছি।
8. মুহাম্মদ ইবনে কাসেম আনবারী (ইবনুল আনবারী বা আম্বারী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি আম্বারের অধিবাসী। এ স্থানটি সাসানী আমলে ইরানের শস্যভাণ্ডার ছিল। তিনি আবুল আব্বাস সা ’ লাবের ছাত্র এবং 327 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
9. আবু ইসহাক ,ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সারি ইবনে সাহল (জুজায নামে প্রসিদ্ধ): তিনি মুবাররেদ ও সা ’ লাবের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঁচ ও স্ফটিকের পাত্র ও ছাঁচ তৈরি করতেন। এ কারণেই তাঁকে ‘ জুজায ’ বলা হয়। কথিত আছে প্রতিদিন তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ হতে এক দিরহাম তাঁর শিক্ষক মুবাররেদকে শিক্ষার পারিশ্রমিক হিসেবে দিতেন। তিনি 310 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
10. আবু আলী ফারেসী: তিনি ফার্সের ফাসার অধিবাসী ও দাইয়ালামার (দাইলামী শাসকদের) সমসাময়িক। কেউ কেউ তাঁকে সর্বশেষ আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন। ‘ তাসিসুশ শিয়া ’ গ্রন্থের 51 পৃষ্ঠায় সালামাত ইবনে আয়ায শামীর ‘ আল মিসবাহ্ ’ গ্রন্থের সূত্রে বলা হয়েছে ,নাহুশাস্ত্র (আরবী ব্যাকরণের বাক্য গঠনের নিয়মাবলী সম্পর্কিত শাস্ত্র) ফার্সে উৎপত্তি লাভ করে ফার্সেই সমাপ্তি ঘটেছে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো নাহু ফার্সের সিবাভেইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর বিকাশ আবু আলী ফারেসীর মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত কথায় অতিরঞ্জন রয়েছে।
11. আবদুল কাহের জুরজানী: তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ,ব্যাকরণবিদ ,অভিধান রচয়িতা ও অলংকারশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য আবদুল কাহেরের প্রসিদ্ধি বিশেষত অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত) ও বাগ্মিতায়। তদুপরি তিনি বৈয়াকরণ হিসেবেও পরিচিত।
বালাগাত বা অলংকারশাস্ত্রে তাঁর কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে ,যেমন আসরারুল বালাগাহ্ ,দালায়িলুল ইজায ,ইজাযুল কোরআন প্রভৃতি। তিনি 471 অথবা 474 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রসিদ্ধ আরো কিছু ব্যাকরণবিদ ইরানী ছিলেন। এখানে আমরা শুধু তাঁদের নাম উল্লেখ করছি: খালফ আহমার (দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর) ,আবু হাতেম সাজেসতানী ,ইবনে সিককীত আহওয়াযী (শিয়া ছিলেন) , ‘ আদাবুল কাতিব ’ গ্রন্থের লেখক ইবনে কুতাইবা দিনওয়ারী। ইবনে কুতাইবা দিনওয়ারী এ গ্রন্থ ছাড়াও উয়ুনুল আখবার ,আল মা ’ আরিফ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবু হানিফা দিনওয়ারী ভাষাবিদ ছাড়াও ঐতিহাসিক ,গণিতবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। আবু বাকর ইবনিল খাইয়াত সামারকান্দীসহ পূর্বোক্তগণ তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর ইরানী ব্যাকরণবিদগণের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারযবান সিরাফী সিরাজী (পূর্বে তাঁর পরিবার মাজুসী ছিল ও পরবর্তীতে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন) ,ইউসুফ ইবনে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারযবান সিরাফী ,আবু বাকর খাওয়ারেজমী তাবারিস্তানী এবং ইবনে খলাভেই হামেদানী। এ ছাড়া পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর আবু মুসলিম ইসফাহানী এবং সপ্তম হিজরী শতাব্দীর নাজমুল আইম্মা রাযী আসতারাবাদী প্রসিদ্ধ ইরানী ব্যাকরণবিদগণের অন্তর্ভুক্ত।
আরবী ভাষার অলংকারশাস্ত্রেও অনেক ইরানী অবদান রেখেছেন ,যেমন আবদুল কাহের জুরজানী ,মুহাম্মদ ইবনে ইমরান মারযবানী খোরাসানী (তিনি একজন শিয়া এবং বলা হয়ে থাকে আরবী ভাষার বর্ণনাশাস্ত্রে তিনি পুরোধা ছিলেন। তিনি 371 হিজরীতে মারা যান) ,যামাখশারী ,সাহেব ইবনে ইবাদ তালেকানী (385 হিজরীতে মৃত্যু) ,সাক্কাকী খাওয়ারেজমী (মৃত্যু সপ্তম হিজরী শতাব্দী) ,সাক্কাকীর ‘ মিফতাহ্ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচয়িতা কুতুব উদ্দীন সিরাজী (মৃত্যু 710 হিজরী) ,তাফতাযানী নাসয়ী অথবা সারাখসী (মৃত্যু 791 হিজরী) এবং মীর সাইয়্যেদ শারিফ জুরজানী (মৃত্যু 816 হিজরী) ।
আরবী অভিধানশাস্ত্রবিদগণের মধ্যেও অনেক ইরানী রয়েছেন। যেমন ‘ সেহহাহুল লুগাত ’ গ্রন্থের রচয়িতা জাওহারী নিশাবুরী (মৃত্যু চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) ,রাগেব ইসফাহানী (তিনি ‘ মুফরাদাতুর রাগেব ’ নামক অভিধান গ্রন্থ রচনা করেন ও 565 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন) , ‘ কামুসুল লুগাত ’ গ্রন্থের রচয়িতা মাজদুদ্দীন ফিরুযাবাদী (মৃত্যু 816 হিজরী) , ‘ আস্ সামী ফিল আসামী ’ গ্রন্থের রচয়িতা মাইদানী নিশাবুরী (তিনি ‘ মাজমাউল আমছাল ’ নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং 518 হিজরীতে মারা যান) এবং অন্যান্য অনেকেই।
মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অনেকে ইরানী। যেমন আবু হানিফা দিনওয়ারী ,ইবনে কুতাইবা দিনওয়ারী ,তাবারী ,বালাজুরী (মৃত্যু 279 হিজরী) ,আবুল ফারাজ ইসফাহানী (তিনি উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত ও 356 হিজরীতে মারা যান) ,হামযা ইসফাহানী (মৃত্যু 350 হিজরী) প্রমুখ।
মুসলিম ঐতিহাসিকদের সংখ্যা প্রচুর। সম্ভবত ইতিহাসের মতো খুব কম বিষয়েই এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
‘ মুসলমানরা অন্যান্য সকল জাতি হতে ইতিহাসে অগ্রসর ছিল ও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিল। ‘ কাশফুল জুনুন ’ গ্রন্থে মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা 1300 বলা হয়েছে। অবশ্য এ সংখ্যা শুধু মূল গ্রন্থের ;ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ নয় এবং সংক্ষিপ্ত ও বিলুপ্ত গ্রন্থসমূহের নামও সেখানে আনা হয়নি... ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর ‘ মুরুজুয যাহাব ’ গ্রন্থে তাঁর সময়ে বিদ্যমান প্রচুর ইতিহাস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন... । ’
ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন জাতি অংশগ্রহণ করেছে ,যেমন স্পেনের ইবনে আবদুল বার ,ইবনে বাশকাওয়াল ও ইবনে আবার ,মিশরের মাকরিযী ও জামাল উদ্দীন কাফতী ,সিরিয়ার ইবনে আসাকির ও সাফাদী ,ইরাকের খতিব বাগদাদী ,আবদুর রহমান ইবনিল জাওযী ও তাঁর দৌহিত্র শামসুদ্দীন আবুল মুজাফ্ফার ইবনিল জাওযী ,ইরানী বংশোদ্ভূত ইবনে খাল্লেকান আরবিলী এবং তিউনিসিয়ার ইবনে খালদুন।
ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। যেমন জীবনী বা সিরাত গ্রন্থ (যেমন সীরায়ে নাবাভী) ,বিশেষ ব্যক্তি ,কোন সম্রাট বা বাদশার ইতিহাস ,শহরের ইতিহাস (যেমন তারিখে কোম) ,দেশের ইতিহাস (তারিখে মিশর ,তারিখে দামেস্ক প্রভৃতি) ,বিশেষ জ্ঞান বা শাস্ত্রের ইতিহাস (যেমন তাবাকাতুল হুকামা ,তাবাকাতুল আতেব্বা ,তাবাকাতুল হুফ্ফাজ প্রভৃতি) ,সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ (যেমন তারিখে ইয়াকুবী ,তারিখে তাবারী)। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক ভূগোলবিদও ইতিহাস লিখেছেন ,যেমন ‘ আহসানুত্ তাফাসীর ’ গ্রন্থের লেখক আল মাকদেসী , ‘ সুয়ারুল আকালিম ’ ও ‘ মাসালিকুল মামালিক ’ গ্রন্থের লেখক ইসতাখরী ফারেসী প্রমুখ। আল্লামা সুয়ূতীর অনুসরণে জর্জি যাইদান ইসলামী যুগের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক হিসেবে দু ’ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন :
একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি একজন শিয়া ও ইরানী এবং অপরজন হলেন উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়ামের পুত্র)। কিন্তু আল্লামা সাইয়্যেদ হাসান সাদর প্রমাণ করেছেন ইসলামের সর্বপ্রথম ইতিহাস রচয়িতা হযরত আলীর বায়তুল মাল রক্ষক উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে। তিনি একজন মিশরীয় ও কিবতী বংশের। তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আলীর খেলাফতকালের তাঁর সহযোগী ব্যক্তিবর্গের বিবরণ রয়েছে।
যদি ‘ সীরায়ে নাবাভী ’ ও ‘ সীরায়ে ইবনে হিশাম ’ 284 গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মাতলাবী ইরানী হয়ে থাকেন তবে বলা যায় ইবনে আবি রাফের পর ইসলামের ইতিহাসে যে দু ’ ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁদের একজন ইরানী ও অপরজন আরব কোরেশী (উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর)। তবে বর্তমানে এ তিন ব্যক্তির মধ্যে শুধু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের লিখিত গ্রন্থ আমাদের হাতে রয়েছে ,অন্য দু ’ টি বিলুপ্ত হয়েছে।
ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে প্রথম যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা ‘ মাওয়ালী ’ ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।
‘ মাওয়ালী ’ শব্দটির অর্থ সম্ভবত অনারব। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই যে , ‘ মাওয়ালী ’ বলতে ইরানীদের নাকি অনারবদের সকল জাতিকে ,নাকি আরবদের বিভিন্ন গোত্র যারা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ তাদের বোঝান হয়। ইবনুন নাদিম ঐতিহাসিকদের অনেককেই মাওয়ালী বলে উল্লেখ করেছেন ও তাঁদের অনেকেই ইরানী ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। তিনি যাঁদের নিশ্চিতভাবে ইরানী বলেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়াকেদী (মৃত্যু 207 হিজরী) ,আবুল কাসেম হাম্মাদ ইবনে সাবুর দাইলামী (মৃত্যু 156 হিজরী) ,আবু জান্নাদ ইবনে ওয়াসেল আল কুফী ,আবুল ফাযল মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল হামিদ আল কাতিব এবং আলান শুয়ূবী কুলাইনী রাযী।
আমাদের উপরোক্ত আলোচনা হতে কেউ যেন অসচেতনভাবে না ভাবেন যে ,আরবী ভাষা ,সাহিত্য ,ব্যাকরণ ,অভিধানশাস্ত্র ,অলংকারশাস্ত্র ,ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে কেবল ইরানীরাই ভূমিকা রেখেছেন ;বরং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে অন্যান্য জাতির মানুষ ,যেমন আরব ,মিশরীয় ,স্পেনীয় ,সিরীয় ,তুর্কী ,কুর্দী ও রোমীয় সকলেই অবদান রেখেছে যাঁদের অনেকেই বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আমরা এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তাঁদের নাম উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি।
আরবী ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ চারটি গ্রন্থ ও এগুলোর রচয়িতা: ইবনে কুতাইবা দিনওয়ারীর ‘ আদাবুল কাতিব ’ ,মুবাররেদ রচিত ‘ আল কামিল ’ ,জাহিয রচিত ‘ আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন ’ এবং আবু আলী কালীর ‘ নাওয়াদের ’ ।
এ চার প্রসিদ্ধ লেখকের শুধু একজন ইরানী ,আর তিনি হলেন ইবনে কুতাইবা। তা ছাড়া মুবাররেদ হলেন আযদী আরব ,জাহিয হলেন কিনানী আরব এবং আবু আলী কালী হলেন এশিয়া মাইনর বা তুরস্কের দিয়ারবেকীরর অধিবাসী।
আহমাদ আমিন তাঁর ‘ দোহাল ইসলাম ’ গ্রন্থে ‘ আল মুযহার ’ গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন ,দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে আরবী ভাষা ,অভিধান ও কবিতার ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল ,যাঁদের পূর্বে ও পরবর্তীতে সমকক্ষ কেউ আসেনি। তাঁরা হলেন :
1. আবু যাইদ আনসারী খাজরাজী (মৃত্যু 215 হিজরী)।
2. আসমায়ী (প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ,মৃত্যু 215 হিজরী)।
3. আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনুল মুসান্না (মৃত্যু 210 হিজরী)।
উপরোক্ত তিনজনের মধ্যে একমাত্র আবু উবাইদা ইরানী বংশোদ্ভূত। আবু যাইদ মদীনার খাজারাজ গোত্রীয় আরব এবং আসমায়ী বাহেলী আরব।
কালামশাস্ত্র
কালামশাস্ত্র ইসলামের একটি নিজস্ব জ্ঞান। কালামশাস্ত্র ইসলামের মৌলবিশ্বাস ও এর প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত গবেষণামূলক জ্ঞান। কালামশাস্ত্রে আল্লাহর একত্ববাদ ও গুণাবলীকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলী) জ্ঞান যেমন রয়েছে তেমনি ওহী ও হাদীসনির্ভর বর্ণনামূলক (নাকলী) জ্ঞানও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শিয়াদের দৃষ্টিতে ইমামত। সুতরাং কালামশাস্ত্র আকলী ও নাকলী জ্ঞানের সমন্বয়ে সৃষ্ট।
ইসলামের মতো ধর্মে যা স্রষ্টা ,সৃষ্টি ,পুনরুত্থান ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ও এ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছে এরূপ একটি জ্ঞান বিদ্যমান থাকা আবশ্যকীয়। বিশেষত প্রথম শতাব্দীগুলোতে মুসলিম সমাজে জ্ঞানের প্রতি যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তাতে কালামশাস্ত্রের ন্যায় জ্ঞানের উদ্ভব ঘটা স্বাভাবিক ছিল।
পবিত্র কোরআন তাওহীদ ,নবুওয়াত ও আখেরাতের মতো আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক স্থানে দলিল উপস্থাপন করেছে এবং এর বিরোধীদেরকে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে। যেমন বলেছে ,قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‘ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে প্রমাণ উপস্থাপন কর। ’ 285
নিঃসন্দেহে ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ,যেমন সসীম ও অসীম ,স্রষ্টা ও সৃষ্ট ,স্থান-কালের ঊর্ধ্বে ও স্থান-কালের অধীন ,বাধ্যবাধকতা ,স্বাধীনতা (জাবর ও ইখতিয়ার) ,মৌলিকত্ব ও যৌগিকতা ও এরূপ অন্যান্য আলোচনা সর্বপ্রথম হযরত আলী (আ.) উপস্থাপন করেছেন। এ কারণেই শিয়াগণ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল।
ইসলামে ইরানীদের অবদানের আলোচনায় কালামশাস্ত্রে ইরানীদের ভূমিকার বিষয়টি শিয়া কালামশাস্ত্রবিদদের দিয়ে শুরু করছি।
1. প্রথম শিয়া কালামশাস্ত্রবিদ যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি হলেন আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে মাইসাম তাম্মার। তাঁর পিতামহ মাইসাম হযরত আলীর বিশিষ্ট সাহাবী ও প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। তিনি বাহরাইনের হিজরের অধিবাসী হলেও বংশগতভাবে ইরানী ছিলেন। তাঁর পৌত্র আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে মাইসাম ,দারার ইবনে আমর ,আবুল হাযিল আলাফ ও আমর ইবনে উবাইদের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। এরা সকলেই দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর কালামশাস্ত্রবিদ। তিনি এদের সঙ্গে কালামশাস্ত্রীয় আলোচনা করতেন।
2. হিশাম ইবনে সালেম জাওযাজানী: এই ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)-এর বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সাহাবী। ইমাম সাদিকের কিছু সাহাবীকে ইমাম নিজে ‘ কালামশাস্ত্রবিদ ’ বলে অভিহিত করেছিলেন ,যেমন হামরান ইবনে আইয়ান ,মুমিন আলতাক ,কাইস ইবনিল মাসের ,হিশাম ইবনে হাকাম প্রমুখ।286
কাইস ইবনিল মাসের ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন জয়নুল আবেদীন (আ.)-এর নিকট কালাম শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে।
3. ফাযল ইবনে আবু সাহল ইবনে নওবাখত: তিনি নওবাখত বংশের। ইবনুন নাদিমের বর্ণনা মতে এ বংশটি শিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ ও তিন শতাব্দী ধরে তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ আলেমের আগমন ঘটেছিল। ফাযলের পিতামহ নওবাখত একজন জ্যোতির্বিদ ও আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের দরবারে কর্মরত ছিলেন।
একদিন নওবাখত তাঁর পুত্র আবু সাহলকে মনসুরের দরবারে নিয়ে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। মনসুর তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন , ‘ খুরশীদ মাহ তিমাযাহ মা বজারাদ বাদ খসরু না শাহ। ’ মনসুর বলেন , ‘ এর পুরোটাই তোমার নাম ? ’ তিনি বলেন , ‘ হ্যাঁ। ’ মনসুর হেসে বলেন , ‘ তোমার বাবা তোমার কি অবস্থা করেছে! তোমার নামকে সংক্ষিপ্ত কর ,তিমাযা রাখ নতুবা আমার দেয়া ‘ আবু সাহল ’ নামটি গ্রহণ কর। ’ আবু সাহল এ নাম গ্রহণে রাজী হলেন।287 এর পরবর্তীতে নওবাখতীদের অধিকাংশের নাম ‘ আবু সাহল ’ রাখার প্রচলন ছিল।
শিয়া কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকেই নওবাখতী বংশের ,যেমন ফাযল ইবনে আবি সাহল ইবনে নওবাখত যিনি খলীফা হারুনের ‘ বায়তুল হিকমাহ্ ’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল ও ফার্সী হতে আরবীতে গ্রন্থসমূহ অনুবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তেমনি ইসহাক ইবনে আবি সাহল ইবনে নওবাখত ,তাঁর দু ’ পুত্র ইসমাঈল ইবনে ইসহাক ইবনে আবি সাহল ও আলী ইবনে ইসহাক নওবাখত এবং পৌত্র আবু সাহল ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনে ইসহাক সকলেই শিয়া কালামশাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষত আবু সাহল ইসমাঈল ইবনে আলী শিয়াদের মধ্যে ‘ শাইখুল মুতাকাল্লিমীন ’ (কালামশাস্ত্রবিদগণের নেতা) উপাধি পান। তাঁর ভাগ্নেয় হাসান ইবনে মূসা নওবাখতীসহ ইরানী এ বংশটির আরো কিছু ব্যক্তি প্রসিদ্ধ শিয়া মুতাকাল্লিমদের
অন্তর্ভুক্ত।
4. ফাযল ইবনে শাজান নিশাবুরী: তিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ফাযল ইবনে শাজান ইমাম রেযা (আ.) ,ইমাম জাওয়াদ এবং ইমাম হাদী (আ.)-এর শিষ্য হিসেবে পরিগণিত। তিনি কালামশাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
5. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মামলাক জুরজানী ইসফাহানী: তিনি তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবু আলী জাবায়ীর সমসাময়িক।
6. আবু জাফর ইবনে কুব্বা রাযী: তিনি তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর কালামশাস্ত্রবিদদের অন্যতম। তিনি ইমামতের বিষযে আবুল কাসেম কা ’ ব বালখীর সঙ্গে পত্র বিনিময় ও বিতর্ক করেছেন।
7. আবুল হাসান সুসানগারদী: তিনি ইবনে কুব্বা রাযীর সমসাময়িক। কথিত আছে তিনি আবু সাহল ইসমাঈল ইবনে আলী নওবাখতীর দাস ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বার হেঁটে হজ্বব্রত পালন করেন।
8. আবু আলী ইবনে মাসকাভীয়ে রাযী ইসফাহানী: তিনি ইসলামের বিশিষ্ট কালামশাস্ত্রবিদ ,দার্শনিক ও চিকিৎসকদের অন্যতম। এ শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ দু ’ টি গ্রন্থ হলো ‘ আল ফাউযুল আকবার ’ ও আল ফাউযুল আসগার ’ যা বর্তমানে মুদ্রিত ও ছাপা হয়েছে। তাঁর লিখিত ‘ তাহারাতুল আরাক ’ ইসলামী নৈতিকতার বিষয়ে লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনার সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব এবং 431 হিজরীতে মারা যান।
শিয়া কালামশাস্ত্রবিদগণ ইরানী অ-ইরানী সব মিলিয়ে অনেক। আমরা শুধু উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় হতে চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর কিছু সংখ্যক কালামশাস্ত্রবিদের নাম উল্লেখ করলাম। অবশ্য সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদদের মূল ভিত্তি হিসেবে শিয়া কালামশাস্ত্রবিদরাই মুখ্য।
বিশিষ্ট দার্শনিক ,কালামশাস্ত্রবিদ ,গণিতবিদ ও রাজনীতিক খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর আবির্ভাব ও ‘ আত তাজরীদ ’ গ্রন্থ রচনার ফলে শিয়া কালামশাস্ত্র বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং এর পরবর্তীতে শিয়া ও সুন্নী উভয় কালামশাস্ত্রই এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে আলোচনা উপস্থাপন শুরু করে।
সুন্নী কালামশাস্ত্রবিদগণ
আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদই ইরানী।
1 ও 2. আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে প্রাচীন কালামশাস্ত্রবিদ হলেন হাসান বাসরী। অতঃপর তাঁর ছাত্র ওয়াসেল ইবনে আতা গাজাল। এরা উভয়েই ইরানী। হাসান বাসরী প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষার্ধ হতে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধের কিছুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি 110 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।288
ওয়াসেল ইবনে আতা তাঁর ছাত্র হলেও তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন মতবাদের জন্ম দেন। তাঁর মতবাদ ‘ মুতাযিলা ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 181 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।289
3. আবুল হাযিল আলাফ: এ ব্যক্তিও ইরানী। তাঁকে আহলে সুন্নাতের বুদ্ধিবৃত্তিক কালামশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি দর্শন গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং বিতর্কে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। একবার মিলাস নামের এক মাজুসী লেখক তাঁর কিছু সঙ্গীকে নিয়ে আবুল হাযিলের সঙ্গে একত্ববাদ ও দ্বিত্ববাদ নিয়ে বিতর্ক করতে আসেন। আবুল হাযিল তাদের পরাস্ত করলে মিলাস মুসলমান হন। শিবলী নোমানী তাঁর ‘ তারিখে ইলমে কালাম ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,কয়েক হাজার ইরানী মাজুসী আবুল হাযিলের মাধ্যমে মুসলমান হয়। বিধর্মীরা তাঁর সঙ্গে বিতর্কে ভীত থাকত। কারণ তিনি বিতর্কে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবী সালেহ ইবনে আবদুল কুদ্দুসের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের প্রসিদ্ধ কাহিনীটি ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবুল হাযিল একমাত্র যে ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্কে ভয় পেতেন তিনি হলেন হিশাম ইবনে হাকাম যিনি ইমাম সাদিকের শিষ্য ও প্রসিদ্ধ শিয়া কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন।290
4. ইবরাহীম ইবনে সাইয়ার (নিযাম নামে প্রসিদ্ধ): ইবনে খাল্লেকান তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করিম শাহরেস্তানীর জীবনী আলোচনায় এ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাঁকে বালখের অধিবাসী বলেছেন । কালামশাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর মত প্রসিদ্ধ। নিযাম হিশাম ইবনে হাকামের ছাত্র ছিলেন।
5. আমর ইবনে উবাইদ ইবনে বাব: তাঁর পিতা বসরার নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীতে কাজ করতেন। আমর ইবনে উবাইদ 80 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 150 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
আমর ইবনে উবাইদ খারেজী291 চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত এবং উন্নত চিন্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের পূর্ব পরিচিত বন্ধু ছিলেন। মনসুর তাঁর খেলাফতের সময় একদিন তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি মনসুরের নিকট এলে মনসুর তাঁকে উপদেশ ও নসিহত করতে বলেন। তিনি মনসুরকে যে উপদেশ দেন তাতে বলেন , ‘ যে রাজত্ব তোমার হস্তগত হয়েছে তা যদি কারো জন্য স্থায়ী হতো তবে কখনই তা তোমার হাতে এসে পৌঁছত না। ঐ রাত্রিকে স্মরণ কর যার পর আর কোন রাত নেই। ’ আমর এ কথা বলে চলে যেতে উদ্যত হলে মনসুর তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। মনসুর তাঁকে কসম দিয়ে তা গ্রহণের কথা বলেন। আমরও কসম করে তা গ্রহণ না করার কথা বলেন। সে মুহূর্তে মনসুরের পুত্র ও ঘোষিত উত্তরাধিকারী মাহ্দী অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বলেন , ‘ এর অর্থ কি ? আপনি খলীফার বিপরীতে কসম করছেন ? ’ আমর মনসুরকে প্রশ্ন করেন , ‘ এই যুবক কে ? ’ মনসুর বলেন , ‘ আমার পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ’ আমর তাঁকে বলেন , ‘ তাকে সৎ কর্মশীলদের মতো পোশাক পরিয়েছ ও উত্তম নাম (মাহ্দী) রেখেছ ,অথচ সে এ দু ’ টির কোনটিরই উপযুক্ত নয়। তার জন্য এমন এক পদ নির্ধারণ করেছ যা তাকে দান করা অসচেতনতা ছাড়া কিছু নয়। ’ অতঃপর আমর মাহ্দীর দিকে তাকিয়ে বলেন , ‘ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এতে কোন অসুবিধা নেই যে ,তোমার পিতা কোন বিষয়ে কসম করবে এবং তোমার চাচা তা ভঙ্গের জন্য কসম করবে। যদি আমি ও তোমার পিতার মধ্যে যে কোন একজন কসম ভঙ্গ করি তবে তার কাফ্ফারা দানের ক্ষমতা তোমার পিতার রয়েছে ;আমার নেই। ’ মনসুর তাঁকে বলেন , ‘ কোন কিছু চাওয়ার থাকলে আমাকে বল। ’ আমর বলেন , ‘ আমার একটিই চাওয়া। আর তা হলো আমাকে আর কখনও ডেকে পাঠিয়ো না। ’ মনসুর বলেন , ‘ এর ফলে তুমি মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। ’ আমর বলেন , ‘ আমিও তাই চাই। ’ এ কথা বলে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে দরবার হতে বেড়িয়ে গেলেন। মনসুর তাঁর যাওয়ার পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি আপন মনে নিম্নোক্ত কবিতা পড়তে লাগলেন :
‘ কিরূপ দেখলে তার ধীর গতির প্রস্থান
যে চায় সে-ই হয় শিকার
আমর ইবনে উবাইদ ছাড়া সে অন্য কেউ নয়। ’ 29 2
আমর ইবনে উবাইদ হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর পাঠ দানের সময় হিশাম ইবনে হাকাম একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে সেখানে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে ইমামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে পরাস্ত করেন। আমর ইবনে উবাইদ এ প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার দক্ষতায় বুঝতে পারেন তিনি হিশাম ইবনে হাকাম। ফলে তাঁর প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেন (যদিও তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন)।293
উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ আহলে সুন্নাতের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির প্রসিদ্ধ ইরানী কালামশাস্ত্রবিদ। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে অসংখ্য ইরানী সুন্নী কালামশাস্ত্রবিদের উদ্ভব ঘটেছিল। আমরা এখানে শতাব্দীর পর্যায়ক্রমে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি।
আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক রাভান্দী কাশানী ,ইবনুল মুনজেম নাদিমুল মুয়াফ্ফাক ,সাসানী শাসক ইয়ায্দ গারদের বংশধারার আল মুকতাফি বিল্লাহ্ ,আবুল কাসেম কা ’ বী বালখী ,আবু আলী জাবায়ী খুজিস্তানী ,তাঁর পুত্র আবু হাশেম জাবায়ী প্রমুখ তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর ,আবু মনসুর মাতুরিদী সামারকান্দী ,ইবনে ফুরাক ইসফাহানী নিশাবুরী ,আবু ইসহাক ইসফারাইনী প্রমুখ চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর ,আবু ইসহাক সিরাজী ,ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী ,ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর এবং ফাখরুদ্দীন রাযী ,আবুল ফাযল ইবনুল আরাকী ও শাহরেস্তানী ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর সুন্নী ইরানী কালামশাস্ত্রবিদ।
দর্শন ও প্রজ্ঞা
প্রচলিত অর্থে দর্শন চর্চা মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে মূলত গ্রীক বিভিন্ন গ্রন্থ (কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়) আরবীতে অনূদিত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। অবশ্য দর্শন ,গণিতবিদ্যা ,চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞানের গ্রন্থসমূহের অনুবাদ কখন হতে শুরু হয় সে সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে। কারো কারো দাবি হলো ,এ কাজ সর্বপ্রথম প্রথম হিজরী শতাব্দীতে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার সময় শুরু হয়।
কথিত আছে খালিদ প্রথম ব্যক্তি যিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত কতিপয় ব্যক্তিকে এ কর্মে নিয়োগ করেন। তাঁরা রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক কিছু গ্রীক ও মিশরীয় (কিবতী) গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।294
নিঃসন্দেহে আব্বাসীয় বংশের শাসনকালে দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ শুরু হয়। এ সময়ে নৈতিকতা এবং সামাজিক রীতিসম্বলিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পের গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়।
ফার্সী ভাষা হতে দর্শনশাস্ত্রের কোন গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়নি। যে সকল ইরানী গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে তন্মধ্যে সাহিত্য ,ইতিহাস ,জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রকৃতিবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরস্ত ’ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ফার্সী ভাষার যে সব গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর কোনটিই দর্শন সম্পর্কিত ছিল না। দর্শন সম্পর্কিত একমাত্র যে গ্রন্থটি আরবীতে অনূদিত হয়েছিল তা ছিল গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা যা পাহলভী ভাষায় পূর্বে অনূদিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ইসলামী শাসনামলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফা ’ অথবা তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফার মাধ্যমে পাহলভী ভাষা হতে আরবীতে অনূদিত হয়েছিল।
ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম প্রবন্ধে (দর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধে) বলেছেন ,
‘ পূর্বে গ্রীস ও রোমে দর্শন চর্চার প্রচলন ছিল। রোম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে দর্শন চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে কোন কোন দর্শন গ্রন্থ পুড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কোনটি শিক্ষিত ব্যক্তিরা লুকিয়ে ফেলেন। এ সময় সর্বসাধারণের জন্য দর্শন চর্চাকে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ তারা দর্শনকে খ্রিষ্টধর্মের (বিধানের) পরিপন্থী মনে করত। অতঃপর রোম সময়ের পরিক্রমায় খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দর্শনের দিকে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে। এটি ঘটে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশিষ্ট দার্শনিক ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকার ব্যক্তিত্ব সামিসথিউস রোমের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ’
ইবনুন নদিম অতঃপর ইরান সম্রাট শাপুর যুল আকতাফের সঙ্গে রোম সম্রাটের যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। এ যুদ্ধে শাপুর বন্দী হন। কিন্তু জেলখানা হতে পালিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তিনি রোমীয়দের ইরান হতে বহিষ্কার করেন এবং তাঁর সমর্থনেই কনস্টান্টিনোপল রোমের সম্রাট হন। এ সময়েই রোম দ্বিতীয় বারের মতো খ্রিষ্টধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও দর্শনের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইবনুন নাদিম আরো উল্লেখ করেছেন ,
‘ ইরানীরা গ্রীক হতে যুক্তিবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থ পূর্বেই পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করেছিল যা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফা ’ ও অন্যরা আরবীতে অনুবাদ করেন।295
বাহ্যত ইরানে কোন দর্শন গ্রন্থই অনূদিত হয়নি। গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষার দর্শন গ্রন্থসমূহের কোন অনুবাদকও ইরানী ছিলেন না। কিন্তু ইসলামী সভ্যতায় ইরানীদের অবদানের একটি অংশ হিসেবে অনুবাদশাস্ত্রে তাঁদের ভূমিকা এখানে তুলে ধরছি। আমরা ইবনুন নাদিমের ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ অবলম্বনে ফার্সী হতে আরবীতে অনুবাদকারী ইরানী ব্যক্তিবর্গের নাম এখানে উল্লেখ করছি। (অবশ্য ফার্সী হতে আরবীতে অনুবাদক সকলেই ইরানী ছিলেন না)।
আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফা ’ অ্যারিস্টটলের গ্রীক যুক্তিবিদ্যা ,ফার্সী গ্রন্থ ‘ খোদায়ীনামে ’ যা ফেরদৌসীর শাহনামা গ্রন্থের মূল উৎস এবং সম্রাট আনুশিরওয়ানের সময় ফার্সীতে অনূদিত ভারতীয় গ্রন্থ ‘ কালিলা ওয়া দিমনা ’ উচ্চমানের আরবীতে অনুবাদ করেন। অন্যতম বিশিষ্ট অনুবাদক হলেন খলীফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তি ‘ বাইতুল হিকমা ’ র প্রধান আবু সাহল ফাযল ইবনে নওবাখত। এ ছাড়া হাসান ইবনে মূসা নওবাখতী ,প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ‘ ফুতুহুল বুলদান ’ গ্রন্থের লেখক আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া বালাজুরী ,মূসা ইবনে খালিদ ,ইউসুফ ইবনে খালিদ ,আলী ইবনে যিয়াদ তামিমী ,হাসান ইবনে সাহল ,আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া জাবের ,হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের দলিল লেখক জাবাল্লাহ্ ইবনে সালেম ,ইসহাক ইবনে ইয়াযীদ ,মুহাম্মদ ইবনে জাহাম বারমাকী ,হিশাম ইবনুল কাসেম ,মূসা ইবনে ঈসা আল কুর্দী ,যদাভী ইবনে শাহভীয়ে ইসফাহানী ,মুহাম্মদ ইবনে বাহরাম ইবনে মিতইয়ার ইসফাহানী ,বাহরাম ইবনে মারদানশাহ্ ,আমর ইবনুল ফারখান , ‘ বায়তুল হিকমা ’ র দায়িত্বশীল সালেম ,হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের রাজকীয় দলিল লেখক সালেহ ইবনে আবদুর রহমান এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আলীর নাম উল্লেখযোগ্য।
এখন আমরা মুসলিম দার্শনিকদের পর্যায়ক্রমিক (শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত) বিবরণ প্রদান করব। পূর্বে ফিকাহ্শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে এরূপ বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন হলেও এ শাস্ত্রে তা হয়নি বিধায় এ পর্বটির মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে ।
যদিও এ কাজ সহজ নয় ,কিন্তু যেহেতু ইসলামী সভ্যতায় দর্শনের ইতিহাস নিয়ে আমি পূর্বে কাজ করেছি সেহেতু এ বিষয়ের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। ইসলামী দর্শনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে হলে অবশ্যই বিভিন্ন যুগের দার্শনিকদের পরিচিতি জানা প্রয়োজন। আমরা এখানে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে দার্শনিকদের পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করব।
ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে দার্শনিকদের পর্যায়ক্রমিক এ বিন্যাসে আমরা সে সব দার্শনিকের নামই উল্লেখ করব যাঁরা ইসলামী পরিবেশে কার্যক্রম চালিয়েছেন। এদের অনেকেই হয়তো মুসলমান নন ;বরং ইহুদী বা খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান হলেও তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বা কারো কারো মতে তাঁরা নাস্তিক ছিলেন। আমরা এদের নাম উল্লেখের পর (প্রথম যুগ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত) সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।
প্রথম স্তরের দার্শনিক
ইসলামী দর্শন ‘ ফিলসুফুল আরাব ’ নামে প্রখ্যাত দার্শনিক আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দীর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। আল কিন্দী খাঁটি আরব এবং আব্বাসীয় খলীফা মামুন ও মুতাসিম বিল্লাহর সমসাময়িক। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব হলেন হুনাইন ইবনে ইসহাক ও আবদুল মাসিহ ইবনে নায়েমা হামাছী। তাঁরা উভয়েই প্রসিদ্ধ অনুবাদক। ‘ উসূলুজিয়া ’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে ,এ গ্রন্থটি আবদুল মাসিহ অনুবাদ করেছেন এবং আবু ইয়াকুব কিন্দী তা সংস্কার ও সংশোধন করেছেন। স্বয়ং আবু ইয়াকুব অনুবাদক ছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। অবশ্য কিন্দীর ছাত্র আবু মাশার বালখী বর্ণনা করেছেন ,কিন্দী ইসলামী শাসনামলের প্রথম শ্রেণীর চারজন অনুবাদকের অন্যতম। কিন্দীর সময়কাল ইসলামী সভ্যতার অনুবাদের যুগ হলেও কিন্দী দর্শনের ক্ষেত্রে উচ্চতর অবস্থানে ছিলেন ও স্বতন্ত্র মতের অধিকারী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তাঁর প্রায় দু ’ শ ’ সত্তরটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা ছিল। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা ,দর্শন ,জ্যোতির্বিদ্যা ,গণিতশাস্ত্র ,জ্যামিতি ,চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর রচিত তাঁর গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়েছেন। কিন্দীর রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থগুলো হতে এই দার্শনিকের মূল্য তাঁর সম্পর্কে পূর্ব ধারণা হতে অনেক বেশি তা বোঝা গিয়েছে। কিন্দী নিঃসন্দেহে বিশ্বের এক বিরল প্রতিভা ও ইসলামী সভ্যতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। কোন কোন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ তাঁকে বিশ্ব ইতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের শ্রেষ্ঠ বারোজন ব্যক্তির অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।296
কিন্দী আত্মপরিশোধিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পূর্বের ও পরের মুসলমান ও অমুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর ন্যায় উত্তম ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।
কিন্দী বসরা ও বাগদাদে শিক্ষাজীবন কাটালেও সে সময় এ দু ’ স্থানে কোন দার্শনিকই ছিলেন না। তাই কিন্দী তাঁর পূর্বের কোন দার্শনিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন হিসেবে ইসলামী দর্শনের প্রথম বিন্দুতে অবস্থান করছেন।
জনাব তাকী যাদেহ্ তাঁর ‘ তারিখে উলুম দার ইসলাম ’ গ্রন্থে এবং অধ্যাপক হেনরী কেরবেন তাঁর ‘ ইসলামী দর্শনের ইতিহাস ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,কিন্দী তাঁর এক গ্রন্থে (পুস্তিকায়) ইসলামী খেলাফতের সময়কাল কতদিন স্থায়ী হবে তা নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা প্রায় সঠিক হয়েছিল। আমরা এখানে অধ্যাপক কারবানের বক্তব্যটি তুলে ধরছি :
‘ এই দার্শনিক (কিন্দী) তাঁর এক পুস্তিকায় গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা ও কোরআনের তাফসীরের সহায়তায় ইসলামী খেলাফতের স্থায়িত্ব 693 বলেছিলেন। ’
কেউ কেউ বলেছেন , ‘ মুসলমানগণ গ্রীক দর্শনের সঙ্গে গ্রীস ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন দার্শনিকের গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ইহুদী ও খ্রিষ্টান মনীষী ,যেমন কুয়াইরী ,ইউহান্না ইবনে হাইলান ,আবু ইয়াহিয়া আল মারওয়াজী (মারূরুদী সুরইয়ানী) ,আবু বাশার মাত্তা ইবনে ইউনুস ও আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে আদীর মাধ্যমে তা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ বক্তব্যটি সঠিক নয় ;বরং মুসলমানদের দর্শনের পরিচিতি এমনকি তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার দার্শনিকের উদ্ভবও উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের যুগের পূর্বে ঘটেছিল। কারণ ইসলামী দর্শন আবু ইউসুফ ইয়াকুব কিন্দীর মাধ্যমে শুরু হয় এবং তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকে।
উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ ,যেমন ইবরাহীম কুয়াইরী ,ইউহান্না ইবনে হাইলান ,ইবরাহীম মুরুজী ,ইবনে কারনিব আল কিন্দীর ছাত্রদের সমসাময়িক। আবার কেউ কেউ ,যেমন আবু বাশার ইবনে মাত্তা ও ইয়াহিয়া ইবনে আদী প্রমুখ তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং ইসলামী দর্শনে তাঁদের প্রভাব কতটুকু ছিল তাও বিশ্লেষণ করব।
কিন্দী যেমন একদিকে উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক ছিলেন তেমনি পবিত্র চিন্তার অধিকারী ও ধর্মীয় বিশ্বাসের একজন রক্ষক ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সপক্ষে যুক্তিনির্ভর অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। কেউ কেউ তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যকে নির্ভর করে তাঁকে শিয়া বলেছেন। কিন্দী সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ইসলাম ও দর্শনের মৌলনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ইসলামের পক্ষাবলম্বন করতেন। যেমন বিশ্বজগতের সৃষ্ট হওয়া ও কিয়ামতে দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়ে তিনি ইসলামের মতকে সমর্থন করেছেন।
কিন্দী সব সময় চেষ্টা করতেন ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনের মৌলনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের। সমন্বয়ের এ বিষয়টি কিন্দীর মাধ্যমে শুরু হয় ও অব্যাহত থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো কেউ কেউ তাঁর নাম ইয়াকুব ,তাঁর পিতার নাম ইসহাক ও উপনাম আবু ইউসুফ হওয়ায় তাঁকে ইহুদী মনে করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তিনি কোরআনের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনার চিন্তা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ বর্ণনা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।
বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে এ বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়েছে যে ,প্রথমত পূর্বে তাঁর কর্মের মূল্য সম্পর্কে যে ধারণা করা হতো তাঁর অবদান তা হতে অনেক বেশি ;দ্বিতীয়ত তিনি একজন পবিত্র হৃদয়ের মুসলমান হিসেবে ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিরক্ষক ছিলেন ;তৃতীয়ত তাঁর সামাজিক ও জ্ঞানগত অবস্থানের কারণে তাঁর প্রতি অন্যরা হিংসা করত ও তাঁর নামে অপপ্রচার চালাত।
পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে ,তিনি তাঁর স্তরের অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের একমাত্র দার্শনিক। তাঁর যুগে তিনি ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিক ছিলেন না। কিন্দী 258 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
দ্বিতীয় স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরে দু ’ দল দার্শনিক রয়েছেন যাঁদের একদল কিন্দীর ছাত্র ও অন্যদল কিন্দীর ছাত্র নন। প্রথম দলের ব্যক্তিবর্গ হলেন :
1. আহমাদ ইবনুন তাইয়্যেব সারাখশী (আবুল আব্বাস): তিনি কিন্দীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র। তিনি 218 হিজরীতে জন্ম ও 286 হিজরীতে কাসেম ইবনে উবাইদুল্লাহর হাতে নিহত হন। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ সারখশীর চুয়ান্নটি গ্রন্থ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন যার কোনটি এখন বিদ্যমান নেই। তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ আল মাসালিক ওয়াল মামালিক ’ যা সম্ভবত ভূগোলশাস্ত্রে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। তিনি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ,যুক্তিবিদ্যা ,দর্শনের মৌলনীতি ও বিতর্কের কৌশল বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।
হেনরী কারবান বলেছেন , ‘ তিনি আরবী ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভাবক এবং হামযা ইসফাহানীর মাধ্যমে এর পূর্ণতা ঘটে। ’ তিনি আরো বলেছেন , ‘ দার্শনিক জেনোর ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা তিনি আরবীতে ব্যাখ্যা করেন ও তা হতে মূল্যবান তথ্য হস্তগত করেন। যদি তিনি তা না করতেন তবে জেনোর দর্শন সম্পর্কে মুসলিম বর্ণনাসমূহে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকত। ’
তিনিও নাস্তিকতার অপবাদ হতে বাঁচতে পারেননি। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে ‘ লিসানুল মিযান ’ ও ‘ আইয়ানুশ শিয়া ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে শিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
2. আবু যাইদ আহমাদ ইবনে সাহল বালখী: তিনি সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। ইবনুন নাদিম তাঁর জীবনী আলোচনায় তাঁকে সাহিত্যিক ও লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ;দার্শনিক হিসেবেও তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।297 তিনি মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযীর জীবনী আলোচনায় মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযী ইবনে বালখীর নিকট দর্শন শিক্ষা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে বালখী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। যদিও তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করেননি যে ,এই ব্যক্তি আবু যাইদ বালখী নাকি অন্য কোন ইবনে বালখী। তিনি বলেছেন , ‘ আমি বিভিন্ন বিষয়ে ইবনে বালখী কর্তৃক লিখিত অনেক গ্রন্থ দেখেছি যেগুলো অসম্পূর্ণ ও খসড়া অবস্থায় ছিল। ’
বালখী দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও ইসলামী সাহিত্যের প্রথম সারির একজন সাহিত্যিক ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সাহিত্যে জাহেযের সমকক্ষ ,আবার কেউ কেউ জাহেযের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন।
ইবনুন নাদিম তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় শারায়িউল আদইয়ান ,নাজমুল কোরআন ,কাওয়ারিউল কোরআন ,গারিবুল কোরআন ও ফাযায়িলু মাক্কা নামক গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে বালখী 322 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ইবনুন নাদিমের ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ ও ইবনে কাফতীর ‘ তারিখুল হুকামা ’ গ্রন্থে বালখী যে কিন্দীর ছাত্র ছিলেন তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাঁকে কিন্দীর ছাত্র বলেছেন। সম্ভবত এ বর্ণনাটি তাঁরা ইয়াকুব হামাভীর ‘ মুজামুল উদাবা ’ গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি বালখী প্রকৃতই 322 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে থাকেন তবে তাঁর পক্ষে কিন্দীর ছাত্র হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কিন্দী 258 হিজরীতে মারা যান ,বালখীর মৃত্যুর 64 বছর পূর্বে তিনি পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। অবশ্য যদি ধরা হয় যে ,বালখী একশ ’ বছরের মতো বেঁচে ছিলেন ,কিন্তু ‘ মুজামুল উদাবা ’ য় উল্লিখিত হয়েছে বালখী 87 বছর বেঁচে ছিলেন। সে ক্ষেত্রে কিন্দীর মৃত্যুর সময় বালখীর বয়স ছিল 23 বছর। তাই বালখী হয় কিছু সময়ের জন্য কিন্দীর ছাত্র ছিলেন নতুবা তাঁর ছাত্রের ছাত্র হিসেবে পরোক্ষভাবে তাঁর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত বালখীও শিয়া ছিলেন। যে কারণে তাঁকেও নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কথিত আছে প্রসিদ্ধ দার্শনিক আবুল হাসান আমেরী বালখীর ছাত্র ছিলেন ,কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তা সঠিক নয় বলে মনে হয়।
3. আবু মাশার জাফর ইবনে মুহাম্মদ বালখী: তিনি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। প্রথম জীবনে কিন্দীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করতেন। কিন্দী বিভিন্ন কৌশলে তাঁকে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আসক্ত করে তাঁর শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতার অপনোদন করেন। ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে তাঁকে কিন্দীর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।298 আবু মাশার একশ ’ র অধিক বছর জীবিত ছিলেন ও 272 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দার্শনিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে অধিকতর প্রসিদ্ধ ।
ইবনুন নাদিম হাসনাভীয়া ,নাফতাভীয়া ,সালামাভীয়া ও এরূপ কাছাকাছি নামের আরেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাঁদের কিন্দীর ছাত্র বলেছেন। এদের সম্পর্কে আমরা ইবনুন নাদিমের বর্ণনার অতিরিক্ত কিছু জানি না। তবে এটুকু জানি ,সালামাভীয়া নামের একজন চিকিৎসক কিন্দীর সমসাময়িক ছিলেন যিনি আব্বাসীয় খলীফা মুতাসিমের বিশেষ চিকিৎসক ছিলেন। ইবনুন নাদিম ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ব্যক্তি সুরিয়ানী ও খ্রিষ্টান ছিলেন। কিন্তু এই সালামাভীয়াকেই ইবনুন নাদিম কিন্দীর ছাত্র বলেছেন কিনা তা আমরা জানি না।
দাবিস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ নামে কিন্দীর অপর এক ছাত্র ছিলেন যাঁর সম্পর্কে ইবনুন নাদিম আলোচনা করেছেন। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ কিন্দীর লিখিত পত্রসমূহের আলোচনায় যারনাব নামের অপর এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেছেন , ‘ এ পত্রটি জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নকারী ছাত্র যারনাবের প্রতি লিখিত। ’
দ্বিতীয় স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা কিন্দীর ছাত্র ছিলেন না তাঁরা হলেন :
1. আবু ইসহাক ইবরাহীম কুয়াইরী: ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে আবুল আব্বাস সারাখশীর নামের পর ইবরাহীম কুয়াইরী নাম উল্লেখ করে বলেছেন , ‘ তাঁর নিকট অনেকেই যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করতেন। তিনি পূর্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যাদাতা ও বিশ্লেষক ছিলেন। ’
ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর ‘ উউনুল আম্বা ’ গ্রন্থে ফারাবীর জীবনী আলোচনায় ফারাবীর বর্ণনা হতে গ্রীসে দর্শনের জন্ম ও সেখান হতে আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থানান্তরের ইতিহাসের আলোচনার পর কুয়াইরীর সম্পর্কে ফারাবীর নিম্নোক্ত বক্তব্য এনেছেন :
‘ ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞান ইনতাকীয়ায় (সিরিয়া) স্থানান্তরিত হয়। ফলে দর্শনজ্ঞানের এমন এক মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যে ,ইনতাকীয়ায় একজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নিকট মারভের এক ব্যক্তি ও হারানের অধিবাসী অপর এক ব্যক্তিই শুধু দর্শন শিক্ষা করেছিলেন । এ দু ’ ব্যক্তি ইনতাকীয়া হতে বেশ কিছু গ্রন্থ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইবরাহীম মুরুজী ও ইউহান্না ইবনে হাইলান মারভের ঐ ব্যক্তির নিকট এবং ইসরাঈল আসকাফ ও ইবরাহীম কুয়াইরী হারানের অধিবাসীর নিকট দর্শন শিক্ষা করেন। ইসরাইল ও কুয়াইরী উভয়েই বাগদাদে যান। ইসরাইল ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যাপৃত হলেও কুয়াইরী শিক্ষা দান শুরু করেন। ইউহান্না ইবনে হাইলানও ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ,কিন্তু ইবরাহীম মুরুজী শিক্ষা দানকে অগ্রাধিকার দেন। আবু বাশার মাতী তাঁর নিকট দর্শন শিক্ষা লাভ করেন।299
অবশ্য ফারাবীর বিস্তারিত বর্ণনা হতে বোঝা যায় ইনতাকীয়ার খ্রিষ্টীয় শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা যুক্তিবিদ্যার মধ্যেই সীমিত ছিল। ফারাবীর নিজের বর্ণনা মতে তিনি ইউহান্না ইবনে হাইলানের নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি বলেন ,যুক্তিবিদ্যা জ্ঞান মুসলমানদের নিকট আসার পরই গীর্জা কর্তৃক যুক্তিবিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়।
মাসউদী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ আত তানবীহ্ ওয়াল আশরাফ ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ আমি ফুনুনুল মা ’ আরিফ ওয়া মা জারা ফিদ দুহুরিস সাওয়ালিফ গ্রন্থে উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রটি ইনতাকীয়ায় স্থানান্তরের কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে তা আন্টাকিয়া হতে হারানে স্থানান্তরিত হয়। মু ’ তাদিদের শাসনামলে300 এ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকতার দায়িত্ব ইবরাহীম কুয়াইরী ,ইউহান্না ইবনে হাইলান (মুক্তাদিরের সময় বাগদাদে মারা যান) ও ইবরাহীম মুরুজীর হাতে অর্পিত ছিল। অতঃপর আবু আহমাদ ইবনে কারনিব ও আবু বাশার মাত্তা এ দায়িত্ব লাভ করেন। ইবনুন নাদিমের বর্ণনা মতে কুয়াইরী আবু বাশার মাত্তার শিক্ষক ছিলেন।
2. আবু ইয়াহিয়া: তিনিই পূর্বোল্লিখিত ইবরাহীম মুরুজী। তিনিও আবু বাশার মাত্তার শিক্ষক ছিলেন । ইবনুন নাদিম বলেছেন , ‘ তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং যুক্তিবিদ্যার সকল গ্রন্থ সুরিয়ানী ভাষায় লিখেছেন। ’ 301
3. ইউহান্না ইবনে হাইলান: পূর্বে ইবরাহীম কুয়াইরীর সঙ্গে তাঁর নাম আমরা উল্লেখ করেছি। বলা হয়ে থাকে তিনি ফারাবীর যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ফারাবী কোথায় তাঁর নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছেন তা জানা যায়নি। অবশ্য কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন ফারাবী যুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য হারানে ইউহান্নার নিকট যান।302
কাফতী বলেছেন ,বাগদাদে তিনি তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন।303 কিন্তু ‘ উয়ুনুল আম্বা ’ য় ফারাবীর বর্ণনা মতে মনে হয় ইউহান্না বাগদাদে আসেননি।
4. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইরানশাহরী নিশাবুরী: এই ব্যক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আবু রাইহান বিরুনী তাঁর ‘ আল আছারুল বাকীয়াহ্ ’ এবং নাসির খসরু তাঁর ‘ যাদাল মুসাফিরিন ’ গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযীর কিছু দার্শনিক চিন্তা ,যেমন স্থানের চিরন্তনতা ,অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের মাঝে একটি বিষয় (هيولا ) তাঁর নিকট থেকে নেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। কথিত আছে তিনি অনারবদের নবী হিসেবে নিজেকে দাবি করেছিলেন।304 ইরানশাহরী কিন্দীর ছাত্র ছিলেন নাকি কুয়াইরী ,ইবনে হাইলান ও মুরুজীর স্তরের তা স্পষ্ট নয়।
উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট যে ,চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত দর্শন শিক্ষায় দু ’ টি ধারা বিদ্যমান ছিল। প্রথম ধারা কিন্দীর মাধ্যমে শুরু হয় এবং তিনি দর্শনের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যা ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,জ্যোতির্বিদ্যা ,সংগীতকলা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা দিতেন। অন্য ধারাতে যুক্তিবিদ্যার অধিক কিছু শিক্ষা দেয়া হতো না।
তৃতীয় স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরে পাঁচ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন :
1. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযী: তিনি ‘ আরবের গ্যালেন ’ 305 নামে প্রসিদ্ধ । তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত চিকিৎসাশাস্ত্রে। এ শাস্ত্রে তিনি ইতিহাসে প্রখ্যাত। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারিক ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ে অনেকে তাঁকে ইবনে সিনার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি 251 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 313 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। পূর্বে আমরা বলেছি ,ইবনুন নাদিম তাঁকে বালখীর শিষ্য বলেছেন। সম্ভবত এই বালখীই কিন্দীর ছাত্র ছিলেন। তাই রাযী কিন্দীর পরোক্ষ ছাত্র।
আবু যাইদ বালখী 243 অথবা 244 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ছাত্র যাকারিয়ার চেয়ে 7 বা 8 বছরের বড় ছিলেন। রাযী কিছুটা বেশি বয়সে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। আবু যাইদ তাঁর ছাত্রের মৃত্যুর পরও নয় বছর জীবিত ছিলেন। রাযীর অপর শিক্ষক ছিলেন আবুল আব্বাস ইরানশাহরী। রাযী দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ মত পোষণ করতেন। তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত অ্যারিস্টটলের দর্শনের অনুসারী ছিলেন না। তিনি পদার্থের সৃষ্টিতে অণুর সমন্বয়ের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ‘ পাঁচ চিরন্তন অস্তিত্বে ’ বিশ্বাসী ছিলেন যা বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফারাবী ,আবুল হাসান শহীদ বালখী ,আলী ইবনে রিদওয়ান মিশরী ও ইবনুল হাইসাম বাসরী তাঁর এই তত্ত্বকে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।
যাকারিয়া রাযীর গ্রন্থের তালিকায় ‘ কিতাবুন ফিন নবুওয়াত ’ নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে যাকে অন্যরা তিরস্কারের মনোবৃত্তি নিয়ে ‘ নাকজুল আদইয়ান ’ বা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর অপর একটি গ্রন্থ ‘ ফি হাইলিল মুতানাব্বিয়ীন ’ ও অন্যদের দ্বারা ‘ মুখারিকুল আম্বিয়া ’ নামে অভিহিত ও সমালোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ দু ’ টি বর্তমানে বিদ্যমান নেই। কিন্তু ইসমাঈলী কালামশাস্ত্রবিদ আবু হাতেম রাযীও সম্ভবত তাঁরই সূত্রে নাসের খসরু যাকারিয়ার উপরোক্ত গ্রন্থ দু ’ টি হতে কিছু বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ,তিনি নবুওয়াতের অধিকারী ছিলেন। যদিও আবু হাতেম রাযী যাকারিয়ার নাম উল্লেখ না করে বলেছেন এক নাস্তিক এ কথা বলেছে তদুপরি স্পষ্ট ,তাঁর লক্ষ্য হলো যাকারিয়া রাযী।
যেহেতু ঐ গ্রন্থ দু ’ টি আমাদের হাতে নেই তাই সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন মতামত দান সম্ভব নয়। তবে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় ,যাকারিয়া নবুওয়াত অস্বীকারকারী ছিলেন না ;বরং ‘ মুতানাব্বিয়ীন ’ বা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রেই শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির গৃহে শহরের নামকরা ও সুপরিচিত ব্যক্তিদের সামনে যাকারিয়া রাযী ও আবু হাতেম ইসমাঈলী যে বিতর্ক করেন তাতে যদি রাযী প্রকাশ্যে সকল নবুওয়াতকেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতেন তবে তাঁর পক্ষে পরবর্তীতে সেখানে সম্মানের সঙ্গে বাস করা সম্ভব হতো না। কেউ কেউ যে দাবি করেছেন আবু রাইহান বিরুনী ‘ নাকজুল আদইয়ান ’ ও ‘ মুখারিকুল আম্বিয়া ’ নামের দু ’ টি গ্রন্থ রাযীর রচিত বলেছেন এ বিষয়টি সঠিক নয়। কারণ স্বয়ং আবু রাইহান এ দু ’ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে বলেছেন ,এরূপ দাবি করা হয়েছে ;বরং তিনি ‘ কিতাবুন ফিন নবুওয়াত ’ ও ‘ ফি হাইলিল মুতানাব্বিয়ীন ’ নামেই বই দু ’ টির উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় অন্যরা এরূপ নাম দিয়েছিল। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ এরূপ নামের গ্রন্থ যাকারিয়ার ছিল না বলে মন্তব্য করে বলেছেন , ‘ সম্ভবত কোন মন্দ ব্যক্তি ‘ মুখারিকুল আম্বিয়া ’ নামের গ্রন্থ রচনা করে যাকারিয়ার সম্মানহানি করতে প্রয়াস পেয়েছিল। রাযীর শত্রুদের মধ্যে কেউ ,যেমন আলী ইবনে রিদওয়ান মিশরীও তাঁর গ্রন্থের এরূপ নামকরণ করে থাকতে পারেন। ’ ইবনে আবি আছিবায়ার বক্তব্য হতে বুঝা যায় যাকারিয়ার ‘ কিতাবুন ফিন নবুওয়াত ’ ও ‘ ফি হাইলিল মুতানাব্বিয়ীন ’ নামক গ্রন্থ থাকলেও ‘ মুখারিকুল আম্বিয়া ’ নামের কোন গ্রন্থ ছিল না ;বরং অন্যরা তাঁর প্রতি এরূপ গ্রন্থ রচনার অপবাদ আরোপ করেছিল।
তদুপরি যাকরিয়া রাযী খোদা ,পরকাল ও আত্মার মৌলিকত্ব ও চিরন্তনতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি স্রষ্টা সম্পর্কে ‘ ফি ইন্না লিল ইনসানে খালেকান মুত্তাকেনান হাকিমান ’ নামে এবং মনী ধর্মের দ্বিত্ববাদকে খণ্ডন করে ‘ সিসান সানাভী ’ নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে আলী ইবনে শাহীদ বালখীর নিকট একটি পুস্তিকা পাঠান যাতে তিনি পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের মতকে খণ্ডন করেছেন। তিনি ‘ ফি ইন্নান নাফসা লাইসা বিজিসমিন ’ নামে অপর এক গ্রন্থে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তাই প্রশ্ন হলো- যে ব্যক্তি স্রষ্টা ,পরকাল ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তিনি কিভাবে নবুওয়াত ও শরীয়তকে অস্বীকার করতে পারেন ? তদুপরি তিনি ‘ ফি আছারিল ইমামিল ফাযিলিল মাসুম ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্ভবত এ গ্রন্থটি তিনি শিয়া দৃষ্টিতে ইমামতের ধারণা হতে লিখেছেন। ইমামত সম্পর্কে ‘ আন নাকজ আলাল কায়াল ফিল ইমামত ’ ও ‘ কিতাবুল ইমাম ওয়াল মামুমুল মুহিক্কীন ’ নামের তাঁর আরো দু ’ টি গ্রন্থ রয়েছে। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে ইমামতের ধারণা তাঁর চিন্তাকে মশগুল রাখত। স্পষ্ট যে ,নবুওয়াত অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি ইমামতের বিষয়ে এতটা সংবেদনশীল হতে পারে না ।
সম্ভবত তাঁর মধ্যে শিয়া ইমামতের চিন্তা বিদ্যমান থাকায় শিয়াদের শত্রুরা তাঁর প্রতি এরূপ অপবাদ আরোপ করেছিল যেমনটি তারা অন্যান্য শিয়া চিন্তাবিদদের ওপরও আরোপ করত।
তা ছাড়া নবুওয়াত অস্বীকারের দলিল হিসেবে রাযী থেকে যে সকল বর্ণনা আনা হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তাঁর মতো ব্যক্তিদের নিকট থেকে তা উপস্থাপিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। যেমন বলা হয়েছে যে ,রাযী বলেছেন ,যদি সকল মানুষের হেদায়েত পাওয়াই আল্লাহর লক্ষ্য তবে সকল মানুষ কেন নবী হলো না ?
এটি সত্য হলে শুধু এটুকু বলা যায় ,রাযীর চিন্তায় কিছু বিকৃতি ও ভুল ছিল কিন্তু তা নবুওয়াত ও শরীয়ত অস্বীকারের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু তাঁর শত্রুরা তাঁর এরূপ চিত্র অংকন করেছে। বর্তমান সময়েও আমরা লক্ষ্য করি এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো ভুলত্রুটি মুক্ত নয় ,কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলোর বিরোধীরা এমনভাবে সেগুলোকে চিত্রায়িত করে উত্তর প্রদান করেন যে ,কেউ মূল গ্রন্থটি দেখলে সন্দেহে পড়বে যে ,জবাব গ্রন্থটি এ গ্রন্থের নাকি অন্য কোন গ্রন্থের।
যাকারিয়া রাযীর দু ’ ধরনের শত্রু ছিল। একদল তাঁর দর্শনের মত খণ্ডন করে গ্রন্থ লিখেছেন ,যেমন ফারাবী ,শাহীদ বালখী ,ইবনে হাইসাম প্রমুখ এবং আরেক দল তাঁর মাযহাবী মতকে খণ্ডন করে গ্রন্থ লিখেছেন ,যেমন ইসমাঈলী মতাবলম্বীরা। একমাত্র তারাই রাযীকে ইতিহাসে নাস্তিক বলে প্রচার চালিয়েছে ও অন্যদেরও এ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য ইতিহাস ইসমাঈলীদেরও নাস্তিক বলেছে। আমাদের সমকালীন নাস্তিকগণ ইসমাঈলীদের অনুকরণে যাকারিয়া রাযীকে নাস্তিক বলে প্রচার করছে এ উদ্দেশ্যে যে ,তাদের কর্ম অন্যদের কাছে বৈধতা পাবে। অন্য আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য ,চিকিৎসাশাস্ত্রে যাকারিয়া রাযী বিরল প্রতিভা হলেও দর্শনে তিনি তেমন যোগ্য ছিলেন না। এ কারণেই আবু রাইহান আল বিরুনীর প্রশ্নের জবাবে ইবনে সিনা যাকারিয়া রাযী সম্পর্কে বলেছেন , ‘ অনধিকার সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কালামশাস্ত্রবিদ সাজিয়েছেন ’ অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও অনধিকার চর্চা করেছেন। এ কথাটি কিছুটা হলেও সত্য।
2. আবুল হুসাইন শাহীদ ইবনিল হুসাইন বালখী: তিনি যেমন দার্শনিক ছিলেন তেমনি কবি। তিনি আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় কবিতা লিখেছেন। তিনি ইরানের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। ইবনুন নাদিম বলেছেন ,তিনি শাহীদ বালখীকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেননি। এ কারণেই তিনি তাঁকে ‘ যে ব্যক্তি শাহীদ ইবনিল হুসাইন নামে পরিচিত ও তাঁর উপনাম আবুল হুসাইন ’ এ শিরোনামে আলোচনা করেছেন। অতঃপর ইবনুন নাদিম বলতে চেয়েছেন ,তিনি আবু যাইদ বালখীর ছাত্র ছিলেন। যদিও এ বিষয়টি অন্য কেউ বলেছেন বলে আমি দেখিনি। ইবনুন নাদিম বলেছেন ,শাহীদ বালখী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যাকারিয়া রাযীর বিতর্ক হয়েছে।
শাহীদ বালখী রাযীর ‘ চিরন্তন পাঁচ সত্তা ও অস্তিত্ব ’ এবং ‘ আনন্দ উপভোগ ’ সম্পর্কিত দার্শনিক তত্ত্বের খণ্ডন করেছেন। তিনি 325 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আবু আহমাদ হুসাইন ইবনে আবুল হুসাইন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে যাইদ ইবনে কাতেব (ইবনে কারনিব নামে প্রসিদ্ধ): তিনি প্রসিদ্ধ মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ ,প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। অন্যদিকে তাঁর ভ্রাতা আবুল হুসাইন ইবনে কারনিব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল আলা ইবনে আবিল হুসাইন ছিলেন গণিতজ্ঞ। ইবনুন নাদিম তাঁদের নাম গণিতজ্ঞদের তালিকায় এনেছেন। আবু আহমাদ ইবনে কারনিব একাধারে কালামশাস্ত্রবিদ ,দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থ মতে তিনি কালামশাস্ত্র ও দর্শন উভয় বিষয়ই শিক্ষা দান করতেন। তাঁর স্বনামধন্য কিছু ছাত্রও ছিল। ইবনুন নাদিম বলেছেন ,তিনি তৎকালের প্রচলিত প্রকৃতিবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইবনুন নাদিমের বর্ণনাটিই ইবনে কাফতী তাঁর ‘ তারিখুল হুকামা ’ ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর ‘ উউনুল আম্বা ’ গ্রন্থে হুবহু এনেছেন। ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর নাম কুয়াইরী ও মুরুজীর পরবর্তী স্তরে এবং আবু বাশার মাতীর স্তরে এনেছেন। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে ,তিনি কুয়াইরী ও মুরুজীর ছাত্র ছিলেন যদিও বলা হয়ে থাকে আবু বাশার মাতী ইবনে কারনিবের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইবনে কারনিবের জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের নাম জানা যায়নি। তবে সম্ভাবনা রয়েছে তিনি এই স্তরের দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। দর্শনে ‘ বিপরীতমুখী দু ’ গতির মাঝে স্থিতির অবশ্যম্ভাবিতা অথবা অসম্ভাব্য ’ বিষয়ে সাবিত ইবনে কোররার মতকে খণ্ডন করে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে কাফতীর ‘ তারিখুল হুকামা ’ এবং ইবনে আবি আছিবায়ার ‘ উউনুল আম্বা ’ গ্রন্থের অনুকরণে ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থে এ দার্শনিক মতকে ‘ সমমুখী দু ’ গতি ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে ,কিন্তু এটি সঠিক নয় ;বরং ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে উল্লিখিত মতটিই সঠিক ;সেখানে এ মতকে ‘ বিপরীতমুখী দু ’ গতি ’ বলা হয়েছে।
4. আবু বাশার মাত্তা ইবনে ইউনুস: তিনি একজন গ্রীক ও খ্রিষ্টান যুক্তিবিদ। তিনি বাগদাদে বাস করতেন। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থে তাঁকে গ্রীক বংশোদ্ভূত ও দিরকানীর অধিবাসী বলেছেন। ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থের বর্ণনা মতে দিরকানী হলো বাগদাদের নিকটবর্তী দিরমারমারী যা মারমারী স্কুল নামেও পরিচিত। ইবনুন নাদিম বলেছেন , ‘ তিনি তাঁর সময়ে যুক্তিবিদ্যা ধারার সর্বশেষ নেতা। তিনি ইবরাহীম কুয়াইরী ,আবি আহমাদ ইবনে কারনিব ,দুফিল (রুবিলও বলা হয়ে থাকে) এবং বিন ইয়ামীনের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। ’
ইবনে আবি আছিবায়াহ্ ফারাবীর জীবনী আলোচনায় বলেছেন , ‘ আবু বাশার মাত্তা ‘ ইসাগুযী ’ (যুক্তিবিদ্যায় অ্যারিস্টটলের ধারা) বিষয়ে একজন খ্রিষ্টান মনীষীর (সম্ভবত বিন ইয়ামীন) নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যুক্তিবিদ্যার ‘ ক্যাথাগোরাস ’ (বিধেয় সম্পর্কিত আলোচনা) অধ্যায় রুবিলের নিকট এবং ‘ অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত ’ -এর বিষয়টি আবু ইয়াহিয়া মুরুজীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ’
আবু বাশার অনুবাদক ছিলেন ,আবার দার্শনিকও। তবে বর্তমানে দার্শনিক বলতে যা বুঝায় তা ছিলেন না ;বরং বর্তমানের দৃষ্টিতে তাঁকে যুক্তিবাদী বললে যথার্থ হবে। ইবনে কাফতীর বর্ণনা মতে তাঁর রচিত যুক্তিবিদ্যা গ্রন্থ ও অ্যারিস্টটলের এ সম্পর্কিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দান করা হতো।306 তিনি 320 অথবা 330 হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে ইবনে কাফতী উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবি আছিবায়ার মতে আবু বাশার মাত্তা 328 হিজরীতে মারা যান।
5. আবু নাসর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তুরখান ফারাবী: এ স্বনামধন্য দার্শনিকের পরিচয় দেয়ার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে দর্শনের ‘ দ্বিতীয় শিক্ষক ’ ও ‘ মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক ’ উপাধি দানের বিষয়টি যথার্থ। তিনি তুর্কিস্তানের অধিবাসী। তিনি তুর্কী না ইরানী ছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে তিনি তুর্কী ও ফার্সী উভয় ভাষা জানতেন। তিনি অত্যন্ত আত্মতুষ্ট ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণত ঝরনা বা নদীর তীরে অথবা ফুল বাগান ও উদ্যানের নিকট বাসস্থান নির্ধারণ করতেন এবং ছাত্ররা সেখানেই তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায় কিন্দীর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করেন। কথিত আছে ,তাঁর পূর্বে যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণকলা ও গাণিতিকরূপ সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ অনূদিত হয়নি বা আরবদের নিকট ছিল না। ফারাবী স্বয়ং তা উদ্ভাবন করেন। তিনি যুক্তির পাঁচ ক্ষেত্রের (প্রামাণ্য দলিল ,বক্তব্য ,কবিতা ,তর্কশাস্ত্র ও ভ্রমাত্মক যুক্তি) প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। ফারাবী ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সম্পর্কে অন্যরা অতিরঞ্জিত কথা বলে থাকে। যেমন বলা হয়েছে ,তিনি সত্তরটি ভাষা জানতেন। তবে এটি সঠিক যে ,ফারাবী আত্মপ্রশিক্ষিত এক বিরল প্রতিভা ছিলেন।
তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন শিক্ষক ছিল না। শুধু যুক্তিবিদ্যায় তাঁর শিক্ষক ছিলেন ইউহান্না ইবনে হাইলান। সাম্প্রতিক কিছু লেখক উল্লেখ করেছেন ,তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে বাগদাদে আবু বাশার মাত্তার নিকট পড়াশোনা করেন। অতঃপর হারানে যান ও ইউহান্না ইবনে হাইলানের নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করেন। সম্ভবত তাঁদের এ বক্তব্যের উৎস ইবনে খাল্লেকানের বক্তব্য। তিনিও কোন গ্রন্থ উৎসের উল্লেখ না করে এ মতটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনুল কাফতী ও ইবনে আবি আছিবায়ার বর্ণনানুযায়ী ফারাবী ,আবু বাশার মাত্তার সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর সময়ে আবু বাশার হতে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক ঊর্ধ্বে ছিল।
ইবনুল কাফতী বলেছেন ,ফারাবী আবু বাশার মাত্তা ইবনে ইউনুসের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। বয়সে তিনি আবু বাশারের কনিষ্ঠ হলেও জ্ঞানে তাঁর অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ও এরূপ মন্তব্য করেছেন। তদুপরি এটি অসম্ভব যে ,ফারাবী বাগদাদে আবু বাশার মাত্তার নিকট শিক্ষাগ্রহণের পর হারানে ইউহান্না ইবনে হাইলানের নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য যাবেন। স্বয়ং ফারাবীও তাঁর গ্রন্থে একমাত্র ইউহান্না ইবনে হাইলানকে শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ইবনুল কাফতী দাবি করেছেন ,ফারাবী বাগদাদে ইউহান্না ইবনে হাইলানের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।
ফারাবী 257 হিজরীতে (যাকারিয়া রাযীর জন্মের ছয় বছর পর ও কিন্দীর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 339 হিজরীতে 82 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
ফারাবী মাশশায়ী ধারার (অ্যারিস্টটলের ধারার) দার্শনিক হলেও ইশরাকী ধারা (প্লেটোনিক ধারা) হতেও পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।307 তিনি একজন প্রথম সারির গণিতজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞও বটে। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর বিশেষ মত ,বিশেষত ‘ আদর্শ নগরী ’ র ধারণাটি প্রসিদ্ধ। ফারাবী তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক ধারণার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটান এবং অ্যারিস্টটলের উত্তরাধিকারী হিসেবে দর্শনের ‘ দ্বিতীয় শিক্ষক ’ উপাধি পান।
চতুর্থ স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের খুব বেশি সংখ্যক দার্শনিকের পরিচয় আমাদের জানা নেই। তবে বিভিন্ন বর্ণনা হতে যতটুকু জানা যায় ফারাবী ,আবু বাশার মাত্তা ও কারনিবের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ছিল ,কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। এ পর্যায়ের দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন :
1. ইয়াহিয়া ইবনে আদি: তিনি একজন খ্রিষ্টান যুক্তিবিদ ও ইবনুন নাদিমের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। ইবনুন নাদিম তাঁর কর্মতৎপরতায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। ইবনুন নাদিম ,ইবনুল কাফতী ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ একমত ,ইয়াহিয়া আবু নাসর ফারাবী ও আবু বাশার মাত্তার ছাত্র ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিশেষত ইবনুল কাফতী ইয়াহিয়ার অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যার অধিকাংশই যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত। অবশ্য তিনি ঐশী দর্শন নিয়েও গ্রন্থ লিখেছেন যা ফারাবীর পূর্বে সার্বিকভাবে দর্শনে বিশেষত খ্রিষ্টীয় দর্শনে লক্ষ্য করা যায় না। ইবনুন নাদিম ও তাঁর অনুসরণে ইবনুল কাফতী ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ বলেছেন ,ইয়াহিয়া তাঁর সমকালীন যুক্তিবিদগণের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি 363 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল 81 বছর।
2. চতুর্থ স্তরে ইয়াহিয়া ইবনে আদি ছাড়াও ‘ ইখওয়ানুস সাফা ওয়া খিলানুল ওয়াফা ’ নামে দার্শনিকদের একটি দল ছিল। তাঁরা অপরিচিত থাকতে চাইতেন বলে এরূপ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁরা প্রমাণ করেছেন ,তাঁরা একদিকে যেমন দার্শনিক ছিলেন তেমনি অন্যদিকে ছিলেন ধার্মিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁরা ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন তার আদলে সমাজ সংস্কারের চিন্তায় সমিতি বা দল গঠন করেছিলেন। তাঁরা সদস্য সংগ্রহ করতেন ও এর জন্য বিশেষ নিয়ম ছিল। তাঁরা তাঁদের বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের ওপর 52টি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এক দৃষ্টিতে এটি তৎকালীন সময়ের একটি এনসাইক্লোপেডিয়া যা ইসলামী বিশ্ব ও সভ্যতার উৎকৃষ্ট নমুনা। ইখওয়ানুস সাফা তাঁদের পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বিশেষত ফারাবীর
চিন্তাধারা দ্বারা যেমন প্রভাবিত ছিল তেমনি পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এ উভয় ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকলেও তা আমাদের এ গ্রন্থের লক্ষ্য বহির্ভূত।
ইখওয়ানুস সাফার সদস্যদের নাম তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব আবু হাইয়ান তাওহীদী উল্লেখ করেছেন। যেমন আবু সুলাইমান মুহাম্মদ ইবনে মা ’ শার বাস্তী ,আবুল হাসান আলী ইবনে হারুন যানজানী ,অবু আহমাদ মেহেরজানী আউফী ,যাইদ ইবনে রাফায়া প্রমুখ। আবার অনেকে অন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন ,যেমন ইবনে মাসকুইয়া রাযী (মৃত্যু 421 হিজরী) ,ঈসা ইবনে যারআ (মৃত্যু 398 হিজরী ,তিনি দার্শনিক ছাড়াও অনুবাদক ছিলেন) ,প্রসিদ্ধ গণিতবিদ আবুল ওয়াফা বুযাজানী (মৃত্যু 387 হিজরী) এবং অন্যান্য। এদের অনেকেই পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর প্রথম দশকসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিভিন্ন বর্ণনা মতে ইখওয়ানুস সাফার কর্মকাণ্ড চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিচিতি লাভ করেছিল।
আবু হাইয়ান তাওহীদী 373 হিজরীতে ইখওয়ানুস সাফার বিশ্বাস ,চিন্তাধারা ,নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সামসামুদ্দৌলা ইবনে আজদুদ্দৌলার মন্ত্রীর নিকট বিবরণ পেশ করেন এবং বলেন , ‘ এ বিবরণটি আমার শিক্ষক আবু সুলাইমান মানতেকী সাজেস্তানীর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি তাঁদের সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশ করেন। ’ এ সম্পর্কিত আবু হাইয়ানের পুস্তিকাটি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল বিধায় ইখওয়ানের ব্যক্তিত্বদের ফারাবীর ছাত্রদের সমসাময়িক হিসেবে এ স্তরের দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছি।
ইখওয়ানুস সাফা বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের সঙ্গে দীন ও শরীয়তের সমন্বয় ঘটিয়েছিল এবং এ দু ’ বিষয়কে একে অপরের পরিপূরক ও পূর্ণতা দানকারী হিসেবে দেখেছে । তাঁরা দর্শনে পীথাগোরাসের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেছে ও সংখ্যাতত্ত্বের ওপর অধিকতর জোর দিয়েছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে ইসলামী দিক দিয়ে তাঁরা শিয়া চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড ঝুঁকে ছিলেন বলা যায়।
পঞ্চম স্তরের দার্শনিকগণ
1. আবু সুলাইমান মুহাম্মদ ইবনে তাহির ইবনে বাহরাম সাজেস্তানী (আবু সুলাইমান মানতেকী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি বিশিষ্ট যুক্তিবিদ ইয়াহিয়া ইবনে আদী মানতেকীর ছাত্র। ইবনুল কাফতীর ‘ তারিখুল হুকামা ’ গ্রন্থের বর্ণনা মতে তিনি আবু বাশার মাত্তার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তিনি শিক্ষা জীবনের শুরুতে আবু বাশার মাত্তার ছাত্র ছিলেন এবং পরে ইয়াহিয়া ইবনে আদীর নিকট পড়াশোনা করেন।
ইসলামী বিশ্বের বিশিষ্ট মনীষী ,সাহিত্যিক ও লেখক আবু হাইয়ান মূল্যবান অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। যেমন আল মুকাবিসাত ,আল এমতা ,আল মাওয়ানিসাহ্ ,আস সিদ্দীক ওয়াস সাদাকাত। আবু হাইয়ান তাঁর এ গ্রন্থসমূহে তাঁর শিক্ষক সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। ইবনুন নাদিম ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ আবু সুলাইমানের পরিচিতি ও বিবরণ দান করলেও সংক্ষিপ্তরূপে তা উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য ইবনুল কাফতী তাঁর সম্পর্কে অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
আবু সুলাইমান সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনাটি আমি মরহুম মুহাম্মদ কাযভীনীর ‘ বিসত মাকালেহ্ ’ গ্রন্থের 2য় খণ্ডে (পৃ. 128-166) দেখেছি।
আবু সুলাইমানের গৃহে দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আসর বসতো। তিনি তাঁর গোত্রের নেতা বলে পরিগণিত হতেন। আবু সুলাইমানের আসরে দার্শনিক পরিবেশ বিরাজ করত। সেখানে দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানগত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হতো। দার্শনিকগণ একে অপরের আলোচনা হতে লাভবান হতেন। আবু হাইয়ান এ ক্ষেত্রে ‘ একে অপরের হতে আলোকিত হতেন ’ বলেছেন। আবু হাইয়ান তাঁদের আসরকে 106টি সভায় বিভক্ত করে ‘ মুকাবিসাত ’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
আবু সুলাইমানের জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক বছর জানা যায়নি। তবে নিশ্চিত যে ,তিনি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মরহুম কাযভীনীর ধারণায় আবু সুলাইমান 307 হিজরীতে জন্ম ও 380 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তিনি 390 হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলেও ধারণা করা হয়।
আবু সুলাইমানের জ্ঞানের আসরে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তাঁদের অধিকাংশই ইয়াহিয়া ইবনে আদীও আবু সুলাইমানের ছাত্র ছিলেন। যেমন আবু মুহাম্মদ উরুযী ,আবু বাকর কাউমাসী ,ঈসা ইবনে যারায়াহ্ প্রমুখ।
2. আবুল হাসান আমেরী নিশাবুরী: এই ব্যক্তি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। ইবনুন নাদিম ,ইবনুল কাফতী ও ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর নামোল্লেখ করেননি। ইয়াকুত তাঁর ‘ মুজামুল উদাবা ’ গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।
‘ সেহ্ হাকিমে মুসলমান ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: ‘ আমেরীর দু ’ টি গ্রন্থ রয়েছে ;একটি নৈতিকতা সম্পর্কিত যার নাম ‘ আস সায়াদাহ্ ওয়াল আসআদ ’ এবং অন্যটি দর্শন সম্পর্কিত যার নাম ‘ আল আমাদ ইলাল আবাদ ’ । তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষায় অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে ‘ আল আলাম বি মানাকিবুল ইসলাম ’ নামের একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি গ্রীক দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সাসানী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি আবু যাইদ বালখীর ছাত্র ছিলেন।
কেউ কেউ দাবি করেছেন ,আমেরী ও ইবনে সিনার মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছে। কিন্তু এটি সম্ভবত ঠিক নয়। কারণ তাঁর মৃত্যুর সময় ইবনে সিনার বয়স ছিল এগার বছর। আমেরী আবু যাইদ বালখীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন এ কথাটিও সম্ভবত সঠিক নয়। কারণ বালখী 322 হিজরীতে মারা যান এবং আমেরী 381 হিজরীতে। শিক্ষক ও ছাত্রের মৃত্যুর মধ্যকার সময়ের ব্যবধান উনষাট বছর।
3. আবুল খাইর হাসান ইবনে সাওয়ার (ইবনুল খিমার নামে প্রসিদ্ধ): তিনি একাধারে চিবিৎসক ,দার্শনিক এবং সুরিয়ানী ভাষা হতে আরবী ভাষার একজন অনুবাদক। কিন্তু দার্শনিক ও অনুবাদক অপেক্ষা তাঁর প্রসিদ্ধি চিকিৎসক হিসেবে অধিক। তিনি ইয়াহিয়া ইবনে আদীর ছাত্র এবং স্বয়ং অনেক ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করেছেন। তিনি প্রথম জীবনে খ্রিষ্টান ছিলেন তবে শেষ জীবনে মুসলমান হয়েছিলেন বলে ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।
ইবনুন নাদিম তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন ,যদিও এ গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুর বছর উল্লিখিত হয়নি। মুহাম্মদ কাযভীনী তাঁর ‘ বিসত মাকালেহ্ ’ গ্রন্থের ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ নামক প্রবন্ধের শেষাংশে আবুল খাইরের মৃত্যু 408 হিজরীতে ঘটেছিল বলে দাবি করেছেন।308
কথিত আছে ইবনে সিনা তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতেন না। তদুপরি তাঁর গ্রন্থে আবুল খাইরের নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন , ‘ আবুল খাইরকে অন্যদের সমপর্যায়ে ধরা ঠিক হবে না। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটান। ’ 309
4. আবু আবদুল্লাহ্ নাতেলী: এই ব্যক্তির নিকটই ইবনে সিনা প্রথম জীবনে কিছুদিন যুক্তিবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর তেমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত তাঁর ছাত্রের কারণেই।
নাতেলী একজন চিকিৎসকও ছিলেন। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ আবুল ফারাজ ইবনুত্ তিবের জীবনী আলোচনায় নাতেলীকে তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসকদের নামের তালিকায় এনেছেন। অনেকে ইবনে আবি আছিবায়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ,আবুল ফারাজ ইবনুত্ তিব নাতেলীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ ইবনে আবি আছিবায়াহ্ নাতেলীকে আবুল ফারাজের সমসাময়িক ব্যক্তি হিসেবে এনেছেন ,তাঁর ছাত্র হিসেবে নয়।
ষষ্ঠ স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরকে বিরল প্রতিভার দার্শনিকদের স্তর বলা যেতে পারে। অন্য কোন স্তরেই এ স্তরের ন্যায় উজ্জ্বল দার্শনিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।
1. আবু আলী আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব মাসকুইয়া (মাসকাভীয়ে) রায়ী: তিনি রেইয়ের আদি অধিবাসী। তিনি আবু রাইহান বিরুনী ,ইবনে সিনা ,আবুল খাইর ,আবু নাসর ইরাকী ও খ্রিষ্টান ব্যক্তিত্ব আবু সাহলের সঙ্গে একত্রে কিছুদিন খাওয়ারেজম শাহের দরবারে ছিলেন। তিনি 420 হিজরীতে ইসফাহানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক সাল জানা যায়নি ,তবে বলা হয়েছে ,তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন।
আবু হাইয়ান তাওহীদীর বর্ণনা মতে ইবনে মাসকাভীয়ে কিছুদিন আবুল খাইরের ছাত্র ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি আবুল হাসান আমেরীর নিকটও শিক্ষা লাভ করেছেন। অবশ্য এ বর্ণনাটির সঙ্গে ‘ মু ’ জামুল উদাবা ’ গ্রন্থের বর্ণনার পার্থক্য রয়েছে। সেখানে আবুল হাসান আমেরীর রেই শহরে পাঁচ বছর অবস্থানকালীন সময়ে ইবনে মাসকাভী তাঁর কাছে যাননি বলা হয়েছে। সম্ভবত তাঁদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল।
ইবনে সিনার ইবনে মাসকাভীর সভায় উপস্থিত হওয়ার কাহিনীটি ইবনে মাসকাভী তাঁর নৈতিকতা বিষয়ক ‘ তাহারাতুল আরাক ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এরূপ: একদিন ইবনে সিনা ইবনে মাসকাভীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সম্মুখে একটি আখরোট ছুঁড়ে দিয়ে এর আয়তন নির্নয় করতে বলেন। ইবনে মাসকাভী তাঁকে বলেন , ‘ তোমার এই আখরোটের আয়তন জানা অপেক্ষা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষার জন্য আমার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ’ ইবনে সিনা তাঁর সমকালীন কোন ব্যক্তির প্রতি তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন না। ইবনে মাসকাভীয়ে সম্পর্কে তিনি বলেছেন ,একটি বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনভাবেই তা বুঝতে সক্ষম হননি।
ইবনে মাসকাভীয়ের পিতা যারথুষ্ট্র হতে মুসলমান হয়েছিলেন। কারো কারো মতে ইবনে মাসকাভীয়ে শিয়া ছিলেন। যা হোক এটি নিশ্চিত যে ,তিনি শিয়া বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ হলো ইতিহাস বিষয়ক ‘ আল ফাউযুল আসগার ’ এবং নৈতিকতা বিষয়ক ‘ তাহারাতুল আরাক ’ ।
2. আবু রাইহান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ বিরুনী খাওয়ারেজমী: তিনি ইলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম সারির একজন ব্যক্তিত্ব। কোন কোন প্রাচ্যবিদের মতে ইসলামী বিশ্বে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি গণিতশাস্ত্র ,জ্যোতির্বিদ্যা ,ইতিহাস ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের ধর্ম ও বিশ্বাসে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গবেষণামূলাক এমন কিছু গ্রন্থ লিখেছেন যা বিশেষজ্ঞদের আশ্চর্যান্বিত করে। যেমন তাহকীকু মিলালেল হিন্দ ,আল আসারুল বাকীয়া ,কানুনে মাসউদী ইত্যাদি।
বিরুনী 362 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও 442 হিজরীতে মারা যান। তিনি তাঁর মাতৃভাষা খাওয়ারেজমী ছাড়াও ফার্সী ,আরবী ,সুরিয়ানী ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরবীকে জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ভাষা মনে করতেন এবং এ ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন , ‘ আমাকে আরবী ভাষায় কেউ মন্দ বললেও আমি খুশী ,এমনকি কোন কোন ভাষায় আমার প্রশংসা করা অপেক্ষাও। ’ এক ব্যক্তি ছাড়া তাঁর আর কোন শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়নি । ঐ ব্যক্তি হলেন আবু নাসর ইবনে আলী ইবনে আরাকী যিনি আবু নাসর আরাকী নামে প্রসিদ্ধ। আবু রাইহানের কোন ছাত্র ছিল কিনা তাও জানা যায়নি।
আবু রাইহান এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন ও জীবনকে জ্ঞানার্জনের পথে ব্যয় করেছিলেন। তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। বছরে মাত্র দু ’ দিন ছুটি কাটাতেন। আবু রাইহান ও ইবনে সিনা 400 হিজরীতে খাওয়ারেজমে পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। আবু রাইহান ইবনে সিনা হতে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তিনি ইবনে সিনাকে দর্শন বিষয়ে আঠারটির মতো প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে কয়েকটি অ্যারিস্টটলের মতের বিরুদ্ধে ছিল। ইবনে সিনা প্রশ্নগুলোর উত্তর দান করেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা তিক্ততামূলক বিতর্কে পৌঁছেছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ প্রশ্নগুলো ইবনে সিনা খাওয়ারেজম হতে চলে যাওয়ার পর বিরুনী তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আবু রাইহান তাঁর ‘ আল আসারুল বাকীয়া ’ গ্রন্থে ইবনে সিনার প্রতি উপস্থাপিত প্রশ্নসমূহ ‘ জ্ঞানী যুবক ’ শিরোনামের আলোচনায় এনেছেন।
আবু রাইহান ইসলামের মৌলনীতির প্রতি একান্ত অনুরাগী ও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর লেখায় একজন প্রকৃত ঈমানদারের ন্যায় পবিত্র ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই কোরআনের আয়াত এনেছেন। তিনি ‘ শুয়ূবী ’ আন্দোলনের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতেন এবং তাঁর বিভিন্ন লেখায় এ আন্দোলনের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবু রাইহান যথাসম্ভব শিয়া ছিলেন।
3. আবু আলী হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনা: তিনি একজন কিংবদন্তী ও বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁকে চিনতে এক জীবন সময় এবং কয়েক খণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। তিনি 35 বছর বয়সে গোরগানে আসার সময় পর্যন্ত নিজ জীবন ইতিহাস এক ছাত্রের অনুরোধে বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্বনামধন্য ছাত্র আবু উবাইদ জাওযাজানী ঐ ছাত্রের লিখিত বিবরণকে পূর্ণ করে ইবনে সিনার পূর্ণ জীবনেতিহাস লিখেছেন। এ ইতিহাস হতে মোটামুটিভবে ইবনে সিনার শিক্ষা ,রাজনীতি ও সার্বিক জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ও অশান্তিপূর্ণ ছিল এবং তিনি নাতিদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। অবশ্য নাতিদীর্ঘ অশান্তিপূর্ণ ও ঘটনাবহুল এ জীবনে তিনি যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ও যত অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।
আশ্চর্যের বিষয় হলো ইবনে আবি অছিবায়াহ্ ও ইবনুল কাফতী উভয়েই ইবনে সিনার উপরোক্ত জীবনেতিহাস কোন পার্থক্য ছাড়াই হুবহু বর্ণনা করলেও তাঁর মৃত্যুর সময় নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর মৃত্যু 54 বছর বয়সে হয়েছিল বলেছেন ,কিন্তু ইবনুল কাফতী 58 বছর বলে উল্লেখ করেছেন। ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর মৃত্যু 63 বছর বয়সে হয়েছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।
উল্লেখ্য ,ইবনে সিনার ব্যক্তিত্ব তাঁর পূর্বের সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর গ্রন্থগুলোই আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়।
ইবনে সিনার পূর্বে বাগদাদ চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু ইবনে সিনা বাগদাদে যাননি। তাঁর পিতা ছিলেন বালখের অধিবাসী এবং মাতা বুখারার। তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ এ অঞ্চলেই কেটেছে। বিশেষ কারণে তিনি খোরাসান ও গোর্গানে আসেন ও বিভিন্ন শহরে স্বল্প সময় কাটান। অতঃপর ইসফাহানে আসেন ও হামেদানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। জ্ঞানান্বেষণকারীদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সকল দিক হতে তাঁরা তাঁর নিকট আসা শুরু করেন। তিনি অনেক ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করেন। ইবনে সিনার ব্যক্তিত্ব ও পরবর্তীতে তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধি ইরানেই ঘটে ও তাঁর গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এখানেই গবেষণাকর্ম শুরু হয়। ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের কেন্দ্র বাগদাদ হতে ইরানে স্থানান্তরিত হয়।
4. আবুল ফারাজ ইবনুত তাইয়্যেব: তিনি ইরাকী। সম্ভবত বাগদাদের অধিবাসী। তিনি চিকিৎসক ও দার্শনিক ছিলেন। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধি অধিক। ইবনে সিনা তাঁর সমসাময়িক হিসেবে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রশংসা করেছেন ,তবে দর্শনে তাঁকে তেমন কিছু মনে করতেন না। অবশ্য ইবনে সিনা দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের কাউকেই গুরুত্ব দিতেন না। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে উল্লিখিত হয়েছে ,ইবনে সিনা আবুল ফারাজের দর্শনগ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন ,তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ বিক্রেতাদের উচিত তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া ও তাঁর নিকট আরো অর্থ চাওয়া। একই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে ,যখন ইবনে সিনা ও আবু রাইহান বিরুনীর মধ্যে বিতর্ক চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন বিরুনী ইবনে সিনার প্রতি একটি কড়া পত্র প্রেরণ করেন। এ খবর আবুল ফারাজের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ,যদি কেউ অন্যদের প্রতি কঠোর আচরণ করে তার প্রতিও সেরূপ আচরণ হয়ে থাকে।
ইবনুল কাফতী ইবনে সিনার বক্তব্যের উল্লেখের পর আবুল ফারাজ সম্পর্কে বলেন , ‘ যে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই বলবেন আবুল ফারাজ পুরাতন জ্ঞানসমূহকে প্রকাশিত ও পুনর্জীবিত করেছিলেন। ’
আবুল ফারাজ খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি আবুল খাইরের ছাত্র ছিলেন এবং বেশ কিছু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইবনুল কাফতী বলেছেন ,তিনি 420 হিজরীর পরও জীবিত ছিলেন। কথিত আছে তিনি 435 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. আবুল ফারাজ ইবনে হিন্দু: তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনে আবুল খাইরের ছাত্র এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ,কবি ও বক্তা ছিলেন।
6. আবু আলী হাসান ইবনে হাসান (অথবা হুসাইন) ইবনুল হাইসাম বাসরী: তিনি একাধারে দার্শনিক ,চিকিৎসক ,পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি 354 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও 430 হিজরীতে মারা যান। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ,নীল নদীতে পানি হ্রাস পেলে তিনি এ থেকে মুক্তির পরিকল্পনা নকশা তৈরি করে কায়রোর শাসনকর্তার নিকট নিয়ে যান। শাসক হাকিম বিল্লাহ্ তা গ্রহণ তো করেননি ;বরং তাঁর ওপর রাগান্বিত হন। তিনি কায়রো হতে পালিয়ে দামেস্কে চলে আসেন। বলা হয়ে থাকে যে ,তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বিশেষ অবস্থার বিষয়টিও উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে ,তিনি জীবনের একটি অংশ মরক্কোয় কাটিয়েছেন। সাইয়্যেদ হাসান তাকী যাদেহ্ তাঁর ‘ তারিখে উলুম দার ইসলাম ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ তাঁর অনেক রচনা ছিল। তাঁর রচনার সংখ্যা এত অধিক যে ,মনে হয় সমগ্র জীবন এ কর্মেই রত ছিলেন। ’ সার্টনের বর্ণনা মতে ইবনুল হাইসাম পদার্থবিদ্যায় মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এ শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। বিশিষ্ট দার্শনিক রজার বেকন এবং বিশিষ্ট পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার তাঁর গ্রন্থ হতে লাভবান হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন... ইবুনল হাইসাম আলোকরশ্মি ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি নিয়ে উচ্চমানের গবেষণা চালিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অন্ধকার ঘরে আলোকরশ্মির ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালান... তিনি দ্বিঘাত সমীকরণ উদ্ভাবন করেন এবং পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের আয়তন নির্ণয়ের চেষ্টা চালান। ’
তাঁর সমসাময়িক প্রথম সারির গণিতজ্ঞদের মধ্যে রয়েছেন- আবুল ওয়াফা বুজাযানী নিশাবুরী ,আবদুর রহমান সুফী রাযী ,আবু সাহল কুহেস্তানী তাবারেস্তানী প্রমুখ।
সপ্তম স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের দার্শনিকগণ দু ’ ভাগে বিভক্ত। প্রথম দল ইবনে সিনার ছাত্র এবং দ্বিতীয় দল তাঁর ছাত্র নন। প্রথম দলের ব্যক্তিরা হলেন :
1. আবু আবদুল্লাহ্ ফাকীহ্ মাসুমী: ইবনে সিনা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন , ‘ সে আমার কাছে প্লেটোর নিকট অ্যারিস্টটলের ন্যায়। ’ ‘ ইশক ’ নামক পুস্তিকাটি ইবনে সিনা তাঁর অনুরোধে ও তাঁর নামে লিখেন। তিনিই ইবনে সিনা ও আবু রাইহানের মধ্যে পত্র বিনিময়ের মাধ্যম ছিলেন। আবু রাইহান ইবনে সিনার প্রতি কঠোর সমালোচনামূলক পত্র লিখলে ইবনে সিনা নিজে এর জবাব দিতে রাজী হননি। ফাকীহ্ মাসুমী আবু রাইহানকে পত্র লিখে বলেন , ‘ যদি আপনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারো জন্য ঐ ভাষাসমূহ ব্যবহার করতেন তাহলে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ হতো। ’ বায়হাকীর মতে ফাকীহ্ বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্তু সত্তার সংখ্যা নির্ণয় ও শ্রেণীবিন্যাস (উৎপত্তির ভিত্তিতে) করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থটি আমাদের হাতে পৌঁছার পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঠিক বছর জানা যায়নি। তবে 450 হিজরীর দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।310
2. আবুল হাসান বাহমানইয়ার ইবনে মারযবান আজারবাইজানী: তিনি প্রথম জীবনে মাজুসী ছিলেন ,পরে মুসলমান হন। তিনি ইবনে সিনার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্র। তাঁর প্রসিদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ইবনে সিনাকে অধিক প্রশ্ন করা। তাঁর প্রশ্নের উত্তরের যে জবাব ইবনে সিনা দিয়েছেন তা হতে তাঁর ‘ মুবাহেসাত ’ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। বাহমানইয়ারের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘ আত তাহছীল ’ । বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থে এর নাম বারবার এসেছে। সাদরুল মুতাআল্লেহীন (মোল্লা সাদরা) তাঁর ‘ আসফার ’ গ্রন্থের কয়েক স্থানে ‘ আত তাহছীল ’ গ্রন্থ হতে এবং দু ’ টি স্থানে বাহমানইয়ারের অপর গ্রন্থ ‘ আল বাহজাত ওয়াস সাআদাত ’ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সম্প্রতি ‘ আত তাহছীল ’ গ্রন্থটি ‘ ইলাহিয়াত ’ মহাবিদ্যালয়ের প্রকাশনালয় হতে আমার (মুতাহ্হারী) সংস্করণ ও সংযোজনসহ প্রকাশিত হয়েছে। বাহমানইয়ার 458 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আবু উবাইদ আবদুল ওয়াহেদ জাওযাজানী: তিনি বিশ বা পঁচিশ বছর ইবনে সিনার ছাত্র ছিলেন। তিনিও ইবনে সিনার জীবনী গ্রন্থ সংকলন ও পূর্ণ করেন।
ইবনে সিনা তাঁর বক্তব্য ও লেখনী সংরক্ষণে তেমন প্রয়াসী ছিলেন না। কখনও প্রয়োজন পড়লে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন পুস্তক লিখে কোন ছাত্রের হাতে দিতেন এর কোন অনুলিপি নিজের কাছে না রেখেই। সম্ভবত ইবনে সিনার কিছু সংখ্যক গ্রন্থ আবু উবাইদের কারণেই বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে সিনার গণিতশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ ‘ নাজাত ’ ও ‘ দানেশনামে আলাঈ ’ তিনি সম্পূর্ণ করেন। এর বেশি কিছু তাঁর সম্পর্কে জানা যায়নি।
4. আবু মনসুর হুসাইন ইবনে তাহির ইবনে যিলেহ্ ইসফাহানী: ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেন ও তাঁর হাই ইবনে ইয়াকযানের প্রতি লিখিত পুস্তিকাটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সংগীতশাস্ত্রের ওপর একটি গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি সংগীতকলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষক ইবনে সিনার 22 বছর পর 450 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে যিলেহ্ও বাহমানইয়ারের ন্যায় ইবনে সিনার নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর জেনে তা সংকলন করেছেন। কথিত আছে ‘ মুবাহেসাত ’ গ্রন্থটিতে বাহমানইয়ারের প্রশ্নাবলী ছাড়াও ইবনে যিলেহ্ ও অন্যান্যদের প্রশ্নোত্তরও সংকলিত হয়েছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ইবনে সিনার অন্যান্য ছাত্র ছিলেন যাঁদের নামোল্লেখ হতে আমরা বিরত থাকছি।
এই স্তরে যাঁরা ইবনে সিনার ছাত্র ছিলেন না তাঁর হলেন :
1. আলী ইবনে রিদওয়ান মিসরী: তিনি দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা যাকারিয়া রাযীর মতকে খণ্ডন করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন ,কিন্তু তাঁর চেহারা ছিল কদাকার। ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থের মতে তিনি তাওরাত ,ইঞ্জিল ও দার্শনিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সর্বশেষ নবী (সা.)-এর নবুওয়াতকে প্রমাণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 453 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
2. আবুল হাসান মুখতার ইবনে হাসান ইবনে আবদান ইবনে সাদান ইবনে বাতলান বাগদাদী: তিনি একজন খ্রিষ্টান ও ইবনে বাতলান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি পূর্বোল্লিখিত খ্রিষ্টান দার্শনিক আবুল ফারাজ ইবনুত্ তাইয়্যেবের ছাত্র। তিনিও তাঁর শিক্ষকের ন্যায় একাধারে চিকিৎসক ও দার্শনিক ছিলেন ,তবে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি অধিক। আলী ইবনে রিদওয়ানের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল ও তাঁকে ‘ জ্বিনদের কুমীর ’ বলে তিরস্কার করতেন। একবার মিশরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি হালাব ও কনস্টানটিনোপোলেও গিয়েছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং 444 হিজরীতে মারা যান।
3. আবুল হাসান আম্বারী: তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের উপসংহার হতে এতটুকু জানা যায় যে ,তিনি দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। তবে গণিতজ্ঞ হিসেবে অধিকতর প্রসিদ্ধ। গণিতজ্ঞ উমর খৈয়াম তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন।
অষ্টম স্তরের দার্শনিকগণ
এই স্তরের দার্শনিকগণ হয় ইবনে সিনার ছাত্রদের ছাত্র নতুবা তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন :
1. আবুল আব্বাস ফাযল ইবনে মুহাম্মদ লুকারী মারভী: তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তাঁকে সাধারণত সাহিত্যিক আবুল আব্বাস লুকারী বলে অভিহিত করা হয়। তিনি বাহমানইয়ারের ছাত্র। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ বায়ানুল হাক্ব বি জিমানিস সিদ্ক ’ যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও মুদ্রিত হয়নি। তবে তাঁর এ গ্রন্থটি পরবর্তীকালের দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মোল্লা সাদরার ‘ আসফার ’ গ্রন্থে ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ে তাঁর নামোল্লিখিত হয়েছে। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও ছাত্র প্রশিক্ষণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বায়হাকী তাঁর ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন , ‘ লুকারীর মাধ্যমে দর্শন খোরাসানে প্রচারিত হয়। ’
মাহমুদ মুহাম্মদ খাদিরী (আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) বাগদাদে অনুষ্ঠিত ইবনে সিনার সহস্র বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধে311 উল্লেখ করেন , ‘ আবুল আব্বাস দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন ,তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক সাল আমার জানা নেই। আমার ধারণা তিনি পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর শেষাংশে মৃত্যুবরণ করেন। ’
আবদুর রহমান বাদাভী তাঁর ‘ তালিকাতে ইবনে সিনা ’ গ্রন্থের 8 পৃষ্ঠায় বুরুক লেমেন হতে বর্ণনা করেছেন ,লুকারী ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর প্রথমদিকে 517 হিজরীতে মারা যান। তবে তিনি বারক লেমেনের সূত্রটি কি সে সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
2. আবুল হাসান সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহ্ ইবনে হুসাইন: ইবনে আবি আছিবায়াহ্ বলেছেন , ‘ তিনি চিকিৎসক হিসেবে শ্রেষ্ঠ হলেও দার্শনিক হিসেবে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। ’ তিনি আবদান কাতিব এবং আবুল ফাযল কাতিফাতের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা উভয়েই আবুল ফারাজ ইবনুত তাইয়্যেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইহুদী ও খ্রিষ্টান ছাত্র গ্রহণ করতেন না। ‘ আল মুতাবার ’ গ্রন্থের লেখক আবুল বারাকাত বাগদাদী প্রথম জীবনে ইহুদী ছিলেন। তিনি আবুল হাসানের গৃহের পেছনে বসে চতুরতার সাথে তাঁর পাঠ দান শুনতেন। এভাবে এক বছর চলার পর আবুল হাসান এরূপ ছাত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন ও তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করে পাঠে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।
ইবনে আবি আছিবায়াহ্ বলেছেন ,আবুল বারাকাত আবুল হাসান রচিত ‘ আত তালখিসুন নিযামী ’ গ্রন্থটি তাঁর নিকটই শিক্ষা লাভ করেন।
এ গ্রন্থটি দর্শনের না চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর লিখিত তা আমার জানা নেই। সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহ্ 495 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. হুজ্জাতুল হাক্ব আবুল ফাত্হ উমর ইবনে ইবরাহীম খাইয়ামী নিশাবুরী (খাইয়াম বা ওমর খৈয়াম নামে প্রসিদ্ধ): তিনি দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত কবিও ছিলেন। দুঃখজনকভাবে খাইয়াম দর্শন বা গণিতের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ না করে কবিতার কারণে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন ,অথচ তিনি বিশেষভাবে গণিতশাস্ত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। খাইয়ামের নামে প্রচলিত কবিতাসমূহের অধিকাংশই তাঁর এমন এক চেহারা ফুটিয়ে তুলেছে যেন তিনি একজন সন্দেহবাদী ,দায়িত্বহীন ও নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন যা তাঁর প্রকৃত চরিত্রের সঙ্গে সংগতিশীল নয়। ফিজ্জেরাল্ড নামের যে ইংরেজ কবি তাঁর চতুর্পদী (রুবাঈ) কবিতাসমূহকে-তাকী যাদের বর্ণনানুযায়ী কোথাও কোথাও বিকৃত ও পরিবর্তন করে-(উচ্চমানের সাহিত্যরূপ দিয়ে ইংরেজিতে) অনুবাদ করেছেন তিনিই তাঁর এ মিথ্যা প্রসিদ্ধির কারণ হয়েছেন বলে মনে করা হয়। খাইয়াম প্রণীত দর্শন সম্পর্কিত কিছু পুস্তিকা এখনও বিদ্যমান রয়েছে যা তাঁর চিন্তার প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে। ফার্স প্রদেশের বিচারক আবু নাসর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম নাসভীর প্রতি প্রেরিত তাঁর উত্তর পত্রটির নাম ‘ কৌন ওয়া তাকলীফ ’ । খাইয়াম এ পত্রে আবু নাসর কর্তৃক সৃষ্টি ,সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইবাদাতের দর্শন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আবু নাসর খাইয়ামের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন যাতে তাঁকে জীবনসঞ্চারী বারির অধিকারী মেঘপুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থের উত্তরসমূহকে অকাট্য বলেছেন।
খাইয়াম তাঁর এ পত্রে তাঁর শিক্ষক অথবা শিক্ষকের শিক্ষক ইবনে সিনার নির্দেশিত কাঠামোর ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি ইবনে সিনার প্রদত্ত এ সম্পর্কিত কাঠামোর রূপ সম্পর্কে অবহিত থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন খাইয়াম এ বিষয়ে কতটা যথার্থ চিন্তা করতেন। উক্ত পত্রে খাইয়াম ইবনে সিনাকে নিজ শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করে একজন দৃঢ়চেতা দার্শনিকের ন্যায় বিশ্বজগতে বৈপরীত্যের উপস্থিতি ও মন্দের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন , ‘ আমি ও আমার শিক্ষক ইবনে সিনা এ বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত গবেষণা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি এবং সন্তুষ্ট হয়েছি। হয়তো কেউ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমাদের দুর্বলতা মনে করতে পারে ,কিন্তু আমাদের মতে এ উত্তর সন্তোষজনক। ’
এ পত্রটি তাঁর আরো কিছু পত্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছাপা হয়েছে। পূর্বে মিশরেও ‘ জামেউল বাদায়ী ’ নামে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সোভিয়েত প্রকাশক দাবি করেছেন ,মিশরীয় প্রকাশক ‘ বিশ্বজগতে বৈপরীত্যের উপস্থিতি ’ সম্পর্কিত পত্রটি ‘ কৌন ওয়া তাকলীফ ’ নামক পত্র হতে স্বতন্ত্র পত্র বলে মনে করেছেন যা সঠিক নয় ;বরং ঐ পত্র এ পত্রটিরই অংশ।
ঘটনাক্রমে এ পত্রে যে সকল বিষয়ে খাইয়াম দৃঢ় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাঁর নামে প্রচলিত কবিতায় সে সব বিষয়েই দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন ইউরোপীয় ও ইরানী গবেষক এ কবিতাগুলো খাইয়ামের নয় বলেছেন। কেউ কেউ ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন খাইয়াম নামের দু ’ ব্যক্তি ছিলেন। একজন কবি এবং অপরজন গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। আবার কেউ মনে করেন একজনের নাম ছিল আলী খাইয়াম এবং তিনি ছিলেন কবি। অপরজনের নাম ছিল ওমর খাইয়ামী এবং তিনি দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন।
কেউ কেউ বলেছেন ,খাইয়ামীর আরবী উচ্চারণ খাইয়াম এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ স্বয়ং খাইয়াম তাঁর ‘ অস্তিত্ব ’ সম্পর্কিত পুস্তিকায় আরবীতে তাঁর নাম ‘ আবুল ফাত্হ ওমর ইবরাহীম আল খাইয়ামী ’ লিখেছেন।
তবে এটুকু নিশ্চিত যে ,তিনিও তাঁর মতো অনেক মনীষীর ন্যায় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস সত্ত্বেও বকধার্মিক ও বাহ্যিকভাবে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁর সকল গ্রন্থই তাঁর প্রকৃত ধর্মপরায়ণতার স্বাক্ষর বহন করে ,এমনকি বিতর্কিত বলে কথিত ‘ নওরুয নামে ’ গ্রন্থটিও।
বায়হাকী বলেছেন ,
‘ তিনি ইবনে সিনার উত্তরসূরি ছিলেন বলা যায় যদিও তাঁর চরিত্রে কিছুটা সংকীর্ণতা এবং প্রশিক্ষণ ও লিখনে কৃপণতা লক্ষণীয়... এক দিন তিনি আবদুর রাজ্জাক ইবনুল ফাকীর পরামর্শদাতা শিহাবুল ইসলামের নিকট আগমন করলে বিশিষ্ট কারী আবুল হুসাইন গাজ্জালী কোরআনের কোন একটি আয়াতের বিষয়ে ক্বারীদের মধ্যে পঠন পদ্ধতির পার্থক্যের আলোচনা তুললেন। শিহাবুল ইসলাম বললেন: যখন জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত তখন আমরা নিশ্চুপ থাকছি।... খাইয়াম পঠন পদ্ধতির পার্থক্যের বিভিন্ন রূপ ও সেগুলোর প্রতিটির পেছনে যুক্তি উপস্থাপন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন । ইমাম আবুল ফাখর এতে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বললেন: ‘ আল্লাহ্ আলেমদের মধ্যে আপনার মতো ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। ’
খাইয়ামের জন্মের তারিখ জানা যায়নি। তবে তাঁর মৃত্যুর সাল 517 অথবা 526 হিজরী বলা হয়ে থাকে। তিনি দীর্ঘ নব্বই বছর জীবিত ছিলেন বলা হয়। তদুপরি ইবনে সিনার নিকট তাঁর সরাসরি শিক্ষা লাভ করার বিষয়টি যথসম্ভব সঠিক নয়। তিনি ইবনে সিনাকে নিজ শিক্ষক হিসেবে স্বীয় গ্রন্থে যে সম্বোধন করেছেন তা এজন্য যে ,ইবনে সিনার গ্রন্থ ও চিন্তার পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করেছেন কিংবা সম্ভবত তিনি ইবনে সিনার ছাত্রের ছাত্র ছিলেন।
4. আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাজ্জালী তুসী: অবশ্য তাঁকে পারিভাষিক অর্থে দার্শনিক বলাটা সঠিক হবে না। কারণ তিনি নিজেকে দার্শনিক মনে করেননি ;বরং দর্শনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন ;বিশেষত ইবনে সিনার বিরুদ্ধে। তিনি কোন শিক্ষকের নিকট দর্শন পড়েননি। তিন বছর নিজে বিভিন্ন দর্শনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। অতঃপর দর্শনের বিরুদ্ধে ‘ মাকাসিদুল ফালাসাফা ’ এবং ‘ তোহফাতুল ফালাসাফা ’ নামের দু ’ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী গ্রন্থ।
ইসলামী বিশ্বে দর্শনের বিরোধী অনেকেই ছিলেন ,তবে তাঁদের কেউই গাজ্জালীর ন্যায় ক্ষুরধার ছিলেন না। যদি গাজ্জালীর নিকটবর্তী সময়ে সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর মতো দার্শনিকের আবির্ভাব না ঘটত তাহলে গাজ্জালী দর্শনের মূলোৎপাটন করতেন। গাজ্জালীর দর্শনবিরোধী তৎপরতা সত্ত্বেও যেহেতু তাঁর বিভিন্ন মত দর্শনের বিবর্তনে কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছিল সেহেতু তাঁকে আমরা দার্শনিকদের তালিকায় এনেছি। তিনি 450 হিজরীতে জন্ম ও 505 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। গাজ্জালীর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হলো ‘ এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন ’ । মুসলমানদের মধ্যে খুব কম গ্রন্থই এ গ্রন্থের ন্যায় প্রচারিত হয়েছে ও প্রভাব ফেলতে পেরেছে।
নবম স্তরের দার্শনিকগণ
1. শারাফুদ্দীন মুহাম্মদ ইলাকী: তিনি আবুল আব্বাস লুকারী ও ওমর খাইয়ামের ছাত্র। তিনি একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। কথিত আছে তিনি 536 হিজরীতে কাতওয়ানের যুদ্ধে নিহত হন। কেউ কেউ তাঁকে বাহমানইয়ারের ছাত্র বলেছেন। কিন্তু উভয়ের মৃত্যুর বছরের তুলনা করলে এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। ইলাকী ‘ আল বাসায়িরুন নাসিরিয়া ’ গ্রন্থের লেখক কাজী যাইনুদ্দীন উমর ইবনে সাহলান সাভেজীর শিক্ষক।
2. আবুল বারাকাত হাব্বাতুল্লাহ্ ইবনে ইয়ালী মিলকায়ী বাগদাদী: তিনি ইহুদী ছিলেন ও পরবর্তীতে মুসলমান হন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আমরা পূর্বে সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহর নিকট তাঁর শিক্ষা লাভের বিবরণ দিয়েছি। দর্শনে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো ‘ আল মুতাবার ’ যা মোল্লা সাদরার মতো দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবু বারাকাত দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তিনি ইবনে সিনার বিরোধী ছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের ক্রমধারা ফারাবী পর্যন্ত পৌঁছায়। কারণ তাঁর শিক্ষক ছিলেন সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহ্ যিনি আবু ফাজল কাতিফাত ও আবদান কাতিবের ছাত্র। আবুল ফারাজ আবুল খাইর হাসান ইবনে আওয়ারের ছাত্র যিনি ইয়াহিয়া ইবনে আদী মানতেকীর শিষ্য এবং ইয়াহিয়া মানতেকী আবু নাসর ফারাবীর ছাত্র। কথিত আছে দার্শনিক ওমর খাইয়ামকে বলা হয়েছিল , ‘ আবুল বারাকাত বাগদাদী ইবনে সিনার মতকে প্রত্যাখ্যান করেন। ’ তিনি বলেন , ‘ সে ইবনে সিনার কথাই বুঝতে পারেনি তাই কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করবে। ’ 312
তিনি আরবী অভিধান রচয়িতা ইবনুল ফাজলান ও ইবনুদ দাহান ,বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মাহযাবউদ্দীন ও মুসলমানদের হাতে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের গুজব রটনাকারী আবদুল লতিফ বাগদাদীর পিতার শিক্ষক ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ও এই ছাত্রদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় লিখতেন।313
3. মুহাম্মদ ইবনে আবি তাহের তাবাসী মুরুজী: তিনি লুকারীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর পিতা মারভের প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং মাতা খাওয়ারেজমের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 539 হিজরীতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে সারাখসে মৃত্যুবরণ করেন।314
4. আফজাল উদ্দীন গিলানী উমর ইবনে গিলান: তিনিও লুকারীর ছাত্র। তাঁর সম্পর্কে পূর্ণ ইতিহাস জানা যায়নি। তিনি সাদরুদ্দীন সারাখসীর শিক্ষক ছিলেন। মুহাম্মদ খাদিরীর বর্ণনামতে ইমাম ফাখরে রাযী তাঁর ‘ আল মুহাসসেল ’ গ্রন্থে তাঁর নাম স্মরণ করে তাঁর ওপর রহমতের দোয়া করেছেন। কথিত আছে তাঁর চিন্তা ইবনে সিনার চিন্তার বিরোধী ছিল। তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি মারভের সেনাদলে 523 হিজরী পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।
5. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনুস সায়েগ আন্দালুসী: তিনি ইবনে বাজা নামে প্রসিদ্ধ এবং দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ‘ নাফস ’ নামক পুস্তিকাটি সম্প্রতি315 পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ সাফির হাসান মাসুমী সংকলন করে প্রকাশ করেছে। আবু বাকর 533 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্পেনের স্বনামধন্য মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদের শিক্ষক ছিলেন।
6. আবুল হাকাম মাগরেবী আন্দালুসী: তিনি একাধারে দার্শনিক ,কবি ও চিকিৎসক ছিলেন। অবশ্য কবি বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে অধিকতর লক্ষণীয়। তাঁর লেখায় দৃঢ়তার অভাব ছিল ,অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌতুক ও উপহাসের প্রবণতা লক্ষণীয়। তিনি বাহেলী আরব ছিলেন। তবে দীর্ঘদিন আন্দালুসে (স্পেনে) থাকার পর প্রাচ্যে আসেন এবং মিশর ও সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। তিনি 549 হিজরীতে মারা যান। তিনি শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষকের শিক্ষক ইবনুস সালার শিক্ষক ছিলেন।
দশম স্তরের দার্শনিকগণ
1. সাদরুদ্দীন আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হারেসান আল সারাখসী: তিনি আফজালউদ্দীন গিলানীর ছাত্র এবং ফরিদউদ্দীন দামাদের শিক্ষক। তাঁর সম্পর্কে সঠিকভাবে তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি।
তিনি খাজা নাসিরউদ্দীন তুসীর শিক্ষকের শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের উপসংহারে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। মাহমুদ মুহাম্মদ খাদিরী ‘ খারিদাতুল কাছর ’ গ্রন্থের লেখক হতে বর্ণনা করেছেন ,তিনি দর্শন ,ঘনজ্যামিতি ও হিসাববিজ্ঞানের ওপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কিছুদিন বাগদাদে ছিলেন ও আবু মনসুর জাওয়ালিকীর (মৃত্যু 539 হিজরী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সারাখসে ফিরে আসেন। তিনি 545 হিজরীতে সম্ভবত যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
2. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে তোফাইল আন্দালুসী: তিনি স্পেনের প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক। সম্ভবত তিনি ইবনুস সায়েগের ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত ‘ হাই ইবনে ইয়াকজান ’ গ্রন্থের মাধ্যমে যা ইবনে সিনার হাই ইবনে ইয়াকজানের প্রতি লিখিত পত্রের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতাদানকারী পুস্তিকা। এই গ্রন্থটি ইরানে বদিউজ্জামান ফুরুজান কর্তৃক অনূদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। আবু বাকর দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন ও 581 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. কাজী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ আন্দালুসী: তিনি একাধারে দার্শনিক ,চিকিৎসক ও ফিকাহ্শাস্ত্রবিদ ছিলেন। এর প্রতিটি বিভাগেই তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। দর্শনে তাঁর অ্যারিস্টটলের ‘ মা বাদাত তাবিয়িয়াত ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো ‘ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ’ । তাঁর রচনা সমগ্র বোম্বাই হতে প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপীয়গণ দর্শনশাস্ত্রে ইবনে রুশদকে ইবনে সিনার সমকক্ষ মনে করেন। কিন্তু ইসলামী দর্শনে তাঁর মতের কোন মূল্যই নেই।
ইবনে রুশদের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ তোহাফাতুল তোহাফাহ্ ’ যা তিনি গাজ্জালীর ‘ তোহাফাতুল ফালাসাফা ’ গ্রন্থের জাবাবে লিখেছেন। ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটলের প্রতি অত্যন্ত অন্ধ ছিলেন। ইবনে সিনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে ,ইবনে সিনা অ্যারিস্টটলের প্রতি অন্ধ ছিলেন না ;বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব মতকে তাঁর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আসাদাবাদীর (আফগানী) সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব (পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন) ফরাসী দার্শনিক আর্নেস্ট রেনান ইবনে রুশদ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ইবনে রুশদ 595 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. মাজদুদ্দীন জিলী: এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নেই। শুধু এতটুকু অবহিত হয়েছি যে ,তিনি ‘ মারাগে ’ নামক স্থানে পাঠ দান করতেন ও ইমাম ফাখরে রাযী তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।316 শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীও তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রথমদিকে মারাগেতে তাঁর ছাত্র ছিলেন।317 সম্ভবত তিনি কালামশাস্ত্র ,দর্শন ,ফিকাহ্ ও উসূলশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইয়াকুত তাঁর ‘ মুজামুল উদাবা ’ গ্রন্থে সোহরাওয়ার্দীর জীবনী আলোচনায় তাঁকে ফকীহ্ ,কালামশাস্ত্রবিদ ও উসূলবিদ বলে উল্লেখ করেছেন।318
5. কাজী যাইনুদ্দীন উমর ইবনে সাহলান সাভেজী: তিনি ইবনে সাহলান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইরানের সাভেতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিশাবুরে জীবনযাপন করতেন । গ্রন্থ নকলের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের বর্ণনামতে তিনি দর্শন ও শরীয়তকে (ফিকাহ্শাস্ত্র) এক গ্রন্থে সমন্বিত করেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিত্ব শারাফুদ্দীন ইলাকী তাঁর শিক্ষক ছিলেন। কথিত আছে যে ,তিনি ইবনে সিনার ‘ রিসালাতুত তায়ের ’ গ্রন্থটি ফার্সীতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ আল বাসাইরুন নাসিরিয়া ’ যা মিশর হতে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির যুক্তিবিদ্যা অংশটি যুক্তিবিদ্যার সর্বোত্তম গ্রন্থসমূহের একটি। ‘ সাওয়ানুল হিকমাহ্ ’ গ্রন্থের পরিবর্ধনে বর্ণিত হয়েছে ,তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থটি ব্যতীত অন্য সকল গ্রন্থ দুর্ঘটনায় ভস্মিভূত হয়েছিল। ইবনে সাহলান দর্শনের জীবন্ত ব্যক্তিত্বদের একজন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও বর্ষ আমার জানা নেই ।
6. আবুল ফুতুহ নাজমুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আস সারী: তিনি ইবনুস সালাহ্ নামে প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাঁকে ইরানের হামেদানের অধিবাসী ,আবার কেউ ইরাকের ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর তীরবর্তী সামিসাতের অধিবাসী বলেছেন। তিনি সেখান হতে বাগদাদে যান ও আবুল হাকাম মাগরেবীর নিকট পড়াশোনা করেন। তিনি 548 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (স্বীয় শিক্ষকের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে)। তাঁর জন্মবছর আমার জানা নেই। তাঁকে নবম স্তরের দার্শনিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাঁর শিক্ষক আবুল হাকাম মাগরেবী নিজের ওপর ইবনুস সালার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। উল্লিখিত হয়েছে যে ,তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ ও ইবনে মাসকাভীর ‘ আল ফাওযুল আসগার ’ গ্রন্থ দু ’ টির ব্যাখ্যা লিখেছেন।
7. মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম আনসারী মারদিনী: তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর জন্ম ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাসের (কুদসের) নিকটবর্তী স্থানে। তাঁর পিতামাতা সেখানেই বাস করতেন। সম্ভবত তাঁর পূর্বপুরুষ মদীনার আনসার ছিলেন। তাঁর দর্শনের শিক্ষক ছিলেন ইবনুস সালাহ্। তিনি ইবনে সিনার প্রসিদ্ধ কাসীদা ‘ কাসীদায়ে আইনিয়া ’ ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনুল কাফতীর বর্ণনামতে শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী কিছুদিন তার নিকট দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। মারদিনী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 594 হিজরীতে 82 বছর বয়সে প্রশান্ত মন নিয়ে স্রষ্টার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।
একাদশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. ফাখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনুল হুসাইন আর রাযী (ফাখরে রাযী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি একাধারে ফকীহ ,কালামশাস্ত্রবিদ ,দার্শনিক ,মুফাসসির ,বক্তা এবং চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন জ্ঞানের গভীরতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। যদিও তিনি দর্শনে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন তদুপরি তাঁর চিন্তাধারা কালামশাস্ত্রীয় ,দার্শনিক নয় ;বরং তিনি দর্শনের ওপর ক্ষুরধার আক্রমণ করেছেন ও দর্শনের বিভিন্ন সন্দেহাতীত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর বিন্যাস ,বাচনভঙ্গী ও উপস্থাপন ক্ষমতা অত্যন্ত সুন্দর ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাদরে মুতাআল্লেহীন এ ক্ষেত্রে তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ দর্শন গ্রন্থ ‘ আল মাবাহিসুল মাশরেকীয়া ’ । তাঁর পরিচিতি সবচেয়ে বেশি ‘ মাফাতিহুল গাইব ’ নামের তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে যা কোরআনের তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। দর্শনে তাঁর একমাত্র শিক্ষক ছিলেন মাজদুদ্দীন জিলী (জাইলী)। সম্ভবত এ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অধিক পঠন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে। তবে তাঁর কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিল ,যেমন শামসুদ্দীন খসরুশাহী ,কুতুবুদ্দীন মিশরী ,যাইনুদ্দীন কাশী ,শামসুদ্দীন খুয়ী এবং শাহাবউদ্দীন নিশাবুরী। ফখরুদ্দীন রাযী 534 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 606 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. শেখ শাহাবুদ্দীন ইয়াহিয়া ইবনে হাবাশ ইবনে মিরাক সোহরাওয়ার্দী যানজানী: তিনি শেখ ইশরাক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ের বিরলতম প্রতিভা। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ,ক্ষুরধার মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। দর্শনের ইশরাকী ধারার (প্লেটোনিক ধারার ইসলামীরূপ) চিন্তা তাঁর পূর্বের ফারাবী ও ইবনে সিনার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও যে ব্যক্তি এ ধারার দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন ও মাশশায়ী বা অ্যারিস্টটলীয় ধারার ইসলামীরূপ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ধারা হিসেবে এর জন্ম দেন তিনি হলেন সোহরাওয়ার্দী। কেউ কেউ এ দু ’ য়ের পার্থক্য অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারার পার্থক্য মনে করলেও বস্তুত অ্যারিস্টটলীয় ধারার ইসলামীরূপ (মাশশায়ী) হতে ইশরাকী ধারার পার্থক্যে অনেক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যা সোহরাওয়ার্দীর নিজস্ব উদ্ভাবন ও সৃষ্টি। তিনি মাজদুদ্দীন জাইলীর নিকট মারাগেতে ,জহিরুদ্দীন ক্বারীর নিকট ইসফাহানে ও ফাখরুদ্দীন মারদিনীর নিকট ইরাকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি কিছুদিন মারদিনীর একান্ত সান্নিধ্যে ছিলেন। মারদিনী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন , ‘ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ,মনোযোগ ও একাগ্রতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। আমি তাঁর জীবনের ব্যাপারে আশংকা করছি। ’ 319 বলা হয়ে থাকে ,তিনি ইবনে সাহলানের ‘ আল বাসাইরুন নাসিরিয়াহ ’ গ্রন্থটি জহিরউদ্দীন ক্বারীর নিকট পড়েছেন।
সোহরাওয়ার্দী অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে ফিকাহ্শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন । তিনি সিরিয়া ও হালাব গিয়েছিলেন ও হালাবের হালাভীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক শেখ ইফতিখারউদ্দীনের নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র পড়েন। তিনি এ শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হন ও শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি ও নৈকট্য লাভ করেন। তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিষয়টি সালাহউদ্দীন আইউবীর পুত্রের (আল মুলকুয যাহিরের) নজরে পড়ে। তিনি বিভিন্ন কালামশাস্ত্রবিদ ও ফকীহ্দের ডেকে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক সভার প্রচলন করেন। তাঁর উপস্থিতিতে এ সকল সভায় সোহরাওয়ার্দী নির্ভীকতার সাথে সকলকে পরাস্ত করেন। এ বিষয়টি তাঁদের বিদ্বেষের কারণ হয় ও তাঁরা সালাউদ্দীন আইউবীর কান ভারী করে তাঁকে হত্যায় প্ররোচিত করেন। ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দেন এ মহান আলেমকে হত্যা করার জন্য। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। তিনি মাত্র 36 বছর বয়সে 586 হিজরীতে অথবা 38 বছর বয়সে 587 হিজরীতে নিহত হন।
কথিত আছে ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তাঁর রচিত ‘ তালভীহাত ’ গ্রন্থটি ফখরুদ্দীন রাযীকে দেয়া হলে তিনি তা চুম্বন করে নিজ সহপাঠীর কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করেছিলেন।
সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন কালামশাস্ত্রবিদ ও ফকীহ্দের সঙ্গে বিতর্কে শুধু বেপরোয়াই ছিলেন না ;বরং আক্রমণাত্মক বিতর্কে জড়াতেন। সম্ভবত বয়সের অপরিপক্বতার কারণে এতটা বেপরোয়া ছিলেন যে ,দর্শনের এমন অনেক তত্ত্ব যা সর্বসম্মুখে উপস্থাপন করা অনুচিত-যেরূপ ইবনে সিনা তাঁর ‘ ইশারাত ’ গ্রন্থের পবিশেষে বলেছেন-তিনি তা প্রকাশ্যে করতেন। তাঁর শিক্ষক মারদিনী পূর্বেই তাঁর বিষয়ে আশংকা করেছিলেন। তাই যখন তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছে তখন তিনি বলেন , ‘ আমি যা আশংকা করেছিলাম তাই ঘটেছে। ’ সোহরাওয়ার্দীর ব্যাপারে অনেকে তাই বলেন ,তাঁর জ্ঞান তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রাধান্য লাভের ফলেই এমনটি হয়েছে।
3. আফজালউদ্দীন মারকী কাশানী: তিনি ‘ বাবা আফজাল ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি যদিও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তদুপরি তাঁর সঠিক জীবনেতিহাস জানা যায়নি। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন যার তালিকা সম্প্রতি মুজতাবা মিনুয়ী ও ডক্টর ইয়াহিয়া মাহদাভী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন হতে ‘ এনসাইক্লোপেডিয়া অব পারসিয়ান ’ -এর ফার্সী অনুবাদে উল্লিখিত হয়েছে , ‘ আফজালউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন কাশানী একজন ইরানী আরেফ ও কবি। এক বর্ণনামতে তিনি 582 অথবা 592 হিজরীতে কাশানের মারকে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং 654 অথবা 664 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।... তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ’ ‘ দেহখোদা ’ ফার্সী অভিধান এবং ‘ গাজ্জালী নামেহ ’ গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু 707 হিজরী বলা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু 666 অথবা 667 বলেছেন।
‘ দাওয়াতুত তাকরীব ’ গ্রন্থে মাহমুদ খাদিরীর লেখা ‘ আফজালউদ্দীন আর কাশানী ফিলসুফুন মাগমুরুন ’ নামক প্রবন্ধে ‘ মুখতাছার ফি যিকরিল হোকামাউল ইউনানী ওয়াল মুসলিমীন ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মৃত্যু 610 হিজরী বলা হয়েছে।
‘ ফালাসাফায়ে ইরানী ’ গ্রন্থে মাহমুদ খাদিরীর প্রবন্ধ ও সাঈদ নাফিসীর ভূমিকা হতে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ শারহে ইশারাত ’ গ্রন্থের ‘ কিয়াস ’ অধ্যায়ে আলোচনায় উল্লিখিত প্রমাণ উপস্থাপন করে বলা হয়েছে আফজালউদ্দীনের মৃত্যু 667 হিজরীর অনেক পূর্বে হয়েছিল। কারণ ‘ শারহে ইশারাত ’ গ্রন্থটি খাজা নাসিরুদ্দীন 624-644 হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে লিখেছেন এবং তাতে আফজালউদ্দীনের নাম উল্লেখ করে ‘ রহমত উল্লাহ্ ’ লিখেছেন যা হতে বোঝা যায় ইতোপূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীন বাবা আফজালের প্রশংসায় নিম্নোক্ত চতুষ্পদী কবিতাটি রচনা করেন :
“ যদি আসমানের স্রষ্টা অনুমতি দেন বলার ,
কে সর্বোত্তম জ্ঞানী ও জ্ঞানের ভাণ্ডার।
সকল ফেরেশতা তাসবীহ না করে বলবেন ,
তিনি হলেন আফজাল ,আফজাল। ”
‘ সারগুজাশত ওয়া আকায়েদে ফালসাফীয়ে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী ’ গ্রন্থে স্বয়ং খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী হতে বর্ণিত হয়েছে , ‘ আমার পিতা আমাকে বিভিন্ন জ্ঞানান্বেষণে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও মতের কথা শ্রবণে উদ্বুদ্ধ করতেন। আমার পিতার সঙ্গে আফজালউদ্দীন কাশানী (রহ.)-এর ছাত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদের পরিচিতি ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আফজালউদ্দীনের নিকট গণিত ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আমার পিতা আমাকে তাঁর নিকট গণিতশাস্ত্র শিক্ষার জন্য সমর্পণ করেন।
উপরিউক্ত বক্তব্য হতে বুঝা যায় খাজা নাসিরুদ্দীন আফজালউদ্দীনের ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। তাই তিনি খাজা নাসিরুদ্দীনের নিকটতম ব্যক্তি হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয় ;বরং সঠিক হলো বাবা আফজালের মৃত্যু 606 বা 610 হিজরীতে ঘটেছিল।
দ্বাদশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. ফরিদউদ্দীন দামাদ নিশাবুরী: তাঁর জীবনেতিহাস ,সঠিকভাবে জানা নেই। এতটুকু জানা যায় ,তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর শিক্ষক ছিলেন ও তুসী ইবনে সিনার ‘ ইশারাত ’ গ্রন্থটি তাঁর নিকট পড়েছেন।320 ফরিদউদ্দীন সাদরুদ্দীন সারাখসীর ছাত্র ছিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীনের শিক্ষকের ধারাবাহিকতা তাঁর মাধ্যমে ইবনে সিনা পর্যন্ত পৌঁছায়। কারণ খাজা তুসী ফরিদউদ্দীন দমাদের ছাত্র। তিনি সাদরুদ্দীন সারাখসীর ছাত্র ,তিনি আফজালউদ্দীন গিলানীর ছাত্র। তিনি আবুল আব্বাস লুকারীর ছাত্র ,তিনি বাহমানইয়রের ছাত্র এবং বাহমাইয়র ইবনে সিনার ছাত্র। তাঁর মৃত্যুর বছর আমাদের জানা নেই।
2. শামসুদ্দীন আবদুল হামিদ ইবনে ঈসা খসরুশাহী (শামসুদ্দীন খসরুশাহী নামে প্রসিদ্ধ): ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁকে ‘ আলেমদের ইমাম ’ , ‘ দার্শনিকদের নেতা ’ , ‘ মানুষের আদর্শ ’ এবং ‘ ইসলামের সম্মান ’ বলে উল্লেখ করেছেন।321 তিনি ফখরুদ্দীন রাযীর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি দর্শন ,চিকিৎসা ও ফিকাহ্শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন। দর্শনে তাঁর প্রসিদ্ধি কিছু প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে যা তাঁর ছাত্র খাজা নাসিরুদ্দীন তাঁকে করেছিলেন ও দর্শন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
3. কুতুবুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ সালামী: তিনি কুতুবুদ্দীন মিশরী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ফখরুদ্দীন রাযীর ছাত্র ছিলেন। ইবনে আবি আছিবায়াহর মতে তিনি মরক্কোর অধিবাসী ,কিন্তু মিশরে বসবাস করতেন। তিনি সেখান হতে ইরানে চলে আসেন ও ফখরুদ্দীন রাযীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। তিনি দর্শনে ফখরুদ্দীন রাযীকে দর্শনের ক্ষেত্রে ইবনে সিনার ওপর প্রাধান্য দিতেন এবং খ্রিষ্টান চিকিৎসক আবু সাহলকেও চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার ওপর মনে করতেন। তিনি নিশাবুরে মোগলদের হামলার সময় নিহত হন। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী ও ফখরুদ্দীন রাযীর ছাত্রের ছাত্র ছিলেন ।
4. কামালুদ্দীন ইউনুস মৌসেলী অথবা কামাল উদ্দীন ইবনে ইউনুস (ইবনে মানআ নামে প্রসিদ্ধ): ইবনে আবি আছিবায়াহ্ তাঁর সমকালীন ছিলেন ও তাঁকে ‘ প্রজ্ঞাবানদের নেতা ’ ও ‘ আলেমদের ইমাম ’ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি মৌসেলের শিক্ষাকেন্দ্রে দর্শন পাঠ দান করতেন ও বেশ কিছু ছাত্রকে শিক্ষা দান করেছেন। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থের বর্ণনামতে নাসিরুদ্দীন তুসী এ ব্যক্তির নিকটও কিছু পড়াশোনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের 5ম খণ্ডের 9 পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ,তিনি আহলে সুন্নাতের প্রথম সারির আলেম ও দার্শনিকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ,ফিকাহ্ ,হাদীস ,তাফসীর ,চিকিৎসাবিদ্যা ,ইতিহাস ,সংগীত ,জ্যামিতি ,দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যায় সমকালীন মনীষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বল্প সময়ে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অনেকেই তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন ,এমনকি দূরবর্তী স্থান হতেও তাঁর নিকট ছাত্র ও মনীষীরা সমবেত হতেন।... তিনি 639 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ত্রয়োদশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. খাজা নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন আত তুসী: তাঁকে ‘ মানবের শিক্ষক ’ উপাধি দেয়া হয়েছে। আলাদাভাবে তাঁর পরিচয় দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। দর্শনে তাঁর অবদান ও এ শাস্ত্রের বিবর্তনে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশ্বের সীমিত সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তিত্বের একজন। তিনি টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যায় নতুন পথ উন্মোচন করেছিলেন। তাকী যাদের মতে নাসিরুদ্দীন তুসী তাঁর ‘ তাযকিরাহ্ ’ গ্রন্থে টলেমীর যে সকল মতের ওপর সমালোচনা করেছেন তা কোপার্নিকাসের ওপর প্রভাব ফেলেছিল ও তিনি সে অনুযায়ী জ্যোতির্বিদ্যায় নতুন তত্ত্ব দিয়েছিলেন।
খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীরও ইবনে সিনার ন্যায় ঘটনাবহুল জীবন ছিল। তিনি তাঁর ‘ শারহে ইশারাত ’ গ্রন্থে এ সকল দুঃখজনক ঘটনার কিছু মর্মবেদনা তুলে ধরেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি অনেক ছাত্রকে প্রশিক্ষিত ও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 597 হিজরীতে জন্ম ও 672 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2 আসিরুদ্দীন মুফাজ্জাল ইবনে উমর আবহারী : তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ‘ হিদায়াহ্ ’ যা প্রকৃতি ও স্রষ্টা বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। এ গ্রন্থটি কাজী হুসাইন মাইবাদী ও সদরুল মুতায়াল্লেহীন ( মোল্লা সাদরা ) ব্যাখ্যা করেছেন। বিশে ষত মোল্লা সাদরার ব্যাখ্যাগ্রন্থটি তাঁকে ও গ্রন্থটির বিশেষ পরিচিতি দান করেছে। আল্লামা হিল্লীর ‘ জাওহারুন নাদিদ ’ গ্রন্থের 78 পৃষ্ঠায় বিপরীত ঋণাত্মক আংশিক উক্তির ( Opposite Negative Particular Proposition )আলোচনায় ঋণাত্মক আংশিক উক্তির বিপরীত উক্তি নেই বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে , ‘ এর ব্যতিক্রম শুধু বিশেষ শর্তাধীন ও সাধারণ উক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়। ’ বলা হয় যুক্তিবিদ্যার এ নীতিটি আসিরুদ্দীন মুফাজ্জাল ইবনে উমর আবহারী উদ্ঘাটন করেন। আসিরুদ্দীন ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযীর ছাত্র ছিলেন।
3. নাজমুদ্দীন আলী ইবনে উমর কাতেবী কাযভীনী: তিনি ‘ দাবিরান ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রথম সারির দার্শনিক ,যুক্তিবিদ ও গণিতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। দর্শনে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো ‘ হিকমাতুল আইন ’ যার অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যুক্তিবিদ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ শামসীয়াহ্ ’ যা খাজা শামসুদ্দীন সাহেব দিওয়ান জুয়াইনীর নামে উৎসর্গ করে লিখিত এবং গ্রন্থটি কুতুবুদ্দীন রাযী ব্যাখ্যা করেছেন। মূল গ্রন্থ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ দু ’ টিই যুক্তিবিদ্যার ছাত্রদের পাঠ্য। কাতেবী আল্লামা হিল্লী ও কুতুবুদ্দীন শিরাজীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর সহায়তায় মারাগেতে একটি মানমন্দির তৈরি করেন। তিনি 675 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
চতুর্দশ স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের দার্শনিকগণ সকলেই নাসিরুদ্দীন তুসীর ছাত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন :
1. হাসান ইবনে ইউসুফ ইবনে মুতাহ্হার হিল্লী (আল্লামা হিল্লী নামে প্রসিদ্ধ): যদিও আল্লামা হিল্লী ফিকাহ্শাস্ত্রে সর্বাধিক পরিচিত তদুপরি তিনি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এ দু ’ শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা ফকীহ্দের আলোচনায় ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম বিরল এই ব্যক্তিত্বের বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আল্লামা হিল্লী আরব ছিলেন এবং কাতেবী ও খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ছাত্র ছিলেন। তিনি 648 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 711 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. কামালউদ্দীন মাইসাম ইবনে মাইসাম বাহরানী: তিনি ইবনে মাইসাম বাহরানী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে ফকীহ্ ,সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কারো কারো মতে নাসিরুদ্দীন তুসীও এর বিপরীতে তাঁর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা করেন।322 ইবনে মাইসাম হযরত আলীর বাণী ‘ নাহজুল বালাগা ’ র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নাহজুল বালাগার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 678 অথবা 679 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ‘ আজ্জররিয়া ’ গ্রন্থের লেখকের মতে তিনি 699 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।323
3. কুতুবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে মাসউদ ইবনে মুছলেহ শিরাজী (কুতুবুদ্দীন শিরাজী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি কাতেবী কাযভীনির নিকট যুক্তিবিদ্যা এবং খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর নিকট দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা পড়াশোনা করেন। তিনি ইবনে সিনার চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ ‘ কানুন ’ এবং সোহরাওয়ার্দীর দর্শন গ্রন্থ ‘ হিকমাতুল ইশরাক ’ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দর্শনের প্রকারভেদ নিয়ে ফার্সীতে ‘ দুররাতুত তাজ ’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এ তিনটি গ্রন্থই বেশ মূল্যবান। তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত দর্শনের ‘ হিকমাতুল ইশরাক ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীকে মারাগেতে ‘ মানমন্দির ’ তৈরিতে সহযাগিতা করেছিলেন। তিনি 710 অথবা 716 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন ।
4. হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শারাফ শাহ আলাভী হুসাইনী আসতারাবাদী: তিনি ইবনে শারাফ শাহ নামে পরিচিত। তিনি মারাগেতে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর নিকট পড়াশোনা করেন ও তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর মৃত্যুর পর মৌসেলে যান এবং সেখানকার ‘ নুরীয়া ’ মাদ্রাসায় দর্শন শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ তাজরীদ ’ গ্রন্থে টীকা সংযোজন করেন ও ‘ কাওয়ায়েদুল আকায়েদ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। তিনি 717 অথবা 718 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
পঞ্চদশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবি জাফর রাযী: তিনি কুতুবুদ্দীন রাযী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একজন যুক্তিবিদ ,দার্শনিক ,ফকীহ্ এবং ইসলামের অন্যতম প্রসিদ্ধ মনীষী। তিনি আল্লামা হিল্লীর নিকট পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি তাঁকে (কুতুবুদ্দীন) তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছিলেন। শহীদে আউয়াল (মুহাম্মদ ইবনে মাক্কী) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর (রাযী) নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি নিয়েছিলেন। শহীদে আউয়াল তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ,কুতুবুদ্দীন রাযী কাতেবী কাযভীনীর ‘ শামসীয়াহ্ ’ গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেছেন যা যুক্তিবিদ্যার ছাত্রদের পাঠ্য। তিনি দর্শনে ‘ মুহাকিমাত ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যাতে দর্শনের দু ’ দিকপাল ও ইবনে সিনার ‘ আল ইশারাত ’ গ্রন্থের দু ’ ব্যাখ্যাকারের (ফখরুদ্দীন রাযী ও নাসিরুদ্দীন তুসীর) মতামতের পর্যালোচনা ও বিচার করেছেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায় কাজী সিরাজউদ্দীন আরমাভীর ‘ মাতালিউল আনওয়ার ’ রচিত গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেছেন যা ‘ শারহে মাতালী ’ নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এ গ্রন্থটি ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রচলিত। যদিও কুতুবুদ্দীন রাযী তাঁর উপরোক্ত তিন গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ তদুপরি তার অন্যান্য গ্রন্থও রয়েছে। তিনি 766 অথবা 776 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুবারাক শাহ মারভী (মিরাক বুখারায়ী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি কাতেবী কাযভীনীর ‘ হিকমাতুল আইন ’ গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেছেন। এ কারণে দর্শন গ্রন্থসমূহের অনেক স্থানেই তাঁকে ‘ হিকামাতুল আইন ’ ব্যাখ্যাকারী নামে উল্লেখ করা হয়। তাঁর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের সঙ্গে মীর সাইয়্যেদ শারিফ জুরজানী টীকা সংযোজন করেছেন। মিরাক বুখারায়ীর মৃত্যু সম্পর্কে জানা যায়নি।
3. কাজী এ ’ দ্দুদ্দীন আবদুর রহমান আইজী শিরাজী: তিনি একাধারে দার্শনিক ,কালামশাস্ত্রবিদ ও উসূলী324 ছিলেন। উসূলশাস্ত্র ,দর্শন ও কালামশাস্ত্রে তাঁর কোন কোন মত উপস্থাপিত হয়ে থাকে। তাঁর ‘ মুয়াফিক ’ নামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি কালামশাস্ত্রের নামে প্রসিদ্ধ হলেও তা দর্শন নির্ভর। আমরা জানি খাজা নাসিরুদ্দীনের পরবর্তী সময় হতে বিশেষত খাজার ‘ তাজরীদ ’ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে কালামশাস্ত্র দর্শনের অনেক নিকটে চলে আসে অর্থাৎ কালামশাস্ত্রের লক্ষ্য কালামশাস্ত্রের নীতিতে প্রমাণিত ও বাস্তবায়িত না হয়ে দর্শনের নীতিতে প্রমাণিত ও ব্যাখ্যাত হতে শুরু করে এবং স্রষ্টাতত্ত্বের দর্শনের সার্বিক ও আংশিক বিষয়সমূহ কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হতে থাকে। এ দৃষ্টিতে ‘ মুয়াফিক ’ গ্রন্থটি বেশ উপযুক্ত। মীর সাইয়্যেদ শারিফ জুরজানী এ গ্রন্থটিরও ব্যাখ্যা করেছেন যা মূল অংশসহ পুনঃপুন মুদ্রিত হয়েছে। কাজী এ ’ দ্দুদ্দীন বেশ কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দান করেছেন। যেমন সাদুদ্দীন তাফতাযানী ,শামসুদ্দীন কেরমানী ,সাইফুদ্দী আবহারী প্রমুখ। তিনি 700 অথবা 701 হিজরীতে জন্ম এবং 756 অথবা 760 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ষোড়শ স্তরের দার্শনিকগণ
1. সা ’ দুদ্দীন মাসউদ ইবনে উমর ইবনে আবদুল্লাহ্ তাফতাযানী: তিনি মোল্লা সা ’ দ তাফতাযানী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পরিচিতি মূলত কালামশাস্ত্র ও ভাষার অলংকারশাস্ত্রে। তিনি সার্বিকভাবে বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে জানতেন এবং দর্শন সম্পর্কেও তাঁর মোটামুটি জ্ঞান ছিল। তিনি সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম ‘ তাহযীবুল মানতেক ’ । এ গ্রন্থটি তৎকালীন সময় হতে এখন পর্যন্ত দীনী শিক্ষাঙ্গনসমূহের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে প্রচলিত। তাফতাযানী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে ,মোগলদের আক্রমণের পর তিনি ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের অনেক জ্ঞান নিজ স্মরণ শক্তির সাহায্যে নতুন করে সুন্দর ভাষায় লিখেন। আমরা বিভিন্ন স্তরের দার্শনিকদের নিয়ে যে আলোচনা করছি তা শুধু দর্শনে নিজস্ব মতের অধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে নয় ;বরং যে সকল ব্যক্তি দর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন ও এ শাস্ত্রকে পরবর্তী স্তরে পৌঁছে দিতে ভূমিকা রেখেছেন আমরা তাঁদেরকেও এ দলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাফতাযানী যুক্তিবিদ্যায় এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 712 অথবা 722 হিজরীতে নাসা শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং 792 অথবা 793 হিজরীতে সারাখসে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি সামারকান্দে মারা যান ;অতঃপর তাঁর মরদেহ সারাখসে স্থানান্তরিত করা হয়।
2. সাইয়্যেদ আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী জুরজানী: তিনি মীর সাইয়্যেদ শারিফ জুরজানী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁকে গবেষক বা মুহাক্কেক শারিফ নামে অভিহিত করা যথার্থ হয়েছে। তিনি গবেষণায় সূক্ষ্মদর্শী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি দর্শন শিক্ষা দিতেন এবং এ শাস্ত্রে অনেক ছাত্রকে শিক্ষাদান করেছেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মুহাক্কেক শারিফের বিপুল সংখ্যক মূল্যবান রচনা রয়েছে। কাজী নুরুল্লাহর মতে মুহাক্কেক শারিফের পরবর্তী প্রজন্মের সকল মুসলিম আলেম ও মনীষী তাঁর পরিবারের সদস্য ও মেহমান। তিনি প্রচুর টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। যেমন দর্শনে ‘ শারহে হিকমাতুল আইন ’ গ্রন্থের টীকা সংযোজিত গ্রন্থ ;যুক্তিবিদ্যায় ‘ শারহে মাতালিই ’ ও ‘ শামসিয়াহ্ ’ গ্রন্থদ্বয়ে টীকা সংযোজন ;বাগ্মিতা ও অলংকারশাস্ত্রে তাফতাযানীর ‘ মুতাওয়াল ’ গ্রন্থের এবং সাক্কাকীর ‘ মিফতাহুল ইলম ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ ,যামাখশারীর অলংকারশাস্ত্রভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ ‘ কাশশাফ ’ -এর টীকাগ্রন্থ ;কালামশাস্ত্রে এ ’ দ্দুদ্দীনের ‘ মুয়াফিক ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রভৃতি। মীরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো ‘ তারিফাত ’ যা ‘ তারিফাতে জুরজানী ’ নামে পরিচিত। যুক্তিবিদ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ কুবরা ’ যা ফার্সীতে লিখিত। আরবী ব্যাকরণের ‘ সারফ ’ বা শব্দগঠনের ওপর তাঁর রচিত ‘ সারফে মীর ’ গ্রন্থটি এ শাস্ত্রের প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী যা ফার্সী ভাষায় লিখিত ও তাঁর সময় থেকেই ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ।
মীর সাইয়্যেদ শারিফ কুতুবুদ্দীন রাযীর ছাত্র। যদিও তিনি জুরজানের অধিবাসী ছিলেন ,কিন্তু শিরাজে বসবাস করতেন। ‘ রওযাত ’ গ্রন্থে ‘ মাজালিসুল মুমিনীন ’ গ্রন্থসূত্রে বর্ণিত হয়েছে তখন বাদশাহ সুজা ইবনে মুজাফফার গোরগানে সাইয়্যেদ শারিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নিজের সঙ্গে শিরাজে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘ দারুশ শিফা ’ মাদ্রাসার দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেন। আমীর তৈমুর লং ‘ শিরাজ ’ অধিকার করলে মীরকে সামারকান্দে নিয়ে যান। তিনি সেখানে সাদুদ্দীন তাফতাযানীর সঙ্গে বিতর্ক করেন। তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় শিরাজে ফিরে আসেন এবং আমরণ সেখানে ছিলেন। মীর সাইয়্যেদ শারিফ বিশ বছর বয়স হতেই শিক্ষা দান ও গবেষণার কাজে ব্রত হন। তিনি দর্শনশাস্ত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ক্লাসসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটত।
কথিত আছে যে ,তাঁর ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন খাজা লিসানুল গাইব হাফেয শিরাজী। যদি কেউ তাঁর ক্লাসে কবিতা পাঠ করত তাহলে তিনি বলতেন , ‘ অনর্থক এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দর্শন চর্চা কর। ’ কিন্তু যদি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেয শিরাজী কবিতা পাঠ করতেন তাহলে তিনি বলতেন , ‘ তোমার ওপর কি ইলহাম হয়েছে আমাকে শোনাও। একটি গজল আবৃতি কর। ’ এতে অন্য ছাত্ররা প্রতিবাদ করে বলত , ‘ আমাদেরকে আপনি কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেন ,অথচ হাফিযের কবিতা শোনার আগ্রহ কেন ব্যক্ত করেন ? তিনি জবাবে বলতেন , ‘ হাফিযের সকল কবিতাই হাদীসে কুদসী ,ইলহাম ,কোরআনের সুন্দর ও লক্ষণীয় বিষয়সমৃদ্ধ যা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা সমন্বিত। ’ 325
মীর সাইয়্যেদ শারিফ 740 হিজরীতে গোরগানে (জুরজান) জন্মগ্রহণ এবং 816 হিজরীতে শিরাজে মৃত্যুবরণ করেন।326
সপ্তদশ স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের অধিকাংশ ব্যক্তিত্বই মুহাক্কেক শারিফের ছাত্র ও তাঁর চিন্তাধারার প্রচারক। যেমন :
1. মুহিউদ্দীন গুশকিনারী: তিনি মীর সাইয়্যেদ শারিফ জুরজানীর ছাত্র ও মুহাক্কেক দাওয়ানীর শিক্ষক। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সাল সম্পর্কে আমার জানা নেই।
2. খাজা হাসান শাহ বাক্কাল: তিনি ও মুহাক্কেক শারিফের ছাত্র এবং মুহাক্কেক দাওয়ানীর শিক্ষক। সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব আলী দাওয়ানী তাঁর ‘ শারহে যিন্দেগানীয়ে জালালুদ্দীন দাওয়ানী ’ গ্রন্থে হাবিবুস সাইর হতে বর্ণনা করেছেন ,মুহিউদ্দীন গুশকিনারী ও খাজা হাসান শাহ বাক্কাল মির্জা মুহাম্মদ বাইসানকারের আমলে শিরাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের দাবি তুলেছিলেন।
3. সাদুদ্দীন আসআদ দাওয়ানী: তিনি জালালউদ্দীন দাওয়ানীর পিতা। তিনিও শারিফ জুরজানীর ছাত্র ছিলেন।
4. কাওয়ামুদ্দীন কারবালী: তিনি সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকী ও জালালউদ্দীন দাওয়ানীর শিক্ষক ছিলেন। তিনিও শারিফ জুরজানীর ছাত্র।
আমরা এ স্তরের অন্য কোন দার্শনিকের সম্পর্কে জানি না। এ সময়ে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মোগলদের ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমীর তৈমুর লং-এর আক্রমণ এর ভয়াবহতাকে আরো প্রকট করে তুলেছিল। আমাদের জানা নেই ,এ সময় শিরাজের বাইরে অন্য কোন স্থানে তখন শিক্ষাঙ্গন চালু ছিল কি না ?
অষ্টাদশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. সাইয়্যেদুল হুকামা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হুসাইনী দাশতকী শিরাজী: তিনি সাইয়্যেদ সিন্দ এবং সাদরুদ্দীন দাশতকী নামে সুপরিচিত। তিনি ইসলামী জগতের প্রথম সারির দার্শনিকদের অন্যতম। মীর দামাদের সময় পর্যন্ত তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব জালালুদ্দীন দাওয়ানীর দার্শনিক মত ও গ্রন্থসমূহ এ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের নিকট সমাদৃত হতো। তার কোন কোন মত এখনও মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে প্রচলিত এবং কোন কোনটি সকলের নিকট গৃহীত। তিনি 828 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 903 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সাইয়্যেদ শারিফের ছাত্র কাওয়ামুদ্দীন কারবালী ও সাইয়্যেদ ফাজেল ফার্সীর নিকট দর্শন শিক্ষা করেন।
2. আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আসয়াদুদ্দীন দাওয়ানী সিদ্দিকী: তিনি আল্লামা ও মুহাক্কেক দাওয়ানী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দর্শন ,যুক্তিবিদ্যা ও অংকশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর অনেক মতই বর্তমানের দর্শন গ্রন্থসমূহেও রয়েছে। তিনি কাওয়ামুদ্দীন কারবালী ,মুহিউদ্দীন গুশকিনারী ,হাসান শাহ বাক্কাল ও স্বীয় পিতা আসয়াদুদ্দীন দাওয়ানীর নিকট দর্শন শিক্ষা করেছিলেন।
‘ রাওজাত ’ ও ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থদ্বয়ের লেখকগণ মনে করেছেন মুহাক্কেক দাওয়ানী মীর সাইয়্যেদ শারিফের প্রত্যক্ষ ছাত্র। কিন্তু সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব আলী দাওয়ানী তাঁর ‘ শারহে যিন্দেগানীয়ে জালালুদ্দীন দাওয়ানী ’ নামক মূল্যবান গ্রন্থে এটি ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন ,আল্লামা দাওয়ানী মীর সাইয়্যেদ শারিফকে শিক্ষক হিসেবে পান নি ;বরং তাঁর ছাত্রদের নিকট পড়াশোনা করেছেন।
আল্লামা দাওয়ানীর অনেক দার্শনিক মত তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর শোরগোলের সৃষ্টি করেছিল। জীবিত থাকাকালে তিনি সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকীর সঙ্গে মৌখিক ও লিখিতভাবে কয়েকবার বিতর্ক করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থসমূহ দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর বিভিন্ন মত আলোচিত ও পর্যালোচিত হতে থাকে। মোল্লা সাদরা তাঁর ‘ আসফার ’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিন পৃষ্ঠা আল্লামা দাওয়ানীর মত পর্যালোচনা ও প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন , ‘ তাঁর মতের পর্যালোচনাটি দীর্ঘ করার কারণ হলো অনেকে ধারণা করেন আল্লামার মতটি একত্ববাদের আলোচনার ক্ষেত্রে শেষ কথা। তাই আমরা তাঁর মতের বিভিন্ন ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করে তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। ’
মোল্লা সাদরার উপরোক্ত কথা থেকে বোঝা যায় আল্লামা দাওয়ানীর মতামত পরবর্তী দার্শনিকদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।
আল্লামা দাওয়ানীর প্রসিদ্ধির চূড়ান্ত সময়ে শিরাজ নগরী দর্শনের কেন্দ্র ছিল। তখন খোরাসান ,আজারবাইজান ,কেরমান হতে ,এমনকি রোম ,তুরস্ক ও বাগদাদ হতেও শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট শিরাজে আসতেন।327 আল্লামা দাওয়ানী 830 হিজরীতে জন্ম ও 903 অথবা 908 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আলী ইবনে মুহাম্মদ সামারকান্দী কুশজী (মোল্লা আলী কুশজী নামে পরিচিত): তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ তাজরীদ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। কুশজী একাধারে গণিতশাস্ত্রবিদ ও কালামশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গিয়াসউদ্দীন জামশিদ ও আলগবিকের (রোমীয় কাজী বা বিচারক) নিকট জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক আলগবিক ইবনে শাহরুখ ইবনে আমীর তাইমুরের (বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ) নির্দেশে তাঁর ‘ জ্যোতিষ্ক চার্ট ’ টি তৈরি করেন। তিনি তাবরীজ ও উসমানীতে সফর করেছেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত উসমানীতে কাটান। তাঁর রচিত খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ তাজরীদ ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সকল দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাতে অনেক মনীষীই টীকা সংযোজন করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ঐশী দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তিনি 879 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ঊনবিংশ স্তরের দার্শনিকগণ
এই স্তরের দার্শনিকগণ সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকী ও আল্লামা দাওয়ানীর ছাত্র। তাঁরা হলেন :
1. গিয়াসউদ্দীন মানসুর দাশতকী: তিনি সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকীর পুত্র এবং বিশিষ্ট দার্শনিকদের অন্যতম। কথিত আছে যে ,তিনি বিশ বছর বয়সে তৎকালীন সময়ের প্রচলিত সকল জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শাহ তাহমাসবের শাসনামলে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে পদত্যাগ করে শিরাজে ফিরে আসেন। শিরাজের প্রসিদ্ধ ‘ মানসুরীয়া ’ মাদ্রাসাটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত। তিনি পিতার অনুসরণে আল্লামা দাওয়ানীর মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। তিনি কখনও কখনও তাঁদের উভয়ের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি দর্শনের ওপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ইসবাতুল ওয়াজিব ,শারহে হায়াকিলুন্ নূর (সোহরাওয়ার্দীর গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ,খাজা নাসিরুদ্দীনের ‘ শারহে ইশারাত ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ ,ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রভৃতি।
মোল্লা সাদরা তাঁর ‘ আসফার ’ গ্রন্থের ‘ ইলাহীয়াত ’ অধ্যায়ে তাঁকে পবিত্র ,সমর্থিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত পিতার রহস্য ,আলেম ও নেতাদের সাহায্যকারী এবং ঐশী জগতের অধিপতির অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। গিয়াসউদ্দীন দাশতকী 940 অথবা 948 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মাহমুদ নাইরিযী: তিনি সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকীর অন্যতম ছাত্র। তিনি জালালুদ্দীন দাওয়ানীর কয়েকটি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলোতে তাঁর বিভিন্ন মতের সমালোচনা ও স্বীয় শিক্ষক দাশতকীর পক্ষাবলম্বন করেছেন।
3. কাজী কামালুদ্দীন মাইবাদী ইয়াযদী: তাঁর প্রসিদ্ধি দু ’ টি গ্রন্থের মাধ্যমে। একটি হলো আসিরুদ্দীন আবহারীর ‘ হেদায়া ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা ‘ শারহে হেদায়ায়ে মাইবাদী ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং অপরটি হলো হযরত আলীর ‘ কবিতা সমগ্রের ’ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি দর্শনশাস্ত্রে ‘ জামে গীতি নামা ’ শীর্ষক ফার্সীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।
4. জামালউদ্দীন মাহমুদ শিরাজী: তিনি জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বিভিন্ন অঞ্চল হতে তাঁর নিকট ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতেন। ‘ মুকাদ্দাস আরদেবিলী ’ নামে প্রসিদ্ধ মোল্লা আহমাদ আরদেবিলী ,মোল্লা আবদুল্লাহ্ শুশতারী , ‘ তাহজীবুল মানতেক ’ গ্রন্থের টীকা সংযোজক মোল্লা মির্জা জান শিরাজী প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন।
5. মোল্লা হুসাইন ইলাহী আরদেবিলী: তিনি খাজা শারাফুদ্দীন আবদুল হক আরদেবিলীর পুত্র। তিনি আল্লামা দাওয়ানী ও আমীর গিয়াসুদ্দীনের ছাত্র। তিনি শিয়া ছিলেন। তিনি প্রথম সাফাভী শাসক শাহ ইসমাঈল সাফাভীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। এ কারণে তাঁর অনেক লেখা তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে লিখেছেন ও তাঁকে উপহার দিয়েছেন। তিনি ইরানের আরদেবিলের অধিবাসী হলেও ইরানের অন্যান্য শহরেও জ্ঞানান্বষণে সফর করেছেন ,যেমন শিরাজ ও হেরাত (যা বর্তমানে আফগানিস্তানের অংশ)। তিনি যুক্তিবিদ্যা ,দর্শন ,কালামশাস্ত্র ,জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতির ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তৎকালীন সময়ের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তিনি পুরাতন গ্রন্থগুলোতে টীকা সংযোজন করেছেন ও সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন শারহে মুয়াফিক ,শারহে মুতালেই ,শারহে শামসিয়াহ্ ,শারহে হেদায়ায়ে মাইবাদী ,শারহে তাজরীদ ,শারহে চাগমিনী প্রভৃতি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ এবং খাজা নাসিরুদ্দীনের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ শারহে তাযকিরাহ্ ,জ্যামিতিতে এক্লিডসের রচিত গ্রন্থ ,গ্রহ নক্ষত্রের উচ্চতা ও গতিবিধি (অ্যাস্ট্রোলেব) সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সময় আমাদের জানা নেই।
বিংশ স্তরের দার্শনিকগণ
1. মোল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী: তিনি ‘ তাহজীবুল মানতেক ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ ‘ হাশিয়েয়ে মোল্লা আবদুল্লাহ্ ’ র জন্য সুপরিচিত যা দীনী ছাত্রদের যুক্তিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক। কেউ কেউ মনে করেন তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন না ,কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ তিনি ফিকাহ্ ও যুক্তিবিদ্যা (মানতেক) উভয় শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিরাজে জামালুদ্দীন মাহমুদ ও গিয়াসউদ্দীন দাশতকীর নিকট পড়াশোনা করেন। শেষ জীবনে ইরাকে চলে যান ও 981 হিজরীতে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মোল্লা হাবিবুল্লাহ্ বাগনাভী শিরাজী: তিনি মোল্লা মির্জা জান ও ফাজেল বাগনাভী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি জামালুদ্দীন মাহমুদের ছাত্র ছিলেন ও আল্লামা দাওয়ানীর কয়েকটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। আল্লামা সাবযেওয়ারী তাঁর ‘ শারহে মানযুমা ’ গ্রন্থের ‘ প্রকৃতিতত্ত্ব ’ অধ্যায়ে ‘ ফাজেল বাগনাভী ’ র নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি 994 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ খাফারী শিরাজী: তিনি আমীর গিয়াসউদ্দীন মনসুরের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত তিনি আল্লামা দাওয়ানী ও সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন দাশতকীরও ছাত্র ছিলেন। তিনি ‘ শারহে তাজরীদ ’ ও ‘ শারহে হিকমাতুল ওয়াজিব ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মোল্লা সাদরা তাঁর ‘ আসফার ’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাঁর মতের উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন। খাফারীকে ঊনবিংশ
স্তরের দার্শনিকও বলা যেতে পারে। কারণ এ স্তরে তিনি যুবক ছিলেন এবং বিংশ
স্তরে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছেছিলেন। তিনি 957 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি 935 হিজরীতে মারা যান।
4. খাজা আফজালুদ্দীন তারাকাহ্: তিনি জামালুদ্দীন মাহমুদের ছাত্র।328 ‘ রাওজাত ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন , ‘ বিশিষ্ট দার্শনিক খাজা আফজালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হাবিবুল্লাহ্ তারাকাহ্ ‘ নাসরুল বায়ান ’ নামে প্রসিদ্ধ শেখ আবুল কাসেম কাযরুনীর শিক্ষক ছিলেন। ’ নাসরুল বায়ান তাঁর ‘ সিলমুস সামাওয়াত ’ গ্রন্থের ‘ দার্শনিকদের ইতিহাস ’ অংশে তাঁর শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে তাঁর প্রসিদ্ধির সময়কাল 970-990 হিজরী বলেছেন। তারাকাহ্ ইরাক ও খোরাসানে জীবন কাটান।
5. হাকিম দাউদ ইবনে উমর এনতাকী মিসরী: তাঁর নাম আমি শুধু ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থে দেখেছি। তিনি দশম হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ ও একাদশ হিজরী শতাব্দীর প্রথমাংশের একজন প্রথম সারির দার্শনিক ও চিকিৎসক। তিনি স্বয়ং নিজ জীবনী সম্পর্কে বলেছেন ,তিনি জন্মান্ধ ছিলেন ও সাত বছর পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবন কাঠিয়েছেন। এ অবস্থায়ই প্রাথমিক পড়াশোনা ও কোরআন মুখস্থ করেন। সব সময় নিজ আরোগ্যের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। এ সময় মুহাম্মদ শরীফ নামের এক ইরানী তাঁর এলাকায় আসেন ও চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁকে আরোগ্য দান করেন। মুহাম্মদ শরীফ নামের এই ব্যক্তি তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধা লক্ষ্য করে তাঁকে নিজ ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন ও তাঁকে দর্শন ,যুক্তিবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দান শুরু করেন। দাউদ ফার্সী ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে শিক্ষকের নিকট তা শেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু মুহাম্মদ শরীফ তাঁকে গ্রীক ভাষা শেখা উত্তম বলে তা শেখান। তখন ঐ অঞ্চলে কেউ গ্রীক ভাষা জানত না।
অতঃপর দাউদ কায়রোতে যান। কিন্তু মিশরের অধিবাসীদেরকে দর্শনের প্রতি অনাগ্রহী লক্ষ্য করে সেখান হতে ফিরে আসেন। তিনি শেষ জীবন মক্কায় কাটান ও সেখানেই 1008 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ ,যেমন ইবনে সিনার কানুন ,শাফা ও ইশারাত ,ইখওয়ানুস সাফাদের পুস্তিকাদি ,হিকমাতুল মাশরিকিয়া ,তালিকাত ,মুহাকিমাত ,মুতারিহাত প্রভৃতিতে পণ্ডিত ছিলেন।
দাউদ বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে ‘ এশ্ক ’ গ্রন্থটি সম্পর্কে ‘ নামে দানেশওয়ারান ’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।329
একুশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মীর মুহাম্মদ বাকের দামাদ: তিনি এতটা প্রসিদ্ধ যে তাঁর পরিচয় দেয়ার আর প্রয়োজন নেই।330 দার্শনিক হিসেবে তাঁকে যদিও প্রথম সারির বলা যায় না ,তবে তিনি দ্বিতীয় সারির দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একাধারে দার্শনিক ,ফকীহ্ ,সাহিত্যিক ,হাদীসশাস্ত্রবিদ ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। বলা যায় ,বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। নিজেকে দর্শনের ‘ তৃতীয় শিক্ষক ’ বলে দাবি করতেন।331
তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। দ্বাবিংশ স্তরে তাঁর কিছু ছাত্রের নাম আমরা উল্লেখ করব। মীর দামাদ কার নিকট দর্শন শিক্ষা করেছেন সে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে অনেকে তাঁর শিক্ষকের তালিকায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম এসেছেন। যেমন শেখ আবদুল আলী কোর্কী ,সাইয়্যেদ নুরুদ্দীন আমেলী ,তাজউদ্দীন হুসাইন সায়েদ তুসী ,ফাখরুদ্দীন আসতারাবাদী সামাকী প্রমুখ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষক ছিলেন ;দর্শনে নয়। একমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তি দর্শনের শিক্ষক ছিলেন।
সাইয়্যেদ আলী বেহবাহানী ‘ মীর দামাদের জীবনী ও দর্শনের পর্যালোচনা ’ নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন , ‘ ফাখরুদ্দীন মুহাম্মদ হুসাইনী আসতারাবাদী সম্রাট তাহমাসবের (918-984 হিজরী) সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। ইসকান্দারবিকের বর্ণনা মতে ,তিনি আসতারাবাদের সামাকের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ও মীর দামাদ তাঁর ছাত্র ছিলেন। মুহাক্কেক খাফারীর অনুকরণে ফাখরুদ্দীনকে ‘ মুহাক্কেক ফাখারী ’ বলা হতো। কিন্তু সম্ভবত মীর দামাদ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না ও তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি।
মুহাদ্দিস কুমীও তাঁর ‘ আল কুনী ওয়াল আলকাব ’ গ্রন্থে তাঁকে মীর দামাদের শিক্ষক বলেছেন। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থেও তা-ই বলা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ সকল গ্রন্থে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বিষয়ে ফাখরুদ্দীন আসতারাবাদী হুসাইনী নামে অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে যিনি আল্লামা কুশচীর ‘ শারহে তাজরীদ ’ গ্রন্থের ইলাহিয়াত ,জাওয়াহির ও আওয়ারিজ অধ্যায়ের টীকা লিখেছেন। জনাব আলী দাওয়ানীর বর্ণনানুসারে তিনি দাওয়ানীর ‘ তাহসীবুল মানতেক ’ গ্রন্থেরও টীকা লিখেছেন। যদিও সাধারণভাবে মনে হয় তাঁরা দু ’ ব্যক্তি নন ;বরং একজন ,কিন্তু ‘ যুররিয়া ’ গ্রন্থের লেখকের মতে তাঁরা দু ’ ব্যক্তি। একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ফাখরুদ্দীন সামাকী এবং অপরজন হলেন ফাখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন সামাকী।
আমরা মীর দামাদের দর্শনের শিক্ষকদের সম্পর্কে এর অধিক কিছু জানি না। ফাখরুদ্দীন সামাকীর ছাত্র কারা ছিলেন বা তিনি কার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাও আমাদের জানা নেই । তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাও অজ্ঞাত। কথিত আছে তিনি (ফাখরুদ্দীন) গিয়াসুদ্দীন মনসুর দাশতকীর ছাত্র ছিলেন।
2. শেখ বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুস সামাদ আমেলী: তিনি জাবালুল আমেলের অধিবাসী ও ইরানে হিজরত করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পে পণ্ডিত ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মোল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী ব্যতীত অন্য কারো সম্পর্কে আমরা জানি না। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে (যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে) তাঁর শিক্ষকের ক্রমধারা (ওপর দিকে) মোল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদীর মাধ্যমে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী ও ইবনে সিনা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি নিশ্চিত যে ,শেখ বাহাউদ্দীন সাহিত্যিক ,ফকীহ্ ,মুফাসসির ,গণিতজ্ঞ ,স্থপতি এবং কবি ছাড়া দার্শনিকও ছিলেন। তবে তাঁর দর্শনের ছাত্রদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। প্রসিদ্ধি আছে যে ,মোল্লা সাদরা (সাদরুল মুতাআল্লেহীন) তাঁর নিকট দর্শন পড়েছেন এবং তিনি তাঁর (সাদরার) মধ্যে বিশেষ প্রতিভা লক্ষ্য করে মীর দামাদের নিকট প্রেরণ করেন। শেখ বাহাউদ্দীনের দর্শন বিষয়ক কোন লেখা আমাদের হাতে নেই তবে সম্প্রতি মিশর হতে ‘ ওয়াহ্দাতে উজুদ ’ সম্পর্কিত তাঁর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। শেখ বাহাউদ্দীন 1030 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. মীর আবুল কাসেম ফানদারাসকী: তিনি ইরানের আসতারাবাদের ফানদারাসকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে গণিতজ্ঞ ,দার্শনিক ও আরেফ ছিলেন। যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বড় শিক্ষাঙ্গন ও অসংখ্য ছাত্র ছিল তদুপরি তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । তিনি শেখ বাহায়ী ও মীর দামাদের সমকালীন ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতবর্ষেও সফর করেছেন ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তিনি যুক্তিবিদ্যার ‘ আনায়াত ’ বা পঞ্চশাস্ত্র (বিতর্ক ,কবিতা ,বক্তব্য ,ভ্রান্তযুক্তি ও যুক্তি) নিয়ে পুস্তিকা রচনা করেছেন। তিনি মাশশায়ী ধারায় (অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের ইসলামীরূপ) ‘ গতি ’ সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি 1050 হিজরীতে 80 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
বাইশতম স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের দার্শনিকগণ হলেন শেখ বাহাউদ্দীন ,মীর দামাদ ও মীর ফানদারাসকীর ছাত্র।
1. রাফিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হায়দার হুসাইনী তাবাতাবায়ী নাইনী (মির্জা রাফিয়া নামে প্রসিদ্ধ): তিনি শেখ বাহায়ী ও মীর ফানদারাসকীর ছাত্র ছিলেন। তিনি নাইন ,যাওয়ারাহ ও আরদেস্তানের সাইয়্যেদদের বংশধর। কাজার শাসকদের সমকালীন বিশিষ্ট দার্শনিক মির্জায়ী জেলভে (মৃত্যু 1314 হিজরী) তাঁরই উত্তরপুরুষ। তিনি (রাফিউদ্দীন) অস্তিত্বের পর্যায় বিষয়ে যে পুস্তিকা লিখেছিলেন তা পরবর্তী দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ শারহে ইশারাত ’ ও শারিফ জানজানীর ‘ হিকমাতুল আইন ’ গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। তিনি দর্শনের ‘ ইসতিলজাম ’ বিষয়েও পুস্তিকা রচনা করেছেন। মৌল আকীদা বিষয়ক তাঁর ‘ সামারেয়ে সাজারায়ে ইলাহীয়া ’ নামক পুস্তিকাটি দার্শনিক ভূমিকাসহ সম্প্রতি বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ্ নুরানী প্রকাশ করেছেন। মির্জা রাফিয়া 999 হিজরীতে জন্ম ও 1083 হিজরীতে 85 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কাওয়ামী শিরাজী (মোল্লা সাদরা ও সাদরুল মুতাআল্লেহীন নামে প্রসিদ্ধ): তিনি বিশিষ্ট দার্শনিক ও ঐশীপ্রজ্ঞাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ঐশী দর্শনকে নতুন দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে নব পর্যায়ে উত্তরণ ঘটান। সাদরা সর্বোচ্চ দর্শন বা ঐশী প্রজ্ঞাকে-যাকে ‘ প্রকৃত দর্শন ’ নামে অভিহিত করা হয় (পূর্বে প্রকৃতিবিজ্ঞান ,গণিত ও অন্যান্য বিষয়কে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হতো)-স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন ও পূর্বের অনেক মৌল নীতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক মতকে ছাপিয়ে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।
মোল্লা সাদরার দর্শন চারটি নদীর মিলনস্থলের ন্যায় চারটি মতকে সমন্বিত করেছে অর্থাৎ তিনি অ্যারিস্টটল ও ইবনে সিনার মাশশায়ী দর্শন ,সোহরাওয়ার্দীর ইশরাকী দর্শন ,মুহিউদ্দীন আরাবীর এরফানী দর্শন ও কালামশাস্ত্রীয় চিন্তাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায় যে ,তিনি চারটি মৌলের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন মৌলের সৃষ্টি করেছেন যা পূর্ববর্তী উপাদান হতে স্বতন্ত্র।
মূলত মোল্লা সাদরার দর্শন ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক অবিরত পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের ফল। মোল্লা সাদরার দর্শন বাহ্যিকভাবে সহজ মনে হলেও অত্যন্ত কঠিন ও সহজবোধ্য নয়। তাঁর বিবরণ ও লেখার ধারা সাহিত্যিক ও দক্ষতাসম্পন্ন। তাই ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ণ মেধার ব্যক্তিত্বকেও দীর্ঘদিন তাঁর গ্রন্থের ওপর কাজ করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে তা অধ্যয়ন করে বুঝেছি মনে করলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের অধ্যয়নে তিনি যে সঠিক বুঝেননি তা বুঝতে পারবেন। এ কারণেই এমন অনেক ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন মোল্লা সাদরার দর্শন গ্রন্থ পড়িয়েও তার গভীরে প্রবেশে সক্ষম হননি। তাই সাদরার দর্শন বোঝা যে কোন দর্শন পড়া ব্যক্তির জন্যই সম্ভব নয়। মোল্লা সাদরা শেখ বাহায়ী ও মীর দামাদের ছাত্র ছিলেন। তিনি ‘ উসূলে কাফী ’ র ব্যাখ্যাগ্রন্থে শেখ বাহায়ীকে তাঁর ‘ উলুমে নাকলীর ’ (কোরআন ও হাদীস) এবং মীর দামাদকে ‘ উলুমে আকলী ’ র (যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের) শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা সাদরার গ্রন্থসমূহ এতটা প্রসিদ্ধ যে ,তার পরিচয় দানের প্রয়োজন নেই। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ আসফার ’ যা দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ বলে বিবেচিত। তিনি ইরান হতে সাত বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন। সপ্তমবার 1050 হিজরীতে হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনের পথে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।
3. শামসুদ্দীন গিলানী (মোল্লা শামসা নামে পরিচিত): তিনি মীর দামাদের অন্যতম ছাত্র। তাঁর ও মোল্লা সাদরার মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয়েছে। মোল্লা শামসা দর্শনের পরিমাণগত গতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অন্যান্য বিষয়ে (যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্ব) মোল্লা সাদরাকে প্রশ্ন করেছেন ও মোল্লা সাদরা পত্রের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত উত্তরগুলো তাঁরই ‘ মাবদা ওয়া মায়াদ ’ নামের গ্রন্থে টীকা আকারে সংযোজন করে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।
4. সুলতানুল উলামা আমুলী মাজেনদারানী (খলীফাতুস সুলতান নামে প্রসিদ্ধ): তিনিও শেখ বাহায়ী ও মীর দামাদের ছাত্র ছিলেন। সাফাভী শাসক শাহ আব্বাস স্বীয় কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। তিনি কিছুদিন শাসক শাহ সাফী ও দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভাল গবেষক ছিলেন। ‘ মায়ালিম ’ ও ‘ শারহে লোমআ ’ গ্রন্থে তাঁর টীকা সংযোজিত অংশটি তাঁর গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর। তিনি এতে বাহুল্য ও অনাবশ্যক কথা পরিহার করেছেন। তিনি আল্লামা কুশচীর ‘ শারহে তাজরীদ ’ গ্রন্থেরও টীকা লিখেছেন। তিনি 1063 হিজরীতে 64 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।
5. সাইয়্যেদ আহমাদ আমেলী: তিনি মীর দামাদের খালাতো ভাই ও ছাত্র। তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থে ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ের টীকা লিখেছেন। তাঁর টীকা সংযোজিত গ্রন্থটি তেহরান হতে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ টীকাগ্রন্থের কিছু অংশ মীর দামাদের উদ্ধৃতি যার কোন কোনটি তিনি সংশোধন করেছেন ও নিজে মত দিয়েছেন। মীর দামাদ ও সাইয়্যেদ আহমাদ উভয়েই মুহাক্কেক কুরকীর দৌহিত্র।
6. কুতুবুদ্দীন আশকুরী: তিনি ‘ মাহবুবুল কুলুব ’ নামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক। তিনি দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে মীর দামাদের নিকট পড়াশোনা করেন।
7. সাইয়্যেদ আমীর ফাজলুল্লাহ্ আসতারাবাদী: এ ব্যক্তিও মীর দামাদের ছাত্র। তাঁর স ¤পর্কে সঠিক কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। ‘ রওজাত ’ গ্রন্থে মুকাদ্দাস আরদেবিলীর জীবনী আলোচনায় ‘ রিয়াজুল উলামা ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ,আমীর ফাজলুল্লাহ্ মুকাদ্দাস আরদেবিলীর স্বনামধন্য ছাত্রদের একজন। মুকাদ্দাস আরদেবিলীর অন্তিম মুহূর্তে (মৃত্যুর পূর্বে) তাঁর পর দীনী বিষয়ে কার নিকট জনগণ প্রশ্ন করবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন , ‘ শরীয়তের বিষয়ে আমীর আলামের নিকট এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে আমীর ফাজলুল্লাহর নিকট। ’ 332
তেইশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মোল্লা মুহসেন ফায়েয কাশানী: তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ,দার্শনিক ও আরেফ। তিনি মোল্লা সাদরার ছাত্র ও জামাতা ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট দর্শন পড়েছেন । দর্শন সংক্রান্ত তাঁর একটি পুস্তিকা এখনও বিদ্যমান। ‘ উসূলুল মাআরিফ ’ নামের তাঁর একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।
দর্শনে ফায়েয হতে যে সকল বিবরণ আমাদের নিকট রয়েছে তা হুবহু মোল্লা সাদরার বক্তব্যের সারাংশ। আমরা ইতোপূর্বে মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের আলোচনায় ফায়েয কাশানীর নাম উল্লেখ করেছি। তিনি 1091 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মোল্লা আবদুর রাজ্জাক লাহিজী: তিনি ‘ শাওয়ারিকুল ইলহাম ’ ও ‘ গাওহার মুরাদ ’ গ্রন্থের লেখক। তিনি মোল্লা সাদরার ছাত্র ও জামাতা। তিনি মোল্লা মুহসেন ফায়েযের তুলনায় অনেক কম তাঁর শিক্ষকের চিন্তাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই তাঁর লেখায় মোল্লা সাদরা অপেক্ষা পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ ,যেমন মুহাক্কেক দাওয়ানী ও গিয়াসউদ্দীন দশতাকীর প্রভাব অধিকতর লক্ষণীয়। তিনি 1071 অথবা 1072 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. মোল্লা রজব আলী তাবরীজী ইসফাহানী: ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক ‘ রিয়াজুল উলামা ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে ,তিনি দ্বিতীয় শাহ আব্বাস (সাফাভী শাসক) ও সভাসদদের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন ও তাঁরা সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট আসতেন। মোল্লা রজব আলীর ছাত্রদের মধ্যে মাওলা মুহাম্মদ তানকাবানী ,হাকিম মুহাম্মদ হুসাইন কুমী ও কাজী সাঈদ কুমী উল্লেখযোগ্য। তিনি মীর ফানদারাসকীর ছাত্র ছিলেন এবং 1080 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. মোল্লা মুহাম্মদ বাকের: তিনি মুহাক্কেক সাবযেওয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রথম সারির একজন দার্শনিক ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি শেখ বাহায়ী ও মীর ফানদারাসকীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থের ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ের সুন্দর টীকা লিখেছেন। ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন , ‘ মুহাক্কেক খুনসারী ও ‘ সারাব ’ বা মরীচিকা নামে প্রসিদ্ধ মোল্লা মুহাম্মদ তানকাবানী তাঁর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত মুহাক্কেক খুনসারী ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ছাত্র ছিলেন ;দর্শনশাস্ত্রে নয়। তিনি 1090 হিজরীতে মারা যান।
5. অগা হুসাইন খুনসারী (মুহাক্কেক খুনসারী নামে প্রসিদ্ধ): তিনি মরহুম সাবযেওয়ারীর ছাত্র (হাদীস ও ফেকাহ্শাস্ত্রে) ও বোন জামাতা। তিনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় মীর ফানদারাসকীর ছাত্র ছিলেন। তিনিও ‘ শাফা ’ গ্রন্থের ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ের ওপর প্রসিদ্ধ একটি টীকাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ শারহে ইশারাত ’ ,আল্লামা কুশচীর ‘ শারহে তাজরীদ ’ ও ‘ মুহাকিমাত ’ গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। তিনি 1098 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক মোল্লা যামান ইবনে মোল্লা কালাব আলী তাবরীজীর জীবনীতে লিখেছেন , ‘ ফারায়িদুল ফাওয়ায়িদ ফি আহওয়ালিল মাদারিস ওয়াল মাসাজিদ ’ নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে যা তিনি ইসফাহানের ‘ লুতফুল্লাহ্ ’ মাদ্রাসায় থাকাকালীন লিখেছিলেন। এ মাদ্রাসায় যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি পড়াশোনা করেছেন তিনি তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন অগা হুসাইন খুনসারী ,মোল্লা শামসাই গিলানী ,মোল্লা হাসান লানবানী গিলানী (তিনি একজন দার্শনিক ও আরেফ ছিলেন এবং মাওলানা রুমীর ‘ মসনভী ’ গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেছেন)। তন্মধ্যে মোল্লা হাসান লানবানী তাকওয়া পরহেজগারীর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।... ঐ মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে আরেফগণের আদর্শ ও গবেষকদের পুরোধা মোল্লা রজব আলী তাবরীজী ও তাঁর ছাত্র মীর কাওয়ামুদ্দীন রাযী তেহরানীও ( ‘ আইনাল হিকমা ’ গ্রন্থ রচয়িতা) ছিলেন। ’ 333 তিনি আরো উল্লেখ করেছেন , ‘ এ মাদ্রাসায় বিশিষ্ট দার্শনিক ও গবেষক মোল্লা আবুল কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রাবী গুলপায়গানীও পড়াশোনা করেছেনথ- যিনি আকলী ও নাকলী বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সূক্ষ্ম টীকা লেখায় পারদর্শী ছিলেন... সম্ভবত তিনি প্রথম মাজলিসীর ছাত্র ছিলেন। ’ 334
উপরোল্লিখিত মোল্লা হাসান লানবানী আল্লামা মাজলিসীর অন্যতম ছাত্র মোল্লা হুসাইন লানবানীর পিতা। লানবানী ও গুলপায়গানী উভয়েই এ স্তরের ব্যক্তিত্ব।
এ স্তরের আরো কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা তেমন প্রসিদ্ধ নন। যেমন মোল্লা সাদরার ছাত্র আলী রেজা অগাজানী ও শেখ হুসাইন তানকাবানী। আনন্দের বিষয় ,সম্প্রতি মাশহাদের ‘ ইলাহিয়াত ওয়া মায়ারেফে ইসলামী ’ মহাবিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন অশতিয়ানী ‘ মীর দামাদ ও মীর ফানদারাসকীর সময় হতে বর্তমান সময়ের ইরানের নির্বাচিত দার্শনিকদের বিবরণ ’ শিরোনামের গ্রন্থে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণনাও দিয়েছেন।
চব্বিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ মুফিদ কুমী: তিনি কাজী সাঈদ নামে পরিচিত এবং তাঁর উপাধি হলো ‘ হাকিমে কুচাক ’ অর্থাৎ ক্ষুদ্র দার্শনিক। তিনি মোল্লা মুহসেন ফায়েয ,মোল্লা আবদুর রাজ্জাক লাহিজী ও মোল্লা রজব আলী তাবরীজীর ছাত্র। তিনি ইসফাহানে মোল্লা রজব আলীর নিকট পড়াশোনা করেন ও ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখকের বর্ণনানুসারে তিনিও তাঁর শিক্ষক রজব আলীর ন্যায় সাফাভী শাসক শাহ আব্বাসের নিকট সম্মানিত ছিলেন। তিনি মোল্লা আবদুর রাজ্জাকের নিকট কোমে এবং সম্ভবত কোমেই ফায়েয কাশানীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ‘ রওজাত ’ এবং ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থের লেখকদ্বয় তাঁর মৃত্যুর সঠিক বছর সম্পর্কে অবগত নন ,তবে ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের পাদটীকায় ‘ আয যুররিয়া ’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর জন্ম 1049 হিজরী ও মৃত্যু 1103 হিজরী বলেছেন।
2. মোল্লা মুহাম্মদ তানকাবী সারাব: তিনি মোল্লা রজব আলী তাবরীজী এবং মুহাক্কেক সাবযেওয়ারীর ছাত্র ছিলেন।
3. জামালুদ্দীন খুনসারী (আগা জামাল খুনসারী নামে পরিচিত): তিনি অগা হুসাইন খুনসারীর (পূর্বোল্লিখিত) পুত্র ও ছাত্র। তিনি সাবযেওয়ারীর নিকটও পড়াশোনা করেছেন। তিনি ইবনে সিনার ‘ শাফা ’ গ্রন্থের ‘ তাবিয়িয়াত ’ বা প্রকৃতি বিষয়ক অধ্যায়ের টীকা লিখেছেন। তিনি নাসিরুদ্দীন তুসীর ‘ শারহে ইশারাত ’ গ্রন্থেরও টীকা লিখেছেন। তিনি বর্ণনামূলক (ফিকাহ্ ও হাদীস) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক (যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন) উভয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি 1121 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. কাওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ রাযী: তিনি ‘ কাওয়ামুদ্দীন হাকিম ’ নামে পরিচিত। জনাব হুমায়ী তাঁর ‘ শারহে মাশায়িরে মোল্লা জাফর লানগরুদী ’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন ,তিনি মোল্লা রজব আলী তাবরীজীর ছাত্র এবং শেখ এনায়েতুল্লাহ্ গিলানীর শিক্ষক ছিলেন। জনাব সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন অশতিয়ানী ‘ মীর দামাদ ও মীর ফানদারাসকীর সময় হতে বর্তমান সময়ের নির্বাচিত ইরানী দার্শনিকদের বিবরণ ’ শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
5. মুহাম্মদ রাফী পীরযাদেহ্: তিনিও মোল্লা রজব আলী তাবরীজীর ছাত্র ও পরোক্ষভাবে মীর ফানদারাসকীরও ছাত্র। জনাব জালালুদ্দীনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।
6. আলী কুলী খান: তিনি কারচেকায়ী খান খিলজী কুমীর পুত্র। অগা হুসাইন খুনসারী ,মোল্লা শামসায়ী গিলানী ও মোল্লা রজব আলী তাবরীজী তাঁর শিক্ষক ছিলেন। জনাব মুর্দারেসী তাবাতাবায়ীর ‘ তুরবাত ’ নামক গ্রন্থের 235-240 পৃষ্ঠায় তাঁর রচিত অনেকগুলো পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে। আলী কুলী খান 1020 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 1097 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে কোমের খান মাদ্রাসাটি তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মাহ্দী কুলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
পঁচিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মোল্লা মুহাম্মদ সাদিক আরদিসতানী: তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা যায় যে ,তিনি দার্শনিক ছাড়াও একজন সাধক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফলে অন্যদের তিরস্কার ,লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়েছেন। তাঁকে কাফের প্রতিপন্ন করা হয়েছে ও তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি 1134 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হুমায়ী ও অশতিয়ানীর বর্ণনামতে মোল্লা মুহাম্মদ সাদিক মানবসত্তা ও প্রবৃত্তির বস্তুগত ও আত্মিক শক্তির বিষয়ে ‘ হিকমতে সাদিকিয়া ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা এখনও বিদ্যমান।
2. শেখ এনায়েতুল্লাহ্ গিলানী: তিনি মাশ্শায়ী ধারার একজন শিক্ষক ও মীর কাওয়াম হাকিমের ছাত্র।
3. মীর সাইয়্যেদ হাসান তালেকানী: তিনি মুহিউদ্দীন আরাবীর ‘ শারহে ফুসুস ’ এবং সোহরাওয়ার্দীর ইশরাকী দর্শনের গ্রন্থসমূহ পড়াতেন ।
ছাব্বিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মোল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী: মোল্লা ইসমাঈল বিগত কয়েক হিজরী শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তিনি ইরানের উত্তরাঞ্চলের মাজেনদারানের অধিবাসী। ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক তাঁর বেশ প্রশংসা করেছেন ;তাঁর জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক) ,প্রজ্ঞা ,তাকওয়া ,উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মর্যাদার বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন। বলা হয়েছে ,সম্রাট নাদির শাহ কারো প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে না দেখলেও এ মনীষীকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। এ সময়েই আফগানরা ইরানে আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী তাঁর কোন কোন লেখায় এ ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা করেছেন। ‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক তাঁর শিক্ষকদের সম্পর্কে জানা যায়নি বলে প্রকাশ করেছেন। আফগানদের ধ্বংসযজ্ঞের পর ইরানে দর্শন চর্চা এ ব্যক্তির মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। যেমন অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী ,মোল্লা মাহ্দী নারাকী ,মির্জা আবুল কাসেম ইসফাহানী ও মোল্লা মেহরাব গিলানী। ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী 1173 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মির্জা মুহাম্মদ তাকী আলমাসী: ‘ রওজাত ’ গ্রন্থে তাঁকে আল্লামা মাজলিসীর বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পিতা প্রথম মাজলিসীর পৌত্র ছিলেন। তিনি অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর শিক্ষক ছিলেন বলা হয়েছে।
3. মোল্লা হামযা গিলানী: তিনি মোল্লা মুহাম্মদ সাদিক আরদিসতানীর ছাত্র ও 1134 হিজরীতে মারা যান।
4. মোল্লা আবদুল্লাহ্ হাকিম: তিনিও ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী ও আলমাসীর ন্যায় অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর শিক্ষক ছিলেন।
সাতাশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী গিলানী ইসফাহানী: তিনি বিগত নিকটবর্তী শতাব্দীসমূহের অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তিনি মোল্লা সাদরার দর্শনের পুনর্জীবন দানকারী। মোল্লা সাদরার দর্শন তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে প্রচলিত থাকলেও তা পূর্ববর্তী দার্শনিক ,যেমন ইবনে সিনা ও শেখ সোহরাওয়ার্দীর দর্শনের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসারের কারণে তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। বিশেষত পূর্ববর্তী ধারার দর্শনের কারণে প্রাচীন ধারার মীর ফানদারাসকী ও তাঁর ছাত্র মোল্লা রজব আলী তাবরীজী শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন।
স্বয়ং মোল্লা সাদরা বলেছেন ,তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সম্মানের পাত্র ছিলেন না ;বরং একজন সাধারণ ছাত্রের ন্যায় জীবনযাপন করতেন ,অথচ তাঁর প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব মোল্লা রজব আলী তাবরীজী এতটা প্রসিদ্ধ ছিলেন যে ,রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। মোল্লা সাদরার দর্শন ধীর গতিতে পরিচিতি লাভ করে। সম্ভবত মাটির গভীরে সুপ্ত এ প্রস্রবণের উন্মুক্ত পথটি সর্বপ্রথম অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়। ‘ রওজাত ’ গ্রন্থ অনুসারে বাইদাবাদী একজন পরহেজগার ,দুনিয়াবিমুখ ,আত্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। শেখ আগা বুযুর্গ তেহরানী তাঁর গ্রন্থসমূহে তাঁকে একজন মহান আরেফ ও সাধক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রকৃতই একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী সাধক ছিলেন। এরফানশাস্ত্রে তাঁর রচিত দু ’ টি গ্রন্থ কোমের বিশিষ্ট আলেম মুদাররেসী তাবাতাবায়ী কর্তৃক অনূদিত হয়েছে যা 1352 হিজরীতে প্রকাশিত ‘ ওয়াহিদ ’ নামক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐশী প্রবণতা শাসকগোষ্ঠী হতে তাঁকে দূরে রাখত ,যদিও তাঁরা তাঁর নিকট আসতেন ,তবে তিনি তাঁদের উপেক্ষা করতেন।
বাইদাবাদী অনেক স্বনামখ্যাত ছাত্রকে শিক্ষাদান করেছেন যাঁদের সম্পর্কে আমরা কিছু পরেই আলোচনা করব। তিনি 1197 হিজরীতে মারা যান।
2. মোল্লা মাহ্দী নারাকী: তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ও দার্শনিক। তিনি ও তাঁর পুত্র মোল্লা মাহমুদ নারাকী উভয়েই ইসলামী বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম এবং বিবরণমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মোল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ীর ছাত্র। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের শিফতী ইসফাহানী ও মুহাম্মদ ইবরাহীম কালবাসী তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম।
3. মির্জা আবুল কাসেম হুসাইনী খাতুনাবাদী: তিনি ‘ মুদাররিস ’ নামে প্রসিদ্ধ ও আল্লামা মাজলিসীর বংশধর। তিনিও মোল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ীর ছাত্র। 1203 হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
4. মোল্লা মেহরাব গিলানী: তিনি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আরেফ। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে তাঁকে খাওয়াজুয়ী ও বাইদাবাদীর ছাত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ‘ রওজাত ’ গ্রন্থে তাঁকে শুধু খাওয়াজুয়ীর ছাত্র বলা হয়েছে।
অগা বুযুর্গ তেহরানী তাঁর ‘ নুকাবাউল বাশার ’ গ্রন্থের 1114 পৃষ্ঠায় ‘ মারেফাতুল কিবলা ’ গ্রন্থের লেখক মির্জা আবদুর রাজ্জাক খান বাগায়েরীকে মোল্লা মেহরাবের দৌহিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি 1197 হিজরীতে মারা যান।
আটাশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মোল্লা আলী নূরী মাজেনদারানী ইসফাহানী: তিনি ইসলামী দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। গত চার শতাব্দীতে যে সকল ব্যক্তিত্ব মোল্লা সাদরার দর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রথম জীবনে মাজেনদারান ও কাযভীনে পড়াশোনা করেন ও পরবর্তীতে ইসফাহানে আসেন। সেখানে তিনি অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী ও সাইয়্যেদ আবুল কাসেম মুদাররিস ইসফাহানীর নিকট পড়াশোনা করেন। তিনি পরবর্তী সময়ে ইসফাহানে দর্শনের সর্ববৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।
মোল্লা আলী নূরী শিক্ষাদান ও ছাত্র প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সত্তর বছর সাধনা করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারে তিনি বিরল ভূমিকা রেখেছেন।
মুহাম্মদ হুসাইন খান মারভী তেহরানের মারভী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সম্রাট ফাত্হ আলী শাহকে অনুরোধ করেন এ মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে মোল্লা আলী নূরীকে ইসফাহান হতে তেহরানে দাওয়াত করার। সম্রাট তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি উত্তর দেন ইসফাহানে তাঁর নিকট দু ’ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষারত রয়েছে যাঁদের মধ্যে চার শতাধিক যোগ্য ছাত্র রয়েছে। তাঁদের ত্যাগ করে তেহরান আসলে ইসফাহানের মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবে। সম্রাট পুনরায় পত্র লিখে তাঁর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে তেহরানে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণের আহ্বান জানালে তিনি মোল্লা আবদুল্লাহ্ জানুজীকে প্রেরণ করেন। মোল্লা আলী নূরীর সকল ছাত্রই ইসফাহানের ছিলেন না। তাঁর ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতেন। সত্তর বছরব্যাপী বিভিন্ন ছাত্র তাঁর নিকট হতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মশাল নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।
‘ রওজাত ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন , ‘ আমি শৈশবে তাঁকে দেখেছি। তখন তিনি শুভ্র চুলের বৃদ্ধ ছিলেন। সাইয়্যেদ মসজিদে তিনি সাইয়্যেদ বাকের হুজ্জাতুল ইসলামের সঙ্গে নামাজের উদ্দেশ্যে আসতেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের হুজ্জাতুল ইসলাম তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁরা নামাজের পর আলোচনার জন্য বসতেন। তিনি ও ইসফাহানের শিয়াদের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও নেতা হাজ কালবাসী অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাজ কালবাসী বিভিন্ন সভায় মোল্লা আলী নূরীকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন।
এ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কর্মপ্রচেষ্টাতেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে। তিনি মোল্লা সাদরার ‘ আসফার ’ গ্রন্থের কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। তিনি সূরা ইখলাসের একটি দীর্ঘ তাফসীরও লিখেছেন। তিনি 1246 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. হাজী মোল্লা আহমাদ নারাকী: তিনি মোল্লা মাহ্দী নারাকীর পুত্র। তিনি একজন ফকীহ্ ,মুজতাহিদ ও মুফতী ছিলেন। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পণ্ডিত ছিলেন যা স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি 1244 অথবা 1245 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা তেহরানী তাঁর ‘ আলকিরামুল বারারাহ্ ’ ও ‘ নুকাবাউল বাশার ’ গ্রন্থে মোল্লা হাবিবুল্লাহ্ কাশানীর ‘ লুবাবুল আলকাব ’ গ্রন্থসূত্রে উল্লেখ করেছেন ,কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কাশান বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর বেশ কিছু সংখ্যক দার্শনিকের নাম এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যাঁরা কাশানে শিক্ষা লাভ করেছেন। সম্ভবত নারাকের আলেমদের মাধ্যমে সেখানে দর্শন প্রসার লাভ করেছিল।
3. মির্জা মাহ্দী ইবনে মির্জা হেদায়েতুল্লাহ্ শাহীদ মাশহাদী: তিনি তাঁর সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও আলেম ছিলেন। তিনি উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্রে ওয়াহিদ বেহবাহানীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সাইয়্যেদ মাহ্দী বাহরুল উলুম ও শেখ জাফর কাশেফুল গেতার সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত তিনি ইসফাহানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসফাহানে আগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর নিকট দর্শন শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে মাশহাদে যান এবং সেখানে দর্শন ,উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন যা স্বীয় শ্বশুর শেখ হুসাইন আমেলীর নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্রত্রয় মির্জা হেদায়েতুল্লাহ্ ,মির্জা আবদুল জাওয়াদ ও মির্জা দাউদ দর্শনে গভীর বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষোক্ত দু ’ পুত্র খোরাসানের প্রথম সারির দু ’ গণিতজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বংশধারায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন বিশিষ্ট দার্শনিক ,আরেফ ও মুজতাহিদ মির্জা হাবিব রাজাভী ,চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর বিশিষ্ট দার্শনিক আগা বুযুর্গ হাকিম শাহিদী মাশহাদী প্রমুখ।
মির্জা মাহ্দী ইবনে সিনার ‘ ইশারাত ’ ও কিছু সংখ্যক গণিত বিষয়ক গ্রন্থও পাঠদান করতেন। তিনি সম্রাট নাদির শাহের পৌত্র নাদির মির্জা কর্তৃক শহীদ হন। তাঁর জন্ম 1152 হিজরীতে । তাঁকে 1218 হিজরীতে শহীদ করা হয়।
উনত্রিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মির্জা হাসান নূরী: তিনি মোল্লা আলী নূরীর পুত্র। তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে আকর্ষণীয় পাঠচক্রের আয়োজনে সক্ষম হন। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আগা আলী মুদাররেস জানুযী তেহরানী তাঁর ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন। অধ্যাপক জালালুদ্দীন হুমায়ী তাঁর নির্বাচিত কবিতা সংকলন গ্রন্থে ইসফাহানের তিন শ্রেষ্ঠ কবির আলোচনায় তাঁকে তাঁর পিতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কোন রচনা বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলেও তাঁর ছাত্রদের নিকট হতে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যা হোক তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দর্শনশাস্ত্রে ভূমিকা রেখেছেন।
2. মোল্লা ইসমাঈল ইবনে মোল্লা মুহাম্মদ সামিই ’ দারবেকুশাকী ইসফাহানী: তিনি ‘ ওয়াহিদুল আইন ’ বা এক চক্ষুধারী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মোল্লা আলী নূরীর বিশিষ্ট ছাত্রদের
অন্তর্ভুক্ত এবং হাজী মোল্লা হাদী সাবযেওয়ারীর শিক্ষক। তাঁর দর্শনের ক্লাসসমূহ আকর্ষণীয় ছিল। তিনি মোল্লা সাদরার ‘ আরশিয়া ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মাশায়ি ’ র ও ‘ আসফার ’ গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। এ ছাড়া তিনি লাহিজীব সাওয়ারিক গ্রন্থের টীকাও লিখেছেন। তিনি 1277 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. মোল্লা আবদুল্লাহ্ জানুযী: তিনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে মুহাম্মদ হুসাইন খান মারভীর অনুরোধে হাকিম নূরী ইসফাহান হতে তেহরানে পাঠদানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ইসফাহানের জ্ঞানকেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য ক্রমাগ্রত হ্রাসের পর জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে তেহরানের আবির্ভাব এ সময়েই ঘটে। মোল্লা আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁর স্বনামধন্য পুত্র আগা আলী মুদাররেস যে বিবরণ দিয়েছেন তা হতে জানা যায় ,তিনি তাঁর জীবনের প্রাথমিক পড়াশোনা আজারবাইজানে সম্পন্ন করেন। অতঃপর কারবালায় যান। তিনি সেখানে সাহেবে রিয়াজের নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কোমে বিশিষ্ট মুজতাহিদ মির্জায়ে কুমীর নিকট পড়াশোনা করেন। পরে তিনি কোম হতে ইসফাহানে যান ও হাকিম নূরীর নিকট দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 1237 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. মোল্লা মুহাম্মদ জাফর লাঙ্গরুদী লাহিজী: তিনি মোল্লা আবদুল্লাহ্ জানুজীর সমসাময়িক। তিনি সাইয়্যেদ আবুল কাসেম মুদাররেস ইসফাহানী ,মোল্লা মেহরাব গিলানী এবং বিশেষত মোল্লা আলী নূরীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো মোল্লা সাদরার ‘ মাশায়ের ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থটি সম্প্রতি মোল্লা সাদরার চারশ ’ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে ডক্টর সাইয়্যেদ হুসাইন নাসর ,অধ্যাপক জালালউদ্দীন হুমায়ী ও অধ্যাপক সাইয়্যেদ জালালউদ্দীন অশতিয়ানীর লিখিত ইংরেজি ও ফার্সী ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ‘ মাশায়ের ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়াও কুশচীর ‘ শারহে তাজরীদ ’ ও এ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ ‘ হাশিয়ায়ে খাফারী ’ র টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ‘ শারহে তাজরীদ ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থটি সুলতান মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে 1255 হিজরীতে রচিত হয়।
তাঁর মৃত্যুর সঠিক সময় সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে জনাব হুমায়ী বলেছেন ,তাঁর মৃত্যু 1294 হিজরীর পূর্বেই ঘটেছিল।
আশ্চর্যের বিষয় হলো ,বিশিষ্ট আলেম শেখ আগা বুযুর্গ তেহরানী তাঁর ‘ আল কিরামুল বারারাহ্ ফিল কারনিস সালিছ বা ’ দাল আশারা ’ গ্রন্থের 239 এবং 257 পৃষ্ঠায় একই নামের সমসাময়িক ও গিলানের অধিবাসী হিসেবে তিনজন দার্শনিকের নাম যথাক্রমে শেখ জাফর লাহিজী ,শেখ মুহাম্মদ জাফর লাঙ্গরুদী (যিনি মোল্লা সাদরার আরশিয়ে গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন) ও শেখ মুহাম্মদ জাফর লাহিজী (যিনি মাশায়ির ও শারহে তাজরিদ গ্রন্থের টীকা লিখেছেন) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই নামের ও একই এলাকার সমসাময়িক তিনজন দার্শেিকর অস্তিত্বের বিষয়টি সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। তাই বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে।
5. মোল্লা আগায়ে কাযভীনী: তিনিও মোল্লা আলী নূরীর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন। তিনি ইসফাহান হতে কাযভীনে ফিরে আসার পর বড় একটি দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য সমবেত হন। আলী মুদাররেস জানুজী তাঁর নিজ জীবনীতে লিখেছেন ,এই বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি কিছুদিন কাযভীনে অবস্থান করেছিলেন। মোল্লা আগায়ে কাযভীনী মোল্লা আলী নূরীর অন্যতম ছাত্র মোল্লা ইসমাঈল ইসফাহানীর নিকটও পড়াশোনা করেন। এ কারণে তাঁকে হাজী সাবযেওয়ারীর সমসাময়িক হিসেবে ত্রিশতম স্তরের দার্শনিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তিনি 1282 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
ত্রিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. হাজী মোল্লা হাদী সাবযেওয়ারী: তিনি শেষ চার শতাব্দীর দার্শনিকদের মধ্যে মোল্লা সাদরার পর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 1212 হিজরীতে সাবযেওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। দশ বছর বয়সে তিনি পবিত্র মাশহাদ শহরে যান। তিনি সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন। ইসফাহানের দার্শনিকদের সুনামে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসফাহান গমন করেন। তিনি ইসফাহানের দার্বে কুশাকীতে মোল্লা ইসমাঈলের নিকট সাত বছর পড়াশোনা করেন । তিনি হাকিম নূরীর জীবনের শেষ দু ’ তিন বছর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি মাশহাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনা করেন। সেখান হতে তিনি মক্কায় যান। তিনি মক্কা হতে ফেরার পথে দু ’ তিন বছর কেরমান শহরে বসবাস করতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। অতঃপর সাবযেওয়ার ফিরে আসেন। সে সময় হতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি এ শহর হতে বের হননি। এ শহরেই তিনি অধ্যয়ন ,অধ্যাপনা ,গবেষণা ,রচনা ,সংকলন ,ইবাদাত ,আত্মশুদ্ধি ও ছাত্র প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ,বিভিন্ন অঞ্চল হতে ছাত্র সংগ্রহ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন শহরে প্রেরণের ক্ষেত্রে তিনি হাকিম নূরীর পরেই স্থান লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধি ইরান এবং ইরানের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দর্শন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর নিকট আসতেন। এ বিশিষ্ট দার্শনিকের কারণেই পরিত্যক্ত সাবযেওয়ার শহরটি ইসলামী দর্শন শিক্ষার্থীদের সমবেত হওয়ার স্থান ও দীনী কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।
বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক কান্ট গোবিনু যিনি ইতিহাসের দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ,ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর তিন বছর ইরানে অবস্থানের সময় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেন , ‘ তাঁর (হাজী সাবযেওয়ারী) প্রসিদ্ধি এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে ,বিভিন্ন দেশ ,যেমন ভারত ,তুরস্ক ,হেজায হতে তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা আসতেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাবযেওয়ারের দীনী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন। ’
দার্শনিক সাবযেওয়ারী বাগ্মিতা ও লেখনী শক্তিতে ছিলেন বিরল। আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষা দান করতেন। তিনি দর্শন ও প্রজ্ঞার জ্ঞান ছাড়াও এরফানী জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন সুশৃঙ্খল ,আত্মপরিশুদ্ধ ,আরাধক ,শরীয়তের অনুগত। অর্থাৎ সর্বোপরি তিনি ছিলেন আল্লাহর পথের পথিক। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁর ছাত্ররা তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিরল। তাঁর অন্যতম ছাত্র তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরও তাঁর নাম শ্রবণে অশ্রু বিসর্জন করতেন।
দার্শনিক সাবযেওয়ারী ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন । তিনি তাঁর কবিতায় অনেক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোন কোন কবিতা অদ্ভুত সুন্দর ,উচ্চ মানের ও উত্তেজনাপূর্ণ।
হাজী সাবযেওয়ারী 1289 হিজরীতে এক আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি করে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর এক ছাত্র নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছিলেন :
‘ এক রহস্য পৃথিবী হতে নিল বিদায়
যাঁর আহ্বান পৌঁছেছিল ভূমি হতে আরশে খোদায়
যদি তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন কর
বলব আমি মরেননি তিনি ,লাভ করেছেন জীবন আরো উচ্চতর। ’
হাজী সাবযেওয়ারীর যে সকল ছাত্র সম্পর্কে আমার নিকট তথ্য রয়েছে তাঁরা হলেন :
1. মোল্লা আবদুল করিম খাবুশানী (কুচানী) যিনি ‘ মানজুমে মানতেক ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন।
2.মির্জা হুসাইন সাবযেওয়ারী যিনি মোল্লা মুহাম্মদ হাইদাযী ও মির্জা আলী আকবর ইয়াযদীর শিক্ষক ছিলেন।
3. মির্জা হুসাইন আলাভী সাবযেওয়ারী যিনি জ্ঞানের সব শাখায় তাঁর সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ।
4. ফার্স প্রদেশের বিশিষ্ট দার্শনিক হাকিম আব্বাস দারাবী।
5.শাইখুর রাইস কাযারের শিক্ষক শেখ ইবরাহীম সাবযেওয়ারী।
6. শেখ মুহাম্মদ ইবরাহীম তেহরানী।
7. সাইয়্যেদ আবুল কাসেম মুসুভী জানজানী।
8. সাইয়্যেদ আবদুর রহিম সাবযেওয়ারী।
9. মোল্লা মুহাম্মদ সাব্বাগ।
10. শেখ হাদী বীরজান্দীর শিক্ষক শেখ মুহাম্মদ রেজা বরুগানী।
11. মির্জা আবদুল গফুর দারাবী।
12.হাজ ফাজেল খোরাসানী ও আগা বুযুর্গে শাহেদী মাশহাদীর শিক্ষক মোল্লা গোলাম হুসাইন মাশহাদী।
13. হাজী ফাজেল খোরাসানী ও আগা বোজুর্গ শাহিদী মাশহাদীর শিক্ষক মির্জা মুহাম্মদ সারুকাদী।
14. শেখ আলী ফাজেল তাব্বাতী
15.মির্জা অগা হাকিম দারাবী
16.মির্জা মুহাম্মাদ ইয়াযদী
17.মির্জা আবু তালেব জানজানী
18.মোল্লা ইসমাঈল আরেফ বেজনূরদী
19.শেখ আবদুল হুসাইন শাইখুল ইরাকাইন এবং
20.মির্জা মুহাম্মদ হাকিম এলাহী
হাকিম সাবযেওয়ারীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন বিশিষ্ট আরেফ ,দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ ফকীহ্ মোল্লা হুসাইন কুলি হামেদানী। এই মহান ব্যক্তি এক পবিত্র চরিত্রের মেষ পালকের সন্তান ছিলেন। তিনি শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হামেদান হতে তেহরানে আসেন। হাকিম সাবযেওয়ারীর প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক আকর্ষণে তিনি সাবযেওয়ারে আসেন এবং সেখানে পড়াশোনা শুরু করেন। অতঃপর ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য আতাবাতে আসেন ও শেখ মুর্তাজা আনসারীর ছাত্র হন। এ সময়েই তিনি আগা সাইয়্যেদ ইলী শুসতারীর ছাত্র হন ও তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রবাদ পুরুষে পরিণত হন।
যদি হাকিম সাবযেওয়ারীর মাদ্রাসার ছাত্ররা এ মাদ্রাসায় পড়ার কারণে গৌরব লাভ করে থাকেন তবে বলা যায় ,এ ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে মাদ্রাসা গৌরবান্বিত হয়েছিল।
আখুন্দ মোল্লা হুসাইন কুলি যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তা ছাত্রদের শিক্ষাদান হতে তাদের প্রশিক্ষণ ও মানব গঠনে অধিকতর গুরুত্ব দিত। এ মাদ্রাসায় অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করেছেন।
বিভিন্ন সূত্র হতে যতটুকু জানা যায় সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানী তাঁর নাজাফে অবস্থানকালে দু ’ ব্যক্তি হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন শেখ মুর্তাজা আনসারী এবং অপরজন মোল্লা হুসাইন কুলি হামেদানী। সম্ভবত সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন মোল্লা হুসাইন কুলির নিকট বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কোন সূত্র অনুযায়ী সাইয়্যেদ জামাল মোল্লা হুসাইন কুলির ছাত্র সাইয়্যেদ আহমদ কারবালায়ী ও সাইয়্যেদ সাঈদ হুবুবী যাঁরা তাঁর নিকট এরফানশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করতেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতেন। এ দিকটি এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের (সাইয়্যেদ জামাল) এক আশ্চর্যজনক ও অনুদ্ঘাটিত দিক যা খুব কম ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
2. আগা আলী যানুযী: তিনি আগা আলী হাকিম ও আগা আলী মুদাররেস নামে পরিচিত। তিনি পূর্বোল্লিখিত মোল্লা আবদুল্লাহ্ যানুযীর পুত্র। তিনি সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোর বিরল শিক্ষকদের একজন। আগা আলী যানুযী 1234 হিজরীতে ইসফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা হতে ফিকাহ্শাস্ত্র ও দর্শনের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি দর্শন শিক্ষা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আতাবাতে যান। সেখান থেকে ইসফাহানে ফিরে আসেন ও মির্জা হাসান নূরীর ছাত্র হন। অতঃপর কাযভীনে যান ও মোল্লা আগায়ে কাযভীনীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে ইসফাহানে ফিরে এসে হাসান নূরীর নিকট তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপনের পর তেহরানের সেপাহ্সালার মাদ্রাসায় শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত হন। তিনি 1307 হিজরীতে তেহরানে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আগা মুহাম্মদ রেযা হাকিম কামশেহী: তিনিও বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও আরেফ। তিনি ইসফাহানের কামশেহ শহরের অধিবাসী। তরুণ বয়সে তিনি শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইসফাহানে আসেন। তিনি মির্জা হাসান নূরী এবং মোল্লা মুহাম্মদ জাফর লাঙ্গরুদীর নিকট পড়াশোনা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ইসফাহানের দীনি শিক্ষাকেন্দ্রে দর্শন শিক্ষাদান করেন। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি তেহরানের সাদর মাদ্রাসায় অবস্থান করেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট থেকে লাভবান হতেন। এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সময় ছিল।
তিনি একজন পূর্ণ আরেফ ছিলেন। তিনি একাকিত্বকে পছন্দ করতেন ও সমাজ হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকতেন। যুবক বয়সে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 1288 হিজরীর দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি একজন দরবেশের ন্যায় জীবনযাপন করেন। যখন আগা আলী হাকিম মুদাররেস যানুযী ও মির্জা আবুল হাসান যেলভে দর্শনশাস্ত্রের শিখরে অবস্থান করছিলেন তখনই হাকিম কামশেহী তেহরানে আসেন। তিনি মোল্লা সাদরার দর্শনের অনুসারী হলেও ইবনে সিনার দর্শন গ্রন্থসমূহ পড়াতেন। তিনি ইবনে সিনার দর্শনে পণ্ডিত হিসেবে মির্জা আবুল হাসান যেলভের অবস্থানকে টলিয়ে দেন।
হাকিম কামশেহী কখনই তাঁর গ্রামীণ পোশাক পরিত্যাগ করে আলেমদের পোশাক পরিধান করেননি। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র জাহাঙ্গীর খান কাশকায়ী বর্ণনা করেছেন , ‘ হাকিম কামশেহীর প্রসিদ্ধির কথা শুনে তাঁর নিকট হতে শিক্ষা লাভের পরম আগ্রহ নিয়ে তেহরান গিয়েছিলাম। তেহরান পৌঁছে প্রথম রাতেই তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর পোশাক আলেমদের মত ছিল না । তাঁর পোশাক ছিল তাঁবু ও ক্যানভাসের কাপড় বিক্রেতাদের মতো। আমি তাঁকে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। তিনি তেহরানে বাইরের একটি কফির দোকানে (যেখানে দরবেশদের আড্ডা ছিল) আমাকে পরদিন আসতে বললেন। আমি মোল্লা সাদরার ‘ আসফার ’ গ্রন্থটি সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলাম তিনি এক কোণায় একটি চাটাইয়ের ওপর বসে রয়েছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে ‘ আসফার ’ গ্রন্থটি খুলে বসলাম। তিনি তা হতে পড়ে আমাকে বুঝাতে লাগলেন। তাঁর পাঠ দানের প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে আমি আত্মহারা হলাম। তিনি আমার অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন: হ্যাঁ ,এ শক্তিই পাত্রটিকে ভেঙ্গেছে। ’
তিনি উচ্চ পর্যায়ের কবি ছিলেন। নিজ কবিতাসমূহকে ‘ লাল মদ ’ ছদ্ম নামে প্রকাশ করতেন। তিনি 1306 হিজরীতে তাঁরই মাদ্রাসার স্বীয় কক্ষের এক কোণে একজন নীরব সূফীর ন্যায় নশ্বর পৃথিবী হতে বিদায় নেন। একই দিনে তেহরান শহরের সবচেয়ে বড় মুফতি মোল্লা আলী কুনীও মৃত্যুবরণ করেন। সে দিন এ শহরে শোকের ছায়া নেমেছিল। যদিও তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর বন্ধু মহল ও ছাত্ররা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি যে এমন মৃত্যুই চেয়েছিলেন তা তাঁর একটি কবিতা হতে বোঝা যায় :
‘ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ তো বাদশাদের জন্য ,আমার জন্য নয়
আমি পাগলের জন্য একটি কোণাই যথেষ্ট ,পৃথিবীতে তা কম নয়। ’
হাকিম কামশেহী অনেক ছাত্রকে শিক্ষাদান করেছেন। আগা মির্জা হাশেম এশকাওয়ারী ,আগা মির্জা হাসান কেরমানশাহী ,আগা মির্জা শিহাব নাইরিযী ,জাহাঙ্গীর খান কাশকায়ী ,আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাশী ইসফাহানী ,মির্জা আলী আকবর ইয়াযদী ,শেখ আলী নূরী মুদাররেস ,মির্জা মুহাম্মদ বাকের হাকিম ,শহীদ মুজতাহিদ ইস্তিহবানাতী ,বিশিষ্ট কবি হাকিম সাফায়ী ইসফাহানী ,শেখ আবদুল্লাহ্ রাশতী রিয়াযী ,শেখ হাইদার খান নাহাভান্দী কাযার ,মির্জা আবুল ফযল কালানতার তেহরানী ,মির্জা সাইয়্যেদ হুসাইন রাজাভী কুমী ,শেখ মাহমুদ বুরুজারদী ,মির্জা মাহমুদ কুমী প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন।
4. মির্জা আবুল হাসান যেলভে: তিনি এই স্তরের অন্যতম দর্শনের প্রসিদ্ধ শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। অনেক ছাত্র তাঁর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি 1238 হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও 1314 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইবনে সিনার দর্শনের সমর্থক ছিলেন। তাই মোল্লা সাদরার দর্শনকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তিনি ইসফাহানের অধিবাসী ছিলেন তবে তেহরানে হিজরত করেন। তিনি মির্জা হাসান নূরী ও মির্জা হাসান চিনির ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে যে ,তিনি ইসফাহান হতে সাবযেওয়ারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তেহরানে আসেন। পরে সাবযেওয়ারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তেহরানেই থেকে যান। আবুল হাসান যেলভে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশের শ্রেষ্ঠ তিন দার্শনিকের একজন। অবশ্য অপর দু ’ জন তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাকিম কামশেহীর ছাত্ররা তাঁরও ছাত্র ছিলেন।
একত্রিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. মির্জা হাশেম এশকাওয়ারী রাশতী: তিনি দর্শন ও এরফানের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিক্ষক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা হতে অনেক ছাত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি তাঁর স্তর হতে পরবর্তী স্তরে দর্শন ও এরফানশাস্ত্র স্থানান্তরের মাধ্যম হয়েছিলেন। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের থেকে এরফানশাস্ত্রের তত্ত্ব জ্ঞানে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ফান্নারী রচিত ‘ মিসবাহুল ইনস ’ গ্রন্থটির (যা কৌনাভী রচিত ‘ মিফতাহুল গাইব ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একাধারে কামশেহী ,আগা আলী মুদাররেস ও মির্জা যেলভের ছাত্র ছিলেন। তিনি 1332 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মির্জা হাসান কেরমানশাহী: তিনি হাশেম এশকাওয়ারীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। পূর্বোক্ত তিন শিক্ষক তাঁরও শিক্ষক ছিলেন। কেরমানশাহীর নিকট অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রকে তাঁর পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি 1336 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. মির্জা শিহাবউদ্দীন নাইরিযী শিরাজী: তিনি হাকিম কামশেহী ও মির্জা যেলভের ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ ও উসূলশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। এরফানশাস্ত্রের মুহিউদ্দীনী ধারার ওপরও তাঁর দক্ষতা ছিল। হাকিম নাইরিযী তেহরানের সাদর মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষক হাকিম কামশেহীর স্থলাভিষিক্ত হন। সেখানে তিনি পাঠ দান ,গবেষণা ও ছাত্র প্রশিক্ষণের কাজে ব্রত হন। তিনি
অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা রচনা করেন। শেখ আগা বুযুর্গ তেহরানী তাঁর জীবনী বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন ,উপরোক্ত পুস্তিকটি তাঁর নিকট রয়েছে।
4. মির্জা আব্বাস শিরাজী দারাবী: তিনি হাকীম আব্বাস নামে পরিচিত ও ফার্স প্রদেশের দর্শনের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের একজন। তিনি হাকিম সাবযেওয়ারীর ছাত্র ছিলেন যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। শেখ আগা বুযুর্গ তেহরানী বলেছেন ,তিনি একাধারে দর্শন ও ফিকাহ্শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মোল্লা সাদরার ‘ আসফার ’ গ্রন্থটি স্বহস্তে কপি করে তাতে টীকা সংযোজন করেছেন। তিনি দোয়া-ই কুমাইল ও মীর ফানদারাসতীর কাসিদার ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি চিরুনী নির্মাতা নামে প্রসিদ্ধ শেখ আহমাদ শিরাজী ও মির্জা ইবরাহীম নাইরিযীর শিক্ষক ছিলেন। ফুরআত উদ্দৌলা শিরাজী তাঁর ‘ আসারুল আযাম ’ গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু 1300 হিজরীতে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবর শিরাজের হাফিযিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে।
5. জাহাঙ্গীর খান কাশকায়ী: প্রায় মধ্যবয়সে তাঁর মধ্যে জ্ঞানের নেশা উজ্জীবিত হয় ও তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হন। পরবর্তীতে ইসফাহানের প্রতিষ্ঠিত দর্শন শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন। জাহাঙ্গীর খান জ্ঞান ও দর্শনে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা ছাড়াও ধৈর্য ,স্থিরতা ,নৈতিক শৃঙ্খলা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর পূর্বের সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও পরিচিতদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। জাহাঙ্গীর খান আগা মুহাম্মদ রেযা কামশেহীর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত তিনি প্রথম দিকে মির্জা আবদুল জাওয়াদ খোরাসানী ও মোল্লা ইসমাঈল ইসফাহানী দারবে কুশাকীরও ছাত্র ছিলেন। জাহাঙ্গীর খান 1243 হিজরীতে ইসফাহানের দেহাকানে জন্মগ্রহণ এবং 1328 হিজরীতে ইসফাহানে মৃত্যুবরণ করেন।
6. আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাশী: তিনি জাহাঙ্গীর খানের সমসাময়িক ও আগা মুহাম্মদ রেযা কামশেহীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইসফাহানের সাদর মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করতেন। জাহাঙ্গীর খানের ন্যায় তিনিও শেষ জীবন পর্যন্ত কুমার ছিলেন। তিনি সুফী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অনেক বড় বড় আলেম ,যেমন প্রসিদ্ধ মারজা হাজী আগা হুসাইন বুরুজারদী ,হাজী আগা রহীম আরবাব ও অন্যান্য অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি 1332 হিজরীতে ইসফাহানে মৃত্যুবরণ করেন। ইসফাহানের তাখতে ফোলাদে জাহাঙ্গীর খানের সমাধির নিকট তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।
7. মির্জা মুহাম্মদ বাকের এসতেহবানাতী: তিনিও আগা আলী হাকিম কামশেহী ও মির্জা যেলভের ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আতাবাতে যান। সেখানে অনেক বড় বড় আলেম ,যেমন তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ গবেষক শেখ মুহাম্মদ হুসাইন ইসফাহানী দারভী ও শেখ গোলাম রেযা ইয়াযদী তাঁর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইরানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে (1326 হিজরী) এসতেহবানাতে শহীদ হন।
8. মির্জা আলী আকবর হুকমী ইয়াযদী কুমী: তিনি পূর্বোল্লিখিত তিনি শিক্ষক ছাড়াও মির্জা হুসাইন সাবযেওয়ারীর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট তিনি এরফান ও যোগ সাধনা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কোমে বসবাস শুরু করেন। যখন বিশিষ্ট মুজতাহিদ শেখ আবদুল করিম হায়েরী কোমে দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তখন অনেক বড় বড় আলেম ,যেমন বিশিষ্ট মারজা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাকী খুনসারী ,সমসাময়িক মারজা সাইয়্যেদ আহমদ খুনসারী এবং আমার শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ শুরু করেন। মির্জা আলী আকবর 1345 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
9. শেখ আবদুন নবী নূরী: তিনি দর্শন ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রে বড় মির্জা শিরাজীর ছাত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে আগা আলী মুদাররেসের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত তিনি কামশেহী ও মির্জা যেলভেরও ছাত্র ছিলেন। তিনি 1344 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন । তাঁর কবর রেই শহরের শাহ আবদুল আযীমের মাযারের নিকট। শেখ আবদুন নবী বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীতেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশিষ্ট ফকীহ্ ও দার্শনিক শেখ মুহাম্মদ তাকী আমুলী (মৃত্যু 1391 হিজরী) 14 বছর তাঁর ছাত্র ছিলেন।
10. মির্জা হুসাইন আলাভী সাবযেওয়ারী: তিনি হাজী সাবযেওয়ারীর নিকট দর্শনশাস্ত্র এবং মির্জা শিরাজীর নিকট উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও মুখস্থ করার ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ইজতিহাদ করার ক্ষমতার বিষয়ে মির্জা শিরাজী এতটা প্রশংসা করেছেন যে ,অন্য কারো বিষয়ে তা শোনা যায়নি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি সারাজীবন সাবযেওয়ারে অবস্থানের কারণে তাঁর নিকট হতে দীনী ছাত্ররা তেমন লাভবান হতে পারেনি। আলাভী সাবযেওয়ারী 1268 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 1352 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
11. শেখ গোলাম হুসাইন শাইখুল ইসলাম খোরাসানী: তিনিও হাজী সাবযেওয়ারীর ছাত্র। তিনি ছয় বছর তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘদিন পবিত্র মাশহাদ শহরে দর্শনশাস্ত্রের আলো বিতরণ করেছিলেন। শেখ গোলাম হুসাইনের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে শেখ আব্বাস আলী খোরাসানীর নাম উল্লেখযোগ্য যিনি হাজ ফাজেল নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 1246 হিজরীতে জন্ম এবং 1319 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
12. মির্জা মুহাম্মদ সুরুকাদী মাশহাদী: তিনি হাজী সাবযেওয়ারীর অন্যতম ছাত্র। তিনি মাশহাদের দর্শনশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের একজন। হাজী ফাজেল খোরাসানীও তাঁর ছাত্র ছিলেন।
13. মোল্লা মুহাম্মদ হায়দাজী জানজানী: তিনি জানজান ও কাযভীনে প্রাথমিক পড়াশোনার পর তেহরানে আসেন। তিনি সেখানে আগা মির্জা হুসাইন সাবযেওয়ারীর নিকট এরফান এবং মির্জা যেলভের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর অধ্যয়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আতাবাতে যান। সেখানেও ফিকাহ্ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পুনরায় তেহরানে ফিরে এসে অধ্যাপনায় রত হন। তিনি হাকিম সাবযাওয়ারীর ‘ শারহে মানজুমা ’ গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ লিখেন যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে পুনঃপুন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকের মতই আত্মপরিশুদ্ধির পথে যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের অনুকরণে শেষ জীবন পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তিনি 1339 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় বেশ কিছু সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর একটি আকর্ষণীয় ও উপদেশমূলক ওসিয়তনামা রয়েছে যা তাঁর কবিতাগ্রন্থের শেষে সংযোজিত করে মুদ্রিত হয়েছে।
বত্রিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
1. শেখ আব্বাস আলী ফাজেল খোরাসানী: তিনি মধ্যবর্তী একজন শিক্ষকের সূত্রে দর্শনশাস্ত্রে হাজী সাবযেওয়ারীর ছাত্র। ফিকাহ্শাস্ত্রে তিনি মির্জা শিরাজীর ছাত্র। তিনি গত শতাব্দীর বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারীদের অন্যতম নমুনা। তিন ব্যক্তি গত শতাব্দীর বহু বিষয়ক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবাদপুরুষ ছিলেন। তাঁরা হলেন মাশহাদের হাজী ফাজেল খোরাসানী ,তেহরানের হাজী শেখ আবদুন নবী নূরী এবং সাবযেওয়ারের হাজী মির্জা হুসাইন আলাভী। হাজী মির্জা হুসাইন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাজী ফাজেল তাঁর সময়ে মাশহাদে দর্শনের স্বীকৃত গ্রন্থসমূহের শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 1344 হিজরীতে মাশহাদে মৃত্যুবরণ করেন।
2. মির্জা আসকারী শাহিদী মাশহাদী: তিনি ‘ আগা বুযুর্গ হাকিম ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মির্জা মাহ্দী শাহিদের বংশধর এবং মোল্লা আলী নূরীর সমপর্যায়ের। মির্জা মাহ্দী শাহিদীর মাশহাদের বাসস্থানটি দীর্ঘ দেড়শ ’ বছর জ্ঞান ,প্রজ্ঞা ও ছাত্র প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আগা বুযুর্গে হাকিম মির্জা জাবিহুল্লাহর পুত্র ছিলেন। মির্জা জাবিহুল্লাহ্ মির্জা হেদায়েতউল্লাহর সন্তান এবং তিনি মির্জা মাহ্দী শাহিদের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন। মির্জা মাহ্দী শাহিদ আগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী এবং শেখ হুসাইন আমেলীর ছাত্র ছিলেন।
আগা বুযুর্গ হাকিমের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে আমার তেমন জানা নেই। সম্ভবত তিনি মাশহাদে স্বীয় পিতা ,মোল্লা সুরুকাদী এবং গোলাম হুসাইন শাইখুল ইসলামের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মাশহাদ হতে তেহরানে আসেন। তিনি মির্জা যেলভের নিকট কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র চর্চা করেন। তিনি হাকিম এশকাওয়ারী এবং হাকিম কেরমান শাহীর নিকটও শিক্ষা লাভ করেন।
আমি যখন আরবী ভাষার প্রাথমিক পড়াশোনার জন্য 1352 হতে 1354 হিজরী পর্যন্ত মাশহাদে অবস্থান করছিলাম তখন তাঁকে একজন সাধারণ ও অতিশয় বৃদ্ধরূপে দেখেছি। তাঁর পুত্র মির্জা মাহ্দী সে সময় মাশহাদের জমজমাট দীনী মাদ্রাসায় উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রজ্বলিত ছিলেন। তিনি ‘ শারহে মানজুমা ’ , ‘ আসফার ’ এবং ‘ কেফায়া ’ পড়াতেন। তাঁর বয়স তখন ত্রিশের অধিক ছিল। এ বয়সেই তিনি 1354 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে মাশহাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। পরবর্তী বছরই তাঁর পিতা আগা বুযুর্গ হাকিম মৃত্যুবরণ করেন। এ দু ’ ব্যক্তির মৃত্যুর মাধ্যমে এ বংশের আলেম ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে।
আগা বুযুর্গ হাকিম স্পষ্টভাষী ,স্বাধীনচেতা ও মুক্ত মনের অধিকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যদিও তিনি খুবই দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন করতেন তথাপি কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতেন না। একবার তাঁর এক আলেম বন্ধু তাঁর দারিদ্র্যের অবস্থার কথা জানতে পেরে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে মোটা অংকের অনুদান সংগ্রহ করেন এবং তা পত্রসহ তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি পত্র পাঠে বিষয়টি অবহিত হয়ে খামের বিপরীত দিকে লিখেন , ‘ আমি দরিদ্র অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকার সম্মানকে হারাতে চাই না। ’ অতঃপর প্রেরিত অর্থসহ খামটি ফেরত পাঠান।
3. আগা সাইয়্যেদ হুসাইন বাদকুবেয়ী: আগা বাদকুবেয়ী 1293 হিজরীতে বাদকুবেয়ীর একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর তেহরানে আসেন। এখানে তিনি মির্জা যেলভের নিকট এরফান এবং হাকিম এশকাওয়ারী ও হাকিম কেরমান শাহীর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি নাজাফে যান এবং আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাযেম খোরাসানী ও শেখ হাসান মামাকানীর নিকট উসূলে ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল্লামা তেহরানী তাঁর ‘ নুকবাউল বাশার ’ গ্রন্থে বলেছেন ,আগা বাদকুবেয়ী নাজাফে দর্শন ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অনেক বড় বড় আলেম তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। আমাদের শিক্ষক আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী ইবনে সিনার ‘ শিফা ’ গ্রন্থের ‘ তাবইয়াত ও ইলাহিয়াত ’ অধ্যায় পুরোটাই তাঁর নিকট পড়েছিলেন। আল্লামা তেহরানীর বর্ণনামতে আগা বাদকুবেই এবং শেখ মুহাম্মদ হুসাইন গারভী সে সময় নাজাফে দর্শনশাস্ত্রের দু ’ দিকপাল ছিলেন। এ মহান আলেম 1358 হিজরীতে নাজাফে মৃত্যুবরণ করেন।
4. অগা মির্জা মুহাম্মদ আলী শাহ আবাদী তেহরানী: তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসফাহানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মির্জা যেলভে এবং মির্জা এশকাওয়ারীর নিকট দর্শন ও এরফানশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তেহরানে মির্জা হাসান আশতিয়ানীর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে নাজাফ ও সামেরায় আখুন্দ খোরাসানী ও মির্জা মুহাম্মদ তাকী শিরাজীর নিকট উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্রের উচ্চতর পড়াশোনা করেন। তিনি তেহরানে মারজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শেখ আবদুল করিম হায়েরীর কোমে অবস্থানকালে তিনি কোমে চলে আসেন এবং শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি এরফানশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী এই মহান ব্যক্তির নিকট পড়াশোনা করেছেন এবং এরফানশাস্ত্রে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি 1369 হিজরীতে তেহরানে মৃত্যুবরণ করেন।
5. আগা সাইয়্যেদ আলী মুজতাহিদ কাজেরুনী শিরাজী: তিনি সাইয়্যেদ আব্বাস মুজতাহিদ কাজেরুনীর পুত্র। তিনি 1278 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 1291 হিজরীতে তিনি কাজেরুন হতে শিরাজে আসেন। 1304 হিজরী পর্যন্ত শিরাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক জ্ঞান অধ্যয়নে রত থাকেন। তিনি হাকিম আব্বাস দারাবীর ছাত্র শেখ আহমাদ শিরাজী নাজাফী এবং শেখ মুহাম্মদ হুসাইন শানেসাযের নিকট যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। সম্ভবত তিনি হাকিম আব্বাস দারাবীর (মৃত্যু 1300 হিজরী) নিকটও কিছুদিন পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি 1304 হতে 1315 হিজরী পর্যন্ত নাজাফে অবস্থান করেন এবং আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাযেম খোরাসানীর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র পড়াশোনা করেন। তিনি 1319 হিজরী হতে শেষ জীবন পর্যন্ত (1343 হিজরী) শিরাজে দর্শন ও এরফানশাস্ত্র শিক্ষাদানে রত থাকেন। শিরাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক শাস্ত্রের ছাত্রদের অধিকাংশই তাঁর ছাত্র। অগা সাইয়্যেদ আলী মুজতাহিদ পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল আলেমদের মধ্যকার একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছাত্র ও শিরাজের সাধারণ মানুষদের নিকট থেকে তাঁর পবিত্র আত্মার পরিচয় বহনকারী অনেক ঘটনা শোনা যায়।
6. আগা শেখ মুহাম্মদ খোরাসানী গুণাবাদী ইসফাহানী: তিনি ‘ আগা শেখ মুহাম্মদ হাকিম ’ ও ‘ আগা শেখ মুহাম্মদ খোরাসানী ’ এ উভয় নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাশী ও জাহাঙ্গীর খান কাশকায়ীর ছাত্র ছিলেন। তাঁদের দু ’ জনের মৃত্যুর পর তিনি ইসফাহানে দর্শনশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক হন। তিনি ইসফাহানের সাদর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। হাজী মির্জা আলী আগা শিরাজী এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জালালউদ্দীন হুমায়ী তাঁর ছাত্র ছিলেন। হাকিম খোরাসানী আত্মিক পরিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষক জাহাঙ্গীর খান ও আখুন্দ কাশীর ন্যায় শেষ জীবন পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তিনি 1355 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর মৃত্যুর পর হাজী আগা সাদর কুপায়ী এবং শেখ মাহমুদ মুফিদ ইসফাহানের এ জ্ঞানকেন্দ্রের আলোকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। এ দু ’ ব্যক্তির মৃত্যুর পর ইসফাহানের জ্ঞান কেন্দ্রটি চারশ ’ বছর আলো বিতরণের পর প্রায় নিভে গিয়েছিল।
7. হাজী শেখ মুহাম্মদ হুসাইন গারভী ইসফাহানী: তিনি জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক) ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি 1296 হিজরীতে নাজাফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাযেমাইনের একজন ধার্মিক ব্যবসায়ী ছিলেন।
মুহাম্মদ হুসাইন গারভী বিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাযেমাইনে ছিলেন এবং সেখানে প্রাথমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি নাজাফে চলে আসেন। সেখানে তিনি আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাযেম খোরাসানীর শেষ জীবন পর্যন্ত (1329 হিজরী) তাঁর ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে মির্জা মুহাম্মদ বাকের হাকিম এসতেহবানাতীর ছাত্র ছিলেন। উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্রে মুহাম্মদ হুসাইন গারভী ইসফাহানীর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো ফিকাহ্ ও উসূলশাস্ত্রের ছাত্রদের জন্য আজও চিন্তার খোরাক যুগিয়ে আসছে ও জীবন্ত রয়েছে। তিনি ‘ তোহফাতুল হাকিম ’ নামে দর্শনের একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পরকাল সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী দীর্ঘ দশ বছর (1344-1354 হিজরী) এ মহান ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন এবং এ নিয়ে গর্ববোধ করতেন। তিনি 1361 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।
8. আগা শেখ মুহাম্মদ তাকী আমোলী: তিনি 1304 হিজরীতে তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা বিশিষ্ট দার্শনিক আগা শেখ মুহাম্মদ আমোলীর (1263-1336 হিজরী) নিকট দর্শন ও ফিকাহ্শাস্ত্রের প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। অতঃপর মির্জা কেরমান শাহীর মৃত্যুর পর তিনি শেখ আবদুন নবী মুজতাহিদ নূরীর নিকট প্রায় চৌদ্দ বছর পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে নাজাফে হিজরত করেন। সেখানে হাজী মির্জা হুসাইন নায়িনী ,সাইয়্যেদ আবুল হাসান ইসফাহানী এবং অগা জিয়াউদ্দীন ইরাকীর নিকট উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মহান আরেফ হাজী মির্জা আলী আগা কাজী ফায়েযের নিকট আখলাক বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি তেহরানে অবস্থানকালে ফিকাহ্ ও দর্শন উভয় শাস্ত্রই শিক্ষাদান করতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো হাকিম সাবযেওয়ারীর ‘ শারহে মানজুমা ’ গ্রন্থের টীকা গ্রন্থ। ফিকাহ্শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘ শারহে উরওয়াতুল উসকা ’ যেটি একটি দলিলভিত্তিক বই। তিনি 1391 হিজরীতে তেহরানে মৃত্যুবরণ করেন।
9. আগা মির্জা মাহ্দী আশতিয়ানী: তিনি বর্তমান শতাব্দীর (চতুর্দশ হিজরী শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অন্যতম। তাঁর পিতা মির্জা জাফর যিনি ‘ মির্জা কুচাক ’ নামে প্রসিদ্ধ আগা মুহাম্মদ রেজা হাকিম কামশেয়ীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর মাতা তেহরানের প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ মির্জা হাসান অশতিয়ানীর কন্যা।
মির্জা মাহ্দী মির্জা হাসান কেরমান শাহী এবং মির্জা হাশেম এশকাওয়ারীর ছাত্র। তিনি দীর্ঘদিন তেহরানে দর্শন ও এরফানশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। তিনি 1365-1366 হিজরীর দিকে কোমের ছাত্র ও শিক্ষকদের আহ্বানে কোমে আসেন এবং সেখানে শিক্ষকতায় রত হন। আমি সে সময় কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম।
তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের টীকাগ্রন্থ লিখেছেন যা ‘ শারহে মানজুমা ’ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত। তিনি ‘ কায়েদাতুল ওয়াহেদ ’ (একত্বের নিয়ম) এবং ‘ ওয়াহ্দাতে উজুদ ’ (অস্তিত্বের একতা) সম্পর্কিত ‘ আসাসুত তাওহীদ ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই। তিনি 1372 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
10. আগা মির্জা আহমাদ আশতিয়ানী: তিনি হাজী মির্জা হাসান মুজতাহিদ আশতিয়ানীর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ ,দর্শনশাস্ত্রসহ বিভিন্ন জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন। তাকওয়া-পরহেজগারীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। তিনি চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে তেহরানে উসূল ,ফিকাহ্ ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দান করেছেন। তিনি হাকিম কেরমান শাহী ও হাকিম এশকাওয়ারীর ছাত্র ছিলেন।
তিনি 1345 হিজরীতে ফিকাহ্শাস্ত্রের শিক্ষা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নাজাফে যান। সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতাও করেন। অনেক স্বনামধন্য মুজতাহিদ ও শিক্ষকও তাঁর নিকট দর্শনের ‘ আসফার ’ গ্রন্থটি পড়তেন। আমার শিক্ষক আল্লামা তাবাতাবায়ী সে সময় ‘ আসফার ’ গ্রন্থটির কিছু অংশ তাঁর নিকট পড়েছেন। এ মহান ব্যক্তি প্রায় শত বছর বয়সে 1395 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
11. আগা মির্জা তাহের তানকাবানী: তিনিও বর্তমান শতাব্দীর দর্শনের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকদের একজন। দর্শনের বিভিন্ন মতের ওপর তাঁর আশ্চর্যজনক দখল ছিল। তিনি 1280 হিজরীতে মাজেনদারানের কালারদাসতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা সম্পন্নের পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে তেহরানে আসেন। তিনি মির্জা যেলভে ,হাকিম কামশেয়ী এবং হাকিম মুদাররেসের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন ,তবে হাকিম কেরমান শাহী এবং হাকিম নাইরেযীর নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন কি না তা আমার জানা নেই। পূর্বোক্ত তিন দার্শনিকের (তাঁর শিক্ষকত্রয়) পর তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে তেহরানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে অভিহিত হন। তিনি 1360 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
12. আগা সাইয়্যেদ আবুল হাসান রাফিয়ী কাযভীনী: তিনি বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের একজন। তিনি বর্ণনামূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় জ্ঞানেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাকিম কেরমান শাহী ও হাকিম এশকাওয়ারীর নিকট দর্শন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কোমের দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি শেখ আবদুল করিম হায়েরীর আহ্বানে কোমে আসেন। কিছুদিন আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর নিকট শিক্ষা লাভের পর তিনি হাকিম সাবযেওয়ারীর ‘ শারহে মানজুমা ’ ও মোল্লা সাদরার ‘ আসফার ’ গ্রন্থ শিক্ষাদান শুরু করেন। আমার মহান শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী ‘ শারহে মানজুমা ’ সহ ‘ আসফার ’ গ্রন্থের কিছু অংশ তাঁর নিকট পড়েছেন এবং তাঁর পাঠ দানের পদ্ধতি ও বর্ণনার প্রশংসা করতেন। সাইয়্যেদ রাফিয়ী কাযভীনী আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর জীবদ্দশাতেই কাযভীনে ফিরে যান । সেখানে দর্শনের ছাত্ররা তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসতেন। পরবর্তীতে তিনি মারজা হন এবং তেহরানে বসবাস শুরু করেন । তিনি 1394 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
13. আগা শেখ মুহাম্মদ হুসাইন ফাজেল তুনী: তিনি বর্তমান শতাব্দীর দর্শনের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের অন্যতম। দর্শনের ‘ ইলাহিয়াত ’ অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন যার ভূমিকাতে নিজেকে জাহাঙ্গীর খান ও হাকিম এশকাওয়ারীর ছাত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে সাহিত্য ,দর্শন ও ফিকাহ্শাস্ত্র শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি কায়সারী রচিত ‘ শারহে ফুসুস ’ গ্রন্থের ভূমিকার ওপর টীকা লিখেছেন। তিনি 1309 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
14. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কাযেম আসসার: তিনি বর্তমান শতাব্দীর দর্শনের শিক্ষকদের অন্যতম। তিনি 1305 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 18 বছর বয়সে তিনি ইসফাহানে আসেন এবং সেখানে তিন বছর জাহাঙ্গীর খান ও আখুন্দ মোল্লা মুহাম্মদ কাশীর নিকট দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ছয় বছর তেহরানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হাকিম এশকাওয়ারী ,হাকিম কেরমান শাহী এবং হাকিম নাইরিযীর নিকট দর্শন শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি আতাবাতে যান। দশ বছর সেখানে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষকদের নিকট উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। 1340 হিজরীতে 35 বছর বয়সে তিনি তেহরানে ফিরে আসেন এবং উসূল ,ফিকাহ্ ও দর্শন শিক্ষাদান শুরু করেন। 1353 হিজরীতে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাহিত্য ,দর্শন ও ফিকাহ্ বিষয়ক বিভাগে শিক্ষাকতা শুরু করেন। 1365 হিজরীতে তেহরানের সেপাহ্সালার মাদ্রাসাটি দীনী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করলে তিনি সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত এখানেই এ পেশায় রত থাকেন।
সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কাযেম আসসার একজন খোলামনের মানুষ ছিলেন। সবকিছুই তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করতেন। তিনি ওয়াহ্দাতে উজুদ ,বাদা (ভাগ্যের পরিবর্তন) ,হাদীসশাস্ত্র এবং তাফসীর সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 1394 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
তেত্রিশতম স্তরের দার্শনিকগণ
এ স্তরের দার্শনিকগণ আমার শিক্ষক পর্যায়ের। বিশেষ কিছু কারণে এ সম্পর্কিত বর্ণনা হতে আপাতত বিরত থাকছি। সুবিধা অনুযায়ী অন্য সময় ও স্থানে ইনশাআল্লাহ্ আলোচনা করব।
দার্শনিকদের এরূপ স্তরবিন্যাস ইতোপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। প্রথমবারের মত আমি এটি করায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। প্রথম ত্রুটি হলো এটি সামগ্রিক হয়নি। অনেকেই হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়েছেন আবার অনেককে আমি নিজেই বাদ দিয়েছি। কারণ এ সকল স্তরের সকল দার্শনিকের নামের তালিকা ও বিবরণ দান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া এ কাজটি সহজও নয়। আমরা শুধু সেই সকল দার্শনিক যাঁরা শিক্ষাদান ,ছাত্র প্রশিক্ষণ কিংবা গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্রকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের নিয়েই এখানে আলোচনা করেছি । কারণ তাঁরা ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানের এ বিশেষ ধারাটির টিকিয়ে রাখা ও অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। সবশেষে কয়েকটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি :
1. এ স্তর বিন্যাসটি অন্যান্য স্তর বিন্যাসের মতই পূর্ণ ও যথার্থ নয়। যদিও এই স্তর বিন্যাসটি ছাত্র-শিক্ষকের সময়গত অবস্থান অনুযায়ী করা হয়েছে তদুপরি আমরা জানি যে সকল ছাত্র একই শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন তাঁরা সকলেই এক স্তরের (সময় অনুযায়ী) নন ;বিশেষভাবে যখন ঐ শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষাদান করেন। সাধারণত তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী ও শিক্ষা লাভের সময় অনুযায়ী কেউ অগ্রগামী কেউ পশ্চাদ্গামী।
উদাহরণস্বরূপ হাজী সাবযেওয়ারীকে আমরা মির্জা যেলভে এবং হাকিম কামশেয়ীর সমস্তরে উল্লেখ করেছি। যদিও হাজী সাবযেওয়ারী তাঁদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং মির্জা যেলভে ছিলেন তাঁদের কনিষ্ঠ (এমনকি আমরা উল্লেখ করেছি মির্জা যেলভে হাজী সাবযেওয়ারীর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য সাবযেওয়ার যেতে চেয়েছিলেন ,কিন্তু তেহরানেই থেকে যান)। কারণ যেমনভাবে মির্জা যেলভে ও হাকিম কামশেয়ী মোল্লা আলী নূরীর ছাত্রের ছাত্র ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে হাজী সাবযেওয়ারী মোল্লা ইসফাহানীর ছাত্র হিসেবে জনাব নূরীর ছাত্রের ছাত্র।
2. তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে ইসলামী দর্শনের ইতিহাস শুরু হয়। তখন থেকে চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত অনুবাদের যুগ বলে পরিচিত। এই সময়কালের অধিকাংশ দার্শনিকই অনুবাদক ছিলেন এবং অধিকাংশ অনুবাদকও দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য কোন কোন অনুবাদক যেমন দার্শনিক ছিলেন না তেমনি অনেক দার্শনিক ও অনুবাদক ছিলেন না। তবে দর্শনের সংকলন ও গবেষণার যুগ অনুবাদের যুগ হতে পৃথক নয় যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন ,ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে এক বা দু ’ শতাব্দীতে শুধু অনুবাদ হয়েছে এবং সে সময় কোন প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন না। পরবর্তীতে প্রকৃত অর্থে দার্শনিকের আগমন হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয় ,বরং প্রথম যুগেই অনুবাদ শুরুর সাথে সাথে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দীর ন্যায় বিরল প্রতিভার দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তিনি অনেক দার্শনিক তৈরি করেছেন। আল কিন্দী হুনায়েন ইবনে ইসহাক ইবাদী এবং আবদুল মাসিহ হেমসির ন্যায় অনুবাদকদের সমসাময়িক এবং সাবেত ইবনে কোররাহ্ ও অন্যান্য দর্শন গ্রন্থ অনুবাদকদের পূর্ববর্তী সময়ের।
3. দর্শনের অনুবাদকদের অধিকাংশই ছিলেন ইহুদী ,খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী। অনুবাদকদের মধ্যে মুসলমান খুবই কম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন যারথুষ্ট্র অনুবাদকও ছিলেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফাকে একমাত্র যারথুষ্ট্র অনুবাদক হিসেবে অনেকে বলেছেন যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি যারথুষ্ট্র ছিলেন না ;বরং মনুয়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুসলমান হন। কিন্তু এই পর্যায়ের দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা স্বতন্ত্র মতের অধিকারী ছিলেন তাঁরা সকলেই মুসলমান। এই স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে একজন অমুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়টি ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গবেষণার দাবি রাখে।
4. অনুবাদের যুগের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ অনুবাদের যুগ হতে ষষ্ঠ বা সপ্তম হিজরী পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিক দর্শনের পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করতেন। তাই তাঁরা একদিকে যেমন দার্শনিক ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন চিকিৎসাবিদ। যেমন ইবনে সিনা একই সাথে দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ ছিলেন। এ সকল দার্শনিকদের কেউ কেউ চিকিৎসক হিসেবে অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন।
দার্শনিক-চিকিৎসাবিদদের এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে মুসলমান ,ইহুদী ও খ্রিষ্টান সকলেই ছিলেন। সাবেয়ীনদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ যুগে উচ্চমানের ইহুদী ও খ্রিষ্টান বেশ কিছু চিকিৎসকের কথা আমরা জানি যাঁরা পাশাপাশি দার্শনিকও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ উচ্চমানের দার্শনিক ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ আবুল ফারায ইবনুত ত্বিব ইবনে সিনার সমসাময়িক ছিলেন এবং একজন বড় চিকিৎসক হিসেবে ইবনে সিনা তাঁর প্রশংসা করেছেন ,কিন্তু তিনি দর্শনের চর্চা করলেও ইবনে সিনাসহ অন্য কেউই তাঁকে দার্শনিক বলে মনে করতেন না। তবে এ ক্ষেত্রে আবুল বারাকাত বাগদাদী এবং এমনকি আবুল খায়ের হাসান ইবনে সাওয়ারকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। কারণ আবুল বারাকাত ইহুদী হিসেবে স্বকীয় চিন্তার দার্শনিক ছিলেন। অনুরূপ খ্রিষ্টান হিসেবে আবুল খায়ের। তবে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এ দু ’ ব্যক্তিই পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। অনুবাদের যুগে আমরা যেমন লক্ষ্য করেছিলাম কেবল মুসলমান দার্শনিকগণই স্বকীয় দর্শন চিন্তার অধিকারী ছিলেন ,তেমনি দার্শনিক-চিকিৎসকের যুগেও আমরা লক্ষ্য করি যে ,এ যুগে অমুসলমানদের মধ্যে উচ্চমানের চিকিৎসক থাকলেও তাদের মধ্যে স্বকীয় দর্শন চিন্তার তেমন কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ বিষয়টি থেকে বুঝা যায় ,অন্যান্য ধর্ম হতে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের প্রাণ দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে অধিকতর সঙ্গতিশীল।
সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো ইসলামী যুগের দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বারোশ ’ বছরের ইতিহাসে কোন যারথুষ্ট্র দার্শনিক ও চিকিৎসকের সন্ধান আমরা পাই না (সম্ভবত গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই)। স্বভাবতই এ যুগে যেমনিভাবে ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ জ্ঞান ,সংস্কৃতি ও দর্শনের আন্দোলনে মুসলমানদের পাশাপাশি যে ভূমিকা রেখেছেন যারথুষ্ট্রগণও তা রাখতে পারতেন ,কিন্তু তাঁরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। ইসলামপূর্ব যুগেও বিশ্ব সংস্কৃতিতে তাঁদের কোন ভূমিকা ছিল না। ইসলামপূর্ব যুগে ইরানের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মশাল খ্রিষ্টান ,ইহুদী এবং সাবেয়ীরাই বহন করত এবং জান্দী শাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়টি তারাই পরিচালনা করত।
ইসলামী যুগে একমাত্র বাহমানইয়ার ইবনে মার্জবান (আজারবাইজানের অধিবাসী) যারথুষ্ট্র ছিলেন যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হন। চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র আলী ইবনে আব্বাস যিনি ইবনুল মাজুসী নামে প্রসিদ্ধ তিনি যারথুষ্ট্র ছিলেন বলে মনে করা হয় । কিন্তু এডওয়ার্ড ব্রাউনসহ অনেকেই তাঁকে মুসলিম চিকিৎসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি তাঁর নাম হতেও বুঝা যায় তিনি মুসলমান ছিলেন এবং হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষগণ যারথুষ্ট্র ছিলেন।
প্রকৃত কথা হলো যারথুষ্ট্র ধর্মটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল (বা একে পৌঁছানো হয়েছিল) যে ,কখনই তা জ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাই যদি কেউ তা অস্বীকার করে জ্ঞান অন্বেষনে লিপ্ত হতেন পরিশেষে দেখা যেত তিনি যারথুষ্ট্র ধর্ম ত্যাগ করেছেন।
5. মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অধিকাংশই শিয়া ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায় বহির্ভূত দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র স্পেনের দার্শনিকগণ ছাড়া (যাঁরা শিয়া পরিবেশ ও চিন্তা হতে দূরে ছিলেন) বাকিরা প্রায় সকলেই শিয়া চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে ,শিয়াদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রথম হতেই দর্শনকেন্দ্রিক ছিল। আমরা ‘ নাহজুল বালাগা ’ র তাৎপর্য গ্রন্থে (সেইরী দার নাহজুল বালাগাহ্) এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে অধিক আলোচনার জন্য আরো বেশি সময় প্রয়োজন। তাই এখানে তা হতে বিরত থাকছি।
6. দর্শন ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইরানীদের অবদান ইসলামী সংস্কৃতিতে অ-ইরানীদের সমগ্র অবদান হতে এতটা অধিক যে ,তাতে ইরানীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যই ফুটে উঠেছে ;বিশেষত দশম হিজরী শতাব্দী হতে যখন ইরানে নিরঙ্কুশ শিয়া প্রাধান্য লাভ করে তখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় হতে মুসলিম দার্শনিকদের সকলেই ইরানী। যদিও ইরানীরা ইসলামী দর্শনের সূচনাকারী নয় এবং সর্বপ্রথম মুসলিম দার্শনিক একজন আরব ,তদুপরি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের পর হতে ইরানীরা এর পতাকা স্বহস্তে ধারণ করে এবং অন্যান্য সকল জাতি হতে দর্শনের সঙ্গে অধিকতর স ¤পৃক্ত হয়ে পড়ে। আমার দৃষ্টিতে এর পেছনে দু ’ টি কারণ রয়েছে। প্রথমত যারথুষ্ট্রদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও (ইসলামপূর্ব যুগে) ইরানীদের চিন্তার প্রকৃতি ছিল দর্শনভিত্তিক। দ্বিতীয়ত ইরানে শিয়া চিন্তার প্রভাব। যদি ইরানী দার্শনিকদের মধ্য হতে আরব ,তুর্কী বা অন্য কোন বংশোদ্ভূতদের পৃথক না করি (যেমন ফখরুদ্দীন রাযী ,জালালউদ্দীন দাওয়ানী ,সাদরুদ্দীন দাশতাকী ,গিয়াসউদ্দীন দাশতাকী প্রমুখদের বাদ না দিই) তবে বলা যায় অ-ইরানী দার্শনিকদের সংখ্যা নগণ্য।
অ-ইরানী দার্শনিকদের মধ্যে একদল হলেন অমুসলমান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মিশর ,সিরিয়া ,স্পেন প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসক-দার্শনিকগণ। অপর দল হলেন অ-ইরানী মুসলমান ,যেমন ইবনে হাইসাম বাসরী মিশরী ,আবুল বারাকাত বাগদাদী ,আলী ইবনে রেজওয়ান মিশরী আল কিন্দী ,ইবনে রুশদ ,ইবনে তোফাইল ,ইবনুস সায়িতা ,কুতুবউদ্দীন মিশরী ,কামালউদ্দীন ইউনুস মৌসেলী এবং কারো কারো মতে ফারাবীও এদের অন্তর্ভুক্ত।
7. ইবনে সিনার পূর্বে দর্শন শিক্ষার কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। ইবনে সিনা এ কেন্দ্রকে ইরানে স্থানান্তর করেন। ইবনে সিনা কোন সময়েই বাগদাদে যাননি ,এমনকি তাঁর দর্শনের কোন শিক্ষকও ছিল না ,যদিও একজন শিক্ষকের নিকট কিছুদিন যুক্তিবিদ্যা পড়েছিলেন। ইবনে সিনার বিরল প্রতিভা ও প্রসিদ্ধি জ্ঞান অন্বেষণকারীদের বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর নিকট আসতে ও তাঁর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করত। তাঁর গ্রন্থসমূহ ছিল পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের যুক্তি খণ্ডনকারী ও সমালোচক। যদিও প্রথমদিকে তাঁর গ্রন্থসমূহের পাঠদানকারী শিক্ষকরা শুধুই ইরানী ছিলেন তবে পরবর্তীতে তা ইরানের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে সিনার চিন্তার প্রভাব ,তাঁর লিখিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থসমূহ এবং এ গ্রন্থসমূহের পাঠদানকারী তাঁর সকল ছাত্রই ইরানী হওয়ায় বাগদাদ হতে দর্শনের কেন্দ্র ইরানে স্থানান্তরিত হয়। যদিও এ সময় বাগদাদে ইবনে সিনার গ্রন্থসমূহ পাঠদান শুরু হয় তবে বাগদাদের পূর্বের সেই জৌলুস ছিল না।
পরবর্তীতে ইবনে সিনার ছাত্রের ছাত্র আবুল আব্বাস লুকারী ইরানে দর্শন শিক্ষাকেন্দ্রটি যা ইরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল- তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে খোরাসান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন।
8. পরবর্তীতে একদিকে মোগলদের আক্রমণ ও অপরদিকে গাজ্জালীর মতো ব্যক্তিদের হামলায় ইরানের বাইরে দর্শনের শিকড় উৎপাটিত হয়। তবে ইরানে দর্শনের প্রদীপ তখনও টিম টিম করে জ্বলছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে এ দুর্বল প্রদীপটি শক্তি সঞ্চয় করে আলো দিতে শুরু করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল ফার্স প্রদেশ। আরো পরে সাফাভীরা ক্ষমতায় আসলে ইসফাহানে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আন্দোলন নতুনভাবে শুরু হয় এবং মীর দামাদ ও মোল্লা সাদরার মাধ্যমে দর্শন পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়।
9. সাফাভীদের সময়কাল হতে ইসলামী দর্শন ইরানী শিয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে ইরানের সব অঞ্চল সমানভাবে ইসলামী দর্শনে ভূমিকা রাখেনি। কোন কোন অঞ্চল বর্ণনামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ভূমিকা রাখলেও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাখেনি বা রাখলেও তা নগণ্য। খুজিস্তান আরবী ব্যাকরণ ,হাদীস এবং ফিকাহ্শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও দর্শন ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাখেনি। সিস্তান-বেলুচিস্তানের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এ অঞ্চলের একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হলেন আবু সোলায়মান মানতেকী সাজেস্তানী। কোন কোন প্রদেশ স্বল্প ভূমিকা রেখেছে। যেমন আজারবাইজান। আজারবাইজানের বিশিষ্ট দার্শনিকদের মধ্যে বাহমানইয়ার ,শামসউদ্দীন খসরুশাহী ,মোল্লা রজব আলী ,মোল্লা হুসাইন আরদেবিলী ,আলী হাকিম যানুযী এবং বর্তমান সময়ের আল্লামা তাবাতাবায়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। আবার কোন কোন প্রদেশ দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যেমন খোরাসান ,ইসফাহান এবং ফার্স।
যে বিষয়টি অনেকের নিকটই আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে তা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মীর দামাদের সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইরানের উত্তরাঞ্চলের তিনটি প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। এ তিনটি প্রদেশ হলো গীলান ,মাজেনদারান এবং গোরগান। দর্শনের প্রসিদ্ধ ত্রিশজন শিক্ষক এ অঞ্চলের। যেমন মীর দামাদ ,মোল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী ,মুহাম্মদ বাইদাবাদী ,মোল্লা আলী নূরী ,মীর ফানদারাসকী ,আবদুর রাজ্জাক লাহিযী ,মোল্লা মুহাম্মদ জাফর লাঙ্গরুদী প্রমুখ । যদিও এ ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের বলয় ছিল ইসফাহান ,কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উত্তর ইরানের অধিবাসী।
10. এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে যে ,দার্শনিকদের নামসমূহ এনেছি তা ধারাবাহিক ,অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কিত হিসেবে একটি অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির নমুনা। ফিকাহ্ ,হাদীসশাস্ত্র ,এরফান ,সাহিত্য ,ব্যাকরণ ,এমনকি গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এরূপ নমুনা পেশ করা সম্ভব। শিক্ষক-ছাত্রের ভিত্তিতে রচিত এ তালিকায় শুধু দু ’ স্থানে অস্পষ্টতা রয়েছে। একটি স্থান হলো ইরানে আফগানদের আক্রমণের সময় দার্শনিক মোল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ীর বিষয়। আর তা হলো তিনি স্বয়ং বা তাঁর সম্পর্কে যাঁরা বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের কেউই তাঁর শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেননি। অন্য স্থানটি হলো জনাব মীর দামাদের শিক্ষক ফাখরুদ্দীন সামাকীর শিক্ষকদের সম্পর্কে কেউ কিছু উল্লেখ করেননি।335
অবশ্য এ দু ’ টি বিষয় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত। এ তালিকায় কোন অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেনি। তাই এ দু ’ স্থানকে বাদ দিলে আমার শিক্ষকদের ধারাবাহিকতা ইবনে সিনা পর্যন্ত পৌঁছায় (অর্থাৎ তাঁদের সকলের নাম আমরা উল্লেখ করতে সক্ষম)। অন্যদিকে শেখ বাহায়ীকে যদি দার্শনিক হিসেবে ধরি তবে ঐ দু ’ স্থানের অস্পষ্টতাও দূর হয়ে যায় এভাবে যে ,মীর দামাদকে বাদ দিয়ে যদি শেখ বাহায়ীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করি তবে তাঁর শিক্ষক মোল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদীর মাধ্যমে আমার শিক্ষকের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্নভাবে ইবনে সিনা পর্যন্ত পৌঁছায়। যেহেতু ইবনে সিনার দর্শনের আদৌ কোন শিক্ষক ছিল না সেহেতু ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত এ তালিকা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।
11. অবশ্য ইবনে সিনা ছাড়াও দু ’ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে ,তাঁদের দর্শনের শিক্ষক ছিল না। তাঁরা দর্শনের গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে দার্শনিক হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আল কিন্দী ও ফারাবী। ইতিহাসে আল কিন্দীর কোন শিক্ষকের নাম উল্লিখিত হয়নি । এমনকি বাস্তবেও আল কিন্দীর অঞ্চলে কোন দার্শনিকের অস্তিত্ব ছিল না। তাই ইসলামী দর্শনের ধারা আল কিন্দী হতেই শুরু হয়েছে। ফারাবীও ইউহান্না ইবনে হাইলানের নিকট শুধু যুক্তিবিদ্যা পড়েছিলেন। তাঁরও দর্শনের কোন শিক্ষক ছিল না। অনেকে ফারাবীর শিক্ষক হিসেবে আবু বাশার মাত্তার নাম উল্লেখ করেছেন ,কিন্তু এটি যে ঠিক নয় তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য ,মুসলমানগণ দর্শনের গ্রন্থের ক্ষেত্রে অমুসলমানদের নিকট ঋণী হলেও দর্শনের শিক্ষকের ক্ষেত্রে কখনই তা নয়।
এখন আমরা এরফান ও তাসাউফশাস্ত্রে ইরানী মুসলমানদের অবদান নিয়ে আলোচনা করব।
এরফান ও তাসাউফ
অপর যে জ্ঞানটি ইসলামী সংস্কৃতির কোলে জন্ম নিয়ে ও লালিত-পালিত হয়ে বিকশিত ও পূর্ণতা পায় তা হলো এরফান (অধ্যাত্ববাদ)।
এরফান সম্পর্কে দু ’ টি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে পারে। যার একটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও অপরটি সংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ।
আরেফগণের সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের পণ্ডিতগণ ,যেমন মুফাসসির ,মুহাদ্দিস ,ফকীহ্ ,কালামশাস্ত্রবিদ ,সাহিত্যিক ,ব্যাকরণবিদ ও কবিগণের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হলো এই যে ,এ শ্রেণীটি অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রেণী হিসেবে এরফান নামে স্বতন্ত্র জ্ঞানের সৃষ্টি ,স্বতন্ত্র চিন্তার মনীষীর আবির্ভাব ,গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার বাইরেও ইসলামী বিশ্বে একটি সামাজিক দলের সৃষ্টি করেছিল। দার্শনিক ,ফকীহ্ ও অন্যান্য শ্রেণী শুধুই একটি সাংস্কৃতিক শ্রেণী ছিল ;স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী বলে পরিগণিত হতো না। কিন্তু আরেফগণ সমাজের বিশেষ শ্রেণী ও মতের ব্যক্তি ছিলেন। আরেফগণকে সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ‘ উরাফা ’ এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে ‘ মুতাসুফা ’ বা সুফী মতাবলম্বী হিসেবে অভিহিত করা হয়।
আরেফ ও সুফিগণ যদিও ইসলামের স্বতন্ত্র কোন মাযহাবের বলে নিজেদের দাবি করতেন না বরং সকল মাযহাবেই তাঁদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তদুপরি তাঁরা সামাজিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত এক বিশেষ দল ,তাঁদের বিশেষ চিন্তাধারা রয়েছে ,পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ রীতির অনুসারী ,বিশেষ পোশাক পরিধান করেন ,বিশেষভাবে চুল-দাড়ি রাখেন এবং বিশেষ স্থানে (খানকায়) বাস করেন। এ বিষয়গুলো তাঁদের বিশেষ সামাজিক দল ও মাযহাবের রূপ দিয়েছে । অবশ্য আরেফগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন (বিশেষত শিয়াদের মাঝে) যাঁরা সমাজের অন্য শ্রেণী হতে বাহ্যিকভাবে স্বতন্ত্র ছিলেন না ,কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এরফানের পথে গভীর সাধনায় রত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্তরাই আরেফ নামের যোগ্য ,অন্যরা নয়- যারা নিজেরা বিভিন্ন রীতি-নীতি ও বেদআতের জন্ম দিয়েছে।
আমরা এখানে এরফানের ‘ তাসাউফ ’ প্রবণতা তথা সামাজিক ও ফিরকাগত উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব না ;বরং শুধু তাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকটি নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ এরফানকে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি শাখা হিসেবে যা শতাব্দীকাল ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে সে দৃষ্টিকোণ হতে দেখব ;একটি সামাজিক ফিরকা ও তরীকা বা পথ হিসেবে নয়।
এরফানের জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত কাঠামোতে দু ’ টি অংশ রয়েছে: ব্যবহারিক দিক ও তত্ত্বগত দিক।
ব্যবহারিক দিকটি মানুষের নিজসত্তা ,স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের ধরন ও কর্তব্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এ দিক হতে এরফান নৈতিকতার মত একটি ব্যবহারিক জ্ঞান ,তবে এ দু ’ য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এরফানের এই দিকটিকে ‘ পথ ও পথপরিক্রমা ’ (আরবীতে সাইর ওয়া সুলুক) নামে অভিহিত করা হয়। এরফানের এ অংশে পথিক (সালিক) কিরূপে মানবতার চূড়ান্ত শিখরে অর্থাৎ একত্ববাদে পৌঁছতে পারে ,এ যাত্রা কোথা হতে শুরু করবে ,কোন্ কোন্ পথ অতিক্রম করবে ,পথের বিভিন্ন পর্যায়ে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে ,সে কি লাভ করবে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অবশ্য পথিককে এ পথ পরিক্রমাটি কোন পূর্ণ মানবের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে যিনি এ সকল পর্যায় অতিক্রম করেছেন-এর বিভিন্ন পর্যায়ের সমস্যা ও সামাধান সম্পর্কে অবহিত। নতুবা তার বিচ্যুতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। নব্য পথিকের জন্য যে পূর্ণ মানব সহযোগী হন তাঁকে আরেফগণ কখনও খিজির ,আবার কখনও ‘ পবিত্র পাখি ’ (তাইরু কুদ্স) বলে থাকেন। কবির ভাষায় :
‘ হে পবিত্র পাখি দেখাও মোরে পথ সঠিক
গন্তব্য যে দীর্ঘ পথ ,আর আমি নব্য পথিক
এ পথে খিজির ছাড়া ত্যাগ কর না আমায়
অন্ধকার পথ ,রয়েছে ভ্রষ্টতার বিপদ সেথায়।
অবশ্য আরেফগণ যে তাওহীদ বা একত্ববাদের কথা বলেন ও ঐশী পথ পরিক্রমার শেষ বিন্দু বলে বিশ্বাস করেন সে তাওহীদের সঙ্গে তাওহীদের সাধারণ অর্থ ,এমনকি দার্শনিক অর্থেরও (ওয়াজিবুল উজুদ বা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব একের অধিক হতে পারে না) বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আরেফদের মতে মহান আল্লাহ্ একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু তাঁরই প্রকাশ ও বাহ্যিক চিহ্ন মাত্র- প্রকৃত অস্তিত্ব নয়। অন্যভাবে বলা যায় ,বাস্তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আরেফদের ভাষায় তাওহীদ হলো পথ পরিক্রমা শেষে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই না দেখা। এরফানের এ মতের বিরোধীরা একে সমর্থন করেন না ,বরং একে কুফ্র বলে মনে করেন। কিন্তু আরেফগণ বিশ্বাস করেন এটিই প্রকৃত তাওহীদ এবং তাওহীদের অন্যান্য পর্যায়সমূহ র্শিকমুক্ত নয়। তাঁদের মতে এ পর্যায়ে পৌঁছানো বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে সম্ভব নয় ;এ পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কঠোর সাধনা করতে হয় ও দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শেষে মানবহৃদয় সেখানে পৌঁছায়।
উপরিউক্ত আলোচনাটি এরফানের ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ দৃষ্টিতে আখলাক বা নৈতিকতার সঙ্গে এরফানের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য রয়েছে। আখলাকের আলোচনায়ও ‘ কি করা উচিত ’ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। তবে এরফানের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো: প্রথমত এরফান মানুষের সঙ্গে তার নিজ সত্তা ,বিশ্বজগৎ ও স্রষ্টার সম্পর্ক নিয়ে বিশেষত স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এর বিপরীতে নৈতিকতার অনেক মতই স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আদৌ আলোচনা করে না ,শুধু নৈতিকতার ধর্মীয় মতসমূহ নিয়ে আলোচনা করে থাকে।
দ্বিতীয়ত এরফানের পথ পরিক্রমা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও গতিশীল। এর বিপরীতে নৈতিকতার বিষয় স্থির। এরফানে ঐশী যাত্রার শুরু ,গন্তব্য ও মধ্যবর্তী অনেক পর্যায় রয়েছে এবং এ পথের যাত্রীকে পর্যায়ক্রমে তা অতিক্রম করে চূড়ান্ত বিন্দু বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে হয়। আরেফগণের দৃষ্টিতে অকৃত্রিমভাবে মানুষের জন্য পথ রয়েছে এবং মানুষকে পর্যায়ক্রমে সে পথ অতিক্রম করতে হয়। এ পথের পর্যায়সমূহ এক একটি গন্তব্য এবং পূর্ববর্তী গন্তব্য অতিক্রম ব্যতীত পরবর্তী
গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে মানবাত্মা একটি শিশু বা চারাগাছের ন্যায় যার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা বিশেষ নিয়মের অধীন। এর বিপরীতে নৈতিকতায় শুধু এক ধরণের উচ্চতর নৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়। যেমন- সততা ,সত্যবাদিতা ,ন্যায়রায়ণতা ,পরোপকার ,সচ্চরিত্র ,ইনসাফ ,আত্মত্যাগ প্রভৃতি এবং মানুষকে এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিজকে অলংকৃত করার পরামর্শ দেয়া হয়। আখলাকের দৃষ্টিতে মানবাত্মা একটি গৃহের ন্যায় এবং মানুষ সে গৃহকে বিভিন্ন সৌন্দর্য উপকরণ দিয়ে সাজাবে ,এটিই লক্ষ্য। সেখানে শুরু ,গন্তব্য ও পর্যায় প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ দেয়ালের চিত্রকর্ম দিয়ে নাকি ছাদের নকশা দিয়ে ,ওপর হতে নাকি নীচ হতে-এ বিষয়গুলো নেই। কিন্তু এরফানে নৈতিকতার বিষয়সমূহ প্রাণবন্ত ও গতিশীল আকারে উপস্থাপিত হয়।
তৃতীয়ত নৈতিকতার আত্মিক উপাদানসমূহ সীমিত এবং সাধারণত সকলেই সেগুলো সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু এরফানের আত্মিক উপাদানসমূহের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও ব্যাপক। এরফানের পথ পরিক্রমায় একজন পথিকের (সালিক) বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমের সময় যে বিভিন্ন আন্তরিক অবস্থার সৃষ্টি হয় ও বিভিন্ন অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় এর জ্ঞান ও অনুভূতি সে-ই জানে ;সাধারণ মানুষ তা সম্পর্কে অবহিত নয়।
এরফানের একটি অংশ অস্তিত্বজগৎ নিয়ে। অর্থাৎ এ অংশে খোদা ,বিশ্ব ও মানুষকে ব্যাখ্যা করা হয়। এরফানের এ অংশটি দর্শনের মত অস্তিত্বজগৎকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে। এরফান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আখলাকের ন্যায় মানুষকে পরিবর্তিত করতে চায় এবং তত্ত্বগতভাবে দর্শনের ন্যায় অস্তিত্বজগতের অবস্থান ও অবস্থা বিশ্লেষণ করতে চায়। তবে এ ক্ষেত্রেও দর্শনের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে।
এরফান ও ইসলাম
তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই এরফানের সঙ্গে ইসলামের অনেক দিক হতে সম্পর্ক ও মিল এবং অনেক দিক হতে অমিল ও সংঘর্ষ রয়েছে। অন্যান্য ধর্ম ও মতের মত (বাস্তবে অন্যান্য ধর্ম ও মত হতে অধিকতর) এরফান মানুষের সঙ্গে স্রষ্টা ,বিশ্বজগৎ ও নিজ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে এবং অস্তিত্বজগৎকে ব্যাখ্যা দিয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেবে ,এরফান এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কি বলেছে ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়সমূহে কিরূপ এবং এ দু ’ দৃষ্টিভঙ্গির মিল বা অমিল কতটুকু ?
অবশ্য মুসলিম সুফী ও আরেফগণ কখনই দাবি করেন না যে ,তাঁরা ইসলাম বহির্র্ভূত কিছু বলছেন ,বরং তাঁরা দাবি করেন অন্যদের হতে তাঁরা উত্তমরূপে ইসলামের বাস্তবতাকে অনুভব ও অনুধাবন করতে পেরেছেন ও তাঁরাই প্রকৃত মুসলমান। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা কোরআন ,সুন্নাত ,নবী (সা.)-এর জীবনপদ্ধতি ,আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের বাণী ও বিশিষ্ট সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি হতে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।
কিন্তু অন্যরা তাঁদের সম্পর্কে ভিন্নদৃষ্টি পোষণ করেন । আমরা এ মতসমূহ ক্রমানুসারে তুলে ধরছি :
1. কোন কোন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসের মত হলো সুফী ও আরেফগণ আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারী নয়। তাঁদের কোরআন ও হাদীস হতে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্য বলা হয়ে থাকে। তাঁদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।
2. বর্তমান সময়ের কিছু নব্য চিন্তার অনুসারীদের মত: এ দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলামের তেমন ভাল সম্পর্ক নেই বিধায় তারা তাদের দৃষ্টিতে যাদের মধ্যে নিরপেক্ষতার গন্ধ পাওয়া যায় তাদের মতকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করে আর সেই মতকে ইসলাম ও ইসলামী বিধিবিধানের প্রতি এক প্রকার অনীহা ও প্রতিবাদ বলে প্রচার করে থাকেন। তাই তারাও প্রথম দলের ন্যায় আরেফদের মধ্যে কোন ইসলামী আচরণ ও বিশ্বাস নেই বলে মনে করে ও দাবি করে যে ,এরফান ও সুফীবাদ ইসলাম ও আরবদের বিরুদ্ধে অনারবদের প্রতিবাদের রূপ। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার ছত্রচ্ছায়ায় তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।
এ ব্যক্তিবর্গও প্রথম দলের ন্যায় এরফান ও সুফীবাদকে ইসলামের বিরুদ্ধবাদী একটি মত বলে মনে করে। তবে প্রথম দল ইসলামের পবিত্রতার ধারণা ও সাধারণ মুসলমানদের অনুভূতির ওপর নির্ভর করে আরেফ ও সুফীবাদের তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের মতকে ইসলামী জ্ঞানের বহির্ভূত বলার প্রয়াস চালান ,আর দ্বিতীয় দল কোন কোন আরেফ ও সুফীর বিশ্বজনীন মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ইসলামকে ছোট করার চেষ্টা চালায়। তারা বলে ,এরফানের সূক্ষ্ম ও উচ্চ মর্যাদার চিন্তা ইসলাম ও এর সংস্কৃতি বহির্ভূত। অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতির বাইরে থেকে তা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং ইসলাম ও ইসলামী চিন্তা এরফানী চিন্তা হতে অনেক নিম্নমানের। তারা দাবি করে যে ,আরেফগণ জনসাধারণের ভয়ে ও তাকিয়াগত কারণে কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তাঁদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতেন এবং এভাবে তাঁরা চেয়েছেন নিজেদের জীবন রক্ষা করতে।
3. নিরপেক্ষ দলের মতামত: এ দলের মতে তাসউফ ও এরফানে বিশেষত এরফানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক স্থানে কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী বিদআত ও বিচ্যুত কর্ম লক্ষ্য করা যায় যা অনেক সময় স্বতন্ত্র ফির্কার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আরেফগণ ইসলামী সংস্কৃতির অন্যান্য দলের (ইসলামের বিভিন্ন মতের অনুসারী) ন্যায় খাঁটি নিয়্যতে ইসলামের সেবায় রত হয়েছিলেন এবং কখনো তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেননি। হয়তো আরেফ ও সুফিগণের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার পণ্ডিতগণ ,যেমন কালামশাস্ত্রবিদ ,দার্শনিক ,মুফাসসির এবং ফকীহ্দের মধ্যকার অনেকের ন্যায় ভুলভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু তাঁদের ভুল-ভ্রান্তির পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না।
আরেফদের সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব রয়েছে এ ধারণা এক বিশেষ শ্রেণীর পক্ষ হতে বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন ,হয় ইসলামকে গ্রহণ কর অথবা এরফান ও সুফীবাদকে। যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে আরেফদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন এ শর্তে যে ,তিনি এরফানশাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত তাহলে হয়তো লক্ষ্য করবেন ,তাঁদের বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে ,কিন্তু এটি বুঝতে পারবেন যে ,আরেফ ও সুফিগণ ইসলামের প্রতি পূর্ণ আন্তরিক ছিলেন।
আমরা তৃতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিই এবং বিশ্বাস করি ,আরেফগণ কখনই অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করেন নি। তাই প্রয়োজন রয়েছে ইসলামের গভীর জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত এবং এরফানশাস্ত্রের ওপর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষভাবে ইসলামের সঙ্গে এরফানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করবেন।
একটি বিষয় এখানে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ,আর তা হলো ইসলামী এরফান কি উসূল ,ফিকাহ্শাস্ত্র ,তাফসীর ও হাদীসের ন্যায় জ্ঞান যা মুসলমানগণ ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও উৎস হতে গ্রহণ করেছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও বিধিমালা উদ্ঘাটন করেছে নাকি গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয় যা ইসলামী বিশ্বের বাইরে থেকে ইসলামী বিশ্বে প্রবেশ করেছে এবং মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রোড়ে বিকশিত হয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে নাকি তৃতীয় কোন মত এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে ?
আরেফ ও সুফিগণ প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং অন্য মতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন কোন প্রাচ্যবিদ প্রমাণ করতে চান এরফানশাস্ত্র এবং এর সূক্ষ্ম ও যথার্থ চিন্তাধারা ইসলামী বিশ্বের বাইরে থেকে ইসলামী বিশ্বে প্রবেশ করেছে। কখনো কখনো তাঁরা বলেন ,ইসলামী এরফানের মূল খ্রিষ্টধর্ম হতে এসেছে এবং মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিষ্টান দুনিয়াবিমুখ পাদ্রীদের পরিচয় লাভের ফলশ্রুতিতে তা ঘটেছে। কখনো তাঁরা এরফানী মতের উৎপত্তিকে ইসলাম ও আরবদের প্রতি ইরানীদের প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করে থাকেন। কখনো তাঁরা এরফানশাস্ত্রকে নব্য প্লেটোনিক (ঘবড় চষধঃড়হরপ) দর্শনের (যাকে অ্যারিস্টটল ,প্লেটো ,পিথাগোরাস ,আলেকজান্দ্রীয় সুফী এবং খ্রিষ্ট-ইহুদী মতবাদের সংমিশ্রণ বলা হয়ে থাকে) হুবহু অনুকরণ বলে থাকেন। কেউ কেউ আবার এরফান বা সুফীবাদকে বৌদ্ধ বা হিন্দু চিন্তা হতে উৎসারিত মনে করেন ;যেমনটি ইসলামী বিশ্বে সুফীবাদের বিরোধী ব্যক্তিবর্গও বলে থাকেন। অর্থাৎ এরফান ও তাসাউফকে তাঁরা অনৈসলামী ও ইসলাম বহির্ভূত বলে বিশ্বাস করেন।
এ বিষয়ে তৃতীয় মত হলো এরফানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকই (মূল উপাদানসমূহ) ইসলাম হতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই মৌল নীতি ও বিধান তৈরি করা হয়েছে। তবে তা ইসলাম বহির্ভূত দর্শন ও চিন্তাধারা বিশেষত এশরাকী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।
কিন্তু আরেফগণ ইসলামের মৌল উপাদানের ভিত্তিতে সঠিক কোন নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করতে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন বা এ ক্ষেত্রে তাঁদের সফলতা ফকীহ্গণের সমপর্যায়ের কিনা বা এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইসলামের প্রকৃত মৌল নীতি হতে বিচ্যুত না হওয়ার বিষয়ে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন ? তা ছাড়া ইসলাম বহির্ভূত চিন্তাধারা এরফানশাস্ত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছে বা ইসলামী এরফান তাঁদের (অন্যান্য চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ) কতটা আকৃষ্ট করেছে ও তাঁদের স্বীয় রঙে রঞ্জিত করেছে বা নিজ পথ পরিক্রমায় তাঁদের হতে কতটা গ্রহণ করেছে তা যেরূপ বিবেচ্য তেমনি ইসলামী এরফান তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছিল কিনা তাও বিবেচ্য। উপরোক্ত বিষয়সমূহ স্বতন্ত্রভাবে যথার্থরূপে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এটি নিশ্চিত যে ,ইসলামী এরফান তার মূল পুঁজি ইসলাম হতেই গ্রহণ করেছে।
এরফান সম্পর্কিত তিনটি মতের (এরফান কোরআন ও সুন্নাতের প্রতি অনুগত কিনা) মধ্যে প্রথম মতটি পূর্ণরূপে এবং দ্বিতীয় মতটি প্রায় তার অনুরূপ দৃষ্টিতে মনে করে ইসলাম ধর্ম একটি সহজ ,সাধারণের বোধগম্য ,অস্পষ্টতামুক্ত ও গভীর চিন্তামুক্ত ধর্ম। তাঁদের ধারণা মতে ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ হলো গৃহ নির্মাতা ও গৃহের ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু ’ টি সত্তা সম্পর্কে ধারণা। তাই মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য বস্তুসমূহের সম্পর্ক তাওহীদের ধারণায় যুহদের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাঁদের মতে যুহদ অর্থ বিশ্বের ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুসমূহকে ত্যাগ করে আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া। এর পাশাপাশি ইসলামের কিছু দৈনন্দিন পালনীয় কর্তব্য রয়েছে যা বর্ণনার দায়িত্ব হলো ফিকাহ্শাস্ত্রের ওপর। এ দলের মতে আরেফগণ তাওহীদ বলতে যা বলেন তা ইসলামের তাওহীদী ধারণার বহির্ভূত বিষয়। কারণ এরফানের পরিভাষায় তাওহীদ হলো ওয়াহ্দাতে উজুদ (অস্তিত্বের একতা) এবং আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ ,গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্য কিছুর কোন অস্তিত্ত্ব নেই। তা ছাড়া এরফানের পথ পরিক্রমা ইসলামী যুহদ বহির্ভূত পথ পরিক্রমা। কারণ এরফানের পথ পরিক্রমায় এমন কিছু কথা রয়েছে যা ইসলামী যুহদের ধারণায় অনুপস্থিত। যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ,আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়া (ফানাফিল্লাহ্) ,আরেফের হৃদয়ে আল্লাহর জ্যোতির প্রতিফলন ও প্রকাশ প্রভৃতি। এরফানের তরীকতও ইসলামী শরীয়ত বর্হিভূত একটি বিষয়। কারণ তরীকতে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপনা করা হয় যা ইসলামী ফিকাহ্ ও শরীয়ত বহির্ভূত।
এ সকল ব্যক্তির মতে আরেফ ও সুফীরা তাঁদের মত ও পথকে রাসূল (সা.)-এর যে সকল সাহাবী হতে গৃহীত বলে দাবি করেন তাঁরা সাধারণ দুনিয়াবিরাগী (যাহেদ) বৈ কিছু ছিলেন না ,তাঁরা এরফানের তাওহীদ ও পথ পরিক্রমা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তাঁরা দুনিয়ার বস্তুসমূহ হতে বিমুখ এবং আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর আযাবের ভয় এবং বেহেশতের আশাতেই এমনটি করতেন।
এ ব্যক্তিবর্গের মত কখনোই গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ ইসলামের মৌল উপাদান তাঁদের ধারণা (অজ্ঞতাপ্রসূত হোক বা উদ্দেশ্যমূলক) হতে অনেক বেশি গভীর। ইসলামের তাওহীদী ধারণা যতটা সহজ ও অন্তঃসারশূন্য বলে তাঁরা মনে করেছেন তা যেমন সঠিক নয় ,তেমনি ইসলামের নৈতিকতা ও আত্মিক দিক তাঁদের ধারণার শুষ্ক দুনিয়াবিমুখতাও নয়। তেমনি রাসূল (সা.)-এর ঐ সকল সাহাবীও জানতেন ইসলামের বিভিন্ন আচার দৈহিক কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
আমরা এখানে ইসলামের যে সকল মৌল শিক্ষা এরফানের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক গভীর জ্ঞানের উৎপত্তিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল তা হতে একটি অংশের উল্লেখ করছি যাতে করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পবিত্র কোরআন তাওহীদের বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টিকে কখনোই গৃহ নির্মাতা ও গৃহের ন্যায় মনে করেনি। কোরআন মহান আল্লাহ্কে বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে পরিচয় দানের পাশাপাশি তাঁর পবিত্র সত্তা সবকিছুর সঙ্গেই বিদ্যমান রয়েছে বলেছে। যেমন বলেছে ,
) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ (
‘ তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। ’ 336
অন্যত্র বলা হয়েছে :
) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (
‘ আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের রগ হতেও তার নিকটবর্তী। ’ 337
সূরা হাদীদের 3 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :
) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (
‘ তিনিই প্রথম এবং সর্বশেষ (তাঁর থেকেই শুরু হয়েছে এবং তাতেই পরিসমাপ্ত ঘটবে) এবং তিনিই প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত। ’ 338 এবং এরূপ অন্যান্য আয়াত।
সুতরাং স্পষ্ট যে ,এ সকল আয়াত বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাসমূহকে তাওহীদের গভীরতর ও ব্যাপক এক অর্থের প্রতি আহ্বান জানায় যা সাধারণের ধারণার তাওহীদ হতে অনেক ঊর্ধ্বের বিষয়। উসূলে কাফীর এক হাদীসে এসেছে যে ,যেহেতু শেষ যামানায় এমন এক দল গভীর চিন্তার ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে সে কারণেই মহান আল্লাহ্ সূরা হাদীদের প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করেন (যাতে তাওহীদের গভীর ও ব্যাপকতর অর্থ নিহিত রয়েছে)।
এরফানের পথ পরিক্রমায় আল্লাহর নৈকট্য হতে শেষ স্তর (ফানাফিল্লাহ্) পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত যেখানে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ (لقاء الله ) ,আল্লাহর সন্তুষ্টি (رضوان الله ) ,নবী ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে ফেরেশতাদের কথোপকথন ,যেমন হযরত মরিয়ম (আ.) এবং রাসূল (সা.)-এর মিরাজ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ হতে প্রমাণ করা যায়। কোরআনে নাফসে আম্মারা ,নাফসে লাওয়ামা ,নাফসে মুতমাইন্না প্রভৃতি যেমন এসেছে তেমনি বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত জ্ঞান ,স্রষ্টা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ‘ যারা আমাদের পথে কঠোর প্রচেষ্টা ও সাধনা করবে ,অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়ে দেব ’ 339 )-এ বিষয়গুলোও এসেছে যে সম্পর্কে এরফানেও আলোচিত হয়ে থাকে অর্থাৎ বিষয়টি কোরআন হতেই নেয়া।
কোরআন আত্মশুদ্ধির বিষয়টিকে মানুষের সফলতার একমাত্র পথ বলে মনে করেছে। তাই বলা হয়েছে :
) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (
‘ নিশ্চয়ই সে-ই সফল হয়েছে যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে এবং যে আত্মাকে প্রোথিত অর্থাৎ কুলষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। ’ 340
কোরআনে আল্লাহর ভালবাসাকে সকল ভালবাসা ও মানবিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে বিশ্বের সকল বস্তুরই (তা যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক) আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসায় রত থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে ,তা হতে বুঝা যায় মানুষ যদি তার অন্তরকে পূর্ণতায় পৌঁছায় তাহলে বস্তুসমূহের এ প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা শুনতে পাবে। তদুপরি কোরআন মানুষের মধ্যে ঐশী সত্তার উপস্থিতির কথা বলেছে।
উপরোক্ত প্রমাণসমূহ আল্লাহ্ ,বিশ্ব ,মানুষ এবং বিশেষভাবে মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক বিষয়ক ইসলামী নৈতিকতার গভীর ও ব্যাপক ধারণার উপস্থিতিকে প্রমাণ করে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি ,মুসলিম আরেফগণ ইসলামের এই মূলধন হতে সঠিক ধারণাকে গ্রহণ করতে পেরেছেন কি পারেননি তা এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা শুধু ইসলামী নৈতিকতার
অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের (পাশ্চাত্যপ্রেমী কিছু লোকের) প্রচেষ্টাকে ভিত্তিহীন হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছি। মূল কথা হলো ইসলামের অভ্যন্তরে এক বিশাল সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে যা হতে মুসলিম বিশ্ব উত্তমরূপে উপকৃত হতে পারে। যদি ধরেও নিই আরেফগণ সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হননি কিন্তু নিশ্চয়ই অন্য কেউ যাঁরা আরেফ নামে প্রসিদ্ধ নন তাঁরা এ উৎসের সদ্ব্যবহার করেছেন।
তদুপরি বিভিন্ন হাদীস ,ইসলামের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী ,বিভিন্ন দোয়া ,মনীষীদের বক্তব্যসহ ইসলামের বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের ইবাদাত ও যুহদ শুষ্ক দুনিয়াবিমুখতা এবং সওয়াব বা পুরস্কারের আশায় ছিল না। বিভিন্ন হাদীস ,খুতবা বা দোয়াসমূহে উচ্চমার্গের অর্থপূর্ণ প্রচুর বিষয় রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক ব্যক্তিত্বের জীবনী তাঁদের উচ্চ ও আলোকিত প্রাণের পরিচয় বহন করে ,তাঁদের জীবনী আত্মিক প্রেমের পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে।
উসূলে কাফীতে বর্ণিত হয়েছে ,একদিন রাসূল (সা.) ফজরের নামাজের পর এক যুবক সাহাবীর প্রতি তাকিয়ে রইলেন। যুবকটির চক্ষু ছিল কোটরাগত ,দেহ শীর্ণ এবং রং ছিল বিবর্ণ। সে ছিল আত্মমগ্ন ও কিছুটা ভারসাম্যহীন। রাসূল (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন , ‘ কিরূপে রাত কাটিয়েছ ? ’ সে বলল , ‘ ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্জন করে। ’ রাসূল বললেন , ‘ তোমার ইয়াকীনের চিহ্ন কি ? ’ সে বলল , ‘ আমার ইয়াকীন আমাকে গভীর চিন্তায় মগ্ন করেছে ,আমি বিনিদ্র অবস্থায় (আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হয়ে) রাত্রি কাটাচ্ছি ,দিনগুলো কাটাচ্ছি অভুক্ত- পিপাসার্ত অবস্থায় (রোযা রেখে)। আমার ইয়াকীন আমাকে পৃথিবী ও পৃর্থিবীর মধ্যকার সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আমি যেন আল্লাহর আরশ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে সকল মানুষ হিসাবের জন্য সমবেত হয়েছে। পুনরুত্থিত সকল মানুষের মধ্যে আমিও যেন রয়েছি। আমি যেন বেহেশতীদের বেহেশতের নেয়ামতের মধ্যে এবং জাহান্নামীদের আযাবে নিপতিত দেখতে পাচ্ছি। যেন আমি এই কান দিয়েই জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ’ রাসূল (সা.) তাঁর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন , ‘ এই যুবকের হৃদয় আল্লাহ্ ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন। ’ অতঃপর যুবকটির উদ্দেশে বললেন , ‘ তোমার এ অবস্থাকে সংরক্ষণ কর ,যাতে তা পরিবর্তিত না হয়। ’
যুককটি বলল , ‘ আমার জন্য দোয়া করুন যেন শহীদ হতে পারি। ’ এর কিছুদিন পরেই এক যুদ্ধে এ যুবক শহীদ হয়।
স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন বাণী ,দোয়াসমূহ ,আত্মিক অবস্থা ,সর্বোপরি সমগ্র জীবন ঐশী চরিত্র ,উদ্দীপনা ও এরফানী চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)ও এরূপ ছিলেন। অধিকাংশ সুফী ও এরফানী ধারার (সিলসিলা) হযরত আলীতে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর বিভিন্ন বাণী মারেফাত ও নৈতিকতায় পূর্ণ। আমি দুঃখিত যে ,এরূপ দু ’ একটি উদাহরণও এখানে উপস্থাপনের সুযোগ আমার নেই। ইসলামের দোয়াসমূহ বিশেষত শিয়াদের নিকট বিদ্যমান দোয়াসমূহ যেমন ,দোয়ায়ে কুমাইল ,দোয়ায়ে আবু হামযা সুমালি ,শাবান মাসের দোয়া ,সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ায় বর্ণিত দোয়াসমূহ নৈতিকতা ও আত্মিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিন্তা ও বিশ্বাসকে ধারণ করে আছে। আমরা কি ইসলামের মধ্যে বিদ্যমান এই গভীর উৎসসমূহকে বাদ দিয়ে এর বহির্ভূত কোন উৎসের সন্ধান করব ?
এর পাশাপাশি ইসলামের সামাজিক দিকটিও রাসূলের বিভিন্ন সাহাবী ,যেমন আবু যার গিফারীর মধ্যে তীব্রভাবে লক্ষণীয়। তিনি তাঁর সময়ের অত্যাচারী শাসকের বৈষম্য ,অবিচার ,আত্মপূজা ও অনাচারমূলক বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে এতটা প্রতিবাদী ছিলেন যে ,তাঁকে নির্বাসিত হতে হয় এবং তিনি নির্বাসনেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করেন।
কোন কোন প্রাচ্যবিদ আবু যারের এরূপ ভূমিকার উৎস ও কারণ খুঁজতে ইসলামী চিন্তার বাইরে হাতিয়ে বেড়িয়েছেন। যেমন জর্জ জুরদাক তাঁর ‘ আল ইমাম আলী সওতাল আদালাতুল ইনসানিয়াহ্ ’ গ্রন্থে বলেছেন , ‘ আমি এ সকল ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করি ,তারা এক ব্যক্তিকে কোন বৃহৎ নদী বা সমুদ্রের পাশে পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিন্তায় পতিত হয় এ পাত্রটি সে কোথা হতে পানি দিয়ে পূর্ণ করল। অথচ তারা ঐ নদী বা সমুদ্রের প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় না। আবু যার ইসলাম ছাড়া অন্য কোন্ উৎস থেকে এ উদ্দীপনা পেতে পারেন ? ইসলাম ভিন্ন কোন্ উৎসটি আবু যারকে এতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে ? ’
এরফানের ক্ষেত্রেও আমরা একই অবস্থা লক্ষ্য করি। এখানেও প্রাচ্যবিদরা এরফানে ইসলামের উচ্চতর নৈতিকতা ভিন্ন অন্য উৎসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁরা ইসলামী নৈতিকতার মহাসমুদ্রকে উপেক্ষা করে থাকে। আমরা কি কোরআন ,হাদীস ,খুতবা ,দোয়া ,মুনাজাত ,জীবনেতিহাস ও অন্যান্য প্রমাণসমূহকে উপেক্ষা করে এ সব প্রাচ্যবিদ ও তাঁদের অনুসারীদের অনুকরণে এরফানের ইসলাম ভিন্ন উৎসের অনুসন্ধান করব ?
আনন্দের বিষয় হলো যে ,সম্প্রতি কিছু প্রাচ্যবিদ ,যেমন ব্রিটিশ লেখক নিকলসন এবং ফরাসী লেখক মসিও নিওন ইসলামী এরফানশাস্ত্রের ওপর ব্যাপক পড়াশোনার পর স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন ,ইসলামী এরফানশাস্ত্রের মূল উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ্। এ সম্পর্কে নিকলসনের বক্তব্য হতে কিছু অংশ তুলে ধরে এ আলোচনা শেষ করব। তিনি বলেছেন ,
‘ কোরআনে আমরা এমন কিছু আয়াত লক্ষ্য করি ,যেমন ‘ মহান আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি ’ 341 , ‘ তিনি প্রথম ও সর্বশেষ ’ 342 , ‘ তিনি ভিন্ন ইলাহ্ নেই ’ 343 , ‘ তিনি ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ’ 344 , ‘ আমি মানুষের মধ্যে নিজ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছি ’ 345 , ‘ নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং কি তার সত্তাকে দ্বিধান্বিত করে তা আমরা অবগত এবং আমরা তার ঘাড়ের রগ অপেক্ষা তার নিকটবর্তী ’ 346 , ‘ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন ’ 347 , ‘ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান ’ 348 , ‘ যাকে আল্লাহ্ আলো হতে বঞ্চিত করেন তার জন্য কোন আলোই অবশিষ্ট থাকে না ’ 349 প্রভৃতি নিশ্চিতভাবে এরফানশাস্ত্রের বীজ রোপন করেছিল। প্রাথমিক যুগের সুফীদের নিকট এ আয়াতসমূহ আল্লাহর বাণী হিসেবেই শুধু নয় ,সে সাথে তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়েছিল। ইবাদাত ও কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে গভীর চিন্তার (বিশেষত যে সকল মিরাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে) মাধ্যমে সুফিগণ রাসূল (সা.)-এর আত্মিক অবস্থা উদ্ঘাটনের চেষ্টায় রত হয়েছেন এবং নিজেদের মধ্যে সে অবস্থা আনয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। ’
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,
‘ সুফীবাদের ঐক্যের মৌল নীতিটি কোরআনে যেমনভাবে এসেছে তেমনি নবীর হাদীসেও এসেছে । নবী (সা.) বলেছেন: (হাদীসে কুদসী) আল্লাহ্ বলেছেন যে বান্দা ইবাদাত ও সৎ কর্মের মাধ্যমে আমার এতটা নিকটবর্তী হয় যে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। ফলে আমি তার কর্ণে পরিণত হই এরূপে যে ,আমার মাধ্যমেই সে শোনে ,আমি তার চক্ষুতে পরিণত হই এরূপে যে ,আমার মাধ্যমেই সে দেখে ,আমি তার জিহ্বা ও হস্তে পরিণত হই এরূপে যে ,আমার মাধ্যমেই কথা বলে এবং ধারণ করে। ’
এ বিষয়টি নিশ্চিত যে ,প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে সুফী বা আরেফ বলে কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে ,সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটিকে সুফী হিসেবে অভিহিত করা হয় তিনি হলেন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর কুফার অধিবাসী আবু হাশেম সুফী। তিনি প্রথমবারের মত ফিলিস্তিনের রামাল্লায় মুসলিম আবেদ ও যাহেদদের জন্য খানকা তৈরি করেন।
আবু হাশেমের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। আবু হাশেম সুফিয়ান সাওরীর (মৃত্যু 161 হিজরী) শিক্ষক ছিলেন। ড. কাশেম গনী তাঁর ‘ তারিখে তাসাউফ দার ইসলাম ’ গ্রন্থের 19 পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়ার ‘ সুফীয়া ওয়া ফুকারা ’ গ্রন্থের উদ্ধতি দিয়ে বলেছেন ,
‘ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সুফীদের জন্য খানকা তৈরি করেন তিনি হাসান বসরীর শিষ্য আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়িদের একজন শিষ্য। ’
যদি আবু হাশেম সুফী আবদুল ওয়াহেদের শিষ্য হয়ে থাকেন তবে এই দু ’ বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।
প্রসিদ্ধ সুফী ও আরেফ আবুল কাসেম কুশাইরী বলেছেন , ‘ সুফী ’ পরিভাষাটি 200 হিজরী শতাব্দীর পূর্বেই উৎপত্তি লাভ করেছে। নিকলসনের বর্ণনা মতেও পরিভাষাটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উসূলে কাফীর 5ম খণ্ডের ‘ কিতাবুল মায়িশাত ’ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় ,এ পরিভাষাটি ইমাম সাদিক (আ.)-এর সময় হতেই অর্থাৎ 2য় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধেই উৎপত্তি লাভ করেছিল এবং এ সময়েই সুফিয়ান সাওরীসহ অনেককেই এ নামে ডাকা হতো। যদি আবু হাশেম কুফী সুফী নামে অভিহিত প্রথম ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে তিনি সুফিয়ান সাওরীর শিক্ষক হওয়ার সম্ভবনাটি প্রবল। তাই নিকলসন ও অন্যান্যের মতে এ মতটি সঠিক যে ,সুফী নামটি 2য় হিজরী শতাব্দীর প্রথম হতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুফীয়া বা সুফী পরিভাষাটি ‘ সাওফ ’ صوف শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ পুরু পশম। যেহেতু এ ব্যক্তিবর্গ মসৃণ কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকতেন এবং বিশেষভাবে তৈরি পুরু পশমের কাপড় পরতেন সেহেতু তাঁদের ‘ সুফী ’ বলে অভিহিত করা হতো। এ বিষয়টি তাঁদের যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার নিদর্শন ছিল।
তবে এরূপ ব্যক্তিবর্গকে কখন হতে ‘ আরেফ ’ নামে অভিহিত করা হয় সে বিষয়ে সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। সেররী সাকতির (মৃত্যু 243 হিজরী) বর্ণনা হতে জানা যায় ,তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হতেই এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। কিন্তু আবু নাসর শিরাজের ‘ আল্লাময়ু ’ গ্রন্থ (যা এরফান ও তাসাউফ সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ) হতে জানা যায় ,দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এ পরিভাষাটি উৎপত্তি লাভ করেছিল।350
যা হোক প্রথম হিজরী শতাব্দীতে সুফী নামে কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। এ পরিভাষাটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে উৎপত্তি লাভ করেছিল। সম্ভবত এ সময়েই স্বতন্ত্র একটি দল হিসেবে সুফিগণ পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম হিজরী শতাব্দীতে সুফী বা আরেফ নামে কোন বিশেষ দলের অস্তিত্ব না থাকলেও এর অর্থ এটি নয় যে ,রাসূল (সা.)-এর সাহাবিগণ সাধারণ অর্থে যাহেদ বা আবেদ ছিলেন এবং ঈমানের মানদণ্ডে তাঁরা সকলে সাধারণ পর্যায়ে ছিলেন বা তাঁরা আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার উচ্চতর পর্যায় সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন যেমনটি পাশ্চাত্যের কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে থাকেন। যদিও সাহাবীদের কেউ কেউ ইবাদাত ও যুহদের ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যায়ে অবস্থান করতেন তদুপরি তাঁদের অনেকেই উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে ছিলেন তাঁরাও সকলে এক পর্যায়ের ছিলেন না ,এমনকি হযরত সালমান ফার্সী (রা.) এবং হযরত আবু যার গিফারী (রা.)ও এক পর্যায়ের ছিলেন না। সালমানের আধ্যাত্মিকতার ধারণ ক্ষমতা যে পর্যায়ে ছিল আবু যার তা ধারণে সক্ষম ছিলেন না। এ সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো :
لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لَقتله
‘ সালমানের হৃদয়ে যা রয়েছে যদি তা আবু যার জানত ,তাহলে তাকে (সালমানকে) সে হত্যা করত। ’
এখন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী হতে দশম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সুফী ও আরেফগণের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করবো।
দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. হাসান বসরী: পারিভাষিক অর্থে এরফানশাস্ত্রের ইতিহাস হাসান বসরীর মাধ্যমে শুরু হয়েছে যেমনটি আহলে সুন্নাতের কালামশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। হাসান বসরী 22 হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং 110 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনের নয়-দশমাংশ সময় প্রথম হিজরী শতাব্দীতেই অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং তিনি সুফী নামে অভিহিত ছিলেন না। তবে তিনি তাসাউফের বিষয়ে ‘ রেয়াইতু হুকুকুল্লাহ্ ’ (আল্লাহর হক আদায়) নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা তাসাউফ সস্পর্কিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। বর্তমানে এ গ্রন্থটির একটি মাত্র খণ্ডই বিদ্যমান রয়েছে যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। নিকলসন দাবি করেছেন ,
‘ সুফী জীবন পদ্ধতির সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন হাসান বসরী অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে তিনিই এ পদ্ধতির প্রবক্তা। সাম্প্রতিক লেখকগণ তাসাউফের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার জন্য যে পথের বর্ণনা দিয়ে থাকেন তার প্রথম পর্যায় হলো তওবা। অতঃপর ধারাবাহিক কিছু আমল রয়েছে... যার প্রতিটি পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে অতিক্রম করতে হয়। ’
কোন কোন আরেফ ও সুফী তাঁদের সিলসিলাকে হাসান বসরীর মাধ্যমে হযরত আলী (আ.) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। যেমন আবু সাঈদ আবুল খায়েরের সিলসিলা। ইবনুন নাদিম তাঁর ‘ আল ফেহেরেস্ত ’ গ্রন্থের 5ম অধ্যায়ের 5ম প্রবন্ধে আবু মুহাম্মদ এবং জাফার খুলদীর সিলসিলাকেও হাসান বসরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলেছেন ,হাসান বসরী 70 জন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।
কোন কোন বর্ণনা মতে ,হাসান বসরী ও তাঁর অনুসারীরা পরবর্তীতে সুফী নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এরূপ কয়েকটি বর্ণনা আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করব। হাসান বসরী একজন ইরানী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি।
2. মালেক ইবনে দীনার: তিনি বসরার অধিবাসী। এ ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে খুবই কড়াকড়ি করতেন। বৈধ উপভোগ্য অনেক বিষয়কেই তিনি চরমভাবে বর্জন করতেন। তিনি 131 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. ইবরাহীম আদহাম: তিনি বাল্খের অধিবাসী। তাঁর ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবনী অনেকটা গৌতম বুদ্ধের মতো। তিনি বাল্খের বাদশাহ ছিলেন। এক রাতের এক ঘটনায় তিনি পরিবর্তিত হন এবং সুফী হয়ে যান। সুফীরা তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মাওলানা রুমী ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম আদহাম 161 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. রাবেয়া আদভীয়া: এই নারী বংশগতভাবে বসরার অথবা মিশরের। তিনি তাঁর সময়ের বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পিতামাতার চতুর্থ কন্যা হিসেবে তাঁকে রাবেয়া বলা হতো। রাবেয়া আদভীয়া ও রাবেয়া শামিয়া এক নারী নন। রাবেয়া শামিয়া একজন সুফী ও আরেফ ছিলেন যিনি নবম হিজরী শতাব্দীর জামীর সমসাময়িক। রাবেয়া আদাভীয়া এরফান ও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিচয় বহনকারী বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। তাঁর কিছু বাণী হতেও তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে হাসান বসরী ও মালেক ইবনে দীনারের সাক্ষাতের আকর্ষণীয় ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি 135 বা 136 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি 180 বা 185 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. আবুল হাশেম সুফী কুফী: তিনি সিরিয়ার অধিবাসী। সিরিয়াতেই তিনি জন্মগ্রহণ এবং জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে জানা যায়নি। তিনি সুফিয়ান সাওরীর শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবত তিনি সুফী হিসেবে অভিহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তি। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন , ‘ আবুল হাশেম না থাকলে রিয়া সম্পর্কে যথার্থভাবে আমি জানতে পারতাম না। ’
6. শাকীক বালখী: তিনি ইবরাহীম আদহামের শিষ্য ছিলেন। ‘ রাইহানাতুল আদাব ’ গ্রন্থে আলী ইবনে ঈসা আরবিলীর ‘ কাশফুল গুম্মাহ ’ এবং শাবলানজীর ‘ নুরুল আবসার ’ গ্রন্থের সূত্রে বলা হয়েছে ,এ ব্যক্তির সঙ্গে মক্কায় হযরত মূসা ইবনে জাফর (আ.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি ইমাম মূসার উচ্চ মর্যাদার পরিচয় বহনকারী কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। শাকীক বালখী 153 হিজরীতে (কোন কোন বর্ণনায় 174 বা 184 হিজরীতে) মৃত্যুবরণ করেন।
7. মারুফ কুর্খী: তিনি বাগদাদের কুর্খের অধিবাসী। যেহেতু এ ব্যক্তির পিতার নাম ফিরুজ সেহেতু মনে হয় তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত। তিনি প্রসিদ্ধ আরেফদের মধ্যে পরিগণিত। কথিত আছে যে ,তাঁর পিতামাতা খ্রিষ্টান ছিলেন এবং তিনি ইমাম রেজা (আ.)-এর মাধ্যমে মুসলমান হন। তিনি ইমাম রেযার সান্নিধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। আরেফদের দাবি অনুযায়ী কোন কোন এরফানী সিলসিলা মারুফ কুর্খীর মাধ্যমে ইমাম রেযাতে এবং ইমাম রেযার মাধ্যমে স্বয়ং রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণেই এরফানের এই সিলসিলাটিকে ‘ সিলসিলাতু যাহাব ’ অর্থাৎ ‘ স্বর্ণের শিকল ’ বলা হয়ে থাকে। যাহাবী সিলসিলার আরেফগণ সাধারণত এ দাবি করে থাকেন। মারুফ কুর্খী 200 হতে 206 হিজরীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।
8. ফাজেল ইবনে আয়াজ: তিনি খোরাসানের মার্ভের অধিবাসী। তবে আরব বংশোদ্ভূত ইরানী। কথিত আছে ,তিনি প্রথম জীবনে মরুদস্যু ছিলেন। এক রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে একটি ঘরে প্রবেশ করতে গেলে ঐ গৃহের এক ব্যক্তির কণ্ঠে কোরআনের একটি আয়াত শুনে তিনি পরিবর্তিত হয়ে যান। ‘ মিসবাহুশ শারীয়াত ’ গ্রন্থটি তাঁর রচিত । কথিক আছে যে ,এ গ্রন্থটি তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করে রচনা করেছিলেন। বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাজী মির্জা হুসাইন নূরী তাঁর ‘ মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে উপরোক্ত গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ফাজেল ইবনে আয়াজ 187 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. বায়েজীদ বাস্তামী: প্রকৃত নাম তাইফুর ইবনে ঈসা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আরেফ এবং ইরানের বাস্তামের অধিবাসী। কথিত আছে তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলেন। বায়েজীদ বাস্তামী আল্লাহ্ সম্পর্কে অসংলগ্ন কিছু বলার কারণে অন্যেরা তাঁকে কাফের বলেছে। কোন কোন আরেফ তাঁকে মাতাল ও চিন্তাশক্তি লোপপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে বায়েজীদ যখন বুদ্ধিশক্তি হারাতেন তখনই এরূপ কথা বলতেন। কথিত আছে ,বায়েজীদ ইমাম সাদিক (আ.)-এর গৃহে পানি আনার কাজ করতেন ,কিন্তু এ বর্ণনাটি সঠিক নয়। কারণ বায়েজীদ ইমাম সাদিকের মৃত্যুর 113 বছর পর অর্থাৎ 261 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁর পক্ষে ইমাম সাদিকের গৃহে কাজ করার বিষয়টি অমূলক।
2. বাশার হাফী: তিনি বাগদাদের অধিবাসী। তবে তাঁর পিতৃপুরুষ খোরাসানের মার্ভের অধিবাসী ছিলেন। তিনিও প্রসিদ্ধ আরেফদের একজন। কথিত আছে ,প্রথম জীবনে তিনি একজন অসৎ লোক ছিলেন ;পরবর্তীতে তওবা করেন। আল্লামা হিল্লী তাঁর ‘ মিনহাজুল কারামাহ্ ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,বাশার হাফী ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)-এর নিকট তওবা করেন এবং যেহেতু তওবা করার মুহূর্তে তাঁর পা ছিল নগ্ন যাকে আরবীতে ‘ হাফী ’ বল হয় সেহেতু তিনি বাশার হাফী নামে পরিচিতি লাভ করেন। বাশার হাফী 226 অথবা 227 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. সেররী সাকতী: তিনি বাগদাদের অধিবাসী। তিনি বাশার হাফীর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। সেররী সাকতী একজন ত্যাগী ,দয়ালু ও মানব সেবক ছিলেন। ইবনে খাল্লেকান তাঁর ‘ ওফাইয়াতুল আইয়ান ’ গ্রন্থে সেররীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ,তিনি বলেছেন , ‘ এক আলহামদুলিল্লাহ্ বলার কারণে আমি ত্রিশ বছর ধরে অনুশোচনা ও জন্য তওবা করছি । ’ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন , ‘ এক রাত্রে বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে আমি গৃহ হতে এ উদ্দেশ্যে বের হলাম যে ,আমার দোকানে আগুন লেগেছে কিনা। যখন দেখলাম আমার দোকানে আগুন লাগেনি তখন সন্তুষ্ট হয়ে বললাম: আলহামদুলিল্লাহ্। তখনই আমার মনে হলো আমি অন্য মুসলমানদের চিন্তা না করে নিজের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় কেন্ খুশি হলাম ? ’ কবি সাদী এই ঘটনাটিকে সামান্য পার্থক্য সহকারে নিম্নোক্ত কবিতায় বর্ণনা করেছেন :
‘ এক রাত্রে অগ্নিকাণ্ডের এক ঘটনা ঘটল
শুনলাম তাতে বাগদাদ হয়েছে প্রজ্বলিত
ধূলিভস্মের মাঝে এক ব্যক্তি আল্লাহর শোকর করল
এ আনন্দে যে ,তার দোকান হয়নি ভস্মীভূত
অন্তর হতে বিবেক বলল ,হে প্রবৃত্তি পূজারী! হে নষ্ট!
আপন মু্ক্তিতেই হলি তুই সন্তুষ্ট ?
পুরো শহর হলো ধ্বংস ,তুই কেন হলি না রুষ্ট ?
যদি নিজেও হতি আক্রান্ত তবেই কি পেতি কষ্ট ? ’
সেররী সাকতী মারুফ কুর্খীর শিষ্য ছিলেন। বিশিষ্ট আরেফ জুনায়েদ বাগদাদী তাঁর ভাগ্নে ও শিষ্য ছিলেন। তিনি ঐশী প্রেম এবং তাওহীদ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তিনি আরেফকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ,আরেফ হলেন সূর্যের ন্যায় পৃথিবীতে আলো বিতরণকারী। আরেফ পৃথিবীর ন্যায় ভাল-মন্দের বোঝা পৃষ্ঠে বহন করেন ,আরেফ পানির ন্যায় অন্তরসমূহের জীবনের মাধ্যম এবং অগ্নির ন্যায় শিখা বিতরণকারী। সেররী 245 অথবা 250 হিজরীতে 98 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
4. হারেস মুহাসেবী: তিনি বসরার অধিবাসী এবং জুনায়েদ বাগদাদীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি মুরাকাবা (ধ্যান) এবং মুহাসাবা (আত্মসমালোচনা) এ উভয় বিষয়েই অধিকতর গুরুত্ব দিতেন বিধায় তাঁকে মুহসেবী বলা হতো। তিনি আহমাদ ইবনে হাম্বলের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল যেহেতু কালামশাস্ত্রের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন সেহেতু কালামশাস্ত্রবিদ হিসেবে হারেস মুহাসেবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এ কারণেই জনসাধারণকে তাঁর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন। হারেস 243 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. জুনায়েদ বাগদাদী: তিনি নাহাভান্দের অধিবাসী ছিলেন। সুফী ও আরেফগণ তাঁকে ‘ সাইয়্যেদুত তায়েফা ’ নামে অভিহিত করেছেন যেমনিভাবে শিয়া ফকীহ্গণ ফিকাহ্শাস্ত্রের পুরোধা হিসেবে শেখ তুসীকে ‘ শাইখুত তায়েফা ’ বলে থাকেন। জুনায়েদ বাগদাদী একজন ভারসাম্যপূর্ণ আরেফ। অনেক আরেফ হতে যেরূপ অসংলগ্ন কথা শোনা যায় তাঁর থেকে তা কখনই শোনা যায়নি। তিনি কখনই সুফীদের পোশাক পরিধান করেননি ;বরং আলেম ও ফকীহ্দের পোশাক পরিধান করতেন। তাঁকে বলা হয়েছিল অন্তত শিষ্যদের কারণে খিরকা (সুফীদের বিশেষ পোষাক) পরিধান করুন। তখন তিনি বলেছিলেন , ‘ যদি পোশাক মানুষকে তৈরি করতে পারে এটি নিশ্চিত হতাম ,তবে প্রয়োজনে লোহার পোশাক পরিধান করতাম। ’ অতঃপর বলেন ,
ليس الإعتبار بالْخرقة إنّما الإعتبار بالْحرقة
‘ খিরকা দ্বারা কার্যসিদ্ধি সম্ভব নয় ,কার্যসাধণের জন্য হিরকা (অন্তরের) অগ্নিশিখার প্রয়োজন। ’
জুনায়েদ বাগদাদী 297 হিজরীতে 90 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
6. যুন্নুন মিসরী: তিনি মিশরের অধিবাসী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ এবং ফিকাহ্শাস্ত্রে মালেক ইবনে আনাসের ছাত্র ছিলেন। জামী তাঁকে সুুফীদের নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম এরফানশাস্ত্রে রহস্যময় প্রতীকসমূহ ব্যবহার শুরু করেন যাতে করে এ পরিভাষাগুলো কেবল আরেফগণই বুঝতে পারেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিটি পরবর্তীতে আরেফদের মধ্যে প্রচলন লাভ করে এবং প্রতীকী অর্থে বিভিন্ন গজলে ও কবিতায় ব্যবহৃত হতে থাকে। কারো কারো মতে নব্য প্লেটোনিক দর্শনের চিন্তাধারা যুন্নন মিসরীর মাধ্যমে এরফান ও তাসাউফে প্রবেশ করছে। যুন্নুন মিসরী 240 হতে 250 হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন।
7. সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তুরী: তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ সুফী। তিনি শুস্তারের অধিবাসী ছিলেন।
আরেফদের মধ্যে যে দলটি নাফসের সঙ্গে সংগ্রামকে মূল বলে ধরেছেন তাঁরা সাহলীল (তাঁর নাম অনুসারে) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যুন্নুন মিসরীর সঙ্গে মক্কায় একবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি 283 অথবা 293 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
8. হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ: তিনি ইরানের শিরাজ প্রদেশের বাইদার অধিবাসী ছিলেন। তবে ইরাকেই জীবন অতিবাহিত করেন । আরেফগণের মধ্যে তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ হয়েছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে অসংলগ্ন ও অবোধগম্য কথা বলার কারণে তাঁকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরের শাসনামলে এ অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেক আরেফই তাঁকে গোপন রহস্য ফাঁস করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কবি হাফেয শিরাজী এ সম্পর্কে বলেছেন ,
‘ বললেন পীর ,বন্ধুকে351 আমার ঝুলানো হয়েছে ফাঁসির কাষ্ঠে
অপরাধ তাঁর ছিল এটাই ,বলেছিল সে গোপন কথা প্রকাশ্যে। ’
কেউ কেউ তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করেছেন। অনেক আরফেই তাঁর ও বায়েজীদ
বাস্তামীর সমালোচনা করে বলেছেন ,তাঁরা বোধশক্তিহীন অবস্থায় এরূপ কুফরী কথা বলেছেন। আরেফগণ তাঁকে শহীদ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তিনি 306 অথবা 309 হিজরীতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।
চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. আবু বাকর শিবলী: তিনি জুনায়েদ বাগদাদীর মুরীদ ও শিষ্য ছিলেন। তিনি খোরাসানের অধিবাসী এবং একজন প্রসিদ্ধ আরেফ। ‘ রাওজাতুল জান্নাত ’ এবং অন্যান্য জীবনী গ্রন্থে তাঁর নিকট হতে অনেক এরফানী কবিতা ও বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী বলেছেন , ‘ এরফানে প্রতীকী পরিভাষার ব্যবহার যুন্নুন মিসরীর মাধ্যমে শুরু হয় এবং জুনায়েদ বাগদাদী এর সুবিন্যস্ত রূপ দেন। পরবর্তীতে শিবলী এ জ্ঞানটির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটান। ’ শিবলী 234 হতে 244 হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে 87 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
2. আবু আলী রুদবারী: তিনি সাসানী বংশোদ্ভূত এবং তাঁর বংশধারা সম্রাট আনুশিরওয়ানে পৌঁছায়। তিনি তাসাউফের ক্ষেত্রে জুনায়েদ বাগদাদীর শিষ্য। তবে আবুল আব্বাস ইবনে শারীহর নিকট ফিকাহ্শাস্ত্র এবং সা ’ য়ালাবের নিকট আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি শরীয়ত ,তরীকত এবং হাকীকতের সমন্বয় সাধনকারী ছিলেন। তিনি 322 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আবু নাসর শিরাজ তুসী: তিনি এরফান ও তাসাউফশাস্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ আল্লুমা ’ র রচয়িতা। তরীকতে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তিত্বই তাঁর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ছাত্র। তিনি 378 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন তাঁর সমাধি মাশহাদ স্ট্রীটে অবস্থিত যা পালয়ান্দুজ পীরের কবর বলে প্রসিদ্ধ।
4. আবুল ফাযল সারখসী: তিনি খোরাসানের অধিবাসী এবং আবু নাসর সিরাজের শিষ্য। তাঁর শিষ্য আবু সাঈদ আবুল খায়ের একজন খুব প্রসিদ্ধ আরেফ। আবুল ফাযল সারাখসী 400 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. আবু আবদুল্লাহ্ রুদবারী: তিনি আবু আলী রুদবারীর ভাগ্নেয়। পৈত্রিকসূত্রে তিনি সিরীয় এবং সে অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ আরেফ। তিনি 369 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
6. আবু তালেব মাক্কী: তাঁর পরিচিতি মূলত এরফানশাস্ত্রে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ কুওয়াতুল কুলুব ’ -এর মাধ্যমে। এ গ্রন্থটি এরফান ও তাসাউফশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর অন্যতম। আবু তালেব মূলত ইরানের জাবাল এলাকার অধিবাসী। তবে যেহেতু দীর্ঘদিন মক্কায় বসবাস করেছেন সেহেতু মাক্কী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 385 অথবা 386 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. শেখ আবুল হাসান খারকানী: তিনি প্রসিদ্ধতম আরেফদের একজন। তাঁর সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে ,তিনি বায়েজীদ বোস্তামীর কবরের নিকটে গিয়ে তাঁর রূহের সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাঁর সমস্যা সমাধান করতেন। মাওলানা রুমী বলেছেন ,
‘ অনেকদিন হলো বায়েজীদের হয়েছে ওফাত
আবুল হাসান পেতে চাইল তাঁর সাক্ষাৎ
কখনো কখনো সতেজ এক মন352 নিয়ে
গিয়ে বসতেন বায়েজীদের কবরের ’ পরে
যখনই পড়তেন তিনি কোন সমস্যায়
গুরুর সমীপে353 পেতেন সমাধান সেথায়। ’
মাওলানা রুমী ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থে তাঁর কথা অনেক বার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে ,প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইবনে সিনা এবং বিশিষ্ট আরেফ আবু সাঈদ আবুল খায়েরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি 425 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
2. আবু সাঈদ আবুল খায়ের নিশাবুরী: তিনি আরেফদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি অনেক চতুষ্পদী কবিতা রচনা করেছেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: ‘ তাসাউফ কি ? ’ তিনি বললেন , ‘ তাসাউফ হলো যা কিছু তোমার মাথায় রয়েছে তা অস্বীকার কর এবং যা কিছু তোমার হাতে রয়েছে তা বিলিয়ে দাও এবং যা কিছু তোমার ওপর আপতিত হয় তা থেকে পলায়ন কর। ’ তাঁর সঙ্গে ইবনে সিনার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একদিন ইবনে সিনা আবু সাঈদের বক্তব্য শোনার জন্য তাঁর মজলিসে যান। আবু সাঈদ আমলের গুরুত্ব ,আল্লাহর আনুগত্য এবং গুনাহের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমরা নিজের কর্মের ওপর নয় ;বরং আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করি-ইবনে সিনা এটি বুঝানোর জন্য নিম্নোক্ত চতুষ্পদী কবিতাটি পাঠ করেন :
‘ আমরা আপনার ক্ষমার প্রতি আকৃষ্ট
তদুপরি করছি আনুগত্য ,হয়েছি গুনাহের প্রতি রুষ্ট
যাকে আপনি করবেন অনুগ্রহ সে-ই পাবে মুক্তি
আপনার ইচ্ছাই সকল কিছুর নির্ধারক শক্তি। ’
আবু সাঈদ ত্বরিত বললেন ,
‘ ওহে! যে সওয়াব অর্জন না করে গুনাহই করেছে অর্জন
অথচ তাঁর অনুগ্রহে মুক্তির আশায় গণিছ ক্ষণ
শুধু আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থেকো না বসে
যদিও তাঁর ইচ্ছাই সকল কিছুর নির্ধারক পরিশেষে। ’
আবু সাঈদ রচিত অপর একটি চতুষ্পদী কবিতা হলো :
‘ আগামীকাল যখন পৃথিবী ধ্বংস হবে
তোমার মর্যাদা তোমার মারেফাত অনুযায়ী হবে
সৎ গুণাবলী অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাও সবে
তোমার অর্জিত গুণাবলীর রূপেই তুমি পুনরুত্থিত হবে। ’
আবু সাঈদ 440 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আবু আলী দাকাক নিশাবুরী: তিনিও শরীয়ত ও তরীকতের একজন সমন্বয়কারী। তিনি একজন মুফাসসির ও ওয়ায়েজ ছিলেন। তিনি মুনাজাতের সময় এত অধিক ক্রন্দন করতেন যে তাঁকে ‘ ক্রন্দনকারী শেখ ’ উপাধি দেয়া হয়েছিল। তিনি 405 অথবা 412 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. আবুল হাসান আলী ইবনে উসমান হিজভিরী গজনভী: তাঁর রচিত ‘ কাশফুল মাহযুব ’ গ্রন্থটি তাসাউফশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি 470 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী: তিনি আরব বংশোদ্ভূত এবং বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর বংশধর। খাজা আবদুল্লাহ্ প্রসিদ্ধ আরেফদের অন্যতম। ইবাদাতের ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর হতে বিভিন্ন চতুষ্পদী কবিতা ,মুনাজাত এবং জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি অনেক বাণী ,কবিতা ও মুনাজাত রেখে গেছেন। যেমন ,
‘ শিশুকালে ছিলে হীন ,যুবাবস্থায় মাতাল ,
বৃদ্ধাবস্থায় হয়েছ অক্ষম ,তাই এখন হয়েছ খোদা উপাসক। ’
‘ মন্দের জবাব দান মন্দের দ্বারা কুকুরের কাজ
ভালোর জবাবে ভালো করা গাধার কাজ ,
আর মন্দের জবাব দান ভালোর দ্বারা খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারীর কাজ। ’
‘ নিজেকে বড় মনে করা ত্রুটি জেনো
নিজেকে উত্তম ভেবে অন্যদের কর হীন
চোখের মণির মতো হও তুমি উদার
তবেই সকলকে দেখবে তুমি নিজেকে না দেখে। ’
খাজা আবদুল্লাহ্ হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। তিনি ‘ হেরাতের পীর ’ নামে প্রসিদ্ধ। 481 হিজরীতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। খাজা আবদুল্লাহ্ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরফানশাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হলো ‘ মানাজিলুস সায়েরীন ’ যা এরফানশাস্ত্রের উত্তম গ্রন্থসমূহের একটি এবং এ শাস্ত্রের ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটির অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।
6. ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী তুসী: তিনি ফিকাহ্শাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি বাগদাদের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের পদ লাভ করেছিলেন ,কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ থেকে দূরে আত্মগোপন করেন। 10 বছর তিনি পরিচিত পরিবেশের বাইরে বায়তুল মোকাদ্দেসের নিকটবর্তী এক স্থানে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় রত থাকেন। এ সময়েই এরফান ও তাসাউফের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত কোন সামাজিক পদ গ্রহণে রাজী হন নি। দীর্ঘ দিন তাসাউফ সাধনার পর তিনি ‘ এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি 505 হিজরীতে তাঁর জন্মস্থান তুসে মৃত্যুবরণ করেন।
ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. আইনুল কুযযাত হামেদানী: তিনি আরেফদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ ছিলেন বলে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ গাজ্জালীর ভ্রাতা বিশিষ্ট আরেফ আহমদ গাজ্জালীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এরফানশাস্ত্রে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর আকর্ষণীয় কবিতাগুলো ভ্রমাত্মক ও অসংলগ্ন কথামুক্ত নয়। ফলে তাঁকে কাফের হিসেবে অভিযুক্ত করে হত্যা করা হয় এবং তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। তিনি 525 অথবা 533 হিজরীতে নিহত হন।
2. সানায়ী গজনভী: তিনি একজন প্রসিদ্ধ এরফানী কবি। তাঁর কবিতাগুলো তাসাউফের গভীর অর্থ বহন করে। মাওলানা রুমী তাঁর ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থে তাঁর অনেক কবিতা বর্ণনা করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধে মৃত্যুবরণ করেন।
3. আহমদ জামী: তিনি ‘ জেন্দে পিল ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রসিদ্ধ আরেফ ও সুফীদের একজন। তাঁর সামাধি ইরানের সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের জামে অবস্থিত।
আল্লাহর ভয় ও রহমতের আশা সম্পর্কিত তাঁর একটি কবিতা হলো :
‘ গর্বিত হয়ো না ,
অনেক প্রসিদ্ধ মানুষের বাহন হয়েছে ভূপাতিত এ কংকরময় ভূমিতে
নিরাশও হয়ো না ,
অনেক সুফী এক রাতে তসবীহ জপে পৌঁছেছেন গন্তব্যে। ’
তিনি অকাতরে দান ও কৃপণতার মধ্যে ভারসাম্যের বিষয়ে তাঁর এক কবিতায় বলেছেন ,
‘ কুঠারের ন্যায় নিজের জন্য পুরোটাই রেখে দিও না
আবার বান্দার ন্যায় সবকিছুই বিলিয়ে দিও না
নিজের জীবনে করাতের মতো হও
নিজের জন্য কিছু রেখে বাকিটা বিলিয়ে দাও। ’
তিনি 536 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
4. আবদুল কাদের জিলানী: তিনি ইরানের উত্তরাঞ্চলের গিলানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বাগদাদে জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। কেউ কেউ তাঁকে বাগদাদের নিকটবর্তী জিল শহরের অধিবাসী বলেছেন। তিনি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তি। কাদেরিয়া সিলসিলার সুফী ধারাটি তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তাঁর কারামত সম্পর্কে অনেক কথা প্রচলিত আছে। তিনি ইমাম হাসান (আ.)-এর বংশধারার একজন সাইয়্যেদ। 560 অথবা 561 হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
5. শেখ রুয বাহান বাকলী শিরাজী: তিনি শেখ শাত্তাহ্ নামে প্রসিদ্ধ। কারণ খুব বেশি ভ্রমাত্মক (শাত্তাহ্) কথা বলতেন। সম্প্রতি তাঁর কিছু কিছু গ্রন্থ প্রাচ্যবিশারদগণ প্রকাশ করেছেন। তিনি 606 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
সপ্তম হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
এ শতাব্দীতে অনেক উচ্চ পর্যায়ের আরেফের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমরা এখানে তাঁদের মৃত্যু সনের ধারাবাহিকতা অনুসারে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি :
1. শেখ নাজমুদ্দিন কোবরা খাওয়ারেজমী: তিনি আরেফদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সুফী ধারার কয়েকটি সিলসিলা তাঁর মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। তিনি শেখ রুয বাহান বাকলী শিরাজীর শিষ্য ও জামাতা। তাঁর অসংখ্য মুরীদ ছিল। তাঁর বিশিষ্ট মুরীদদের একজন হলেন মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর পিতা বাহাউদ্দীন। শেখ নাজমুদ্দীন খাওয়ারেজমের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সময়কালেই মোগলরা হামলা চালায়। মোগলরা এতদঞ্চলে আক্রমণের পূর্বে তাঁর নিকট এ মর্মে পত্র পাঠায় , ‘ আপনি আপনার নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যান। তারপর আমরা আক্রমণ চালাব। ’ তিনি জবাবে বলেন , ‘ আমি এ জনসাধারণের সুখের দিনে তাদের সাথে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেছি। এখন আমি কঠিন সময়ে তাদের ত্যাগ করতে পারব না। ’ অতঃপর তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অতঃপর সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করে শহীদ হন। এটি 616 হিজরী শতাব্দীর ঘটনা।
2. শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার নিশাবুরী: তিনি প্রথম শ্রেণীর আরেফদের একজন। তাঁর বেশ কিছু কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রয়েছে। আরেফ ও সুফীদের জীবনীর ভিত্তিতে রচিত ‘ তাযকিরাতুল আউলিয়া ’ নামক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর জীবনী দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন এবং ইমাম বাকির (আ.)-এর জীবনী দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। প্রাচ্যবিদগণ গ্রন্থটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর রচিত ‘ মানতেকুত তায়ির ’ গ্রন্থটি এরফানশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার।
মাওলানা রুমী ফরিদউদ্দীন আত্তার এবং সানায়ী সম্পর্কে বলেছেন ,
‘ আত্তার ছিলেন তাঁর প্রাণ আর সানায়ী ছিলেন চোখের মনি
আমারা সানায়ী আর আত্তারের অনুসারী পথযাত্রী। ’
অন্যত্র তিনি বলেছেন ,
‘ আত্তার প্রেমের সাত শহর বেড়িয়েছে ঘুরে
আমরা এখনও এক শহরের গলিতে রয়েছি পড়ে। ’
এখানে মাওলানা রুমী সাত শহর বলতে এরফানের সাতটি গন্থব্য ও পর্যায় বুঝিয়েছেন যে সম্পর্কে ফরিদউদ্দীন আত্তার তাঁর ‘ মানতেকুত তায়ির ’ গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন।
মাহমুদ শাবেস্তারী তাঁর ‘ গুলশানে রায ’ গ্রন্থে বলেছেন ,
‘ আমার নগণ্য কাব্য প্রতিভায় আমি লজ্জাবোধ করি না
কারণ আত্তারের ন্যায় কবি তো শত শতাব্দীতেও আসে না। ’
ফরিদউদ্দীন আত্তার শেখ নাজমুদ্দীন কোবরার মুরীদ শেখ মাযদুদ্দীন বাগদাদীর শিষ্য। তিনি তাঁর সমসাময়িক আরেফ কুতুবউদ্দীন হায়দারের নামে প্রসিদ্ধ হায়দারীয়া শহরে সমাহিত হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ফরিদউদ্দীন আত্তারও মোগলদের আক্রমণের সময় নিহত হন।
3. শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী জানজানী: তাসাউফ ও এরফানশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ‘ আওয়ারিফুল মাআরিফা ’ গ্রন্থটি তাঁরই রচিত। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের বংশধর। কথিত আছে ,তিনি প্রতি বছর মক্কা-মদীনায় যিয়ারতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আবদুল কাদের জিলানীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদী এবং কামালউদ্দীন ইসমাঈল ইসফাহানী তাঁর মুরীদ ছিলেন। সাদী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ,
‘ আমার জ্ঞানী মুর্শিদ পীর শাহাব
দু ’ টি উপদেশ দিয়েছেন আমার অন্তরের ’ পর
নিজ প্রবৃত্তির প্রতি কভু কর না সুধারণা
অপরের প্রতি কভু কর না কুধারণা। ’
বিশিষ্ট দার্শনিক শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী যিনি ‘ শেখ এশরাক ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং 581 হতে 590 হিজরীর মধ্যবর্তী সময় হালাবে নিহত হন। তিনি এবং আরেফ শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এক ব্যক্তি নন। আরেফ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী 632 হিজরীতে মৃত্যবরণ করেন।
4. ইবনুল ফারেজ মিশরী: তিনিও প্রথম সারির আরেফদের একজন। আরবী ভাষায় লিখিত তাঁর এরফানী কবিতাসমূহ অতি উচ্চ মানের। তাঁর রচিত কবিতাসমূহ বিভিন্ন স্থানে বারবার ছাপা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কবিতাসমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে নবম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আরেফ আবদুর রহমান জামীও রয়েছেন। ইবনুল ফারেজের আরবীতে রচিত এরফানী কবিতাসমূহ কবি হাফেযের ফার্সীতে রচিত এরফানী কবিতার সমতুল্য । বিশিষ্ট আরেফ মুহিউদ্দীন আরাবী তাঁকে তাঁর কবিতাসমূহ ব্যাখ্যা করে গ্রন্থ রচনার আহ্বান জানালে তিনি বলেন , ‘ আপনার ‘ ফুতুহাতে মাক্কীয়া ’ গ্রন্থটিই আমার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ’ । ইবনুল ফারেজ অধিকাংশ সময়ই এরফানী আবেগে আপ্লুত থাকতেন এবং এ অবস্থায়ই কবিতা রচনা করতেন। তিনি 632 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. মুহিউদ্দীন আরাবী হাতেমী তায়ী আন্দালুসী: তিনি হাতেম তায়ীর বংশধর। তিনি আন্দালুসে (স্পেনে) জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের অধিকাংশ সময় মক্কায় এবং সিরিয়ায় অতিবাহিত করেন। তিনি 6ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর আরেফ আবু মাদিন মাগরেবী আন্দালুসীর শিষ্য। তাঁর তরীকাটি শেখ আবদুল কাদের জিলানী হতে উৎসারিত।
মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী এরফানশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ত্ব। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরেফদের কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। এ কারণেই তাঁকে ‘ শেখে আকবার ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ইসলামী এরফান-এর উৎপত্তিকাল হতে শতাব্দীকাল ধরে তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে (প্রতি শতাব্দীর আরেফগণের মাধ্যমে ধারাবাহিক পূর্ণতা অর্জন করে) 7ম হিজরী শতাব্দীতে মুহিউদ্দীন আরাবীর মাধ্যমে বৈপ্লবিকভাবে বিকশিত হয়ে পূর্ণতার শিখরে পৌঁছায়। মুহিউদ্দীন আরাবী এরফানশাস্ত্রকে নব্য পর্যায়ে উত্তরণ ঘটান। তিনি এরফানশাস্ত্রের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়ে এর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেন। তাঁর পরবর্তী যুগের এরফানশাস্ত্র তাঁরই রেখে যাওয়া ফসল। তিনি তাঁর সময়ের এক আশ্বর্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যের কারণেই তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিপরীতমুখী বক্তব্য এসেছে। কেউ কেউ তাঁকে ‘ আরেফকুল শিরোমণি ’ আবার কেউ কেউ তাঁকে কাফেরও বলেছে। কেউ কেউ তাঁকে দীনকে পুনর্জীবিতকারী ,আবার কেউ কেউ তাঁকে দীনের হত্যাকারী বলেছে। দর্শনের বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব মোল্লা সাদরা মুহিউদ্দীন আরাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মুহিউদ্দীন ইবনে সিনা এবং ফারাবী থেকে অনেক ঊর্ধ্বের ব্যক্তিত্ব। তিনি দু ’ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ত্রিশের অধিক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে । তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ‘ ফুতুহাতে মাক্কীয়া ’ যাকে এরফানশাস্ত্রের এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। তাঁর রচিত ‘ ফুসুসুল হেকাম ’ এরফানশাস্ত্রের গভীর অর্থবহ ,সূক্ষ্ম ও যথার্থ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি এতটা গভীর অর্থবহ যে ,প্রতি শতাব্দীতে সম্ভবত দু ’ তিন ব্যক্তির অধিক ব্যক্তিত্ব তা বুঝতে সক্ষম হন নি। মুহিউদ্দীন আরাবী 638 হিজরীতে দামেশ্কে মৃত্যুবরণ করেন। সিরিয়ায় তাঁর মাজার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।
6. সাদরুদ্দীন মুহাম্মদ কৌনাভী: তিনি মুহিউদ্দীন আরাবীর স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান এবং তাঁর শিষ্য ও মুরীদ। তিনি মাওলানা রুমী এবং খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর সময়সাময়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে খাজা নাসিরউদ্দীন তুসীর পত্রালাপ হতো এবং নাসিরুদ্দীন তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন।
মাওলানা রুমীর কৌনাভীতে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মাওলানা রুমী তাঁর পেছনে নিয়মিত নামাজ পড়তেন। কোন কোন বর্ণনা মতে মাওলানা রুমী সাদরুদ্দীন কৌনাভীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর নিকট হতেই মুহিউদ্দীন আরাবীর এরফানশাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ করেন। কথিত আছে ,একদিন মাওলানা রুমী কৌনাভীর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর আসন ছেড়ে দিয়ে তাঁকে সেখানে বসতে বলেন। মাওলানা রুমী বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন , ‘ আপনার আসনে আমি বসলে আল্লাহর নিকট কি জবাব দেব ? ’ সাদরুদ্দীন কৌনাভী তখন আসনটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন , ‘ যে আসন তোমার জন্য মানায় না সে আসন আমার জন্যও মানায় না। ’
মুহিউদ্দীন আরাবীর চিন্তা ও কর্মধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী হলেন সাদরুদ্দীন কৌনাভী। সম্ভবত তিনি না থাকলে মুহিউদ্দীন আরাবীর চিন্তাধারা বোধগম্য হতো না। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ গত ছয় শতাব্দী ধরে ইসলামী এরফান ও দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্যগ্রন্থ। সাদরুদ্দীন কৌনাভীর প্রসিদ্ধ তিনটি গ্রন্থ হলো যথাক্রমে মিফতাহুল গাইব ,নুসুস এবং ফুকুক। কৌনাভী 672 হিজরীতে (যে বছর মাওলানা রুমী এবং খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী মৃত্যুবরণ করেন) অথবা 673 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
7. মাওলানা জালালউদ্দীন মুহাম্মদ বালখী রুমী: তিনি মৌলাভী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থটি বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি আরেফদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি হযরত আবু বকরের বংশধর। তাঁর রচিত ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থটি জ্ঞান ,প্রজ্ঞা ,আত্মিক অবস্থার সূক্ষ্ম দিক নির্দেশক এবং এরফানের উচ্চতর ভাবধারা সম্বলিত। তদুপরি এর সামাজিক দিকটিও যথার্থ। তিনি ইরানের প্রথম সারির কবিদের একজন। তিনি মূলত
আফগানিস্তানের বালখের অধিবাসী। শৈশবেই তিনি পিতার সাথে বালখ হতে মক্কায় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হন। নিশাবুরে তিনি শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মক্কায় যিয়ারত সম্পন্ন করে তিনি পিতার সঙ্গে কৌনিয়ায় যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। মাওলানা রুমী একজন প্রথম সারির আলেম ছিলেন এবং দীন শিক্ষাদান করতেন। সমাজে তাঁর বিশেষ অবস্থান ছিল। একদা যখন প্রসিদ্ধ আরেফ শামস তাবরিযীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সবকিছু ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত গজল ও কবিতাগুলো ‘ দিওয়ানে শামস ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর ‘ মাসনভী ’ গ্রন্থে বারবার শামসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বিয়োগ ব্যথার শোককে কবিতায় তুলে ধরেছেন। মাওলানা রুমী 672 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
8. ফাখরুদ্দীন ইরাকী হামেদানী: তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও গজল রচয়িতা এবং সাদরুদ্দীন কৌনাভী ও শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য ছিলেন। তিনি 688 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
অষ্টম হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. আলাউদ্দৌলা সেমনানী: তিনি প্রথম জীবনে বিচার কার্যের সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে তা ত্যাগ করেন এবং তাসাউফের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরফানশাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কিছু মত রয়েছে যা এরফানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি 736 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি খাজুয়ে কেরমানী তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর প্রসংশায় নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেছেন :
‘ যে কেউ আলীর পথে নিজেকে গড়বে
খিজিরের ন্যায় প্রাণের উৎসের সন্ধান লাভ করবে।
শয়তানী প্ররোচণা হতে যদি হতে পার মুক্ত
আলাউদ্দৌলা সেমানীর সঙ্গে হতে পারবে যুক্ত। ’
2. আবদুর রাজ্জাক কাশানী: তিনি এ শতাব্দীর একজন বিশেষজ্ঞ আরেফ। তিনি মুহিউদ্দীন আরাবীর ‘ ফুসুসুল হিকাম ’ এবং খাজা আবদুল্লাহর ‘ মানাজিলুস সায়েরীন ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘ রাউযাতুল জান্নাত ’ গ্রন্থের লেখক তাঁর গ্রন্থে শেখ আবদুর রাজ্জাক লাহিযীর জীবনী আলোচনায় আবদুর রাজ্জাক কাশানী সম্পর্কে শহীদে সানীর প্রশংসাবাণী উল্লেখ করেছেন। মুহিউদ্দীন আরাবী কর্তৃক উপস্থাপিত এরফানের তাত্ত্বিক বিষয়ে আবদুর রাজ্জাক কাশানীর সঙ্গে আলাউদ্দৌলা সেমনানীর আলোচনা ও বিতর্ক হতো। তিনি 735 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
3. খাজা হাফেয শিরাজী: হাফিযের বিশ্বপরিচিতি থাকলেও তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। যতটুকু জানা যায় ,তিনি একজন আলেম ,আরেফ ,হাফেয এবং কোরআনের মুফাসসির ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতাসমূহে পুনঃপুন এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
‘ হে হাফেয!
তোমার কবিতা হতে আকর্ষণীয় কোন কবিতা আমি দেখিনি
শপথ ঐ কোরআনের যা রেখেছি এ সিনায়
তোমার প্রেমের সুর বাজে সকল হাফেযের বীণায়
তোমার ন্যায় চৌদ্দ নিয়মে কোরআন পাঠ কেউ শিখেনি
বিশ্বের কোন হাফেযই আমার ন্যায় একত্র করেনি
সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার কথাসমূহ থেকে কোরআনের বাণী। ’
তিনি তাঁর কবিতাসমূহে তরীকতের পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কে অসংখ্য কথা বললেও তাঁর মুর্শিদ কে ছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায় না। তাঁর এরফানী কবিতাসমূহ এতটা উচ্চ পর্যায়ের যে ,খুব কম ব্যক্তিই এর গভীর অর্থ অনুধাবনে সক্ষম। তাঁর পরবর্তী যুগের সকল আরেফই স্বীকার করেছেন ,তিনি এরফানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব হাফেযের কবিতাসমূহের ব্যাখ্যা লিখেছেন। যেমন নবম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক মুহাক্কেক জালালউদ্দীন দাওয়ানী হাফেযের একটি কবিতার নিম্নোক্ত চরণ দু ’ টিকে ব্যাখ্যা করে পুস্তিকা রচনা করেছেন :
‘ সৃষ্টির কলম কোন ভুলই করেনি জগৎ সৃষ্টিতে
ধন্যবাদ ঐ ত্রুটি আবৃতকারী পবিত্র দৃষ্টিকে। ’
হাফেয 791 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।354
4. শেখ মাহমুদ শাবেস্তারী: তিনি এরফানের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের একটি কাব্যগ্রন্থ ‘ গুলশানে রায ’ -এর রচয়িতা। বলা যেতে পারে ,এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। গ্রন্থটির অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ সব ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে সম্ভবত শেখ মুহাম্মদ লাহিযীর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সর্বোত্তম। তিনি 720 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
5. সাইয়্যেদ হায়দার আমোলী: তিনি বিশিষ্ট দার্শনিকদের একজন ,তাঁর রচিত ‘ জামেউল আসরার ’ গ্রন্থটি এরফানশাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয়ের একটি মূল্যবান গ্রন্থ যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো মুহিউদ্দীন আরাবীর ‘ ফুসুস ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ নাসসুন নুসুস ’ । তিনি প্রসিদ্ধ ফকীহ্ আল্লামা হিল্লীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সময় জানা যায়নি।
6. আবদুল করিম যিলী: তিনি ‘ আল ইনসানুল কামিল ’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানবের বিষয়টি সর্বপ্রথম মুহিউদ্দীন আরাবী উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে এই বিষয়টি ইসলামী এরফানশাস্ত্রে বিশেষ স্থান লাভ করে। মুহিউদ্দীন আরাবীর শিষ্য সাদরুদ্দীন কৌনাভীর ‘ মিফতাহুল গাইব ’ গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমার জানা মতে দু ’ জন আরেফ এ নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের একজন হলেন আবদুল করিম যিলী এবং অপর জন হলেন আজিজউদ্দীন নাসাফী যিনি সপ্তম হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন আরেফ। তিনি মাত্র 38 বছর বয়সে 805 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন ।
নবম হিজরী শতাব্দীর সুফী ও আরেফগণ
1. শাহ নেয়ামতউল্লাহ্ ওয়ালী: তিনি হযরত আলী (আ.)-এর বংশধর এবং প্রসিদ্ধ আরেফদের একজন। বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধতম তাসাউফের সিলসিলা হলো নেয়ামতউল্লাহী । তাঁর মাজারটি কেরমানের মাহান শহরে অবস্থিত। তিনি 95 বছর বয়সে 827 অথবা 834 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সঙ্গে কবি হাফেয শিরাজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর প্রচুর এরফানী কবিতা রয়েছে।
2. সায়েনউদ্দীন আলী তারাকেহ ইসফাহানী: তিনি বিশিষ্ট আরেফদের অন্যতম। মুহিউদ্দীন আরাবীর এরফানী ধারার ওপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তাঁর রচিত ‘ তামহিদুল কাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থটি এরফানশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।
3. মুহাম্মদ ইবনে হামযা ফানারী রুমী: তিনি তুরস্কের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর ‘ মিসবাহুল উনস ’ গ্রন্থের কারণে এরফানশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর এ গ্রন্থটি সাদরুদ্দীন কৌনাভী রচিত ‘ মিফতাহুল গাইব ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
মুহিউদ্দীন আরাবী এবং সাদরুদ্দীন কৌনাভীর গ্রন্থসমূহ ব্যাখ্যা করা সহজ কাজ নয়। তাঁর পরবর্তী যুগের আরেফগণ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের যথার্থ মূল্য দিয়েছেন।
4. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ লাহিযী নূরবাখশী: তিনি বিশিষ্ট দার্শনিক মীর সাদরুদ্দীন দাশতকী এবং আল্লামা দাওয়ানীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তিনি মাহমুদ শাবেস্তারীর ‘ গুলশানে রায ’ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। তিনি শিরাজের অধিবাসী ছিলেন। কাজী নুরুল্লাহ্ তাঁর ‘ মাজালিসুল মুমিনীন ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,সাদরুদ্দীন দাশতকী এবং আল্লামা দাওয়ানী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ইবনে ফাহাদ হিল্লীর ছাত্র সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নূরবাখশের শিষ্য ছিলেন। লাহিযী ‘ গুলশানে রায ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থের 689 পৃষ্ঠায় তাঁর তাসাউফের সিলসিলাটি তাঁর শিক্ষক সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নূরবাখশের মাধ্যমে মারুফ কুর্খী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং যেহেতু মারুফ কুর্খী ইমাম রেযার মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষা লাভ করেছিলেন সেহেতু এ সিলসিলাটি রাসূল (সা.)-এ পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেছেন। তাই তিনি এ সিলসিলাকে ‘ স্বর্ণ নির্মিত সিলসিলা ’ (সিলসিলাতুয যাহাব) বলে অভিহিত করেছেন।
‘ গুলশানে রায ’ গ্রন্থটির যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তা এরফানের উচ্চ পর্যায়ের একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি এর রচনাকাল 877 হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সময় আমাদের জানা নেই।
5। নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী: তিনি আরব বংশোদ্ভূত এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ্ হাসান শাইবানীর বংশধর। জামী একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁকে ফার্সী সাহিত্যের সর্বশেষ বড় এরফানী কবি বলা হয়। প্রথম জীবনে তাঁর ছদ্ম নাম ছিল দাশতী ,কিন্তু পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে তাঁর জন্মস্থান জামের (মাশহাদের নিকটবর্তী একটি শহর) নামানুসারে জামী নাম রাখেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ,
‘ জন্ম যেহেতু জামে আমার ,অধিবাসী জামের
মুরীদ আমি জামের অধিবাসী শাইখুল ইসলামের।355
এ কথাই তুলে ধরেছি আমার কবিতায়
হয়েছি আমি জামী দু ’ অর্থে তাই। ’
জামী আরবী ব্যাকরণ (সারফ ও নাহু) ,উসূল ও ফিকাহ্শাস্ত্র ,যুক্তিবিদ্যা ,দর্শন এবং এরফানসহ জ্ঞানের বিভিন্নি শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।
তন্মধ্যে মুহিউদ্দীন আরাবীর ‘ ফুসুসুল হিকাম ’ ,ফাখরুদ্দীন ইরাকীর ‘ লোমাআত ’ ,ইবনে ফারেযের ‘ তাইয়্যা ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ,শেখ সাদীর ‘ গুলিস্তান ’ গ্রন্থের ধাঁচে ‘ বাহরেস্তান ’ এবং ‘ লাওয়াইহ ’ নামে দু ’ টি গ্রন্থ ,রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় রচিত ‘ শারহে কাসীদায়ে বুরদাহ্ ’ ,ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)-এর প্রশংসায় রচিত কবি ফারাযদাকের কাসীদায়ে মহিমিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং আরেফদের জীবনী অবলম্বনে ‘ নাফাহাতুল উনস ’ উল্লেখযোগ্য। তিনি নকশাবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দীন নকশবন্দের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহাউদ্দীন নকশবন্দের তরীকার অনুসারী হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে বাহাউদ্দীন নকশবন্দ হতে অধিক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত। যেহেতু আমরা এরফানের সাংস্কৃতিক ধারার ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি-তরীকতী ধারা নিয়ে নয়-তাই আবদুর রহমান জামীর নাম এখানে আসলেও তাঁর পীরের নাম এখানে আসেনি। তিনি 898 হিজরীতে 81 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
এতক্ষণ আমরা এরফানশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল হতে নবম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। নবম হিজরী শতাব্দীর পর থেকে এরফানশাস্ত্র ভিন্নরূপ লাভ করেছে বলে আমরা মনে করি। এরফানশাস্ত্রের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং তাসাউফ বিষয়ক ধারার বিভিন্ন সিলসিলার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বগণের প্রায় সকলেই নবম হিজরী শতাব্দীর পূর্বের। এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :
প্রথমত এর পরবর্তী সময়ের সুফী ও আরেফগণ পূর্ববতীদের ন্যায় ততটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নন। সম্ভবত এর কারণ হলো এর পরবতী সময়ে তাসাউফ আচারসর্বস্ব ও বাহ্যিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদআত প্রচলিত হয়।
দ্বিতীয়ত এর পরবর্তী সময়ের আরেফদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যায় মুহিউদ্দীন আরাবীর এরফান তত্ত্বের ওপর অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও তাসাউফের বিভিন্ন সিলসিলা ও ধারার কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যেমন সাদরুল মুতাআল্লেহীন শিরাজী (মৃত্যু 1091 হিজরী) ,তাঁর ছাত্র ফায়েয কাশানী (মৃত্যু 1391) এবং তাঁর ছাত্রের ছাত্র কাজী সায়ীদ কুমী তাঁদের সমকালীন প্রসিদ্ধ সুফী ব্যক্তিবর্গ থেকে মুহিউদ্দীন আরাবীর এরফান তত্ত্বের ওপর অধিকতর জ্ঞান রাখতেন ,অথচ এই ব্যক্তিবর্গ তাসাউফের কোন ধারারই অন্তুর্ভুক্ত নন। বর্তমান সময়েও প্রসিদ্ধ অনেক আরেফ তাসাউফের কোন ধারার অনুসারী না হয়েও এরফানশাস্ত্রের ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ,যেমন গত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম আগা মুহাম্মদ রেযা হাকিম কামশেহী এবং আগা মির্জা হাশেম রাশতী।
মোটামুটিভাবে বলা যায় ,মুহিউদ্দীন আরাবী এবং সাদরুদ্দীন কৌনাভীর মাধ্যমে এরফান দার্শনিক ভিত্তি লাভ করে এবং এর তাত্ত্বিকতার বীজ বপিত হয়। সম্ভবত মুহাম্মদ ইবনে হামযা ফানারী এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু দশম হিজরী শতাব্দীর পর থেকে যে সকল ব্যক্তি এরফানশাস্ত্রের ওপর বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন তাঁরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এরফানী পথের পরিব্রাজক ছিলেন না নতুবা পরিব্রাজক হলেও প্রচলিত সুফী তরীকার কোন সিলসিলারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বিষয়টি স্পষ্ট।
তৃতীয়ত দশম হিজরী শতাব্দীর পর থেকে শিয়া বিশ্বে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব ও দলের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা এরফানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরিব্রাজক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং এরফানের পথ সর্বোত্তম উপায়ে পরিক্রমণ করেছিলন। যদিও তাঁরা এ ক্ষেত্রে তাসাউফ সংক্রান্ত ধারার কোন সিলসিলারই অন্তুর্ভুক্ত ছিলেন না ,এমনকি তাসাউফের পূর্ববর্তী তরীকাসমূহের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচক ছিলেন।
এ দলটির একটি বিশেষত্ব হলো তাঁরা সকলে যেহেতু ফিকাহ্শাস্ত্রের ওপর অভিজ্ঞ ছিলেন তাই তাঁদের এরফানী পথ পরিক্রমও এর সাথে সঙ্গতিশীল ছিল। এই ধারার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ এখানে না থাকায় তা থেকে বিরত থাকছি।
পরিশেষে বল যায় ,ইসলামী সংস্কৃতির এরফানী ধারাটি এর অন্যান্য ধারার মতই সারা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপৃত ছিল। স্পেন ,মিশর ,সিরিয়া ও রোম হতে খাওয়ারেজম পর্যন্ত এর শাখা বিস্তৃত ছিল এবং এ শাস্ত্রে ইরানীদের অবদান অন্যান্যদের থেকে নিশ্চিতভাবেই অধিক ছিল। আরেফ ও সুফীদের প্রথম সারির ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই যেমন ছিলেন ইরানী তেমনি আবার অনেকেই অ-ইরানী।
শিল্প ও সাহিত্য
এতক্ষণ জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিষয়ে আমরা যা আলোচনা করলাম তাতে ইসলামে ইরানীদের চিন্তাগত অবদান ফুটে উঠেছে। ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার বিকাশে ইরানীরা যে অবদান রেখেছিল তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এখন আমরা ইসলামের শিল্পকলা ও সাহিত্যে ইরানীদের অবদানের বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরব। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে ইরানীদের অবদান অন্য সকল ক্ষেত্র হতে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে উত্তমরূপে তুলে ধরতে সক্ষম। কারণ এ ক্ষেত্রটির সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসার সম্পর্ক অধিকতর। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ,শৈল্পিক সৃষ্টিসমূহ মানুষের গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কারো নিকট থেকে মহাসৃষ্টি আদায় করা সম্ভব নয়। তাই ভালবাসা ও ঈমানই পারে শুধু মহাসৃষ্টি করতে। চিন্তাগত মহাসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তবে শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি আরো স্পষ্ট। ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে যেমন ইরানীদের মহাসৃষ্টি রয়েছে তেমনি সাহিত্য ও শিল্পকলাতেও রয়েছে।
ইসলামী যুগে স্থাপত্য শিল্প ,চিত্র শিল্প ,ক্যালিগ্রাফি ,স্বর্ণ-কারুকার্য শিল্প ,অঙ্গুরি শিল্প ,মোজাইক শিল্প ,লৌহ শিল্প প্রভৃতিতে ইরানীরা যে সৃষ্টিশীল অবদান রেখেছে তার অধিকাংশই ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত।
এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত। কারণ বিষয়টি আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের দাবি রাখে।
এ মহাসৃষ্টিসমূহ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদ ,পবিত্র স্থান ,মাদ্রাসা ,কোরআন ,দোয়াগ্রন্থসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টি যেমন মসজিদ ,মাদ্রাসা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের স্থাপত্যকর্মে ফুটে উঠেছে তেমনি বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে স্বর্ণলিপি ,অঙ্গুরি ও মোজাইকেও তা পরিদৃষ্ট হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে (এমনকি ইসলামী বিশ্বের বাইরেও অমুসলিম দেশসমূহের জাদুঘরেও) কোরআনের যেসব অনুলিপি রয়েছে তা এ ক্ষেত্রে ইরানীদের শিল্পমনস্কতা ও তাদের অন্তরে বিদ্যমান ইসলামের প্রতি ভালবাসাকে তুলে ধরেছে।
ইরানীরা ইরানের বাইরে ও অন্যান্য স্থানে ইসলামী শিল্পকলাতে ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। বিশ্বের অমুসলিম বিভিন্ন দেশ যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যলঘু ,যেমন ভারত ও চীনেও ইরানীরা এমন অনেক মহাকীর্তি সৃষ্টি করেছে যা ইরানীদের ইসলামপ্রেম ও নিষ্ঠাকেই প্রমাণ করে। এ বিষয়ে গবেষণার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।
অন্য যে ক্ষেত্রটিতে ইরানীরা তাদের রুচি ও অনুভূতির স্বাক্ষর রেখেছে তা হলো ফার্সী ভাষার মাধ্যমে ইসলামের উপস্থাপন। ইরানী কবি ,সাহিত্যিক ,আরেফ ও বাগ্মী আলেমগণ ইসলামের প্রকৃত বর্ণনাকে ফার্সীর অলংকৃত পোশাক পরিয়ে সর্বোত্তম রূপে উপস্থাপন করেছেন ;ইসলামের অভ্যন্তরীণ রূপকে রূপকভাবে প্রতিমূর্ত করেছেন। তাঁরা কোরআনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়কে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় রূপে কাব্য আকারে উপস্থাপন করেছেন। মাওলানা রুমীর ‘ মাসনভী ’ এর সর্বোত্তম উদাহরণ।
দারী ফার্সী (ইসলাম পরবর্তী ইরানী ফার্সী) ইসলামে যে আবদান রেখেছে তা স্বতন্ত্রভাবে গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে কেউ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন ,এ ভাষাটি ইসলামের আবির্ভাবের পরে বারোশ ’ বছরের অধিক সময় ধরে ইসলামের সেবাতেই যেন নিয়োজিত ছিল।
কেউ যদি শুধু ইসলামের তাওহীদ ,কোরআন ,নবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রশংসায় রচিত ফার্সী ভাষায় বিদ্যমান উচ্চমানের কবিতাসমূহ নিয়েই গবেষণা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ,এর পরিমাণ কয়েক খণ্ড পুরু গ্রন্থের সমান। ফার্সী ভাষায় বিদ্যমান ইসলামের রূপ বর্ণনাকারী বিভিন্ন গজল ,কাহিনী ,উপদেশমূলক গল্পসমূহ সামনে রাখলে এর পরিমাণ হবে তার কয়েকগুণ।
গত বারোশ ’ শতাব্দী ধরে ফার্সী সাহিত্য ,কোরআন ও হাদীসের বাণী ও ভাবধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফার্সী ভাষায় বর্ণিত বিভিন্ন উপদেশ বাণী ও এরফানী গভীর তত্ত্বসমূহ কোরআন ও হাদীস হতেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েই তা বিকশিত হয়েছে।
দারী ফার্সীর সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির শত্রুতা এ কারণেই যে ,এ ভাষাটি ইসলামী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির শক্তিশালী উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তাঁরা জানেন এ ভাষার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত ইসলামকে পরাভূত করা যাবে না। ফার্সী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আলোচনার গুরুদায়িত্বটি বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। কারণ এ বিষয়ে তাঁরাই অধিক যোগ্য।
দু ’ শতাব্দীর নীরবতা
সম্মানিত পাঠকগণ! এ গ্রন্থের তৃতীয় আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে তা হলো ইরানীরা উদারতা ,মহত্ত্ব ও কৃতজ্ঞচিত্ত নিয়ে ইসলামের প্রতি অনুগত হয়েছিল এবং ইসলামের মধ্যে তাদের প্রকৃতি ও আত্মিক চাহিদারই প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি। ইরানীদের নিকট ইসলাম যেন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির নিকট সুস্বাদু খাদ্যের মতো ছিল। ইরানীরা তৃষ্ণার্ত ছিল এবং ইসলাম যেন তাদের জন্য সুপেয় পানি এনে দিয়েছিল। ইসলামপূর্ব ইরানী ভৌগোলিক ও সময়গত সামাজিক অবস্থান ও ইরানীদের প্রকৃতি ইসলামের প্রতি ইরানীদের আকৃষ্ট করেছিল এবং তা তাদের জীবনসঞ্চারে শক্তি দিয়েছিল । পরবর্তীতে ইরানীরা নিজেদের জীবন ও শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিবেদিত করেছিল।
আমরা জানি ,41 হিজরী হতে 123 হিজরী পর্যন্ত প্রায় একশ ’ বছর উমাইয়্যারা মুসলিম বিশ্বে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। ইসলাম জাতি ও বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের যে জাহেলী রীতির অবসান ঘটিয়েছিল উমাইয়্যারা তা পুনর্জীবিত করেছিল। তাদের রাজনীতি ছিল জাতিগত বৈষম্যকেন্দ্রিক। তারা আরবদের মধ্যে পার্থক্য করত। বিশেষত ইরানীদের সাথে উমাইয়্যাদের আচার অন্যান্য জাতি হতে নিকৃষ্টতর ছিল। এর প্রকৃত করণ হলো হযরত আলী (আ.)-এর প্রতি ইরানীদের বিশেষ ভালবাসা। যেহেতু হযরত আলীর রাজনীতি ইসলামের জাতি-বর্ণ ও শ্রেণীহীন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উমাইয়্যা বা আরব ও কুরাইশ হিসেবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দেখিয়ে ক্ষমতার ক্ষেত্রে লাভবান হতো সেহেতু তারা আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। এ কারণেই আলী (অ.)-এর অনুসারী আরব ,ইরানী ,আফ্রিকীয় সকলেই তাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে অন্যদের হতে ইরানীরাই বেশি নির্যাতিত হয়েছে।
132 হিজরীতে যখন আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসেন তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। খলীফা মুতাসিম বিল্লাহর ক্ষমতা হারানোর পূর্ব পর্যন্ত আব্বাসীয়দের নীতি ছিল আরবদের পরিবর্তে ইরানীদের পৃষ্টপোষকতা ও শক্তিশালী করা। খলীফা মুতাসিমের সময়কালে তুর্কীরা ইরানীদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আব্বাসীয় শাসনের প্রথম একশ ’ বছর ইরানীদের স্বর্ণযুগ ছিল। আব্বাসীয় শাসকদের বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী ,যেমন বার্মাকী (বালখের সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান ;পরবর্তীতে তাঁরা মুসলমান হন) এবং ফাযল ইবনে সাহল সারখসী (যুররিয়াসাতাইন) খলীফার পর সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন।
আব্বাসীয় শাসনের প্রথম শতাব্দীতে ইরানীরা স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিল না ;বরং রাজনৈতিকভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীন হিসেবে স্বাচ্ছন্দে কাজ করত। কিন্তু এক শতাব্দী পর হতে যখন তাহেরিয়ান বংশ খোরাসানের ক্ষমতা লাভ করে ,তখন থেকে ইরানীরা মোটামুটি স্বাধীন হয়ে পড়ে এবং বিশেষভাবে সাফারিয়ানদের শাসনামলে ইরানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।
অবশ্য এ শাসকবর্গের স্বাধীন ক্ষমতা থাকলেও আব্বাসীয় শাসনামলের শেষ সময় পর্যন্ত নৈতিকভাবে তাঁরা আব্বাসীয় খলীফাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইরানের জনসাধারণ মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খলীফাদের বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ইরানী শাসক খলীফার পক্ষ হতে অভিষিক্ত না হতেন ততক্ষণ তারা তা শরীয়তসম্মত মনে করত না। সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে যখন আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে তখন অভিষিক্ত হওয়ার এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। আব্বাসীয় শাসনের পতনের পর উসমানী শাসকরা ইরানের বাইরে অন্যান্য স্থানে নৈতিক প্রভাব রাখলেও ইরানে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। এর কারণ হলো ইরানী জনসাধারণের শিয়া প্রবণতা এবং উসমানী খিলাফতকে সঙ্গত মনে না করা। কোন কোন প্রাচ্যবিদ ,যেমন ব্রিটিশ লেখক সার্জন ম্যালকম ইরানে ইসলামের আবির্ভাবের সময়কাল হতে ইরানের স্বাধীন ক্ষমতা লাভের সময়কাল পর্যন্ত (প্রথম হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) ‘ ইরানীদের নীরবতা ও দাসত্বের যুগ ’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ মত অনেক ইরানীকে প্রভাবিত করেছে।
যদি আমরা বিষয়টিকে সার্জন ম্যালকমের দৃষ্টিতে দেখি অর্থাৎ এ দু ’ শতাব্দীতে ইরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ে নজীরবিহীন যে পরিবর্তন হয়েছিল এবং তাদের জন্য এটি কতটা কল্যাণকর হয়েছিল সে বিষটিকে উপেক্ষা করে ইরানের পূর্ববর্তী শাসকবর্গের দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখি তাহলে এ সময়কালকে ‘ নীরবতার যুগ ’ বলতে পারি।
যদি আমরা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও আবু মুসলিম খোরাসানীদের আদর্শ হিসেবে ধরি ,যাঁদের একজন 1 লক্ষ 20 হাজার লোক হত্যা করেছিলেন এবং অপরজন 6 লক্ষ লোক ,সে ক্ষেত্রে কোন গোঁড়া আরবের ন্যায় জাতীয়তাবাদের প্রতীক হাজ্জাজের হাতে কেন এই 6 লক্ষ লোক নিহত হলো না সেজন্য আফসোস করতে পারি । সেরূপ আমাদেরও আফসোস হতে পারে ,আবু মুসলিম খোরাসানী কেন ইরানী হিসেবে আরো 1 লক্ষ 20 হাজার লোক হত্যা করতে পারলেন না। যদি তা করতে পারতেন তবে তিনিও আরব হাজ্জাজের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারতেন ,কিন্তু তা যখন হয়নি তাহলে নিশ্চয় এ দু ’ শতাব্দী ইরানীদের নীরবতার যুগ ।
কিন্তু ইরানের সাধারণ মানুষের অর্থাৎ কর্মকার ,চর্মকার ,শ্রমিক যাদের মধ্য হতে সীবাভেই ,আবু হানিফা ,আবু ওবায়দা ,বনী শাকের ,বনী নৌবাখত এরূপ অনেক ব্যক্তিত্ব ও বংশের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের দৃষ্টিতে দেখি তবে দেখব এ দু ’ শতাব্দী ইরানীদের জোশ ,উদ্দীপনা ,সুর ও ছন্দের যুগ ছিল। কারণ তারা এ সময়েই পেরেছিল নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ও স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতা করতে। যেন ইরানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত তারা জ্ঞান ,সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে অন্যান্য জাতির ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছিল। তারা তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে স্বভূমি ও ব্যক্তিসত্তার সম্মানকে চির উন্নত ও স্থায়ী করতে পেরেছিল।
এই দু ’ শতাব্দীতেই ইরানীরা জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে মানবিক ও বিশ্বজনীন এক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এ আদর্শের সত্তাকে তারা স্থান ,কালের ঊর্ধ্বে এক ঐশী সত্য হিসেবে বুঝতে পেরেছিল। কোরআন ও ইসলামের বিশ্বজনীন ভাষা যা কোন বিশেষ জাতির জন্য নয় বরং একটি ধর্মের ভাষা ,তাকে নিজ জাতীয় ভাষার ওপর প্রধান্য দিয়েছিল।
আশ্চর্যের বিষয় হলো এরা বলে থাকে দু ’ শতাব্দীতে ইরানীরা বাকরুদ্ধ হয়েছিল ,শুধু তরবারীই তাদের কথা বলাতো।
প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্যের অর্থ আমার বোধগম্য নয়। তবে কি জ্ঞান ও সাহিত্যের ভাষা কোন ভাষা নয় ? সীবাভেইয়ের সাহিত্যে ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের মহাগ্রন্থটি (যেটি টলেমারী ‘ ম্যাজেস্টি ’ এবং অ্যারিস্টটলের ‘ যু্িক্তবিদ্যা ’ গ্রন্থের সমমানের বলা যেতে পারে) কি এ সময়েই রচিত হয়নি ? ইবনে কুতাইবার ‘ আদাবুল কাতিব ’ নামক মহাসৃষ্টিটি কি এ সময়েই রচিত হয়নি ? ব্যাকরণ সম্পর্কিত সৃষ্টি কি ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ?
সম্ভবত তাঁরা বলবেন ,এসব গ্রন্থ তো আরবী ভাষায় রচিত হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হলো ,কেউ কি ইরানীদের বাধ্য করেছিল আরবী ভাষায় মহাসৃষ্টি করতে ? আদৌ জোরপূর্বক মহাসৃষ্টি করান সম্ভব কি ? যদি ইরানীরা কোন ভাষাতে ঐশী মুজিযার সন্ধান পেয়ে থাকে এবং জানতে পারে ,তা কোন জাতির জন্য শুধু নয় ;বরং এটি এক গ্রন্থের ভাষা। অতঃপর তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাকে শক্তিশালী করার কাজে ব্রত হয়ে থাকে তবে একে কি ত্রুটি বলা যায় ? যদি ইরানীরা তাদের প্রাচীন ভাষার সঙ্গে এ নতুন ভাষার শব্দ ও ভাবার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে আকর্ষণীয় ও মিষ্টি নবীন ফার্সী ভাষার সৃষ্টি করে থাকে তাহলে তাকে অপরাধ বলা যাবে কি ?
তাঁরা বলে থাকেন যে ,ইসলামপূর্ব ইরানী ভাষা এমন এক জাতির ভাষা ছিল যা সাহিত্য ,সংস্কৃতি ও জ্ঞানে পূর্ণ ছিল ,অথচ এ জাতিটি আরবদের মুখোমুখি হওয়ার পর কি শুনে নীরব হয়ে গেল ?
ড. যেররিন কুব উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই এর জবাব দিয়েছেন ,
“ বলা হয়ে থাকে আরবী ভাষা অন্ধকার জাতির ভাষা হিসেবে এর কোন মধুরতা ,স্নিগ্ধতা ছিল না। তদুপরি যখন ইরান সাম্রাজ্যের আকাশে এ ভাষার আযান প্রতিধ্বনিত হলো তখন প্রাচীন পাহলভী ভাষা এর বিপরীতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কথা হলো ,যদি এমনটি হয়ে থাকে তবে যে ঘটনাটি ইরানীদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল তা হলো কোরআনের বাণী। সাধারণের বোধগম্য অথচ অলৌকিক এ বাণী আরবদের যেমন বিস্মিত করেছিল তেমনি তা ইরানীদের চিন্তাশক্তিকে বিস্মিত এবং হতবিহ্বল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইরানীরা নতুন এ ধর্মের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিল যা তাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত করেছিল এবং তারা আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে একে গ্রহণ করেছিল। তারা এতটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে ,কোন কবি বা বক্তাই তা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। ”
মুসলিম খলীফাগণ এমন কি উমাইয়্যা খলীফাদের ব্যাপারেও এরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি যে ,তাঁরা ইরানীদের তাদের প্রকৃত ভাষার ক্ষেত্রে-ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকলেও প্রচলিত মূল ভাষার ব্যাপারে-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। তাই এ বিষয়ে যেরূপ দাবি করা হয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই ;বরং বুঝা যায় তাঁরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কল্পনাপ্রসূত এরূপ কথা বলেছেন। কোরআনের অর্থ ,শব্দ বিন্যাস এবং এর বিশ্বজনীন শিক্ষার আকর্ষণ বিশ্বের সকল মুসলমানকে এ ঐশী গ্রন্থের প্রতি অনুরাগী করেছে। ফলে তারা তাদের নিজ ভাষার ওপর কোরআনের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই বিষয়টি শুধু ইরানীদের ক্ষেত্রেই নয় ;বরং সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল এবং তারা তাদের নিজ ভাষাকে কোরআনের ভাষার বিপরীতে বিসর্জন দিয়েছিল। আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে ,যদি আব্বাসীয় খলীফাগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরববিরোধী নীতি গ্রহণ না করতেন তবে বর্তমানে প্রচলিত ফার্সী ভাষার (যার সাথে ইসলামপূর্ব ফার্সীর পার্থক্য রয়েছে) উৎপত্তি হতো না। আব্বাসীয় খলীফাগণ ফার্সী ভাষার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা কখনোই চাননি ,আরবী ভাষা ইরানের সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলন লাভ করুক। বনি আব্বাস আরববিরোধী শুয়ূবীয়া আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শুয়ূবী নেতা আলান আরবদের বিভিন্ন ত্রুটি তুলে ধরে ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন ,অথচ তিনি খলীফা হারুন ও মামুনের দরবারের কর্মচারী ও তাঁদের স্থাপিত জ্ঞানকেন্দ্রের অনুবাদকের দায়িত্বে ছিলেন এবং নিয়মিত মজুরি পেতেন। শুয়ূবী চরমভাবে আরববিদ্বেষী ছিলেন এবং আরবদের কটুক্তি করে গ্রন্থ রচনা করতেন। অথচ তিনি হারুন ও মামুনের স্থাপিত জ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতেন।356 পূর্বে ফার্সী ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি ,খলীফা মামুন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনাকে উৎসাহিত করেছেন।
সুতরাং ইরানীদের প্রাচীন ফার্সীকে বাদ দিয়ে নতুন ফার্সী গ্রহণের বিষয়টি যাকে কোন কোন প্রাচ্যবিদ ইরানীদের বাকরুদ্ধ হওয়া বলে অভিহিত করেছেন- তা এ জাতির জন্য অনুশোচনার বিষয় নয় ;বরং খুশী হওয়ার মত বিষয়। প্রত্যেক ভাষারই নিজম্ব কিছু সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য রয়েছে ,ফার্সী ভাষাও এরূপ সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি ভাষা। এ ভাষার সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে ইরানীরা ঈমানের বলে ইসলামে মূল্যবান অবদান রেখেছে।
এ বিষয়টি মূল্যায়নে এডওয়ার্ড ব্রাউন ইনসাফ রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন ,
‘ ইরানের ইতিহাস বিষয়ে রচিত দু ’ টি গ্রন্থ সম্পর্কে ব্রিটিশরা অধিক পরিচিত। যার একটি স্যার জন ম্যালকমের এবং অপরটি ক্রিমেনটেজ মার্কহাম রচিত। এ দু ’ টি গ্রন্থে 1ম হিজরী শতাব্দীতে (সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতাব্দী) আরবগণ কর্তৃক ইরান বিজয়ের সময়কাল হতে 3য় হিজরী শতাব্দীতে
(9ম খ্রিষ্ট শতাব্দী) ইরানীদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ইরানের ইতিহাস সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং বিষয়টিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে... অথচ অনেক ক্ষেত্রেই এ সময়কালটি পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের চেয়ে ইরানীদের জন্য উদ্দীপনাময় সময় ছিল এবং ইরানের ইতিহাসে জ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এ সময়টিতে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ’
অন্যত্র তিনি সালমান ফার্সী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ,
‘ সালমান ফার্সীই যিনি ইরানীদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে রাসূলের সম্মানিত ও বিশেষ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের অনেক উচ্চ পর্যায়ের আলেম ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আরবদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী কিছু ব্যক্তি ,যেমন জালুলা যুদ্ধে বন্দী ইবনে শিরীন ও তাঁর তিন ভ্রাতা ইসলামী বিশ্বে আলেম হিসেবে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাই যে সকল ব্যক্তি বলে থাকেন আরবগণ কর্তৃক ইরান জয়ের পর দু ’ শতাব্দী ধরে ইরানীরা জ্ঞান ও নৈতিকতা হতে বঞ্চিত ছিল সেটি কখনোই সত্য নয় ;বরং এর বিপরীতে ইসলামের অবির্ভাবের পরবর্তী দু ’ তিন শতাব্দী ইরানীরা এ ক্ষেত্রে এতটা আকৃষ্ট হয়েছিল যা ইতিহাসে নজীরবিহীন। এ সময়কালটিকে নবীন ও প্রবীণ সভ্যতার মধ্যে সংমিশ্রণের যুগ বলা যায়। এ যুগটি প্রাচীন আচার ,বিশ্বাস ও চিন্তার পরিবর্তনের যুগ এবং কোন অবস্থায়ই একে মৃত্যু ,পতন বা নীরবতার যুগ বলা যায় না। ’
এ দু ’ শতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব হলো ইরানী মুসলমান ব্যক্তিত্বগণ তাঁদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আশ্বর্যজনক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার পাশাপাশি দীনী দৃষ্টিতেও উচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। তাঁদের অনেকেই অন্যান্য জাতির নিকটও অতীব সম্মানার্হ ছিলেন। এখনও ইরানের বাইরের আহলে সুন্নাতের গ্রন্থসমূহে এ সকল ব্যক্তির নাম অতি সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ইসলামী বিশ্বের দূরবর্তী দেশসমূহেও তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। এ যুগটি জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের হলেও ধর্মীয় সম্মান লাভের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় ইরানীরা এ সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হতে পেরেছিল।
যদি আমরা এ দু ’ শতাব্দীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে চাই তবে অবশ্যই আমাদের ইরানে ইসলামের বিজয়ের সময়কাল হতে খোরাসানে ইরানীদের (তাহরিয়ান বংশ) স্বাধীন ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত সময়কালের ইরানের সমাজকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
অবশ্য যে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের অসচেতন হওয়া যাবে না তা হলো ইরানে সাফারিয়ান ও সামানিয়ান শাসনামলে যে সকল ইরানী মনীষী তাঁদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের সকলেই ইরানে বাস করতেন না। তাঁদের অনেকেই ইরাকে অথবা হেজাযে বসবাস করতেন।
ইরানীদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর নৈকট্য ও সাহচর্যের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিরল সম্মান লাভ করেছিলেন তিনি হলেন সালমান ফার্সী357 । তিনি শিয়া মুসলমানদের দৃষ্টিতে রাসূল ও হযরত আলীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে রাসূলের প্রথম সারির সাহাবীদের একজন । মসজিদে নববীর দেয়ালে প্রথম সারির অন্যান্য সাহাবীদের সাথে তাঁর নাম খচিত রয়েছে।
রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবী ছাড়াও ইরানের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ এ দু ’ শতাব্দীতে ইরান ও ইরানী জাতির জন্য যে সম্মান-মর্যাদা ও সম্ভাবনা বহন করে এনেছেন তা আলোচনা করলে দেখব প্রকৃতপক্ষেই ইরানের ইতিহাসে তা ছিল অভূতপূর্ব।
এ দু ’ শতাব্দীতে একদল ইরানী কেরাআত ,তাফসীর ,হাদীস এবং ফিকাহ্শাস্ত্রে ধর্মীয়ভাবে এতটা উচ্চ স্থানে পৌঁছেছিলেন যে ,অন্যান্য জাতির মুসলমানরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত। বিশ্বের 55 কোটি সুন্নী মুসলমান তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করে। নাফে ,আসেম ,ইবনে কাসীর ,মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ,মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাবুরী ,তাউস ইবনে কাইসান ,রাবীতুর রাঈ ,আমাশ ,আবু হানিফা ,লাইস ইবনে সা ’ দ প্রমুখ এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত। লাইস ইবনে সা ’ দ একজন ইরানী ছিলেন যিনি মিশরের প্রধান মুফতির পদে অধিষ্ঠিত হন। একবার তিনি হজ্বব্রত পালন করতে এলে আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট ফকীহ্ সুফিয়ান সাওরী (যিনি একজন আদনানী আরব) তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে তাঁর উষ্ট্রের দড়ি টেনে এনে বাঁধেন।
এ দু ’ শতাব্দীতে আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রে যে সকল ইরানী বিশেষ ভূমিকা রাখেন তাঁদের কয়েকজন হলেন সিবাভেই কেসায়ী ,ফাররা ,আবু ওবায়দা মুয়াম্মার ইবনে মুসান্না ,ইউনুস ,আখফাস ,হাম্মাদ রাভীয়া ,ইবনে কুতাইবা দীনওয়ারী। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ,আবু হানিফা দীনওয়ারী এবং ‘ ফুতুহুল বুলদান ’ গ্রন্থের লেখক বালাযুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। কালামশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আলে নাওবাখত ,আবুল হাজিল আলাফ ,নিযাম ,ওয়াসিল ইবনে আতা ,হাসান বসরী ,আমর ইবনে ওবায়িদ প্রমুখ। দর্শন ,গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় শাকের খাওয়ারেজমীর পুত্রগণ ,নাওবাখতিগণ ,আবু মা ’ শার বালখী ,আবুত তায়্যিব সারাখসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইরানী মুসলিম সেনা নায়কদের মধ্যে তাহের যুল ইয়ামিনাইন এবং স্পেন বিজয়ী সেনাপতি মূসা ইবনে নাসিরের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত উদাহরণসমূহ এ দু ’ শতাব্দীতে ইরানীদের নীরবতার তথাকথিত দাবিকেই খণ্ডন করছে।
সমাপ্ত
তথ্যসূত্র:
1. এ গ্রন্থ রচনার সময়কালের পরিসংখ্যান।
2. ঊনবিংশ শতাব্দী।
3. জাতীয়তাবাদ আরব দেশগুলোতেও দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং এ দেশগুলোর অনেক মানুষই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আরব জাতীয়তার প্রতি বিশেষ গোঁড়ামি প্রদর্শন করে ,অথচ এটি ইসলামের উপস্থাপিত ঐক্যের ব্যাপক মানদণ্ড যা একমাত্র মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভরশীল তার বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ। এ কর্মের মন্দ ফল সর্বপ্রথম তাদের ওপরই আপতিত হয়েছে। কারণ এত বিপুল জনগোষ্ঠী ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়েও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না। নিঃসন্দেহে আরবরা যদি ধর্র্মীয় অনুভূতির শক্তিকে কাজে লাগাত তবে তাদের এরূপ পরাজয় বরণ করতে হতো না। একজন পাকিস্তানী লেখক লিখেছেন , “ জুন মাসের (1967) যুদ্ধে ধর্মীয় শক্তি (যায়নবাদী) জাতীয়তাবাদী শক্তির (আরব) ওপর বিজয়ী হয়েছে। ” যদিও এ কথায় ভুল রয়েছে তবুও আরবদের আরব জাতীয়তাবাদের ওপর নির্ভর করার বিষয়টিকে যেভাবে সমালোচনা করা হয়েছে তা সঠিক। (কথাটি এ দৃষ্টিতে ভুল যে ,যায়নবাদীদের নিকট সব সময়ই ধর্মের ওপর বর্ণের [ Race] প্রাধান্য ছিল এবং এখনও রয়েছে) গত বছর (1387 হিজরীতে) যখন হজ্বে গিয়েছিলাম তখন ‘ রাবেতা আল আলাম আল ইসলামী ’ -এর একজন তুখোড় বক্তা তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন , ‘ আল্লাহর শপথ! ইসলাম এ যুদ্ধে অংশ নেয় নি ;বরং আরব জাতীয়তাবাদ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ’
4. যে সকল সূরা ও আয়াতে মিল্লাত শব্দটি এসেছে সেগুলো হলো সূরা বাকারা : 120 ,130 ও 135 ;
আলে ইমরান : 95 ;নিসা : 125 ;আনআম : 161 ;আ ’ রাফ : 88 ও 89 ;ইউসূফ : 37 ও 38 ;ইবরাহীম : 13 ;নাহল : 123 ;কাহফ : 20 ;হজ্ব : 78 এবং সোয়াদ : 7।
5. সূরা হজ্ব : 78।
6. সূরা আনআম : 161।
7. সূরা বাকারাহ্ : 282।
8. ফার্সী ভাষায় লিখিত উসূলে উলুমে সিয়াসী।
9. উদারতাবাদ বা Liberalism.
10. সূরা তাকাভীর : 27।
11. সূরা নিসা : 133। তাফসীরুল মিযান ও বাইযাভীর মতে এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সা.) সালমান ফারসীর কাঁধে হাত দিয়ে বলেন ,তারা এ ব্যক্তির সম্প্রদায় ও জাতি।
12. সূরা মুহাম্মদ : 38।
13. মাজমাউল বায়ান ,91 খণ্ড ,164 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সূরা জুমুআর 3 নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : আবু হুরায়রা বলেছেন , ‘ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় সূরা জুমআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদের তা পাঠ করে শুনান। তিনিو أخرين منهم لمّا يلحقوا بهم পাঠ করলে আমরা প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা ? তিনি সালামন ফারসীর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন : যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে তবে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা আসমান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে। ’ মা ’ রেফুল কোরআন ,1369 পৃষ্ঠা ,1ম খণ্ড।
14. পরবর্তী আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে ,প্রথম হিজরী শতাব্দী ব্যতীত কখনই হেজায ইসলামের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র ছিল না ;বরং সব সময় ইসলামের বৃহৎ কেন্দ্রসমূহ মিশর ,বাগদাদ ,নিশাবুর বা দজলা ,ফোরাতের তীরবর্তী অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অনারবরা সেখানে ইসলামের অগ্রগামী পতাকাধারী ছিল।
15. সূরা হুজুরাত : 13।
16. আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু শুয়ুবীর বাড়াবাড়ি আচরণের আলোচনা আমরা পরবর্তীতে করব।
17. তোহাফুল উকুল ,পৃ 34 ;সীরাতে ইবনে হিশাম ,2য় খণ্ড ,পৃ. 414।
18. সুনানে ইবনে দাউদ ,2য় খণ্ড ,624 পৃষ্ঠা।
19. সাফিনাতুন বিহার ,سَلَمَ ধাতু।
20. সুনানে ইবনে দাউদ ,2য় খণ্ড ,625 পৃষ্ঠা।
21. বিহারুল আনওয়ার ,21 খণ্ড ,137 পৃষ্ঠা।
22. রাওজায়ে কাফী ,8ম খণ্ড ,203 নং হাদীস।
23. লেখক পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।
24. ইবনে কাসির প্রণীত কামিলুত তাওয়ারিখ ,খ. 2 ,পৃ. 28।
25. নাহজুল বালাগাহ্ ,খুতবা 148। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়কালীন অবস্থার বর্ণনা করে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর বক্তব্য।
26. যেমন হযরত ইমাম হুসাইন পূর্ণ ঈমান ,বিশ্বাস ও লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা সত্ত্বেও ইয়াযীদের বাহিনীর হাতে সকল সঙ্গী-সাথী নিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ইউরোপেও মুসলমান আরবদের বিজয় প্রথমদিকে অগ্রসর হলেও পরবর্তীতে ইউরোপীয়দের প্রতিরোধের মুখে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিরোধ হীনতার কারণে মুসলমানদের বিজয় সহজ হতো ;বিশেষত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ তাদের বিজয়কে ত্বরাণ্বিত করত।
27. ড. সাইদ নাফিসী তাঁর তারিখে এজতেমায়ীয়ে ইরান গ্রন্থে এ পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন।
28. মরহুম মুহাম্মদ কাযভীনী তাঁর ‘ বিশটি প্রবন্ধ ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন : সীমান্ত প্রহরীদের একাংশ যখন সাসানী শাসন কর্তৃত্বের দুর্বল অবস্থা লক্ষ্য করল এবং ইরানী সৈন্যবাহিনী আরব মুসলমানদের হাতে কয়েকবার পরাস্ত হলো তখন তারা আরবদের সহযোগিতায় এগিয়ে গিয়ে তাদের বিজয়েই শুধু নয় ;বরং নতুন নতুন এলাকা ও ভূমি দখলের পথ বাতলে দিতে শুরু করল। আরব সৈন্যরা যে সকল স্থানে আক্রমণ করেনি তাদের সে সকল স্থানে আক্রমণে আমন্ত্রণ জানাল। আরবরা যেন তাদের স্বীয়পদে অ ‘ িধষ্ঠ রাখে এ জন্য স্বহস্তে কোষাগার ও দুর্গসমূহের চাবি আরবদের হাতে তুলে দিল।
মরহুম কাযভীনী এখানে শুধু যে সকল ব্যক্তি ইসলামী সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়েছে তাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ,কিন্তু সাসানী শাসকবর্গকে সহায়তা হতে তাদের হাত গুটিয়ে নেয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেননি। কেন ইরানীরা জাতীয়বাদীদের ভাষায় বিজাতীয় বলে পরিগণিত ব্যক্তিদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে ? তারা কি সাসানী শাসকবর্গ ও তাদের পৃষ্ঠপোষক যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার কারণেই মুসলমানদের জয়ের মধ্যে তাদের মুক্তির বাণী খুঁজেনি ?
29. দীবাচেই বার রাহবারী ,267-270 পৃষ্ঠা।
30. ‘ আভেস্তা ’ হলো যারথুষ্ট্র ও পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ।
31. উমাইয়্যাদের নিকট থেকে আব্বাসীয়দের হাতে।
32. প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্য।
33. ‘ দশটি প্রবন্ধ ’ ।
34. স্বয়ং রাসুল (সাঃ) বলেছেন , ‘ নিশ্চয় হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের সাইয়্যেদ (নেতা)। ’ যা শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সবাই জুমআর নামাজের দ্বিতীয় খুতবায় পড়ে থাকে।
35. তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ,1ম খণ্ড ,পৃ. 142।
36. যারথুষ্ট্র বা মাজুসী।
37. খ্রিষ্টানগণ।
38. সাফিনাতুল বিহার ,2য় খণ্ড ,ولي ধাতু ,পৃ. 692-693।
39. ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ (মাযদা ইয়াসনা ও ফার্সী সাহিত্য) ,পৃ. 16।
40. ‘ হুনারে ইসলামী ’ ,ফার্সী অনুবাদক ইঞ্জিনিয়ার হুশাঙ্গ তাহেরী ,পৃ. 6।
41. ‘ হুনারে ইসলামী ’ ,পৃ. 7।
42. Man and his destiû নামে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
43. এ গ্রন্থটি ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সংঘটিত হওয়ার পূর্বে লিখিত।
44. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব ,পৃ. 552।
45. Histiry of literature,Mr. Brown. Vol 1 ,চ. 303.
46. ইরানের সামাজিক ইতিহাস (ফার্সী ভাষায় লিখিত) ,2য় খণ্ড ,পৃ. 20-24।
47. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 138 ;মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 9-12।
48. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 178।
49. প্রাগুক্ত।
50. তামাদ্দুনে ইরানী (ফার্সী ভাষায় অনূদিত) ,পৃ. 178।
51. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 321।
52. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 218-219।
53. প্রাগুক্ত ,পৃ. 466।
54. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 510।
55. মনী ওয়া দীনে উ ,পৃ. 28 ,29।
56. প্রাগুক্ত গ্রন্থ ,পৃ. 36।
57. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 222।
58. মনী ওয়া দীনে উ ,পৃ. 18।
59. প্রাগুক্ত গ্রন্থ ,পৃ. 19 (পাদটীকা)।
60. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 225।
61. প্রাগুক্ত ,পৃ. 363 ,364।
62. প্রাগুক্ত গ্রন্থ।
63. তারিখে এজতেমায়ীয়ে ইরান ,খ. 2 ,পৃ. 46-47।
64. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান (ফার্সী ভাষায় লিখিত) ,পৃ. 382।
65. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান (সাসানী শাসনামলে ইরান) ,পৃ. 384-386।
66. সূরা
67. আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর 2001 সালে এ বৌদ্ধ মূর্তিটি ধ্বংস করে। -অনুবাদক।
68. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 42-44 ও 60।
69. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 407।
70. তারিখে এজতেমায়ীয়ে ইরান ,খ. 1 ,পৃ. 27-28।
71. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 45।
72. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 43।
73. ‘ যারদুশত ’ বা ‘ যারতুশত ’ শব্দটি ইসলামের পরবর্তী সময়ের উচ্চারণ। আরবী গ্রন্থসমূহে সাধারণত ‘ যারদুশত ’ বলা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞগণ এর প্রকৃত উচ্চারণ ‘ যারথুষ্ট্রর ’ বা ‘ যারতুষ্ট্র ’ বলেছেন যার অর্থ ‘ হলুদ উটের মালিক ’ ।
ডক্টর রেজা যাদেহ শাফাক সংকলিত ‘ মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে ইরান ’ গ্রন্থের 2য় অধ্যায়ের 133 পৃষ্ঠায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আলমেস্টাডের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে তিনি তাঁর ‘ পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস ’ গ্রন্থের 9ম অধ্যায়ে বলেছেন ,যারতুশত খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর ঐশী আহ্বান শুরু করেন। তাঁর প্রকৃত নাম হলো ‘ যারতুশতার ’ যার অর্থ হলো ‘ হলুদ উষ্ট্র অধিপতি ’ ,তাঁর পিতার নাম ‘ পুরুশাসপ ’ অর্থাৎ ধূসর বর্ণের অশ্বের মালিক এবং তাঁর মাতার নাম ছিল ‘ দুগদাভা ’ অর্থাৎ সাদা গাভী দোহনকারিণী। তাঁর পরিবার ও বংশের নাম ছিল ‘ সেপিতামেহ ’ অর্থাৎ শুভ্রবংশ। এ সকল নাম তাঁদের রাখালী জীবনের ইঙ্গিত বহন করে।
74. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 162 ,163 ,459 ও 538।
75. প্রাগুক্ত ,পৃ. 163-164।
76. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 168-169।
77. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 49 ও 50।
78. তারিখে জামেএ ইরান ,পৃ. 301।
79. তারিখে তামাদ্দুনে ইরানী ,ফার্সী ভাষায় ডক্টর বাহনাম কর্তৃক অনূদিত ,পৃ. 144।
80. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 89।
81. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 198।
82. পবিত্র কোরআন বলছে ,لن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التّقوى منكم ‘ কুরবানীর মাংস ও রক্তসমূহ কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না ;বরং যা তাঁর নিকট পৌঁছায় তা হলো তোমাদের তাকওয়া। ’
অন্যদিকে কোরআন দরিদ্র-মিসকীনদের খাদ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে কুরবানী নিষেধ করেনি। তাই বলেছে ,
و أطعموا البائس الفقير فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ ‘ তখন তা (কুরবানী) হতে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্চা করে না তাকে এবং যে যাঞ্চা করে তাকে। ’ (সূরা হজ্ব : 36-37)
83. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 112 ও 110 যেখানে রাজাবের চিত্রে খোদার আকৃতি ,257 পৃষ্ঠায় রুস্তমের শিলালিপিতে খোদার প্রতিকৃতি এবং 481 পৃষ্ঠায় বুস্তানের খিলানে খোদার আকৃতি নিয়ে আলোচিত হয়েছে।
84. সূরা আনআম।
85. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ ,পৃ. 420।
86. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 421।
87. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 168।
88. প্রাগুক্ত ,পৃ. 173।
89. ক্রিস্টেন সেন ‘ আলবিরুনী ’ হতে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন।
90. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 141।
91. মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ,পৃ. 53 ও 54।
92. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 380।
93. প্রাগুক্ত ,পৃ. 349 (পাদটীকা)।
94. সূরা শুরা : 11।
95. সূরা রূম : 27।
96. মাফাতিহুল জিনান ,দোয়ায়ে জাওশান আল কাবীর।
97. সূরা বাইয়্যেনাহ্ : 5।
98. মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ,পৃ. 36।
99. তারিখে জামে আদইয়ান ,পৃ. 306।
100. ‘ ঘ ’ ধারায় বলা হবে যে ,সেপান্ত মাইনিও-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ হলো আনগারা মাইনিও যে সেপান্ত মাইনিও হতে অস্তিত্ব লাভ করে নি। সুতরাং আহুরামাযদার জন্য দু ’ ধরনের ইচ্ছার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে হয়। পবিত্র ইচ্ছা ও অপবিত্র ইচ্ছা। অথবা আহুরামাযদা তাঁর পবিত্র ইচ্ছাকে ভাল ও মন্দ এ দু ’ ধরনের আত্মার সাহায্যে সম্ভাব্য অবস্থা হতে কার্যকর অবস্থায় এনেছেন। তদুপরি ‘ সম্ভাব্য হতে কার্যকর ’ অবস্থায় আনয়ন প্রথম সৃষ্টির জন্য দার্শনিকভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত।
101. তারিখে জামে আদইয়ান ,পৃ. 306-308।
102. সূরা সিজদাহ্ : 7।
103. বিহারুল আনওয়ার ,খ. 76 ,পৃ. 194।
104. সূরা হজ্ব : 61।
105. সূরা আনআম : 1।
106. সূরা ত্বাহা : 49-50।
107. মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ,পৃ. 25।
108. সূরা সিজদাহ্ : 7।
109. সূরা ত্বাহা : 50।
110. সূরা ইবরাহীম : 22।
111. সূরা দাহর : 2-3।
112. ‘ হে জিন ও মানব জাতি! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের ক্ষমতাধীন হয় ,তবে অতিক্রম কর। কিন্তু তাঁর প্রভাব ও অনুমতি ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ’ - সূরা রাহমান : 33।
113. তারিখে জামে ইরান ,পৃ. 315।
114. তামাদ্দুনে ইরান ,পৃ. 188।
115. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 458-459।
116. মনী ও তাঁর ধর্ম ,পৃ. 39 ও 40।
117. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 364 ,365।
118. মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ,পৃ. 278।
119. যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে ‘ আল্লাহর পুত্র ’ বলত এবং কোরআন তাদের এ কর্মের জন্য তীব্র সমালোচনা করেছে।
120. যেমনটি অন্ধকার যুগের আরবরা ফেরেশতাদের ‘ আল্লাহর কন্যা ’ বলত। কোরআন তাদেরও তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে।
121. মাযদা ইয়াসনা ও আদাবে পার্সী ,পৃ. 276।
122. তারিখে জামে আদইয়ান ,পৃ. 309 ও 110।
123. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 309।
124. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 456 ও 457।
125. সূরা লোকমান : 25।
126.هؤلاء شفعاؤنا عند الله ‘ এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য শাফায়াতকারী ’ - সূরা ইউনুস : 18।
127. মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ,পৃ. 339 ও 340।
128. সূরা হিজর : 21।
129. আশ্চর্যের বিষয় হলো অগ্নি উপাসনগণ অগ্নিকে জ্যোতি হিসেবে জ্যোতিসমূহের জ্যোতি (نور الأنوار ) অর্থাৎ খোদার প্রকৃতি বলে দাবি করেন অথচ সূর্য জ্যোতি হওয়া সত্ত্বেও অগ্নির ওপর এর পতনকে অগ্নির অপবিত্রতার কারণ বলেন।
130. ‘ হুমে ’ কে যারদুশত অপবিত্র বলে নিষিদ্ধ করেছিলেন।
131. কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি বুন্দহেশে উল্লিখিত হয়েছে যে ,অগ্নি ‘ বিশ্বের আশ্রয় ’ ও ‘ খোদা ’ ,কিন্তু এই আশ্রয়কেই তারা ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।
132. ‘ মাযদা ইয়াসনা ওয়া আদাবে পার্সী ’ নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।
133. মাওলানা রুমি ,হাফিয সিরাজী ,সা ’ দী ,ফরিদুদ্দীন আক্তার প্রমুখ।
134. সূরা নাহল : 100।
135. সূরা বনি ইসরাইল : 33।
136. শেখ বাহায়ী তাঁর প্রসিদ্ধ গজলে আছে :
“ সাকী আধ্যাত্মিক শরাবের পাত্র আন হেথায়
কিছু মুহূর্ত দেহের এ পর্দা হতে মুক্তি পেতে চাই।
ধর্ম ও অন্তর হারিয়ে হয়েছি আনন্দিত
প্রেমের জুয়ায় মন হারিয়ে কেউ হয় না মর্মাহত।
সিজদা করি আমি মূর্তিকে ,ভুলে গিয়েছি মসজিদ
(একেই করেছি আমি আমার ধর্মের ভিত)
প্রেমের পথে কাফের আমি ,কোথায় মুসলমানী ?
হে দুনিয়া বিমুখ! তোমার জন্য বেহেশত ও হুর খুবই সস্তা
এ মূল্যবান প্রাণ এ পথে তাই বিকিয়ে দিও না।
শরাবখানায় দেখলাম এক দুনিয়াত্যাগী মাতাল শরাবে
বললাম ,হে আর্মেনীয় মুসলমান! মোবারকবাদ তোমাকে।
হে সন্ন্যাসী! আমার অন্তররূপ গৃহে তোমার অনুগ্রহের প্রাসাদ বানাও
এ ক্ষুদ্র গৃহ ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই তাকে সাজাও। ’
137. ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ নারাকী আত্মিক পরিশুদ্ধতায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন ,
‘ সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির যার অন্তরে রয়েছে ভালবাসার যোগ
আত্মসমর্পণ ও জীবন উৎসর্গের পেয়েছে সে সুযোগ।
শরাবখানার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হলো
শরাবপিয়াসী মাতাল আমার জন্য দোয়া করল।
পরিতৃপ্ত আমি ,তার মুরীদ হওয়ার মহান লক্ষ্য অর্জিত হলো।
পূর্বের সকল ইবাদাতের কাযা আদায়ের সুযোগ এ অন্তর পেল। ’
অন্যত্র তিনি বলেছেন ,
‘ সুদর্শন বালকেরা মঠে রয়েছে যতক্ষণ
সন্ন্যাসীদের মঠে আমি রইব ততক্ষণ।
কোন্ বাণীতে হয়েছে ভালবাসা নিষিদ্ধ হায়!
হে উপদেশদাতা! তা তুমি দেখাও আমায় ?
যে শরাব পানে বন্ধুর গৃহের পথ খুঁজে পাওয়া যায়
কোন্ ধর্মে সে শরাব নিষিদ্ধ করা হয় ?
প্রেমের অনেক কথা ,তাকে বললাম বিস্তারিত
বললেন এ কাহিনী এখনও রয়েছে অসমাপ্ত।
আমার গৃহ হতে রয়েছে গোপন পথ
সে পথে বন্ধুর বাড়ি দু ’ কদম পথ।
(আনন্দিত) শরাবখানায় সব সময় কি সুন্দর পরিবেশ!
(আফসোস) দীনী মাদ্রাসাগুলো নিয়েছে সাধারণের বেশ। ’
মরহুম নারাকী দীনী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হয়েও বলেছেন ,
“ আশ্চর্য আমি ,কেন এখানে মাদ্রাসা করা ?
যেখানে তৈরি করা যেত শরাবখানা।
138. দেবদারু
139. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 247।
140. কামিলে ইবনে আসির ,2য় খণ্ড ,পৃ. 319-320।
141. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 343-346।
142. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 359।
143. তারিখে ইজতেমায়ীয়ে ইরান ,খ. 2 ,পৃ. 25-26।
144. মাতা-পিতা ,ভ্রাতা-ভগ্নি ,ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী ,ভগ্নিপুত্র-ভগ্নিপুত্রী ,নাতী-নাতনী প্রভৃতি।
145. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 448।
146. ওয়াসায়েলুশ শিয়া ,খ. 3 ,পৃ. 368।
147. তাওহীদে সাদুক ,পৃ. 306 ;ওয়াসায়েলুশ শিয়া ,খ. 3 ,পৃ. 46।
148. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 354।
149. সূরা শুয়ারা : 198-199।
150. তাফসীরে সাফীতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইবনে ইবরাহীম কুমীর তাফসীর হতে উল্লিখিত হয়েছে ,কোরআনে যেأعجم শব্দটি এসেছে তাতে ইরানী-অ-ইরানী সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাহ্যত হাদীসেأعجم বলতে ইরানীদের বুঝানো হয়েছে। যদি নাও হয় তবু ইরানীরাও এর অন্তর্ভুক্ত।
151. সাফিনাতুল বিহার ,عجم ধাতু।
152. রোমীয় ঐতিহাসিক যিনি চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর সাসানীদের সমসাময়িক ছিলেন।
153. সাসানী শাসক কাবাদ ও অনুশিরওয়ানের সমসাময়িক।
154. মুজতাবা মিনুয়ীর প্রবন্ধ হতে।
155. ডক্টর যেররিন কুব ঘটনাটিকে অসত্য ও বানোয়াট বলেছেন।
156. আহমাদ আমিন প্রণীত দ্বোহাল ইসলাম ,খ. 1 ,পৃ. 64।
157. মরহুম ডক্টর ইব্রাহীম আয়াতী প্রণীত স্পেনের ইতিহাস।
158. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 65 (জর্জি যাইদান)।
159. তারিখে তামাদ্দুন ( History of Civilization),উইল ডুরান্ট ,খ. 11 ,পৃ. 224।
160. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 66।
161. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 11 ,পৃ. 315।
162. ক্রিস্টেন সেন রচিত ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 385।
163. ইবনুন নাদিম প্রণীত আল ফেহেরেসত ,পৃ. 351 ,মিশর হতে প্রকাশিত।
164. আল ফেহেরেসত ,পৃ. 386।
165. তারিখে ইলম ( History of Science) ,পৃ. 371।
166. প্রাগুক্ত।
167. History of Civilization,Will Durant
168. তারিখে তামাদ্দুন ,ফার্সীতে অনূদিত ,খ. 11 ,পৃ. 219।
169. খ্রিষ্টান লেখকদের মতে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার মূর্তিপূজকদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
170. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব ,পৃ. 263-265।
171. শিবলী নোমানী রচিত ‘ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ’ ,পৃ. 16-18।
172. ডক্টর যাবিউল্লাহ্ সাফাও তাঁর ‘ তারিখে উলুমে আকলী দার ইসলাম ’ গ্রন্থের 6 পৃষ্ঠায় বলেছেন , ‘ ইয়াহিয়া নাহভী পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দীর শেষার্ধ হতে ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ’ অর্থাৎ তিনি হিজরতের একশ ’ বছর পূর্বের একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 18 পৃষ্ঠায় লিখেছেন , ‘ বলা হয়ে থাকে তিনি 641 খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবনে আস কর্তৃক মিশর জয়ের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মতে তিনি পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দীর শেষার্ধ হতে ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন ব্যক্তিত্ব। তাই পাঁচশ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধ হতে সপ্তম খ্রিষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাঁর জীবিত থাকা বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বাভাবিক নয়। ’
173. শিবলী নোমানী রচিত ‘ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ’ ,পৃ. 50।
174. শিবলী নোমানী রচিত আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ,পৃ. 53-56।
175. প্রাগুক্ত।
176. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 11 ,পৃ. 220।
177. জর্জি যাইদান প্রণীত তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 3 ,পৃ. 64 (ফার্সীতে অনূদিত)।
178. ‘ শুয়ূবীয়া ’ ইরানীদের একটি আন্দোলন যা আরবদের বিরুদ্ধে তারা শুরু করেছিল। এ গ্রন্থের তৃতীয়াংশে আমরা এ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছি।
179. ‘ মাওলা ’ শব্দটির আরবীতে বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে ,এমনকি বিপরীত অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ কখনও নেতা ও অভিভাবক অর্থে ব্যবহৃত হয় ,যেমন নবী (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে বলেছেন ,من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ‘ আমি যার অভিভাবক এই আলীও তার অভিভাবক। ’ আবার তেমনি দাস ও অনুগত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মূলতمولى শব্দটিولاء শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ বন্ধন ও নৈকট্য। এ কারণেই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মাওলার অপর একটি অর্থ হলো মুক্ত দাস। তাই যে সকল ব্যক্তি পূর্বে দাস ছিল ও পরবর্তীতে মুক্ত হয়েছিল তাদের ও তাদের সন্তানদের মাওলা বলা হতো। আবার যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করত তাকেও মাওলা বলে অভিহিত করা হতো। কখনও কখনও কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে বিশেষত কোন অনারব যদি আরব গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতো এ মর্মে যে ,ঐ গোত্র তার পৃষ্ঠপোষকতা করবে তবে তাকেও মাওলা বলা হতো। ইরানীদের এ জন্য মাওলা বলা হতো তাদের পিতৃপুরুষ দাস ছিল ও পরবর্তীতে মুক্ত হয়।
180. মুহাম্মদ আবু যোহরা রচিত ‘ আবু হানিফার জীবন ,তাঁর সময়কাল ,ফিকাহ্ ও তাঁর মত ’ গ্রন্থের 15 পৃষ্ঠা হতে।
181. তামাদ্দুনাত কাদিমী - গুসতাভ লুবুন রচিত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ।
182. খাল্লাকীয়াত মা ইরানীয়ান ,পৃ. 108।
183. প্রাগুক্ত ,পৃ. 81-82।
184. কিলম্যান অথবা কোলম্যান।
185.اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (সূরা বাকারাহ্ : 255)।
186.سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (সূরা সাফফাত : 180)।
187.وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ (সূরা হাদীদ : 4)।
188.هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (সূরা হাদীদ : 3)।
189.لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (সূরা আনআম : 103)।
190. অবশ্যই সে-ই সাফল্য লাভ করেছে যে পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। (সূরা শামস : 9)
191. আপনি বলুন ,আল্লাহর সজ্জিত বস্তুসমূহকে যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে ? (সূরা আ ’ রাফ : 32)
192. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 284।
193. ইরান দার যামানে সাসানীয়ান ,পৃ. 284।
194. অযদী ফারদ ওয়া কুদরাতে দৌলাত ,পৃ. 5।
195. সাফাভী বংশীয় শাসকরা কাঁসা শিল্প ,দাইলামিগণ জেলে সম্প্রদায়ের ,গজনভিগণ দাস শ্রেণীর এবং সাফাভীরা দরবেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন।
196. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 247।
197. তামাদ্দুনে ইরানী ,পৃ. 20।
198. আল মাহাসিন ওয়াল আযদাদ ,পৃ. 4।
199. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 10 ,পৃ. 234।
200. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 10 ,পৃ. 251-255।
201. প্রাগুক্ত।
202. প্রাগুক্ত।
203. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 10 ,পৃ. 256।
204. ‘ ইরান আজ নাজারে খভার সেনাসন ’ নামে ফার্সীতে লিখিত।
205. নেগাহী দার তারিখে জাহান।
206. মাহমুদ তাফাজ্জুলী কর্তৃক অনূদিত ‘ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ’ ,2য় খণ্ড ,পৃ. 1038-1042।
206. প্রাগুক্ত।
207. ইবনুন নাদিম প্রণীত - আল ফেহেরেস্ত ,সপ্তম প্রবন্ধ ,পৃ. 352-353।
208. যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র।
209. হাদীস ,ফিকাহ্শাস্ত্র ও উসূল।
210. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 204।
211. দোহাল ইসলাম. খ. 1 ,পৃ. 163।
212. প্রাগুক্ত।
213. ফকীহ্ বলতে এখানে আহ্লে সুন্নাতের ফকীহ্ বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে শিয়া ফকীহ্গণও কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। শাইখুত তায়িফা শেখ আবু জাফর তুসী তাঁর ‘ আল খিলাফ ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘ কিতাবুল মুরতাদ ’ অধ্যায়ে ‘ মুরতাদ ’ ও ‘ জিন্দিকে ’ র মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন মুরতাদ হলো যে বাহ্যিকভাবে ইসলামকে অস্বীকার করেছে ,এরূপ ব্যক্তির তওবা গ্রহণীয় ;কিন্তু বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করলেও আন্তরিকভাবে অস্বীকারকারী হলো জিন্দিক। তার তওবা এ পথ হতে তার ফিরে আসার চি হ্ন বলে বিবেচিত হবে না।
214. সাফিনাতুল বিহার ,ওয়ালী ধাতুর আলোচনা ,পৃ. 129।
215. সূরা হুজুরাত : 13।
216. সূরা যুমার : 9।
217. সূরা হুজুরাত: 13
218. সূরা নিসা : 95।
219. ইন্দোনেশিয়ার পুনরুত্থান।
220. চতুর্দশ খ্রিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ ছিল ও সেখানে বৌদ্ধদের রাজত্ব ছিল।
221. বইটি বিভিন্ন দেশের মনীষীদের লেখা প্রবন্ধের একটি সংকলন।
223. তিনি ইন্দোনেশিয়ার ভাষা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
224. পূর্বের নিবন্ধে মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী তাঁর জন্ম সামারকান্দে বলে উল্লেখ করলেও আওারাদী তা সঠিক বলে মনে করেননি। তিনি তাঁর জন্ম সিস্তানে বলেছেন ,যা হোক উভয় স্থানই ইরানের অংশ।
225. বর্তমানের আফগানিস্তানে ,প্রাচীন ইরানের খোরাসান।
226. আত্তারাদীর লেখা হতে।
227. প্রবন্ধটি জনাব দাউদ সিতিং কর্তৃক লিখিত। তিনি লেবাননে চীনা দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। তিনি চীনের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং চীনের মুসলমানদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও বক্তাদের অন্যতম।
228. উল্লিখিত দূত সা ’ দ রাসূল (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী সা ’ দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস নন। কারণ সা ’ দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মদীনাতেই ইন্তেকাল করেন ও সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।
229. ‘ ইসলাম : সিরাতে মুস্তাকিম ’ ,পৃ. 420-423।
230. ইসলাম : সিরাতে মুস্তাকিম ,পৃ. 424।
231. হোয়াংহোও হতে পারে। -অনুবাদক।
232. ইসলাম : সিরাতে মুস্তাকিম পৃ. 432।
233. ইসলাম : সিরাতে মুস্তাকিম পৃ. 437।
234. 1947 সাল।
235. ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল।
236. হাজারেয়ে শেখ তুসী ,পৃ. 180-182।
237. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,(ফার্সী ভাষায় অনূদিত) ,পৃ. 247।
238. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,পৃ. 246-247।
239. ‘ কাত্তাবে ওহী ’ বলে প্রসিদ্ধ।
240. শহীদে সানী প্রণীত ‘ মুনিয়াতুল মুরীদ ’ ,পৃ. 5।
241. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম (ফার্সীতে অনূদিত) ,পৃ. 264।
242. বর্তমানের উজবেকিস্তান।
243. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,পৃ. 257।
244. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,391-392।
245. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 94-95।
246. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 93।
247. প্রাগুক্ত গ্রন্থ ,পৃ. 314।
248. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 75।
249. তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ,খ. 1 ,পৃ. 396-397।
250. প্রাগুক্ত ,পৃ. 392-396।
251. বিহারুল আনওয়ার ,খ. 2 ,পৃ. 91।
252. নাহজুল বালাগাহ্ ,হিকমাত 80।
253. বিহারুল আনওয়ার ,খ. 2 ,পৃ. 97।
254. বিহারুল আনওয়ার ,খ. 4 ,পৃ. 96।
255. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 247।
256. তারিখে তামাদ্দুন ,পৃ. 207।
257. ইতোপূর্বে কোরআনে ও আরবী বর্ণে ‘ নুকতাহ ’ প্রচলন ছিল না ও ‘ নুকতাহ ’ সম্পন্ন বিভিন্ন বর্ণ যেমন
ب,ت,ث,ج,خ,ذ,ز,ض,ظ,ق,ف,ن প্রভৃতি ‘ নুকতাহ ’ ছাড়াই লিখা হতো ,ফলে সদৃশ বর্ণ হতে পার্থক্য করা কঠিন ছিল।
258. তাসিসুশ শিয়া লি উলুমিল ইসলাম ,পৃ. 316-322।
259. রাইহানাতুল আদাব ,চতুর্থ খণ্ড ,পৃ. 426।
260. ঐতিহাসিক সূত্রমতে রাসূলের ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল এগার অথবা তের বছর।
260. তারিখে তামাদ্দুন (ফার্সীতে অনূদিত) ,খ. 3 ,পৃ. 95।
261. ‘ শহীদে ফাখ ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম হাসান (আ.)-এর প্রপৌত্র ও মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ফাখে আব্বাসীয় খলীফার প্রতিনিধিদের হাতে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাতবরণ করেন।
262. তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম ,খ. 3 ,পৃ. 97।
263. তাসিসুশ শিয়া. পৃ. 284।
264. প্রাগুক্ত ,পৃ. 280।
265. হাদীস সমগ্র।
266. হাযারেয়ে শেখ তুসী ,2য় খণ্ড এবং ইয়াদ নামেহ শেখ তুসী ,3য় খণ্ড।
267. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল ,খ. 3 ,পৃ. 497।
268. শাযরাতুয যাহাব ফি আখবারি মিন যাহাব ,খ. 4 ,পৃ. 126-127।
269. মুহাক্কেক হিল্লী প্রণীত আল মুতাবার।
270. আল কুনী ওয়াল আলকাব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
271.যদিও ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তদুপরি শাহ আব্বাস ও মুহাক্কেক আরদেবিলীর মৃত্যুর সময়ের পার্থক্য ঘটনার সত্যতার প্রতি সন্দেহের ছায়া ফেলে।
272. আলী দাওয়ানী রচিত যিন্দেগীয়ে জালালউদ্দীন দাওয়ানী।
273. যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন।
274. ফিকাহ্ ও হাদীস।
275. আখাবারিগণ বিশ্বাস করত কোরআন আমাদের বোধগম্য নয়। তাই ইসলামের বিধিবিধানের জন্য হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে যদিও ঐ হাদীস দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ হয়।
276. চৌদ্দ শতক।
277. জাবালে আমাল ফিত তারিখ গ্রন্থ হতে।
278. তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 3 ,পৃ. 104-105।
279. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 305।
280. তাসিসুশ শিয়া ,পৃ. 298।
281. রাইহানাতুল আদাব ,2য় খণ্ড ,পৃ. 213।
282. আল ফেহেরেসত ,পৃ. 69।
283. রাইহানাতুল আদাব ,খ. 8 ,পৃ. 189।
284. ইবনে ইসহাক ইবনে হিশামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন বিধায় ‘ সীরায়ে ইবনে হিশাম ’ নামে তা প্রসিদ্ধ।
285. সূরা বাকারাহ্ : 111।
286. কাফী , ‘ কিতাবে হুজ্জাত ’ অধ্যায় ,1ম খণ্ড ,পৃ. 171।
287. তাসিসুশ শিয়া ,পৃ. 363 এবং 364।
288. রাইহানাতুল আদাব ,খ. 1 ,পৃ. 269।
289. ইবনে খাল্লেকান রচিত আল ফেহেরেস্ত গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু 131 হিজরী বলা হয়েছে। সম্ভবত এটিই সঠিক।
290. তারিখে ইলমে কালাম- শিবলী নোমানী ,পৃ. 31।
291. এ সম্পর্কে জানতে হলে শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী রচিত ‘ হযরত আলী (রা.)-এর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ’ বইটি পড়ুন।
292. তারিখে ইবনে খাল্লেকান ,খ. 3 ,পৃ. 131 ,132।
293. কাফি ,1ম খণ্ড ,পৃ. 170।
294. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 352।
295. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 351।
296. হেনরী কারবান ,তারিখে ফালসাফায়ে ইসলামী (ফার্সীতে অনূদিত) ,পৃ. 199। ডক্টর হুসাইন নাসর তাঁর ‘ সেহ্ হাকিমে মুসলমান ’ গ্রন্থের 166 পৃষ্ঠায় বলেছেন , ‘ কার্ডানূস কিন্দীর নামকে অ্যারিস্টটল ,আর্কিমিডিস ও অ্যাক্লিডসের নামের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ’
297. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 204।
298. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 179।
299. উউনুল আম্বা ,খ. 3. পৃ. 225।
300. 279-289 হিজরী।
301. আল ফেহেরেস্ত ,পৃ. 382 ,কাফতী প্রণীত তারিখুল হুকামা ,পৃ. 435।
302. ইবনে খাল্লেকান প্রণীত ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান।
303. তারিখুল হুকামা ,পৃ. 277।
304. ডক্টর মাহ্দী মুহাক্কিকের ‘ আস সিরাতুল ফালসাফিয়াতুর রাযী ’ গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
305. গ্রীসের প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকিম জালিনুস। তাঁর প্রকৃত নাম গ্যালেন (খ্রিষ্টপূর্ব 201-131 অব্দ)।
306. তারিখুল হুকামা ,পৃ. 323।
307. ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থ হতে।
308. বিসত মাকালেহ্ ,খ. 2 ,পৃ. 141।
309. তারিখে উলুমে আকলী দার তামাদ্দুনে ইসলামী ,পৃ. 204।
310. তালিকাতে ইবনে সিনা ,পৃ. 8।
311. ‘ আল কিতাবুয যাহাবী লিল মেহেরজান আল আলফী লিযিকরী ইবনে সিনা ’ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত ,পৃ. 55।
312. সাওয়ানুল হিকমাহ্ ,পৃ. 110 ও 111।
313. উউনুল আম্বা ,খ. 2 ,পৃ. 298-299।
314. সাওয়ানুল হিকমাহ্।
315. লেখকের ‘ ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান ’ গ্রন্থটি 1970 সালে লিখিত।
316. উউনুল আম্বা ,3য় খণ্ড ,পৃ. 34।
317. মুজামুল উদাবা ,খ. 7 ,পৃ. 269।
318. প্রাগুক্ত।
319. মুজামুল উদাবা ,খ. 7 ,পৃ. 269।
320. রওজাতুল জান্নাত ,পৃ. 582।
321. উউনুল আম্বা ,খ. 3 ,পৃ. 383।
322. রওজাতুল জান্নাত ,পৃ. 582।
323. রাইহানাতুল আদাব ,খ. 8 ,পৃ. 243।
324. উসূলী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ফিকাহ্শাস্ত্রের বিভিন্ন সাধারণ নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।
325. ডক্টর মুহাম্মদ মুঈন প্রণীত হাফেযে শিরিন সুখান।
326. রওজাতুল জান্নাত ,পৃ. 476।
327. জালালুদ্দীন দাওয়ানীর জীবনী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
328. জালাল উদ্দীন দাওয়ানীর জীবনী ,পৃ. 110।
329. নামে দানেশওয়ারান ,খ. 9 ,পৃ. 89 ও 204।
330. তিনি মীর দামাদ নামে প্রসিদ্ধ। সাফাভী শাসক শাহ আব্বাস সাফাভীর অভ্যুদয়ের সমকালে ইসফাহান ইসলামী দর্শনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মীর দামাদ ,শেখ বাহায়ী ,মীর ফানদা রাসকীর মত ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব ঘটে। মোগল আক্রমণের পর ইরানে বিদ্যমান শিরাজের শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোথাও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না ,তাই ইসফাহানে জ্ঞানকেন্দ্র সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন ধারা সৃষ্টি হয় ,এমনকি শিরাজ হতে মোল্লা সাদরা ও জাবালে আমাল হতে মুহাক্কেক কোর্কীও এখানে আসেন।
331. দর্শনে অ্যারিস্টটলকে ‘ প্রথম শিক্ষক ’ ও আবু নাসর ফারাবীকে ‘ দ্বিতীয় শিক্ষক ’ বলা হয়।
332. রওজাত ,পৃ. 23।
333. রাওজাতুল জান্নাত ,পৃ. 117।
334. প্রাগুক্ত।
335. সৌভাগ্যক্রমে ফাখরুদ্দীন সামাকীর একজন শিক্ষকের নাম সম্প্রতি আমার হস্তগত হয়েছে। তিনি হলেন গিয়াসউদ্দীন মনসুর। তাই এ স্থানের অস্পষ্টতাও দূরীভূত হলো।
336. সূরা বাকারাহ্ : 115।
337. সূরা ক্বাফ : 16।
338. সূরা হাদীদ :3 ।
339. সূরা আনকাবুত : 69।
340. সূরা শামস : 9 ,10।
341. সূরা নূর : 35।
342. সূরা হাদীদ : 3।
343. সূরা বাকারাহ্ : 163।
344. সূরা রহমান : 26।
345. সূরা হিজর : 29।
346. সূরা ক্বাফ : 16।
347. সূরা হাদীদ : 4।
348. সূরা বাকারাহ্ : 115।
349. সূরা নূর : 40।
350. আল্লুমা ,পৃ. 427।
351. বন্ধু বলতে এখানে মনসুর হাল্লাজকে বুঝিয়েছেন।
352. হুজুরে ক্বালব নিয়ে।
353. তাঁর রূহের নিকট হতে।
354. হাফেয শিরাজী ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি।
355. কবি ও আরেফ আহমাদ জামীকে ‘ শাইখুল ইসলাম ’ বলা হতো।
356. জর্জি যাইদান রচিত তারিখে তামাদ্দুন ,খ. 3 ,পৃ. 310-311।
357. রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন , ‘ সালমান আমার আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ’
সূচীপত্র :
প্রথম ভাগ 10
ইরানী জাতির দৃষ্টিতে ইসলাম 10
আমরা এবং ইসলাম 11
‘ মিল্লাত ’ ( জাতি) শব্দের অর্থ 17
ইসলামের মানদণ্ড 33
ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ 37
ফার্সী ভাষা 67
শিয়া মাযহাব 75
ইরানীদের শিয়া প্রবণতা 90
দ্বিতীয় ভাগ 97
ইরানে ইসলামের অবদান 97
অনুগ্রহ নাকি বিপর্যয় 98
রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে যারথুষ্ট্র ধর্ম 123
খ্রিষ্টধর্ম 128
মনী ধর্ম (মনাভী) 134
মাযদাকী ধর্ম 138
বৌদ্ধধর্ম 145
আর্য বিশ্বাসসমূহ 149
ইরান ও মিশরের গ্রন্থাগারসমূহে অগ্নি সংযোগ 244
ইরানে ইসলামের কর্মতালিকা 283
ইসলামের প্রতি ইরানের অবদান 297
ইরানীদের ইসলামী কর্মকাণ্ড 311
ভারতবর্ষে ইরানীদের কর্মকাণ্ড 314
ইসলামের প্রচার ও প্রসার 338
চীনে ইসলামের প্রবেশ ও বিস্তার 349
কেরাআত ও তাফসীর 372
আহলে সুন্নাতের তাফসীর গ্রন্থসমূহ : 384
হাদীসশাস্ত্র 390
আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহ ও এগুলোর রচয়িতা 397
ফিকাহ্শাস্ত্র 400
আহলে সুন্নাতের ফকীহ্গণ 427
প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফকীহ্ 431
আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব 434
কালামশাস্ত্র 443
সুন্নী কালামশাস্ত্রবিদগণ 447
দর্শন ও প্রজ্ঞা 450
প্রথম স্তরের দার্শনিক 453
দ্বিতীয় স্তরের দার্শনিকগণ 456
তৃতীয় স্তরের দার্শনিকগণ 461
চতুর্থ স্তরের দার্শনিকগণ 468
এরফান ও তাসাউফ 547
এরফান ও ইসলাম 551
শিল্প ও সাহিত্য 587