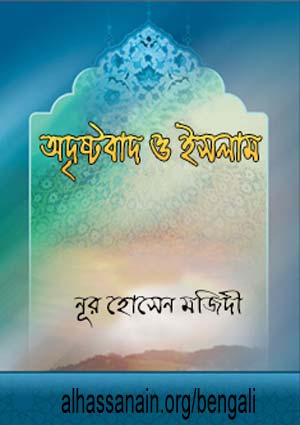অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম
নূর হোসেন মজিদী
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ভূমিকা
আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে মানুষের রয়েছে এক অনন্য অবস্থান। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট এটা সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত যে , প্রাণী প্রজাতিসমূহের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব যতোটা তার সৃজনশীলতার কারণে , তার চেয়ে অনেক বেশী তার বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) ও ইচ্ছাশক্তির কারণে। এ দু’ টি বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ তার সহজাত প্রকৃতিকে পরাভূত করতে সক্ষম। যেমন: কোনো ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে তার ভক্ষণোপযোগী কোনো খাদ্য থাকলে এবং তা খাবার পথে কোনো বাধা বা বিপদাশঙ্কা না থাকলে সে অবশ্যই তা খাবে ; সে তা খাবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মানুষ এর ব্যতিক্রম। সে চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও তার সামনে নির্ঝঞ্ঝাট খাদ্যোপকরণ পেয়েও না খেয়ে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হতে পারে।
বস্তুতঃ মানুষের কাজকর্ম তার ধ্যানধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসের অনুবর্তী। সে যদি নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায়ও সুস্বাদু খাদ্যোপকরণ উপেক্ষা করে মৃত্যুকে স্বাগত জানায় , তো তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসের কারণেই তা করে থাকে। অতএব , তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাস যদি সঠিক হয় তাহলে তা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে এবং তা যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তা তাকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে ঠেলে দেবে।
যে সব বিষয় গোটা মানব জাতির কর্ম ও আচরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা থাকা-নাথাকা সংক্রান্ত ধারণা। এ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ মানুষই তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস করে যে , মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বলতে কিছুই নেই , বরং তার জন্ম-মৃত্যু এবং সারা জীবনের কার্যাবলী ও সুখ-দুঃখ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে বা তার প্রতিটি কাজই আল্লাহ্ তা‘ আলা তার দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে প্রমাণিত হয় যে , তারা নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী। বস্তুতঃ তাদের তাত্ত্বিক বিশ্বাস তাদের কর্ম ও আচরণের ওপর খুব কমই ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে , বরং তা কেবল ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাবই বিস্তার করে থাকে।
মানব জাতিকে , বিশেষ করে মুসলমানদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রশ্নটির সঠিক সমাধান উদ্ভাবন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই অত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।
আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনেক বড় বড় মনীষী এ বিষয়ে বহু মূল্যবান বই-পুস্তক রচনা করেছেন। চাইলে এ সব বই-পুস্তক থেকে কোনোটি অনুবাদ করা যেতো। কিন্তু কয়েকটি কারণে কোনো গ্রন্থের অনুবাদ না করে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক গ্রন্থ রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।
প্রথমতঃ বাংলা ভাষার তুলনায় আরবী ও ফার্সী ভাষায় দ্বীনী জ্ঞানচর্চা ব্যাপকতা ও মান উভয় বিচারেই উন্নততর। ফলে উক্ত দুই ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের ইসলামী বিষয়াদি সংক্রান্ত আলোচনার গ্রহণক্ষমতাও উন্নততর। এ কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত বই-পুস্তকাদির বিষয়বস্তু বিন্যাস ও আলোচনার পদ্ধতি এমন যে , তার অনুবাদ বাংলাভাষী অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার জন্যই সহজবোধ্য হবে না।
দ্বিতীয়তঃ মানুষের কোনো লেখাই লেখকের একান্ত নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। এ কারণে বহু মনীষী লেখকের একই বিষয়ক লেখার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য অনেক বেশী। তাই যার বক্তব্য বা প্রতিপাদ্যের সাথে শতকরা একশ’ ভাগ একমত হওয়া যাবে এমন কোনো গ্রন্থ নির্বাচন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার , বরং প্রায় অসম্ভব।
তৃতীয়তঃ কালের প্রবাহে সব সময়ই নব নব যুগজিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কারণেই পরবর্তী কালে জাগ্রত জিজ্ঞাসা সমূহের জবাব পূর্ববর্তী মনীষীদের লেখায় পাবার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম।
এসব কারণে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।
আলোচ্য বিষয়ে উপসংহারে উপনীত হওয়ার জন্যে চারটি সূত্র থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে , তা হচ্ছে: বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) , কোরআন , হাদীছ ও মনীষীদের মতামত। এর মধ্যে‘ আক্বল্ হচ্ছে সর্বজনীন মানদণ্ড যা আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝেই নিহিত রয়েছে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র মানদণ্ড। অন্যদিকে‘ আক্বল্ কোরআন মজীদের ঐশিতায় ও বিকৃতিহীনতায় উপনীত হয়। তাই মুসলমানদের জন্য এ দু’ টি হচ্ছে বিতর্কাতীত মানদণ্ড। অন্যদিকে স্বয়ং কোরআন মজীদ‘ আক্বলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।
কোরআন মজীদ জীবন ও জগতের মৌলিকতম সত্য অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ব , পরকালীন জীবনের সত্যতা এবং নবুওয়াত ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ) প্রশ্নে‘ আক্বলের নিকট আবেদন করেছে। কোরআন মজীদ এসব বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে অন্ধভাবে মেনে নিতে বলে নি ; বললে তাতে কেউ সাড়া দিতো না ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকতো। এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে , কোরআন মজীদ স্বীয় দাবীর সপক্ষে বিচারবুদ্ধির দলীল (যুক্তি) উপস্থাপন করেছে এবং এরপরও যারা তা গ্রহণ করে নি তাদেরকে বার বার বলেছে:افلا تعقلون (অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না ?) এমনকি যারা বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) প্রয়োগ করে না , কোরআন মজীদ তাদেরকে‘ নিকৃষ্টতম পশু’ (شر الدوابّ ) বলে অভিহিত করেছে (সূরাহ্ আল-আনফাল্: ২১-২২)।
যারা সঠিকভাবে‘ আক্বলের প্রয়োগ করে ও তার রায়কে মেনে নেয় তারা জীবন ও জগতের মহাসত্যগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য। ফলে তারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত এবং সর্বশেষ , পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে কোরআন মজীদকে মেনে নেয়। অন্যদিকে‘ আক্বল্ জীবন ও জগতের যে মহাসত্যগুলোতে উপনীত হয় কোরআন মজীদ সে সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ধারণা প্রদান করে। আর যেহেতু এ গ্রন্থ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে সেহেতু এতে প্রদত্ত ধারণা পুরোপুরি অকাট্য-যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। (অবশ্য কতক আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ প্রশ্নে মতপার্থক্য হতে পারে , তবে বিস্তারিত পর্যালোচনায় সে সব মতপার্থক্যের নিরসন অবশ্যম্ভাবী।)
জীবন ও জগতের মহাসত্যসমূহ (উছূলে দ্বীন বা দ্বীনের মূল ভিত্তিসমূহ ও তার শাখা-প্রশাখা সমূহ) সম্বন্ধে হাদীছে ও মনীষীদের লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মনীষীদের বক্তব্য বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদের পাশাপাশি হাদীছ ও তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ওপরও ভিত্তিশীল। মূলতঃ শেষোক্ত দু’ টি সূত্রের ওপর নির্ভর করার কারণেই দ্বীনের মূল ভিত্তিসমূহের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলী ও কর্ম সংক্রান্ত ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা‘ মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা থাকা-নাথাকা’ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে শুধু মতপার্থক্যই ঘটে নি , বরং তাঁদের অনেকে পরস্পর একশ’ আশি ডিগ্রী বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। এ সব মতামত পর্যালোচনা করে সঠিক উপসংহারে উপনীত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ , সে আলোচনা হবে যেমন জটিল , তেমনি অত্যন্ত দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ এবং তাকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে হলে বিশালায়তন গ্রন্থ রচনা করতে হবে-যা থেকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের উপকৃত হতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম।
তাছাড়া মনীষীদের সাথে সাধারণ মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভাবাবেগের সম্পর্ক জড়িত আছে বিধায় তাঁদের মতামতের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা-সমালোচনা গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি খুব কম লোকেরই আছে। অন্যদিকে মনীষীদের মতামত যেহেতু মৌলিক দলীল নয় , বরং মৌলিক দলীল অবলম্বনে কৃত আলোচনা , সেহেতু তাঁদের মতামত টেনে না এনে মৌলিক দলীলের সাহায্যে প্রশ্নের জবাব সন্ধানই সঠিক পন্থা।
বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদ হচ্ছে মৌলিকতম ও নির্ভুলতম অকাট্য দলীল। দলীল হিসেবে হাদীছের মর্যাদা এতদুভয়ের পরে। তাছাড়া বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদ থেকে দিকনির্দেশ পাওয়া যতো সহজ , হাদীছ থেকে দিকনির্দেশ পাওয়া ততো সহজ নয়। বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদ যেরূপ অকাট্য , সীমিত সংখ্যক মুতাওয়াতির্ হাদীছ (যা প্রতি স্তরে এমন বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত যাদের পক্ষে মিথ্যা রচনার জন ঐক্যবদ্ধ ও একমত হওয়া বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব) বাদে হাদীছ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার তদ্রূপ অকাট্য নয়।“ খবরে ওয়াহেদ” নামে অভিহিত এসব হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারে সঠিক (ছ্বহীহ্) হাদীছের মাঝে কিছু জাল ও বিকৃত হাদীছের প্রবেশ ঘটার বিষয়টি অনস্বীকার্য। তাই হাদীছ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাছাই করা সত্ত্বেও মনীষীদের মধ্যে কতক হাদীছের যথার্থতা প্রশ্নে মতপার্থক্য হয়েছে। একজন যে হাদীছকে ছ্বহীহ্ বলেছেন আরেক জন তাকে জাল বলেছেন। এ থেকেই দু’ জনের রায় দু’ রকম হয়েছে।
এখানে হাদীছ সম্পর্কে দু’ টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উল্লেখ অপরিহার্য। প্রথমতঃ কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য সম্বলিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ শরী‘ আতের খুটিনাটি বিস্তারিত বিধানের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের শর্তসাপেক্ষ গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির (উছূলে দ্বীন) শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের অকাট্যতা প্রশ্নাতীত নয় , সেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে (ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে) খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণ করা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে এরূপ বিষয়ে যখন পরস্পর বিরোধী হাদীছ পাওয়া যায় তখন দুই মতের মধ্যকার অন্ততঃ একটি মতের সমর্থনকারী হাদীছের জাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা থাকা-নাথাকা সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী মতের উৎস বা পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে এ ধরনের পরস্পরবিরোধী হাদীছ সমূহ। কেউ যখন এক মতের সমর্থনকারী একটি হাদীছ গ্রহণ করেছেন ও তার বিপরীত মতের হাদীছকে জাল বলে গণ্য করে প্রত্যাখ্যান করেছেন , তখন অন্য একজন ঠিক এর বিপরীত আচরণ করেছেন। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীছগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলে একদিকে যেমন তা বিশাল আয়তন ধারণ করবে , অন্যদিকে তাতে ফয়সালায় উপনীত হওয়া যাবে না। কারণ , অতীতের মনীষীগণ যেভাবে ঐসব হাদীছ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন তার সাথে একটি নতুন মতপার্থক্য যুক্ত হবে মাত্র।
সর্বোপরি কথা হচ্ছে , অকাট্য দলীল‘ আক্বল্ ও কোরআন মজীদের সাহায্যে যেখানে কোনো প্রশ্নের সঠিক জবাব মেলে সেখানে পরস্পর বিরোধী হাদীছ নিয়ে সুদীর্ঘ পর্যালোচনার প্রয়োজন কী ?
এ কারণেই অত্র গ্রন্থে‘ আক্বায়েদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন ক্ষমতা থাকা-নাথাকা বিষয়ক আলোচনায় শুধু‘ আক্বল্ ও কোরআন মজীদের দলীলের ওপরই নির্ভর করেছি।
আল্লাহ্ রাব্বুল‘ আলামীন অত্র গ্রন্থকে এর লেখক , প্রকাশ-প্রচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ এবং পাঠক-পাঠিকাদের হেদায়াত ও পরকালীন নাজাতের জন্য সহায়ক করে দিন। আমীন।
ঢাকা বিনীত
১৫ই জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০ নূর হোসেন মজিদী
২৮শে বৈশাখ ১৪১৬
১১ই মে ২০০৯।
কৃতজ্ঞতা
অত্র গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্র হচ্ছে কেবল বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) ও কোরআন মজীদ। অন্য কোনো কোনো সূত্র থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যালোচনার সুবিধার্থে মাত্র , প্রামাণ্য দলীল হিসেবে নয়। তবে কতক মনীষীর লেখা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থাবলী আমাকে এ বিষয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁদেরকে শুভ প্রতিদান দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলার দরবারে বিশেষভাবে দো‘ আ করছি। তবে গ্রন্থটিকে যাতে কেবল‘ আক্বল্ ও কোরআন মজীদের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয় সে উদ্দেশ্যে এখানে তাঁদের নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।
অত্র গ্রন্থে কোরআন মজীদের যে সব আয়াত উদ্ধৃত করেছি সে সবের অনুবাদ কোনো বিশেষ অনুবাদগ্রন্থ থেকে গ্রহণ না করে সরাসরি অনুবাদ করাকেই উত্তম মনে করেছি এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানকে প্রাধান্য দিয়েছি। তবে কিছু কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বিভিন্ন আরবী , ফার্সী , ইংরেজী ও বাংলা তাফসীর ও তরজমা এবং কোরআনিক পরিভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছি। সর্বোপরি , আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত খুঁজে বের করার জন্য মুহাম্মাদ ফুআদ‘ আবদুল বাক্বী প্রণীত আল্-মু‘ জামুল্ মুফাহরিস্ লি-আলফাযিল্ কোরআানিল্ কারীম্ থেকে সহায়তা নিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে‘ আশায়েরী মতের উদ্ভবের ঘটনা ও অন্য যে ক’ টি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লিখিত হয়েছে তা-ও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।
আল্লাহ্ তা‘ আলা সংশ্লিষ্ট মুফাসসির , গ্রন্থকার ও অনুবাদকগণকে তাঁদের মহান খেদমতের শুভ প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।
ঢাকা বিনীত
১৫ই জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০ নূর হোসেন মজিদী
২৮শে বৈশাখ ১৪১৬ । ১১ই মে ২০০৯।
অদৃষ্টবাদ: বিশ্বাস বনাম আচরণ
আমাদের সমাজে ইসলামী পরিভাষা“ তাক্বদীর্” (تقدیر )-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়‘ ভাগ্য’ বা‘ ভাগ্যলিপি’ । সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে , আমাদের ভালো-মন্দ সব কিছুই আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এর ভিত্তি হচ্ছে“ ঈমানে মুফাছ্বছ্বাল্” (বিস্তারিত ঈমান) নামে শৈশবে মুসলমানদেরকে যে বাক্যটি মুখস্ত করানো হয় তার অংশবিশেষ-যাতে বলা হয়:والقدر خيره و شره من الله تعالی (আর ভাগ্য ; এর ভালো ও মন্দ আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত) , যদিও কোরআন মজীদের কোথাওই এ বাক্যাংশটি নেই।
এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে , ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ও তার শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির (عقل ) রায় বা কোরআন মজীদের দলীল থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে কোরআন মজীদ বা বিচারবুদ্ধির রায় নয় এমন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসে যদি মুসলমানদের মধ্যে‘ মতৈক্য’ (ইজমা‘ -اجماع ) না থাকে , বরং বিতর্ক থাকে , তাহলে তা কিছুতেই ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ ও তার শাখা-প্রশাখার অন্যতম বলে গণ্য হতে পারে না।
অবশ্য কোনো কোনো হাদীছে এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে যে , মানবশিশু জন্মগ্রহণের পূর্বেই অর্থাৎ ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে থাকাকালেই আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা এসে তার ভাগ্যলিপিতে তার পুরো ভবিষ্যত জীবনের সব কিছুই লিখে দিয়ে যায় ; এমনকি সে নেককার হবে , নাকি গুনাহ্গার হবে তথা বেহেশতে যাবে , নাকি দোযখে যাবে তা-ও লিখে দিয়ে যায়।
এ ধরনের হাদীছ মুসলিম উম্মাহর সকল ধারার দ্বীনী চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিকট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নয় এবং তা মুতাওয়াতির্ (প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) নয় , বরং এগুলো খবরে ওয়াহেদ্ (অন্ততঃ প্রথম স্তরে অর্থাৎ ছ্বাহাবীদের স্তরে কম সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীছ। আর খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উতরে যাওয়া সাপেক্ষে আহ্কামের খুটিনাটি নির্ধারণে এবং অন্য অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানগত বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হলেও ঈমানের মৌলিক বিষয়াদিতে ও এর শাখা-প্রশাখায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর ছ্বাহাবীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। এমতাবস্থায় ঈমানের অন্যতম মৌলিক গুরুত্ব সম্পন্ন কোনো বিষয়ে তাঁর দেয়া বক্তব্য বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র দু’ চার জন ছ্বাহাবীর জানা থাকবে , অন্যদের জানা থাকবে না অর্থাৎ তা মুতাওয়াতির্ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে না এটা অসম্ভব।
এটা সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য যে , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকাল এবং ছ্বিহাহ্ সিত্তাহ্ (ছয়টি নির্ভুল হাদীছ্ গ্রন্থ) হিসেবে অভিহিত হাদীছগ্রন্থ সমূহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সংকলনের মধ্যবর্তী দুই শতাধিক বছর সময়ের মধ্যে বহু মিথ্যা হাদীছ রচিত হয়েছিলো। হাদীছ সংকলনকারী ইমামগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্বাচিত হাদীছের সংকলন করা সত্ত্বেও এ সব সংকলনে কতক জাল হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে যে সব হাদীছের বক্তব্য‘ আক্বল্-এর অকাট্য রায় ও কোরআন মজীদের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক তা জাল হবার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।
অতএব , এটা সন্দেহাতীত যে , ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যকার কোনো বিষয়ে বা তার শাখা-প্রশাখায় খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এ ধরনের হাদীছের ভিত্তিতে অদৃষ্টবাদকে ঈমানের অন্যতম মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করে নেয়া হয়েছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেকের মন-মগয থেকেই শৈশবে শেখানো অদৃষ্টবাদিতার এ অন্ধ বিশ্বাস উবে যায় এবং মানুষের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস তার স্থান দখল করে নেয়। তবে বর্তমান প্রজন্মের মনে মানুষের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসের পিছনে প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদের প্রভাব সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলার অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁর নিকট জবাবদিহিতা সম্পর্কে উদাসীনতা সংমিশ্রিত থাকে।
অন্যদিকে যারা অদৃষ্টবাদের প্রবক্তা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তা ও আচরণে কিন্তু অদৃষ্টবাদের প্রতিফলন ঘটে না। বরং তারা কার্যতঃ কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী । কেবল‘ আক্বা’ এদী বিতর্কের বেলায়ই তারা অদৃষ্টবাদের পক্ষে যুক্তি দেখায়। এভাবে আমাদের সমাজে চিন্তা ও আচরণের মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে মুসলমানদের কাছ থেকে যেখানে আল্লাহ্ তা‘ আলার ওপর নির্ভরতা সহকারে কর্মমুখরতাই বাঞ্ছনীয় সেখানে তার পরিবর্তে দেখা যায় যে , সমাজের একটি অংশ স্থবিরতা ও হতাশায় নিমজ্জিত এবং অপর অংশটি পুরোপুরি বস্তুবাদী ধ্যানধারণা ও পার্থিবতায় নিমজ্জিত। এ উভয় ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক চিন্তা ও আচরণে উত্তরণের জন্য মানুষের জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রণের কারক সমূহ ও সে সবের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা অপরিহার্য।
কোরআন মজীদে“ ক্বাদর্ ” ও “ তাক্বদীর্ ” পরিভাষা
আলোচনার শুরুতেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে , মুসলিম সমাজের বেশীর ভাগ অংশেই শৈশব কালেই“ ঈমানে মুফাছ্বছ্বাল্” (বিস্তারিত ঈমান) নামক বাক্যে‘ ভাগ্যের’ ভালো-মন্দের কথা শিক্ষা দেয়া হয়। উল্লিখিত বাক্যে‘ ভাগ্য’ বুঝাবার জন্যالقدر (আল্-ক্বাদর্) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে‘ ভাগ্যলিপি’ বুঝাবার জন্যتقدير (তাক্বদীর্) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। তাই আমরা আলোচনার শুরুতেই দেখতে চাই যে , কোরআন মজীদে এ পরিভাষা দু’ টি‘ ভাগ্যলিপি’ বা‘ ভাগ্যনির্ধারণ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান থেকে যে জবাব পাওয়া যায় তা না-বাচক।
“ ক্বাদর্” শব্দটি একটি ক্রিয়াবিশেষ্য। এ শব্দটি এবং এ থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী (ক্রিয়াপদ , বিশেষ্য ও বিশেষণ) কোরআন মজীদে মোট একশ’ বত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবগুলো শব্দ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা খুবই দীর্ঘায়িত হবে। তাই আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবো।
কোরআন মজীদে“ ক্বাদর্” শব্দটি ও তা থেকে সরাসরি নিষ্পন্ন পদসমূহ‘ শক্তি’ ,‘ মর্যাদা ও মূল্যায়ন’ ,‘ পরিমাপ করণ’ ,‘ যথাযথভাবে নির্ধারণ’ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং“ আল্-ক্বাদর্” শব্দটি কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-ক্বাদর্-এ তিন বার উল্লিখিত হয়েছে। এ সূরায় শব্দটি তিন বারই“ লাইলাতুল্ ক্বাদর্” পরিভাষার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ‘ মহিমান্বিত রজনী’ ।
এ ছাড়া তিনটি সূরায় আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রসঙ্গে“ ক্বাদর্” শব্দটি এবং এতদসহ এ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :
( وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ )
“ আর তারা আল্লাহকে তাঁর যথোপযুক্ত মূল্যায়নে মূল্যায়ন করে নি।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আাম্: ৯১ ; আল্-হাজ্জ: ৭৪ ; আয্-যুমার্: ৬৭)
এছাড়া আরো একটি আয়াতে“ ক্বাদর্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে:
( إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا )
“ অবশ্যই আল্লাহ্ তার (তাক্ব্ওয়া অবলম্বনকারীর) কাজকে পূর্ণতায় উপনীতকারী ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের জন্যই“ ক্বাদর্” তৈরী করে রেখেছেন।” (সূরাহ্ আত্ব্-ত্বালাক্ব: ৩)
এই শেষোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে , এখানে আল্লাহ্ তা‘ আলা“ ক্বাদর্” শব্দটিকে‘ মূল্যায়ন’ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রতিটি জিনিসেরই মূল্যায়ন নির্ধারণ করে রেখেছেন বিধায়ই মুত্তাক্বীর কাজকে পূর্ণতায় উপনীত করে দেবেন।
দেখা যাচ্ছে যে , কোরআন মজীদে“ ক্বাদর্” ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر )টি কোথাওই মানুষের ভাগ্যনির্ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। অনুরূপভাবে এ ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদগুলোও ভাগ্যনির্ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। বরং ক্রিয়াপদগুলো‘ মূল্যায়ন করা’ ,‘ পরিমাপ করা’ (পরিমাণ মতো প্রদান) ,‘ সক্ষম হওয়া’ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ , এরশাদ হয়েছে:
( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ )
“ আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্ক্ব প্রশস্ত করে দেন এবং পরিমাপ করে (বা তার পরিমাণ নির্ধারণ করে) দেন।” (সূরাহ্ আর্-রাদ্: ২৬) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলা যাকে চান তার প্রাপ্যের চেয়েও তাকে বেশী রিয্ক্ব প্রদান করেন এবং সে বেশী পরিমাণটা সুনির্দিষ্ট করে দেন। অবশ্য অনেক মুফাসসিরের মতে , এখানেيقدر (পরিমাপ করে দেন) কথাটি যাদেরকে রিয্ক্ব প্রশস্ত করে দেন তাদের ব্যতীত অন্যদের সাথে সম্পর্কিত এবং এ কথাটির মানে হচ্ছে সে প্রকৃতই যা পাবার হক্ব্দার তাকে তা-ই প্রদান করেন অর্থাৎ তার চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী ও প্রাকৃতিক কার্যকারণের আওতায় তার যা প্রাপ্য তিনি তাকে তা-ই প্রদান করেন , বেশী দেন না।
অনেকে এই শেষোক্ত আয়াতে উল্লিখিতيقدر ক্রিয়াপদের অর্থ করেন‘ কমিয়ে দেন’ । কিন্তু এ ক্রিয়াপদ থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণ করার কোনো আভিধানিক বা ব্যাকরণগত ভিত্তি নেই। এরপরও , এমনকি যুক্তির খাতিরে যদি এ অর্থকে সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় , তাহলেও এ থেকে এ ক্রিয়াপদের মূল অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ্য“ ক্বাদর্” শব্দ থেকে‘ ভাগ্য নির্ধারণ’ অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলা যাকে চান তার রিয্ক্ব বৃদ্ধি করে দেন এবং যাকে চান তার রিয্ক্ব কমিয়ে দেন-এ কথার মানে এ নয় যে , তিনি মানুষকে সৃষ্টির সময় তার ভাগ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক্ব্ লিখে দিয়েছেন। কারণ , পরম জ্ঞানী আল্লাহ্ তা‘ আলা যদি আগেই কোনো কিছু নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন , তো পরে তা বৃদ্ধি বা হ্রাস করার কোনো কারণই নেই। কারণ , স্বীয় নির্ধারিত পরিকল্পনায় পরবর্তীতে পরিবর্তন সাধন অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী সত্তার কাজ-যার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ত্রুটি ছিলো বিধায়ই সে পরবর্তীতে তাতে পরিবর্তন সাধন করে তা কার্যকর করে। আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে তার প্রাপ্য হতে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেন-এর মানে হচ্ছে তার মূল প্রাপ্য স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দেন নি , বরং তার চেষ্টাসাধনা ও প্রাকৃতিক কার্যকারণের ফলেই তা নির্ধারিত হয়েছিলো , কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশী বা কম দেয়াতেই তার বা সমষ্টির কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন বলেই দয়া করে তাকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশী বা কম দিয়েছেন।
অনুরূপভাবে“ ক্বাদর্” ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে নিষ্পন্ন অপর একটি শব্দ (এটিও ক্রিয়াবিশেষ্য) হচ্ছেتقدير (তাক্বদীর্)-যে শব্দটিকে ক্রিয়াবিশেষ্য হিসেবে নয় , বরং সাধারণ বিশেষ্য হিসেবে মানুষের‘ ভাগ্য’ বা‘ ভাগ্যলিপি’ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদে কোথাওই এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। যেমন , এ শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতে প্রাকৃতিক বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:
( وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )
“ আর তিনি (আল্লাহ্) রাত্রিকে আরামদায়ক এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব স্বরূপ (বর্ষ ও তিথি গণনায় সহায়ক) বানিয়েছেন। এ হচ্ছে মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ (তাঁর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান)। ” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আাম্: ৯৬)
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:
( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا )
“ তারা রৌপ্যপাত্রকে (তাতে রক্ষিত/ প্রদত্ত পানীয়কে) পরিমাণ করবে (পূর্ণ করবে) ঠিক পরিমাণ করার মতোই (অর্থাৎ ঠিক মতো পূর্ণ করবে ; কমও হবে না , উপচেও পড়ব না)। ” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ১৬)
আরো এরশাদ হয়েছে:
( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا )
“ আর তিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাণ (নির্ধারণ) করে দিয়েছেন ঠিক পরিমাণ করার মতোই (অর্থাৎ যথাযথভাবে)। ” (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্: ২) নিঃসন্দেহে এখানে পরিমাণ নির্ধারণ বলতে প্রতিটি জিনিসের গঠন-উপাদান সমূহ ও তার অনুপাত বুঝানো হয়েছে।
আল্লাহ্ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন:
( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ )
“ আর আমি চন্দ্রের জন্য মনযিল সমূহ (চন্দ্রকলা বা তিথি সমূহ) নির্ধারণ করে দিয়েছি।” (সূরাহ্ ইয়া-সীন্: ৩৯)
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:
( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ )
“ আর আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি পরিমাণ মতো।” (সূরাহ্ আল্-মু’ মিনূন: ১৮)
উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতের সবগুলোতেই জড়বস্তু সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে , মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণশীল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কে কথা বলা হয় নি। তবে‘ তিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন’ (خلق کل شیء ) বলতে যদি মানুষ সহ প্রাণশীল সৃষ্টিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় সে ক্ষেত্রেও পরিমাণ নির্ধারণের মানে হবে বিভিন্ন প্রাণীর গঠন-উপাদান ও সে সবের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া ; প্রতিটি প্রাণীপ্রজাতির প্রতিটি সদস্যের সারা জীবনের সব কিছু নির্ধারণ করে দেয়া নয়।
“ ক্বাদর্” ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী সম্বলিত কোরআন মজীদের সবগুলো আয়াত নিয়ে আলোচনা করলেও কোথাওই এটা পাওয়া যাবে না যে ,“ মানব প্রজাতিকে সৃষ্টির পূর্বে বা সৃষ্টির সমসময়ে তার‘ ভাগ্যলিপি’ বা‘ ভাগ্য নির্ধারণ’ অর্থে“ ক্বাদর্” বা“ তাক্বদীর্” অথবা এর কোনোটি থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করেন বা তার দ্বারা সম্পাদন করিয়ে নেন-এ অর্থেও উপরোক্ত শব্দ বা তা থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলীর কোনোটি ব্যবহৃত হয় নি।
অদৃষ্টবাদের প্রকারভেদ
অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস কেবল মুসলমানদের মধ্যেই প্রচলিত নয় , অমুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতের অনুসারীদের অদৃষ্টবাদী চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অদৃষ্টবাদী চিন্তা ও বিশ্বাসকে সংক্ষেপে চার প্রকরণে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।
এক ধরনের অদৃষ্টবাদী চিন্তা ও বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টিকর্মের সূচনার পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন অনন্ত কাল পর্যন্ত এ বিশ্বলোকে কী কী ঘটনা সংঘটিত হবে এবং মানুষ সহ প্রাণীকুলের প্রত্যেকে কী কী করবে ; কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা এবং কোনো প্রাণশীল সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মও এর বাইরে নয়।
দ্বিতীয় প্রকারের অদৃষ্টবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রতি মুহূর্তের ছোটো-বড় প্রতিটি ঘটনাই সরাসরি সংঘটিত করাচ্ছেন এবং তিনি যখন যা কিছু ইচ্ছা করছেন তখন তা-ই সংঘটিত হচ্ছে।
তৃতীয় ধরনের অদৃষ্টবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘ আলা মাঝে মাঝে সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। যেমন: প্রতি বছর শবে বরাতের রাতে তিনি প্রত্যেকের জন্য তার পরবর্তী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন যা পরবর্তী শবে কদর থেকে কার্যকর করা হয়। এটা অনেকটা বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বাজেটের ন্যায়।
চতুর্থ ধরনের অদৃষ্টবাদ অনুযায়ী , প্রতিটি প্রাণী , বিশেষতঃ মানুষ মাতৃগর্ভে আসার কয়েক দিন পর প্রাথমিক ভ্রূণ থাকাকালে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে তার আয়ু , সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও বেহেশতী বা দোযখী হওয়া সহ তার ভবিষ্যত সারা জীবনের সকল কাজকর্ম ও অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়-যার কিছুতেই অন্যথা হয় না।
কিন্তু এ চার ধরনের অদৃষ্টবাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকলেও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে , অধিকাংশ মুসলমানই একই সাথে এ চার ধরনের বিশ্বাস পোষণেরই দাবী করে থাকে। তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয় যে , তাদের বিশ্বাসের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং একই সাথে তাদের আচরণ ও দাবীকৃত এ সবগুলো বিশ্বাসের মধ্যেও পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে। তবে বিভিন্ন ধরনের অদৃষ্টবাদের মধ্যে যে বিষয়টি অভিন্ন তা হচ্ছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসহীনতা।
উপরোক্ত সবগুলো অদৃষ্টবাদী বিশ্বাস অনুযায়ীই যা কিছু হচ্ছে তার সবই স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলা করছেন বা করাচ্ছেন ; মানুষ নিমিত্তের ভাগী মাত্র। মানুষ নিজে কিছুই করে না এবং করার ক্ষমতাও রাখে না ; তাকে দিয়ে করানো হয়। তাকে দিয়ে যা করানো হয় সে তা-ই করে ; সে তা-ই করতে বাধ্য।
অদৃষ্টবাদীদের মতে , এমনকি কে বেহেশতে যাবে ও কে দোযখে যাবে তা-ও আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টিকর্মের সূচনার পূর্বে অথবা প্রাণীর ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় নির্ধারণ করে রেখেছেন। আবার এ ধরনের বিশ্বাসও আছে যে , পূর্বনির্ধারণ বা কর্মফল বলতে কিছু নেই , বরং তিনি তাঁর নিঃশর্ত অধিকারের বদৌলতে যাকে ইচ্ছা বেহেশতে নেবেন , যাকে ইচ্ছা দোযখে নিক্ষেপ করবেন।
আবার কতক অদৃষ্টবাদীর মতে , বিষয়টি এমন নয় যে , যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে দোযখে নেবেন এবং যে মন্দ কাজ করবে তিনি তাকে বেহেশতে নেবেন , বরং তিনি যাকে বেহেশতে নিতে চান তাকে ভালো কাজের তথা বেহেশতে যাবার উপযোগী কাজের সুযোগ দেন এবং যাকে তিনি দোযখে নিতে চান সে মন্দ কাজ তথা দোযখে যাবার উপযোগী কাজের সুযোগ পায়।
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি একটি অনস্বীকার্য সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অদৃষ্টবাদীদের বক্তব্য এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা যাকে দিয়ে ভালো কাজ করাবার ইচ্ছা করেন বা যার জন্য তার সৃষ্টির পূর্বেই ভালো কাজ নির্ধারণ করে রেখেছেন সে-ই ভালো কাজের ইচ্ছা করবে এবং স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করবে , অন্যদিকে তিনি যাকে দিয়ে মন্দ কাজ করাবার ইচ্ছা করেন বা যার জন্য তার সৃষ্টির পূর্বেই মন্দ কাজ নির্ধারণ করে রেখেছেন সে অবশ্যই মন্দ কাজের ইচ্ছা করবে এবং স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ সম্পাদন করবে। অর্থাৎ তাদের মতে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে দিয়ে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ তথা বেহেশতে যাবার উপযোগী কাজ ও দোযখে যাবার উপযোগী কাজ করিয়ে নেন। অতএব , তাদের মত মেনে নিলে এটাই মেনে নিতে হয় যে , মানুষ যে শিরক্ করে , যুলুম-অত্যাচার করে , চুরি-ডাকাতি করে , এমনকি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় , এ সব কাজ আল্লাহ্ই মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেন। (সুব্হানাল্লাহে‘ আম্মা ইয়াছেফূন্-তারা আল্লাহর ওপর যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করছে তা থেকে তিনি পরম প্রমুক্ত।)
ইতিপূর্বে যেমন আভাস দেয়া হয়েছে , অদৃষ্টবাদীদের কতকের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা যেহেতু যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং যা ইচ্ছা তা-ই করার নিরঙ্কুশ অধিকার রাখেন সেহেতু তিনি তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার প্রমাণ করার জন্যে শেষ বিচারের দিনে কতক নেককার লোককে দোযখে নিক্ষেপ করবেন এবং কতক পাপী লোককে বেহেশতে পাঠাবেন।
বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদীদের এসব বিশ্বাস হচ্ছে ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস-যা সুস্থ বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় ও কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী।
অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বিচারবুদ্ধি যা অনুভব ও লক্ষ্য করে তা হচ্ছে এই যে , সে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির অধিকারী একটি স্বাধীন প্রাণী। যদিও সে পুরোপুরি স্বাধীন নয় ; তার কর্মের স্বাধীনতা বহু পার্থিব ও অপার্থিব উপাদানের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ , তবে সে স্বাধীনতাবিহীন যন্ত্রতুল্য নয়। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে সব সময়ই যালেম-শোষক ও স্বৈরাচারী শ্রেণী সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার জন্য অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণা প্রচার করেছে যা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করতো না।
তারা নিজেরা কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করতো। এ কারণে তারা কখনোই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতো না। বরং তারা সব সময়ই অত্যন্ত কর্মতৎপর থাকতো। নিজেদের বৈধ-অবৈধ স্বার্থ হাসিল ও সংরক্ষণ , অন্যদের বৈধ অধিকারের বিনাশ সাধন এবং অন্যায় বিরোধী যে কোনো চেষ্টা-সংগ্রামকে প্রতিরোধে , বরং টুটি টিপে হত্যা করার কাজে তারা খুবই সক্রিয় থাকতো। তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতায় তাদের সে বিশ্বাস ছিলো সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি শূন্য। এমনকি তাদের অধিকাংশই ছিলো এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও পরকালীন জীবন সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ আদৌ কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন কি নেই ; থাকলে এক , নাকি একাধিক-কোনটি হওয়া সম্ভব এবং মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জীবন আছে কি নেই , থাকলে সে জীবনে বর্তমান জীবনের জন্য জবাবদিহি করতে হবে কিনা-এ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে এবং বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্)-এর আলোকে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালায় উপনীত হতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না।
অবশ্য তাদের পক্ষে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করা বা মানুষকে তা অস্বীকার করতে বাধ্য করানো সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী করে তোলা তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য অপরিহার্য ছিলো এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বের অস্বীকৃতি জনসাধারণকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী রাখার জন্য অনুকূল হতো না। তাই তারা (শাসকগোষ্ঠী-যারা ধনসম্পদেরও একচ্ছত্র মালিক ছিলো) স্বার্থান্বেষী দুনিয়াপূজারী যাজক-পুরোহিতদের সহায়তায় কল্পিত দেবদেবীর অস্তিত্ব প্রচার করে এবং তাদেরকেই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে দাবী করে।
তাদের প্রচারিত এ ধরনের চিন্তা-বিশ্বাসে আদি স্রষ্টার বিষয়টি হয় অনুপস্থিত থাকতো , নয়তো তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করে হলেও মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সর্বময় ক্ষমতা তাঁর জন্য কল্পিত সন্তান-সন্ততিরূপ দেব-দেবীর বলে দাবী করা হতো। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রায়শঃই নিজেদেরকে তাদের কল্পিত তথাকথিত মহাশক্তিধর কোনো না কোনো দেবদেবীর বংশধর বলে দাবী করতো এবং আত্মবিক্রিত যাজক-পুরোহিতরা তাদের এ দাবীকে সত্য বলে প্রচার করতো। তারা দাবী করতো যে , দেব-দেবীদের অনুগ্রহেই তাদের বংশধর শাসকগোষ্ঠী শক্তি-ক্ষমতা ও ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছে এবং দেব-দেবীদের ইচ্ছায়ই সাধারণ মানুষ তাদের অধীনস্থ দাস ও প্রজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। অতএব , এটাই তাদের ভাগ্যলিপি ; এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে দেব-দেবীদের আক্রোশের শিকার হয়ে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।
শাসকগোষ্ঠী স্বয়ং অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতো না বলেই স্বীয় শক্তি-ক্ষমতা রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য ভাগ্যের বা কল্পিত দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বসে থাকতো না , বরং নিজেরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের রাজত্ব দখল করার বা তাদের আক্রমণ থেকে স্বীয় রাজত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করতো। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের ওপর নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালাবার লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দেব-দেবীর বংশধর বলে এবং স্বীয় কুলদেবতাকে অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর কুলদেবতার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বলে দাবী করতো। আর যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ সাধারণ জনগণকে এটাই বিশ্বাস করাতো যে , তাদের কুলদেবতা অধিকতর শক্তিশালী বিধায়ই তারা বিজয়ী হতে পেরেছে।
এর পাশাপাশি নাস্তিক লোকেরা মানুষকে নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করতো। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ও পরকালীন জীবনের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের কারণে তাদের এ চিন্তাধারার পরিণতি জীবনকে উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন গণ্যকরণ এবং হতাশাবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না এবং নয়।
কিন্তু যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ (‘ আঃ) আবির্ভূত হয়ে এ উভয় প্রান্তিক মতের অসারতা তুলে ধরেন এবং মানুষের সামনে এ ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক ধারণা উপস্থাপন করেন-যা সুস্থ বিচারবুদ্ধির কাছেও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা মানুষকে নিয়তির হাতের অসহায় পুতুল বলে গণ্য করেন নি , বরং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করেছেন এবং তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সঠিক কর্ম সম্পাদনের জন্য আহবান জানিয়েছেন। তাঁরা লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে , (যেহেতু তারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম সম্পাদনের এখতিয়ারের অধিকারী সেহেতু) তাদেরকে স্বীয় চিন্তা , কথা ও আচরণের হিসাব দিতে হবে।
তবে নবী-রাসূলগণ (আঃ) সেই সাথে তাদেরকে এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন যে , মানুষ ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট মানুষ ও এ বিশ্বজগতের ব্যাপারে উদাসীন নন। তিনি এ সব কিছুকে অর্থহীনভাবে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি। তাই তিনি সব কিছুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি রাখছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবায়িত হয় ; মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টি স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের এখতিয়ারের অপব্যবহার করে সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত করতে উদ্যত হলে কিছুতেই তিনি তাদেরকে সে সুযোগ দেবেন না। একইভাবে তিনি ব্যক্তিমানুষদের ব্যাপারেও অমনোযোগী নন।
মুসলিম সমাজে অদৃষ্টবাদ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারবাদ
হযরত আদম (‘ আঃ) থেকে শুরু করে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই (‘ আঃ) মানুষকে আল্লাহ্ তা‘ আলার নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পিত হয়ে চলার দিকে আহবান জানিয়েছেন। তাঁরা মানুষের নিকট প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও আচরণবিধি উপস্থাপন করেন ও তাদেরকে তা শিক্ষা দেন এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে তা পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত করেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ইসলাম পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে নাযিল হয় এবং এ জীবনবিধান সহ মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলার পরিপূর্ণ বাণী কোরআন মজীদকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলাই সামান্যতম বিকৃতি থেকেও রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেন (সূরাহ্ আল্-হিজর্: ৯)।
কোরআন মজীদ মানুষের গড়া অন্ধ‘ আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্ম ও মতাদর্শ সমূহের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং তাদেরকে বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) প্রয়োগের জন্য আহবান জানিয়েছে। কোরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে:افلا تعقلون (অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না ?) আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ )
“ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই বধির-বোবার দল যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না।” (সূরাহ্ আল-আনফাল্: ২২)
অবশ্য কোরআন মজীদ‘ আক্বলের অগম্য ক্ষেত্রসমূহের জন্য এবং‘ আক্বলের গম্য ক্ষেত্রসমূহেও তাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা ও তাকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দিয়েছে। আর হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ছিলেন জীবন্ত কোরআন ; তিনি কোরআন মজীদের প্রচার করেছেন , লোকদেরকে সেদিকে আহবান করেছেন , তা শিক্ষা দিয়েছেন , প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এবং স্বীয় জীবনে ও সমাজে তা বাস্তবায়িত করেছেন।
হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও আচরণ শিক্ষা দিয়ে যান তা তাঁর ওফাতের পরেও কয়েক দশক পর্যন্ত , বিশেষ করে বানী উমাইয়াহর শাসনামল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি অব্যাহত থাকে। তাই এ যুগে মুসলিম সমাজে অদৃষ্টবাদ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারবাদের উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। কিন্তু বানী উমাইয়াহর রাজতান্ত্রিক শাসনামল শুরু হবার পর অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারা গড়ে উঠতে থাকে। এর আভাস পাওয়া যায় ইয়াযীদের এতদসংক্রান্ত যুক্তি উপস্থাপনের মাঝে। হযরত ইমাম হোসেন (‘ আঃ)-এর বোন হযরত যায়নাব (সালামুল্লাহ্‘ আলাইহা)-এর সাথে বিতর্ককালে ইয়াযীদ তাঁকে বলেছিলো:“ আমরাই সত্যের ওপরে আছি ; আল্লাহ্ তোমার পিতার নিকট থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে আমার পিতাকে দিয়েছেন এবং হোসেনকে লাঞ্ছিত ও আমাকে সম্মানিত করেছেন।”
ইয়াযীদের দাবী ছিলো এবং তার অনুগতরা প্রচার করতো যে , আল্লাহর ইচ্ছা না হলে ইয়াযীদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হতে পারতো না। অবশ্য দ্বীনী বিষয়ে মানুষ যাদের কথা মেনে চলতো এবং যাদের নিকট থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করতো তাঁদের মধ্যে তখনো অদৃষ্টবাদিতা প্রবেশ করে নি। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতির কারণে অদৃষ্টবাদিতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। পরবর্তী কালে দ্বীনী চিন্তাবিদগণের কারো কারো মধ্যে এর প্রভাব কিছুটা হলেও প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণেই দ্বীনী ব্যক্তিত্ববর্গের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক বিষয়াদিকে সযত্নে এড়িয়ে চলার পথ বেছে নেন। অর্থাৎ দ্বীনী ব্যক্তিত্ববর্গের কতক যেখানে উমাইয়াহ্ বংশের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাংশ অহিংস অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে স্বাধীনভাবে দ্বীনী জ্ঞান-গবেষণা ও জনগণকে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন , তখন এই তৃতীয় অংশটি উক্ত উভয় পন্থা পরিহার করে‘ অরাজনৈতিক’ দ্বীনী চর্চায় মশগূল হন।
জাবারীয়্যাহ্ ও মু’ তাযিলী চিন্তাধারার আবির্ভাব
মুসলমানদের মধ্যকার‘ অরাজনৈতিক’ দ্বীনী চর্চায় মশগূল ধারার অনুসারীদের মধ্যে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অদৃষ্টবাদিতা একটি মতাদর্শরূপে গড়ে ওঠে যা‘ জাবারিয়্যাহ্’ মতবাদ নামে পরিচিত। এ ধারার সর্বপ্রথম বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন স্বনামখ্যাত ছূফী সাধক হাসান বাছ্বরী (২১-১১০ হিজরী)। অবশ্য তাঁর সময় অদৃষ্টবাদী চিন্তা-বিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটে নি। পরবর্তী কালে আবুল হাসান আশ্‘ আরীর (২৬০-৩২৪ হিজরী) মাধ্যমে অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।
হাসান বাছ্বরীর অন্যতম শিষ্য ওয়াছেল্ বিন্‘ আত্বা (৮০-১৩১ হিজরী) তাঁর সাথে মতপার্থক্য করে তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান এবং নিজস্ব চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি কোরআন ও হাদীছের যে সব উক্তির বাহ্যিক বা আক্ষরিক তাৎপর্য বিচারবুদ্ধির রায়ের সাথে খাপ খায় না বলে মনে করেন সে সব উক্তিকে ভাবার্থক বা রূপকার্থক বলে ব্যাখ্যা করেন। এর ভিত্তিতেই তিনি মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীন কর্মক্ষমতার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এ চিন্তাধারা অনুযায়ী , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের কাজকর্মে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন না।
ওয়াছেল্ বিন্‘ আত্বা তাঁর শিক্ষক হাসান বাছ্বরী থেকে ও হাসান বাছ্বরীর অন্যান্য শিষ্য থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় তাঁকে“ মু‘ তাযিলী” (বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কোণায় চলে যাওয়া) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ থেকে তাঁর চিন্তাধারার অনুসারীদেরকেও“ মু‘ তাযিলী” নামে অভিহিত করা হয়।
ওয়াছেল্ বিন্‘ আত্বা ও হাসান বাছ্বরীর অনুসারীদের মধ্যে একদিকে অদৃষ্টবাদ বনাম নিরঙ্কুশ এখতিয়ারবাদ নিয়ে , অন্যদিকে কোরআন মজীদের অর্থগ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে। কারণ , মু‘ তাযিলীদের মতের বিপরীতে , হাসান বাছ্বরীর অনুসারীরা কোরআন-হাদীছের একটিমাত্র বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন। এমনকি তাঁরা কোরআন মজীদের“ মুতাশাবেহ্” আয়াতেরও বাহ্যিক ও আক্ষরিক তাৎপর্যের প্রবক্তা ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ: তাঁরা আল্লাহ্ তা‘ আলার হাত থাকা এবং তাঁর‘ আরশে অধিষ্ঠান সংক্রান্ত আয়াতের আক্ষরিক তাৎপর্য গ্রহণ করতেন।
এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে , ওয়াছেল্ বিন্‘ আত্বা (৮০-১৩১ হিজরী) এবং ইসলামের ইতিহাসের তিনজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনী ইমাম ও মনীষী হযরত ইমাম জাফর ছ্বাদেক (‘ আঃ) (৮৩-১৪৮ হিজরী) , হযরত ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিজরী) ও হযরত ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিজরী) ছিলেন সমসাময়িক। আলোচ্য বিষয়ে এ তিনজন ইমামের চিন্তাধারা ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। অর্থাৎ তাঁরা না জাবারীয়্যাহ্ ছিলেন , না মু‘ তাযিলী ছিলেন।
পরবর্তী কালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হানাফী মাযহাবের (ইমাম আবূ হানীফাহর নাম ভাঙ্গিয়ে যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবূ ইউসুফ্ ও মুহাম্মাদ্ বিন্ হাসান শায়বানী) ব্যাপক বিস্তার ঘটে। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ্ঃ)-এর সমপর্যায়ের দ্বীনী ইমামের অনুপস্থিতির কারণে এবং আবুল হাসান আশ্‘ আরী কর্তৃক মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা গ্রহণ করে তার প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগের ফলে তাঁর ও তাঁর চিন্তাধারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এভাবে এক সময় অ-হানাফী জাবারীয়্যাহ্‘ আক্বিদাহ্ (অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারা) বাহ্যতঃ হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অন্যান্য মাযহাব , বিশেষতঃ হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীরাও এ চিন্তাধারার দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ে।
যেহেতু জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার অনুসারীরা‘ আক্বায়েদের ক্ষেত্রে‘ আক্বল্ (বিচারবুদ্ধি) প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন এবং এর বিপরীতে মু‘ তাযিলীরা‘ আক্বল্-এর ব্যবহারের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন , আর মানুষ স্বভাবতঃই যে কোনো বিষয়ে কমবেশী বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) প্রয়োগ করে এবং কোরআন মজীদেও‘ আক্বলের প্রয়োগের ওপর তাকিদ করা হয়েছে , যারা‘ আক্বল্ কাজে লাগায় না তাদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে , সেহেতু মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার উদ্ভব হওয়ার পর থেকেই এ চিন্তাধারার অনুসারীদের মোকাবিলায় জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার অনুসারীরা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু আবুল হাসান আশ্‘ আরী কর্তৃক মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা গ্রহণের ফলে স্রোতের গতি বিপরীতমুখী হয়ে যায়।
এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে , জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা মূলগতভাবে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ তথা যুক্তি প্রয়োগের বিরোধী হবার দাবী করলেও বিভিন্ন যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা মু‘ তাযিলী চিন্তাধারা খণ্ডন ও জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার যথার্থতা প্রমাণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিহাস এই যে , তাদের চিন্তাধারার মধ্যকার এবং চিন্তা ও আচরণের মধ্যকার এ স্ববিরোধিতার প্রতি যথাযথভাবে দৃষ্টি প্রদান ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি।
জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চার
জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চারকারী আবুল হাসান আশ্‘ আরী (২৬০-৩২৪ হিজরী) ছিলেন সমকালীন মু‘ তাযিলী শেখ আবূ আলী জুবাঈ-র (ওফাত ৩০৩ হিজরী) শিষ্য। আবুল হাসান আশ্‘ আরী কর্তৃক মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা গ্রহণের ঘটনাটি নিম্নরূপ:
আবুল হাসান একদিন তাঁর শিক্ষক আবূ আলী জুবাঈকে জিজ্ঞেস করলেন:“ বান্দাহর কল্যাণ সাধন করা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য কিনা ?” আবূ আলী বললেন:“ হ্যা।” আবুল হাসান বললেন:“ কাফেরের সন্তান সেই তিনটি শিশু সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী যাদের একজন বালেগ্ব হবার পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিলেন এবং অপর দু’ জনকে জীবিত রাখলেন , অতঃপর তাদের একজন মুসলমান ও আল্লাহর হুকুমের অনুগত হলো , আর অপর জন কাফের হলো ও গুনাহ্গার হলো ? কিয়ামতের দিন এ তিন ভাইয়ের অবস্থা ও তাদের সম্পর্কে হুকুম কী হবে ?”
জবাবে আবূ আলী বললেন:“ যে মুসলমান হলো সে বেহেশতে যাবে , আর যে কাফের হলো সে দোযখে যাবে এবং যে বালেগ্ব হবার আগে মারা গেলো সে না বেহেশতে যাবে , না দোযখে যাবে।”
তখন আবূল হাসান বললেন:“ যে বালেগ্ব হওয়ার আগেই মারা গেলো সে যদি বলে:“ হে আল্লাহ্! আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখতেন তাহলে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করতাম এবং আজ বেহেশতে গিয়ে আপনার বেহেশতী নে‘ আমতের অধিকারী হতাম।” তখন আল্লাহ্ তাকে কী জবাব দেবেন ?”
আবূ আলী বললেন:“ সে তো জানে না যে , হয়তো জীবিত থাকলে সে কাফের হতো এবং জাহান্নামে যেতো। আল্লাহ্ তা‘ আলা জানেন যে , এতেই তার কল্যাণ নিহিত যে , সে বালেগ্ব হওয়ার আগেই মারা যাবে।”
তখন আবূল হাসান বললেন:“ আল্লাহ্ তা‘ আলা এ তিন জনের মধ্য থেকে এক জনের ক্ষেত্রে কেন কল্যাণ নিশ্চিত করলেন ? যে কাফের হয়েছে তার ক্ষেত্রে কেন কল্যাণ নিশ্চিত করলেন না ?”
আবূ আলী এ কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তখন আবূল হাসান তাঁর নিকট থেকে চলে গেলেন এবং বললেন:“ আল্লাহ্ তা‘ আলার হুকুম (বা কাজ)কে মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার সাহায্যে পরিমাপ (বিশ্লেষণ) করা যাবে-তা থেকে তিনি উর্ধে।” অতঃপর তিনি মু‘ তাযিলী চিন্তাধারা খণ্ডনে আত্মনিয়োগ করলেন।
ঘটনার পর্যালোচনা
এ ঘটনাটি মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাধিক প্রচারিত ঘটনাবলীর অন্যতম। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে শত শত বছর ধরে ব্যাপক জনগণের মধ্যে অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারার ভিত্তি হিসেবে এ ঘটনাটি কাজ করে আসছে। এখনো অদৃষ্টবাদিতার পক্ষে যুক্তি হিসেবে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। তাই এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ , এ ঘটনাটির মধ্যে যেমন স্ববিরোধিতা রয়েছে তেমনি রয়েছে ভ্রমাত্মক যুক্তি (مغالطة - fallacy)।
আলোচ্য ঘটনায় আবুল হাসান আশ্‘ আরী ও শেখ আবূ আলী জুবাঈ উভয়ের মধ্যেই , তাঁদের নিজ নিজ‘ আক্বীদাহ্ প্রশ্নে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।
আবুল হাসান আশ্‘ আরী মু‘ তাযিলী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা গ্রহণ করেন। জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা‘ আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির সত্য উদ্ঘাটন ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ এ চিন্তাধারার দাবী অনুযায়ী যুক্তিতর্কের দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি‘ আক্বল্ প্রয়োগ করে অর্থাৎ যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়ে মু‘ তাযিলী চিন্তাধারাকে ভুল প্রতিপন্ন করে জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি , মুখে স্বীকার না করলেও কার্যতঃ স্বীকার করে নিলেন যে ,‘ আক্বলের প্রয়োগ বা যুক্তিতর্কের সাহায্যে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা সম্ভব। এর উপসংহার দাঁড়ায় এই যে , মু‘ তাযিলী চিন্তাধারা ভুল হলেও জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা সঠিক নয়। কারণ , যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এ মতের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে , যদিও এ মত অনুযায়ী যুক্তিতর্কের সাহায্যে কোনো কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আবুল হাসান আশ্‘ আরী এ সত্যটির দিকে দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হন এবং তিনি যে মানদণ্ডকে বাতিল করে দিয়েছেন সে মানদণ্ডের দ্বারাই স্বীয় মত প্রমাণের চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি চিন্তার ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি এক ভুল থেকে আরেক ভুলে স্থানান্তরিত হন।
শেখ আবূ আলী জুবাঈর চিন্তাধারাও স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। আর তার কারণ হচ্ছে যুক্তিতর্ককে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা। তিনি এমন একটি বিষয়কে সঠিক ধরে নিয়ে যুক্তিতর্কে অংশগ্রহণ করেন যা মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার মূল ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক।
মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না ; মানুষ তার কাজকর্মের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। কিন্তু আবুল হাসান ও আবূ আলীর মধ্যকার কথোপকথনে দেখা যাচ্ছে , আবুল হাসান আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে হস্তক্ষেপ করার পরিচায়ক একটি বিষয় উপস্থাপন করলে আবূ আলী তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে আবূল হাসানের প্রশ্নের জবাব দেন।
আবুল হাসান আশ্‘ আরী নাবালেগ্ব্ শিশুর মৃত্যুর জন্য একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছাকে। তিনি অন্য কোনো কারণকে বিবেচনায় নেন নি। এটা জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল , মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।
মু‘ তাযিলী চিন্তাধারা অনুযায়ী আবূ আলীর বলা উচিত ছিলো যে , শিশুটির মৃত্যুর জন্য প্রাকৃতিক কারণ (এবং মানবিক কারণও , যেমন: পিতামাতার পক্ষ থেকে যথাযথ যত্ন না নেয়া) দায়ী। কিন্তু তিনি এখানে জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারাকেই মেনে নিয়েছেন। এটা তাঁর চিন্তাধারার স্ববিরোধিতার পরিচায়ক।
চিন্তাধারার স্ববিরোধিতা ছাড়াও উভয়ের উপস্থাপিত বক্তব্যে অনেক দুর্বলতা নিহিত রয়েছে।
প্রথমতঃ কথিত নাবালেগ্ব শিশুর মৃত্যুর জন্য কেবল আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছাকেই দায়ী করা হয়েছে এবং অন্যান্য কারণকে (প্রাকৃতিক ও মানবিক) উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা ইতিবাচকভাবে বা কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যতীত বান্দাহর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দৃশ্যতঃ আল্লাহ্ তা‘ আলার কোনো হস্তক্ষেপ নেতিবাচক হলেও (যেমন: মৃত্যু ও ধ্বংস) উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিক থেকে তা ইতিবাচক ও কল্যাণকর। আল্লাহ্ তা‘ আলার সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত করা এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে অপরিহার্য না হলে আল্লাহ্ তা‘ আলা কোনো নেতিবাচক হস্তক্ষেপ করেন না। (এ প্রসঙ্গে পরে অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে।)
দ্বিতীয়তঃ কাফেরের যে সন্তান নাবালেগ্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে সে বেহেশতেও যাবে না , দোযখেও যাবে না-এ ধারণা হচ্ছে একটি কল্পিত ধারণা যার পিছনে কোনো অকাট্য ভিত্তি নেই। কোরআন মজীদে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝখানে আ‘ রাফবাসীদের সাময়িক অবস্থানের কথা আছে যারা শেষ পর্যন্ত বেহেশতে যাবে (সূরাহ্ আল্-আ‘ রাফ: ৪৬-৪৯)। কিন্তু এ আ‘ রাফবাসীদের মধ্যে নাবালেগ্বরা শমিল নয়। এছাড়া নাবালেগ্বদের জন্য বেহেশত ও দোযখের বাইরে তৃতীয় কোনো পারলৌকিক জগতের কথা কোনো অকাট্য সূত্রেই বর্ণিত হয় নি।
তৃতীয়তঃ বেহেশতীদের সামনে চিরন্তন শিশু-কিশোররা ঘুরে বেড়াবে (সূরাহ্ আল্-ওয়াক্বেয়াহ্: ১৭)। নিঃসন্দেহে এ শিশু-কিশোররা সেই সব মানবসন্তান যারা নাবালেগ্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কেবল মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান হওয়া অপরিহার্য হতে পারে না। কারণ , শিশু-কিশোররা যেহেতু নিষ্পাপ সেহেতু তাদের মধ্যে পার্থক্য করার কথা চিন্তনীয় নয়।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে , এই শিশু-কিশোররা বেহেশতবাসী হিসেবে পরিগণিত হবে কিনা। এর জবাব হচ্ছে , না। কারণ , বেহেশতবাসী হওয়া মানে শুধু বেহেশতের মাঝে অবস্থান করার সুযোগ লাভ নয়। বরং পারিভাষিক অর্থে বেহেশতবাসী বলতে বুঝায় ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ বেহেশতে অবস্থান (ও তার উপকরণাদি ভোগের সুযোগ লাভ)। এ অর্থে‘ চিরন্তন শিশু-কিশোররা’ ‘ বেহেশতবাসী’ বলে পরিগণিত হবে না , বরং তারা হবে বেহেশতের উপকরণ। কারণ , বেহেশতবাসীরা তাদেরকে এবং তাদের চলাফেরা ও খেলাধুলা দর্শন করে এবং তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করে আনন্দিত হবে। বেহেশতবাসীরা বেহেশতের মাঝে যে সব গায়ক পাখীর গান শুনে আনন্দিত হবে সে সব পাখী নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসী বলে পরিগণিত নয় , বরং বেহেশতের উপকরণ রূপে পরিগণিত।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে , বেহেশতে যে সব বস্তুগত ভোগোপকরণ থাকবে তাতে দৃশ্যতঃ বিভিন্ন বেহেশতবাসীর মধ্যে কোনো রূপ পার্থক্য হবে না। কারণ , বেহেশতবাসীরা যা চাইবে তা-ই পাবে। কিন্তু বেহেশতে যে সব আত্মিক ও মানসিক নে‘ আমত লাভ হবে তা পার্থিব জীবনে ব্যক্তির আত্মিক-মানসিক গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন হবে এবং তার গুরুত্ব হবে এতোই বেশী যে , বস্তুগত নে‘ আমতকে কিছুতেই তার সাথে তুলনা করা যাবে না। এ সব নে‘ আমতের অধিকারীদের নিকট ঐ সব আত্মিক ও মানসিক নে‘ আমতের তুলনায় বেহেশতের বস্তুগত উপকরণ খুবই নগণ্য বলে মনে হবে। অথচ অনেকে এ ধরনের আত্মিক ও মানসিক নে‘ আমত লাভের ইচ্ছাই পোষণ করবে না। অবশ্য বস্তুগত নে‘ আমত নেক আমলের পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্তির মধ্যে একটা আত্মিক-মানসিক আনন্দ রয়েছে যা অভিন্ন বস্তুগত নে‘ আমত স্রেফ দান হিসেবে প্রাপ্তির মধ্যে থাকে না।
বলা বাহুল্য যে , চিরন্তন শিশু-কিশোররা বেহেশতের বস্তুগত নে‘ আমত ভোগ করলেও তা হবে কর্মের প্রতিদানপ্রাপ্তির অনুভূতিজাত নে‘ আমত ও অন্যান্য আত্মিক-মানসিক নে‘ আমত থেকে শূন্য। এমনকি যে সব বস্তুগত নে‘ আমতের মধ্যে আত্মিক-মানসিক দিক জড়িত আছে তা থেকেও শিশু-কিশোরদের পক্ষে পরিপূর্ণ ভোগ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বেহেশতবাসী নারী-পুরুষের পবিত্র জুটির কথা বলা যায়। কারণ , একজন যুবকের দৃষ্টিতে একজন যুবতী এবং একজন যুবতীর দৃষ্টিতে একজন যুবক যে ধরনের নে‘ আমত , একটি শিশুর দৃষ্টিতে তা নয়।
অতএব , বেহেশতে থাকা সত্ত্বেও শিশু-কিশোরদেরকে পারিভাষিক অর্থে বেহেশতবাসী বলা যাবে না। কারণ , তাদেরকে বেহেশতবাসী বলতে হলে বেহেশতের গায়ক পাখী ও প্রজাপতিদেরকেও বেহেশতবাসী বলতে হবে।
চতুর্থতঃ ওপরে যেমন উল্লিখিত হয়েছে , বেহেশতের সুখ বেহেশতবাসীর আত্মিক-মানসিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল হবে বিধায় বিভিন্ন জনের সুখ-আনন্দ ভোগের মাত্রায় পার্থক্য হতে বাধ্য। কারণ , প্রত্যেকে স্বীয় আত্মিক-মানসিক গঠন অনুযায়ী যা চাইবে তা-ই লাভ করবে। অতএব , শিশু-কিশোরদের মনে বেহেশতবাসীদেরকে দেয় উচ্চতর নে‘ আমত সমূহ লাভের আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত হবে না , ঠিক যেভাবে কয়েক দিন বয়সী ব্যঘ্র শিশুর সামনে মাতৃস্তন ও হরিণ শাবক বা তার গোশত থাকলে সে মাতৃস্তন পান করবে ; হরিণ শাবক বা তার গোশতের প্রতি তার কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। অতএব , নাবালেগ্ব শিশুর পক্ষ থেকে‘ বেহেশতবাসী’ হতে না পারার জন্য অভিযোগ উত্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না।
পঞ্চমতঃ আবুল হাসান আশ্‘ আরী তাঁর শিক্ষকের সাথে কথোপকথনের উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন তা ভ্রমাত্মক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বললেন:تعالی ذوالجلال ان توزن احکامه بالاعتزال -“ মহাপরাক্রান্তের (আল্লাহ্ তা‘ আলার) হুকুম (বা কাজ) সমূহ মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার দ্বারা পরিমাপ (বিশ্লেষণ) করা যাবে-তা থেকে তিনি উর্ধে।” তাঁর এ কথার লক্ষ্য যদি শুধু মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার ত্রুটিনির্দেশ হতো তাহলে তা অতো গুরুত্ব বহন করতো না। কিন্তু এ কথার লক্ষ্য ছিলো (এবং পরে আশ্‘ আরী চিন্তাধারার পক্ষ থেকে যা সুস্পষ্ট ভাষায় দাবী করা হয়): আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর কাজের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতি অনুসরণ করেন বলে মনে করা ঠিক নয় এবং মানুষের বিচারবুদ্ধি তাঁর কাজের কোনো নিয়মনীতি উদ্ঘাটন করতে সক্ষম নয়।
আশ্‘ আরীদের যুক্তি: আল্লাহ্ নিয়ম মানতে ‘ বাধ্য ’ নন
এ প্রসঙ্গে আশ্‘ আরী চিন্তাধারার অনুসারীদের পক্ষ থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিসিদ্ধ একটি বক্তব্য পেশ করা হয়। তা হচ্ছে আল্লাহর অধিকার ও সক্ষমতার দোহাই। বলা হয় , যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন , সেহেতু তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই করার অধিকার আছে। অতএব , তিনি সকলকে দোযখে নিক্ষেপ করলেও তাঁকে যালেম বলা যাবে না , কারণ , তা তাঁর অধিকার এবং তিনি সকলকে জান্নাতে পাঠালেও তাঁকে বেহিসাবী বলা যাবে না , কারণ , তা তাঁর অধিকার।
কিন্তু এ ধরনের দাবী শুধু বিচারবুদ্ধির রায়ের সাথেই সাংঘর্ষিক নয় , বরং কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণারও বিরোধী।
এতে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা নিয়মনীতি প্রণয়নে ও অনুসরণে‘ বাধ্য’ নন। কারণ , এমন কেউ বা কিছু নেই যে বা যা তাঁকে এ কাজে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: নিয়মহীনতা বা নিয়ম ভঙ্গের পিছনে কী কারণ নিহিত থাকে ? নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো দুর্বলতাই নিয়মহীনতা বা নিয়ম অনুসরণ না করার পিছনে দায়ী থাকে। এমতাবস্থায় পরম প্রমুক্ত যে সত্তা তিনি নিয়ম রচনা ও অনুসরণ করবেন না এটা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁকে নিয়ম বিহীন খামখেয়ালী আচরণকারী বলে মনে করা মানে তাঁর মহান সত্তা সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করা। অবশ্য তাঁকে কেউ নিয়ম রচনা ও অনুসরণে বাধ্য করতে পারে না , কিন্তু তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় নিয়ম রচনা ও অনুসরণ করবেন-এটা তাঁর সত্তার প্রমুক্ততারই দাবী। কোরআন মজীদে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন , আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন: ( کتب علی نفسه الرحمة ) -“ তিনি রহমত (প্রদর্শন)কে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ১২)
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে , সৃষ্টিলোকের প্রতি সর্বজনীন করুণা প্রদর্শন আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক রচিত ও অনুসৃত এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। অতএব , সকলেই এ করুণা লাভ করে (যদি না সৃষ্টি নিজেরা নিজেদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে)। তেমনি আল্লাহ্ তা‘ আলা কখনোই তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করেন না। তিনি এরশাদ করেন: ( وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) -“ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের প্রতি যুলুমকারী নন।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ১৮২) একই কথা আরো কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে।
আল্লাহ্ তা‘ আলা কেবল সর্বজনীন দয়া ও করুণাকেই নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেন নি , বরং মু’ মিনদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহকেও নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন এবং একে তিনি তাঁর ওপর‘ অবধারিত’ (حقاً ) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন:
( حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ )
“ এটা আমার ওপর অবধারিত যে , আমি মু’ মিনদেরকে নাজাত দেবো।” (সূরাহ্ ইউনুস্: ১০৩)
আল্লাহ্ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন: ( وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ) -“ আর (হে রাসূল!) আপনি কখনো আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবেন না।” (সূরাহ্ আল্-আহযাব্: ৬২)
আরো কয়েকটি আয়াতে এই একই কথা বলা হয়েছে। অতএব , এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা কতক স্বরচিত অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসরণ করেন।
উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের কারণ এই যে , এ ঘটনার মধ্য দিয়ে জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারা (অদৃষ্টবাদ)-এর নব-উত্থান ঘটে এবং অচিরেই আশ্‘ আরিয়াহ্ চিন্তাধারা নামে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। শুধু তা-ই নয় , এখনো অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারার সপক্ষে যুক্তি স্বরূপ উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। তাই এ যুক্তির দুর্বলতা তুলে ধরা অপরিহার্য মনে করেছি।
এবার আমরা বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্)-এর দৃষ্টিতে জাবারীয়্যাহ্ ও এখতিয়ারীয়াহ্ উভয় মত সম্পর্কে আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে , মানুষ যে স্বাধীন এখতিয়ারের (আংশিক বা পুরোপুরি) অধিকারী এবং আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন না-এ ধারণা শুধু মু‘ তাযিলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারার বিপরীত মতকে আমরা এখানে“ মু‘ তাযিলী” না বলে ব্যাপকতর অর্থে“ এখতিয়ারীয়্যাহ্” বলে অভিহিত করছি। অবশ্য এখ্তিয়ারীয়াহ্ চিন্তাধরারও দু’ টি ধারা রয়েছে ; একটি ধারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ (مطلق ) মনে করে এবং অপর ধারাটি আল্লাহ্ তা‘ আলার কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপ সহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী।
বিচারবুদ্ধির আলোকে জাবর্ ও এখতিয়ার
জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারায় নীতিগতভাব মনে করা হয় যে , বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না , বিশেষ করে আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। আর মজার ব্যাপার হলো , তাঁরা তাঁদের এ মত প্রমাণের জন্যই যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।
জাবারীয়াহ্ মতের একটি যুক্তি হচ্ছে এই যে , মানুষকে স্বাধীন এখতিয়ারের (স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতার) অধিকারী মনে করা মানে আল্লাহ্ তা‘ আলাকে অক্ষম গণ্য করা এবং মানুষকে ছোট ছোট খোদা রূপে গণ্য করা।
তাঁদের এ যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা যেখানে তাঁর নিজস্ব , বরং তাঁর সত্তার বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ তাঁর সত্তা , ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা স্বতন্ত্র নয় , সেখানে মানুষের সত্তা , ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা পরস্পর স্বতন্ত্র এবং তিনটিই আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি ; তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে এ দু’ টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার আল্লাহ্ তা‘ আলারই দান। আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলেই তার এখতিয়ার কেড়ে নিতে পারেন বা তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন (যদিও সৃষ্টির কল্যাণার্থে অপরিহার্য না হলে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না)। অতএব , মানুষকে এখতিয়ারের অধিকারী গণ্য করা মানে তাদেরকে ছোট ছোট খোদা গণ্য করা-এরূপ যুক্তি অপযুক্তি বৈ নয়। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা‘ আলা সব সময় ও মানুষের সব কাজে হস্তক্ষেপ করেন না মনে করা মানে আল্লাহ্ তা‘ আলাকে অক্ষম গণ্য করা-এ-ও একটি অপযুক্তি। কারণ , তিনি সর্বাবস্থায় ও সব সময় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় এ থেকে বিরত থাকেন।
মানুষের সকল কাজই আল্লাহ্ করান (সৃষ্টিকর্মের আদি সূচনাকালীন পূর্বনির্ধারণের মাধ্যমেই হোক , বা প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টির জন্মের সূচনাকালীন ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমেই হোক , বা প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই হোক , অথবা বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই হোক)-এ দাবীর মানে হচ্ছে , মানুষ যতো খারাপ কাজ করে (চুরি , ডাকাতি , মিথ্যাচার , হত্যা ও যেনা-ব্যভিচার সহ) তার সবই আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে দিয়ে করিয়ে নেন। এভাবে আল্লাহ্ তা‘ আলাকে সকল প্রকার পাপাচারের কর্তা গণ্য করা হয় যা অত্যন্ত মারাত্মক ও জঘন্য ধারণা। কিন্তু যে কোনো পাপ কাজ , এমনকি যে কোনো নিরর্থক কাজের কারণ হচ্ছে কর্তার কোনো না কোনো দুর্বলতা। আর পরম পূর্ণতার (کمال مطلق ) অধিকারী আল্লাহ্ তা‘ আলা সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত (سبحان ) ।
সৃষ্টিজগতে আমরা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণতা লক্ষ্য করি। কিন্তু খুটিনাটি ক্ষেত্রে পূর্ণতার পাশাপাশি অপূর্ণতাও দেখেতে পাই। আল্লাহ্ তা‘ আলা পরম পূর্ণতার অধিকারী , তাই তাঁর কাজের ফলে অপূর্ণতা বা ত্রুটি অকল্পনীয়। এমতাবস্থায় অপূর্ণতার একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। তা হচ্ছে , আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্ম ও ব্যবস্থাপনার আওতায় তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান এবং বস্তুগত ও প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়ের ক্রিয়াশীলতার সুযোগ রেখেছেন। ফলে এসব কারণের প্রভাবে বিভিন্ন মাত্রার পূর্ণতা ও অপূর্ণতার সংমিশ্রিত প্রতিক্রিয়া থেকে অপূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে।
জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক বড় ধরনের বিভ্রান্তিকর যুক্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানের যুক্তি। তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে , যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞান অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যতকে আয়ত্ত করে আছে সেহেতু তিনি জানেন ভবিষ্যতে কী হবে। আর আল্লাহ্ যা জানেন তার অন্যথা হতে পারে না। অর্থাৎ সৃষ্টির সিদ্ধান্তের মুহূর্তেই তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন যে , ক্বিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে এবং এমনকি তার পরেও কী কী ঘটবে অর্থাৎ কে বেহেশতে যাবে আর কে দোযখে যাবে।
তাঁরা আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানের যুক্তিটি যেভাবে উপস্থাপন করছেন তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তা হচ্ছে , এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানকে শুধু ইতিবাচক বা নেতিবাচক তথ্য হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও জ্ঞানের বিরাট বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে। তা হচ্ছে শর্তাধীন ঘটনাবলীর জ্ঞান।
আল্লাহ্ তা‘ আলা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ারে অধিকারী সৃষ্টির ভবিষ্যতের অনেক বিষয়কে এভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে , সৃষ্টি স্বেচ্ছায় অমুক কাজ করলে অমুক ফল হবে এবং না করলে বা তার বিপরীত কাজ করলে সে ফল হবে না বা তার বিপরীত ফল হবে। ভবিষ্যতের এ অংশটি এভাবেই আল্লাহর জ্ঞানে নিহিত রয়েছে। তবে সৃষ্টির পক্ষ থেকে যখন এরূপ কোনো শর্তযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে এমন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ (مقدمات ) সম্পাদন করা হয় যখন কাজটির দুই সম্ভাবনার মধ্য থেকে একটি সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায় ও অপরটি নিশ্চিত হয়ে যায় , তখন আর তা শর্তাধীন থাকে না এবং তা এভাবেই আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানের আওতায় ইতিবাচক বা নেতিবাচক নিশ্চিত ভবিষ্যত রূপে স্থানলাভ করে।
বলা হয় , আল্লাহ্ কি আগেই জানতেন না যে , তাঁর সৃষ্টি দুই সম্ভাবনাযুক্ত ভবিষ্যত কর্মের ব্যাপারে কোন্ সম্ভাবনার পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে ? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টির এ ভবিষ্যত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টিকেও দুই বা বহু সম্ভাবনা বিশিষ্ট রূপে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এ রূপেই জানেন।
জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারার দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘ আলা সব কিছুই সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন , অতঃপর তা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হচ্ছে এবং তার কোনোই অন্যথা হচ্ছে না। যদি তা-ই হয় , তাহলে বলতে হবে যে , একবার সব কিছু নির্ধারণ করে দেয়ার পর আল্লাহ্ তা‘ আলার আর কোনো করণীয় নেই। এমনকি তাঁকে ঘটনাবলীর নীরব পর্যবেক্ষকও বলা যাবে না। কারণ , সব কিছু পূর্বনির্ধারিত হলে তিনি তো জানেনই যে , কী হতে যাচ্ছে ; নতুন কিছু হচ্ছে না। অতএব , এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের কোনোই গুরুত্ব নেই ; বরং এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কথাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ অসীম সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা‘ আলা সম্পর্কে এ কথা ভাবাই যায় না যে , তিনি একবার সৃষ্টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের (সব কিছু পূর্বনির্ধারণ করে দেয়ার) পর আর কিছুই করছেন না।
এ ক্ষেত্রে জাবারীয়াহ্ ও মু‘ তাযিলী চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কারণ , উভয় চিন্তাধারাই আল্লাহ্ তা‘ আলাকে সৃষ্টি সম্পর্কে মাত্র একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য করে , অনবরত নব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মনে করে না। তবে পার্থক্য এই যে , জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারায় প্রাণীকুলের কর্মকেও পূর্বনির্ধারিত গণ্য করা হয় , কিন্তু মু‘ তাযিলী চিন্তাধারায় তা গণ্য করা হয় না । [ইয়াহূদীরা যে দাবী করতোيد الله مغلولة – “ আল্লাহর হাত সংবদ্ধ (অকর্মণ্য)।” (সূরাহ্ আল্-মায়েদাহ্: ৬৪) , তখন সম্ভবতঃ তারা এটাই বুঝাতে চাইতো যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা একবার সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে এবং সেই সাথে মানুষ ও প্রাণীকুল স্বাধীনভাবে যার যার কাজ করছে , অতঃপর আর তাঁর কিছুই (দান করণও যার অন্যতম) করণীয় নেই।]
অন্যদিকে জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারার যে সব প্রবক্তা দাবী করেন যে , কারণবিধি [অর্থাৎ যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা যে কোনো কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভূত হওয়ার পিছনেই কারণ নিহিত রয়েছে-এই প্রাকৃতিক বিধি । ইংরেজীতে একে বলা হয় cause and effect, বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ এর অনুবাদ করা হয়‘ কার্যকারণ বিধি’ । কিন্তু একে‘ কারণবিধি’ বা‘ কারণ ও ফলাফল বিধি’ বলাই শ্রেয়।] বলতে কিছুই নেই অর্থাৎ , তাঁদের মতে , আল্লাহ্ তা‘ আলা কারণবিধি সৃষ্টি করেন নি , বরং যে কোনো কাজের প্রতিটি পর্যায়ই আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত হয় , তখন তা প্রকৃত পক্ষে জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারার মূল দাবী অর্থাৎ“ আল্লাহ্ তা‘ আলার পূর্বনির্ধারণ” -এর সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পাদিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় , প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ করেন বা করান-এ দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারার প্রবক্তারা তা-ই দাবী করে থাকেন। যেমন: তাঁরা বলেন , আমরা যখন দেখি যে , এক ব্যক্তি একটি কাগজ পোড়াচ্ছে তখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা‘ আলাই তার মনে কাগজ পোড়ানোর ইচ্ছা জাগ্রত করে দেন , নয়তো তার মনে কাগজ পোড়াবার ইচ্ছা সৃষ্টি হতো না। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘ আলা তার হাতকে আগুন লাগাবার জন্য সক্রিয় করে দেন , নয়তো তার ইচ্ছার কারণে তার হাত সক্রিয় হতো না। অতঃপর আল্লাহ্ তার হাতের মাধ্যমে কাগজে আগুন লাগিয়ে দেন , নয়তো (ধরুন) ম্যাচের কাঠির খোঁচায় আগুন জ্বলতো না। অতঃপর তিনি আগুনে দহনক্ষমতা সৃষ্টি করে দেন , নয়তো আগুনের দহনক্ষমতা নেই।
তাদের এ দাবী একজন প্রাথমিক স্তরের ও স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদকের জন্য প্রযোজ্য , মহাজ্ঞানী স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একজন প্রাথমিক স্তরের উৎপাদক একটি ধাতব পাত্র তৈরীর জন্য আকরিক বা খনিজ ধাতবকে হাপরে গলিয়ে ঢালাই করে , এরপর তা হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে বিশেষ আকৃতি প্রদান করে , অতঃপর করাত বা বাটালী দ্বারা অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলে , রেত দিয়ে ঘষে মসৃণ করে এবং অন্য যন্ত্রপাতি দ্বারা তাতে তার নাম ও নকশা খোদাই করে। কিন্তু বহুমুখী ও ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদনকার্যে মশগুল একজন বিজ্ঞানী মালিক-উৎপাদক প্রথমে একটি স্বয়ংক্রিয় ও জটিল কারখানা নির্মাণ করেন , অতঃপর তার উৎপাদন কার্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক ও পরিচালক এবং বিভিন্ন অংশের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেন। এরপর সেখানে যন্ত্রের নির্ধারিত দিকসমূহ দিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের আকরিক ধাতব প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় এবং নির্ধারিত দিকসমূহ দিয়ে বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত ধরনের , ডিজাইনের , মানের ও মাপের ধাতবপাত্র সমূহ বেরিয়ে আসে।
সর্বোপরি জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারাকে সঠিক গণ্য করা হলে বলতে হবে যে , নাউযুবিল্লাহ্ , তিনি একজন খামখেয়ালী স্রষ্টা যে কারণে তিনি অযথাই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একজন যালেম স্রষ্টা যে কারণে তিনি প্রাণশীল সৃষ্টির ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এরূপ চিন্তা সঠিক হলে পাপ-পুণ্য বলতে কিছুই নেই ; যার ভাগ্যে যা লেখা আছে তার জন্য তা-ই ঘটবে ; পাপ লেখা থাকলে সে পাপ কাজ করবে , পুণ্য লেখা থাকলে সে পুণ্য কাজ করবে। অথচ কী পরিহাস (!) , তিনিই যে পাপ করালেন সে পাপের জন্য তিনি বান্দাহকে শাস্তি দেবেন এবং তিনিই যে পুণ্য কাজ করালেন সে পুণ্য কাজের জন্য বান্দাহকে পুরস্কার দেবেন!! পরম প্রমুক্ত আল্লাহ্ তা‘ আলা সম্বন্ধে এরূপ জঘন্য ধারণা পোষণ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার।
এ প্রসঙ্গে জাবারীয়াহ্ চিন্তাধারায় একটি উদ্ভট অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তা হচ্ছে এই যে , মানুষের দায়িত্ব আমল করা (কাজ করা) ; যার ভাগ্যে জান্নাত লেখা আছে সে জান্নাতে যাবার উপযোগী কাজের সুযোগ পাবে এবং যার ভাগ্যে জাহান্নাম লেখা আছে সে জাহান্নামে যাবার উপযোগী কাজের সুযোগ পাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে , সব কিছুই যদি পূর্বনির্ধারিত হবে এবং সব কিছু যদি আল্লাহ্ই করেন বা করান , তাহলে দায়িত্ব , কর্তব্য , উচিত , অনুচিত , ধর্ম , আমল , সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি কথার কোনোই অর্থ হয় না।
আবার পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরষ্কার সম্বন্ধে স্ববিরোধী ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় , যদিও আল্লাহ্ তার ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন তথাপি যেহেতু সে স্বেচ্ছায় এ কাজ করে তাই তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে , ভাগ্যে নির্ধারিত থাকলে অতঃপর‘ স্বেচ্ছায়’ বলতে কিছু থাকে কি ? সে ক্ষেত্রে এ ইচ্ছাও তো পূর্বনির্ধারিত। ব্যক্তির ওপর যদি ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে ইচ্ছার জন্য তাকে শাস্তি বা পুরষ্কার দেয়া চলে কি ?
আবার গোঁজামিল দিয়ে বলা হয় , আল্লাহ্ জানেন , অমুক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ কাজ করবে। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্টির পূর্বেই যখন আল্লাহ্ তা জানতেন তখন তা (সরাসরিই হোক বা কারণবিধির মাধ্যমেই হোক) অবশ্যই আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত , সুতরাং এখানে‘ স্বেচ্ছায়’ কথাটি প্রযোজ্য নয়।
মোদ্দা কথা , বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে জাবারীয়াহ্ মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ যা আল্লাহ্ তা‘ আলা সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে এ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হবার দাবীদার লোকদের বাস্তব কর্মে এ চিন্তাধরার প্রতিফলন ঘটে না , বরং সে ক্ষেত্রে এখতিয়ারিয়্যাহ্ চিন্তাধরারই প্রতিফলন ঘটে। তারা যখন লোকদের সাথে কথা বলে , বিতর্ক করে , ঝগড়া করে , বিরোধ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয় এবং আরো অনেক কাজ সম্পাদন করে তখন এটা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে যে , তারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী। এরূপ ব্যক্তিকে কেউ আঘাত করলে সে প্রত্যাঘাত করে বা অন্ততঃ প্রতিবাদ করে , নিদেন পক্ষে আঘাতকারীকে অন্তরে ঘৃণা করে ; বলে না যে , আল্লাহ্ তা‘ আলাই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে , ঐ ব্যক্তি তাকে আঘাত করবে বা আল্লাহ্ই ঐ ব্যক্তির হাত দিয়ে তাকে আঘাত করেছেন।
এর বিপরীতে বিভিন্ন এখতিয়ারিয়্যাহ্ চিন্তাধারার মধ্যে যারা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদের চিন্তাধারাও ভারসাম্যহীন ও প্রান্তিক। যদিও মানুষের বিচারবুদ্ধি স্বীয় ইচ্ছা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা অনুভব করে ও প্রত্যক্ষ করে , অতএব , তার যে ইচ্ছা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই , কিন্তু এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ও নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া সম্ভব নয়।
এটা অনস্বীকার্য যে , মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তাচেতনার ওপর পারিপার্শ্বিকতা সহ কতক প্রাকৃতিক কারণের নেতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আর বলা বাহুল্য যে , এসব কারণের পিছনে নিহিত সর্বজনীন কারণবিধি সমূহ আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। অতএব , এ ব্যাপারে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা‘ আলার দায়িত্ব রয়েছে। এ কারণেই মানুষের বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্)কে জাগ্রতকরণ এবং তার ওপর থেকে নেতিবাচক প্রভাবের আবরণ সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল (আঃ) প্রেরণ করেন। এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাব না থাকলে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনই হতো না।
দ্বিতীয়তঃ মানুষ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হলেও তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। তাই তাকে ইচ্ছা ও কর্মের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদানকে বিচারবুদ্ধি সমর্থন করে না। বরং তাকে স্বাধীনতা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রণ করাও অপরিহার্য। একটি ছোট শিশুকে যেভাবে তার পিতা বা মাতা উন্মুক্ত স্থানে স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করতে দিলেও তার প্রতি দৃষ্টি রাখে যাতে সে নিজের বা কোনো কিছুর বড় ধরনের ক্ষতি করে না বসে ; এজন্য সে কখনো তাকে সতর্ক করে দেয় , কখনোবা জোর করে ধরে কোনো ঝুঁকি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে , অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা‘ আলাও মানুষকে স্বাধীনতা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজন বোধে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন এটাই দুর্বলতা বিশিষ্ট মানব প্রকৃতির দাবী। অতএব , মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা একটি অসম্ভব ব্যাপার।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। তা হচ্ছে , যেহেতু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুল সহ সমগ্র সৃষ্টিলোক আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক সৃষ্ট এবং সৃষ্ট হওয়ার পরে স্বীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা‘ আলার ওপর নির্ভরশীল , আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধি-বিধান ও পরিবেশ এবং তাঁরই ইচ্ছা ক্রমে অব্যাহত থাকা মানবিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত , আর তার ইচ্ছা ও কর্মশক্তিও তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনি তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই তা স্বাধীনভাবে তৎপরতা চালায়-যা প্রয়োজন বোধে তিনি কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণ করেন , সেহেতু এক হিসেবে বলা চলে যে , সমগ্র সৃষ্টিলোকের সকল কাজই আল্লাহ্ তা‘ আলার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেহেতু মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও আংশিকভাবে স্বাধীন , সেহেতু যে সব কাজ সে বাধ্য হয়ে নয় , বরং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সম্পাদন করে তার ভালোমন্দ ও দায়-দায়িত্ব তার নিজের ওপরে বর্তাবে-এটাই স্বাভাবিক।
এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে , যদিও মানুষের কর্মক্ষমতা বিভিন্ন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ , কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি এতখানি শক্তিশালী যে , যে সব কাজ তার পক্ষে করা‘ সম্ভব’ তা করা বা না-করার ব্যাপারে সে পুরোপুরি স্বাধীন।
কথাটা আরেকটু পরিস্কার করে বললে বলতে হয় , কতগুলো কাজ সে ইচ্ছা করলেও তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ , বিভিন্ন কারণ তার জন্য ঐসব কাজ সম্পাদন অসম্ভব করে রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ , সে ইচ্ছা করতে পারে যে , একটি বিশালায়তন ভবন নির্মাণ করবে বা তার গ্রামের সকল দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে দেবে , কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সে তা করতে পারছে না। অথবা সে ইচ্ছা করছে যে , প্রতিবেশীর প্রাসাদোপম বাড়ীটা দখল করে নেবে , কিন্তু এ জন্য প্রয়োজনীয় জবরদস্তী ক্ষমতা ও শক্তি তার নেই। এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে ঐসব কর্ম সম্পাদনে অক্ষম অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতার অধিকারী নয়। কিন্তু ব্যক্তি অন্যের মালিকানাধীন অরক্ষিত কোনো বস্তু ইচ্ছা করলে নিতে পারে , আবার না-ও নিতে পারে। এমনকি চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও অন্যের মালিকানাধীন অরক্ষিত খাদ্যবস্তু (যেমন: কোনো বাগানের ফল) খেতে পারে , আবার তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতেও পারে। তেমনি সে তার স্বোপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে দরিদ্রদেরকে দান করতে পারে , আবার না-ও করতে পারে। শুধু তা-ই নয় , চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে তার নিজের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাবার (যার অতিরিক্ত নেই) নিজে যেমন খেতে পারে , তেমনি চাইলে অন্যকেও দিয়ে দিতে পারে। এমনকি মানুষ চাইলে বৈধ বা নিজস্ব খাদ্য-পানীয় সামনে থাকা সত্ত্বেও অনশন করে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।
এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে , মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির ক্ষেত্র সীমিত হলেও সে ঐ সীমিত ক্ষেত্রে কোনো কাজ করা বা না-করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন।
কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে
কোরআন মজীদে এমন কতক আয়াত রয়েছে যা থেকে মনে হতে পারে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলাই সব কিছু করেন। অদৃষ্টবাদীরা তাদের দাবীর সপক্ষে এসব আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কোরআন মজীদে এমন আয়াতের সংখ্যা অনেক যা থেকে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। নিরঙ্কুশ এখতিয়ারবাদে বিশ্বাসীরা এসব আয়াতকে তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেন। এ উভয় ধরনের ভূমিকাই একদেশদর্শী । কারণ , উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতের সপক্ষে উপস্থাপনযোগ্য আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং অপর মতের সপক্ষে উপস্থাপনযোগ্য আয়াতগুলোকে এড়িয়ে যান। এভাবে তাঁরা পরস্পর বিরোধী দুই প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অথচ কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বসম্মত মূলনীতি হচ্ছে এই যে , একই বিষয়ের বিভিন্ন আয়াতকে পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক হিসেবে গণ্য করে অর্থ গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করতে হবে।
এখানে আমরা দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক , ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার স্বাধীনতা নির্দেশক এবং শর্তাধীন সম্ভাবনা জ্ঞাপক আয়াত সমূহ থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতক আয়াত উদ্ধৃত করবো এবং উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে অর্থাৎ একই বিষয়ের আয়াত সমূহ পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক-এ মূলনীতির আলোকে আলোচনা করে উপসংহারে উপনীত হবো।
দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক আয়াত
আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )
(১)“ ধরণীর বুকে এমন কোনো বিচরণশীল নেই যার রিযক্বের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয় , আর তিনি তার অবস্থানস্থল ও তার (সাময়িক) বিশ্রামস্থল সম্বন্ধে অবগত ; প্রতিটি (বিষয়)ই এ সুবর্ণনাকারী গ্রন্থে নিহিত রয়েছে।” (সূরাহ্ হূদ: ৬)
অনেকে এ আয়াতে উল্লিখিতمستودعها (তার সাময়িক বিশ্রামস্থল-যেখানে বিশ্রামের পর পুনরায় চারণ বা পথচলা শুরু করে) কথাটির অর্থ গ্রহণ করেছেন“ তার শেষ বিশ্রামস্থল” বা“ যেখানে তার মৃত্যু হবে বা কবর হবে” । এর ভিত্তিতে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে , যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রাণীর মৃত্যুস্থল সম্বন্ধে আগেই জানেন এবং তা কিতাবুম্ মুবীনে লিপিবদ্ধ আছে সেহেতু নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘ আলা তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন।
প্রায় অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক আরেকটি আয়াত:
( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )
(২)“ আর তাঁর (আল্লাহ্ তা‘ আলার) নিকট রয়েছে“ গ্বায়ব্” -এর চাবি সমূহ যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। আর তিনি জানেন যা রয়েছে স্থলে ও জলে। আর এমন কোনো পাতাও ঝরে পড়ে না যা তিনি অবগত নন ; আর না মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্যদানা , না কোনো আর্দ্র বস্তু , না কোনো শুষ্ক বস্তু আছে যা সুবর্ণনাকারী গ্রন্থে নিহিত নেই।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ৫৯)
( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ )
(৩)“ তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে (বর্তমানে ও ভবিষ্যতে) এবং যা আছে তাদের পিছনে (অতীতে)। ” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ২৫৫)
( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ )
(৪)“ আসমান সমূহ ও ধরণীর রাজত্ব তাঁর (আল্লাহ্ তা‘ আলার) ; তিনি প্রাণদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন।” (সূরাহ্ আল্-হাদীদ: ২)
( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ )
(৫)“ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার জন্য চান রিযক্ব্ প্রসারিত করে দেন এবং তাকে পরিমাপ করে দেন।” (সূরাহ্ আল্-‘ আনকাবুত্: ৬২)
( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ )
(৬)“ ধরণীর বুকে এবং তোমাদের সত্তার মধ্যে এতদ্ব্যতীত কোনো বিপদ আপতিত হয় না যা আমরা পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখি নি। নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্যে তা সহজ।” (সূরাহ্ আল্-হাদীদ: ২২)
( وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ )
(৭)“ আর আল্লাহ্ যখন কোনো জনগোষ্ঠীর অকল্যাণ চান তখন আর তার প্রতিরোধকারী থাকে না।” (সূরাহ্ আর-রা‘ দ্: ১১)
( لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ )
(৮)“ প্রতিটি উম্মাহর জন্যে একটি শেষ সময় (আজাল্) রয়েছে ; যখন তাদের শেষ সময় এসে যাবে তখন তারা না এক দণ্ড পিছিয়ে যেতে পারবে , না এগিয়ে আসতে পারবে।” (সূরাহ্ ইউনুস: ৪৯)
( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ )
(৯)“ আর তোমরা ইচ্ছা করছো না (বা করবে না) যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ৩০)
( يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِه )
(১০)“ তিনি যাকে চান (বা চাইবেন) স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান (বা করাবেন)। ” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ৩০)
( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى )
(১১)“ অতএব , (হে মুসলমানগণ!) তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি , বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর (হে রাসূল!) আপনি যখন নিক্ষেপ করলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নি , বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন।” (সূরাহ্ আল্-আনফাল্: ১৭)
( وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )
(১২)“ আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।” (সূরাহ্ আয্-যুমার্: ২৩)
( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ )
(১৩)“ আল্লাহ্ তাদের অন্তর সমূহের ওপর ও তাদের শ্রবণশক্তির (অনুধাবন ক্ষমতার) ওপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর পর্দা রয়েছে।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৭)
( قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ )
(১৪)“ বললাম: হে অগ্নি! ইবরাহীমের ওপর শীতল হয়ে যাও।” (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া’ : ৬৯)
বলা হয় , এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে , আগুনের কোনো দহনক্ষমতা নেই , বরং আল্লাহ্ যখন চান তখন আগুন দহন করতে পারে এবং আল্লাহ্ না চাইলে তখন আগুনের পক্ষে দহন করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ )
(১৫)“ (হে রাসূল!) বলুন , হে আল্লাহ্-(সকল) রাজ্যের অধিপতি! আপনি যাকে চান রাজ্য দান করেন ও যার কাছ থেকে চান রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ২৬)
( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ )
(১৬)“ তিনি তোমাকে যেমন আকৃতিতে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ্ আল্-ইনফিতার্: ৮)
( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ )
(১৭)“ তিনিই (আল্লাহ্) যিনি যেভাবে চান তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে আকৃতি প্রদান করেন।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ৬)
( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ )
(১৮)“ তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৪২)
আমরা দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে মানুষের এখতিয়ার নির্দেশক কতক আয়াত উল্লেখ করবো। কারণ , এসব আয়াতের উল্লেখ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে , উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। অতঃপর বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে পরে তা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।
মানুষের এখতিয়ার নির্দেশকারী আয়াত
মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে কোরআন মজীদের শত শত আয়াত থেকে তা প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে তা থেকে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো:
( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى )
(১)“ নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের মধ্যকার কোনো কর্মসম্পাদনকারীর কর্মকে বিনষ্ট করি না , তা সে পুরুষই হোক , অথবা হোক নারী।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ১৯৫)
এখানে আল্লাহ্ তা‘ আলা সুস্পষ্টতঃই মানুষকে কর্মসম্পাদনকারী বলে গণ্য করেছেন ; তিনি বলেননি ,“ আমি যার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করি” বা“ যাকে দিয়ে কর্ম সম্পাদন করাই” ।
( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )
(২)“ আর এই যে , মানুষ যে জন্য চেষ্টা করে তার জন্য তদ্ব্যতীত কিছু নেই।” (সূরাহ্ আন্-নাজম্: ৩৯)
এখানে সুস্পষ্ট যে , মানুষ চেষ্টা-সাধনার ক্ষমতা রাখে।
( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ )
(৩)“ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে দুনিয়ার ইচ্ছা করে (দুনিয়ার সুখ-সম্পদ পেতে চায়) এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে আখেরাতের ইচ্ছা করে (আখেরাতের সুখ-সম্পদ পেতে চায়)। ” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ১৫২)
) و َمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (
(৪)“ যে ব্যক্তি আখেরাতের ইচ্ছা করলো (আখেরাতের সাফল্য কামনা করলো) এবং সে জন্য ঠিক সেভাবে চেষ্টা-সাধনা করলো যেরূপ চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন , আর সে যদি ঈমানদার হয়ে থাকে , তাহলে তাদের (এ ধরনের লোকদের) চেষ্টা-সাধনার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হবে (এর উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করা হবে)। ” (সূরাহ্ ইসরা’ / বানী ইসরাঈল্: ১৯)
এখানে ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টা-সাধনা উভয়ই মানুষের ওপর আরোপ করা হয়েছে।
) إ ِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (
(৫)“ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দেন না যতক্ষণ না তারা (নিজেরাই) তাদের নিজেদের ভিতরের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।” (সূরাহ্ আর্-রা‘ দ্: ১১)
অর্থাৎ কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য স্বয়ং সে জনগোষ্ঠীকে এ পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে এবং তাকে এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
) ل ِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (
(৬)“ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় সে এগিয়ে যাবে অথবা (যে চায়) সে পিছিয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যক্তিই সে যা অর্জন করেছে সে জন্য দায়ী।” (সূরাহ্ আল্-মুদ্দাছছির্: ৩৭-৩৮)
অর্থাৎ ভালো কাজ বা মন্দ কাজ করা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাধীন বিষয় এবং এ কারণে তার কর্মের সুফল ও কুফলের জন্য সে নিজেই দায়ী।
) و َلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (
(৭)“ আর সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনয়ন করতো ও তাক্বওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (ঈমান ও তাক্বওয়ার পথকে) প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব , তারা যা অর্জন করলো সে কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।” (সূরাহ্ আল্-আ‘ রাফ্: ৯৬)
অর্থাৎ ঈমান আনয়ন ও তাক্বওয়া অবলম্বন করা অথবা কুফরীর পথ অবলম্বন করা উভয়ই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার।
) إ ِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (
(৮)“ অবশ্যই আমি তাকে পথপ্রদর্শন করেছি ; (অতএব ,) হয় সে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকারী হবে , অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ৩)
এমনকি বালা-মুছ্বীবত্ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যও মানুষের এখতিয়ারাধীন কর্মকাণ্ডই (নেতিবাচক কর্মকাণ্ড) দায়ী।
) و َمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (
(৯) তোমাদের ওপর যে সব বালা-মুছ্বীবত্ আপতিত হয় তা তোমাদের নিজেদের অর্জনের কারণেই ; অবশ্য তিনি (আল্লাহ্) অনেকগুলোই ক্ষমা করে দেন।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৩০)
) ظ َهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (
(১০)“ মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলভাগে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে-যাতে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্ম (-এর প্রতিক্রিয়া) আস্বাদন করান ; হয়তো তারা (তাদের বিপর্যয়কর কর্মকাণ্ড থেকে) ফিরে আসবে।” (সূরাহ্ আর্-রূম্: ৪১)
কোরআন মজীদে ছ্বালাত্ , ছ্বাওম্ , জিহাদ্ , যুদ্ধ ইত্যাদির আদেশ সম্বলিত বিপুল সংখ্যক আয়াত রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা‘ আলার অপসন্দনীয় কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এসব আদেশ ও নিষেধ মানুষের ইচ্ছাশক্তি , কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতা নির্দেশ করে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা না থাকলে এসব আদেশ-নিষেধ অর্থহীন হয়ে যায় । আর আল্লাহ্ তা‘ আলা অর্থহীন কাজ সম্পাদনের ন্যায় ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে প্রমুক্ত।
দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক আয়াতের ব্যাখ্যা
কোরআন মজীদের যে সব আয়াত থেকে দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলাই সব কিছু করেন বা করান অথবা পূর্ব থেকেই সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তদনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব কিছু সংঘটিত হচ্ছে , সে সব আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কারণেই এরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু এটা কোরআন মজীদের আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এসব আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এবং কোরআন মজীদকে একটি একক ও অবিভাজ্য পথনির্দেশ গণ্য করে অর্থ গ্রহণ করা। নচেৎ কোরআন মজীদে যেখানে দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ ও এখতিয়ারবাদ নির্দেশক উভয় ধরনের আয়াত রয়েছে তখন একে স্ববিরোধী বলে মনে হবে। কিন্তু কোরআন মজীদ যে কোনো ধরনের স্ববিরোধিতারূপ দুর্বলতা থেকে মুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলা কাফেরদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন:
) أ َفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (
“ তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না ? আর তা (কোরআন) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে হতো (কোনো মানুষের রচিত হতো) তাহলে তাতে বহু স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব থাকতো।” (সূরাহ্ আন্-নিসা’ : ৮২)
কিন্তু কোরআন মজীদে দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ ও এখতিয়ারবাদ নির্দেশক ডজন ডজন আয়াত থাকা সত্ত্বেও কোরআন নাযিল কালীন বা তদপরবর্তী কালীন আরব মুশরিক , ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে কোরআন মজীদে স্ববিরোধিতার একটি দৃষ্টান্তও নির্দেশ করা হয় নি। আশ্চর্যের বিষয় যে , তারা কোরআন মজীদকে মানুষের রচিত গ্রন্থ বলে দাবী করা সত্ত্বেও উক্ত চ্যালেঞ্জের মুখেও কোরআন মজীদে এমন দু’ টি আয়াতও খুঁজে পায় নি যাকে পরস্পর বিরোধী বলে দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের পর এক শতাব্দী কালেরও কম সময়ে কতক মুসলিম মনীষী কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতকে প্রেক্ষাপট ও সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন অর্থ গ্রহণ করতে থাকেন যার ফলে ডজন ডজন আয়াত পরস্পর বিরোধী বলে প্রতিভাত হয়। এখানে আমরা উদাহরণ স্বরূপ , দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক আয়াত সমূহের মধ্য থেকে ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াত সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখবো যে , এসব আয়াত আদৌ অদৃষ্টবাদ প্রমাণ করে না।
(১) আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রতিটি প্রাণীর অবস্থানস্থল ও সাময়িক বিশ্রামস্থল (অথবা , বেশীর ভাগ অনুবাদকের গৃহীত অর্থ অনুযায়ী , মৃত্যুস্থল) সম্বন্ধে অবগত (সূরাহ্ হূদ্: ৬)। এমন কোনো পাতাও ঝরে পড়ে না যা তিনি জানেন না (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ৫৯)। তিনি জানেন যা আছে লোকদের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ২৫৫)।
কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলার জানা থাকা মানেই যে তা তাঁর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত-এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কারণ , প্রথমতঃ মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণে অতীতে যে সব কারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘ আলা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। এ কারণে আল্লাহ্ তা‘ আলা তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সম্যক অবগত। ব্যক্তির ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের কারণ সমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক বিধিবিধান , জেনেটিক কারণ , ব্যক্তির নিজের স্বাধীন ইচ্ছা , এখতিয়ার , মন-মেজাজ ও প্রবণতা এবং তার সাথে অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টির অতীত ও বর্তমান সম্পর্ক সহ সব ধরনের কারণ সম্বন্ধেই তিনি পুরোপুরি অবগত । তাই বলে এজন্য তিনিই দায়ী এরূপ দাবী করা ঠিক নয়। অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক বিধিবিধান , জেনেটিক কারণ এবং ব্যক্তির সাথে অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টির অতীত ও বর্তমান সম্পর্ক তার ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকার অধিকারী হওয়ার মানে কখনোই এটা হতে পারে না যে , এর ফলে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা একেবারেই অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং এ ব্যাপারে কোনোই ভূমিকার অধিকারী নয়।
এ প্রসঙ্গে মানবিক জগতের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যেমন: একজন শিক্ষক স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একজন ছাত্র সম্বন্ধে জানেন যে , সে পরীক্ষায় প্রথম হবে এবং আরেক জন ছাত্র সম্বন্ধে জানেন যে , সে অকৃতকার্য হবে। তাই বলে তাদের প্রথম হওয়া ও অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ঐ শিক্ষককে দায়ী করা চলে না। তেমনি একটি রাস্তার মোড়ে অবস্থিত একটি উঁচু ভবনের ছাদে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি যদি মোড়ের দুই দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আগত দু’ টি গাড়ী দেখে , গাড়ী দু’ টির চালকদ্বয় রাস্তার পাশের বাড়ীঘরের কারণে একে অপরের গাড়ীকে দেখতে পাচ্ছে না লক্ষ্য করে এবং গাড়ী দু’ টির গতিবেগ ও রাস্তার মোড় থেকে উভয়ের দূরত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে , দুই মিনিট পর গাড়ী দু’ টির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে , আর সত্যিই যদি দুই মিনিট পর গাড়ী দু’ টির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে , তাহলে ঐ সংঘর্ষের জন্য কিছুতেই ভবিষ্যদ্বাণীকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা যাবে না। স্মর্তব্য , এ ক্ষেত্রে গাড়ী দু’ টির ভিতর ও বাইরের অবস্থা , চালকদ্বয়ের শারীরিক-মানসিক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পথের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান যত বেশী হবে তার পক্ষে তত বেশী নির্ভুলভাবে ও তত আগে এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এ দুর্ঘটনার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না।
দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘ আলার ভবিষ্যত জ্ঞানের মধ্যে এমন কতক বিষয় রয়েছে যা দু’ টি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পর বিরোধী সমান সম্ভাবনার অধিকারী। এমনকি কিছু বিষয় বহু সম্ভাবনার অধিকারী থাকাও স্বাভাবিক। (এ সম্পর্কে পরে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।)
আর‘ কিতাবুম্ মুবীন্’ (সুস্পষ্ট/ সুবর্ণনাকারী গ্রন্থ) সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে , তাকে প্রতীকী বর্ণমালায় কালির হরফে কাগজের বুকে লেখা আমাদের পঠনীয় গ্রন্থ মনে করলে ভুল করা হবে। বরং এ হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও বস্তুলোকের উর্ধস্থিত বিষয় (মুতাশাবেহ্)। অতএব , এতে সব কিছু কী অবস্থায় নিহিত রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে , এতে নিহিত তথ্যবিলীর মধ্যে সমান দুই সম্ভাবনা বা বহু-সম্ভাবনা বিশিষ্ট বিষয়াদিও অন্যতম।
(২) আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন (আল্-হাদীদ্: ২)। এর মানে হচ্ছে , তিনিই জীবনের সূচনা করেন ও মৃত্যুর অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারণ করেন। এছাড়া জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের এবং মৃত্যু ঘটার কারণ সমূহ (কারণ-বিধি) তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সদা দৃষ্টি রাখেন এবং গোটা সৃষ্টিলোক , বা মানব প্রজাতি , বা কোনো জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ব্যক্তির কল্যাণের জন্যে যদি চান যখন ইচ্ছা তাতে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু এর মানে এ নয় যে , জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টি ও মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য কারণের কোনোই ভূমিকা নেই। কারণ , স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলাই মানুষের এ ধরনের ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকার কথা বলেছেন। যেমন , আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )
“ যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বা ধরণীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টির দায়ে ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে হত্যা করলো এবং যে তাকে জীবিত রাখলো (তার জীবন রক্ষা করলো) সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে জীবন দান করলো।” (সূরাহ্ আল্-মায়েদাহ্: ৩২)
এ ছাড়াও কোরআন মজীদে এমন বহু আয়াত রয়েছে যাতে মানুষের হত্যা করার ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। অতএব , মানুষের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ , স্থান ও কারণ পূর্ব থেকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ , তাহলে বলতে হবে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলাই তার ভাগ্যে তা নির্ধারণ করে রেখে ছিলেন। যদি তা-ই হতো তাহলে হত্যার জন্য ঘাতককে অপরাধী ও গুনাহ্গার গণ্য করা ঠিক হতো না। বস্তুতঃ এটা বড়ই অন্যায় ধারণা যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা একজনকে দিয়ে আরেক জনকে হত্যা করাবেন , অথচ হত্যার অপরাধে হত্যাকারীকে (যে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের যান্ত্রিক হাতিয়ার বৈ নয়) শাস্তি দেবেন ; তিনি এরূপ অন্যায় নীতি ও আচরণ থেকে প্রমুক্ত।
(৩) আল্লাহ্ যাকে চান রিযক্ব্ প্রসারিত করে দেন (সূরাহ্ আল্-‘ আনকাবুত্: ৬২)। এ আয়াত থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার জন্য রিযক্বের ধরন , পরিমাণ , সময় ও মাধ্যম নির্ধারণ করে রেখেছেন। কারণ , এ আয়াতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ারূপ (ছ্বীগাহ্) ব্যবহার করা হয়েছে।‘ প্রসারিত করে দেন’ কথাটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে , তিনি তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে রাখেন নি। কারণ , পূর্বনির্ধারণের পর তাতে পরিবর্তন সাধন সীমিত জ্ঞানের অধিকারী দুর্বলমনা মানুষের বৈশিষ্ট্য ; পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা‘ আলা এরূপ দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত। বরং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে , কারণ-বিধির আওতায় ব্যক্তির জন্য রিযক্ব্ নির্ধারিত হয়ে যায় , তবে তিনি চাইলে তাকে তা সম্প্রসারিত করে দেন , নয়তো কারণ-বিধির আওতায় তার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই (পরিমাপ করে) প্রদান করেন।
(৪) প্রতিটি উম্মাহরই একটি শেষ সময় (আজাল্) রয়েছে যা এসে গেলে আর অগ্র-পশ্চাত হয় না (সূরাহ্ ইউনুস: ৪৯)। এখানে“ আজাল্” শব্দের অর্থ করা হয় আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত শেষ সময়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজীদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য তা নয়। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে , কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতির আয়ুষ্কাল অব্যাহত থাকা ও ধ্বংসের জন্য সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী রয়েছে ; যখন তার ধ্বংসের উপযোগী সকল শর্ত পূর্ণ হয়ে যায় তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ , আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُون )
“ এটা এজন্য যে , (হে রাসূল!) আপনার রব কোনো জনপদকে তার অধিবাসীরা অসচেতন থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে তাকে ধ্বংস করেন নি।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ১৩১)
আল্লাহ্ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন:
( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُون )
“ (হে রাসূল!) আপনার রব এমন নন যে , কোনো জনপদের অধিবাসীরা যথোচিত কর্ম সম্পাদনকারী হওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে সে জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন।” (সূরাহ্ হূদ্: ১১৭)
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:
( يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى )
“ তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে আহবান করছেন যাতে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেন এবং তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় (আজালে মুসাম্মা) পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন।” (সূরাহ্ ইবরাহীম্: ১০)
এ আয়াতে নবী (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের শর্তে আজালে মুসাম্মা পর্যন্ত শাস্তি বা ধ্বংস পিছিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ,يوخرکم (তোমাদেরকে অবকাশ প্রদান করেন) কথাটির ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (مصدر ) হচ্ছেتأخير -যার অর্থ পিছিয়ে দেয়া। তাছাড়া এ আয়াতে যে আযাব্ বা ধ্বংস পিছিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা পূর্বাপর আয়াতের ধারাবাহিকতা থেকেই প্রমাণিত হয়। কারণ , কাফেররা নবী (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহ্ তা‘ আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এরশাদ হয়েছে:
( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِين )
“ অতঃপর তাদের রব তাদের নিকট ওয়াহী করলেন যে , অবশ্যই আমরা যালেমদেরকে ধ্বংস করে দেবো।” (সূরাহ্ ইবরাহীম্: ১৩)
বলা বাহুল্য যে , কোনো জাতির ধ্বংসের দিনক্ষণ ও প্রেক্ষাপট যদি সৃষ্টির সূচনায়ই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে ঈমান আনলে ধ্বংস পিছিয়ে দেয়া হবে বলে জানানোর কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া কারো ঈমান বা কুফরী যদি পূর্ব নির্ধারিত হয় তাহলে তার জন্যে ঈমান আনার শর্ত আরোপ করাও অর্থহীন। আর আল্লাহ্ তা‘ আলা অর্থহীন কথা ও কাজ রূপ দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত।
উপরোক্ত প্রথম আয়াতে (সূরাহ্ ইবরাহীম্: ১০)“ আজালে মুসাম্মা” মানে যে পূর্বনির্ধারিত দিন-তারিখ নয় , বরং যদ্দিন তারা নিজেদেরকে পুনরায় ধ্বংসের উপযুক্ত না করে তদ্দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে-তা-ও সুস্পষ্ট। কারণ , পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ পর্যন্ত ঈমান আনার শর্তে অবকাশ প্রদানের কথা বলা স্ববিরোধিতা বৈ নয়। কেননা , অবকাশটি পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকলে সে অবকাশ অনিবার্য হয়ে যায় , ফলে তাকে আর‘ অবকাশ’ নামে অভিহিত করা চলে না।
অবশ্য এখানে“ আজালে মুসাম্মা” বলতে ক্বিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রেও এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে , কোনো জাতির ধ্বংসের জন্য দিনক্ষণ পূর্বনির্ধারিত নেই , বরং তার ধ্বংসের শর্তাবলী নির্ধারিত হয়ে আছে-যা পূর্ণ হলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে , আর পূর্ণ না হলে তার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে এবং তাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে।
অন্য একটি আয়াত থেকেও মনে হয় যে ,“ আজালে মুসাম্মা” মানে ক্বিয়ামত দিবস। এরশাদ হয়েছে:
( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى )
“ তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন , অতঃপর (তোমাদের জন্য)“ আজাল্” -এর অমোঘ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাঁর নিকটে রয়েছে“ আজালে মুসাম্মা” ।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ২)
এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে , প্রথমোক্ত“ আজাল্” মানে‘ শেষ সময়’ বা‘ মৃত্যু’ র‘ অমোঘ বিধান’ এবং দ্বিতীয়োক্ত“ আজালে মুসাম্মা” মানে‘ ক্বিয়ামত দিবস’ । এ আয়াতের বক্তব্য থেকে এ-ও সুস্পষ্ট যে , মানুষের জন্য“ আজাল” -এর ফয়সালা বলতে‘ শেষ সময়’ বা‘ মৃত্যু’ র অনিবার্যতা বুঝানোই এখানে লক্ষ্য , সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ বুঝানো লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের (এবং অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টির) জন্য মৃত্যুর বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন , অতঃপর যখন কোনো না কোনো কারণে কারো জন্য মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায় তখনই তার মৃত্যু ঘটে।
অবশ্য মৃত্যুর জন্য এই প্রাকৃতিক কারণ সমূহ ছাড়াও একটি ব্যতিক্রমী কারণও রয়েছে , তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রত্যক্ষ ফয়সালা। অর্থাৎ সৃষ্টিলোক , মানব প্রজাতি , কোনো জনগোষ্ঠী বা স্বয়ং ব্যক্তির কল্যাণের লক্ষ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৃত্যু বা ধ্বংস আল্লাহ্ তা‘ আলার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হয় তখন মৃত্যু বা ধ্বংসের জন্য প্রাকৃতিক কারণ বিদ্যমান না থাকলেও আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছায় তার মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য। (অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠলেও সৃষ্টিলোক , মানব প্রজাতি , উক্ত জনগোষ্ঠী বা স্বয়ং ব্যক্তির কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলা তা পিছিয়ে দিতে পারেন।) আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছাক্রমে হযরত খিযির (আঃ) কর্তৃক একটি শিশুকে হত্যার ঘটনা (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ্: ৭৪) এ পর্যায়ের-যা শিশুটি ও তার পিতামাতার জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হয়। এ ঘটনা থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে , শিশুটির মৃত্যু আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে (তার জন্মের পূর্ব থেকেই) পূর্বনির্ধারিত ও অনিবার্য ছিলো না। কারণ , তাহলে সে বড় হয়ে অবাধ্যতা ও কুফর্ দ্বারা পিতামাতাকে প্রভাবিত করবে বলে আল্লাহ্ তা‘ আলা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করার (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ্: ৮০) কোনো কারণ থাকতো না এবং তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়ারও প্রয়োজন হতো না।
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে , সাধারণভাবে মানুষদের মৃত্যুর দিনক্ষণ তার জন্মের পূর্বে নির্ধারিত নয় (তবে কতক ব্যতিক্রম থাকা স্বাভাবিক)।
এখানে বিচারবুদ্ধির আলোকে মানুষের‘ আয়ুষ্কাল ও প্রতিভা’ র সম্ভাবনার ওপর দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। বিচারবুদ্ধির পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই যে , একটি মানবসন্তান জন্মগ্রহণের সময়‘ আয়ুষ্কাল ও প্রতিভা’ র বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আসে। কিন্তু জন্মের পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণ তার আয়ুষ্কাল ও প্রতিভার‘ সম্ভাবনা’ র বৃত্ত দু’ টির আয়তনকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করতে থাকে । আমরা যদি তার বয়সকে একটি ক্রমপ্রসারমান নেতিবাচক বৃত্ত হিসেবে এবং তার আয়ুষ্কাল ও প্রতিভার‘ সম্ভাবনা’ র বৃত্ত দু’ টিকে ক্রমসঙ্কোচনরত ইতিবাচক বৃত্ত হিসেবে ধরে নেই , তাহলে তার বয়সবৃত্তের বৃদ্ধি এবং আয়ুষ্কাল ও প্রতিভার সম্ভাবনার বৃত্তদ্বয়ের সঙ্কোচন অব্যাহত থাকায় যখন তার বয়সবৃত্ত ও প্রতিভা সম্ভাবনাবৃত্ত পরস্পর মিলে যাবে তখন তার প্রতিভার বিকাশধারা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং যখন তার বয়সবৃত্ত ও আয়ুষ্কাল সম্ভাবনাবৃত্ত পরস্পর মিলে যাবে তখনই তার মৃত্যু ঘটবে। এর ব্যতিক্রম কেবল তখনই সম্ভব যদি আল্লাহ্ তা‘ আলা তার প্রতিভাসম্ভাবনাবৃত্ত বা আয়ুষ্কালসম্ভাবনাবৃত্ত সঙ্কুচিত হয়ে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সেখান থেকে পিছিয়ে দেন তথা তার সঙ্কোচনকে (আংশিকভাবে হলেও) দূর করে দেন তথা হারিয়ে যাওয়া প্রসারতাকে (আংশিকভাবে হলেও) ফিরিয়ে দেন।
অনুরূপভাবে ব্যক্তির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে তার প্রতিভাসম্ভাবনার অনেকগুলো দিক বা শাখার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় বা তার বিকাশের গতি শ্লথ হয়ে যায় , যদি না কোনো কারণে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে তাতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয়।
(৫) এমন কোনো মুছ্বীবত্ আপতিত হয় না যা পূর্ব থেকেই কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই (সূরাহ্ আল্-হাদীদ: ২২) এবং আল্লাহ্ যখন কোনো জনগোষ্ঠীর অকল্যাণ চান তখন তা কেউ রোধ করতে পারে না (সূরাহ্ আর্-রা‘ দ্: ১১)।
এখানে কিতাবে মুছ্বীবত্ লিপিবদ্ধ থাকা মানে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর কবে কখন কী ধরনের মুছ্বীবত্ আপতিত হবে তা সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই বা সূচনার মুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো-এমন নয়। বরং এ আয়াতে“ আজাল্” -এর লক্ষ্য দু’ টি সম্ভাবনার একটি। হয় এর লক্ষ্য এই যে , মুছ্বীবত্ সমূহের ধরন সুনির্দিষ্ট এবং তার শর্তাবলী কারণবিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব , এর বাইরে নতুন ধরনের কোনো মুছ্বীবত্ হতে পারে না (যা আল্লাহ্ তা‘ আলার জানা থাকবে না এবং তিনি চাইলে যা রোধ করতে পারবেন না)। অথবা এর লক্ষ্য এই যে ,‘ বিভিন্ন কারণে’ (মানবিক , প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য যে মুছ্বীবত্ অবধারিত হয়ে গেছে যথাসময়ে তার বাস্তবায়িত হওয়া অনিবার্য ; তা থেকে কেউ কিছুতেই পালাতে পারবে না।
সূরাহ্ আর্-রা‘ দ্-এর ১১ নং আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে , ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর স্থান ও কালের আওতায় যে বিপদ আপতিত হয় তা সৃষ্টির সূচনার পূর্বে বা সূচনাকালে বা ব্যক্তির অস্তিত্বের সূচনাকালে নির্ধারিত করে রাখা হয় নি। কারণ ,“ আল্লাহ্ যখন চান বা চাইবেন” থেকেই প্রমাণিত হয় যে , তিনি তা সৃষ্টিলোকের সৃষ্টির বা ব্যক্তির অস্তিত্বলাভের সূচনাকালে বা তার পূর্বে নির্ধারণ করে রাখেন নি।
শয়তানের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গ
অনেক মানুষই মনে করে যে , মানুষের গোমরাহীর জন্য কেবল শয়তানই দায়ী। তাদের ধারণা , শয়তানকে সৃষ্টি করা না হলে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হতেন না এবং আমরা (মানব প্রজাতি) বেহেশতেই থাকতাম। কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ এতদূর পর্যন্ত বলে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে গোমরাহ্ করার উদ্দেশ্যেই আগেই শয়তানকে (অর্থাৎ আযাযীল বা ইবলীসকে) সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য যে , এটা মহান আল্লাহ্ তা‘ আলা সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা।
যেহেতু বিষয়টি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারণারই অংশবিশেষ এবং বিশেষ করে এ ধারণায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘ আলাকেই দায়ী করা হয় সেহেতু এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা জরুরী বলে মনে হয়।
প্রথম কথা হচ্ছে এই যে , শয়তানের গোমরাহ্ করার ক্ষমতা অদৃষ্টবাদ প্রমাণ করে না , বরং অদৃষ্টবাদকে খণ্ডন করে। কারণ , এ থেকে প্রমাণিত হয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টির সূচনার পূর্বে মানুষ সহ প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টির ভবিষ্যতের ছোটবড় সবকিছু নির্ধারণ করে রাখেন নি। কেননা , আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টির সূচনার পূর্বে সব কিছু নির্ধারণ করে রেখে থাকলে শয়তানের কোনো ক্ষমতা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। তেমনি শয়তানের ক্ষমতা এ-ও প্রমাণ করে যে , প্রতি মুহূর্তে মানুষ সহ সকল সৃষ্টির প্রতিটি কাজ স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলা করেন বা করিয়ে নেন-এ ধারণাও পুরোপুরি ভ্রান্ত।
এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি আনুষঙ্গিক ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা যরূরী বলে মনে হয়। এসব ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে , আযাযীল (শয়তান) ফেরেশতা ছিলো এবং ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিলো। অবশ্য যারা জানে যে , কোরআন মজীদে আযাযীলের জিন্ প্রজাতির সদস্য হওয়ার কথা উল্লেখ আছে , তাদের অনেকে মনে করে যে , সে জিন্ হলেও ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিলো। আর এদের সকলেই মনে করে যে , সে অত্যন্ত উঁচু স্তরের‘ আাবেদ (আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইবাদতকারী) ছিলো ; অতঃপর আল্লাহ্ তা‘ আলার একটিমাত্র হুকুম অমান্য করে [হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ্ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে] আল্লাহর অভিসম্পাতের শিকার হয়। এজন্য অনেকে বিস্ময়করভাবে দাবী করে যে , আযাযীল ছিলো সবচেয়ে বড় তাওহীদবাদী , এ কারণে সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সিজদাহ্ করতে রাযী হয় নি। (!!!)
এসব দাবী অকাট্য দলীল বিহীন ভিত্তিহীন কাল্পনিক দাবী মাত্র। কারণ , আযাযীল বা ইবলীস ফেরেশতা ছিলো না। ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা‘ আলার নাফরমানী করতে পারে না ; নাফরমানীর মূল চালিকাশক্তি স্বাধীনতা ভোগের প্রবণতা , বিশেষতঃ কুপ্রবৃত্তি থেকে তারা মুক্ত। বরং আযাযীল জিন্ প্রজাতির সদস্য ছিলো (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ্: ৫০) ।
আর যারা স্বীকার করেন যে , আযাযীল জিন্ প্রজাতির সদস্য ছিলো , কিন্তু অত্যন্ত উঁচু দরের আলেম ও‘ আাবেদ ছিলো বিধায় আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে ফেরেশতাদের শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। এ দাবীরও কোনো ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ফেরেশেতাদের সম্পর্কে ইসলামের অকাট্য সূত্রসমূহ থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হচ্ছে তাদের মধ্যে অজ্ঞতা , সুপ্ত প্রতিভা ও প্রতিভার বিকাশ ও জ্ঞানার্জন বলতে কোনো কিছু নেই। বরং সৃষ্টিগতভাবেই তারা আল্লাহ্ তা‘ আলা সম্পর্কিত , স্বীয় নিয়মিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ও আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে সৃষ্টি সম্পর্কে প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং সেই সাথে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে যখনই যে হুকুম দেয়া হয় তা পালনের প্রবণতার অধিকারী। এমতাবস্থায় তাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ধারণা একটি একান্তই অবান্তর ধারণা।
অন্যদিকে জিন্ প্রজাতির সদস্য আযাযীল আদৌ কোনো‘ আাবেদ ছিলো না। বরং হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সে নাফরমান ছিলো। হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ্ করতে আযাযীল ইবলীসের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )
“ সে (আল্লাহর হুকুম পালনে) অস্বীকৃতি জানালো ও বড়ত্ব দাবী করলো (অহঙ্কার করলো) ; আর সে ছিলো কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৩৪)
অনেকে এ আয়াতের শেষ বাক্যের অর্থ করেন:“ আর সে কাফের হয়ে গেলো।” বা“ আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।” কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। সে মুসলমান (আল্লাহর অনুগত) ছিলো , কিন্তু কাফের হয়ে গেলো-এটা বুঝাতে চাওয়া হলে বলা হতো:فاصبح کافراً (ফলে সে কাফের হয়ে গেলো)। কিন্তু আয়াতে যা বলা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট যে , সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিলো। শুধু তা-ই নয় , আয়াত থেকে এ-ও বুঝা যায় যে , হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ্ করার জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে যখন হুকুম দেয়া হয় তখন সে একাই কাফের ছিলো না , বরং পূর্ব থেকেই একটি গোষ্ঠী (একদল জিন্) কাফের ছিলো ; ইবলীস ছিলো তাদের নেতা।
এমনকি আল্লাহ্ তা‘ আলা হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ্ করার জন্য ইবলীসকে হুকুম না দিলে সে হযরত আদম (আঃ) ও মানব প্রজাতির ক্ষতি করার (তাদেরকে গোমরাহ্ করার) চেষ্টা করতো না-এরূপ মনে করাও ঠিক নয়। কারণ , কুফর্ বা খোদাদ্রোহিতার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মু’ মিনদেরকে কুফরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।
অন্যদিকে ঐ সময় ইবলীসের অস্তিত্ব না থাকলেও তথা ইবলীসকে আদৌ সৃষ্টি করা না হলেও মানব প্রজাতিকে বেহেশতে রাখা হতো না। কারণ , মানুষকে সৃষ্টি করাই হয়েছিলো ধরণীর বুকে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৩০)।
অবশ্য বেহেশতে থাকাকালে ইবলীসের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ঘটনা না ঘটলে কোনোরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াই হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ)কে বেহেশত ছেড়ে যমীনে আসতে হতো।
ইবলীসের অস্তিত্ব না থাকলে কোনো মানুষই নাফরমান হতো না তা নয়। কারণ , স্বাধীনতার মানেই হচ্ছে নাফরমানী ও ফরমানবরদারী উভয়েরই সম্ভাবনা। আল্লাহ্ তা‘ আলা যখন ধরণীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফাহ্) পাঠাবার কথা ঘোষণা করেন (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৩০) তখনই ফেরেশতারা ধারণা করে নেয় যে , আল্লাহর প্রতিনিধিগণ (অন্ততঃ তাদের একাংশ) নাফরমানী করবে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৩০)। কারণ ,“ খলীফাহ্” (স্থলাভিষিক্ত) শব্দ থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিলো যে , আল্লাহ্ তা‘ আলার ক্ষমতা , এখতিয়ার ও গুণাবলীর অনুরূপ ক্ষমতা , এখতিয়ার ও গুণাবলী এ নতুন সৃষ্টিকে (সীমিত পরিমাণে হলেও) দেয়া হবে , কিন্তু সৃষ্টি হওয়া জনিত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা স্বীয় ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। অসম্ভব নয় যে , ইতিপূর্বে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টি জিন্ প্রজাতির সদস্যদের একাংশের নাফরমানী দেখেই তাদের এ ধারণা হয়ে থাকবে। বিশেষ করে জিন্ প্রজাতি আল্লাহ্ তা‘ আলার খলীফাহ্ ছিলো না বিধায় তাদের ক্ষমতা , এখতিয়ার ও স্বাধীনতা ছিলো অপেক্ষাকৃত সীমিত , কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলার খলীফাহ্ হওয়ার কারণে মানুষের ক্ষমতা , এখতিয়ার ও স্বাধীনতা হবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যকার অন্ততঃ একাংশের পক্ষ থেকে নাফরমানী হওয়াই স্বাভাবিক।
মোদ্দা কথা , নাফরমান ইবলীস না থাকলেও কতক মানুষ নাফরমান হতো।
বস্তুতঃ“ শয়তান” কোনো ব্যক্তিবাচক নাম নয় , বরং গুণবাচক নাম। তাই আল্লাহ্ তা‘ আলার এ সৃষ্টিলোকে ইবলীস বা আযাযীল একাই শয়তান নয়। কোরআন মজীদে‘ শাইত্বান’ শব্দের বহু বচন‘ শায়াত্বীন্’ শব্দটি ১৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। জিন্ ও মানুষ উভয় প্রজাতির মধ্যেই শয়তান রয়েছে (সূরাহ্ আল্-আন্‘ আম্: ১১২)। শুধু মানুষ শয়তানদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ১৪)। প্রায় অভিন্ন অর্থে“ খান্নাস্” শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে , যে মানুষের অন্তরে ওয়াস্ওয়াসাহ্ (কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ-সংশয়) সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের খান্নাস্ মানুষ ও জিন্ উভয় প্রজাতির মধ্যেই রয়েছে (সূরাহ্ আন্-নাস্: ৫-৬)।
প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গোমরাহ্ করার ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ভূমিকা ইবলীসের চেয়ে বেশী। তাই যে ব্যক্তি গোমরাহ্ হতে চায় না তাকে গোমরাহ্ করার কোনো ক্ষমতাই ইবলীসের নেই (সূরাহ্ ইবরাহীম: ২২ ; আল্-হিজর্: ৪২ ; আন্-নাহল্: ৯৯ ; ইসরা’ / বানী ইসরাঈল: ৬৫)। অন্যদিকে কতক লোক স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয় , কোরআন মজীদের ভাষায় , স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করে (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্: ৪৩ ; আল্-জাছিয়াহ্: ২৩)। এ ধরনের লোককে হেদায়াত করা স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জন্যও সম্ভব ছিলো না (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্: ৪৩)।
অতএব , সুস্পষ্ট যে , মানুষের গোমরাহীর জন্য সে নিজেই মুখ্য কারণ ; ইবলীস সহ অন্যান্য শয়তান গৌণ কারণ মাত্র।
একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত
আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি , ভবিষ্যতের একটি অংশ সুনিশ্চিতরূপে এবং একটি অংশ দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘ আলার ভবিষ্যত বিষয়ক জ্ঞানে এ উভয় ধরনের বিষয়াদিই শামিল রয়েছে। অবশ্য ভবিষ্যতের আরো একটি অংশ রয়েছে যা শূন্য তথা পুরোপুরি অনিশ্চিত।
যে সব বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্ণ কারণ বিদ্যমান তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই পূর্ণ কারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহ্ তা‘ আলার মূল সৃষ্টিলক্ষ্য ও সৃষ্টি পরিকল্পনা , প্রাকৃতিক বিধিবিধানের প্রতিক্রিয়া , প্রাণীজ ও মানবিক কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রাজ্ঞ হস্তক্ষেপের ফল। এর কোনো একটি বা একাধিক বা সবগুলো কারণ যা‘ অনিবার্য’ করে তোলে তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে প্রথম ও শেষ কারণ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলার মূল সৃষ্টিলক্ষ্য ও সৃষ্টি পরিকল্পনা এবং তাঁর হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য কারণের প্রতিক্রিয়াকে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে পরিবর্তিত করে দেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলার তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ ব্যতিক্রম , সেহেতু ভবিষ্যতের এ অংশটিকে অর্থাৎ পূর্ণ কারণ যা অনিবার্য করে ফেলেছে তাকে আমরা অনিবার্য বলে গণ্য করতে পারি।
অন্যদিকে পূর্ণ কারণ ভবিষ্যতের একটি অংশকে দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত করে রেখেছে-ভবিষ্যতে কোনো না কোনো কারণ যার একটি বাদে অপর সম্ভাবনাটিকে বা সম্ভাবনাগুলোকে বিলুপ্ত করে দেবে এবং যে সম্ভাবনাটি অবশিষ্ট থাকবে তা অনিবার্য হয়ে উঠবে।
এছাড়া ভবিষ্যতের রয়েছে এক সীমাহীন শূন্য দিগন্ত যেখানে কোনো কারণ কোনো কিছুকে অনিবার্য অথবা দুই বা ততোথিক সম্ভাবনাযুক্ত করে তোলে নি। অন্য কথায় , ভবিষ্যতের একটি অংশে কোনই কারণ বিদ্যমান নেই অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলা ভবিষ্যতের একটি অংশকে সকল প্রকার কারণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ তা‘ আলার ভবিষ্যত ইচ্ছাই কোনো কিছুকে অনিবার্য অথবা দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত করে তুলতে পারে।
আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ )
“ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং (যা ইচ্ছা করেন) স্থির করে দেন। আর তাঁর সামনে রয়েছে গ্রন্থজননী (উম্মুল কিতাব)। ” (সূরাহ্ আর্-রা‘ দ্: ৩৯) অর্থাৎ উম্মুল কিতাবে কতগুলো ভবিষ্যত বিষয় একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত রূপে নিহিত রয়েছে।
তিনি আরো এরশাদ করেন:
( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً )
“ [তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) পরম বরকতময়] যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে , তোমাদের মধ্যে কর্মের বিচারে কে অধিকতর উত্তম।” (সূরাহ্ আল্-মুলক্: ২)
এর মানে আল্লাহ্ তা‘ আলা সৃষ্টির শুরুতেই নির্ধারণ করে রাখেন নি যে , কর্মের বিচারে কে ভালো হবে ও কে মন্দ হবে। অর্থাৎ তিনি মানুষকে ভালো-মন্দের উভয় সম্ভাবনাযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য সেহেতু তিনি ব্যক্তি-মানুষের ভবিষ্যতকে ভালো ও মন্দের সমান সম্ভাবনাযুক্ত করে দিয়েছেন , অতঃপর বিভিন্ন কারণ তাকে প্রভাবিত করে , তবে ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে বেশী‘ প্রভাবশালী কারণ’ যা অন্য সমস্ত কারণ ও তজ্জনিত সম্ভাবনা সমূহকে পরাভূত করতে সক্ষম।
এছাড়া কোরআন মজীদে এমন বহু আয়াত রয়েছে যাতে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়কে শর্তযুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে যা একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত ভবিষ্যতেরই প্রমাণ বহন করে। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকবো। যেমন , এরশাদ হয়েছে:
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )
“ আর জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো ও তাক্বওয়া অবলম্বন করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে বরকত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।” (সূরাহ্ আল্-আ‘ রাফ্: ৯৬)
এ আয়াতে বরকত প্রাপ্তির জন্য ঈমান আনয়ন ও তাক্বওয়া অবলম্বনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে , বলা হয় নি যে , তাদের ভাগ্যে বরকত লিপিবদ্ধ ছিলো না বিধায় তাদেরকে বরকত প্রদান করা হয় নি। আর এ আয়াত থেকে এ-ও সুস্পষ্ট যে , ঈমান আনয়ন ও তাক্বওয়া অবলম্বন করা তাদের এখতিয়ারাধীন বিষয় , নইলে আল্লাহ্ তা‘ আলা বলতেন না“ যদি ঈমান আনতো ও তাক্বওয়া অবলম্বন করতো” ।
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم )
“ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম সমূহকে সুদৃঢ় করে দেবেন।” (সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৭)
এখানে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তিকে তাঁকে সাহায্য করার (তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা-সাধনার) সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে সাহায্য না করলে তথা তাঁর রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম না করলে তিনি মু’ মিনদেরকে সাহায্য করবেন না ।
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:
( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا )
“ তোমাদের মধ্য থেকে যদি ধৈর্য ও দৃঢ়তার অধিকারী বিশ জন হয় তাহলে কাফেরদের দুইশ’ জনকে পরাজিত করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে (এরূপ) একশ’ জন হলে তাদের এক হাজার জনকে পরাজিত করবে।” (সূরাহ্ আল্-আনফাল্: ৬৫)
এখানে ধৈর্য ও দৃঢ়তাকে বিজয়ের শর্ত করা হয়েছে , ভাগ্যলিপিকে নয়।
অন্যদিকে শূন্য বা পুরোপুরি অনিশ্চিত ভবিষ্যত হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে না কিছু নিশ্চিত হয়ে আছে , না সুনির্দিষ্ট একাধিক সম্ভাবনা আছে , বরং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘ আলার ভবিষ্যত ইচ্ছার সীমাহীন দিগন্ত। এরূপ একটি সীমাহীন দিগন্ত আল্লাহ্ তা‘ আলার চিরন্তন সৃষ্টিশীলতা গুণের জন্য অপরিহার্য। শুধু বর্তমান সৃষ্টিনিচয়ের অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিশীলতাকে (তা যতই না দৃশ্যতঃ সীমাহীন হোক) সীমাবদ্ধ গণ্য করা মানে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাকে সীমিত গণ্য করা-যা থেকে তিনি পরম প্রমুক্ত।
আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিশীলতার ওপরে সীমাবদ্ধতা কল্পনাকারী চিন্তাধারা বর্তমানে প্রাপ্ত বিকৃত তাওরাতে লক্ষ্য করা যায় । তাওরাত নামে দাবীকৃত বাইবেলের প্রথম পুস্তকে (আদি/ সৃষ্টি পুস্তক) বলা হয়েছে:“ পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য হতে নিবৃত্ত হলেন ; সেই সপ্তম দিবসে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হতে বিশ্রাম করলেন।” (২:২)
কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে:
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ )
“ আর ইয়াহূদীরা বলে:“ আল্লাহর হাত সংবদ্ধ।” তাদেরই হাত সংবদ্ধ হোক এবং তারা যা বলেছে সে কারণে তারা অভিশপ্ত হোক। বরং তাঁর (আল্লাহর) উভয় (কুদরাতী) হাতই সম্প্রসারিত।” (সূরাহ্ আল্-মাএদাহ্: ৬৪)
অবশ্য উক্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় এরশাদ হয়েছে:ينفق کيف يشاء -“ তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন।” এ থেকে বাহ্যতঃ আল্লাহ্ তা‘ আলার কুদরাতী হাতের প্রসারতা তাঁর নে‘ আমত প্রদান সংক্রান্ত বলে মনে হলেও এ আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে আল্লাহ্ তা‘ আলার সীমাহীন সৃষ্টিশীলতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন:
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيم )
“ নিঃসন্দেহে (হে রাসূল!) আপনার রব অনবরত সৃষ্টিকারী সদাজ্ঞানী।” (সূরাহ্ আল্-হিজর্: ৮৬)
অন্য এক আয়াত থেকেও অনিশ্চিত ভবিষ্যত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (১৫) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (১৬) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ )
“ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্ ; তিনি হচ্ছেন অ-মুখাপেক্ষী সদাপ্রশংসনীয়। তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে অপসারিত (বিলুপ্ত) করে দেবেন এবং (তোমাদের স্থলে) কোনো নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসবেন (ও তাদেরকে ধরণীর বুকে স্বীয় খেলাফত প্রদান করবেন)। আর আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।” (সূরাহ্ আল্-ফাতের: ১৫-১৭)
সূরাহ্ ইবরাহীমের ১৯ ও ২০তম আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এখানে‘ নতুন সৃষ্টি’ (خلق جديد ) বলতে এমন সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা তিনি এখনো করেন নি।
অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে:
( إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا )
“ হে মানবমণ্ডলী! তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে অপসারিত (বিলুপ্ত) করে দেবেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্য কাউকে (কোনো নতুন সৃষ্টিকে) নিয়ে আসবেন (ও তাদেরকে ধরণীর বুকে স্বীয় খেলাফত প্রদান করবেন)। আর এটা করতে আল্লাহ্ পুরোপুরি সক্ষম।” (সূরাহ্ আন্-নিসা’ : ১৩৩)
অনেকে উপরোক্ত আয়াত সমূহের তাৎপর্য করেছেন এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা এক জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে দিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার কথা বলেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকেايها الناس (হে মানবমণ্ডলী!) সম্বোধন থেকে সুস্পষ্ট যে , তিনি সমগ্র মানব প্রজাতিকে সরিয়ে দেয়ার ও তাদের পরিবর্তে অন্য কোনো নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কথা বলেছেন। তবে তা করা বা না-করার ব্যাপারে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি।
বস্তুতঃ ভবিষ্যতের একাধিক সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত থেকে আশা‘ এরী ও মু‘ তাযিলী উভয় চিন্তাধারাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।
আল্লাহর হস্তক্ষেপ
মানুষ আল্লাহ্ তা‘ আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম হলেও সে সৃষ্টি বৈ নয়। তাই সৃষ্টি হিসেবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বহু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে ধরণীর বুকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত (খলীফাহ্) নিযুক্ত করেছেন। এ কারণে তার পক্ষে আল্লাহ্ তা‘ আলার দেয়া গুণাবলীর ভুল প্রয়োগ অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাই তার জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলার পথনির্দেশ , পর্যবেক্ষণ ও হস্তক্ষেপ অপরিহার্য । সে যদি পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যলিপি অনুযায়ী পরিচালিত হতো তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে হেদায়াত ও ওয়াহীর প্রয়োজন হতো না এবং আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হতো না , বরং সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্বনির্ধারিত কাজ সমূহ সম্পাদন করতো। তা নয় বলেই তার জন্য হেদায়াত ও ওয়াহীর আগমন ঘটে এবং তার কাজে কখনো কখনো আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়।
বস্তুতঃ নবী-রাসূল (আঃ) প্রেরণ ও ওয়াহী নাযিলই একটি বিরাট ইতিবাচক হস্তক্ষেপ। এমনকি যে সব হস্তক্ষেপ দৃশ্যতঃ নেতিবাচক , যেমন: আযাব নাযিল করণ , সে সবেরও উদ্দেশ্য ইতিবাচক । কারণ , এর মাধ্যমে অন্যদেরকে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনন্ত দুর্ভাগ্যের পথ থেকে অবিনশ্বর সাফল্যের পথের দিকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু তা-ই নয় , যাদেরকে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় তাদের জন্যও তা ইতিবাচক। কারণ , পরকালীন জীবনে তথা অনন্ত সৌভাগ্য ও অনন্ত দুর্ভাগ্যের জীবনে ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী তার নে‘ আমত ও শাস্তির পরিমাণ ও মাত্রায় পার্থক্য হবে। তাই পাপীর ধ্বংস সাধনের ফলে তার পাপের বোঝা আর বেশী ভারী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তা তার নিজের জন্যও কমবেশী কল্যাণকর।
আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর রাসূল (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন:
( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ )
“ আপনার জন্য যে কল্যাণের আগমন ঘটে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আপনার ওপর যে অকল্যাণ আপতিত হয় তা আপনার নিজের কারণে।” (সূরাহ্ আন্-নিসা’ : ৭৯)
মানুষের কাজে আল্লাহ্ তা‘ আলার ইতিবাচক হস্তক্ষেপের অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বদর যুদ্ধে মু’ মিনদেরকে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যকরণ (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ১২৩) যার ফলে মুসলমানরা সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হয়েও বিজয়ী হয়েছিলেন।
আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের দো‘ আ কবুল করেন ; এ-ও মানবিক জগতে আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত। যেমন , এরশাদ হয়েছে:
( أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
“ কোনো আহবানকারী (দো‘ আ-কারী/ প্রার্থনাকারী) যখন আমাকে আহবান করে (দো‘ আ করে) তখন আমি তার আহবানে সাড়া দেই (তার দো‘ আ কবুল করি)। ” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ১৮৬)
অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে:
( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ )
“ কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং তার কষ্ট দূর করে দেন ?” (সূরাহ্ আন্-নামল্: ৬২)
বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকের চলমান প্রক্রিয়ায় , বিশেষ করে মানবিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলার তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ জাবারীয়াহ্ ও মু‘ তাযিলী উভয় ধরনের প্রান্তিক চিন্তাধারাকেই ভ্রান্ত প্রমাণ করে।
স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কর্ম আরোপ
কোরআন মজীদের বিরাট সংখ্যক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রদান করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু আয়াতে একই কাজ একই সাথে সৃষ্টির প্রতি এবং আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে কতক আয়াতে সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতি আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের আয়াতের প্রতি মনোযোগ দেন না তাঁরা শেষোক্ত ধরনের আয়াত থেকে এরূপ উপসংহারে উপনীত হন যে , সমগ্র অস্তিত্বলোকে একমাত্র আল্লাহ্ তা‘ আলা ছাড়া আর কোনো কর্মসম্পাদনকারী নেই। অন্যদিকে অনেকে দ্বিতীয়োক্ত ধরনের আয়াত থেকে দোদুল্যমান অবস্থার শিকার হন এবং ভেবে পান না যে , সৃষ্টিকুল যে সব কাজ সম্পাদন করে থাকে কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে তা কি তাদেরই কাজ , নাকি আল্লাহ্ তা‘ আলার কাজ ?
এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে , কোরআন মজীদ একদিকে যেমন সকল জ্ঞানের আধার এবং সে হিসেবে এতে ব্যাপকতম , সূক্ষ্মতম ও গভীরতম সকল জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে , অন্যদিকে তা সাহিত্যিক মানের দিক থেকেও ব্যাপকতম , সূক্ষ্মতম ও গভীরতম ভাব প্রকাশক। কোরআন মজীদ যে সব বৈশিষ্ট্যের কারণে মু‘ জিযাহ্ তার মধ্যে এ দু’ টি বৈশিষ্ট্য অন্যতম।
বস্তুতঃ কোরআন মজীদ কোনো সাহিত্য বা কাব্যগ্রন্থ নয় , বরং এটি হচ্ছে তত্ত্ব , তথ্য , আইন , উপদেশ ও নৈতিক শিক্ষার সমাহার। তা সত্ত্বেও এটি কোনো বিশালায়তন গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করে নি। অন্যদিকে এসব বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ , বিশেষ করে গুরুভার বিষয়বস্তু সম্বলিত মানব রচিত একটি গ্রন্থ সুখপাঠ্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কোরআন মজীদ এসব বিষয়বস্তু সত্ত্বেও একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ যার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও গতিশীল , তেমনি তার সাহিত্যিক ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য মানবিক প্রতিভার উর্ধে। এ কারণেই এতে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা ভাবার্থবাচক। সৃষ্টির কাজকে স্রষ্টার ওপর আরোপ করাও এ ধরনের ভাবার্থবাচক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে গভীর চিন্তার খোরাক ও তত্ত্বজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ এ ধরনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।
এরশাদ হয়েছে:
( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )
“ আর আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সম্পদশালী লোকদেরকে আদেশ দেই , অতঃপর তারা সেখানে পাপাচার করে , ফলে তার (ঐ জনপদের) জন্য (ধ্বংসের) উক্তি অবধারিত হয়ে যায় , অতঃপর আমি তাকে (ঐ জনপদকে) ধ্বংস করে দিই ঠিক যেভাবে ধ্বংস করা উচিত।” (সূরাহ্ আল্-ইসরা’ / বানী ইসরাঈল: ১৬)
বলা বাহুল্য যে , এখানে আদেশ দান বলতে পাপাচারের সুযোগ রুদ্ধ না করা এবং এজন্য প্রাকৃতিক বিধিবিধানকে সহায়ক রাখা। নয়তো আল্লাহ্ তা‘ আলা কখনোই পাপের আদেশ দেন না। বরং কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভালো গুণ ও সংশোধনের সম্ভাবনা নিহিত থাকা সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতা বশে তারা পাপের দিকে অগ্রসর হলে আল্লাহ্ তা‘ আলা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধাবিঘ্ন ও বিপদাপদ সৃষ্টি করে তাদের পাপপ্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠী যখন পাপাচার ও আল্লাহ্ তা‘ আলার নাফরমানীর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন আল্লাহ্ তা‘ আলা তাদের পাপাচারের পথে বাধা সৃষ্টি করেন না। ফলে তারা পাপাচারে অধিকতর বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে যায়। একেই আল্লাহ্ তা‘ আলা ভাবার্থে তাঁর আদেশ বলে অভিহিত করেছেন।
অনুরূপভাবে বানী ইসরাঈলের নাফরমানী ও সে কারণে তাদেরকে শাস্তিদান প্রসঙ্গে তাদের উদ্দেশে সতর্কীকরণমূলক ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করে এরশাদ হয়েছে:
( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ و.... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا )
“ আর আমি বানী ইসরাঈলের উদ্দেশে কিতাবে ফয়সালা করে দিয়েছিলাম যে , অবশ্যই তোমরা ধরণীর বুকে দুই বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অবশ্যই তোমরা গুরুতর ধরণের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেবে। অতঃপর যখন সেই দু’ টি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি এলো তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাহদের পাঠালাম যারা সে জনপদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়লো (এবং তাদেরকে হত্যা করলো।) অতঃপর যখন অপর প্রতিশ্রুতিটি(-এর সময়) সমুপস্থিত হলো তখন তারা (আমার প্রেরিত বান্দাহরা) তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দিলো এবং প্রথম বার যেভাবে প্রবেশ করেছিলো সেভাবেই মসজিদে প্রবেশ করলো এবং যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো সেখানেই সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালালো।” (সূরাহ্ আল্-ইসরা’ /বানী ইসরাঈল: ৪ , ৫ ও ৭)
এখানে‘ কিতাবে ফয়সালা’ করে দেয়া মানে বানী ইসরাঈলের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও অন্যান্য কার্যকারণের আলোকে অবধারিত হয়ে যাওয়া ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবে (তাওরাতে) ভবিষ্যদ্বাণী ; বিনা কারণে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া নয়-এটা আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনা সমূহ থেকে সুস্পষ্ট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে , উপরোক্ত হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ মুশরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলা তাদেরকে স্বীয় কঠোর যোদ্ধা বান্দাহ্ বলে এবং তাদেরকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন , যদিও তারা তাদের পররাজ্যগ্রাস ও সম্পদলিপ্সার লক্ষ্যেই এ অভিযান চালিয়েছিলো এবং মসজিদুল আক্বছা’ -কেও ধ্বংস করেছিলো। যেহেতু বানী ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হওয়ায় ও আল্লাহ্ তা‘ আলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করায় একদিকে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো অন্যদিকে নৈতিক অধঃপতনের কারণে তাদের বীর্যবত্তা ও প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো , সেহেতু মুশরিক দুশমনরা তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে সাহসী হয়ে উঠেছিলো। আর এভাবে বানী ইসরাঈল তাদের পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের পার্থিব শাস্তি লাভ করেছিলো। তাই আল্লাহ্ তা‘ আলা আক্রমণকারীদেরকে তাঁর নিজস্ব বাহিনী বলে অভিহিত করেন। বিশেষ করে সমগ্র সৃষ্টিলোকের সব কিছুই আল্লাহ্ তা‘ আলার নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় এবং মানুষকে তাঁরই দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার ব্যবহারের ফলে এ ধরনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে থাকে তাই ব্যাপকতর অর্থে এ কাজ তিনিই করেছেন বলে বলা যেতে পারে। কারণ , তিনি যদি চাইতেন যে , এ কাজ না হোক তাহলে তা হতো না।
আল্লাহ্ তা‘ আলা অন্যত্র এরশাদ করেন:
( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا )
“ আর , একদল লোক দ্বারা অপর এক দলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দমন করা না হলে খৃস্টানদের গীর্জা ও মঠ , ইয়াহূদীদের‘ ইবাদতখানা এবং মসজিদ সমূহ-যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়-ধ্বংস হয়ে যেতো।” (সূরাহ্ আল্-হাজ্ব: ৪০)
বলা বাহুল্য যে , এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রাকৃতিক বিধি যার আওতায় জাতি সমূহের উত্থান-পতন সংঘটিত হয়। এজন্য এটা অপরিহার্য নয় যে , সংঘাতে লিপ্ত পক্ষদ্বয়ের একটি অথবা আক্রমণকারী পক্ষ অবশ্যই সত্যপন্থী হবে। বরং উভয় পক্ষই বাতিলপন্থী হতে পারে এবং সত্যপন্থীরা এতই দুর্বল হতে পারে যে , তারা কোনো পক্ষ হিসেবে গণ্য হবার পর্যায়ে না-ও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় দুই বাতিল পক্ষের সংঘাত ও একের দ্বারা অপরের ধ্বংসসাধনের ফলে সামগ্রিকভাবে বাতিলই দুর্বল হয়ে যায় এবং সেই অবকাশে দুর্বল অবস্থানের অধিকারী সত্যপন্থীদের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখা ও ধীরে হলেও বিকাশ-বিস্তারের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। যেহেতু এসব সংঘাতের নায়করা আল্লাহ্ তা‘ আলার উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করছে সেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলাই যেন তাদেরকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছেন।
অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা‘ আলা একই কাজকে যেমন ফেরেশতাদের প্রতি আরোপ করেছেন , তেমনি তা তাঁর নিজের প্রতিও আরোপ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের মৃত্যু ঘটানোর কাজ ফেরেশতাদের (“ মালায়েকাহ্” বহুবচন বাচক শব্দ) প্রতি আরোপ করেছেন। এরশাদ হয়েছে:
( فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ )
“ তখন তাদের (কাফেরদের) অবস্থা কেমন হয় যখন ফেরেশতারা তাদের প্রাণ গ্রহণকালে তাদের চেহারায় ও তাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে।” (সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ২৭)
অপর এক আয়াতে প্রাণ গ্রহণের বিষয়টি মৃত্যুর ফেরেশতার (মালাকুল মাওত্=এক বচন/‘ আযরাঈল) প্রতি আরোপ করা হয়েছে:
( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ )
“ (নবী!) বলে দিন: মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ গ্রহণ করবে যাকে তোমাদের (প্রাণ হরণের) দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্: ১১)
কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলা একই কাজ অন্যত্র তাঁর নিজের প্রতি আরোপ করেছেন। এরশাদ হয়েছে:
( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى )
“ আল্লাহ্ নাফ্স্ সমূহকে পরিগ্রহণ করেন তার মৃত্যুর (প্রতিটি নাফসের) মৃত্যুর সময় এবং যে মারা যায় নি তার ঘুমের সময়। অতঃপর , যার ওপর মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর হয়েছে তাকে রেখে দেন এবং অন্যটিকে তার শেষ সময় পর্যন্ত (জীবন ধারণের জন্য পুনরায় ফেরত) পাঠিয়ে দেন।” (সূরাহ্ আয্-যুমার: ৪২)
এ থেকে সুস্পষ্ট যে , মানুষের মৃত্যুর সময় প্রাণ গ্রহণের বিষয়টি একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাধীনে সংঘটিত হয়ে থাকে ; কোনো ফেরেশতা বিশেষ বা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ফেরেশতার দ্বারা নয়। এ ব্যবস্থার শীর্ষপরিচালক ও দায়িত্ব বণ্টনকারী হচ্ছেন একজন ফেরেশতা ; অন্য ফেরেশতারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। তাই এ কাজকে যেমন সরাসরি প্রাণ গ্রহণকারী ফেরেশতার প্রতি আরোপ করা চলে , তেমনি এ ব্যবস্থাপনার পরিচালক মালাকুল মাওতের প্রতিও আরোপ করা চলে। তেমনি এ ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক নির্ধারিত এবং এর মাধ্যমে তাঁরই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় বিধায় তা আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতিও আরোপ করা চলে। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতি আরোপ করার মানে এ নয় যে , স্বয়ং আল্লাহ্ই প্রতিটি প্রাণ গ্রহণ করেন এবং ফেরেশতারা প্রাণ গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত নয়।
অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলা হয় যে , সৃষ্টিজগতের সব কিছুই আল্লাহ্ তা‘ আলা করছেন তাহলে ভুল হবে না। কারণ , ফেরেশতা , মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুল যা কিছু করছে তা আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি হিসেবে , তাঁরই দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত যান্ত্রিক নিয়মে বা তাঁরই দেয়া স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্যে করছে। আল্লাহ্ তা‘ আলা স্বাধীন ইচ্ছা না দিলে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হতে পারতো না এবং তার সঠিক বা ভুল প্রয়োগের প্রশ্নও উঠতো না। অতএব , এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল কাজই আল্লাহ্ তা‘ আলার কাজ। কিন্তু এ হচ্ছে উঁচু স্তরের ভাববাচক কথা। এর মানে এ নয় যে , মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী নয় এবং তাকে দিয়ে যান্ত্রিকভাবে সব কিছু করিয়ে নেয়া হয়। অর্থাৎ এ ধরনের আয়াত থেকে কোনোভাবেই জাবারীয়াহ্ তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ , ঐ সব আয়াতের ভিত্তিতে জাবারীয়াহ্ তত্ত্বকে সঠিক মনে করা হলে যে সব আয়াত থেকে সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রমাণিত হয় সে সব আয়াতকে উপেক্ষা করা হয়।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে , অধীনস্থদের কাজকে উপরস্থ কর্তা বা মালিকের কাজ বলে উল্লেখ করার রীতি মানবিক সমাজেও প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ , কোনো সরকারের আমলে কোনো বড় ধরনের কাজ সম্পাদিত হলে , যেমন: বড় কোনো সেতু বা মহাসড়ক বা ভবন নির্মিত হলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে বলা হয় যে , অমুক এটি নির্মাণ করেছেন। আবার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সংসদ সদস্যের ভূমিকা থাকলে বলা হয় যে , অমুক এমপি এটি বানিয়েছেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে যখন বলা হয় যে , অমুক এটি নির্মাণ করেছেন , তখন তা থেকে এমপি কর্তৃক তা নির্মাণের দাবীকে অস্বীকার করা হয় না এবং এমপি কর্তৃক নির্মাণের কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তা নির্মাণের দাবীকে অস্বীকার করা হয় না। অন্যদিকে সেটির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় একজন মন্ত্রী (ধরুন , যোগাযোগ মন্ত্রী) জড়িত থাকেন এবং এ কারণে তিনি তা নির্মাণ করেছেন বলেও উল্লেখ করা হয়। আবার এ কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মকর্তা , ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মচারীগণ এতে জড়িত থাকেন বিধায় তাঁরাও বলেন যে , আমরা এটি নির্মাণ করেছি। অথচ আক্ষরিক অর্থে যাকে নির্মাণকাজ বলা হয় তাতে এদের কেউই জড়িত থাকেন না। বরং বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক , যেমন: রাজমিস্ত্রী , রাজ-যোগালী ও সাধারণ শ্রমিক , রংকারক , বিদ্যুত মিস্ত্রী , কাঠমিস্ত্রী , ঝালাইকারক ইত্যাদি বহু লোক জড়িত থাকে এবং তারাও বলে যে , আমরা এটি নির্মাণ করেছি। অনুরূপভাবে এর ত্রুটিগুলোও স্বতন্ত্রভাবে তাদের সকলের প্রতিই আরোপ করা হয়। যেমন: বলা হয় যে , অমুক প্রেসিডেন্ট (বা প্রধান মন্ত্রী বা এমপি বা মন্ত্রী) এ স্থাপনাটি নির্মাণ করেছেন , কিন্তু এর ডিজাইনটা ভালো হয় নি , বা (বলা হয়:) নিম্ন মানের সিমেন্ট ব্যবহার করায় এখনই আস্তরণ উঠে যাচ্ছে , যদিও এসব ত্রুটির সাথে তাঁদের কারোই সরাসরি সম্পর্ক নেই। বরং ডিজাইনের ত্রুটির জন্য ইঞ্জিনীয়ার বা স্থপতি এবং নিম্ন মানের সিমেন্টের জন্য ঠিকাদার দায়ী। অথবা ফেটে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের বা রাজমিস্ত্রীদের দায়িত্বহীনতাও দায়ী হতে পারে।
অনুরূপভাবে একটি সংবাদপত্রের উদাহরণ থেকেও বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে। একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক-প্রকাশকের প্রতি পুরো পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ আরোপ করা হয় , যদিও এ সব কাজ তাঁর অধীনস্থ লোকেরাই করে থাকেন ; এমনকি সম্পাদকীয় নিবন্ধ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদকগণ লিখে থাকেন ; সম্পাদক স্বয়ং কদাচিৎ তা লিখে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরো কাজটিই সম্পাদক কর্তৃক নির্ধারিত সম্পাদকীয় নীতিমালার আলোকে সম্পাদিত হয়ে থাকে বিধায় তা সম্পাদকের কাজ বলে বিবেচিত হয় , যদিও প্রতিটি কাজই তাঁর মনমতো বা তাঁর দৃষ্টিতে কাঙ্ক্ষিত মানের হয় না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই সম্পাদকীয় নীতির বরখেলাফ কোনো কাজ করতে পারেন , কিন্তু এ কারণে কাজের প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে না , যদিও এজন্য পরে জবাবদিহি করতে হয় ; এমনকি চাকরিও চলে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অধীনস্থ লোকের ত্রুটিকেও সম্পাদকের প্রতি আরোপ করা হয় এবং তিনি সে কাজের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করেন না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে , তিনিই এ ত্রুটি করেছেন বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে দিয়ে তিনি তা করিয়েছেন এবং এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক দায়ী নন।
মূসা ও খিজির ( আঃ ) এর ঘটনা
মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যে সব কাজ সম্পাদন করে অথবা সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকে তাকে এক বিবেচনায় তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ধরনের কাজ হচ্ছে এই যে , বান্দাহ্ কেবল আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলা চান যে , বান্দাহ্ অমুক কাজটি অবশ্যই সম্পাদন করুক তখন সে সংশ্লিষ্ট কাজটি সম্পাদন করে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা মানে তাঁর সৃষ্টি-ইচ্ছা নয় , বরং তাঁর পসন্দ , তবে সে পসন্দ বান্দাহর জন্য নির্দেশমূলক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলা বান্দাহর দ্বারা একটি কাজ অবশ্যই সম্পাদিত হওয়া পসন্দ করেন , কিন্তু এজন্য তিনি বান্দাহকে বাধ্য করেন না। তবে বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা‘ আলার পসন্দকে গুরুত্ব প্রদান করে বলে সে স্বেচ্ছায় ও স্বীয় স্বাধীন এখতিয়ার ব্যবহার করে তা সম্পাদন করে। বান্দাহদের‘ ইবাদত-বন্দেগী এ পর্যায়ের। তাছাড়া নবী-রাসূলগণ (আঃ) ও আল্লাহর ওলীগণের প্রতি আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ ইচ্ছা (পসন্দ)ও পৌঁছে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা তা সম্পাদন করেন।
আরেক ধরনের কাজ হচ্ছে এই যে , বান্দাহ্ তার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন একটি কাজ সম্পাদনকে যরূরী গণ্য করে , যে কাজটি সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলাও চান যে , তা সম্পাদিত হোক। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা বা পসন্দ বান্দাহর প্রতি নির্দেশমূলক নয়।
তৃতীয় এক ধরনের কাজ আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ কোনো সাধারণ বা নির্দেশমূলক ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই , যদিও হতে পারে যে কাজটি আল্লাহ্ তা‘ আলার নিকট সাধারণভাবে পসন্দনীয় , অথবা‘ অপসন্দনীয় নয়’ অথবা অপসন্দনীয় , কিন্তু অপসন্দনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলা তাকে তা করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন না। এ ক্ষেত্রে বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা‘ আলার কোনো প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত ছাড়াই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বা দ্বীনী ও শর‘ ঈ জ্ঞানের আলোকে একটি কাজকে ভালো জেনে সম্পাদন করে অথবা একটি কাজকে খারাপ জেনেও কুপ্রবৃত্তিবশে তা সম্পাদন করে।
কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-কাহফে উল্লিখিত হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনায় হযরত খিযির (আঃ) কর্তৃক এ তিন ধরনের তিনটি কাজ সম্পাদনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (অবশ্য তৃতীয় ধরনের কাজের ক্ষেত্রে তিনি একটি ভালো কাজ সম্পাদন করেন ; মন্দ কাজ সম্পাদন করেন নি।)
কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-কাহফের ৬০ নং থেকে ৮২ নং আয়াতে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। যদিও এতে হযরত খিযির (আঃ)-এর নাম উল্লিখিত হয় নি , বরং আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁকে স্বীয় বান্দাহদের অন্যতম বলে এবং স্বীয় সন্নিধান থেকে তাঁকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মুফাসসিরগণ একমত যে , তিনি হচ্ছেন হযরত খিযির (আঃ)।
হযরত মূসা (আঃ) দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য তাঁর সাথে থাকার অনুমতি চান। হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)কে এ শর্তে অনুমতি দেন যে , তিনি হযরত খিযির (আঃ)-এর কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না তিনি নিজেই তাঁর কাজের ব্যাখ্যা দেন। হযরত মূসা (আঃ) এ শর্তে রাযী হন।
অতঃপর তাঁরা চলার পথে একটি নৌকায় আরোহণ করলেন এবং হযরত খিযির (আঃ) নৌকাটিতে ছিদ্র করে দিলেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত মূসা (আঃ) কাজটিকে অন্যায় বলে অভিহিত করলেন। তখন হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মূসা (আঃ) তাঁর ভুল স্বীকার করলেন ও তা উপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানালেন । এরপর চলার পথে হযরত খিযির (আঃ) একটি বালককে হত্যা করলেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যার এ কাজকে গুরুতর অন্যায় বলে অভিহিত করলেন। তখন হযরত খিযির (আঃ) পুনরায় হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিলে মূসা (আঃ) কথা দিলেন যে , পুনরায় প্রশ্ন করলে হযরত খিযির (আঃ) আর তাঁকে সাথে রাখতে বাধ্য থাকবেন না। অতঃপর তাঁরা এক জনপদে পৌঁছলেন যেখানকার লোকেরা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত জনপদে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে হযরত খিযির (আঃ) তা মেরামত করে দিলেন। তা দেখে হযরত মূসা (আঃ) বললেন যে , তিনি (খিযির) চাইলে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। তখন হযরত খিযির (আঃ) শর্ত অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পূর্বে তিনি তাঁর কাজের যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।
হযরত খিযির (আঃ) বলেন যে , নৌকাটি ছিলো কয়েক জন দরিদ্র লোকের ও তাদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু অপর পারে এক যালেম শাসক ছিলো যে নৌকাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিতো। তিনি বলেন: তাই“ আমি” তাতে ত্রুটি সৃষ্টি করতে চাইলাম (যাতে তা ছিনিয়ে নেয়া না হয়)। আর যে বালকটিকে তিনি হত্যা করেন তার সম্পর্কে তিনি বলেন যে , তার পিতা-মাতা ঈমানদার , কিন্তু (তিনি বলেন:)“ আমরা” (আমি ও আল্লাহ্ তা‘ আলা) আশঙ্কা করলাম যে , সে তার অবাধ্যতা ও কুফর্ দ্বারা তাদের উভয়কে প্রভাবিত করবে এবং“ আমরা” (আমি ও আল্লাহ্ তা‘ আলা) চাইলাম যে , তাদের উভয়ের (বালকটির পিতা-মাতার) রব (আল্লাহ্ তা‘ আলা) তাদেরকে তার (বালকটির) পরিবর্তে তার তুলনায় উত্তম (একটি সন্তান) প্রদান করুন-যে হবে পবিত্র ও অধিকতর দয়ার্দ্রচিত্ত। আর হযরত খিযির (আঃ) যে ভগ্ন প্রাচীরটি মেরামত করে দেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে , এটির নীচে গুপ্তধন ছিলো এবং এটি ছিলো দু’ জন পিতৃহীন বালকের যাদের পিতা ছিলো সৎকর্মশীল। তিনি বলেন: সুতরাং (হে মূসা!)“ আপনার রব (আল্লাহ্ তা‘ আলা) চাইলেন যে , তারা যৌবনে উপনীত হয়ে এ গুপ্তধন উদ্ধার করুক (এবং প্রাচীরের ভগ্নতার কারণে তা অন্য লোকদের হস্তগত না হোক)। আর আমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এ কাজ (দেয়াল মেরামত) করি নি।”
হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে , হযরত খিযির (আঃ) একটি কাজ কেবল তাঁর নিজের ইচ্ছায় (আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক বাধ্য না হয়ে , এমনকি শর‘ ঈ নির্দেশ না থাকা বা বিশেষ নির্দেশও না পাওয়া সত্ত্বেও) , একটি কাজ আল্লাহ্ তা‘ আলার ও তাঁর নিজের উভয়ের ইচ্ছায় এবং একটি কাজ কেবল আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ ইচ্ছা বা নির্দেশের কারণে সম্পাদন করেছিলেন। আর বলা বাহুল্য যে , এ তিন ধরনের কাজই আল্লাহ্ তা‘ আলার সর্বজনীন ইচ্ছার (বা সর্বজনীন অনুমতি ও অবকাশের) আওতায় বান্দাহ্ কর্তৃক স্বেচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে।
হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর এ ঘটনায় আল্লাহ্ তা‘ আলা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর যৌথ ইচ্ছা অনুযায়ী ঈমানদার পিতা-মাতার নাবালেগ শিশুকে হত্যার ঘটনা থেকে মানবকুলের প্রতি আল্লাহ্ তা‘ আলার অনুগ্রহের আরেকটি মূলনীতি পাওয়া যায়। তা হচ্ছে এই যে , যদিও মানুষের বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) ও ইচ্ছাশক্তি এতই প্রবল যে , বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ্ব্) হওয়ার পর একটি মানুষ সহজাত জ্ঞানের দ্বারা সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ বুঝতে পারে (সূরাহ্ আশ্-শামস্: ৮) এবং স্বেচ্ছায় সত্যের বা মিথ্যার পথ বেছে নিতে পারে , সুতরাং নিঃসন্দেহে বালেগ্ব্ হবার পূর্বে তার ভবিষ্যত ঈমান ও কুফরের বিষয়টি থাকে দুই সম্ভাবনাযুক্ত , তবে বিভিন্ন কারণের প্রভাবে ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে , কোনো কোনো মানবসন্তানের বালেগ্ব্ হবার পরে নাফরমান বা কাফের-মোশরেক হবার বিষয়টি তার বালেগ্ব্ হবার পূর্বেই অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে এবং সে যদি ঈমানদার পিতা-মাতার সন্তান হয় , তো তার কারণে তার পিতা-মাতার নাফরমানীতে জড়িত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘ আলার দয়া ও অনুগ্রহের দাবী হচ্ছে এই যে , তিনি ঐ মানবসন্তানটিকে বালেগ্ব্ হবার পূর্বেই মৃত্যু প্রদান করবেন।
বলা বাহুল্য যে , উক্ত ঘটনায় (এবং এ ধরনের অন্য সকল ঘটনায়ই) আল্লাহ্ তা‘ আলার এ ধরনের বিশেষ হস্তক্ষেপ সন্তান ও পিতামাতা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। আর হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনায় এটি ঈমানদার পিতা-মাতার সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটলেও সম্ভবতঃ খোদায়ী অনুগ্রহের এ নীতিটি কেবল ঈমানদার পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় , বরং সকল নাবালেগ্ব্ই এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ ঈমান ও কুফর্ এবং ভালো ও মন্দের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারা ও স্বেচ্ছায় একটিকে বেছে নেয়ার জন্য উপযুক্ত হবার তথা বিচারবুদ্ধিগত পরিপক্বতার অধিকারী হবার পূর্বেই কোনো বা বিভিন্ন কারণে যে কোনো মানবসন্তানের জন্যই ভবিষ্যত কুফরী‘ অনিবার্য হয়ে গেলে’ আল্লাহ্ তা‘ আলার অনুগ্রহের দাবী হচ্ছে তাকে কুফরী ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। অবশ্য এ থেকে মনে করা ঠিক হবে না যে , বালেগ্ব্ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী সকল মানবসন্তানই বুঝি এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বরং এ হচ্ছে ব্যতিক্রম ; অধিকাংশ নাবালেগ্ব্ মানবসন্তানের মৃত্যুই প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয়ে থাকে যার মধ্যে মানবিক কারণও অন্যতম। তবে কোন্ শিশুর মৃত্যু প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয়েছে এবং কোন্ শিশুর মৃত্যু আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ অনুগ্রহ-ইচ্ছার কারণে হয়েছে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় , ঠিক যেভাবে হযরত খিযির (আঃ) ও আল্লাহ্ তা‘ আলার যৌথ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর (খিযির) দ্বারা নিহত শিশুটির হত্যার ঘটনাটি (মুফাসসিরগণের প্রায় সর্বসম্মত মত অনুযায়ী ,) সাধারণ মানুষের নিকট হত্যা হিসেবে প্রতিভাত হয় নি , বরং প্রকৃতিক কারণে মৃত্যু বলে প্রতিভাত হয়েছিলো।
আল্লাহ্ ও মানুষের কাজের মধ্যে মিল-অমিল
জাবর্ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের পরস্পর বিরোধী ধারণা থেকে সৃষ্ট জটিলতার সমাধানের জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলা ও মানুষের কাজের মধ্যে মিল ও অমিলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে স্বীয় গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ )
“ (এ হলো) আল্লাহর প্রকৃতি ; আল্লাহ্ এর ওপরেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহর সৃষ্টিতে (সৃষ্টির মূল পরিকল্পনা ও কাঠামোতে) কোনোরূপ পরিবর্তনের স্থান নেই।” (সূরাহ্ আর্-রূম্: ৩০)
এ থেকে সুস্পষ্ট যে , আল্লাহ্ তা‘ আলার মধ্যে যে সব গুণ রয়েছে মানুষের মধ্যে তার সবই রয়েছে। জীবন , ইচ্ছাশক্তি , জ্ঞান , প্রকাশ ক্ষমতা , সৃজনশীলতা , দয়া , ভালোবাসা ইত্যাদি আল্লাহ্ তা‘ আলার সব গুণই মানুষকে দেয়া হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্ তা‘ আলার কোনো গুণ না দেয়া হলে তিনি এ কথা বলতেন না যে , তিনি মানুষকে তাঁর প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ মানুষ আল্লাহ্ তা‘ আলার খলীফাহ্ , আর খলীফাহ্ বা প্রতিনিধি হওয়ার দাবী হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা সমগ্র সৃষ্টিলোকের ক্ষেত্রে যত কাজ সম্পাদন করেন মানুষও ধরণীর বুকে তা সম্পাদন করবে। এজন্য তাকে অবশ্যই ঐসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ও তা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অধিকারী থাকতে হবে। অন্যথায় তাকে আল্লাহ্ তা‘ আলার খলীফাহ্ নামে অভিহিত করা সঙ্গত হতো না।
অবশ্য জন্মের সময় মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলী সুপ্ত সম্ভাবনা আকারে বিদ্যমান থাকে , তাই তা কাজে লাগানোর জন্য প্রথমে তার যথাযথ বিকাশের প্রয়োজন। এই বিকাশ যতটা না মানুষের পারিপার্শ্বিকতার ওপরে নির্ভরশীল , তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল।
মোদ্দা কথা , মানুষকে আল্লাহর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করায় এবং সে আল্লাহ্ তা‘ আলার খলীফাহ্ বিধায় তার গুণাবলী আল্লাহর গুণাবলীর অনুরূপ। অতএব , সে ইচ্ছাশক্তি , এখতিয়ার ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার অধিকারী এবং এ কারণে তার কাজকর্ম আল্লাহ্ তা‘ আলার কাজকর্মের অনুরূপ। অতএব , এ থেকে শুধু মানুষের এখতিয়ারই প্রমাণিত হয় না , বরং মানুষের কাজকর্মের ধরন পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ তা‘ আলার কার্যাবলীর ধরন উদ্ঘাটন করা যেতে পারে। কারণ , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষের সত্তায় স্বীয় কার্যাবলীর ধরন নিহিত রেখেছেন এবং সে তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কাজ করে থাকে।
এ হলো গুণাবলী ও কাজকর্মের দিক থেকে আল্লাহ্ তা‘ আলা ও মানুষের মধ্যকার মিল। তবে উভয়ের মধ্যে বিরাট অমিলও রয়েছে। এ অমিল হলো: আল্লাহ্ তা‘ আলা হচ্ছেন মানুষের স্রষ্টা , আর মানুষ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি ; আল্লাহ্ অনাদি , অনন্ত ও অসীম সত্তা , আর মানুষ স্থান ও কালের গর্ভে আবির্ভূত সসীম সত্তা। আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলী ও সত্তা অভিন্ন , কিন্তু মানুষের সত্তা ও গুণাবলী বিভিন্ন। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন বিধায় চিরন্তন ও চির পরিপূর্ণ , কিন্তু মানুষের যে কোনো গুণ তার সত্তায় সম্ভাবনা আকারে বিদ্যমান ও ক্রমবিকাশমান বা ক্রম-অর্জনীয়। সসীমতার কারণে মানুষ বস্তুদেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌন প্রেরণার অধিকারী , কিন্তু অসীমতার কারণে তিনি এসবের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরম প্রমুক্ত। জ্ঞান , যোগ্যতা ও ক্ষমতার পূর্ণতা ও অসীমতার কারণে আল্লাহ্ তা‘ আলার একক ও প্রত্যক্ষ কর্মে কোনোরূপ ত্রুটি অকল্পনীয় , কিন্তু অপূর্ণতা ও সসীমতার কারণে মানুষের যে কোনো কাজে দুর্বলতা ও ত্রুটির সম্ভাবনা থেকেই যায়। আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর কাজের ক্ষেত্রে কারো বা কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত বা বাধাগ্রস্ত হন না ; তিনি যা-ই চান তা যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ায় চান সেভাবে ও সে প্রক্রিয়ায় হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি , এখতিয়ার ও কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা প্রভাবিত হয় এবং সে যেভাবে চায় প্রায়শঃই হুবহু সেভাবে সংঘটিত হয় না। এর ফলে এটা সন্দেহাতীত যে , সে এখতিয়ারের অধিকারী বটে , তবে নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের অধিকারী নয়।
বস্তুতঃ আমরা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদেরকে যেভাবে তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে দেখি তা তার সত্তায় আল্লাহ্ তা‘ আলার কার্যাবলীর অনুসরণ ও অনুকরণের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ , যদিও তার গুণাবলীর সীমাবদ্ধতার কারণে সে হুবহু তা অনুকরণ ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না , বরং তার কাজে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কাজ পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ তা‘ আলার কাজের ধরন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।
আমরা দেখতে পাই যে , কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যে সব কাজ নিজেই সম্পাদনে সক্ষম তার মধ্য থেকে অনেক কিছুই অন্যের দ্বারা সম্পাদন করিয়ে নেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে যেমন কাজের এখতিয়ার প্রদান করেন তেমনি কাজ সম্পাদনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তার কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি সাধারণতঃ নীচের দিকের কর্মকর্তা , কর্মচারী , শ্রমিক ও চাকর-চাকরানীদেরকে স্বয়ং নিয়োগ দেন না , বরং এ দায়িত্ব প্রতিনিধি বা উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দেন , তবে প্রয়োজন বোধে কখনো কখনো কতককে নিজেই নিয়োগ দেন বা বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়োগদানের জন্য প্রতিনিধি বা উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের পথনির্দেশ দেন বা বাধ্য করেন। অনেক ক্ষেত্রে একজন মালিক বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে কোনো গুরুদায়িত্ব প্রদান করতে পারেন যে ব্যক্তি যোগ্য কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। এর কারণ হয়তো পুরোপুরি বিশ্বস্ত সুযোগ্য লোকের অভাব। আবার বিশ্বস্ত লোককে গুরুদায়িত্ব প্রদান থেকে বিরত থাকেন ; কারণ , সে বিশ্বস্ত হলেও সুযোগ্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এমন লোককেও দায়িত্ব দেয়া হতে পারে যে ব্যক্তি বিশ্বস্তও নয় , সুযোগ্যও নয় ; কারণ উভয় ধরনের লোকের অভাব। এটা আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন। মানুষ যে , এ ধরনের ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং তা কার্যকর করতে সক্ষম হচ্ছে তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিব্যবস্থাপনারই অংশবিশেষ মাত্র। তবে আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মে , যেমন: নবী-রাসূলগণকে (আঃ) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কখনোই ভুল ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন নি , কিন্তু মানুষ মালিক বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যথোপযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও সঠিক মনে করেই ভুল ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধি তথা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে পারেন ।
মানবিক জগতে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধি , কর্মকর্তা , কর্মচারী , শ্রমিক ও চাকর-চাকরানীদের কাজে কাজটি সম্পাদনকালে পদে পদে হস্তক্ষেপ করেন না , বরং কাজের শেষে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনকারীকে পুরস্কৃত করেন এবং কাজে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি সৃষ্টিকারী , ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহারকারী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে কাজ সম্পাদনকালেও তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে , স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলাও তাঁর প্রাণশীল সৃষ্টিকুলকে , বিশেষ করে মানুষকে কাজ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন এবং তাদের কাজের ওপর নযর রাখেন , আর প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় হস্তক্ষেপ করেন। তবে সীমাবদ্ধতার অধিকারী হওয়ার কারণে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন , প্রতিনিধি ও কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগদান , কাজের দিকনির্দেশ প্রদান , তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা , কাজে হস্তক্ষেপ এবং তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন , কিন্তু যে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে প্রমুক্ত সত্তা আল্লাহ্ তা‘ আলা কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র ভুল করেন না।
আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টিও মানুষের আচরণ থেকে সহজেই বুঝা যেতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি তার অধীনস্থ লোকদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার বা তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকেন না। অনেক সময় তিনি এর বাইরেও অনেককে অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এ অনুগ্রহ প্রদর্শনের মানদণ্ডও সব সময় এক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন অধীনস্থ ব্যক্তি কেবল তার চুক্তিভিত্তিক বা নিয়োগপত্রে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে না , বরং সে এর বাইরে অতিরিক্ত খেদমতও আঞ্জাম দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক বা কর্তা তার কাছ থেকে অতিরিক্ত খেদমত চায় এবং তা সম্পাদন করায় তার জন্যে নির্ধারিত বিনিময় প্রদান করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক বা কর্তা না চাইলেও সে স্ব-উদ্যোগে অতিরিক্ত কাজ করতে পারে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তার কাজের উদ্দেশ্য দুই ধরনের হতে পারে: হয় সে মালিক বা কর্তাকে খুশী করার জন্য এ কাজ করে , কারণ সে জানে যে , মালিক বা কর্তা খুশী হলে কখনো না কখনো এবং কোনো না কোনোভাবে সে লাভবান হবেই , অথবা কোনো না কোনো কারণে সে মালিক বা কর্তাকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ভালোবাসে বলেই কোনোরূপ বস্তুগত লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ ছাড়াই নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত খেদমত আঞ্জাম দেয়। অন্য কথায় , সে অতিরিক্ত খেদমত আঞ্জাম দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং মালিক বা কর্তার স্নেহ-ভালোবাসা প্রাপ্তি ছাড়া কোনোকিছুর প্রতিই তার দৃষ্টি থাকে না। এমনকি এমনও হতে পারে যে , মালিক বা কর্তার ভালোবাসা প্রাপ্তির দিকেও তার দৃষ্টি নেই , বরং মালিক বা কর্তাকে ভালোবাসতে পেরে ও তদনুযায়ী কাজ করতে পেরেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। এ ধরনের কর্মী মালিক বা কর্তার বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হয় এবং সে অনুগ্রহ বস্তুগত বা অবস্তুগত বা একই সাথে উভয় ধরনের হতে পারে।
আরো কতক ক্ষেত্রেও অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি মালিক বা কর্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে পারে। কোনো কর্মী যে কাজ সম্পাদন করে তার বিনিময়ে যে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা কাজের বিচারে যথেষ্ট হলেও তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি মালিক বা কর্তার নিকট বিশেষ অনুগ্রহের জন্য আবেদন জানাতে পারে। তখন মালিক বা কর্তা তাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করতে পারেন বা কোনো কারণে না-ও করতে পারেন ; তবে এ ক্ষেত্রে অনুগ্রহ প্রদানের সম্ভাবনার পাল্লাই ভারী থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে , সে ব্যক্তি তার অসুবিধা সত্ত্বেও মালিক বা কর্তার নিকট অনুগ্রহের জন্য আবেদন না-ও জানাতে পারে। এমতাবস্থায় মালিক বা কর্তা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করতে পারেন বা না-ও করতে পারেন ; তবে এ ক্ষেত্রে সাহায্য না করার সম্ভাবনাই প্রবল। শুধু তা-ই নয় , অধীনস্থ ব্যক্তি যে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা তার জন্যে যথেষ্ট হলেও এবং তার কোনো বিশেষ অভাব বা অসুবিধা বা সমস্যা না থাকলেও সে আরো বেশী আরাম-আয়েশের জন্য মালিক বা কর্তার কাছে অনুগ্রহের জন্য আবেদন জানাতে পারে। এ ক্ষেত্রেও মালিক বা কর্তা তার প্রতি অনুগ্রহ করতেও পারেন বা না-ও করতে পারেন। অবশ্য মালিক বা কর্তার এসব আচরণের (অনুগহ করা বা না করা) পিছনে বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোনো কর্মচারী মালিককে পসন্দ বা অপসন্দ করতে পারে , কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারে বা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকতে পারে , তার কোনো উত্তম গুণ বা কোনো খারাপ অভ্যাস থাকতে পারে , কোনো উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সাথে সম্পর্কের কারণে তার অনুকূলে সুপারিশ করা হয়ে থাকতে পারে , সে মালিক বা কর্তার কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনের প্রিয়ভাজন বা অপ্রিয়ভাজন হয়ে থাকতে পারে। এভাবে জ্ঞাত-অজ্ঞাত আরো অনেক কারণ থাকতে পারে ; এমনকি এমন কারণও থাকতে পারে যে সম্পর্কে স্বয়ং ব্যক্তি নিজেও সচেতন নয় , বরং কেবল মালিক বা কর্তা অবগত আছেন বলেই তিনি তদনুযায়ী আচরণ করেন। এর মধ্যে কেবল স্বীয় বদান্যতা-গুণের কারণে অনুগ্রহকরণও অন্যতম।
বলা বাহুল্য যে , মানুষের এ সব আচরণ আল্লাহ্ তা‘ আলার আচরণের উদ্ঘাটনকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলাও এভাবেই আচরণ করেন এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সত্তাগতভাবে মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা বিদ্যমান বিধায়ই তারা এরূপ আচরণ করে থাকে। তবে পার্থক্য এখানে যে একজন মানুষ মালিক বা কর্তার মধ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলার সকল গুণই সসীম ও অপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার মধ্যে কোনো কোনো গুণ খুবই কম বা প্রায় শূন্য মাত্রায় থাকতে পারে। ফলে মানুষের আচরণে অন্যায় , সীমালঙ্ঘন , ভ্রান্তি , ভারসাম্যহীনতা ও অযৌক্তিকতা থাকতে পারে-আল্লাহ্ তা‘ আলার আচরণ যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত।
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর সৃষ্টিলোকে প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়ের জন্য , বিশেষ করে মানুষের কাজকর্ম সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া জারী রেখেছেন তা জাবর্-ও নয় , নিরঙ্কুশ এখতিয়ারও নয় , বরং জাবর্ ও এখতিয়ারের সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য তার আওতা বহির্ভূত অসংখ্য কারণ দ্বারা ও আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সব নিয়ন্ত্রণের অধীনে তার সীমিত পরিমাণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার রয়েছে। একজন মানুষ মালিক বা কর্তা যেভাবে তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিকে তার আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও কাজে তজ্জনিত ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন না , কিন্তু তার আওতাভুক্ত ও এখতিয়ারাধীন বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন ও তার ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন , তাতে এ সত্যেরই প্রতিফলন ঘটে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা মানুষকে তার আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও আমলের ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করবেন না , কিন্তু তার যতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে ততটুকুর জন্য তথা তার আওতাভুক্ত ও এখতিয়ারাধীন কার্যাবলীর ভালোমন্দের জন্য তার নিকট জবাবদিহি আদায় করবেন এবং তাকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। এ থেকে এ-ও জানা যায় যে , একজন কর্মীর আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির ওপরে তার প্রতি মালিক বা সর্বময় কর্তার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি নির্ভর করে না , বরং তার নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপরে নির্ভর করে , তেমনি আওতা বহির্ভূত কারণে মানুষের পার্থিব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ধারিত হতে পারে বটে , কিন্তু তার পরকালীন সাফল্য ও ব্যর্থতা তথা আল্লাহ্ তা‘ আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কেবল এর ওপরই নির্ভর করে যে , সে কি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা‘ আলার সন্তুষ্টি অর্জনমূলক কাজ করেছে , নাকি তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে।
সৃষ্টির ত্রুটি ও অপূর্ণতার কারণ
আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিনিচয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যষ্টিক বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ এবং একটি হচ্ছে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে , এ সৃষ্টিলোকে রয়েছে শত শত কোটি ধরনের ও প্রজাতির সৃষ্টি-যে সম্বন্ধে সামান্য চিন্তা করলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় । এই বিভিন্ন ধরন ও প্রজাতির সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষের ন্যায় জটিলতম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। একটি অতি ক্ষুদ্র পিপিলিকার গঠনশৈলী , বুদ্ধিমত্তা ও কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা করলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। আর মানুষ নিয়ে গবেষণা করে এখনো তার চূড়ান্ত কূলকিনারা করা যায় নি।
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় , একটি মানুষের মস্তিষ্কের শুধু স্মৃতিকোষগুলোর ক্ষমতাই চার হাজার সুপার কম্পিউটারের সমান। আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ )
“ আর এ পৃথিবীর মধ্যে এবং তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও , দৃঢ় প্রত্যয় (ইয়াক্বীন্)-এর অধিকারী লোকদের জন্য নিদর্শনাদি রয়েছে ; তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না ?” (সূরাহ্ আয্-যারি‘ আত্: ২০-২১)
( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )
“ অতএব , পরম বরকতময় আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।” (সূরাহ্ আল্-মু’ মিনূন্: ১৪)
কিন্তু ব্যষ্টিক পর্যায়ে আমরা কিছু কিছু সৃষ্টিতে ত্রুটি দেখতে পাই। যেমন: একটি শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে , একটি ফলের এক পাশ শক্ত হয়ে যেতে পারে , ফলে তা আর ভক্ষণোপযোগী থাকে না , ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে , এসব ত্রুটির উৎস কী ? মহান প্রজ্ঞাময় পরম প্রমুক্ত আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিতে তো ত্রুটি থাকার কথা নয় ; তাহলে কেন এ সব ত্রুটি ?
এখানে আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিপরিকল্পনা ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রণিধানের বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে , আদি সৃষ্টিসমূহ , বিশেষ করে সৃষ্টিলোকে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিধান সমূহ আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। তেমনি প্রাথমিক সৃষ্টিসমূহ , বিশেষতঃ ফেরেশতাকুল , বস্তুজগতের মৌলতম উপাদান (যার সাহায্যে পরমাণু গঠন করা হয়েছে) এবং এ ধরনের আরো অনেক সৃষ্টি-যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই-আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। এ সব সৃষ্টির পূর্ণ কারণ স্বয়ং এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা‘ আলা। এ সব সৃষ্টিতে কোনো রকমের ত্রুটি বা অপূর্ণতার প্রশ্নই ওঠে না।
আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে পরবর্তী পর্যায়ের তথা যৌগিক সৃষ্টি সমূহকেও স্বীয় প্রত্যক্ষ ইচ্ছার মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তাতে তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন উপায়-উপাদানের কোনো কার্যকরিতা বা গুণ প্রকাশ পেতো না , তেমনি তিনি যে বিস্ময়কর জটিল প্রাকৃতিক বিধান সৃষ্টি করেছেন তা সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু তিনি চাইলেন যে , যৌগিক সৃষ্টিসমূহে তাঁরই সৃষ্ট প্রাথমিক সৃষ্টিসমূহ (প্রাকৃতিক বিধান , উপায়-উপাদান ও ফেরেশতাকুল) ভূমিকা পালন করুক যাতে তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিক্ষমতার মহিমা প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ , একজন লোক স্বীয় গৃহকর্ম , বাগান রচনা ও কৃষিকাজ অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আঞ্জাম দেয়। কিন্তু আরেক জন লোক একটি কম্পিউটার ও কম্পিউটার-চালিত রোবট তৈরী করেছে এবং তার পক্ষ থেকে ঐ রোবটটি তার সকল কাজ সম্পাদন করে। কম্পিউটার যতই উন্নত হোক না কেন , এমন কতক কাজ আছে যা মানুষ করতে পারে কিন্তু কম্পিউটার বা কম্পিউটার-চালিত রোবট করতে পারে না এবং যে সব কাজ সম্পাদন করে তাতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকসমূহে তার তুলনায় মানুষের দক্ষতা অনেক বেশী থাকে। (এতদসংক্রান্ত অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যে সম্পর্কে এ সব যন্ত্র ব্যবহারকারী ব্যক্তিমাত্রই কমবেশী অবগত , তবে তা আমাদের অত্র আলোচনার জন্য যরূরী নয়।) এ কারণে যে ব্যক্তি নিজের কাজসমূহ নিজেই সূক্ষ্মভাবে সম্পাদন করে তার কাজের তুলনায় কম্পিউটার-চালিত রোবটের কোনো কোনো কাজে অপূর্ণতা বা ত্রুটি প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কম্পিউটার-চালিত রোবটের কাজ তার স্রষ্টা-মালিকের মহিমাই প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে জ্ঞানী , বিজ্ঞানী ও স্রষ্টা হিসেবে কম্পিউটার-চালিত রোবটের স্রষ্টা-মালিকের গুণাবলী ও যোগ্যতা একই কাজ সমূহ প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনকারীর (তা তার কাজ যতই নিখুঁত হোক না কেন) তুলনায় অনেক বেশী বলে স্বীকৃত হবে।
এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে , সৃষ্টিলোকে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সৃষ্টিতে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায় তার কারণ সৃষ্টিকর্মে অন্য সৃষ্টির ভূমিকা ; সৃষ্টির গুণাবলী ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কারণেই কখনো কখনো এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। মোদ্দা কথা , সাধারণতঃ যৌগিক সৃষ্টিকর্ম সমূহে আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি-ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয় , বরং সৃষ্টিকার্যে ভূমিকা পালনকারী অন্যান্য কারণও পূর্ণ কারণের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলাও তাঁর কতক সৃষ্টিকে‘ স্রষ্টা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ; বলেছেন:
( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )
“ অতএব , পরম বরকতময় আল্লাহ্ যিনি স্রষ্টাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।” (সূরাহ্ আল্-মু’ মিনূন্: ১৪)
অবশ্য সৃষ্টিসমূহ সৃষ্টিকর্মে অংশগ্রহণ করলেও যেহেতু তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি তথা সকল সৃষ্টির আদি কারণ আল্লাহ্ তা‘ আলা , সেহেতু গোটা সৃষ্টিকর্মকে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতি আরোপ করা হলেও ভুল হবে না। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা‘ আলাই প্রকৃত স্রষ্টা বা অমুখাপেক্ষী স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান স্রষ্টা। তাই তিনি এরশাদ করেন:قل الله خالق کل شيءٍ -“ (হে রাসূল!) বলে দিন: আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসেরই স্রষ্টা।” (সূরাহ্ আর্-রা‘ দ্: ১৬) তবে এর মানে সৃষ্টিকর্মে সৃষ্টির ভূমিকার অস্বীকৃতি নয়। অতএব , এ আয়াত থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় না যে , সৃষ্টির মধ্যকার ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ তা‘ আলাই দায়ী। এ প্রসঙ্গেও রোবটের কাজের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রোবট যে পণ্য উৎপাদন করে তাকে কিন্তু রোবটের উৎপাদিত পণ্য বলা হয় না , বলা হয় অমুকের (রোবটের মালিকের) বা অমুক কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্য , কারণ তা উৎপাদনের মূলে রয়েছেন ঐ মালিক। কিন্তু রোবটের কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতা জনিত কারণে পণ্যে যে ত্রুটি দেখা দেয় তা যে , রোবট ব্যবহারের কারণেই সে প্রশ্নেও বিতর্কের অবকাশ থাকে না।
তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে , সৃষ্টিকর্মের পূর্ণ কারণে অংশগ্রহণের কারণেই কাউকে স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে কিনা ? কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা সুস্পষ্টভাবেই তাঁর কতক সৃষ্টিকে‘ স্রষ্টা’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে‘ স্রষ্টা’ বলতে‘ সৃষ্টিকর্মে অংশগ্রহণকারী’ বা‘ আল্লাহর সৃষ্ট উপাদান দ্বারা কিছু সৃষ্টিকারী’ ও যে বুঝানো হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ , আল্লাহ্ তা‘ আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সৃষ্টিকর্ম আরোপ করেছেন ; এরশাদ করেছেন:
( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي )
“ আর (হে ঈসা!) স্মরণ করো , যখন তুমি আমার অনুমতিক্রমে মাটি দ্বারা পাখীর প্রতিকৃতি তৈরী করতে , অতঃপর তাতে ফুঁক দিতে , ফলে আমার ইচ্ছায় তা পাখী হয়ে যেতো।” (সূরাহ্ আল্-মায়েদাহ্: ১১০)
এ আয়াতে সুস্পষ্টতঃই হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক পাখীর প্রতিকৃতি সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে যদিও তিনি তা আল্লাহর সৃষ্ট মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন অর্থাৎ তিনি পাখীর প্রতিকৃতি সৃষ্টির পূর্ণ কারণ ছিলেন না , পূর্ণ কারণে অংশগ্রহণকারী ও বস্তুর রূপান্তরকারী ছিলেন মাত্র।
অবশ্য আল্লাহ্ তা‘ আলা যেখানে মানুষকে‘ স্রষ্টাগণ’ (খালেক্বীন্) বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে তাদেরকে শুধু খোদায়ী সৃষ্টিকর্মের পূর্ণ কারণে অংশগ্রহণকারী হিসেবেই নয় , বরং তাদের মনোজাগতিক সৃষ্টিসমূহের পূর্ণ কারণ রূপ স্রষ্টা হিসেবেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ , মানুষ তার মনোজগতে অনেক কিছু সৃষ্টি করে যদিও তা আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টির তুলনায় খুবই দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী। তাছাড়া মানুষ বস্তুজগতে যে সব পরিবর্তন সাধন করে (বাড়ী , গাড়ী ও আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সুপার কম্পিউটার তৈরী পর্যন্ত) তার ভিত্তি হচ্ছে মনোজগতে সৃষ্ট ঐ সব জিনিসের অবস্তুগত রূপ যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই সৃষ্টি এবং ঐ সব মনোজাগতিক সৃষ্টি পার্থিব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল নয়।
বস্তুতঃ কল্পনা ও পরিকল্পনা (এবং চিন্তা-চেতনা) এক ধরনের অস্তিত্ব ; অনস্তিত্ব নয় বা সাথে সাথে অনস্তিত্বে চলে যাওয়ার মতো বিষয় নয়। বরং এর সবই‘ আলমে মালাকুতে বা‘ আলমে বারযাখে সংরক্ষিত থাকে। আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ )
“ (হে রাসূল!) বলে দিন: তোমাদের অন্তঃকরণে যা কিছু আছে তোমরা যদি তা গোপন করো বা প্রকাশ করো (উভয় অবস্থায়ই) আল্লাহ্ তা জানেন।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ২৯)
এছাড়া আল্লাহ্ তা‘ আলা অনেকগুলো আয়াতে নিজেকেعليم بذات الصدور (অন্তরস্থ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সদা অবগত) বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে , বিশেষ করে এ ব্যাপারেذات (সত্তা) শব্দ ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয় যে , অন্তরস্থ বিষয়সমূহ বা মানোজাগতিক সৃষ্টিসমূহ প্রকৃত অস্তিত্ব।
আল্লাহ্ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন:
( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ )
“ তোমরা তোমাদের সত্তায় যা নিহিত আছে তা প্রকাশ করো বা গোপনই করো , আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণ করবেন।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ২৮৪)
বলা বাহুল্য যে , হিসাবের সময় মানুষের ভালো-মন্দ সকল কর্মকে (যার সবই সংরক্ষিত আছে) দেখানো হবে (সূরাহ্ আল্-যিলযাল্: ৭) যাতে ব্যক্তি তার খারাপ আমল সমূহ অস্বীকার করতে না পারে। অতএব , তার মনোজাগতিক ভালো-মন্দ কাজ (চিন্তা-চেতনা , কল্পনা ও পরিকল্পনা)-ও দেখানো হবে যা এ সবের প্রকৃত অস্তিত্ব হওয়া ও সংরক্ষিত থাকাই প্রমাণ করে। এ ধরনের সৃষ্টির পূর্ণ কারণ স্বয়ং মানুষ ; সে এ সব সৃষ্টির প্রকৃত স্রষ্টা।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে , আল্লাহ্ তা‘ আলা তো তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন ; তিনি চাইলেই সৃষ্টি হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে:
( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )
“ নিঃসন্দেহে তাঁর কাজ (বা আদেশ) এমন যে , তিনি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন:“ হও ,” অতএব , তা হয়ে যায়।” (সূরাহ্ ইয়া-সীন্: ৮২) এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টিকার্যে সচেতন সৃষ্টিসমূহের অংশগ্রহণের সুযোগ কোথায় ?
এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে , এ আয়াতে শুধু আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিকার্যের কথা বলা হয় নি , বরং সৃষ্টিকুলের এখতিয়ারাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও মৌলিক নব নব সৃষ্টি সহ তাঁর সকল কার্যের কথাই বলা হয়েছে , যদিও প্রশ্নের বিষয়বস্তু অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যও তার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা‘ আলা যখন সৃষ্টিকার্যের ইচ্ছা করেন তখন তার মানে এ নয় যে , তিনি যখন কোনো সৃষ্টিকার্যের ইচ্ছা করেন তখন সেই মুহূর্তেই তা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য। কারণ , তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তাঁর ইচ্ছার মধ্যে শুধু সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিটির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রকৃতি ও তার উপাদান-উপকরণই শামিল থাকে না , বরং স্থানগত , কালগত ও প্রক্রিয়াগত উপাদানও শামিল থাকে এবং তদনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় যথাসময়ে ও যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টির আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে কোনো সৃষ্টিকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারেন , কিন্তু তাঁর জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে , তিনি কেবল তাৎক্ষণিক ও মাধ্যম বিহীন সৃষ্টির ইচ্ছা করবেন এবং বিলম্বে কার্যকরোপযোগী ও মাধ্যম বিশিষ্ট সৃষ্টির ইচ্ছা করবেন না। বরং তিনি উভয় ধরনের সৃষ্টিরই ইচ্ছা করতে পারেন এবং যা-ই ইচ্ছা করেন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই তার আবির্ভাব অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি চাইলে দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাকেও তাঁর ইচ্ছায় শামিল রাখতে পারেন।
আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি-ইচ্ছা যে তাৎক্ষণিকভাবে ও বিনা মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য নয় তার অন্যতম প্রমাণ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা‘ আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন: ( انی جاعل فی الارض خليفة ) -“ অবশ্যই আমি ধরণীর বুকে প্রতিনিধি নিয়োগকারী।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৩০) এর মানে হচ্ছে , আল্লাহ্ তা‘ আলা যে হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টির ইচ্ছা করেন (সৃষ্টি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন) তা করেন ফেরেশতাদেরকে জানানোর আগেই। কিন্তু তিনি তাঁর এ ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ইচ্ছা করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তেই করেন নি , বরং আরো পরে তা বাস্তবায়ন করেন। শুধু তা-ই নয় , আসমানী কিতাবধারী সকল ধর্মের অভিন্ন মত অনুযায়ী , আল্লাহ্ তা‘ আলার নির্দেশে ফেরেশতারাই হযরত আদম (আঃ)-এর বস্তুগত দেহ তৈরী করেছিলো , যদিও আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে হযরত আদম (আঃ) মাটির উপাদান ও ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই অস্তিত্বলাভ করতেন। তবে সে ক্ষেত্রে মাটির গুণ ও ফেরেশতাদের কর্মক্ষমতা প্রকাশ পেতো না-যা প্রকাশ পাওয়ায় যিনি মাটি ও ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মাহাত্ম্য অধিকতর মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।
আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ সৃষ্টি-ইচ্ছার (قضاء تکوينی الاهی ) বাস্তবায়ন যে তাৎক্ষণিক বা বিনা মাধ্যমে হওয়া অপরিহার্য নয় , বরং তাঁর ইচ্ছায় পুরোপুরি বা আংশিক প্রাকৃতিক কারণ ও অপ্রাকৃতিক মাধ্যম শামিল থাকতে পারে এবং ইচ্ছাকরণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে কালগত ব্যবধানও তাঁর ইচ্ছায় শামিল থাকতে পারে-হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ঘটনা তার আরেকটি প্রমাণ।
আল্লাহ্ তা‘ আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে উদ্দেশ করে এরশাদ করেন:“ (হে রাসূল!) স্মরণ করুন , ফেরেশতারা বললো: হে মারইয়াম! অবশ্যই আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এক বাণীর (তাঁর বাণীর মূর্ত প্রতীক-এর) সুসংবাদ দিচ্ছেন ; তাঁর নাম মাসীহ্ ঈসা ইবনে মারইয়াম।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ৫) এ থেকে সুস্পষ্ট যে , এ সুসংবাদ হযরত মারইয়াম (আঃ)কে প্রদানের পূর্বেই আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁকে সৃষ্টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাথে সাথেই হযরত ঈসা (আঃ) সৃষ্টি হন নি। অতঃপর এ সুসংবাদ পেয়ে হযরত মারইয়াম (আঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন:“ হে আমার রব! কী করে আমার সন্তান হবে যখন কোনো মানুষ (পুরুষ) আমাকে স্পর্শ করে নি ?” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ৪৭) তখন আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁকে ওয়াহী করে বলেন:
( كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )
“ এভাবেই (হবে ; কারণ ,) আল্লাহ্ যাকে চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন তখন নিঃসন্দেহে তাকে বলেন:“ হও ,” অতএব , তা হয়ে যায়।” (সূরাহ্ আালে‘ ইমরান্: ৪৭)
কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলা হযরত ঈসা (আঃ)কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও সাথে সাথে বিনা মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টি করেন নি ; বরং আংশিক প্রাকৃতিক কারণ (মাতা)-এর মাধ্যমে কিছুটা সময় নিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ এ আংশিক প্রাকৃতিক কারণ ও সময় সহই আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছিলেন ; তাৎক্ষণিক ও বিনা মাধ্যমে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন নি ।
বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি সংক্রান্ত বিশেষ ইচ্ছার বিষয়টি নতুন সৃষ্টি-উপাদান বা নতুন প্রজাতি সৃষ্টিকরণ এবং সৃষ্টিলোকের চলমান প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে হস্তক্ষেপকরণ-এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্ট কারণবিধির আওতায় স্বাভাবিকভাবে চলমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ প্রক্রিয়ার সূচনা ও তার নিয়মবিধি আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ সৃষ্টি-ইচ্ছারই প্রতিফলন , অতঃপর এর ধারাবাহিকতা তাঁর সর্বজনীন ইচ্ছারই আওতায় অব্যাহত রয়েছে যার মধ্যে দুই সম্ভাবনা (محو و اثبات )ও অন্তর্ভুক্ত এবং সৃষ্টিকর্মের পূর্ণ কারণের মধ্যে সৃষ্টির অংশগ্রহণ এই দুই সম্ভাবনারই আওতাভুক্ত বিষয়।
সংক্ষেপে , আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি-ইচ্ছা বা সৃষ্টিকার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া দুই ধরনের বলে আমরা দেখতে পাই:
(১) আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি-ইচ্ছা। এতে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন ও অব্যাহত থাকার প্রক্রিয়া , আবির্ভাবের স্থান ও কাল এবং অস্তিত্বলাভের উপায়-উপকরণ ও প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। তার উপায়-উপকরণ প্রকৃতি থেকে নেয়া হবে , নাকি তা সরাসরি সৃষ্টি করা হবে তা-ও তাঁর ইচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।
(২) আল্লাহ্ তা‘ আলার পরোক্ষ বা সর্বজনীন সৃষ্টি-ইচ্ছা। আল্লাহ্ তা‘ আলার এ সৃষ্টি-ইচ্ছার মধ্যে একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত ভবিষ্যতও অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বা পূর্ণ কারণ বিদ্যমান হলে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হবে , নচেৎ তা হবে না। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকার্যে ভূমিকা পালনকারী উপাদান সমূহ যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টি , সে হিসেবে এ সব উপাদানের ভূমিকা আল্লাহ্ তা‘ আলার পরোক্ষ সৃষ্টি-ইচ্ছার আওতাভুক্ত। এ উপাদানগুলো হচ্ছে:
১। আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধিবিধান ,
২। আল্লাহ্ তা‘ আলার পূর্ণ অনুগত সৃষ্টি ফেরশতাগণ ,
৩। প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়ের সহজাত প্রবণতা ,
৪। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়ের সহজাত প্রবণতা এবং
৫। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টি (মানুষ ও জিন্)।
কিন্তু সৃষ্টিতে ত্রুটির কারণ কেবল সৃষ্টিকর্মে সৃষ্টির অংশগ্রহণই নয় , বরং সৃষ্টির স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক ভূমিকাও দায়ী। সৃষ্টিকর্মে অংশগ্রহণ একটি ইতিবাচক ভূমিকা , যদিও ভূমিকা পালনকারীদের অনেকের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কারণে সৃষ্টিতে ত্রুটি প্রকাশ পেতে পারে। অন্যদিকে গোটা সৃষ্টিব্যবস্থার বৃহত্তর লক্ষ্যে তথা পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা‘ আলা বিভিন্ন সৃষ্টির বিকাশ ও স্বার্থের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও সাংঘর্ষিকতা নিহিত রেখেছেন। এই সাংঘর্ষিকতা ও স্বার্থদ্বন্দ্ব একদিকে যেমন দৃশ্যতঃ কতক সৃষ্টির জন্য অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি করে , তেমনি তার প্রভাব নেতিবাচক হিসেবে দেখা যায় তথা কোনো কোনো সৃষ্টিতে ত্রুটি আকারে প্রকাশ পায়। অন্য কথায় , আল্লাহ্ তা‘ আলা তাঁর সৃষ্টিব্যবস্থাপনায় এমন ব্যবস্থা রেখেছেন যার ফলে এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির জন্ম , বিকাশ , বিস্তার ও পূর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ , একটি বড় গাছের নীচে গজানো একটি চারাগাছ পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিকাশ লাভে সক্ষম হয় না। একটি পোকার জীবনধারণ , বিকাশ ও পূর্ণতার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন , কিন্তু এই পোকাটির প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে একটি ফল বা একটি উদ্ভিদ , এমনকি বিশালায়তন একটি বৃক্ষ ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো প্রাণী অপর কোনো কোনো প্রাণীকে ভক্ষণ করে যা শেষোক্তদের জন্য অবাঞ্ছিত। আবার রোগজীবাণু বা অন্য কোনো কিছুর নেতিবাচক প্রভাবে মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে ত্রুটি (যেমন: বিকলাঙ্গতা , অন্ধত্ব ইত্যাদি) প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এই সাংঘর্ষিকতার মধ্যে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিকুলের কল্যাণ বা স্বার্থ নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ , বিভিন্ন প্রাণী একে অপরকে খায় বলেই বিশ্বে প্রাণী প্রজাতি সমূহের মধ্যে সংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় থাকে ও স্থানসঙ্কুলানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ , বিভিন্ন ধরনের মাছ ও পাখী বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে। এ না হলে মানুষ ও পশুপাখীর জন্য কোনো পানযোগ্য পানি ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণোপযোগী বায়ু এবং বিচরণ করার মতো কোনো ভূখণ্ড অবশিষ্ট থাকতো না। তাছাড়া উদ্ভিদ , পোকামাকড় , কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণী প্রজাতিকে অন্যদের ভক্ষণ হতে নিরাপদ রাখা হলে তথা কোনো প্রাণীর মধ্যেই অন্য প্রাণীকে ভক্ষণের স্পৃহা সৃষ্টি করা না হলে প্রাণীকুলের জন্য খাদ্য হিসেবে শুধু জড় পদার্থ তথা মাটি ও পানি গ্রহণের স্পৃহা সৃষ্টি করতে হতো। তাহলে প্রাণীকুলের মধ্যে কোনো ধরনের আন্তঃক্রিয়াই সংঘটিত হতো না এবং আন্তঃক্রিয়া থেকে তাদের মধ্যকার যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য তথা প্রবণতা ও সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা ঘটতো না। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে সকল প্রজাতি হতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন তথা কখনোই পরস্পর মিলিত হবে না এমন সরল রেখার মতো। সে ক্ষেত্রে জড়দেহে চেতনার অধিকারী সৃষ্টিনিচয়ের পরিবর্তে কেবল ফেরেশতা সৃষ্টি করাই বিধেয় হতো। কিন্তু তার ফলে আল্লাহ্ তা‘ আলার সৃষ্টিক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ সীমিত হয়ে পড়তো।
অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে , রোগজীবাণুর অস্তিত্ব মানুষের জন্য কষ্টের ও তাদের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টির কারণ হলেও তা চিকিৎসা-গবেষণার প্রেরণাদাতাস্বরূপ ভূমিকা পালন করেছে এবং এর ফলে মানুষের নিকট বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণ ও মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বিস্ময়কর জটিল ব্যবস্থাপনার জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে। রোগজীবাণু , রোগব্যাধি এবং মানুষ , প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে ত্রুটি না থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটতো না এবং মানুষ আল্লাহ্ তা‘ আলার বহু সৃষ্টি সম্বন্ধে জানা ও তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিকুশলতা অনুভব করা থেকে বঞ্চিত থাকতো।
মোদ্দা কথা , সৃষ্টিতে ত্রুটি ও দুর্বলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে সাংঘর্ষিকতা ও স্বার্থদ্বন্দ্ব যা সমগ্র সৃষ্টিব্যবস্থাকে পূর্ণতায় উপনীত করার জন্য অপরিহার্য।
উপসংহার
আমরা পুরো আলোচনা থেকে এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে , মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্ম ও পরিণতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাবর্ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের চিন্তাধারা ভ্রান্ত। আল্লাহ্ তা‘ আলা প্রতিটি মানুষের জীবন , কর্ম ও চূড়ান্ত পরিণতির সব কিছু তাকে সৃষ্টি করার পূর্বে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘটিত হচ্ছে অথবা আল্লাহ্ তা‘ আলা স্বয়ং প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদন করছেন বা তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন-এ ধারণা ঠিক নয়। তেমনি মানুষ এ দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি স্বাধীন এবং আল্লাহ্ তা‘ আলা তার কোনো কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না-এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সঠিক বিষয় এর মাঝামাঝি। তা হচ্ছে , মানুষকে পার্থিব জীবনে স্বাধীন এখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা দেয়া হয়েছে , তবে বিভিন্ন পার্থিব তথা প্রাকৃতিক ও প্রাণীজ কারণ সে এখতিয়ার ও কর্মক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ , ব্যাহত ও সঙ্কুচিত করে। তেমনি আল্লাহ্ তা‘ আলা এ সৃষ্টিলোকের প্রতি ও বিশেষভাবে মানুষের প্রতি সব সময় দৃষ্টি রাখেন এবং সাধারণভাবে মানুষকে প্রদত্ত স্বাধীন এখতিয়ার ও কর্মক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করলেও সৃষ্টিলোককে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং সমষ্টি ও ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হলে তাতে হস্তক্ষেপ করেন।
দ্বিতীয়তঃ পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ মানুষকে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করায় পার্থিব দৃষ্টিতে সে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয় বটে , কিন্তু পরকালীন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে বিশেষ হস্তক্ষেপ হতে পারে , তবে সে হস্তক্ষেপের ফল পার্থিব জীবনের জন্য যা-ই হোক না কেন , চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের দৃষ্টিতে অর্থাৎ পরকালীন জীবনের জন্য অবশ্যই তা ইতিবাচক-তা তার মাত্রা যতখানিই হোক না কেন ; আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপের ফলাফল মানুষের পরকালীন জীবনের জন্য কখনোই নেতিবাচক নয়। মানুষকে এমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে যে , সে চাইলে যে কোনো অবস্থায়ই তার প্রকৃত (পরকালীন) সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে পারে ; কোনো পার্থিব কারণই তাকে চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের কবলে নিক্ষেপ করতে পারে না যদি না সে নিজেই তাকে স্বাগত জানায়।
আমরা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলোকে তালিকা আকারে এভাবে সাজাতে পারি:
১) আল্লাহ্ তা‘ আলার মূল সৃষ্টিপরিকল্পনা ও সৃষ্টিলক্ষ্য -যাকে আমরা“ ইরাদায়ে তাক্বভীনীয়ে‘ আামে ইলাহী” (আল্লাহ্ তা‘ আলার সাধারণ বা সর্বজনীন সৃষ্টি-ইচ্ছা) নামে অভিহিত করতে পারি।
২) আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক সৃষ্ট জড় উপাদান সমূহ ও জড় জগতে প্রতষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিধিবিধান। প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজীদে একেই“ তাক্বদীর্” বলা হয়েছে , যেহেতু এসব নিয়ম সুনির্দিষ্ট , অপরিবর্তনীয় ও সৃষ্টিকুলের জন্য অলঙ্ঘনীয়। ফেরেশতাদের কাজের একটি অংশ এ পর্যায়ের , কারণ (দ্বীনী সূত্রের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী) তারা সৃষ্টিজগতের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্ তা‘ আলার স্থায়ী নির্দেশ কার্যকর করে মাত্র ; তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কিছুই করে না। ফলে তাদের কাজ মানুষের ভাগ্যের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা প্রাকৃতিক বিধিবিধানেরই অনুরূপ। [ফেরেশতাদের কাজের অপর অংশটি আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ ইচ্ছা বা হস্তক্ষেপ কার্যকরকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।]
৩) প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়। এই প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়কে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের জীবন ও পার্থিব ভাগ্যকে কমবেশী প্রভাবিত করতে পারে: (ক) উদ্ভিদ , (খ) রোগজীবাণু , (গ) সহজাত প্রবণতার অধিকারী প্রাণীকুল , যেমন: সাপ , ব্যাঙ , ইঁদুর , ইত্যাদি , (ঘ) একই সাথে সহজাত প্রবণতা ও বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্)-এর অধিকারী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার সম্পন্ন প্রাণী (অন্য মানুষ ও জিন্)।
(৪) আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে সাধারণ ও বিশেষ পথনির্দেশ। সাধারণ পথনির্দেশ হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষের সহজাত প্রবণতা , বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) ও তার সত্তায় নিহিতি ভালো-মন্দের জ্ঞান। আর বিশেষ পথনির্দেশ হচ্ছে ওয়াহী ও ইলহাম্-যা তার প্রাপককেই শুধু নয় , বরং অন্যদেরকেও প্রভাবিত করে। এর মধ্যে শেষোক্ত পথনির্দেশ অর্থাৎ ইলহাম্ সর্বজনীন দ্বীনী বিষয়েও হতে পারে , আবার সর্বজনীন পার্থিব বিষয়েও (যেমন: আবিষ্কার-উদ্ভাবন) হতে পারে , তেমনি তা নেহায়েত ব্যক্তিগত বিষয়েও হতে পারে।
(৫) আল্লাহ্ তা‘ আলার বিশেষ ফয়সালা বা বিশেষ হস্তক্ষেপ যাকে আমরা“ ক্বাযায়ে ইলাহীয়ে খাছ্ব” নামে অভিহিত করতে পারি। এ বিশেষ হস্তক্ষেপ দু’ টি ক্ষেত্রে মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে: পার্থিব ও পারলৌকিক। তেমনি তা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হতে পারে , সমষ্টির ক্ষেত্রেও হতে পারে। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা‘ আলার পক্ষ থেকে দু’ টি লক্ষ্যে এ হস্তক্ষেপ হতে পারে: (ক) গোটা সৃষ্টিলোককে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য অপরিহার্য হলে-যা ব্যক্তি-মানুষ , সমষ্টি , এমনকি গোটা মানবকুলের জন্য পার্থিব দৃষ্টিতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। [স্মর্তব্য , প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে তিনি মানব প্রজাতিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্য কোনো প্রজাতি সৃষ্টি করে তাকে খেলাফত প্রদান করবেন।] (খ) ব্যক্তিবিশেষ , সমষ্টিবিশেষ বা সমগ্র মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে-যা পার্থিব দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ কল্যাণকর বা অকল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে , কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতির বিচারে তা পার্থিব বা পরকালীন বা উভয় জীবনের জন্যই অবশ্যই কল্যাণকর।
(৬) মানুষের ব্যক্তিসত্তা (নাফ্স্)-যে তার পার্থিব ভাগ্যের ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান এবং চূড়ান্ত (পরকালীন) সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র সিদ্ধান্তকর উপাদান। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তথা পরকালীন ব্যাপারে সে যা চায় তা থেকে তাকে বিরত রাখার ক্ষমতা কারোই নেই একমাত্র আল্লাহ্ তা‘ আলা ছাড়া ; কিন্তু আল্লাহ্ তা‘ আলা তার এতদসংক্রান্ত‘ সিদ্ধান্তে’ হস্তক্ষেপ করেন না। তবে দুর্ভাগ্যের পথ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সে যতক্ষণ পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত না নেয় , বা ঔদ্ধত্যের আশ্রয় না নেয় বা এ পথে বেশীদূর অগ্রসর না হয় ততক্ষণ আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে অনুগ্রহপূর্বক তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে তার মধ্যে ঐ পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের পথ বেছে নিয়েছে আল্লাহ্ তা‘ আলা চাইলে তার দুর্বলতা বিবেচনা করে , বিশেষ করে সে আল্লাহ্ তা‘ আলার সাহায্য কামনা করলে , তাকে সাহায্য করেন।
এই নাফ্স্ বা ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনেকগুলো প্রভাবশালী গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে যা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এ সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা , আশা-আকাঙ্ক্ষা , হতাশা , ভাবাবেগ , ঘৃণা-বিদ্বেষ , হিংসা , হিংস্রতা , দয়া , মায়ামমতা , প্রেম-ভালোবাসা , স্নেহ-প্রীতি , লোভ-লালসা , সৌন্দর্যপ্রিয়তা , যৌন কামনা , ক্ষুৎপিপাসা , প্রশংসাপ্রিয়তা , নেতৃত্বলিপ্সা , সম্পদলিপ্সা এবং অন্যের ভালোবাসা ও ঘৃণা , নিন্দা ও প্রশংসা , আদর ও তিরস্কার , অনুরোধ ও শাসনে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন ইত্যাদি খুবই শক্তিশালী উপাদান। এ সব উপাদানের প্রতিটিই পরিচর্যায় কমবেশী বৃদ্ধি পায় এবং শাসনে বা দমনে কমবেশী হ্রাস পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যা , আত্মহত্যা , আত্মত্যাগ (দেশ , দ্বীন বা অন্য কিছু বা কারো জন্য জীবন দান) , ধনসম্পদ ত্যাগ , সংসার ত্যাগ , ইত্যাদির ন্যায় তীব্র ও প্রান্তিক কাজ নাফসের কোনো না কোনো গুণের প্রাবল্যের ফসল। অবশ্য মানুষের বিচারবুদ্ধি (‘ আক্বল্) সর্বাবস্থায়ই ন্যায়-অন্যায় , ভালো-মন্দ , সত্য-মিথ্যা ও উচিত-অনুচিতের পার্থক্য করতে ও ইতিবাচক পথ বেছে নিতে সক্ষম। কিন্তু ব্যক্তি স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে নেতিবাচক গুণের পরিচর্যা ও ইতিবাচক গুণের দমনে এতদূর অগ্রসর হতে পারে যার ফলে নেতিবাচক গুণগুলো তার বিচারবুদ্ধিকে দুর্বল , পরাভূত ও আচ্ছন্ন করে ফেলে , অতঃপর আর তার বিচারবুদ্ধির পক্ষে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না বা হলেও নাফসের পক্ষে আর বিচারবুদ্ধির রায় মেনে চলা সম্ভব হয় না।
পরিশিষ্ট :
আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
জাবর্ ও এখতিয়ার্ কালাম্ শাস্ত্রের ও ইসলামী‘ আক্বাএদের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন বিতর্কের বিষয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে এই যে , না নিরঙ্কুশ জাবর্ , না নিরঙ্কুশ এখতিয়ার্ , বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। কিন্তু জাবর্ ও এখতিয়ার্ সংক্রান্ত আলোচনায় জটিলতম গিঁট হচ্ছে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞানের সংজ্ঞা। কারণ , নিরঙ্কুশ জাবর্-এর প্রবক্তাদের মত হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা স্বীয় অনাদিকালীন জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অবহিত , আর তাঁর‘ ইলমের অন্যথা হতে পারে না , সুতরাং বান্দাহ্ মোটেই এখতিয়ারের অধিকারী নয়। (এটা মানলে বলতে হবে যে , বান্দাহদের কোনোই দায়-দায়িত্ব নেই।) এ মতের জবাবে বলা হয় , এটা অসম্ভব যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করবেন , অথচ আমরা দেখতে পাই যে , বান্দাহরা মন্দ কাজ করে থাকে।
অবশ্য এ বিষয়ে অতীতে অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং এখনো এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আমি আমার অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি , সুতরাং এখানে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করছি না। এখানে আমরা শুধু সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলম্-এর প্রকৃতি বা ধরন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।
যে বিষয়টি আমাকে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এ সম্পর্কে‘ না জাবর্ , না এখ্তিয়ার্ , বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা’ র প্রবক্তাদের মধ্যকার কারো কারো মত-যা এ বিষয়ে জাবারীদের মতেরই অনুরূপ।
মনীষী অধ্যাপক ও স্বনামখ্যাত ইসলাম-গবেষক হযরত আয়াতুল্লাহ্ নাছ্বের্ মাকারেম শীরাযীর তত্ত্বাবধানে একদল মনীষী লেখকের দ্বারা ফার্সী ভাষায় প্রণীত তাফ্সীরে নামুনে নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান তাফসীরগ্রন্থ। সম্প্রতি (২০১২ সালে) এ তাফসীরগ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং এটির প্রথম খণ্ডের অনুবাদের দায়িত্ব অত্র লেখকের ওপর অর্পিত হয়। অনুবাদের শর্ত ছিলো এই যে , মূল ফার্সীতে যা আছে তা হুবহু ও নির্ভুলভাবে অনুবাদ করা হবে এবং অনুবাদকের দৃষ্টিতে মূল গ্রন্থে কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি ধরা পড়লে সে সম্বন্ধে নোট আকারে স্বতন্ত্রভাবে লিখে অনুবাদ-প্রকাশকের গোচরে আনতে হবে যাতে তা মূল গ্রন্থের লেখকদের জানানো হয়। এ শর্ত অনুযায়ী কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। কিন্তু যেহেতু দু’ একটি বিষয় এমন ছিলো যে , তা কেবল রচনাশৈলীর দুর্বলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না , বরং প্রকাশিত মতামত সঠিক বা ভুল হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো , আর তা কেবল উক্ত তাফসীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না , সেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার মতামত মনীষী ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের গোচরে আনার প্রয়োজন অনুভব করছি। এ সব বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে সৃষ্টিকুল সম্বন্ধে , বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞান।
১৩৭২ ইরানী সালের বসন্তকালে প্রকাশিত উক্ত তাফসীরের প্রথম খণ্ডের ৪৮৯ নং পৃষ্ঠায় সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহর ১৪৩ নং আয়াত ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ ) عَلَى عَقِبَيْهِ -এর ব্যাখ্যায়تفسیر جمله لنعلم উপশিরোনামে বলা হয়েছে:
“ আলোচ্য আয়াতেلنعلم (যাতে আমি জানতে পারি) কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআন মজীদে এ ধরনের আরো কিছু কথা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা ঐ সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতেন না এবং পরে অবগত হয়েছেন। বরং এরূপ ক্ষেত্রে‘ জানা’ মানে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বাস্তবতাটি কার্যতঃ সংঘটিত হওয়া।
“ ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তা‘ আলা অনাদি কাল থেকেই সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবগত যদিও তা ক্রমান্বয়ে অস্তিত্বলাভ করে বা সংঘটিত হয়। অতএব , ঘটনাবলীর সংঘটিত হওয়া ও সৃষ্টিসমূহের অস্তিত্বলাভ আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলমে কিছু যোগ করে না , বরং তিনি পূর্ব থেকেই যা জানতেন তা-ই এভাবে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। এর তুলনা হচ্ছে এই যে , একজন স্থপতি একটি ভবনের নকশা তৈরী করলেন এবং এর ছোট-বড় ও খুঁটিনাটি সব কিছুই তিনি এটি নির্মিত হওয়ার আগেই জানেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে এ নকশাটির বাস্তবায়ন করেন। উক্ত স্থপতি যখন নকশাটির অংশবিশেষ বাস্তব রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি বলেন , এ কাজটি এ উদ্দেশ্যে করছি যে , যা আমি করতে চাচ্ছিলাম তা বাস্তবে দেখতে পারি। অর্থাৎ আমার জ্ঞানে যে নকশা রয়েছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবো। (আমরা আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনায় যেমন বলেছি , নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘ আলার জ্ঞান ও মানুষের জ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে ; এখানে উপমা দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টিকে সুস্পষ্টতর করা।)” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]
এ বিষয়ে প্রায় সকল তাফসীরেই মোটামুটি একই ধরনের মতামত চোখে পড়ে। কিন্তু কেবল ব্যবহৃত শব্দাবলীর পার্থক্য ছাড়া উপরোক্ত মতের ও জাবারী মতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ , যদি এমনটাই হয়ে থাকে যে , সৃষ্টিকুলের , বিশেষতঃ মানবকুলের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী খুটিনাটি সহ আল্লাহ্ তা‘ আলার অনাদি‘ ইলমে মওজূদ থেকে থাকে তাহলে তা সংঘটিত হওয়া অনিবার্য। (তাহলে সৃষ্টিকুলকে স্বীয় কাজের জন্য দায়ী গণ্য করা চলে না।) আর এ মত“ আমর্ বাইনাল্ আমরাইন্” মতের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।
দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘ আলার প্রতি অজ্ঞতা আরোপের ভয় থেকেই উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। আর এ ভয়ের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলমের , বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর‘ ইলমের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি নির্ভুলভাবে মনোযোগ (توجه ) প্রদানে ব্যর্থতা।
উক্ত তাফসীরে ব্যক্ত উপরোক্ত অভিমতটি যে ভুল তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এই যে , একজন ফাছ্বীহ্ ও বালীগ্ব্ বক্তা বা লেখক স্বীয় বক্তব্যে ঠিক সেই সব শব্দ ব্যবহার করেন যা তাঁর উদ্দেশ্যকে নির্ভুলভাবে বুঝানোর জন্য উপযোগী। সুতরাং এখানে আল্লাহ্ তা‘ আলার উদ্দেশ্য যদি‘ বাস্তবতা কার্যতঃ সংঘটিত হওয়া’ হতো তাহলে তিনি‘ জেনে নেয়া’ কথাটি ব্যবহার করতেন না।
দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি ধরে নেই যে , উপরোক্ত মতটি সঠিক তাহলে প্রশ্ন জাগে যে , আল্লাহ্ তা‘ আলা কি এটাই চাচ্ছিলেন যে , তিনি স্বয়ং যা তাঁর অনাদি‘ ইলমে স্বীয় বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন-যাতে তাঁর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কারো কারো ফরমানবরদারী ও কারো কারো নাফরমানী শামিল রয়েছে-‘ বাস্তবতা কার্যতঃ সংঘটিত’ করবেন ? সে ক্ষেত্রে বান্দাহদের দায়িত্বশীলতা কী ?
তৃতীয়তঃ ভবিষ্যতের সমস্ত কিছুই যদি আল্লাহ্ তা‘ আলার অনাদি‘ ইলমে শামিল থেকে থাকে তাহলে কেবল যে স্বীয় কর্মের জন্য বান্দাহদের কোনোই দায়-দায়িত্ব থাকা উচিত নয় শুধু তা-ই নয় , বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘ আলার জন্যও আর করণীয় কিছুই থাকার কথা নয়। কারণ , সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যা কিছুই তাঁর অনাদি‘ ইলমে ছিলো তা-ই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যথাসময়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে তাঁর জন্য নতুন কোনো কাজের বা নতুন কোনো ইচ্ছারই অবকাশ থাকে না। আর ইয়াহূদীরা যে বলতোيد الله مغلولة (আল্লাহর হাত সংবদ্ধ) মূলে হয়তো তা এ অর্থেই ছিলো , অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে , আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছাকরণ ও সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন (خلاقِيت ) চিরন্তন এবং তা কখনোই সমাপ্ত হবে না।
এখানে যা সঠিক বলে মনে হয় তা হচ্ছে , আমরা আমাদের নিজেদের অনুভূতির ভিত্তিতে যে বলি ,“ অতীতে সৃষ্টিকর্মের সূচনার আগে আল্লাহ্ তা‘ আলা যখন সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন” তিনি যখন তাতে ইচ্ছা করেন যে , তিনি ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী কতক সৃষ্টিকে , বিশেষ করে মানুষকে সৃষ্টি করবেন-যারা আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলীর অধিকারী (যদিও সীমিত মাত্রায়) হবে এবং এ কারণে তারা নিজেদের ও বিশ্বজগতের ওপর প্রভাবের (ক্রিয়ার) অধিকারী হবে সেহেতু যদিও ফেরেশতাকুল , প্রাকৃতিক বিধিবিধান ও সৃষ্টিকর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্যর প্রশ্নে তাঁর তাওয়াজ্জুহ্ অকাট্যভাবে সংশ্লিষ্ট হয় , কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টিনিচয়ের ভবিষ্যত ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রটির আওতাভুক্ত কতক বিষয়ে তিনি তাঁর তাওয়াজ্জুহকে বিকল্প সহকারে বা শর্তাধীনতা সহকারে সংশ্লিষ্ট করেন। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার সংশ্লিষ্টতা এরূপ যে , ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টিসমূহ (যে সৃষ্টি যে পরিমাণেই তার অধিকারী হোক না কেন) যদি অমুক কাজ সম্পাদন করে তাহলে অমুক ফল সংঘটিত হবে এবং যদি অমুক (অন্য একটি) কাজ সম্পাদন করে তাহলে অমুক (অন্য একটি) ফল সংঘটিত হবে। আর আল্লাহ্ তা‘ আলা কর্তৃক ইচ্ছাকরণের পর থেকে এটাই‘ বিলুপ্তি ও স্থিতির লাওহে’ (لوح محو و اثبات ) মওজূদ্ ছিলো । ফলে বান্দাহ্ যখন ঐ বিকল্প সম্ভাবনার মধ্য থেকে কোনো একটি কাজ আঞ্জাম দেয় তখন থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য তা ও তার প্রভাব (ক্রিয়া) সমূহ স্থিতি লাভ করে। আর এ শর্তাধীনতা কেবল দু’ টি সম্ভাবনার মধ্যে সীমিত থাকে না , বরং অনেক বিষয়েই দুই-এর অধিক সম্ভাবনা , বরং বিপুল সংখ্যক সম্ভাবনা নিহিত থাকে। দৃশ্যতঃ মনে হয় যে , আমরা নিঃশর্তভাবে‘ ভবিষ্যত’ বলে যা বুঝিয়ে থাকি আল্লাহ্ তা‘ আলা তার বিরাট অংশকেই স্বীয় অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় তাওয়াজ্জুহর বাইরে শর্তাধীন ও পরিবর্তনীয়রূপে রেখে দিয়েছেন। আর‘ ভবিষ্যত’ -এর এ অংশে অনবরত আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা‘ নতুন সৃষ্টি’ (خلق جديد )-এর প্রতি সংশ্লিষ্ট হতে থাকে , তেমনি‘ ভবিষ্যত’ -এর ঐ অংশের অংশবিশেষ ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টিসমূহের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা জাত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাবের দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে।
আল্লাহ্ তা‘ আলা যখন এরশাদ করেন:إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد -“ তিনি যদি চান তো তোমাদেরকে অপসারিত করে দেবেন এবং একটি নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন।” (সূরাহ্ ইবরাহীম্: ১৯ ও সূরাহ্ আল্-ফাত্বের: ১৬) তখন এর মানে হচ্ছে এই যে , মানব প্রজাতিকে অপসারিত করা বা না করার প্রতি এবং তার স্থলে কোনো (অনির্দিষ্ট) নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করা বা না করার প্রতি আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা ও তাওয়াজ্জুহ্“ এখনো” সংশ্লিষ্ট হয় নি।
এখানে উল্লেখ্য যে , কালের প্রবাহে ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টিসমূহের এখতিয়ারাধীন বিষয়াদিতে আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপের বিষয়টিও এ পর্যায়ের বলে মনে হয়। এর মানে হচ্ছে , ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টিসমূহের এখতিয়ারাধীন বিষয়াদিতে আল্লাহ্ তা‘ আলার হস্তক্ষেপের বিষয়টি আল্লাহ্ তা‘ আলার অনাদি জ্ঞানে নীতিগতভাবে কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘ আলা যদি চান তাহলে তিনি ব্যক্তি বা সমষ্টির কল্যাণে বা সৃষ্টিলক্ষ্যের স্বার্থে সৃষ্টিকুলের এখতিয়ারাধীন বিষয়াদিতে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করেন ও করবেন , কিন্তু সেই শুরুতেই অর্থাৎ অনাদিকালে এর বিস্তারিত বিষয়াদিতে ও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর অনাদি ইচ্ছা ও তাওয়াজ্জুহ্ সংশ্লিষ্ট হয় নি। তেমনি তাঁর অনাদি‘ ইলমে নীতিগতভাবে ও সাধারণভাবে কিন্তু অনির্দিষ্টরূপে নিহিত ছিলো যে , ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সহ আল্লাহ্ তা‘ আলার গুণাবলীর অধিকারী এমন সৃষ্টিনিচয়ের মধ্য থেকে কতক দুর্বল (নৈতিক-চারিত্রিক দিক থেকে) সৃষ্টি অবশ্যই এ সব গুণের অপব্যবহার করবে , কিন্তু তাঁর‘ ইলম্ ও তাওয়াজ্জুহ্ এর বিস্তারিত রূপের প্রতি অর্থাৎ ঠিক কোন্ কোন্ ব্যক্তি এ অপব্যবহার করবে তার প্রতি সংশ্লিষ্টতা লাভ করে নি। উদাহরণস্বরূপ , হযরত ইমাম হুসাইন্ (‘ আঃ)-এর ঘাতক কে হবে আল্লাহর অনাদি‘ ইলমে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত ছিলো না , কিন্তু কালের প্রবাহে বান্দাহদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে পথ বেছে নেয়ার পরিণামে তা অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্য থেকে কয়েকটি পরস্পর বিকল্প সম্ভাবনায় সীমিত হয়ে যায় এবং পরে সম্ভবতঃ দুই সম্ভাবনার মধ্য থেকে নিশ্চিত হয়ে যায় যে , ঐ ব্যক্তি হবে শীমার। তেমনি এ ঘটনা সংঘটিত হবার স্থান ও সময় এবং অন্যান্য খুটিনাটি বিস্তারিত বিষয় অসংখ্য পরস্পর বিকল্প সম্ভাবনার মধ্য থেকে কালের প্রবাহে ক্রমান্বয়ে সীমিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়।
এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয় যে , এ বিষয়ে তাফ্সীরে নামুনের উপস্থাপিত ধারণার (অর্থাৎ‘ জানা’ বলতে‘ বাস্তব রূপ প্রদান’ বুঝানো হয়েছে-এ দাবীর) সমর্থনে অন্যত্র কোরআন মজীদ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।
“ যেহেতু আল্লাহ্ তা‘ আলা সব কিছু জানেন তাহলে পরীক্ষা কী জন্য ?” -এ প্রশ্নের জবাবে উক্ত তাফসীরের উক্ত খণ্ডের ৫২৭ নং পৃষ্ঠায় সূরাহ্ আালে‘ ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে , পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে এবং আল্লাহ্ তা‘ আলা অবগত আছেন-তাকে সুস্পষ্ট করে দেয়া।
এখানে‘ দৃশ্যতঃ অভিন্ন’ এমন বিভিন্ন শব্দ (اشتراک لفظی ) থেকে ভুলের উদ্ভব হয়েছে। কারণ , সমস্ত রকমের পরীক্ষার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অভিন্ন নয়। সৃষ্টির অন্তঃকরণে যা লুক্কায়িত আছে তাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে পরীক্ষা এবং সৃষ্টির অন্তঃকরণে এখনো যা ইচ্ছা হিসেবে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নি তাকে সুনির্দিষ্ট হবার পথে এগিয়ে দেয়ার জন্য পরীক্ষা অভিন্ন নয়। প্রথম ক্ষেত্রে‘ জানার জন্য পরীক্ষা’ বলতে‘ জানা’ মানে যা বান্দাহর অন্তঃকরণে আছে এবং আল্লাহ্ জানেন তা‘ সুস্পষ্ট করা’ বা অন্য কথায় ,‘ বাস্তবে রূপায়িতকরণ’ -এ তাৎপর্য সঠিক তাৎপর্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে‘ জানা’ থেকে এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করার উপায় নেই।
আলোচ্য বিষয়ে তাফ্সীরে নামুনে-র প্রণেতাদের কাছে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে , সৃষ্টিকুলের অন্তঃকরণ সমূহে যা কিছু আছে এবং যা আল্লাহ্ তা‘ আলা জানতেন ও এখন প্রকাশিত করে দিতে চাচ্ছেন তা কি তাঁর অনাদি‘ ইলমে হুবহু এ রকমই ছিলো , নাকি তা শর্তাধীন ছিলো বা , অন্য কথায় , তা‘ বিলোপ ও স্থিতি লাওহে’ (لوح محو و اثبات ) নিহিত ছিলো ? তা যদি তাঁর অনাদি‘ ইলমে হুবহু এ রকমই থেকে থাকে তাহলে অনিবার্যভাবেই তা জাবারী বিষয় , সুতরাং এরূপ বিষয়ের জন্য বান্দাহদেরকে দায়ী গণ্য করা যেতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে , বান্দাহ্ যতক্ষণ একটি বিষয়ে তার অন্তরে ইচ্ছা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলমে তা‘ বিলোপ ও স্থিতি’ (محو و اثبات ) রূপে ছিলো। কারো হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়াও এ পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তির দুশমনদের স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত সমূহ সহ বিভিন্ন কারণের প্রভাবে ভবিষ্যতে ঐ ব্যক্তির নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলমে-ও‘ বিলোপ ও স্থিতি’ (محو و اثبات ) রূপে ছিলো।
এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে , এমনকি আল্লাহ্ তা‘ আলার অনাদি‘ ইলমে বেহেশতীদের ও দোযখীদের‘ অনন্তকালীন’ বেহেশতী ও দোযখী জীবনের বিষয়টিও নিরঙ্কুশ বা নিঃশর্ত নয় , বরং তা শর্তাধীন সম্ভাবনা হিসেবে নিহিত রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তা‘ আলা এরশাদ করেন:
( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ )
“ অতএব , যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে এবং তারা অর্তনাদ করতে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকবে ; তারা চিরদিন তথা যতদিন আসমান সমূহ ও পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন সেখানে থাকবে যদি না (হে রাসূল!) আপনার রব অন্যথা ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহে আপনার রব সদা সর্বদাই যা কিছু ইচ্ছা করেন তা-ই সম্পাদনকারী। আর যারা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে তারা জান্নাতে যাবে: তারা চিরদিন তথা যতদিন আসমান সমূহ ও পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন সেখানে থাকবে যদি না (হে রাসূল!) আপনার রব অন্যথা ইচ্ছা করেন। (নচেৎ) এ দান সমাপ্ত হবার নয়।” (সূরাহ্ হূদ্: ১০৬-১০৮)
অত্র আলোচনার সমাপ্তি পর্যায়ে আল্লাহর‘ ইলম্-এ কিছু বৃদ্ধি না হওয়া বিষয়ক অভিমত প্রসঙ্গে বলতে হয় যে , আল্লাহ্ তা‘ আলার সত্তাগত ছ্বিফাত্ রূপ‘ ইলম্ ও ইচ্ছা এবং তাঁর সত্তা অভিন্ন , সুতরাং আল্লাহ্ তা‘ আলার এ‘ ইলম্ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ , এ ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে সদা অবগত। কিন্তু সৃষ্টিনিচয় সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা ও‘ ইলম্ হচ্ছে কর্তাবাচক’ (فاعلی ), আর তাঁর এই কর্তাবাচকতা তথা ইচ্ছা ও‘ ইলম্-এর সক্রিয়তা (فاعليت ) হচ্ছে একটি অব্যাহত সম্পর্ক ; এটা কোন‘ বার বিশিষ্ট’ (دفعی ) ক্রিয়া নয় যে , তাঁর এ ধরনের ইচ্ছা একবার সক্রিয় হয়ে এরপর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে বা আর অস্তিত্বশীল থাকবে না। অন্যদিকে সৃষ্টিকরণ রূপ ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কর্তাবাচক‘ ইলম্ (علم فاعلی ) সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকে সৃষ্টিকরণের ইচ্ছার অভিন্ন সময়ের , তাঁর কর্তাবাচক ইচ্ছার (اراده فاعلی ) অগ্রগামী নয়। সুতরাং তিনি যখন বলেন:“ যদি আল্লাহ্ চান” তখন তার মানে হচ্ছে এই যে , তিনি যা চাওয়া বা না চাওয়া (যেহেতু বলেছেন‘ যদি’ ) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তা যদি চান সে ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে তা চাওয়ার তথা ইচ্ছা করার অভিন্ন সময়ে জানবেন , তা চাওয়ার তথা ইচ্ছা করার আগে নয়। তেমনি ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সৃষ্টিনিচয় কর্তৃক ইচ্ছাকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘ আলার কর্তাবাচক‘ ইলম্ (علم فاعلی )-ও এ পর্যায়েরই অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কোনো সৃষ্টি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করে তখন অভিন্ন সময়েই আল্লাহ্ তা‘ আলা সে সম্বন্ধে অবগত হন , না তার আগে , না তার পরে। কারণ , ইচ্ছাকারীর তুলনায় তাঁর অবগতি বিলম্বিত হওয়ার (সেকেণ্ডের কোটি ভাগের এক ভাগ হলেও) তথা পরে অবগত হবার প্রশ্নই উঠতে পারে না , অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি কর্তৃক ইচ্ছা করার আগে তা অবগত না হওয়ার কারণ এই যে , তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টিনিচয়ের ভবিষ্যত ইচ্ছার প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ , তিনি তাওয়াজ্জুহ্ করলে তা আর সৃষ্টির ইচ্ছাধীন থাকবে না , বরং অনিবার্য-তে পরিণত হয়ে যাবে।
অবশ্য বিভিন্ন কারণের প্রভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভবিষ্যতে কোনো একটি বিষয় ইচ্ছাকরণ নিশ্চিত হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘ আলা তা নিশ্চিত হওয়ার সমসময়ে জানবেন যদিও ঐ ব্যক্তি তখনো তা ইচ্ছা করে নি। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত কথায় ঐ ব্যক্তির প্রতি‘ ইচ্ছাকরণ’ আরোপ করলেও এ ক্ষেত্রে বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন বিষয় নয় , বরং অন্যান্য কারণ দ্বারা তার জন্য ইচ্ছাকরণ নিশ্চিত করার কারণে তা আর স্বাধীন ইচ্ছা থাকে নি এবং প্রকৃত অর্থে ইচ্ছা মানে হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা ; যে ইচ্ছাকরণে বাধ্য করা হয়েছে (তা যে বা যারাই বাধ্য করে থাকুক না কেন) তা প্রকৃত ইচ্ছা নয়। আর এ বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে লক্ষ্যণীয় যে , এ ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তির ইচ্ছাকরণের বিষয়টি আল্লাহ্ তা‘ আলার অনাদি‘ ইলমে নিহিত ছিলো না , বরং বিভিন্ন কারণ তার ইচ্ছাকরণকে নিশ্চিত করে তোলার সমসময়েই তা আল্লাহ্ তা‘ আলার কর্তাবাচক‘ ইলমে (علم فاعلی ) সংশ্লিষ্ট হয় , যদিও এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘ আলার‘ ইলম্ ব্যক্তিটির তথাকথিত ইচ্ছাকরণ-এর (এ জন্য‘ তথাকথিত’ যে , সে বাধ্য হয়ে‘ ইচ্ছা’ করেছে) তুলনায় অগ্রগামী।
সংক্ষেপে: আল্লাহ্ তা‘ আলার ইচ্ছা ও সৃষ্টিকরণ সর্বকালীন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি যে কোনো রকমের শর্তাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে পরম প্রমুক্ত। ভবিষ্যতের যে বিষয়টি বর্তমানে অস্তিত্বহীন ও ভবিষ্যতে যার অস্তিত্বলাভও অনিশ্চিত আল্লাহ্ তা‘ আলা যখন তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ করেন নি তখন কী করে তাঁর প্রতি সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা আরোপ করা যেতে পারে ? কারো প্রতি ভবিষ্যতের কোনো কিছু সম্বন্ধে কেবল তখনই অজ্ঞতা আরোপ করা যেতে পারে যখন তার সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য হয় , অথচ ঐ ব্যক্তির বিষয়টি জানা না থাকে। তেমনি একাধিক সম্ভাবনা বিশিষ্ট ভবিষ্যত সম্বন্ধে-যার কোনো সম্ভাবনাটিরই বাস্তব রূপ লাভ নিশ্চিত নয়-তিনি যখন তার সবগুলো সম্ভাবনা সম্বন্ধেই অবগত থাকেন এবং কোনো সম্ভাবনার ভবিষ্যত বাস্তব রূপায়ন নিশ্চিত না থাকা সম্বন্ধেও অবগত থাকেন সে ক্ষেত্রেই বা কী করে বলা চলে যে , তিনি জানেন না ? তিনি যে , বলেছেন যে ,“ তিনি এখনো জানেন না।” -এর মানে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ভবিষ্যত দুই বা বহু সম্ভাবনার মধ্য থেকে কোনোটিরই বাস্তব রূপায়ন এখনো নিশ্চিত হয় নি এবং তিনি নিজেও উক্ত দুই বা বহু সম্ভাবনার মধ্য থেকে কোনো একটির প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ করতে চান না।
সূচিপত্র
ভূমিকা ২
অদৃষ্টবাদ: বিশ্বাস বনাম আচরণ ৯
কোরআন মজীদে “ ক্বাদর্ ” ও “ তাক্বদীর্ ” পরিভাষা ১২
অদৃষ্টবাদের প্রকারভেদ ১৭
অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ২০
মুসলিম সমাজে অদৃষ্টবাদ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারবাদ ২৩
জাবারীয়্যাহ্ ও মু ’ তাযিলী চিন্তাধারার আবির্ভাব ২৫
জাবারীয়্যাহ্ চিন্তাধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চার ২৭
ঘটনার পর্যালোচনা ২৮
আশ্ ‘ আরীদের যুক্তি: আল্লাহ্ নিয়ম মানতে ‘ বাধ্য ’ নন ৩৩
বিচারবুদ্ধির আলোকে জাবর্ ও এখতিয়ার ৩৬
কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ৪৫
দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক আয়াত ৪৫
মানুষের এখতিয়ার নির্দেশকারী আয়াত ৪৯
দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ নির্দেশক আয়াতের ব্যাখ্যা ৫২
শয়তানের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গ ৬১
একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত ৬৬
আল্লাহর হস্তক্ষেপ ৭১
স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কর্ম আরোপ ৭৩
মূসা ও খিজির ( আঃ ) এর ঘটনা ৮০
আল্লাহ্ ও মানুষের কাজের মধ্যে মিল-অমিল ৮৫
সৃষ্টির ত্রুটি ও অপূর্ণতার কারণ ৯২
উপসংহার ১০২
পরিশিষ্ট : ১০৬
আল্লাহ্ তা ‘ আলার জ্ঞানে সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যত ১০৬